ভারতীয় দর্শনে যে ছয়টি সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় নিঃসংশয়ে বৈদিক বা বেদমূলক। এদের একটি হলো পূর্ব-মীমাংসা বা সংক্ষেপে মীমাংসা, অন্যটি উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত।
সাধারণত বেদের চারটি পর্যায় স্বীকার করা হয়- সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। এদের মধ্যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে বলা হয় কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে, বিশেষ করে যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণগুলিতে বেদের যাজ্ঞিক ক্রিয়াকর্মের স্বরূপ এবং কর্মবিষয়ক বেদবাক্যসমূহের তাৎপর্য বিবৃত হয়েছে। তার বিচারকে বলা হয় পূর্ব-মীমাংসা। আর জ্ঞানকাণ্ড, অর্থাৎ বেদের অন্তিমভাগ বা উপনিষদ (বেদান্ত) যার মূখ্য বিষয় হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যেখানে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি এবং জ্ঞান-বিষয়ক বাক্যসমূহের অর্থ বিবৃত হয়েছে, তার বিচারকে বলা হয় উত্তর-মীমাংসা। কিন্তু দার্শনিকদের ব্যবহার অনুসারে জৈমিনি প্রবর্তিত পূর্বমীমাংসা বোঝাতে কেবল ‘মীমাংসা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়, আর উত্তর-মীমাংসা বোঝাতে সাধারণভাবে ‘বেদান্ত’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পূর্ব-মীমাংসার আরেক নাম ধর্ম-মীমাংসা বা কর্ম-মীমাংসা, এবং উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্তের আরেক নাম ব্রহ্ম-মীমাংসা। তবে এ দুই শাস্ত্রের জন্য যথাক্রমে মীমাংসা দর্শন ও বেদান্ত দর্শন এই দুটি নামই সমধিক প্রচলিত। মীমাংসাদর্শন সম্পূর্ণরূপে বেদমূলক। এতে স্বাধীন মতবাদের অবকাশ নেই বললেই চলে।
মীমাংসা-সাহিত্য
‘অনুমান’ শব্দের অর্থ যার দ্বারা পশ্চাৎ জ্ঞান হয়। যেমন, পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করে পশ্চাতে বহ্নির অস্তিত্বের অনুমান হয়। ‘অনু’ শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, আর ‘মান’ শব্দের অর্থ জ্ঞান বা প্রমা। সাধারণ অর্থে অনুমান হলো সেই জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানকে অনুসরণ করে। কোন পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করে যদি বলা হয় যে, ঐ পর্বতে অগ্নি আছে, তবে এই অগ্নির জ্ঞান অনুমানলব্ধ জ্ঞান।
অনুমান হলো পরোক্ষ জ্ঞান। তা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। কোন একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে অপর একটি অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ হয় তাকেই অনুমান বলে। অর্থাৎ অনুমানলব্ধ জ্ঞানে জ্ঞানের বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা থাকে না। ইন্দ্রিয়সংশ্লিষ্ট অন্য একটি বিষয়ের সাথে অজ্ঞাত জ্ঞানের বিষয়ের ব্যাপ্তি সম্পর্কের মাধ্যমে অনুমান প্রমা হয়। তাই বলা হয়-
‘ব্যাপ্যদর্শনাৎ অসন্নিকৃষ্টার্থজ্ঞানম্ অনুমানম্’।
অর্থাৎ : ব্যাপ্য পদার্থের জ্ঞান থেকে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অসন্নিকৃষ্ট পদার্থের যে জ্ঞান, তাকে অনুমিতি বলে।
যেমন, পর্বত ধূমবান এই জ্ঞান থেকে পর্বত অগ্নিমান এরূপ জ্ঞান। বহ্নির ব্যাপ্য যে ধূম সেই ধূম পর্বতে আছে একথা জেনে পর্বতে বহ্নির যে জ্ঞান, তাকে বলে অনুমিতি। নৈয়ায়িকেরা ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পরামর্শকে অনুমিতির করণ বলেছেন। মীমাংসকেরা যদিও পরামর্শের কারণতা স্বীকার করেন না, তবে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলে স্বীকার করেন। যেমন, ধূম বহ্নিব্যাপ্য এবং পর্বত ধূমবান- এরূপ দুটি জ্ঞানকে পর্বত বহ্নিমান এরূপ অনুমিতির কারণরূপে মীমাংসকেরা স্বীকার করেন।
অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান বা ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপ্তি কী ? মীমাংসামতে ব্যাপ্তি হলো স্বাভাবিক সম্বন্ধ। ভূয়োদর্শনের দ্বারা স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিশ্চয় করা যায়। মানমেয়োদয় গ্রন্থে নারায়ণ ভট্ট বলেছেন-
‘স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ স্বাভাবিকত্বং উপাধিরাহিত্যম্’। -(মানমেয়োদয়)
অর্থাৎ : স্বাভাবিক সম্বন্ধ হলো উপাধিরহিত সম্বন্ধ।
‘উপাধি’ অর্থ শর্তযুক্ত। ব্যাপ্তি হবে শর্তহীন। এজন্য ব্যাপ্তিকে অনৌপাধিক সম্বন্ধ বলা হয়। ধূমের সঙ্গে বহ্নির সম্বন্ধ অনৌপাধিক সম্বন্ধ। কারণ, যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নি থাকবে। সেজন্য এই সম্বন্ধকে বলা হয় ব্যাপ্তি সম্বন্ধ। কিন্তু বহ্নির সঙ্গে ধূমের সম্বন্ধ অনৌপাধিক নয়, আর্দ্রেন্ধন উপাধিযুক্ত। অর্থাৎ, বহ্নি বা আগুন থাকলেই সেখানে ধূম থাকবে এমন নিশ্চয়তা নেই। যেমন, গলন্ত লোহায় আগুন থাকলেও সেখানে ধূম থাকে না। ভেজা কাঠ বা আর্দ্র ইন্ধনযুক্ত আগুনে ধূম থাকে। এই আর্দ্র ইন্ধনযুক্ত শর্তের কারণে বহ্নির সঙ্গে ধূমের এই সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা যায় না। অতএব, ব্যাপ্তিজ্ঞান হলো নিত্যসাহচর্যরূপ সম্বন্ধনিয়মের জ্ঞান। ধোঁয়াকে বারেবারে আগুনের সঙ্গে দেখে এবং আগুন ছাড়া ধোঁয়া কখনো না দেখে ‘যেখানে ধোঁয়া সেখানে আগুন’ এই নিত্যসাহচর্যরূপ সম্বন্ধনিয়মের জ্ঞান হওয়ার পরে পাহাড়ে ধোঁয়া দেখে আগুনের অনুমান ঘটে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, অনুমান প্রমাণও মূলত প্রত্যক্ষপূর্বক বা প্রত্যক্ষাধীন। উল্লেখ্য, কেবল অনুমানই নয়, মীমাংসা স্বীকৃত ছয়প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষভিন্ন সকলেই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষপূর্বক বা প্রত্যক্ষাধীন। এক্ষেত্রে অনুমানের নিয়ত প্রত্যক্ষপূর্বকত্বকে প্রতিপাদন করতে গিয়ে কুমারিলভট্ট তাঁর শ্লোকবার্তিকে বলেন-
‘যত্রাপ্যনুমিতাল্ লিঙ্গাল্ লিঙ্গিনি গ্রহণং ভবেত্ ।
তত্রাপি মৌলিকং লিঙ্গং প্রত্যক্ষাদেব গম্যতে।।’- (শ্লোকবার্ত্তিক: অনুমান-১৭০)
অর্থাৎ : এমনকি যেক্ষেত্রে অনুমিত কোন লিঙ্গ বা জ্ঞাপক ধর্ম থেকে কোন লিঙ্গী বা জ্ঞাপ্য বিষয়ের অনুমান জন্মায় সেক্ষেত্রেও মূলে থাকে প্রত্যক্ষ।
উপাধিরহিত ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার জন্য ভাট্টরা ভূয়োদর্শনের সাহায্য নিয়েছেন। পাকশালা, মহানস প্রভৃতি স্থলে বারবার ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ দর্শন করে এবং ব্যভিচার দর্শন না করে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায়। ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভাট্টরা তর্কের সাহায্য নিয়েছেন। কোন বিষয়ের বৈপরীত্য আশঙ্কার করলে সেই আশঙ্কায় দোষ প্রদর্শন করাই হলো তর্ক। এজন্য একে অনিষ্ট প্রসঙ্গ বলা হয়। ধূম ও বহ্নির স্বাভাবিক সম্বন্ধ বিষয়ে যদি কারো আশঙ্কা থাকে, তাহলে সেই আশঙ্কা দোষদুষ্ট বলে প্রমাণ করাই হলো তর্কের লক্ষ্য। এর দ্বারা ধূম ও বহ্নির স্বাভাবিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। নৈয়ায়িকদের মতো মীমাংসকরাও দু’প্রকার ব্যাপ্তি স্বীকার করেন- সমব্যাপ্তি ও বিষমব্যাপ্তি।
অনুমান বিভাগের ক্ষেত্রে মীমাংসকরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নৈয়ায়িকদের অনুরূপ নানা বিভাগ নির্দেশ করেছেন। প্রথমত, কেবল-অন্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী ভেদে অনুমান ত্রিবিধ। দ্বিতীয়ত, বীত ও অবীত ভেদে অনুমান দ্বিবিধ। বীত অনুমান আবার দৃষ্ট ও সামান্যতঃ দৃষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। তৃতীয়ত, স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান ভেদে অনুমান দ্বিবিধ। এইসব নানা প্রকারের অনুমান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মীমাংসকরা মূলত ন্যায় সম্প্রদায়ের অনুগামী হয়েছেন। তবে পরার্থানুমানের অবয়ব প্রসঙ্গে অবশ্য ন্যায়মতের সঙ্গে মীমাংসামতের পার্থক্য বর্তমান। ন্যায়দর্শনে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, ন্যায়ের এই পাঁচটি অবয়ব স্বীকার করা হয়েছে। যেমন-
পরার্থানুমান :
(১) পর্বত বহ্নিমান (প্রতিজ্ঞা)
(২) কারণ পর্বত ধূমায়মান (হেতু)
(৩) যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি, যেমন- মহানস বা পাকশালা, কামারশালা ইত্যাদি (উদাহরণ)
(৪) পর্বতও ধূমায়মান (উপনয়)
(৫) সুতরাং পর্বত বহ্নিমান (নিগমন বা সিদ্ধান্ত)।
এই পরার্থানুমান সম্পর্কে কুমারিল ভট্টের মত হলো, পাঁচটি অবয়ব অনাবশ্যক। হয় প্রথম তিনটি অথবা শেষ তিনটি অবয়বই যথেষ্ট। ভাট্ট সম্প্রদায় মতে প্রতিজ্ঞা ও নিগমন এবং হেতু ও উপনয় সমার্থক। সুতরাং ন্যায়ের অবয়ব তিনটিই, পাঁচটি নয়।
বিভিন্ন মীমাংসাশাস্ত্রে বিভিন্ন সংখ্যক হেত্বাভাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘শাস্ত্রদীপিকা’ ও ‘ভাট্টচিন্তামণি’ গ্রন্থে অসিদ্ধ, অনৈকান্তিক ও বাধক এই তিন প্রকার হেত্বাভাসের উল্লেখ আছে। আবার ‘মানমেয়োদয়’ গ্রন্থে চার প্রকার হেত্বাভাসের উল্লেখ পাওয়া যায়- অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ, অনৈকান্তিক ও অসাধারণ।
.
অনুমান প্রমাণের প্রমেয়বিষয়ে নানাপ্রকার মতভেদ দেখা যায়। শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিল বলেছেন-
‘তস্মাদ্ধর্ম্মবিশিষ্টস্য ধর্ম্মিণঃ স্যাৎ প্রমেয়তা।
সা দেশস্যাগ্নিযুক্তস্য ধূমস্যান্যৈশ্চ কল্পিতা।।’- (শ্লোকবার্ত্তিক)
অর্থাৎ : পর্বতে ধূমদর্শন ও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের স্মরণ হলে বহ্নিবিশিষ্টত্বরূপে প্রমেয় পর্বতেরই অনুমিতি হয়। অর্থাৎ ধর্মীই অনুমানের প্রমেয়।
মীমাংসকরা উপমানকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে মনে করেন। তাদের মতে উপমানকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। পূর্বে দেখা কোনো বস্তুর সঙ্গে বর্তমান প্রত্যক্ষীভূত কোনো বস্তুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যখন সিদ্ধান্ত করা হয় যে পূর্বে দেখা ও বর্তমানে স্মৃত বস্তুটি বর্তমানে প্রত্যক্ষীভূত বস্তুর সাদৃশ, তখন সেই জ্ঞানের প্রণালীকে উপমান বলে। বলা বাহুল্য, সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় উপমানকে পৃথক প্রমাণরূপে স্বীকার করেন নি। চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, বৈশেষিক ও সাংখ্য সম্প্রদায় উপমানকে পৃথক প্রমাণের মর্যাদা দেননি। মীমাংসা, বেদান্ত ও ন্যায় সম্প্রদায় উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা দিলেও উপমানের স্বরূপ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে ন্যায় ও মীমাংসা সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।
কোন একটি প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদনের জন্য সেই প্রমাণের স্বরূপ, বিষয় ও উৎপাদক এই তিন বিষয়ে বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করা প্রয়োজন। সুতরাং উপমানের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের জন্য উপমান যে স্বরূপত, বিষয়গত এবং করণগত ভিন্ন তা প্রদর্শন করা প্রয়োজন। বিজাতীয় প্রমাই বিজাতীয় প্রমাণকে প্রতিপন্ন করতে পারে। ফলে যাঁরা উপমানকে পৃথক প্রমাণের মর্যাদা দেন, তাঁরা তা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন। মীমাংসক নারায়ণ ভট্ট তাঁর ‘মানমেয়োদয়’ গ্রন্থে মীমাংসাসম্মত উপমানের স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন-
‘দৃশ্যমানার্থসাদৃশাৎ স্মর্যমাণার্থগোচরম্ ।
অসন্নিকৃষ্টসাদৃশ্যজ্ঞানং হি উপমিতির্মতা।।’- (মানমেয়োদয়)
অর্থাৎ : পূর্বদৃষ্ট অসন্নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যবশতঃ স্মরণের মাধ্যমে পূর্ব-অজ্ঞাত দৃশ্যমান বস্তুর সাদৃশ্যজ্ঞানই উপমিতি।
একটি উদাহরণের সাহায্যে উপমানের এই স্বরূপ প্রকাশ করা যেতে পারে। কোন ব্যক্তি স্বগৃহে বা অন্যত্র যদি ‘গরু’ নামক প্রাণী প্রত্যক্ষ করার পর কালান্তরে কোথাও একটি গবয় বা নীলগাই প্রত্যক্ষ করে, তাহলে সে তখন গবয়গত গোসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে গোগত গবয়সাদৃশ্য উপলব্ধি করে। তার এই উপলব্ধির আকার হলো, ‘পূর্বদৃষ্ট গরু প্রত্যক্ষীভূত গবয়সদৃশ’। এরূপ উপলব্ধিই উপমিতি। তাই নারায়ণ ভট্ট বলেন-
‘গবয়স্থিতসাদৃশ্যদর্শনং করণং ভবেৎ।
ফলং গোগতসাদৃশ্যজ্ঞানমিত্যবগম্যতাম্ ।।’- (মানমেয়োদয়)
অর্থাৎ : গবয়টিকে দেখেই যে গবয়ে গরুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়, ফলে পূর্বদৃষ্ট গরুটিতে তার যে গবয়সাদৃশ্যের জ্ঞান হয়, তা-ই উপমিতি।
মীমাংসামতে উক্ত গোগত গবয়-সাদৃশ্য প্রতীতি যেমন প্রত্যক্ষাত্মক হতে পারে না, কারণ ঐ জ্ঞানের উৎপত্তিক্ষণে গরু উপস্থিত থাকে না, তেমনি ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পদজ্ঞানেরও কোন অবকাশ না থাকায় ঐ প্রতীতি অনুমিতি ও শাব্দবোধও হতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে গরু কেবলমাত্র স্মৃতিরই বিষয় হতে পারে। অথচ প্রত্যক্ষীভূত গবয় প্রাণীতে পূর্বদৃষ্ট গরুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষতঃ জেনে তার ফলস্বরূপ স্মৃত গরুতে প্রত্যক্ষীভূত গবয়ের সাদৃশ্যজ্ঞান একটি অনধিগত ও তত্ত্বার্থজ্ঞান। মীমাংসামতে অনধিগতত্ব ও তত্ত্বার্থত্বই প্রমার লক্ষণ। গোগত গবয়সাদৃশ্যরূপ প্রতীতি প্রত্যক্ষ, অনুমিতি বা শাব্দবোধের অতিরিক্ত হওয়ায় এবং তা প্রমা লক্ষণান্তর্গত হওয়ায় ‘উপমিতি’ নামক স্বতন্ত্র প্রমা স্বীকার করতে হয়। এইরূপ প্রমার করণই উপমান।
নৈয়ায়িকরাও উপমানকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেন, কিন্তু মীমাংসকদের উপমানের ব্যাখ্যা নৈয়ায়িকদের ব্যাখ্যার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন-
‘গ্রামীণস্য প্রথমতঃ পশ্যতো গবয়াদিকম্ ।
সাদৃশ্যধীর্গবাদীনাং যা স্যাৎ সা করণং মতম্ ।।’
অর্থাৎ : কোন আরণ্যক ব্যক্তি গ্রামবাসী ব্যক্তিকে বললো, গরুর মতো একপ্রকার প্রাণী অরণ্যে দেখা যায়, তাকে বলে গবয়। পরে কখনও বনে গেলে গ্রামীণ লোকটি যখন গরুর মতো প্রাণিবিশেষ দেখতে পায়, তখন গবয়ে গরুর সাদৃশ্যের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা-ই উপমান, অর্থাৎ উপমিতিরূপ প্রমিতির কারণ।
ন্যায়মতে সংজ্ঞা হতে সংজ্ঞার যে জ্ঞান সেটাই হচ্ছে উপমান। কিন্তু মীমাংসামতে পূর্বে প্রত্যক্ষীভূত বস্তুর সঙ্গে বর্তমান প্রত্যক্ষীভূত বস্তুর সাদৃশ্যজ্ঞানই হলো উপমান। কুমারিল ভট্ট ও প্রাভাকর মিশ্র উভয়ই প্রত্যক্ষীভূত বস্তুর সঙ্গে স্মৃত বস্তুর সাদৃশ্য জ্ঞানকেই উপমান বলে স্বীকার করেছেন।
মীমাংসাদর্শনের মূল উদ্দেশ্য হলো বৈদিক ক্রিয়াকান্ডের যাথার্থ্য ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করা। এবং বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা হলেই তা সম্ভব। সে কারণে মীমাংসকরা স্বীকৃত অন্যান্য প্রমানের চাইতে শব্দ-প্রমানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বেদে যাগযজ্ঞাদি কর্মের বিধান বহুল পরিমাণে বর্তমান। মীমাংসকদের মতে এই কর্মের বিধানই বেদবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য। বেদে যদিও সিদ্ধার্থ বাক্যও রয়েছে, কিন্তু সেগুলিরও উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল বাক্য দ্বারা প্রকাশিত তত্ত্বগুলির অস্তিত্ব ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করে মানুষকে কর্মে প্রণোদিত করা।
মীমাংসা দর্শনের এই ধর্মীয় প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর করতে হলে বেদবাক্যের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। যেমন, বেদে বলা হলো- যজ্ঞ করলে স্বর্গলাভ হবে। পুরো বিষয়টাই ধর্ম; তাকে কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা সম্ভব নয়। সোজা কথায়, প্রত্যক্ষ এক্ষেত্রে ধর্মজ্ঞানের নিমিত্ত বা উপায় হতে অক্ষম। কারণ, জৈমিনির মতে-
‘সত্সংপ্রয়োগে পুরুষস্যোন্দ্রিয়ানাং বুদ্ধিজন্ম তত্ প্রত্যক্ষমনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাত্’।- (মীমাংসাসূত্র: ১/১/৪)
অর্থাৎ : ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের ‘সম্প্রয়োগ’ অর্থাৎ সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধের বশে যে বুদ্ধি বা জ্ঞান জন্মায় তাই প্রত্যক্ষ। সে কেবল তাকেই জানাতে পারে যা বিদ্যমান বা বর্তমান।
যজ্ঞ থেকে প্রাপ্তব্য ফল ভবিষ্যতের গর্ভে অর্থাৎ বর্তমান না হওয়ায় ঐ বেদপ্রতিপাদিত বিষয় অবশ্যই অপ্রত্যক্ষ। তাছাড়া স্বর্গাদি বিষয়টা পুরোপুরি অতীন্দ্রিয়, নিত্যপরোক্ষ হওয়ায় প্রত্যক্ষের প্রশ্নই ওঠে না। আবার অন্যান্য অনুমানাদি প্রমাণও প্রত্যক্ষনির্ভর বলে তাদের দ্বারাও ধর্মের স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে শবরস্বামীর দ্বিধাহীন ভাষ্য-
‘প্রত্যক্ষপূর্বকত্বাচ্চানুমানোপমানার্থাপত্তীনামপ্যকারণত্বম্’।- (শাবরভাষ্য)
অর্থাৎ : প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমান, উপমান এবং অর্থাপত্তিও অনিমিত্ত, অর্থাৎ ধর্মকে জানাতে অপারগ, যেহেতু তারা সকলেই প্রত্যক্ষপূর্বক। প্রত্যক্ষ যার নাগাল পায় না তারাও সেখানে ব্যর্থ।
একারণেই ভারতীয় দর্শনে প্রত্যক্ষকে প্রমাণজ্যেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও মীমাংসকরা তাকে শ্রেষ্ঠ মানতে নারাজ। কারণ, প্রত্যক্ষাত্মক প্রমা জন্মায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, এই অবস্থান অনুযায়ী ইন্দ্রিয়কে বলতে হয় প্রত্যক্ষপ্রমাণ। তা কেবল বিদ্যমান বিষয়কেই গ্রহণ করতে পারে। যা অবর্তমান তা তার অধিগম্য নয়। এটা হচ্ছে প্রত্যক্ষপ্রমাণ ইন্দ্রিয়ের অনস্বীকার্য সীমাবদ্ধতা। ইন্দ্রিয়ের এই সীমিত ক্ষমতা সম্পর্কে ‘ন্যায়রত্নাকরব্যাখ্যা’য় পার্থসারথিমিশ্রও স্পষ্ট করে বলেন-
‘বর্তমানবিষয়মেব প্রত্যক্ষমিত্যস্তি নিয়মঃ। অতো ন তস্য ভবিষ্যতি ধর্মে সামর্থ্যম্, ন তরাং সর্বার্থেষু।’- (ন্যায়রত্নাকরব্যাখ্যা)
অর্থাৎ : প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান বিষয়কেই জানাতে পারে এই হলো নিয়ম। এজন্য ‘ভবিষ্যৎ’ ধর্মকে জানাবার সামর্থ্য তার নেই। বিষয়কে জানানো তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।
ফলে এই সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে থাকা প্রত্যক্ষনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও এমন একটি প্রমাণকে কোন কোন দর্শনে স্বীকার করা হয়, তা হলো শব্দ প্রমাণ। মীমাংসাদর্শনে যা শাস্ত্র বা আগম বলেও পরিচিত। শব্দপ্রাধান্যবাদের এই অন্যতম উৎস হলো মীমাংসক শবরস্বামীর ভাষ্য-
‘চোদনা হি ভূতং ভবন্তং ভবিষ্যন্তং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবংজাতীয়কম্ অর্থং শক্লোত্যবগময়িতুম্, নান্যত্ কিঞ্চন, নেন্দ্রিয়ম্’। (শাবরভাষ্য)
অর্থাৎ : চোদনা অর্থাৎ প্রবর্তক বা বিধায়ক বাক্য অতীত, বর্তমান, ভাবী, সূক্ষ্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগম্য, ব্যবহিত অর্থাৎ স্থান এবং কালের দিক থেকে যার সঙ্গে ব্যবধান, দূরবর্তী এবং এজাতীয় অন্য অর্থকেও জানাতে পারে; যা অন্য কিছু করতে পারে না; এমনকি ইন্দ্রিয়ও নয়।
সোজা কথায় এর মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে শব্দই শুধু অসন্নিকৃষ্ট বা অবর্তমানকে জানাতে সমর্থ। আর এই শব্দের উৎস বা প্রমাণ হলো বেদ। যেহেতু যজ্ঞের ফললাভ বর্তমানে হবার নয়, ভবিষ্যতের ব্যাপার। বিধিবাক্য কেবল সেই অনাগতেরই নির্দেশ দিতে পারে। তাই কুমারিল ভট্টের মতে-
‘ন হি ভূতাদিবিষয়ঃ কশ্চিদস্তি বিধায়কঃ।’- (শ্লোকবার্ত্তিক: চোদনা-৭)
অর্থাৎ : অতীত কিংবা বর্তমান বিধির বিষয় হতে পারে না।
এই যে বিধি বা বিধায়ক বাক্য, তা মূলত বচন বা শব্দ এবং এই বচনের উপর নির্ভর করে যে জ্ঞান লাভ হয় তাকে শব্দজ্ঞান বলা হয়। মীমাংসা মতে বিশ্বাসযোগ্য বচন শব্দ প্রমাণ। অন্যভাবে বললে, শব্দপ্রমাণ হলো আপ্ত বা বিশ্বাসযোগ্য যথার্থবক্তার বাক্য বা উক্তি। আপ্তবাক্য থেকে যে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে বলে শাব্দবোধ বা শাব্দজ্ঞান। শাবরভাষ্যে শাস্ত্র বা শব্দপ্রমাণের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-
‘শাস্ত্রং শব্দবিজ্ঞানাত্ অসন্নিকৃষ্টে অর্থে বিজ্ঞানম্’।- (শাবরভাষ্য)
অর্থাৎ : শাস্ত্র বা শব্দ-প্রমাণ হলো শব্দজ্ঞান থেকে সঞ্জাত, সন্নিকৃষ্ট বা ইন্দ্রিয়সংযুক্ত নয় এমন বিষয়ের জ্ঞান।
শব্দবিজ্ঞান বা বাক্যজ্ঞান না হলে বাক্যার্থজ্ঞান হতে পারে না। শাবরভাষ্যের শাস্ত্রলক্ষণে ‘অসন্নিকৃষ্ট’ এই ‘অর্থ’-বিশেষণটি সবিশেষ তাৎপর্যের বাহক। যে ঘট আমার সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ সন্নিহিত বা ইন্দ্রিয়সংবদ্ধ তাকে ঘট বলে বোঝাবার মধ্যে শব্দের কোন মহিমা নেই। প্রত্যক্ষ হতে ঘটের বাধা নেই। তাহলে শব্দের স্বকীয়ত্ব এখানেই যে সে অবিদ্যমানেরও প্রকাশে সমর্থ।
প্রশ্ন উঠতে পারে, কেবল শব্দপ্রমাণ নয়, অনুমানাদি প্রমাণও অসন্নিকৃষ্টবিষয়ের প্রকাশক। তাহলে শব্দ কেন প্রধান হবে ? এর উত্তরে বলা হয়, অনুমানাদি ভূত, ভাবী, ব্যবহিত ও দূরস্থকে প্রকাশ করে ঠিকই, তবে অনুমানাদি প্রমাণসমূহ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষপূর্বক। কারণ এরা কোন না কোন দেশে বা কালে কারোর না কারোর কাছে বিদ্যমান। কিন্তু একেবারে অবিদ্যমান অলীক বিষয় সম্বন্ধে অনুমানাদি উৎপন্ন হয় না। কেবল শাব্দজ্ঞানই উৎপন্ন হতে পারে। এ বিষয়ে কুমারিলভট্টের ভাষ্য হলো-
‘অত্যন্তাসত্যপি জ্ঞানমর্থে শব্দঃ করোতি হি।’- ( শ্লোকবার্ত্তিক: চোদনা-৬)
অর্থাৎ : যা অত্যন্ত অসৎ অর্থাৎ অলীক ( কোন দেশকালে যার অস্তিত্ব নেই) তার সম্বন্ধেও শব্দজ্ঞান জন্মায়।
উদ্ধৃত কুমারিলভাষ্যের ব্যাখ্যাকালে পার্থসারথিমিশ্র অলীক বা অত্যন্তাসতের উদাহরণ দিলেন- ‘শশবিষাণাদি’, অর্থাৎ শশশৃঙ্গপ্রভৃতি।
‘অত্যন্তাসত্’-কে শব্দ প্রকাশ করতে পারে কিনা এ বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দার্শনিকমহলে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। উদয়ানাচার্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকদের বক্তব্য হলো- শৃঙ্গের সঙ্গে শশের অবয়ব-অবয়বি-ভাবরূপ সম্বন্ধ বাস্তবে অসম্ভব বলে যোগ্যতা বা মানানসহতার অভাববশত ‘শশশৃঙ্গম অস্তি’ বা ‘শশশৃঙ্গং নাস্তি’- কোনটিকেই বাক্য বলা চলে না, অর্থাৎ এ জাতীয় উক্তির অর্থবোধকত্ব নেই। কিন্তু পাণিনীয় প্রস্থান ও বৌদ্ধরা সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর অধিবাসী। তাঁদের মতে কোন বচনই অর্থহীন হতে পারে না। কারণ শব্দার্থ আসলে বুদ্ধিস্থ, কেবল ভাবনা। কোন বস্তু শব্দের অর্থ নয়। এজন্য ‘বহ্নিনা সিঞ্চতি’ (‘আগুন দিয়ে ভিজিয়ে দেয়’) শুনে আমরা দ্রাবিড়ভাষাশ্রবণরত পাশ্চাত্যদের মতো মূকতা অবলম্বন করি না। বক্তাকে বরং পাগল বলে উপহাস করে থাকি। তাছাড়া, বিরোধীদের শাস্ত্রকে ভ্রান্ত বললেও তা থেকে নিশ্চয় কোন অর্থ প্রতীত হয়। ‘শব্দ নিত্য’ এবং ‘শব্দ অনিত্য’- এই দুটো বাস্তবে সত্য হতে পারে না। এরা পরস্পর বিরুদ্ধ। একটা সত্য, অন্যটা মিথ্যা। তথাপি এটা ঘটনা যে ‘বাদে’ বা তর্কে দুটি উক্তিই নিজ-নিজ অর্থের প্রকাশক। আর কবিরা যখন সুন্দর মুখ দেখে মন্তব্য করেন ‘চাঁদের টুকরো দেখলাম’, অথবা কাউকে গাধা, গরু বলে গালি দেয়া হয়, তখন রূপক কোন অর্থ বোঝায় নিশ্চয়ই। না হলে কবির কাব্য শুনে চমৎকৃত কিংবা গালি শুনে ক্ষুব্ধ হবার অবকাশ থাকত না।’ (সূত্র: হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়/ বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা দর্শন, পৃষ্ঠা-১৬)
এসব কারণে বৈয়াকরণরা অভিমত ব্যক্ত করলেন- ‘শশবিষাণ’ ইত্যাদির বহিঃসত্তা না থাকলেও বুদ্ধিসত্তা অর্থাৎ উপচরিত বা আরোপিত সত্তা আছে। বৌদ্ধদর্শনে এর নাম হলো- ‘অভিধেয়সত্তা’। তাই জগদীশ তর্কালঙ্কার-এর মতো নব্য নৈয়ায়িকরাও আপোষে এসে বললেন-
‘বহ্নিনা সেক ইত্যাদ্যপি বাক্যমেব, পরন্তু বাধিতার্থকত্বাদযোগ্যম্’।- (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)
অর্থাৎ : ‘বহ্নিনা সিঞ্চতি’ (‘আগুন দিয়ে ভিজিয়ে দেয়’) ইত্যাদিও সার্থক অর্থাৎ অর্থবহ বচন। কিন্তু যোগ্যতার অভাব থাকায় অপ্রমাণ।
‘অনুমানাদির সঙ্গে শব্দের আরেকটা বড় মাপের তফাৎ রয়েছে, যদিও প্রমাণ হিসাবে নয়, প্রমাণাভাস হিসাবে। প্রমাণ হল প্রমা বা যথার্থ অনুভবের সাধন। অন্যদিকে প্রমাণাভাস যথার্থ অনুভবের সাধন না হয়ে অপ্রমা বা অযথার্থ অনুভবকেই সাধিত করে। শ্রবণযোগ্যতার দিক থেকে শব্দপ্রমাণের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও যা বস্তুবিরোধী তা শব্দপ্রমাণ নয়; সে শব্দপ্রমাণাভাস, সংক্ষেপে শব্দাভাস। প্রমাণ নয় অথচ প্রমাণরূপে প্রতিভাত বা আভাসমান। তাই সে হল প্রমাণাভাস। অনুরূপভাবে অনুমানাভাস ইত্যাদিকেও দেখানো যায়। অনুমানাভাস প্রভৃতির সঙ্গে শব্দাভাসের পার্থক্য প্রবল। চতুর্দশ শতকের ভাট্ট মীমাংসক চিদানন্দ পন্ডিত এ বিষয়ে আলোকপাত করায় তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। কেউ ধূলিসমূহকে ধূম ভেবে তা থেকে বহ্নির অনুমান করতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে জানবে বস্তুটা আসলে ধূম নয়, ধূলি, তখন আর তার ভ্রান্ত অনুমান জন্মাবে না। শুক্তিকে কেউ রজত বলে ভুল করতে পারে। কিন্তু একবার যদি সে জানে যে সামনের বস্তুটা আদৌ রজত নয়, তাহলে পরবর্তী জ্ঞানটা বাধকরূপে কাজ করায় তার আর রজতভ্রম হয় না। শব্দের বেলা ব্যাপারটা অন্যরকম। ‘নদীর তীরে ফল নেই’ এই বিরোধী বা বাধের জ্ঞান হবার পরেও ‘নদ্যাঃ তীরে ফলানি সন্তি’ এই বাক্য পূর্বের মতই অর্থবোধ উৎপাদন করে। কেবল জ্ঞানান্তরের দ্বারা বাধিত এবং বস্তুও অসদৃশ হওয়ায় ওই বাক্যার্থজ্ঞান তখন অযথার্থ বলে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে বাক্যটিকে শব্দপ্রমাণ না বলে বলা হয় শব্দাভাস।’- (সূত্র: বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা দর্শন, পৃষ্ঠা-১৯)
বৈদিক বাক্য যে কখনো শব্দাভাস নয় এ ব্যাপারে মীমাংসকদের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নেই। তাই বেদবাক্য বাধিত না হওয়ায় স্বতঃপ্রমাণ হিসেবে মীমাংসামতে বেদই হলো শব্দ প্রমাণ। মীমাংসক কুমারিল ভট্ট অবশ্য লৌকিক অভিজ্ঞ ব্যক্তির বচনকেও আপ্তবাক্য হিসেবে শব্দ প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। তাঁর মতে মিথ্যাবাদী বা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির বচন বা অনাপ্তবাক্য ছাড়া সমস্ত বাক্যই জ্ঞানোৎপাদন করতে পারে এবং সেজন্যেই তা শব্দ-প্রমাণ বলে গৃহীত হওয়ার যোগ্য।
সুতরাং কুমারিল ভট্টের মতে শব্দ-প্রমাণ দু’প্রকার- পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয়।
কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির বচন থেকে কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের প্রমাণ হলো পৌরুষেয় শব্দ-প্রমাণ, আর বেদবাক্য অপৌরুষেয় শব্দ প্রমাণ। স্মৃতি, পুরাণ ও পুরুষরচিত দর্শনগ্রন্থাদিও পৌরুষেয় শব্দ-প্রমাণ।
কিন্তু প্রাভাকর মীমাংসকরা অপৌরুষেয় বেদবাক্যই কেবল শব্দপ্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, পৌরুষেয় লোকবাক্যের প্রায়শ বাধিত বা অযথার্থ হবার সম্ভাবনা থাকায় তা শব্দপ্রমাণ হতে পারে না। শাবরভাষ্যের করা লক্ষণে শব্দপ্রমাণ বোঝাতে ‘শাস্ত্র’ শব্দের ব্যবহারও প্রাভাকরসমর্থিত শাস্ত্র বা বেদের ব্যতিরিক্ত শব্দগুলির অপ্রামাণ্য সূচিত করে। লৌকিক বক্তা প্রায়ই অনাপ্ত হয়ে থাকে। ফলে লৌকিক কথার অযথার্থ বা অর্থশূন্য অর্থাৎ অর্থব্যভিচারী হবার সম্ভাবনা রয়ে যায়। প্রাভাকর মীমাংস শালিকনাথ মিশ্র তাই প্রকরণপঞ্চিকায় বলেন-
‘লৌকিকং বচনং ন শাব্দং প্রমাণম্ । অভিপ্রায়ে শব্দো লিঙ্গম্, অভিপ্রায়োহপ্যর্থে লিঙ্গম্’।- (প্রকরণপঞ্চিকা)
অর্থাৎ : লৌকিক বাক্যদ্বারা উৎপন্ন যথার্থ জ্ঞান শাস্ত্র বা শব্দজাত জ্ঞান নয় বলে স্বীকৃতির অযোগ্য। লৌকিক বাক্য থেকে প্রথমে বক্তার জ্ঞান বা অভিপ্রায় অনুমিত হয়। দ্বিতীয় পর্বে লৌকিক বাক্যের দ্বারা জ্ঞাপিত ওই বক্তার জ্ঞান বা অভিপ্রায় অর্থকে জ্ঞাপিত করে। জ্ঞাপিত বিষয়টি বস্তুত না থাকলে ওই বাক্যটি হয়ে ওঠে লিঙ্গাভাস। শব্দাভাস সে নয়।
প্রাভাকর মীমাংসকরা তাই পৌরুষেয় শব্দ বা লোকবাক্যকে অনুমানের অন্তর্গত মনে করেন। কোন বচন সত্য কি অসত্য তা অনুমান করে নিতে হয় বক্তার চরিত্রের এবং জ্ঞানের সত্যতার উপর নির্ভর করে। বক্তা যদি বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হয় তাহলে তার বচন শব্দপ্রমাণ হবে। পৌরুষেয় শব্দ অনেক ক্ষেত্রেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। তাই প্রাভাকররা লোকবাক্যকে প্রকৃত প্রমাণ বলে গ্রহণ করেন না।
কিন্তু লৌকিক ব্যবহারের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ ভাট্টরা নৈয়ায়িকদের মতোই মেনে নিতে পারেন নি। শাস্ত্র তো মুখ্যত লোকের জন্য অর্থাৎ লোককে বোঝাবার জন্য। লোকব্যবহারের সেখানে প্রাধান্য হওয়া উচিত অলৌকিকের তুলনায়। ভাট্টরা তাই বলেন-
‘বাক্যার্থোহনুময়া লোকে যদা বেদে তদা ন কিম্ ।
বেদেহভিধানং চেত্ সিধ্যেত্ সিধেৎল্লোকে ততস্তরাম্ ।।’- (নীতিতত্ত্বাবির্ভাব)
অর্থাৎ : বাক্যার্থ যদি লোকে অনুমানলভ্য হয় তাহলে বেদেও তাই হোক। আর বেদে যদি শব্দের দ্বারা অর্থ অভিহিত হয় তাহলে লোকেও শব্দদ্বারা অর্থাভিধান হবে না কেন ?
তাছাড়া লৌকিক বাক্যের শব্দত্বের বিরুদ্ধে যে সব দোষ আবিষ্কার করা হয়েছে তাদের মধ্যে অনেককে চেষ্টা করলে বৈদিক বাক্যের ক্ষেত্রেও দেখানো যায়। অনেক সময় বেদের অর্থবাদকেও শব্দাভাস বলতে হয়। ভাট্টমতে শব্দপ্রমাণ লোক-বেদ-নির্বিশেষে অনুমানের অতিরিক্ত।
বেদ অপৌরুষেয় :
মীমাংসাদর্শনে বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়েছে। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব মীমাংসার একটি অতিপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। ‘অপৌরুষেয়’ শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো যা পুরুষকৃত নয়। কিন্তু এখানে ‘অপৌরুষেয়’ শব্দটির অর্থ হলো যা ঈশ্বরকৃত নয়। মীমাংসামতে কেবল শব্দরূপ ছাড়া দেবতার বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই। যার কোন বাস্তব অস্তিত্বই নেই সে আবার শাস্ত্র রচনা করবে কী করে ? বাকি থাকে মানুষ আর ঈশ্বর। বেদ হলো অলঙ্ঘনীয় সত্য ও অবিসংবাদী জ্ঞানের অপরিমেয় ভান্ডার। মানুষ যতো বড়ো প্রতিভাধরই হোক না কেন তার জ্ঞানবুদ্ধি সীমিত, তার পক্ষে কি অনন্ত সত্যজ্ঞানের আকরস্বরূপ বিপুল বেদরাশি রচনা করা সম্ভব ? বাকি রইলেন এক সম্ভাব্য সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। এ পর্যায়ে নৈয়ায়িকরা বলেন- বেদের রচয়িতা ঈশ্বর। ঈশ্বরই প্রথম বেদবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। প্রাচীন ঋষিরা তা শুনেছিলেন, তারপর পুরুষানুক্রমে ও সম্প্রদায়-পরম্পরায় সেই স্মরণাতীত কাল থেকে মুখে মুখে বেদ ঋষিসমাজে প্রচলিত হয়ে এসেছে। ন্যায় ও যোগদর্শনে পুরুষবিশেষরূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়েছে। তাই তাঁদের মতে বেদ অপৌরুষেয় নয়, পৌরুষেয়।
নৈয়ায়িকেরা এই বেদকেই ঈশ্বরের অস্তিত্বেও পক্ষে একটি প্রমাণরূপে উপস্থিত করেছেন। তাঁদের যুক্তির নমুনাটি হলো- ঈশ্বর না থাকলে বেদ রচনা করলো কে ? সুতরাং বেদ রচনার জন্য একজন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর থাকা প্রয়োজন। বাক্য-মাত্রেরই সৃষ্টিকর্তা রূপে একজন বুদ্ধিমান চেতন ব্যক্তির প্রয়োজন যিনি সর্বপ্রথম উচ্চারণের দ্বারা ঐ বাক্যটি সৃষ্টি করেছেন। বেদ হলো বিপুল বাক্যরাশি। তাই সর্বপ্রথম কোন বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তি নিশ্চয়ই বৈদিক বাক্যগুলি উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি কে হতে পারেন ? তাকে অসীম শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী এক সর্বজ্ঞ পুরুষ হতে হবে। সে তো মানুষ হতে পারে না। তাই ‘অমানুষ’ এক সর্বজ্ঞ পুরুষ সর্বপ্রথম বেদবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনিই ঈশ্বর।
ঈশ্বরের শরীর আছে কী নেই, উচ্চারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ফুসফুস-শ্বাসনালী-জিহ্বা-মাড়ি-দাঁত-ঠোঁট-প্রভৃতি আছে কী নেই, এ প্রশ্নই অবান্তর। অসীম জ্ঞানবিধি বেদ বলে একটা কিছু যখন আছে তখন এর স্রষ্টা ঈশ্বর বলেও একটা কিছু থাকতে হবে। প্রয়োজন হলে অলৌকিক মহিমা বলে তিনি শরীর ধারণও করতে পারেন। এসবই মানতে হবে, নইলে বেদ এলো কোথা থেকে ? ঈশ্বর না থাকলে বেদ হয় না। যদিও বৌদ্ধ বা জৈনদের মতো নাস্তিকদের ধর্মগ্রন্থের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়নি।
কিন্তু মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়নি। (ঈশ্বরের অস্তিত্ব-খন্ডনে মীমাংসা-সম্মত অভূতপূর্ব যুক্তি-আলোচনা ঈশ্বর প্রসঙ্গে যথাস্থানে উপস্থাপন করা হবে।) তাহলে প্রশ্ন, বেদ এলো কী করে ? মীমাংসামতে বেদ ঈশ্বররচিত নয়, ঋষিদের ধ্যানে প্রতিভাত সত্য। মন্ত্রদ্রষ্টাকেই ঋষি বলা হয়। তাই নিত্য বেদবাক্যের প্রামাণ্য সন্দেহাতীত। ঋষিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা হলেও বেদের মন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা নন। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য মীমাংসকরা বলেছেন যে, বেদ ঈশ্বররচিত হলে বেদের রচনাকাররূপে ঈশ্বরের নাম থাকতো। বেদ ও বেদজ্ঞের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু বেদের রচয়িতার নাম কোথাও পাওয়া যায় না। বস্তুত মীমাংসামতে বেদ নিত্য। বেদের উপদেশ গুরু-শিষ্যের পরম্পরায় চলে এসেছে।
শব্দের নিত্যতা :
বেদের নিত্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মীমাংসকরা বর্ণাত্মক বা অক্ষরবাচক শব্দমাত্রকেই নিত্য বলে প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। তাই মীমাংসকদেরকে বর্ণ-রূপ শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রমে বিস্তৃত তর্কজাল রচনা করতে হয়েছে। কুমারিলকে এজন্য শাবর-ভাষ্যের ব্যাখ্যারূপে ৪৪৪টি শ্লোকের আশ্রয় নিতে হয়েছে। বেদ অপৌরুষেয় নিত্য বলেই এতে লেশমাত্র ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। তাহলে বৈদিক বাক্যরাশির অন্তর্গত বর্ণগুলি নিত্য না হলে বেদ নিত্য হয় কী করে। এ ব্যাপারে তাই কুমারিল ভট্ট স্পষ্টতই বলছেন-
‘তস্মাদ্ বেদপ্রমাণার্থং নিত্যত্বমিহ সাধ্যতে’।- ( শ্লোকবার্ত্তিক: শব্দনিত্যতা শ্লোক-৭)
অর্থাৎ : বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধির জন্যই বর্ণের নিত্যতা সিদ্ধির প্রয়োজন।
নৈয়ায়িক মতে ‘বেদ অপৌরুষেয় নয়, কিন্তু পৌরুষেয় এবং ঈশ্বরনামক সর্বজ্ঞ পুরুষের সৃষ্টি’- এই মতের অনুষঙ্গ হিসেবে নৈয়ায়িকদের আরেকটি সুবিদিত সিদ্ধান্ত হলো- শব্দ, শব্দার্থ এবং শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধও ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। কর্তা ছাড়া যেমন কার্য হয় না, তাই বিশ্বের মূলে রয়েছেন এক অনাদি বিশ্বস্রষ্টা। শব্দও কার্য, তাই শব্দের মূলেও একজন শব্দস্রষ্টা থাকতে হয়। শব্দগুলির প্রথম স্রষ্টা তাহলে কে ? যিনি বিশ্বস্রষ্টা তিনিই শব্দস্রষ্টা।
ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করেই আমরা ‘জল’ বলতে জল বুঝি, ‘অগ্নি’ বলতে আগুন বুঝি, উল্টোটা বুঝি না। ন্যায়মতে শব্দের সঙ্গে অর্থের প্রাসঙ্গিক সম্বন্ধ-নির্দেশিকা এই ঈশ্বরেচ্ছাকেই বলে শব্দের ‘শক্তি’। ন্যায়মতে এর অপর নাম ‘সংকেত’।
তাই ‘ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা’য় বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়সম্মত বক্তব্য হলো-
‘পরমেশ্বরেণ হি যঃ সৃষ্ট্যাদৌ পবাদি-শব্দানাম্ অর্থে সংকেতঃ কৃতঃ… তদ্ব্যবহারাচ্চ অন্নদাদীনামপি সুগ্রহঃ সংকেতঃ। সংকেতগ্রহো ন সম্বন্ধস্মৃতিম্ অপেক্ষতে।’- (ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা)
অর্থাৎ : সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর যে শব্দ দ্বারা যে অর্থ বুঝতে হবে বলে ‘সংকেত’ করেছিলেন (যেমন গো-শব্দের গরু অর্থে সংকেত করেছিলেন), এখন বৃদ্ধব্যবহার-পরম্পরায় বালকও সেই শব্দের দ্বারা সেই অর্থ বুঝতে পারে। এজন্য বালকের পক্ষে একথা স্মরণ করার প্রয়োজন পড়ে না যে একদিন ঈশ্বরই শব্দের সঙ্গে অর্থের মিলন ঘটিয়েছিলেন।… এখন বৃদ্ধব্যবহার অর্থাৎ সমাজ ও পরিবারে বড়োদের কথাবার্তাই শব্দার্থের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণের উপায়। কিন্তু সৃষ্টির আদিতে যে মহর্ষি বা দেবতারা ছিলেন তারা জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অলৌকিক শক্তির উৎকর্ষবশত পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সাক্ষাৎভাবে তাঁরই কাছ থেকে সহজেই কোন শব্দের কী অর্থ তা জেনেছিলেন। তাই আমরাও এখন পুরুষানুক্রমিক বৃদ্ধ-ব্যবহারের মাধ্যমে কোন বস্তুকে কী বলে তা সহজেই বুঝে নিতে পারছি।
কিন্তু শব্দার্থ-সম্বন্ধের এই ঐশ্বরিক বিধানের বিরুদ্ধে বাদ সাধলেন নিরীশ্বরবাদী মীমাংসকরা। তাঁদের মতে শব্দ, অর্থ ও শব্দার্থসম্বন্ধ কোনো ঈশ্বরের বিধান নয়। আবার তা কোন মানুষেরও বিধান নয়; ঋষি সম্প্রদায় কোন এক প্রাচীন যুগে সভায় বসে ঠিক করেন নি যে, এখন থেকে অমুক অমুক শব্দের অর্থ হোক, অমুক বস্তুর অমুক নাম হোক। পিতামাতা যেমন পুত্রকন্যার নামকরণ করে তেমনিভাবে মানুষের পক্ষে সামাজিক বিধানের দ্বারা আমাদের পরিচিত বা ব্যবহার্য জাগতিক বস্তুসমূহের নামকরণ করা সম্ভব নয়। মীমাংসদের মতে শব্দার্থসম্বন্ধ স্বাভাবিক, অর্থাৎ ঈশ্বর বা মানুষের অনুশাসনের দ্বারা স্থির হয়নি। স্মরণাতীত কাল থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় চিরকাল ধরে মানুষের সমাজে শব্দার্থ প্রচলিত রয়েছে। কোন মানুষটি কবে প্রথম জলকে ‘জল’ বলতে শিখেছিলো তা বলা যায় না। যার আদি খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ অবিচ্ছিন্ন ধারায় মানুষের ব্যবহারে সচল রয়েছে তাকেই এরা বলেছেন ‘স্বাভাবিক’, ‘নিত্য’ বা ‘অপৌরুষেয়’। এজন্য ঈশ্বর নিষ্প্রয়োজন। পাণিনিদর্শন অনুসারী বৈয়াকরণরা যদিও মীমাংসকদের মতো নিরীশ্বরবাদী নন, তবুও এ ব্যাপারে এরা একমত যে, শব্দের সাথে অর্থের সম্বন্ধ অনাদিকাল থেকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে চলে এসেছে। এর নাম ‘প্রবাহনিত্যতা’। অসাধু শব্দগুলি সাধুশব্দের অপভ্রংশ।
বেদের নিত্যতার অনুষঙ্গরূপে মীমাংসকরা শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদন করার আগে এভাবে শব্দার্থ-সম্বন্ধের নিত্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধটা যদি নিত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে অনুষঙ্গ হিসেবে শব্দ ও অর্থের নিত্যতাও স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। এটা ‘অর্থাপত্তি’-প্রমাণলভ্য। শব্দ ও অর্থের নিত্যতা কল্পনা না করলে এদের সম্বন্ধনিত্যতা উপপন্ন হয় না। তাই শাবরভাষ্যের তর্কপাদে শবরস্বামীর উপভোগ্য যুক্তিটি হলো-
‘বৃদ্ধদের কথাবার্তা ও ব্যবহার লক্ষ্য করে শিশু শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ নির্ণয় করে। ঐ বৃদ্ধরাও যখন শিশু ছিলো তখন তারাও ওভাবেই শব্দের অর্থ শিখেছে। এভাবে যত পেছনেই যাই না কেন শিশুরা সবসময়ই সমকালীন বৃদ্ধদের কাছ থেকেই শব্দের অর্থ শিখেছে। এরূপ কল্পনা করা সম্ভব নয় যে কোনো মানবগোষ্ঠির প্রথম শিশুরা প্রথম বৃদ্ধদের কাছে প্রথম শব্দার্থ শিখেছিলো। কারণ, তখনও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে ঐ কল্পিত প্রথম বৃদ্ধরাও কি একদিন শিশু ছিলো না ? তারা কার কাছে শিখেছিলো ? সুতরাং কোনো মানবগোষ্ঠির প্রথম শিশু, প্রথম বৃদ্ধ ও প্রথম ভাষাশিক্ষা কল্পনা করা যায় না। তাই শব্দ ও শব্দার্থসম্বন্ধ অনাদি। ঐ একই কারণে একথাও বলা যাবে না যে কোনো এক পুরাকালে কোন একদিন বৃদ্ধের দল সভা করে সাব্যস্ত করলো এখন থেকে এই শব্দের এই অর্থ হোক। তারা শব্দগুলি পেলো কোথায় ? সভায় বসে সিদ্ধান্ত নিতে হলে কথাবার্তা চালানোর জন্য যে শব্দগুলির প্রয়োজন সেই শব্দগুলির সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ কে ঠিক করেছিলো ? সুতরাং এমন কিছু শব্দ ও শব্দার্থসম্বন্ধ সমাজে নিশ্চয়ই ছিলো যা কোনো মানুষ নতুন টেবিল-চেয়ার তৈরি করার মতো নতুন করে তৈরি করেনি। একথার অর্থ হলো মানবসমাজে এমন কোনো আদিম কাল ছিলো না যখন শব্দ ও শব্দার্থসম্বন্ধ বর্তমান ছিলো না। এরূপ অনাদিব্যবহার প্রসিদ্ধিবোধে কেউ বলে শব্দ ও শব্দার্থ সম্বন্ধের নিত্যতা।’ (সূত্র: বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা দর্শন, পৃষ্ঠা-১০১)
এখানে উল্লেখ্য যে, এই অনাদিব্যবহার যুক্তির কারণেই মীমাংসকদের মতে পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মান্ড কেউ সৃষ্টি করেনি, পৃথিবী সহ বিশ্বেও জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। তাই মানবজাতিও কেউ সৃষ্টি করেনি, জাতি হিসেবে চিরকাল ছিলো, বংশপরম্পরায় চিরকাল থাকবে। কোন মূল সৃষ্টিকর্তা নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবী ও মানুষ চিরকাল ধরে থাক বা না থাক মীমাংসকদের একটা কথা মূলত ঠিক যে, কোন ভাষাগোষ্ঠির মানুষ কোনদিন সমবেত হয়ে স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে আইন পাশ করে নিজেদের ভাষা সৃষ্টি করেনি, কোন মোড়লের ফরমান দিয়েও সৃষ্টি হয়নি। ‘গরু’ শব্দটির দ্বারা এই রকমের আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী বুঝতে হবে- এহেন আইন বা ফরমানের ভাষা বা শব্দরাশি তো তাহলে আগে থেকেই থাকা দরকার, এই শব্দগুলির সঙ্গে নির্দিষ্ট অর্থের সম্বন্ধটাও নিশ্চয়ই আগে থেকেই ছিলো। না হলে এগুলি কোথা থেকে এলো ?
যারা মনে করেন বেদ অপৌরুষেয় নয়, তাদের দিক থেকে শব্দের নিত্যতা সম্পর্কে নানারূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। যেমন, শব্দ সৃষ্ট তাই শব্দ অনিত্য, শব্দ অনিত্য হলে অসংখ্য শব্দ ও বাক্যের সমষ্টি বেদকেও অনিত্য বলতে হয়। এসব আপত্তি খন্ডন করতে গিয়ে মীমাংসকরা বলেন যে, উচ্চারণ দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, সৃষ্টি হয় না। যে ধ্বনির মাধ্যমে শব্দ প্রকাশ করা হয় তার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। শব্দের বিনাশ হতে পারে না। এসব ব্যাখ্যাকল্পে মীমাংসকরা দু’প্রকার শব্দ স্বীকার করেন- বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ। ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’, ‘ঘ’ প্রভৃতি বর্ণাত্মক শব্দ। এগুলির সাহায্যে পদ বা শব্দ, ধাতু প্রভৃতি গঠিত হয়। যে শব্দ কেবল ধ্বনিমাত্র তাকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে, যেমন ঝড়ের শব্দ, শঙ্খের শব্দ, ভেরীর শব্দ। এই ধ্বনিগুলির পেছনে কোন নিত্য শব্দদ্রব্য নেই। মীমাংসামতে এসব ধ্বন্যাত্মক শব্দ বায়ুর গুণ এবং তা অনিত্য। কিন্তু অর্থবহ ভাষায় প্রযুক্ত ভাষার সংঘটক বর্ণাত্মক শব্দ কোনো দ্রব্যের গুণ নয়। সে নিজেই দ্রব্য এবং নিত্য। বর্ণাত্মক শব্দ বায়বীয় নয়, সেহেতু তার নাশ হয় না। বৈদিক শব্দ বর্ণাত্মক শব্দ তাই বেদও নিত্য। ধ্বনি অনিত্য। ‘ম’ এই বর্ণটি বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি উচ্চারণ করলে বিভিন্ন ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এই বিভিন্ন ধ্বনি একই ‘ম’ বর্ণের প্রকাশ। উচ্চারণের দ্বারা ‘ম’ বর্ণ সৃষ্ট হয় না, প্রকাশ হয় মাত্র। এর ধ্বনি বিভিন্ন। যে ধ্বনির মাধ্যমে শব্দ প্রকাশ করা হয় তার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। শব্দের বিনাশ হতে পারে না। তাই ধ্বনি অনিত্য, শব্দ নিত্য।
শুধু তাই নয়, শব্দের নিত্যতা প্রসঙ্গে মীমাংসকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো- ধ্বন্যাত্মক শব্দকে অর্থবহ শব্দ বলা যায় না। কোন ভাষাগোষ্ঠিতে প্রচলিত কোন শব্দকে যদি সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে হয়, তাহলে সমাজের সকল মানুষকেই একটি নির্দিষ্ট শব্দের দ্বারা একটি সমান নির্দিষ্ট অর্থ বুঝতে হবে। কেউ যদি ‘গরু’ বলতে ছাগল বোঝে, আর কেউ যদি ঘোড়া বোঝে, অন্য কেউ যদি গরু বোঝে, তাহলে মানুষের ভাষা সামাজিক বিপর্যয়ের বাহন হয়ে দাঁড়াবে, কেউ কারো কথার অর্থ বুঝবে না, মানুষের জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এজন্যই ধ্বন্যাত্মক শব্দকে অর্থবহ শব্দ বলা যায় না। ব্যাপারটা আরেকটু ভেবে দেখা যেতে পারে।
আমরা যখন কোনো অর্থ বোঝাবার জন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করতে ইচ্ছা করি তখন আমাদের নিঃশ্বাসবায়ু কণ্ঠ ও জিহ্বামূল থেকে ঠোঁট ও নাক পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চারণ স্থানগুলিতে আঘাত করে নির্গত হয়, তারই ফলে বিভিন্ন ধ্বনি নিষ্পন্ন হয়। এখন এই ধ্বনিগুলিকেই যদি অর্থবহ শব্দ বলি তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াবে- যত লোকে যতবার ‘গরু’ শব্দটি উচ্চারণ করছে ততটা ‘গরু’ শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে বলতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। যদি দশবার উচ্চারিত হয়, দশবারে ধ্বনি দশটি হলেও বোল কিন্তু একই। অর্থাৎ ধ্বনি অসংখ্য হলেও শব্দ একটি ‘গরু’। এর অর্থ হলো অসংখ্যবার অনুরূপ ধ্বনির দ্বারা একই ‘গরু’ শব্দ প্রকাশিত হচ্ছে। এজন্যেই দশখানা অভিধানে দশবার ‘গরু’ শব্দটি ছাপা হলেও আমরা বলি ‘গরু’। শব্দ একটাই, শব্দচিত্রের আকৃতিও একটাই। কিন্তু শব্দচিত্র সংখ্যায় দশটি। এক সংখ্যার ‘১’ এরূপ সংখ্যা-চিত্রটি লক্ষবার লক্ষ জায়গায় ছাপা হলেও আমরা বলি এক এই সংখ্যা একটাই। এর প্রতীকী চিত্রাকৃতিও একটাই, যদিও লক্ষবার ছাপায় আঁকা হয়েছে বলে ‘১’ সংখ্যাটির ছবি সংখ্যায় লক্ষ হয়ে গেছে। কারো বাবার ছবি দশখানা থাকলেও বাবা দশজন হয় না। দশখানা ছবি একই ব্যক্তিকে দশবার প্রকাশ করেছে মাত্র। এভাবেই অসংখ্য ধ্বনি অসংখ্যবার একই শব্দকে প্রকাশ করে বা অভিব্যক্তি করে। উচ্চারিত ধ্বনি তাই শব্দের অভিব্যঞ্জক, শব্দ হলো অভিব্যঙ্গ্য। তাই শাস্ত্রদীপিকা’য় ভাট্টমীমাংসক পার্থসারথি মিশ্র বলেন-
‘এবং চোচ্চারণং শব্দস্য ন কারণং কিন্তু অভিব্যঞ্জকম্ ইতি সিদ্ধম্’।- (শাস্ত্রদীপিকা)
অর্থাৎ : ধ্বনি শব্দের কারণ নয়; ধ্বনি দ্বারা শব্দ উৎপাদিত হয় না, প্রকাশিত হয়।
আবার ধ্বনি উচ্চ হয়, নীচ হয়, দ্রুত হয়, বিলম্বিত হয়, কোমল হয়, কর্কশ হয়। ধ্বনিগুলি আলাদা, অথচ অর্থবোধক শব্দ কিন্তু একটাই। ‘গরু’ শব্দটি উচ্চ নীচ, দ্রুত বিলম্বিত, কোমল কর্কশ যেভাবেই উচ্চারিত হোক না কেন, এতো ধ্বনিভেদ সত্ত্বেও ঐ একটি ‘গরু’ শব্দ চিনে নিতে ভুল হয় না। শব্দের অভিব্যঞ্জক ধ্বনিগুলির দ্রুত-বিলম্বিত প্রভৃতি গুণ অভিব্যঙ্গ্য শব্দটিতে আরোপ করে আমরা বলে থাকি শব্দটা দ্রুত বা বিলম্বিত। আসলে কিন্তু তা নয়। ঐ গুণগুলি প্রকাশক ধ্বনির, প্রকাশ্য শব্দের নয়। ধ্বনিগুলিকে অর্থবহ শব্দ বলে মেনে নিলে প্রকৃতপক্ষেই বিপত্তি দেখা দেবে। তাই ধ্বন্যাত্মক শব্দকে অর্থবহ শব্দ বলা যায় না। ক্ষণস্থায়ী শব্দধ্বনিগুলিকে অর্থবহ শব্দ বলে মেনে নিলে তখন কোন বক্তার পক্ষে কোন শ্রোতাকে কোন শব্দ দ্বারা কোন অর্থ বোঝানো সম্ভব হবে না। একদিকে ধ্বনিভেদে শব্দ আলাদা হয়ে যাবে, আবার অন্যদিকে ব্যক্তিভেদে অর্থও আলাদা হয়ে যাবে। একটি ‘মানুষ’ শব্দের দ্বারা যে কোনো মানুষকে যে আমরা বুঝতে পারি, এবং এভাবে নিয়ন্ত্রিত শব্দার্থ-সম্বন্ধের দ্বারাই একই ভাষাগোষ্ঠির মানুষ যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমাজজীবন এগিয়ে নিয়ে যায়- এই বাস্তব ঘটনাটাই অবাস্তব হয়ে পড়বে। প্রত্যেকটি মানুষ পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এহেন আত্মবিলুপ্তি আর সমাজবিলুপ্তি একই কথা। তাই শব্দধ্বনি যতোই আলাদা হোক, ব্যক্তি যতোই বিভিন্ন হোক, আমরা অসংখ্য ধ্বনির পেছনে একটি সাধারণ সমান শব্দ আবিষ্কার করি, অসংখ্য ব্যক্তির পেছনে একটি সমান সাধারণ অর্থের প্রতিভাস অনুভব করি। তাই ‘মানুষ’ এই একটি শব্দের দ্বারা যে কোনো মানুষকে বুঝতে পারি।
আমরা যখন ‘মানুষ’ বলতে যে কোনো মানুষ বুঝি, ‘গরু’ বলতে যে কোনো গরু বুঝি তখনও ব্যক্তির সাধারণ রূপটিকে বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লিষ্ট করি। এই বিশ্লেষণকে বলে সাধারণীকরণ। শব্দার্থেও সাধারণীকরণ প্রায় সব দার্শনিকই স্বীকার করেন। তাই নৈয়ায়িকরা বলেন, শব্দের অর্থ হলো জাতিবিশ্লিষ্ট ব্যক্তি। ‘জাতি’ মানে একজাতীয় সকল ব্যক্তির (particulars) সাধারণ ধর্ম বা স্বভাব যার দ্বারা অন্যজাতীয় ব্যক্তিসমুদয় থেকে কোনো একজাতীয় ব্যক্তিসমুদয়কে আমরা পৃথক করতে পারি। সকল মানুষের সাধারণ ধর্মকেই বলে মনুষ্যত্ব, সকল গরুর সাধারণ ধর্মকে বলে ‘গোত্ব’। বৌদ্ধমতে ব্যক্তির এই সাধারণ রূপটিকে বলে ‘সামান্য’। বৌদ্ধমতে সামান্য বা জাতি বাস্তব নয়, কাল্পনিক। কিন্তু এ জাতীয় কল্পনা ছাড়া লোকব্যবহার বা সামাজিক জীবনযাত্রা অসম্ভব। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শুদ্ধ ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষ এবং কল্পনাগ্রাহ্য ‘সামান্য’ এই দুয়ের মিশ্রণেই লোকব্যবহার সম্ভব হয়।
মীমাংসকদের মতে, শব্দের প্রাথমিক অর্থ হলো একজাতীয় সকল ব্যক্তিতে নিহিত একটি সাধারণ রূপ, যার অপর নাম ‘আকৃতি’। এই জাতি বা আকৃতি বিষয়ে শবরস্বামী বলেছেন-
‘দ্রব্যগুণকর্মণাং সামান্যমাত্রম্ আকৃতিঃ।’- (শাবরভাষ্য)
অর্থাৎ : দ্রব্যগুণ বা কর্মের সামান্যমাত্রকে আকৃতি বলে।
তবে শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিলভট্ট আরো স্পষ্ট করে বলেছেন-
‘জাতিমেবাকৃতিং প্রার্হুব্যক্তিরাক্রিয়তে যয়া।’- (শ্লোকবার্ত্তিক)
অর্থাৎ : যার দ্বারা ব্যক্তি আকৃত বা নিরূপিত হয়, তাই আকৃতি।
কিন্তু বুদ্ধিবিশ্লিষ্ট আকৃতির দ্বারা ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী কাজকারবার চালানো যায় না। ব্যবহারিক কার্যসাধকতাকে বৌদ্ধ দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয় ‘অর্থক্রিয়াকারিত্ব’। কার্যসাধন হয় ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা। গরুমাত্রের সাধারণ ‘আকৃতি’ বা গোত্ব থেকে দুধ পাওয়া যায় না, দুধ দেয় গো-ব্যক্তি, একটি বিশেষ গরু। ব্যবহারিক মূল্যটা গো-ব্যক্তির, ‘গো-সামান্য’ বা ‘গবাকৃতির’ নয়। সুতরাং শব্দের প্রাথমিক অর্থটি ‘সামান্যাকারে ভাসমান’ হলেও, শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র অর্থটি সাধারণভাবে উপস্থিত হলেও, কান টানলে মাথাটাও চলে আসার মতোই ‘গরু-সাধারণে’র সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক মূল্যের বাহক গরু-ব্যক্তিটিও চলে আসে। কারণ গো-জাতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যটা (গোত্ব) ঘাস খায় না, ঘাস খায় একটি গরু-ব্যক্তি। সামান্য (universal) ও বিশেষ (particular) এই দুই মিলিয়েই বস্তুর সত্তা। তাই কুমারিল বলেছেন- ‘বস্তু দ্ব্যাত্মক’। দুটিই সমান সত্য। দুই মিলে পূর্ণ সত্য। এভাবে সামান্যের মাধ্যমে বিশেষের উপস্থিতিকে, একের অবিচ্ছেদ্য আনুষঙ্গিক রূপে অপরের প্রতিভাস বা জ্ঞানকে বলে ‘আক্ষেপ’ (immediate implication)। সামান্যের দ্বারা বিশেষ আক্ষিপ্ত হয়।
শব্দের শক্তি :
ভাট্টমীমাংসা মতে শব্দ প্রাথমিক স্তরে সোজাসুজি জাতি বা সামান্যকে বোঝায়, দ্বিতীয় স্তরে বোঝায় ব্যক্তিকে। শব্দের এই প্রাথমিক স্তরের অর্থবোধ সামর্থ্যকে বলে ‘অভিধা বৃত্তি’, সংক্ষেপে ‘শক্তি’। দ্বিতীয় স্তরের অর্থবোধ সামর্থ্যকে বলে ‘লক্ষণা বৃত্তি’। এরূপ সামর্থ্যই হলো শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ। ‘বৃত্তি’ মানে সম্বন্ধ। প্রাথমিক স্তরের অর্থকে বলে মুখ্যার্থ, ‘অভিধেয়’ বা ‘শক্যার্থ’ এবং দ্বিতীয় স্তরের অর্থকে বলে ‘লক্ষ্যার্থ’। যেমন ‘গরু ঘাস খায়’ বললে প্রথমে গো-জাতির কথাই মনে হবে, কারণ রামের গরু বা রহিমের গরু, কালো গরু বা সাদা গরুর কথা বলা হয়নি, যে কোনো গরুর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং গো-জাতিই মুখ্যার্থ বা শক্যার্থ। কিন্তু গো-জাতিটা ঘাস খায় না, ঘাস খায় একটি নির্দিষ্ট গো-ব্যক্তি। তাই আমরা দ্বিতীয় স্তরে গো-জাতি থেকে গো-ব্যক্তিতে অর্থাৎ লক্ষ্যার্থে পৌঁছে যাই।
কিন্তু অনেকে এমত স্বীকার করেন না। গরু বললে প্রথমে ‘গো-জাতি’ বুঝি, পরে ‘গো-জাতি’র ‘অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব’ নেই বলে (অর্থাৎ গো-জাতিটা ঘাস খায় না, বা গো-জাতিটাকে বেঁধে রাখা যায় না। এভাবে গো-জাতিটার সঙ্গে সরাসরি কোনো ক্রিয়ার সম্বন্ধ নেই বলে) আমরা গো-জাতির মাধ্যমে গো-ব্যক্তিকে বুঝি, যার সাক্ষাৎ অর্থক্রিয়াকারিত্ব রয়েছে- এরূপ ধারণার অর্থ হলো, ‘গরু’ শব্দটির পরিপূর্ণ অর্থ বুঝতে আমাদের দুটি ক্রমিক স্তর দরকার হয়। একটি আগে আর একটি পরে। কিন্তু এরকম ‘পৌর্বাপর্য’ বা আগ-পর আমাদের অনুভবসিদ্ধ নয়। বোধের এই ক্রমিকত্ব আমাদের বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। আমরা জাতি ও ব্যক্তি একই সঙ্গে বুঝি, জাতি আগে উপস্থিত হয়, ব্যক্তি উপস্থিত হয় বিলম্বে, আমাদের অভিজ্ঞতায় এরূপ খন্ডিত বোধের হদিশ মেলে না। সামগ্রিকভাবে জাতি ও ব্যক্তি মিলিয়ে একই মুহূর্তে আমাদের একটা সামগ্রিক বোধ হয়।
এ প্রেক্ষিতে জাতি ও ব্যক্তির (সামান্য ও বিশেষের) পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শাবরভাষ্যের কুমারিলকৃত ‘তন্ত্রবার্তিক’ নামক টীকার প্রামাণিক ব্যাখ্যাকার ভট্টসোমেশ্বর তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ন্যায়সুধা’য় কুমারিল মতের ব্যাখ্যায় বলেন-
‘জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হলো ভেদাভেদ। অর্থাৎ ভেদ-অভেদ। জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে ঐকান্তিক ভেদ নেই। জাতি হলো বিশেষণ, ব্যক্তি হলো বিশেষ্য। বিশেষণরূপে জাতি বিশেষ্যরূপ ব্যক্তিতে আশ্রিত। জাতি ও ব্যক্তির বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধটি একটি বিশেষ ধরনের সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধের কখনো ছেদ হয় না। কুল কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে, পাকলে লাল হয়, সবুজ রঙ ছেড়ে লাল রঙ গ্রহণ করে। কিন্তু ব্যক্তি এক জাতিকে ছেড়ে অন্য জাতি গ্রহণ করে না। গরুটা ঘোড়া হয়ে যায় না, গোত্ব ছেড়ে দিয়ে অশ্বত্ব গ্রহণ করে না। যারা পরস্পর একান্তই ভিন্ন তাদের একটি আরেকটিকে ছেড়ে থাকতে পারে। যদি বিশেষণরূপ জাতি বিশেষ্যরূপ ব্যক্তি হতে একান্তই ভিন্ন হবে, তা হলে ব্যক্তির জ্ঞানটা সবসময়েই জাতি দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পায় কেন ? কালো গরু, সাদা গরু, যে কোন গো-ব্যক্তিই গরু বলে শনাক্ত হয় কেন ? গোত্ব হলো সকল ব্যক্তির সাধারণ চারিত্রিক ধর্ম বা স্বভাব (essence)। তাই জাতি ও ব্যক্তি অত্যন্ত ভিন্ন হতে পারে না। আবার এরা সম্পূর্ণ একও নয়। কারণ ব্যক্তি বহু, কিন্তু জাতি একই। জাতি ও ব্যক্তি একান্ত অভিন্ন হলে জাতির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে গিয়ে ব্যক্তিও একটাই হতো। অথবা ব্যক্তির সঙ্গে মিলে গিয়ে জাতিও বহু হয়ে যেতো। এজন্যই জাতি ও ব্যক্তির সম্পর্কটা ঐকান্তিক ভেদও নয়, ঐকান্তিক অভেদও নয়, কিন্তু ভেদাভেদ। এই আপেক্ষিক অভেদের জন্যই, কোনো শব্দের দ্বারা জাতির জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে (অর্থাৎ একই সঙ্গে) ব্যক্তিরও জ্ঞান হয়।’ (সূত্র: বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন, পৃষ্ঠা-১০৬)
এখানে আবার প্রশ্ন উঠেছে, শব্দ দ্বারা যখন জাতি-ব্যক্তি দুটোকেই বোঝা যাচ্ছে, তখন কি আমরা শুদ্ধ বা নিছক ব্যক্তি হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে, একই বোধের ভেতরে দুটোকে আলাদা করে বুঝতে পারি ? একই সঙ্গে দুটো মানুষকে যেমন আলাদা করে দেখি, একই সামগ্রিক জ্ঞানে দুটো মানুষ যেমন পৃথকভাবে ভাসমান হয় জাতি ও ব্যক্তির ক্ষেত্রেও কি ব্যাপারটা সেরকমের ? তা যদি না হয় (এবং হতে পারে না, কারণ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আপেক্ষিকভাবে অভেদ রয়েছে) তবে কোনটি অপেক্ষাকৃত প্রধান, কোনটি অপ্রধান ?
সিদ্ধান্ত হলো জাতিই প্রধান, ব্যক্তি অপ্রধান। কারণ ব্যক্তির বোধটাও জাতিরূপে বা সামান্যাকারেই হয়ে থাকে। যেমন ‘সকল মানুষই মরণশীল’ বললে পৃথিবীর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যাবতীয় মানুষের অনন্ত কোটি সম্ভাব্য চিত্র আমাদের মগজের দৃষ্টিকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হয়। আমরা সাধারণভাবে বুঝি যে-কোন মানুষই মরণশীল। মরে মানুষ ব্যক্তিটি, মনুষ্যত্ব নামক জাতি বা সামান্যটা মরে না। ‘মনুষ্যত্বের কবর’ সাহিত্যের আলংকারিক ভাষায় হলেও বাস্তবে হয় না। মনুষ্যত্বটা কবরে বা চিতায় শুয়ে পড়ে না। অর্থাৎ আমরা বুঝি যে-কোনো মানুষ মরে, রাম বা রহিম কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝি না। তেমনি গরু ঘাস খায় বললে রামের কালো রঙের মঙ্গলা গাইটি নির্দিষ্ট করে বুঝি না। বুঝি যেকোনো গরু। এভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষকে নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট না করে ব্যক্তিমাত্রকে বোঝাকে সোমেশ্বর বলেছেন ‘অনির্ধারিতবিশেষা’ ব্যক্তির বোধ। একেই বলে সামান্যাকারে ব্যক্তিবোধ। এভাবে শব্দের দ্বারা সামান্যাকারে অনির্দিষ্টভাবে ব্যক্তি জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয় বলেই জাতি ও ব্যক্তির যুগপৎ বোধ জন্মালেও আকৃতি বা জাতিরই প্রাধান্য স্বীকার করতে হবে।
শব্দনিত্যতা মূলত বর্ণনিত্যতা :
মীমাংসকদের শব্দনিত্যতা মূলত বর্ণনিত্যতা। তাঁরা শব্দের অর্থকে আকৃতি বা জাতি বললেও শব্দকে অনুরূপভাবে জাতি বলতে রাজি নন। তাঁদের মতে অর্থবহ শব্দ উচ্চারিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ হতে পারে না, ধ্বনি বা নাদ থেকে তা স্বতন্ত্র। এ প্রসঙ্গে মীমাংসকদের যুক্তি হলো, ক, খ, গ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বর্ণ নিত্য। যখন বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নবার ‘গ-কার’ উচ্চারণ করে তখন বর্ণধ্বনিগুলি আলাদা আলাদা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বিভিন্ন ‘গ’ ধ্বনিগুলি একটা ‘গ’ বর্ণকে প্রকাশ করছে যার জন্য আমরা বলি- সবাই একই ‘গ’ বলছে। এভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নাকারে উচ্চারিত ‘গ’ ধ্বনি দ্বারা অনাদি-কালস্থিত ‘গ’ শব্দ অবিব্যক্ত হচ্ছে। আমরা ধ্বনিগুলিকে এক বলতে পারি না। কারণ তা হলে একজন ‘গ’ উচ্চারণ করলে সবার মুখ দিয়ে ‘গ’ ধ্বনি বেরিয়ে আসতো। অথবা একজন উচ্চারণ বন্ধ করলে সবার মুখের ‘গ’ ধ্বনি থেমে যেতো। যেমন সকল মানুষ ব্যক্তি হিসেবে এক হলে একজন মারা গেলে সবাই মারা যেতো, একজন জন্মালে সবাই জন্মাতো। শঙ্খের শব্দ, ভেরীর শব্দ এদের বেলা কী হবে ? সিদ্ধান্ত হলো, এই ধ্বনিগুলির পেছনে কোন নিত্য শব্দদ্রব্য নেই, এই ধ্বনিগুলি বায়ুর গুণ। কেবল অর্থবহ ভাষায় প্রযুক্ত, ভাষার সংঘটক বর্ণরূপ শব্দগুলিই নিত্য।
এখন প্রশ্ন, বর্ণ নিত্য হলেই কি বেদবাক্যের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় ? বাক্য নিত্য হতে হলে বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলিও নিত্য হতে হবে। কিন্তু বর্ণ ও শব্দ নিত্য হলেও বাক্য নিত্য হবে এমন কোনো কথা নেই। বাক্য রচনা তো বক্তার ইচ্ছাধীন। একটা সমগ্র অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনে বক্তা শব্দগুলিকে নানাভাবে সাজিয়ে বাক্য রচনা করে। বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি ‘পদ’ বলে পরিচিত। মীমাংসকদেরকে প্রথম ধাপে বর্ণের নিত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করতে হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে আসে পদনিত্যতার প্রশ্ন।
মীমাংসামতে বর্ণগুলি নিত্য। কিন্তু বর্ণগুলি স্বতন্ত্রভাবে কোনো অর্থপ্রকাশ করে না। ক, খ বা গ-এর কোনো অর্থ নেই। শব্দের অর্থ পেতে হলে বর্ণগুলিকে বিভিন্ন ক্রমে সাজাতে হয়। এভাবে বর্ণের বিভিন্ন ক্রমিক সন্নিবেশ, সংস্থান বা পরিপাটিকেই সাধারণভাবে অর্থবহ শব্দ বা পদ বলা হয়। ক্রমের আরেক নাম ‘আনুপূর্বী’। একই বর্ণসমষ্টি বিভিন্ন ক্রমে সাজালে বিভিন্ন অর্থের বাহক বিভিন্ন পদ পাওয়া যায়। যেমন, ‘বন’ (ব্-অ-ন্-অ) এবং ‘নব’ (ন্-অ-ব্-অ)। বর্ণসমষ্টি একই, কিন্তু ক্রমভেদে শব্দ আলাদা হলো, অর্থও আলাদা হলো।
এ প্রেক্ষিতে যে প্রশ্ন মীমাংসকদের সংকটে ফেলেছে তা হলো, বর্ণগুলির এই বিভিন্ন ধরনের ক্রমিক সন্নিবেশ যা অর্থবহ শব্দরূপে সমাজে পরিচিত, এই সন্নিবেশগুলি কি নিত্য, অর্থাৎ পদগুলি কি নিত্য ? কেননা, পদগুলিকে নিত্য বলে স্বীকার না করলে বেদবাক্যকে নিত্য অপৌরুষেয় বলা চলে না। আবার পদগুলিকে নিত্য বললে, আলাদা করে বর্ণগুলিকে নিত্য বলার কোনো মানে হয় না। সমাজে ব্যবহৃত অর্থবহ শব্দগুলি যদি নিত্য ও অনাদি হয় তার মানে দাঁড়াচ্ছে- ক্রমানুপাতী বর্ণসমষ্টি-রূপ শব্দ থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্ণগুলির পৃথক অস্তিত্বের কোনোদিন কোনো অবকাশ ছিলো না। পদ বা শব্দগুলি নিত্য হলে একথা আর বলা চলবে না যে বিভিন্ন বর্ণগুলিকে বিভিন্ন ক্রমানুসারে জুড়ে দিয়ে বিভিন্ন পদ তৈরি হয়েছে। অংশগুলি জোড়া লাগিয়ে যা তৈরি হয় তা আবার নিত্য হয় কী করে ?
বর্ণনিত্যতাবাদী মীমাংসকরা এ প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তরে কিছুটা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বলেন- পদগুলি বিভিন্ন ক্রমসন্নিবিষ্ট বর্ণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্রমবিশিষ্ট বর্ণসমূহকেই পদ বলে। তাই ক্রমবিশিষ্ট বর্ণই অর্থের বাচক। সুতরাং বর্ণ নিত্য হলে পদও নিত্য হবে, ক্রম এবং ক্রমিকভাবে সাজানো বর্ণ এই দুয়ের মধ্যে বর্ণই হলো প্রধান এবং বিশেষ্য, ক্রম হলো অপ্রধান এবং বিশেষণ। তাই বর্ণবিশিষ্ট ক্রমকে অর্থবোধক পদ না বলে ক্রমবিশিষ্ট বর্ণকে অর্থবোধক পদ বলা উচিত।
কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা হলো, ক্রমবিশিষ্ট বর্ণকে পদ বলা হবে, না বর্ণবিশিষ্ট ক্রমকে পদ বলা হবে, কোনটা বিশেষ্য আর কোনটা বিশেষণ, তার বিধিগমনা বা ক্রাইটেরিয়া কী ? বরং ক্রমের প্রাধান্যটাই তো স্বাভাবিক। ইতস্তত ছড়ানো ক, খ, গ বর্ণগুলি নিত্যই হোক আর অনিত্যই হোক, ওগুলির দ্বারা কোনো অর্থই বোঝা যায় না, পৃথকভাবে এদের কোনো অর্থ নেই। বিভিন্ন ক্রমে সাজালেই সেই ক্রমিক সন্নিবেশ বা সংস্থান থেকেই অর্থটা পাওয়া যায়। তাই ক্রমিক বর্ণকে অর্থবহ শব্দ না বলে বর্ণক্রমটাকেই অর্থের বাচক বলা অধিক সংগত নয় কি ? বর্ণ নিত্য হলেও, ক্রমটাও যে নিত্য হবে তার কোনো যুক্তি নেই। কোনো আদিম যুগের মানুষ হয়তো বর্ণগুলিকে বিভিন্ন ক্রমে সন্নিবিষ্ট করে বিভিন্ন শব্দের সৃষ্টি করেছে।
এসব বিবেচনা করে অগত্যা কুমারিলকে পদনিত্যতার ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে আলোচিত ব্যবহারিক নিত্যতা বা প্রবাহনিত্যতার আশ্রয় নিতে হয়েছে-
‘ন চ ক্রমস্য কার্যত্বং পূর্বসিদ্ধপরিগ্রহাত্ ।।
বক্তা ন হি ক্রমং কঞ্চিত্ স্বাতস্ত্র্যেণ প্রপদ্যতে।
যথৈবাস্য পরৈরুক্তিস্তথৈরৈবনং বিবক্ষতি।।
পরে্যাপোবমতশ্চচাস্য সম্বন্ধবদনাদিতা।
তেনৈবং ব্যবহারাত্ স্যাদকৌটস্থ্যেৎপি নিত্যতা।।’- ( শ্লোকবার্ত্তিক: শব্দনিত্যতা শ্লোক-২৮৭-৮৯)
অর্থাৎ : অর্থবহ শব্দগুলি মনুষ্যসমাজে অনাদি-ব্যবহার সিদ্ধ। পূর্ব-পূর্বপুরুষ-পরম্পরাগত শব্দগুলি পরপর পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত হয়ে এসছে। কে বা কারা শব্দগুলি সৃষ্টি করেছিলো, বিভিন্ন ক্রমানুসারে বর্ণগুলি সাজিয়েছিলো তা কেউ বলতে পারে না, এর কোনো মূল আরম্ভ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই পদগুলিও অনাদি নিত্য।
ব্যবহারিক নিত্যতা বোঝাতে ভাট্টমীমাংসক পার্থসারথিমিশ্র একটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, ‘অনিদংপ্রথমত্ব’- অর্থাৎ এটাই কোন শব্দের প্রথম ব্যবহার একথা বলা যায় না। মীমাংসামতে ক, খ, গ প্রভৃতি বর্ণগুলি কূটস্থ নিত্য, অর্থাৎ অবিকৃত, সর্বব্যাপী, নিত্য পদার্থ, যার কোন পরিবর্তন নেই। এই কূটস্থ নিত্য বর্ণগুলিই বিভিন্ন ক্রমানুসারে সন্নিবিষ্ট হয়ে ক্রমিক উচ্চারণ ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু ভাষার ইতিহাসে কোন সর্বপ্রথম মূল উচ্চারণ বা উচ্চারয়িতা নিরূপণ করা অসম্ভব। ক্রমসন্নিবেশের পূর্বেও বর্ণগুলি ছিলো, না হলে ক্রমটা হবে কাদের নিয়ে ? কুমারিলের ভাষ্য অনুযায়ী কেবল আদি জানা যায় না বা জানার উপায় নেই বলে অর্থবহ পদগুলিকে অনাদি নিত্য বলা হয়েছে। বেদ বাক্যগুলিও এভাবে নিত্য।
মানুষ যে বাক্যগুলি রচনা করে, তা অভ্রান্ত নয়। কিন্তু বেদবাক্য অভ্রান্ত বলে মীমাংসকরা স্বীকার করেন। বেদবাক্যের কোনো রচয়িতা আছে বলে কেউ স্মরণ করতে পারে না, ঋষি-পরম্পরায় অনাদি স্মরণাতীত কাল থেকে চলে এসেছে। তাই মানুষের বাক্য অনিত্য হলেও বেদবাক্য নিত্য অপৌরুষেয়। মীমাংসকদের এই যুক্তি অনুসারে বেদনিত্যতা কিন্তু বিশুদ্ধ নিত্যতা নয়। বিশুদ্ধ নিত্যতা হলো বিকারহীন অপরিবর্তনীয় নিত্যতা যাকে বলা হয় ‘কূটস্থ’ নিত্যতা। বেদবাক্য কূটস্থ নিত্য নয়। এদের ব্যবহারিক নিত্যতা বা প্রবাহনিত্যতাই স্বীকার্য।
বর্ণগুলি যে আগে থেকে চিরকালই ছিলো, ক্রমটা অর্থাৎ বর্ণক্রমরূপ শব্দগুলি পরে এসেছে তা শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিল অন্যভাবে বলে দিয়েছেন-
‘বর্ণনামপি নন্বেবমকৌটস্থ্যেৎপি সেত্স্যতি।।
নিত্যেষু সত্সু বর্ণেষু ব্যবহারাত্ ক্রমোদয়ঃ।
ঘটাদিরচনা যদ্বন্ নিত্যেষু পরমাণুষু।।
তদভাবে হি রচনা নির্মূলা নাবধার্যতে।’ ( শ্লোকবার্ত্তিক: ২৯০-৯২)
অর্থাৎ : নিত্য পরমাণুগুলি বরাবর আগে থেকে রয়েছে বলেই তো ঘটপ্রভৃতি বস্তু তৈরি করা সম্ভব। উপাদানগুলি আগে থেকে না থাকলে বস্তুরচনা হবে কী দিয়ে ? তাই বর্ণগুলির কূটস্থ নিত্যতাই স্বীকার করতে হবে, ব্যবহারিক নিত্যতামাত্র নয়।
পরে এসেছে মানেই হলো কোনো এক সময় উৎপন্ন হয়েছে, শুধু কবে প্রথম শুরু হয়েছে বলা যায় না, অর্থাৎ ‘অনিদংপ্রথমত্ব’। এরই নাম ব্যবহারিক নিত্যতা। কুমারিল প্রদত্ত পরমাণু ও ঘটের দৃষ্টান্ত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শেষপর্যন্ত বৈদিক বাক্যেরও মূল আছে, এবং এই মূল হলো নিত্য উপাদানস্বরূপ বর্ণসমূহ। কেননা, উপাদানকে নিশ্চয়ই ‘উপাদেয়’ ক্রমরচনার পূর্বে থাকতে হবে।
পদ যদি ব্যবহারিক নিত্য হয় তবে পদ-সমষ্টিরূপ বেদবাক্যও ব্যবহারিক নিত্যই হবে। সুতরাং বর্ণগুলি যে অর্থে কূটস্থ নিত্য বা বৈশেষিকের পরমাণু যে অর্থে নিত্য, বেদবাক্যকে সে অর্থে নিত্য বলা যাবে না। তাছাড়া বৈদিক পদ ও তার অর্থ যে লৌকিক সংস্কৃত পদ ও তার অর্থ থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়, একথা স্বয়ং শবরস্বামী স্পষ্টভাবেই বলেছেন-
‘য এব লৌকিকাঃ শব্দা স্ত এব বৈদিকাঃ, ত এবৈষামর্থাঃ’- (শাবরভাষ্য: মীমাংসাসূত্র-১/৩/৩০)
অর্থাৎ : বৈদিক পদ ও তার অর্থ লৌকিক সংস্কৃত পদ ও তার অর্থ থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়।
তার মানে, বেদের নিত্যতাও অর্থবহ পদ বা শব্দের মতো ব্যবহারপ্রসিদ্ধ। নিত্য বর্ণগুলি হলো পদ ও বাক্যের মৌলিক উপাদান, ফলে এরা বেদবাক্যেরও উপাদান, বৈদিক শব্দার্থ ও লৌকিক শব্দার্থ অভিন্ন। তাহলে লৌকিক বাক্য থেকে বেদবাক্যের প্রভেদ কোথায় ? প্রভেদটা এখানে যে, লৌকিক বাক্যে লোকে খুশিমতো পদগুলির পরিপাটি রচনা করে, নতুন নতুন বাক্য রচনা করতে পারে, কিন্তু বৈদিক বাক্যের পদক্রম পরিবর্তন করার কোন স্বাধীনতা আমাদের নেই। কারণ কুমারিল বলছেন-
‘যত্নতঃ প্রতিষেধ্যা নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা’- ( শ্লোকবার্ত্তিক: শব্দনিত্যতা শ্লোক-২৯০)
অর্থাৎ : বৈদিক বাক্যের ক্রম অথবা ব্যবহার্য শব্দের ক্রমের কেউ যদি যথেচ্ছভাবে পরিবর্তন করতে, অর্থাৎ ওলটপালট করে পদ বা বর্ণগুলি সাজাতে চান আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করবো।
অতএব শবরস্বামী ও কুমারিলের এসব কথা মনে রাখলে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, বেদের নিত্যতা আসলে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহনিত্যতামাত্র। নিত্যবর্ণের মতো তা বেদবাক্য কূটস্থ নিত্য নয়। এবং বেদের কাল ও রচয়িতা নিরূপণ করা যায় না, তাই বেদ নিত্য অপৌরুষেয়।
.
অভিহিতান্বয় ও অন্বিতাভিধান :
শব্দপ্রমাণ বা বেদবাক্যের নিত্যতা সিদ্ধ করতে গিয়ে শব্দ, বর্ণ, পদ ও শব্দার্থ বিচারের পর মীমাংসকদেরকে বাক্যার্থের বিচারে উপনীত হতে হয়। ভাট্ট-মীমাংসামতে শব্দপ্রমাণ হলো বাক্যার্থজ্ঞান। একাধিক শব্দ বা পদ পরস্পর বাক্যার্থজ্ঞানে অন্বিত হয়ে যে সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে তাই বাক্যার্থ। শব্দার্থকে বলা হয় অভিধান। কোন শব্দের দ্বারা যে বস্তু বা ধারণাকে বোঝায় তা হলো ঐ শব্দের অভিধেয়। পদের এই অভিধার প্রকাশ এবং অন্বয় সম্পর্কে ভাট্ট ও প্রাভাকর সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শব্দের অর্থ কীভাবে প্রকাশিত হয় ? ভাট্টসম্মত শাব্দজ্ঞানের লক্ষণ দিতে গিয়ে নারায়ণ ভট্ট বলেছেন-
‘তত্র তাবৎ পদৈর্জ্ঞাতৈঃ পদার্থস্মরণে কৃতে।
অসন্নিকৃষ্টবাক্যার্থজ্ঞানং শাব্দমিতীর্যতে।’- (মানমেয়োদয়)
অর্থাৎ : প্রথমে পদগুলি জ্ঞানের বিষয় হয়। সেই পদগুলি জ্ঞাত হলে পদের অর্থের স্মরণ হয়। পদার্থের স্মরণের পর অসন্নিকৃষ্ট বাক্যার্থের যে জ্ঞান হয়, তাকেই শাব্দপ্রমা বলে।
শব্দপ্রমাণ হলো বাক্যার্থজ্ঞান। একাধিক পদ পরস্পর বাক্যার্থজ্ঞানে অন্বিত হয়ে যে সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে, তাই বাক্যার্থ। যে বাক্যের অর্থ পূর্বে জানা ছিলো না বা যে বাক্যার্থের বাধজ্ঞান থাকে না, সেরূপ বাক্যার্থকে অসন্নিকৃষ্ট বাক্যার্থ বলে, ঐরূপ বাক্যার্থজ্ঞানই শাব্দপ্রমা। যে বাক্যার্থ পূর্বে জ্ঞাত হয়েছিলো (সন্নিকৃষ্টার্থ) সেরূপ বাক্যার্থজ্ঞান অনুবাদস্বরূপ হওয়ায় তা আর প্রমা হয় না। আর যে বাক্যার্থের জ্ঞান বাধিত হয়, সেই বাক্যার্থজ্ঞান ভ্রমাত্মক হয় বলে তা প্রমা হয় না। এজন্য অসন্নিকৃষ্টার্থ বাক্যার্থজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে।
.
ভাট্টমতে শব্দার্থের জ্ঞান না হলে বাক্যার্থজ্ঞান হতে পারে না। বাক্য হচ্ছে- পদসমষ্টি। পদসমূহের অর্থজ্ঞান বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু, শুধু পদ বা বাক্য বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু নয়। আবার বাক্য না শুনেও অনেক সময় বাক্যার্থের জ্ঞান হতে পারে। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে কুমারিল বলেন-
‘পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং হ্রেষাশব্দজ্ঞ শৃণ্বতঃ।
খুরনিক্ষেপশব্দঞ্চ শ্বেতোহশ্বো ধাবতীতি ধীঃ।
দৃষ্টা বাক্যবিনির্ম্মুক্তা ন পদার্থৈর্বিনা ক্বচিৎ।।’- (শ্লোকবার্ত্তিক)
অর্থাৎ :
এক ব্যক্তি দূর থেকে শাদা রং-এর কোনও প্রাণী দেখে প্রাণীটিকে চিনতে পারলো না। তার শুধু শ্বেতগুণরূপ পদার্থের জ্ঞান হলো। এরপর সেইদিকেই হ্রেষাশব্দ শুনতে পেয়ে শ্বেতবর্ণ প্রাণীটিকে ঘোড়া বলে অনুমান করলো। পরে খুরনিক্ষেপের শব্দ শুনতে পেয়ে লোকটি বুঝলো- (ঘোড়াটি) দৌড়াচ্ছে। তখন লোকটি তিনটি পদার্থের সম্বন্ধকে অর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা গ্রহণ করে বুঝলো যে, শাদা ঘোড়াটি দৌড়াচ্ছে। এই জ্ঞানের মূলে কোন বাক্য না থাকলেও তা বাক্যার্থজ্ঞান।
.
অতএব, তাঁর মতে- বাক্য বা পদ বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু নয়, বরং পদার্থজ্ঞানই বাক্যার্থবোধের হেতু। পদসমূহ আপন আপন অর্থ বুঝিয়ে নিবৃত্ত হয়ে যায়। অন্য কিছু বুঝাতে তাদের সামর্থ্য থাকে না। তাই বলা হয়-
‘শব্দবুদ্ধিকর্ম্মাণাং বিরম্য ব্যাপারাভাবঃ।’
অর্থাৎ : শব্দ, বুদ্ধি এবং ক্রিয়া তাদের ব্যাপার অর্থাৎ কার্য একবার নিবৃত্ত হলে আর ব্যাপার হয় না।
.
আর তাই নিজের অর্থ বুঝিয়ে শব্দের অভিধার কার্য নিবৃত্ত হয়ে যায়। এজন্য তা আর বাক্যার্থের বোধক হতে পারে না। এ কারণেই পদ বা বাক্য বাক্যার্থের বাচক হতে পারে না। মীমাংসক কুমারিলের মতে- কি লৌকিক কি বৈদিক সকল পদই অন্য পদের অপেক্ষা না রেখেই একটি অর্থ প্রকাশ করে। সে অর্থ অভিধাবৃত্তি থেকে লাভ করা যায়, আর অভিধা থেকে পদের যে অর্থজ্ঞান হয় সেই জ্ঞানই অভিধান। এভাবে একাধিক পদ শুনলে প্রথমতঃ প্রত্যেক পদের অর্থের জ্ঞান হয়। পরে পদার্থগুলি (বিভিন্ন পদের অর্থগুলি) বিশেষ্য-বিশেষণভাবে পরস্পরের সাথে অন্বয় সম্বন্ধ হয়। পদের দ্বারা অভিহিত পদার্থগুলি পরে জ্ঞানের বিষয় হয়ে বাক্যার্থ জ্ঞান জন্মায়। বাক্যের প্রত্যেক পদের অর্থের সাথে অপর পদের অর্থের যে পারস্পরিক অন্বয় হয়, তার নামই অভিহিতান্বয়। পরস্পরের এই অন্বয় সম্ভব হয় বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবের দ্বারা। কুমারিলের এই মতবাদ অভিহিতান্বয়বাদ নামে পরিচিত।
.
মোটকথা, কুমারিলের অভিহিতান্বয়বাদ হলো- প্রত্যেকটি শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ পূর্বে নির্ধারণ করে পরে স্বতন্ত্র অর্থযুক্ত শব্দগুলি সাজিয়ে বাক্য রচনা করা হয়। স্বয়ং ভাষ্যকার শবরস্বামীর ঝোঁকও মনে হয় অভিহিতান্বয়বাদেরই পক্ষে। কেননা তিনি তাঁর শাবরভাষ্যে এ বিষয়ে বলেছেন-
‘নানপেক্ষ্যপদার্থন্ পার্থগর্থ্যনে বাক্যমর্থান্তর-প্রসিদ্ধম্ ।… পদানি হি স্বং স্বং পদার্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি। অথেদানীং পদার্থা অবগতাঃ সন্তো বাক্যার্থং গময়ন্তি।’- (শাবরভাষ্য-মীমাংসাসূত্র-১/১/২৫)।
অর্থাৎ :
স্বতন্ত্র অর্থযুক্ত পদগুলির পাস্পরিক অন্বয়েই বাক্যার্থের জ্ঞান জন্মায়, যার সাথে লৌকিক ও বৈদিক পদ এবং পদার্থের মধ্যে কোন ভেদ নেই।… শব্দের দ্বারা বাক্যরচনার পূর্বে স্বতন্ত্রভাবে ‘অভিহিত’ বা বোধিত অর্থগুলি ‘অন্বিত’ বা পরস্পরসম্বন্ধ হয়ে বাক্যার্থ সংঘটিত হয়। (মুক্ততর্জমা)
.
অন্যদিকে মীমাংসক প্রভাকর অভিহিতান্বয়বাদ সমর্থন করেন নি। তিনি অন্বিতাভিধানবাদী। তাঁর মতে, শব্দগুলি কোন-না-কোন বাক্যের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত বা সম্বন্ধ হয়েই নিজ নিজ অর্থ প্রকাশ করতে পারে, অসম্বন্ধ বা অনন্বিত অবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে কোন অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। অর্থাৎ, পদার্থের জ্ঞানের জন্য পদকে পদের ক্রিয়ার সঙ্গে আগে অন্বিত হতে হয়। অন্বিত শব্দেরই শক্তিগ্রহ হয়। প্রথমে পদসমূহের দ্বারা পদার্থসমূহের পৃথক পৃথক অন্বয় হয়। এভাবে পদার্থের (পদের অর্থের) জ্ঞান হয়। পদার্থের জ্ঞান তাই অন্বয়সাপেক্ষ।
.
গুরু প্রভাকর স্বীকৃত অন্বিতাভিধানবাদ মতে, ক্রিয়ার সাথে অন্বিত না হলে কোন পদেরই অর্থজ্ঞান হয় না। অন্বয়শক্তিও পদসমূহে অবস্থিত। ক্রিয়ার সাথে অন্বিত পদেরই অর্থজ্ঞান হয় বলে এই মতের নাম অন্বিতাভিধান। এই মতে একাধিক পদের দ্বারা পরস্পর নিরপেক্ষভাবে একাধিক পদার্থের জ্ঞান হতে পারে না। বিভক্ত্যন্ত একটি পদের অর্থের সাথে অন্বিত অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণরূপ সম্বন্ধে অন্য একটি পদার্থই অনুভবের বিষয়ীভূত হয়। দুটি পদের দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে দুটি পদার্থের অনুভব হয় না। পরস্পর অন্বিতের অভিধানকেই অন্বিতাভিধান বলা হয়েছে। প্রভাকর অন্বিতাভিধানকে বলেছেন- ‘ব্যতিষক্তার্থাভিধান’। ব্যতিষক্ত হলো- ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সম্বন্ধ শব্দার্থ। যাঁরা অন্বিতাভিধানের তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম, প্রভাকর তাদের বিদ্রূপ করে বলেছেন-
‘পদপদার্থনভিজ্ঞো মাতৃপ্রিয়ো ভবান্ ।’- (বৃহতী-মীমাংসাসূত্র-১/১/২৫)
অর্থাৎ : মাতৃস্নেহের অতিরিক্ত আকর্ষণে আপনি বেশিদিন গুরুগৃহে থেকে বিদ্যাভ্যাস করতে পারেন নি, তাই পদ ও পদার্থের তত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ রয়ে গেছেন।
.
প্রাভাকর-মতাবলম্বীরা তাঁদের এই অন্বিতাভিধান সিদ্ধান্তের সমর্থনে শব্দার্থবিষয়ে অজ্ঞ শিশুর প্রাথমিক শব্দার্থবোধের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন (সূত্র: সুখময় ভট্টাচার্য্য, পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন, পৃষ্ঠা-৩২)-
‘শব্দবৃদ্ধাভিধেয়াংশ্চ প্রত্যক্ষেণাত্র পশ্যতি।
শ্রোতুশ্চ প্রতিপন্নত্বমনুমানেন চেষ্টয়া।।
অন্যথানুপপত্ত্যা তু বোধেচ্ছক্তিদ্বয়াত্মিকাম্ ।
অর্থাপত্ত্যাবুধ্যেত সম্বন্ধং ত্রিপ্রমাণকম্ ।।’
অর্থাৎ :
কোন ব্যক্তি তাঁর ভৃত্যকে আদেশ করলেন- ‘গরুটি আন’। এখানে শব্দার্থ বিষয়ে যার জ্ঞান নেই, সেই নিকটস্থ শিশু বাক্যটি শুনলো এবং আদেষ্টা ও আদিষ্ট ব্যক্তিকে দেখলো। সে গরুর আনয়নরূপ কর্মটিও প্রত্যক্ষ করলো। এই বাক্যটি শুনেই যে আদিষ্ট ব্যক্তি আদেষ্টার অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছে, তাও শিশুটি আদিষ্ট কর্তৃক গরুটি আনয়নরূপ শারীরিক চেষ্টা দেখে অনুমান করলো। আদেষ্টার বাক্যের সাথে গরুর আনয়নরূপ কর্মের যে বাচ্যবাচকত্ব সম্বন্ধ রয়েছে, তাও শিশুটি অর্থাপত্তি-প্রমাণের দ্বারা বুঝতে পারলো। (যেহেতু এই বাক্যের বাচকতা না থাকলে আদিষ্ট কর্তৃক গরুটি আনয়নরূপ অর্থের জ্ঞান হতো না।) পরে এই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও অর্থাপত্তি প্রমাণের বলে এবং গরুশব্দসত্ত্বে এই প্রাণীর সত্তা এবং আনয়নশব্দসত্ত্বে সমীপীকরণের সত্তা প্রভৃতি অন্বয়ব্যতিরেকবলে শব্দগুলির সঙ্কেত বা শক্তি শিশুটি জানতে পারলো।
.
এতে বোঝা যাচ্ছে, অন্বিত পদার্থের দ্বারাই প্রাথমিক শব্দার্থজ্ঞান হয়ে থাকে। একটি পদের অর্থমাত্রের দ্বারা লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না। বাক্যস্থিত পদসমূহের অর্থ সর্বদাই অপর পদার্থে অন্বিত। কিন্তু অভিহিতান্বয়বাদী ভাট্ট-মীমাংসকরা, এবং সাধারণভাবে আমাদেরও মনে হয় যে, শিশুকাল থেকে আমরা এক একটি বিচ্ছিন্ন শব্দের ‘বিশুদ্ধ’ বিচ্ছিন্ন অর্থ শিখি (যেমন একে গাছ বলে, একে ফুল বলে ইত্যাদি), তারপর এগুলি মিশিয়ে বাক্যরচনা শিখি। দু-চারটি শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ এভাবে শিশু শেখে বটে। কিন্তু শিশুকাল থেকে আমরা যে শত শত শব্দের শত শত অর্থ শিখি তার কটা এভাবে শেখানো সম্ভব ? অথচ আমাদের অজান্তে শিশু যে কয়েক ডজন শব্দ কখোন ব্যবহার করতে শিখলো, তা ভেবে আমরা অবাক হয়ে যাই। অথচ শিশু কিন্তু এসব শিখে পরিবার-পরিজনের কথাবার্তা শুনে, বিশেষত বড়োদের বাক্যাকারে কথাবার্তার সঙ্গে কোনো-না-কোনো কাজের যোগাযোগ লক্ষ্য করে। প্রভাকরপন্থী মীমাংসকরা এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন প্রাচীন লোকায়ত কৃষিসমাজের উপযোগী কোন প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের দ্যোতক কার্যকলাপ থেকে।-
‘ধরুন বাবা বড়ো ছেলেকে বলল- ‘গাম্ আনয়’ (গরুটাকে নিয়ে এস)। পাশের ছোটো খোকা দেখল বাক্যটি বলার সঙ্গে সঙ্গে দাদা একটা শিংওয়ালা চারপেয়ে প্রাণী নিয়ে এল। শিশু সম্পূর্ণ বাক্যটির একটা সম্পূর্ণ কাজের সঙ্গে সম্পর্ক আন্দাজ করল। বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির পৃথক অর্থ এখনও সে বোঝেনি, অর্থাৎ ‘গাম্’ মানে ‘গরুটাকে’ এবং ‘আনয়’ মানে ‘নিয়ে এস’ এরকম ধারণা তার এখনও হল না। এখন ধরুন বাবা বলল- ‘গাম্ বধান’ (গরুটাকে বেঁধে রাখ), ‘অশ্বম্ আনয়’ (ঘোড়াটাকে নিয়ে এস)। বড়ো ছেলে বাবার আদেশ পালন করল। কয়েকবার এরকম কথা ও কাজের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে শিশু লক্ষ করল বাক্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দাদার কাজের পরিবর্তন ঘটছে, আরও লক্ষ করল, প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে ‘গাম্’ শব্দটি একই থাকছে, কিন্তু ‘আনয়’-এর স্থানে ‘বধান’ এসে যাচ্ছে, একই বস্তুর (প্রাণীর) সম্বন্ধে দুরকম কাজ হচ্ছে। আবার তৃতীয় বাক্যটিতে ‘গাম্’-এর স্থানে ‘অশ্বম্’ এসে যাচ্ছে, দ্বিতীয় বাক্যের ‘বধান’ চলে যাচ্ছে, তার জায়গায় প্রথম বাক্যের ‘আনয়’ আবার ফিরে আসছে, তৃতীয় কাজটা প্রথম কাজের অনুরূপ হচ্ছে। এভাবে বাক্যের অন্তর্গত শব্দের যোগবিয়োগ (আবাপ-উদ্বাপ) এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কাজের পরিবর্তন বার বার লক্ষ করে পাশের শিশুটি ‘গাম্, অশ্বম্, আনয়, বধান’ প্রভৃতি পদের পৃথক অর্থ বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লিষ্ট করে একরকম আন্দাজ করে নিল, পরে নিজেও অনুরূপ পরিস্থিতিতে অনুরূপ বাক্য ব্যবহার করতে শিখল- ‘দাদা, গোরুটাকে নিয়ে এস, গোরুটাকে বেঁধে রাখ, ঘোড়াটাকে নিয়ে এস।’ বলা বাহুল্য, শিশুর এই বিশ্লেষণী বুদ্ধি ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করে হয়নি। শিশুর এটা ‘স্বভাব ন্যায়’ বা instructive logic। কিন্তু শাস্ত্রকাররা শিশুর এ জাতীয় বুদ্ধিবিকাশ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন ভাষা প্রয়োগ করেন যাতে মনে হতে পারে শিশুও বোধ হয় বড়োদের মতো ‘অনুমান’ করছে, যেন সচেতনভাবে ন্যায়বুদ্ধির প্রয়োগ করছে।’- (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন, পৃষ্ঠা-১৩০)।
.
এখানে আরেকটা বিষয়ও লক্ষ্য করতে হয়, শিশু যখন এরূপ ‘বৃদ্ধব্যবহার’ শোনে বা দেখে, তখন কিন্তু বাক্যবিযুক্ত বা শব্দান্তরের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি ‘বিশুদ্ধ’ ‘গো’-শব্দ এবং তার অর্থরূপে অন্য বস্তু বা ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য একটি বিশুদ্ধ ‘গরু’, যে গরু শোয় না, বসে না, হাঁটে না, দৌড়ায় না, খায় না, যে গরু কেবল নিছক গরু মাত্র, এমন একটি নিঃসঙ্গ গোশব্দ এবং নিঃসঙ্গ গো-পদার্থ শিশু কিন্তু কোথাও খুঁজে পায় না। বরং শিশুর মনে স্বাভাবিকভাবে এ ধারণাই জন্মে যে কোনো শব্দ অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েই আত্মপ্রকাশ করে এবং শব্দার্থও অন্য কোনো শব্দার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রকাশিত হয়- এক কথায়, পরস্পরসম্বন্ধ শব্দ পরস্পরসম্বন্ধ অর্থ প্রকাশ করে। জগতের বস্তুসমূহ পরস্পর-সম্বন্ধ বলেই মানুষের ভাষাতেও শব্দগুলি পরস্পরসম্বন্ধভাবে বাক্যাকারে উচ্চারিত হয়। এখনকার শিশুরাও এভাবেই শেষে। পরিবার পরিজনের মধ্যে শিশু অনবরত কথার সঙ্গে কজের সম্বন্ধ লক্ষ্য করে, শব্দ-পরিবর্তনের আনুষঙ্গিকরূপে কার্যপরিবর্তন লক্ষ্য করে। এভাবে কার্যান্বিতরূপে শব্দার্থের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে।
.
এই লোকব্যবহারের সাথে অন্বিতাভিধানবাদী প্রভাকর-মতের সংগতি পরিলক্ষিত হয়। লোকব্যবহারে কোন শব্দার্থ যেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয় না, অন্য কোন শব্দার্থের সঙ্গে অন্বিত রূপেই প্রতিভাসিত হয়, সেহেতু পরস্পরসম্বন্ধ শব্দার্থসমূহই বাক্য, তৎ-অতিরিক্ত বাক্য বলে কিছু নেই। এ পর্যায়ে এসে যে অনিবার্য প্রশ্নটি সামনে চলে আসে তা হলো, ভাষার ব্যাকরণশাস্ত্রের নিয়মগুলি তাহলে কোন প্রক্রিয়া মেনে চলে ? ব্যাকরণের নিয়মে অর্থবহ শব্দ বলতে কী বোঝায় তার বিচারও আবশ্যক মনে হয়।
.
অর্থবহ শব্দ কী ? ভর্ত্তৃহরির মত :
প্রচলিত ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব পড়ে স্বাভাবিকভাবেই একটা ধারণা জন্মে যে, বর্ণগুলি যোগ করে শব্দগুলি তৈরি হয়েছে, যেমন- আম = আ + ম্ + অ, কিংবা বক = ব্ + অ + ক্ + অ, ইত্যাদি। কিন্তু-
‘এ ধারণা ভ্রান্ত। শব্দের মূল যদি বর্ণ হয়, বর্ণ থেকেই যদি অর্থবহ শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকে, তাহলে এর তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে- মানুষের ভাষার এমন একটা আদিম অবস্থা ছিল যখন মানুষ জাগতিক বস্তু বোঝাবার জন্য বা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য শুধু অ, আ, ক, খ জাতীয় পৃথক পৃথক বর্ণগুলিই ব্যবহার করত, এই বর্ণগুলির প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র অর্থ ছিল এবং কালক্রমে এই বর্ণগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে বিভিন্ন অর্থবহ শব্দ সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ অর্থবহ শব্দের আদিমতম রূপ হল এক একটি স্বতন্ত্র বর্ণ। যে কোন ভাষার শব্দসম্পদের তুলনায় বর্ণসম্পদ অতি সীমিত। তাহলে আদিম মানুষকে একটি বর্ণের দ্বারা অসংখ্য বস্তু বুঝতে ও বোঝাতে হত। কিন্তু ভাষার আদিমতম ইতিহাসে অর্থবহ শব্দরূপে কেবল এক একটি স্বতন্ত্র বর্ণমাত্র ব্যবহার করা হত, সমগ্র একটি শব্দের ব্যবহার হত না, এহেন বিচিত্র কল্পনা খুবই কষ্টকর।’- (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়/ বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন, পৃষ্ঠা-১২৩)।
.
দার্শনিক জগতের পরম বিস্ময় ‘বাক্যপদীয়’ গ্রন্থের প্রণেতা ব্যাকরণ দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক প্রবক্তা মহাবৈয়াকরণ ভর্ত্তৃহরি বলেন যে, মানুষ চিরদিন অর্থ বোঝাতে একটা গোটা শব্দই ব্যবহার করতো, শব্দ থেকে বিশ্লিষ্টরূপে এক একটা বর্ণমাত্র ব্যবহার করতো না। এই মতকে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকরাও স্বীকার করেন। তাহলে এর তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে, মানুষের ব্যবহারসিদ্ধ শব্দরূপের উপস্থিতির পূর্বে শব্দের অবয়বরূপে পরিকল্পিত বর্ণগুলির কোনদিন বাস্তব উপস্থিতি ছিলো না। অর্থাৎ প্রাকসিদ্ধ স্বতন্ত্র বর্ণগুলির যোগ-বিয়োগ বা ক্রম পরিবর্তন করে ব্যবহারযোগ্য অর্থবোধক শব্দরাশি সৃষ্টি করা হয়নি। কাজেই আম = আ + ম্ + অ নয়, কিংবা বক = ব্ + অ + ক্ + অ নয়। তার মানে, পরবর্তীকালে ভাষাতাত্ত্বিক বৈয়াকরণ ও শিক্ষাকারগণ ভাষায় ব্যবহৃত মূল শব্দ থেকে বিশ্লেষণী বুদ্ধির দ্বারা বর্ণগুলিকে পৃথক করে বোঝার চেষ্টা করেছেন- এভাবে এক একটি ভাষার ‘বর্ণমালা’ সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং শব্দ থেকেই বর্নের উৎপত্তি হয়েছে। বর্ণ থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়নি। অর্থ বোঝাবার জন্য মানুষ যদি চিরকাল ধরে একটা সমগ্র শব্দই ব্যবহার করে এসে থাকে, কোনদিন স্বতন্ত্রভাবে পৃথক পৃথক এক একটি বর্ণ ব্যবহার না-করে থাকে, তাহলে ভর্ত্তৃহরির এ সিদ্ধান্ত মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে- ‘শব্দ অখণ্ড’। তাই শব্দ একটি পূর্ণরূপ যার বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের দ্বারা বৈয়াকরণ ও শিক্ষাকারগণ অংশাকারে বর্ণগুলি কল্পনা করেছে। পূর্ণই বাস্তব, পূর্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন অংশ বুদ্ধি-পরিকল্পিত।
.
‘বৌদ্ধ বিশ্লেষণের দ্বারা সমগ্র থেকে অংশকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে কল্পনা করাকে ভর্ত্তৃহরি বলেছেন ‘অপোদ্ধার’। ভর্ত্তৃহরির অপোদ্ধার-তত্ত্ব ব্যাকরণ দর্শনের একটি মূল স্তম্ভ। ভর্ত্তৃহরি বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে ঘুরেফিরে বারবার এই তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন। যে সমগ্র শব্দরূপের বৌদ্ধবিশ্লেষণের দ্বারা আমরা কাল্পনিক অংশে উপনীত হই ভর্ত্তৃহরি সেই সমগ্রকে বলেছেন ‘অন্বাখ্যেয়’ শব্দ (অনু-আখ্যেয় = পরে যাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাগ করে ব্যাখ্যা করা হয়)। ভর্ত্তৃহরি অপোদ্ধার তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে অন্বাখ্যেয় শব্দের উদাহরণ দিয়েছেন- ‘ভবতি’। আমরা শিখে এসেছি ভূ ধাতুর সঙ্গে তি (তিপ্) প্রত্যয় (তিঙ্ বিভক্তি) যোগ করে ‘ভবতি’ ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে। তি বিভক্তির অব্যবহিত পূর্বে একটি অতিরিক্ত ‘অ’-কার এসেছে। ভূধাতুর দীর্ঘ ‘ঊ’টি ‘ও’-কারে পরিণত হয়েছে। ‘ও’-কারটির ‘অব্’ এ পরিণত হয়েছে। এত কান্ডের পর ‘ভূ’ ও ‘তি’ মিলে ‘ভবতি’ হয়েছে। (ভূ-তি > ভূ-অ-তি > ভো-অ-তি > ভ্-অব্-অ-তি > ভবতি)। বাস্তবে এ জাতীয় কোনোকিছুই ঘটেনি। কারণ, সংস্কৃত ভাষাভাষী আদিপুরুষরাও প্রথম থেকে ‘ভবতি’ পদটিই বলে এসেছে। মানুষ যা বলে তাই তো ভাষা। ভাষায় কোনোদিন শুধু ‘ভূ’ বা শুধু ‘তি’ বলে কিছু ছিল না। কাজেই ওদের প্রথম মিলন বলে কোনোকিছু ঘটেনি, ওরা চিরদিন মিলিতই ছিল। কেবল ‘ভূ’ বা কেবল ‘তি’ এর কোনো অর্থ নেই। ‘ভূ’ মানে হওয়া, আর ‘তি’ মানে কর্তৃকারক একবচন ও প্রথম পুরুষ, এসব কথা বৈয়াকরণের বৈঠকখানায় পরিশীলিত বিশ্লেষণী বুদ্ধির বস্তুহীন নিপুণ কল্পনা।’- (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়/ বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন, পৃষ্ঠা-১২৫)।
.
এ প্রসঙ্গে অর্থবোধকতা সম্পর্কে স্বয়ং কুমারিলের একটি সর্ববাদীসম্মত বিখ্যাত সাধারণ নীতিবাক্য রয়েছে-
‘প্রকৃতিপ্রত্যয়ৌ সহার্থং ব্রূতঃ।’
অর্থাৎ : প্রকৃতি এবং প্রত্যয় মিলিতভাবে অর্থ প্রকাশ করে, স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করে না।
.
এ প্রেক্ষিতে হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন যে, এরই অনুষঙ্গ হিসেবে আরেকটি নীতিও এসে যায়, তা হলো- শুধু প্রকৃতি বা শুধু প্রত্যয় ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। শব্দ ও শব্দার্থের নিরিখ হলো ভাষাগত সামাজিক ব্যবহার। তাহলে মেনে নেয়া হচ্ছে- মানুষের ভাষায় ‘ভূ’ এবং ‘তি’ কোনোদিন পৃথক সত্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়নি, পৃথক অর্থও কোনোদিন প্রকাশ করেনি। তাহলে এটাও মেনে নিতে হচ্ছে- ‘ভূ’ এবং ‘তি’ জোড়া লেগে ‘ভবতি’-রূপে পরিণত হওয়ার মতো কোনো ঘটনা ভাষার ইতিহাসে কোনোদিন ঘটেনি, মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন পৃথক অর্থও এদের কোনোদিন ছিলো না। সুতরাং ‘ভবতি’ এই সমগ্র রূপটি এবং এর সমগ্র অর্থটি ব্যবহারসিদ্ধ অখন্ড সামাজিক সত্য। তাই মহাবৈয়াকরণ ভর্তৃহরি তাঁর বাক্যপদীয় গ্রন্থে বলেন-
‘অপোদ্ধারপদার্থা যে যে চার্থঃ স্থিতলক্ষণাঃ।
অন্বাখ্যেয়াশ্চ যে শব্দা যে চাপি প্রতিপাদকাঃ।।’- (বাক্যপদীয়-১/২৪)
অর্থাৎ :
অকল্পিত সমগ্র শব্দরূপটি হলো ‘অন্বাখ্যেয়’; শাস্ত্রকারদের দ্বারা কল্পিত খণ্ডিত শব্দাংশ হলো ‘প্রতিপাদক’। সমগ্র শব্দের সমগ্র অর্থ হলো ‘স্থিতলক্ষণ’ (বস্তুত যা অবিভক্ত রূপে স্থিত, স্বরূপ থেকে অপ্রচ্যুত, লোকব্যবহারসিদ্ধ); কল্পিত খণ্ডিত অর্থাংশ হলো ‘অপোদ্ধার’।
.
অপোদ্ধার শব্দের সাধারণ অর্থ কল্পিত বিভাগ। সমগ্র থেকে কল্পনায় খণ্ডিত করে যে অংশকে বের করে দেখানো হয় তাকেও অপোদ্ধার বলে; এখানে অপোদ্ধার মানে অপোদ্ধৃত। বস্তুত শব্দাংশ ও অর্থাংশ উভয়ই অপোদ্ধৃত। তাই ভর্ত্তৃহরির মতে ‘ভবতি’ হলো শব্দের ব্যবহারানুগত বাস্তব রূপ (অন্বাখ্যেয়)। ভূ-তি প্রভৃতি খন্ডিত রূপ হলো কল্পিত, ‘প্রতিপাদক’। তেমনি ‘ভবতি’ শব্দের সামগ্রিক অর্থটিই সত্য (স্থিতলক্ষণ)। ‘ভূ’-ধাতু মানে ‘হওয়া’, তি মানে ‘কর্তৃবাচ্যে প্রথম পুরুষ একবচন’ এরূপ বিভক্ত অর্থ অসত্য, কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় প্রয়োজনে শাস্ত্রকারদের দ্বারা পরিকল্পিত (অপোদ্ধার)। তাই ভর্ত্তৃহরির স্পষ্ট ঘোষণা-
‘শাস্ত্রেষু প্রক্রিয়াভেদৈরবিদ্যৈবোপবর্ণ্যতে।
অনাগমবিকল্পৌ তু স্বয়ং বিদ্যোপবর্ততে।।’- (বাক্যপদীয়-২/২৩৩)
‘উপায়াঃ শিক্ষমাণানাং বালানামপলাপনাঃ।
অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃসত্যং সমীহতে।।’- (বাক্যপদীয়-২/২৩৮)
‘তথা পূর্বপদার্থ উত্তরপদার্থোৎ্যন্যপদার্থঃ প্রতিপাদিকার্থো ধাত্বর্থঃ প্রত্যয়ার্থ ইত্যেক-পদবাচ্যোৎ্যপ্যনিয়ত অবর্ধিহুধা প্রবিভজ্য কৈশ্চিত্ কথঞ্চিদ্ অপোদ্ধ্রিয়তে।’- (বাক্যপদীয়-১/২৪-ভর্তৃহরির নিজস্ব ব্যাখ্যা)
সারার্থ :
ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রক্রিয়াগুলি অসত্য কাল্পনিক। পূর্বপদ, উত্তরপদ, প্রতিপদিক, ধাতু, প্রত্যয় এবং এদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক অর্থ- এ জাতীয় বহুপ্রকার বিভাগগুলি অসত্য, শাস্ত্রকারদের বিকল্পবুদ্ধিপ্রসূত অপোদ্ধার মাত্র। এজাতীয় বিভাগপ্রক্রিয়ার প্রদর্শন এব ধরনের প্রতারণা। তবু এ-জাতীয় মিথ্যা উপায়ের মাধ্যমেই ভাষাশিক্ষার্থী বালক উপেয় সত্যে উপনীত হয়।- (তর্জমা : হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-১২৭)
.
অসত্য কাল্পনিক উপায়ে সত্যে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হলো গাণিতিক চিহ্ন ও গানের স্বরলিপি। ১ ২ ৩ প্রভৃতি রেখাচিহ্নগুলি সংখ্যা নয়, সংখ্যার সঙ্গে চিহ্নগুলির সম্পর্ক অবাস্তব ও কাল্পনিক। কিন্তু ঐ রেখাচিহ্নগুলি ব্যবহার করে আমরা গণিত শিখে থাকি। গানের স্বরলিপি যেমন স্বর নয়, সুর নয়, তাল নয়; কিছু কাল্পনিক চিহ্নমাত্র। তবু ওগুলির মাধ্যমে গানের শুদ্ধ ধারণা জন্মে। তেমনি কোন ভাষা সম্পর্কে ধারণা করার জন্য বর্ণমালা, প্রকৃতি, প্রত্যয় প্রভৃতি কাল্পনিক বিভাগের সাহায্য নিতে হয়। ব্যাকরণ শাস্ত্র এই সাহায্যটুকু করে থাকে।
.
ভর্ত্তৃহরি কেবলমাত্র পদ ও পদার্থের অখণ্ডতার মধ্যেই তাঁর দার্শনিক সিদ্ধান্ত সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তিনি আরও অগ্রসর হয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন- বাক্য ও বাক্যার্থের অখণ্ডতা। এ সিদ্ধান্তেরও প্রধান ভিত্তি হলো সামাজিক ব্যবহার। ভাষা মানুষের সামাজিক আত্মপ্রকাশ, যেখানে ব্যক্তির সামাজিক সত্তা সমাজের কাছে প্রকাশিত হয়, প্রমাণিত হয়। সমাজ-মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন নিছক বিশুদ্ধ ব্যক্তিসত্তা কোনদিন ছিলো না, আজও নেই। অনুরূপভাবে শব্দেরও একটা ‘সমাজ’ আছে। মানুষের পারিবারিক সমাজের মতো শব্দের প্রাথমিক সমাজ হলো বাক্য। বাক্যের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া কোন শব্দের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। বাক্যার্থের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া স্বতন্ত্র অর্থও নেই। কারণ, মানুষের ভাষাগত সামাজিক ব্যবহার বাক্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়, স্বতন্ত্র শব্দের দ্বারা নয়। তাই বাক্যসত্তার অতিরিক্ত শব্দসত্তা নেই। একথাই ভর্ত্তৃহরি একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন-
‘পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে, বর্ণেষ্ববয়বা ন চ।
বাক্যাত্ পদানামত্যন্তং প্রধিবেকো ন কশ্চন।।’- (বাক্যপদীয়-১/৭৩)
অর্থাৎ : পদের মধ্যে কোন (পৃথক) বর্ণ নেই; বর্ণের কোন অবয়ব (অংশ) নেই; বাক্য থেকে পদগুলির কোন ঐকান্তিক ভেদ নেই।
.
বাক্যের মতো বাক্যার্থও অখণ্ড। বাক্যার্থের অন্তর্গত পদার্থসমূহকে ভর্ত্তৃহরি বলেছেন ‘অত্যন্তসংসৃষ্ট’ (পরস্পর সর্বদাই অবিভক্ত)। লোকব্যবহারের দিকে সূক্ষ্ম বস্তুদৃষ্টি নিবদ্ধ করেই বাক্যার্থের মৌলিক চরিত্র চিহ্নিত করতে গিয়ে ভর্ত্তৃহরি যে অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটি করেন, তা হলো-
‘বিশিষ্ট একঃ ক্রিয়াত্মা।’- (স্বোপজ্ঞ বৃত্তি, বাক্যপদীয়-১/২৬)
অর্থাৎ : ক্রিয়াই হলো বাক্যার্থের আত্মা। ক্রিয়াই বাক্যার্থের ঐক্য ও বৈশিষ্ট্যের ধারক।
.
সবদিক মিলিয়ে বিচার করলে মনে হয়, মীমাংসকদের বাক্যার্থসম্পর্কিত আলোচনার ন্যায়সংগত পরিণতি ঘটা উচিত ছিলো বৈয়াকরণসম্মত অখণ্ড বাক্যার্থবাদে। কিন্তু-
‘ভর্তৃহরির মত অনুসরণ করে একথা বোধ হয় বলা যায় যে- বর্ণসমষ্টিকে পদ বলে এবং পদসমষ্টিকে বাক্য বলে- এই মীমাংসক মত মূলত ভ্রান্ত, যদিও এজাতীয় কল্পনা দ্বারা ভাষা শেখার কাজটা চলে যায়, কারণ ব্যাকরণ-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি কাল্পনিক হলেও অসত্য কল্পনার দ্বারা আমরা অনেক সময় সত্যে উপনীত হই। মীমাংসকদের পক্ষে বেদের প্রামাণ্যসিদ্ধির জন্য অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে; আবার অপৌরুষেয়-নিত্যত্ব সিদ্ধির জন্য বর্ণের নিত্যতা প্রমাণ করতে হয়েছে। কিন্তু শুধু বর্ণ-নিত্যতার দ্বারা বেদ-নিত্যতা প্রমাণিত হয় না, এজন্য পদ (শব্দ) ও বাক্যের নিত্যতা সাধন করা প্রয়োজন। তাই ক্রমসন্নিবিষ্ট বর্ণসমষ্টি ছাড়া অতিরিক্ত কোন পদ নেই, এ সিদ্ধান্ত বহাল রেখেও শব্দের ব্যবহারিক বা প্রবাহনিত্যতা স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বেলা প্রবাহনিত্যতাও স্বীকার করা দুরূহ, কারণ বাক্যের ক্রম-ব্যতিক্রম ও আগম-নিগমের (আবাগ-উদ্বাগ) দ্বারা নতুন নতুন বাক্য রচনা করা সম্ভব। অগত্যা তাই মীমাংসককে কেবল বেদবাক্যের প্রবাহনিত্যতা স্বীকার করতে হয়েছে। বেদ বাক্যগুলি স্মরণাতীত কাল থেকে অবিকৃত রয়ে গেছে। বেদবাক্যের কোনো কর্তা বা রচনাকাল স্মরণ করা যায় না। তাই বেদ অপৌরুষেয় বলেই অভ্রান্ত। মানুষের দ্বারা তৈরি হলেই তো ভ্রান্তির সম্ভাবনা। যে বাক্যরাশি কোনো মানুষ রচনা করেনি অথচ চিরকাল ধরে আছে তাতে আর ভ্রান্তির সম্ভাবনা আসবে কোথা থেকে।’- (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়/ বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন, পৃষ্ঠা-১২৯)।
প্রমেয় পদার্থ
মীমাংসা-শাস্ত্রে যজ্ঞকর্মকেই যজ্ঞফলের অদ্বিতীয় কারণ বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু যজ্ঞকর্ম যেহেতু ক্ষণিক এবং এর ফল ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয় না, তাই প্রশ্ন আসে, যজ্ঞক্রিয়াকে কীভাবে ফল-উৎপাদক বলা যায় ? যেমন, বেদের বিধিতে বলা হয়- ‘দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত’- অর্থাৎ, স্বর্গকামী ব্যক্তি দর্শপূর্ণমাস নামের যজ্ঞ করবেন। এই স্বর্গফল প্রাপ্তি কীভাবে সম্ভব হতে পারে ? যজ্ঞের এই ফল-উৎপাদক শক্তিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মীমাংসকরা ‘অপূর্ব’ নামের একটি অদৃষ্ট-শক্তির ধারণা আনয়ন করেন। এই ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, যজ্ঞক্রিয়া বিনষ্ট হলেও তার মাধ্যমে সৃষ্ট অপূর্ব-শক্তিটি কার্যকরি থাকে এবং এই শক্তিই শেষ পর্যন্ত ফল সৃষ্টি করে। বেদ যেহেতু ভ্রান্ত হতে পারে না, এবং বেদ অনুসারে যাগ থেকে স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন হয় উল্লেখ আছে, অতএব মানতেই হবে যাগ এবং স্বর্গাদি-ফল উভয়ের মধ্যে শক্তিবিশেষ উৎপন্ন হয়।
যেহেতু মীমাংসকরা কোনো লোকোত্তর ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন, তাই যজ্ঞকর্ম থেকে উৎপন্ন কাষ্ঠলোষ্ট্রের সমান অচেতন অপূর্ব থেকে ফলপ্রাপ্তি জাতীয় কথা আসলে আদিম জাদুবিশ্বাসের দার্শনিক সমর্থন বলা যায়। এখন প্রশ্ন হলো মীমাংসা-মতে স্বর্গ বলতে কী বোঝায় ?
.
স্বর্গ :
স্বর্গ এবং নরক সম্বন্ধে বহুবিধ মতবাদ প্রচলিত। স্বর্গের লোভ এবং নরকের ভীতি প্রায় প্রত্যেকের অন্তরেই বিদ্যমান। স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই হিন্দুগণ অধিকাংশ কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করে থাকে। মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি কর্মের উদ্দেশ্যও মৃতের আত্মার স্বর্গপ্রাপ্তি। আমাদের কল্পনায় স্বর্গ পরম ঈপ্সিত এবং নরক অত্যন্ত হেয় ও ভীতিপ্রদ। মুক্তিকাম ব্যক্তি ব্যতীত সকলের নিকটই স্বর্গ পরম কাম্য।
.
মীমাংসাদর্শনে বলা হয়- যে-সব যাগের ফল বেদে কীর্তিত হয়নি, সেসব যাগের একটিমাত্র ফল কল্পনা করতে হবে। সেই ফলটি কী ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি জৈমিনি বলছেন-
‘স স্বর্গঃ স্যাৎ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ।’- (মীমাংসাসূত্র-৪/৩/১৫)
অর্থাৎ : সেই ফলটি হচ্ছে স্বর্গ; যেহেতু তা সকলের নিকট অবিশেষে ঈপ্সিত।
.
মীমাংসামতে স্বর্গ মানে সুখ বা প্রীতি হলেও মীমাংসকদের সিদ্ধান্ত খুব স্পষ্ট নয়। তবু শব্দটির নানবিধ অর্থ পাওয়া যায়। প্রাচীন আচার্য্যরা বলেন (সূত্র: সুখময় ভট্টাচার্য্য, পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন)-
‘যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্ ।
অভিলাষোপনীতং যৎ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্ ।।’
অর্থাৎ : যাতে দুঃখের লেশমাত্র নেই, উৎপত্তির পরক্ষণেই যার ধ্বংস হয় না এবং ইচ্ছামাত্রই যা উপস্থিত হয়, সেই সুখকে স্বর্গ বলে।
.
অভিধান থেকে জানা যায়- স্বঃ, অব্যয়, স্বর্গ, নাক, ত্রিদিব, ত্রিদশালয় প্রভৃতি শব্দ একার্থক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্থান বা লোকবিশেষকেই স্বর্গ বলা হয়েছে, যেমন-
‘তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকঃ বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে।। (গীতা-৯/২১)
অর্থাৎ : তাঁরা সেই বিপুল স্বর্গলোক উপভোগ করে পুণ্যক্ষয় (ভোগের দ্বারা পাপের ফল দুঃখ ও পুণ্যের ফল সুখ ক্ষয় হয়।) হলে মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। এভাবে ত্রিবেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করে ভোগকামী ব্যক্তিগণ সংসারে যাতায়াত করেন।
.
শাস্ত্রে চতুর্দশ লোক বা ভুবনের বর্ণনা থেকেও জানা যায়- ভূর্লোকের উর্ধ্বে ভুবর্লোক এবং ভুবর্লোকের উর্ধ্বে স্বর্গলোকের অবস্থিতি। বেদমন্ত্রে, ছান্দোগ্যাদি উপনিষদে এবং ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতিতেও দেবলোক বা স্বর্গলোকের কথা বহুভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবার আচার্য সুরেশ্বর দেবলোকের দিব্যদেহ ব্যতীত নিরতিশয় স্বর্গসুখ ভোগ করা যায় না বলে বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে উল্লেখ করেছেন-
‘কাম্যেহপি শুদ্ধিরস্ত্যেব ভোগসিদ্ধ্যর্থমেব সা।
বিড়বরাহাদিদেহেন ন হ্যৈন্দ্রং ভুজ্যতে ফলম্ ।।’- (সম্বন্ধবার্ত্তিক)
অর্থাৎ : নিত্যকর্মের ন্যায় কাম্যকর্মেরও ফলভোগের নিমিত্তই চিত্তশুদ্ধি ও দেহশুদ্ধি আবশ্যক। শূকরাদির দেহে স্বর্গাদি ফল ভোগ করা যায় না। অর্থাৎ দিব্য ভোগের নিমিত্ত দিব্যদেহও আবশ্যক। কাম্যকর্মের ফলে দিব্য ভোগোপযোগী দিব্যদেহও লাভ হয়।
.
একইভাবে এই দেহে নরকভোগও সম্ভবপর হয় না বলে পাপীকে যাতনা সহ্য করবার উপযোগী কদর্য্য দেহও ধারণ করতে হয়। স্বর্গের বিপরীতে নরকের কল্পনা বা উল্লেখও বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে-
‘অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রষক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ।।- (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-১৬/১৬)
অর্থাৎ : অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ অবিবেকমুগ্ধ হয় এবং বহু সংকল্পে বিক্ষিপ্তচিত্ত, মোহজালে জড়িত ও বিষয়ভোগে আসক্ত হয়ে বিন্মুত্রাদিময় রৌরবাদি নরকে পতিত হয়।
.
গীতার বচনে ‘পতন্তি’ পদ থেকে বোঝা যায় নরক ভূর্লোকের অধোভাগে অবস্থিত, আর ‘অশুচৌ’ থেকে বোঝা যায় নরক অপবিত্র লোকবিশেষ। মহাভারতে বহুস্থানে নরক শব্দ পাওয়া যায়। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেবহূতিসংবাদে পাওয়া যায়-
‘অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ।।’- (ভাগবত-৩/৩০/২৯)
অর্থাৎ : নরকযন্ত্রণা ইহলোকেও ভোগ করতে দেখা যায়। স্বর্গ ও নরক ইহলোকেই।
.
স্বর্গ ও নরক যে ইহলৌকিক, অনুরূপ একটি প্রাচীন উক্তিও পাওয়া যায় (সূত্র: সুখময় ভট্টাচার্য্য/ পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন,পৃষ্ঠা-৯৯)-
‘ইহৈব স্বর্গনরকাবিতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে।
মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্-বিপর্য্যয়ঃ।।’
অর্থাৎ : স্বর্গ ও নরক ইহলোকেই ভোগ্য। মনের প্রীতিকর বিষয়ই স্বর্গ এবং অপ্রীতিকর বিষয়ের নাম নরক।
.
এবং তার্কিক কবি শ্রীহর্ষও তাঁর নৈষধীয়চরিতে বলেছেন-
‘দ্যৌর্ন কাচিদথবাস্তি নিরূঢ়া,
সৈব সা চলতি যত্র হি চিত্তম্ ।’- (নৈষধীয়চরিত-৫/৫৭)
অর্থাৎ : স্বর্গনামে প্রসিদ্ধ কোন স্থান বা অন্য কিছুই নেই। যে বিষয়ে যাঁর অনুরাগ থাকে, সেই বিষয়ই তাঁর নিকট স্বর্গ।
.
কিন্তু এসব আলোচনা থেকে কোন পরিষ্কার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বিভিন্ন শাস্ত্র-পুরাণাদির বচনের আপাতলভ্য অর্থকে গ্রহণ না করে শুভ কর্মের প্রশংসা এবং অশুভ কর্মের নিন্দারূপ অর্থবাদ বলেই মীমাংসকগণ সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করে থাকেন। তাই হয়তো মীমাংসক ভাষ্যকার শবরস্বামী বলেন-
‘যদ্যপি কেবলং সুখশ্রবণার্থাপত্ত্যা তাদৃশো দেশঃ স্যাত্তথাপি অস্মৎপক্ষস্যাবিরোধঃ।’- (শাবরভাষ্য)
অর্থাৎ : শ্রুতিতে যে স্বর্গ শব্দ আছে, সেই শব্দ থেকে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণের বলে যদি কোন স্থানবিশেষও কল্পিত হয়, তবুও নিরতিশয় প্রীতিই যে স্বর্গ, আমাদের এ সিদ্ধান্তের সাথে বিরোধ হয় না।
.
তবে ভট্টপদ কুমারিল স্থানবিশেষকেই স্বর্গ বলেছেন। তিনি ভাষ্যকারের উক্তিকে বলেন- অভ্যুপেত্যবাদ, অর্থাৎ আপাত কথনমাত্র। তিনি বলেছেন-
‘যা প্রীতির্নিরতিশয়া অনুভবিতব্যা, সা চ উষ্ণশীতাদিদ্বন্দ্বরহিতে দেশে শক্যা অনুভবিতুম্ । অস্মিংশ্চ দেশে মুহূর্তশতভাগোহপি দ্বন্দ্বৈর্ন মুচ্যতে। তস্মান্নিরতিশয়াপ্রীত্যনুভবায় কল্প্যো বিশিষ্টো দেশঃ।’
অর্থাৎ : নিরতিশয়া যে প্রীতি অনুভব করতে হবে তা উষ্ণশীতাদি-দ্বন্দ্বরহিত স্থানেই অনুভব করা যেতে পারে। এই মর্ত্যলোকে মুহূর্তের শতাংশ কালও দ্বন্দ্বরহিত নয়। তাই নিরতিশয় প্রীতি অনুভব করবার নিমিত্ত বিশিষ্ট স্থান কল্পনা করতে হয়।
.
এখানে আবার প্রশ্ন ওঠে, স্বর্গ মানে যদি শুধু সুখই হয় এবং যেহেতু সুখ ইহকালেই সম্ভব তাহলে স্বর্গ বলে লোকোত্তর কিছু কি নেই ? এ বিষয়ে ভূতনাথ সপ্ততীর্থ শাবরভাষ্য (৬/১/২)-এর তর্জমায় মন্তব্য করেন-
‘মীমাংসকগণের এ বিষয়ে যথাযথ মত কী তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। ভাষ্যের আপাতলভ্য অর্থে বুঝা যায়, স্বর্গ বা নরকভোগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান বিশেষ অনাবশ্যক।’ (সূত্র: ভারতীয় দর্শন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-২৫৬)।
এই তথাকথিত আপাতলভ্য অর্থটিই যে প্রকৃত অর্থ হবে তার নজির হলো, মীমাংসা-মত খণ্ডনে বৈদান্তিকদের উত্থাপিত যুক্তির পূর্বপক্ষ হিসেবে মীমাংসা-মতকে এই অর্থেই উপস্থাপন করা। যেমন, বেদান্তর বিবরণ প্রস্থানের ‘তত্ত্বদীপন’ টীকায় পূর্বপক্ষ হিসেবে মীমাংসা-মত উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে-
‘কিং লোকবিশেষঃ স্বর্গঃ, উত সুখমাত্রম্ ? নান্যঃ, তত্র মানাভাবাৎ।’-
অর্থাৎ, লোকবিশেষকে স্বর্গ বলা যায় না, তাহাতে কোনো প্রমাণ নাই।
একইভাবে ‘বিররণপ্রমেয়সংগ্রহ’-তেও পূর্বপক্ষ হিসেবে মীমাংসা-মত উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে-
‘অত্রৈব নরক-স্বর্গাবিতি মাতঃ প্রচক্ষতে। মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তাদ্বিপর্যয়ঃ’-
অর্থাৎ, স্বর্গ ও নরক ইহলোকেই ভোগ্য, আর নিরতিশয় যে প্রীতি তাহাই স্বর্গ এবং তদ্বিরুদ্ধ যে-দুঃখ তাহাই নরক।
এক্ষেত্রে, মীমাংসাসূত্র ৬/১/৩ শাবরভাষ্যের মূল প্রতিপাদ-বিষয়, স্বর্গাদি ফলই সাধ্য বা প্রধান, যাগাদি কর্ম তার কারণ বা গুণস্বরূপ। যুক্তি হলো, নিষ্ফল কর্মে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদন করতে পারে না। পক্ষান্তরে কর্ম ক্লেশাত্মক হওয়ায় পুরুষের প্রবৃত্তিকে প্রতিহত করে, অতএব, বিধিশক্তিকে কুণ্ঠিত করে। তাই, যজ্ঞকর্মের ফল যে স্বর্গ বা নিরতিশয় সুখ- অর্থাৎ, নিরতিশয় সুখই উদ্দেশ্য, যজ্ঞকর্ম তার উপায়মাত্র- এই বোধ সুদৃঢ় না হলে যজ্ঞকর্মমূলক বিধি শক্তিশালী হতে পারে না। (সূত্র: ভারতীয় দর্শন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৩২৮)।
মীমাংসকদের এই অর্থবাদ ব্যাখ্যা অনুসারে মানতেই হয় যে, বেদোক্ত ‘স্বর্গকামো যজেত’ বিধিবাক্যটিকে মীমাংসকেরা ‘সুখকামো যজেত’ অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন। শবরস্বামীর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা অনুযায়ী মীমাংসা-দর্শনে এই বিধিবাক্যের উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করায় সহজেই অনুমান হয়, মীমাংসা-মতে বস্তুত সুখলাভই মানুষের চরম উদ্দেশ্য- যজ্ঞ এই সুখলাভের উপায়মাত্র।
.
মোক্ষ :
স্বর্গ নামের উৎকৃষ্ট সুখ যদি ইহলোকেই ভোগ্য হয়, তাহলে এ পর্যায়ে এসে প্রশ্ন ওঠে, মীমাংসা-মতে ইহলৌকিক সুখই কি পুরুষার্থ বা মোক্ষ বলে বিবেচিত হবে ? এখানে উল্লেখ্য, লোকায়ত চার্বাক-মতেও কিন্তু বলা হয়, সুখই পুরুষার্থ। যদিও লোকায়তিকরা যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদিকে পুরোহিত-শ্রেণীর প্রবঞ্চনামূলক উদ্ভাবন বলে বিদ্রূপ করেছেন। তাহলে আস্তিক-নিন্দিত লোকায়তিকদের সঙ্গে আস্তিক-অগ্রণী মীমাংসকদের পুরুষার্থ বিষয়ে মতপার্থক্য কোথায় ? পূর্ব-মীমাংসার নামান্তর কর্মমীমাংসা। বেদের ব্রাহ্মণভাগ বা কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করেই এই দর্শনের উদ্ভব। অতএব কর্মই মীমাংসার মূল আলোচ্য বিষয়। এবং কর্মের ফল স্বর্গ বা সুখ, মোক্ষ নয়। অতএব মীমাংসা-দর্শনে যুক্তিযুক্তভাবে মোক্ষের আদর্শ থাকা সম্ভব নয়। কিংবা কোনো মীমাংসক যদি মোক্ষকেই পুরুষার্থ বলে গ্রহণ করতে চান তাহলে তাঁকে মীমাংসা-দর্শনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করতে হবে। এজন্যেই কি সূত্রকার মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাসূত্রে মোক্ষের কোনো আলোচনা করেননি? এমনকি ভাষ্যকার শবরস্বামীর শাবরভাষ্যেও মোক্ষ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা বা উল্লেখ নেই। তাই মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ তাঁর ‘ভারতীয় দর্শন সমগ্র’-এ বলেন-
‘পূর্ব-মীমাংসা দর্শনের সূত্রকার জৈমিনি মোক্ষর কোনো আলোচনা করেন নাই। ধর্মের সাধন, স্বরূপ প্রভৃতির আলোচনাতেই জৈমিনি-সূত্র পর্যবসিত হইয়াছে।’ (সূত্র: ভারতীয় দর্শন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-২৫৮)।
প্রাচীন মীমাংসার আদিরূপটিতে যুক্তিযুক্তভাবেই মোক্ষের কোনো স্থান না থাকলেও কালক্রমে পরবর্তীকালের মীমাংসকদের মধ্যে মোক্ষই পুরুষার্থ বলে স্বীকার করার ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। মীমাংসক প্রভাকর মিশ্র ও কুমারিল ভট্ট মোক্ষ বিষয়ে আলোচনাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও তাঁদের অনুগামীরা ক্রমশই এ আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, তারই ফলে তাঁরা ক্রমশই সুপ্রাচীন মীমাংসা-মতকে বেদান্ত বা প্রচ্ছন্ন-বেদান্তে পরিণত করেছেন। ‘প্রকরণপঞ্চিকায়’ শালিকনাথ মিশ্র বলছেন-
‘আত্যন্তিকো দেহোচ্ছেদঃ নিঃশেষধর্ম্মাধর্ম্মপরিক্ষীণো মোক্ষঃ।’- (প্রকরণপঞ্চিকা)
অর্থাৎ : কর্মপ্রসূত সমস্ত ধর্মাধর্মের ঐকান্তিক বিলোপই মোক্ষ।
মজার বিষয় হলো, মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করা হলে কর্ম এবং ধর্মকর্ম সবকিছুই পরম পুরুষার্থেও অন্তরায় বলে বিবেচিত হতে বাধ্য এবং যদি তাই হয় তাহলে মীমাংসকদের কাছে মীমাংসা-দর্শনের মূল আলোচ্য-বিষয়ই বর্জনীয় হতে বাধ্য। তারপরও এই স্ববিরোধিতাই পরবর্তীকালের মীমাংসকদের মধ্যে প্রকট হতে দেখা যায়। অর্থাৎ নামে মীমাংসক হলেও পরবর্তীকালের মীমাংসকেরা মীমাংসাকে বেদান্তনুগামী বা বেদান্তনুসারী করবারই প্রয়াস করেছেন। বস্তুত প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে এ-জাতীয় প্রয়াসের প্রকট পরিচয় পাওয়া যায়। সেজন্যেই গৌড় ব্রহ্মানন্দ তাঁর ‘সিদ্ধান্তবিন্দু’ গ্রন্থে বলেন-
‘প্রভাকরভাট্টয়োস্তু বেদান্তদর্শনে বিদ্বেষাভাবঃ।’-(সিদ্ধান্তবিন্দু)
অর্থাৎ : বেদান্ত-দর্শনে প্রভাকরের (ও ভাট্টর) বিদ্বেষ নেই।
পরবর্তী প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের মতে সকল প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক লয়ে ভূমানন্দের যে অনুভূতি হয় তাই মুক্তি। শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই জন্ম এবং এই সম্বন্ধের বিনাশই মৃত্যু। কর্মফল ভোগের জন্য জীবকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে সুখ-দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয়। এইরূপ বিনাশই মুক্তি।
মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে অবশ্য ভাট্ট-সম্প্রদায় ও প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য বর্তমান। প্রাভাকর-মতে সকল দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশই মোক্ষ। মোক্ষলাভে ধর্ম ও অধর্ম দুই-এরই বিনাশ হয়। ধর্ম ও অধর্মের জন্যই জীবের সংসারগতি লাভ হয়। ধর্ম ও অধর্ম সম্পূর্ণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হলে দেহের যে আত্যন্তিক বিনাশ হয়, তাই মোক্ষ। ধর্ম ও অধর্মের বশীভূত হয়েই জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে আবর্তিত হয়। সংসারে আত্যন্তিক সুখ নেই। সংসার-সুখ অস্থির। কর্মের কর্তা-রূপ আত্মায় শুভ বা অশুভ রূপ অদৃষ্ট বা অপূর্ব সমবেত থাকে এবং এই অদৃষ্ট বা অপূর্বের দ্বারাই শুভ ও অশুভ ফল লাভ হয়। এই অপূর্ব লৌকিক প্রমাণের অগম্য, একমাত্র বৈদিক শব্দ প্রমাণের দ্বারাই তার কথা জানা যায়।
বৈদিক কর্মসমূহও যে মরণোত্তর বা জন্মান্তরীয় ফল উৎপাদন করে, সে ক্ষেত্রেও ঐ অদৃষ্ট বা অপূর্ব অলৌকিক শক্তি হিসেবে কাজ করে। কর্ম ইহজীবনে সাময়িককালে অনুষ্ঠিত হলেও তার ফল ভোগ করতে হয় জন্ম-জন্মান্তরে। নিষিদ্ধ কর্মের ফলে যে অশুভ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় পাপ। পাপের ফলে আত্মাকে নরক ভোগ করতে হয়। আর বিহিত কাম্য-কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তার দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়।
প্রাভাকর-মতে এই স্বর্গাদিলাভ শুভকর্মের প্রাসঙ্গিক ফলমাত্র। কর্তব্যবোধেই কর্ম অনুষ্ঠেয় এবং তার ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়, আর শুদ্ধচিত্তেই মোক্ষপ্রাপ্তির প্রত্যক্ষ কারণস্বরূপ জ্ঞান লাভ হয়। তাই বলা হয়, ধর্মজিজ্ঞাসা বা ধর্মানুষ্ঠান ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ববর্তী ধাপ। উল্লেখ্য, এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হলো মূলত বেদান্ত-সিদ্ধান্ত।
লৌকিক শুভকর্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। ভাট্ট-মতে নিত্যকর্ম প্রত্যক্ষভাবে ফলদায়ক নয়। দূরিতক্ষয়ই তার ফল। প্রাভাকর-মতে ফল-নিরপেক্ষভাবেই নিত্যকর্ম অনুষ্ঠেয়। এই কর্মই পুরুষার্থ। কাম্য, নিত্য ও নৈমিত্তিক এই ত্রিবিধ কর্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম। ধর্মমাত্রই দুঃখমিশ্রিত। সেজন্যেই জীবের মোক্ষাভিলাষ জাগে। ইহলোকে বা পরলোকে সুখ বা দুঃখ উৎপাদনকারী সমস্ত প্রকার কর্ম থেকে বিরতিই মোক্ষ। দূরিতক্ষয়কারী প্রয়োজনীয় প্রায়শ্চিত্ত কর্মের দ্বারা সঞ্চিত কর্মের ফলনাশ হয় এবং শম, দম, ব্রহ্মচর্য, সন্তোষ প্রভৃতি দ্বারা শরীরী সত্তা থেকে ক্রমশ মুক্তি হয়। কিন্তু শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বন্ধন-মুক্তি হয় না। তার জন্য বেদবিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান প্রয়োজন। তবে কাম্য কর্ম পুনর্জন্মের প্রযোজক, মোক্ষলাভের ঘটক নয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা পাপ-পুণ্যের ভবিষ্যৎ-বৃদ্ধি বিরত হয়। নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম সাধন করে চিত্ত শুদ্ধ হয়। পরে শমদমাদিসাধন সম্পত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলেই মোক্ষ লাভ হয়।
প্রাভাকর-মতে জীবের এই মুক্তাবস্থা কিন্তু আনন্দদায়ক অবস্থা নয়। মুক্ত আত্মা নির্গুণ বলে তার আনন্দানুভব সম্ভব নয়। নির্গুণ আত্মার স্বাভাবিক রূপের স্ফুরণই মোক্ষ। মোক্ষ সুখ এবং দুঃখ এই দুই-এরই অতীত। কিন্তু ভাট্ট-মতে মোক্ষ আনন্দস্বরূপ। সকল দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশে উৎপন্ন ভূমানন্দ লাভই মোক্ষ। সংসারে জন্মগ্রহণ করে জীবকে সুখ-দুঃখ ভোগ করতেই হয়, আর সুখ-দুঃখের ভোগের দ্বারাই সঞ্চিত ও প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয়। কিন্তু নিষিদ্ধ ও কাম্য বর্ম বর্জন না করলে নব নব ভোগ্যবস্তুর দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং মোক্ষলাভে বাধা সৃষ্টি হয়। তাই শ্লোকবার্ত্তিকের সম্বন্ধাক্ষেপপরিচ্ছেদে কুমারিল ভট্ট বলেছেন-
‘মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ।
নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া।।’- (শ্লোকবার্ত্তিক-সম্বন্ধাক্ষেপপরিচ্ছেদ)
অর্থাৎ : মোক্ষকাম ব্যক্তি কাম্যকর্ম ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত হবেন না। পাপের উৎপত্তি যেন না হয়, এ উদ্দেশ্যে নিত্যকর্ম ও নৈমিত্তিককর্ম অবশ্যই করবেন।
ভূমানন্দস্বরূপ মোক্ষ দুঃখের আত্যন্তিক অভাবস্বরূপ। তাই এই অবস্থা নিত্য। ভাট্টমতে বলা হয়, সূত্রকার জৈমিনি স্বর্গরূপ যে পুরুষার্থেও কথা বলেছেন, তার দ্বারা আসলে মোক্ষই সূচিত হয়। কারণ স্বর্গ বলে কোন স্থান নেই। দুঃখলেশশূন্য পূর্ণানন্দই মোক্ষস্বরূপ। তাই পরবর্তী গ্রন্থকার নারায়ণ ভট্ট তাঁর ‘মানমেয়োদয়’-এ ভাট্টমত উল্লেখ করে বলেছেন-
‘দুঃখাত্যন্তসমুচ্ছেদে সতি প্রাগাত্মবর্ত্তিনঃ।
আনন্দস্যানুভূতিস্তু মুক্তিরুক্তা কুমারিলৈঃ।।’- (মানমেয়োদয়)
অর্থাৎ : দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হলে তখন আত্মাতে পূর্ব থেকে বিদ্যমান নিত্যানন্দের যে অনুভূতি হয়, তাকেই কুমারিল ভট্ট মুক্তি বলেছেন।
এই মোক্ষরূপ স্বর্গই নিত্য, আর কাম্যকর্মজন্য অপূর্ব থেকে লব্ধ যে স্বর্গের কথা বলা হয়েছে, তা অনিত্য। অর্থাৎ পুণ্যের দ্বারা যে স্বর্গলাভ হয়, পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হলে সেখান থেকে আবার মর্ত্যে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু ভূমানন্দস্বরূপ মোক্ষ নিত্য, তাকে আর হারাতে হয় না। মোক্ষ তাই নিত্য আনন্দস্বরূপ।
কিন্তু মুক্তজীবের আনন্দানুভূতি যথার্থই কুমারিলসম্মত কি না, তা বিচার সাপেক্ষ। কেননা শঙ্করাচার্য, মাধবাচার্য, উদয়নাচার্য, নারায়ণভট্ট প্রমুখ আচার্যগণ কুমারিলমতে মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতির কথা বলে গেছেন। কিন্তু কুমারিলের গ্রন্থ ‘শ্লোকবার্ত্তিক’-এ সেরকম দেখা যায় না, বরং বিপরীত সিদ্ধান্তই পরিলক্ষিত হয়। যেমন, শ্লোকবার্ত্তিকের সম্বন্ধাক্ষেপ-পরিহার-প্রকরণে কুমারিল বলছেন-
‘সুখোপভোগরূপশ্চ যদি মোক্ষঃ প্রকল্প্যতে।
স্বর্গ এব ভবেদেষ পর্য্যায়েণ ক্ষয়ী চ সঃ।।
ন হি কারণবৎ কিঞ্চিদক্ষয়িত্বেন গম্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্মক্ষয়াদেব হেত্বভাবেন মুচ্যতে।।
ই হ্যভাবাত্মকং মুক্তা মোক্ষনিত্যত্বকারণম্ ।…ইত্যাদি।’- (শ্লোকবার্ত্তিক)
অর্থাৎ :
যদি সুখের উপভোগরূপ মোক্ষের কল্পনা করা হয়, তবে তা স্বর্গই হবে এবং কালক্রমে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। কারণবিশিষ্ট কোন কার্যবস্তুই অক্ষয় হয় না। অর্থাৎ সকল কার্যবস্তুই বিনষ্ট হয়ে থাকে। অতএব প্রারব্ধাদি কর্মের ক্ষয় হলেই ভোগ্যহেতুর অভাববশত জীবের মুক্তি হয়। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অভাবাত্মক না হলে মুক্তির নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। (সূত্র: সুখময় ভট্টাচার্য্য/ পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন, পৃষ্ঠা-২০২)
.
উল্লেখ্য, এখানে কুমারিল নিত্যসুখের অভিব্যক্তির কথা বলেননি। একারণে কুমারিলমতের সর্বপ্রধান ব্যাখ্যাতা পার্থসারথিমিশ্র কী বলেন তাও উল্লেখ্য। তিনি তাঁর ‘শাস্ত্রদীপিকা’ গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলে রেখেছিলেন-
‘কুমারিলমতেনাহং করিষ্যে শাস্ত্রদীপিকাম্ ।’
অর্থাৎ : আমি কুমারিলের মতকে অবলম্বন করে ‘শাস্ত্রদীপিকা’ রচনা করছি।
.
এই ‘শাস্ত্রদীপিকা’র তর্কপাদে পার্থসারথি আনন্দমোক্ষবাদিগণের মত প্রদর্শন করে বিচারপূর্বক সেই মত খণ্ডন করেছেন, এবং পরিষ্কার বলেছেন-
‘সুখদুঃখাদিসমস্তবৈশেষিকাত্মগুণোচ্ছেদো মোক্ষঃ।’ ইত্যাদি- (শাস্ত্রদীপিকা)
অর্থাৎ : সুখ-দুখাদি আত্মগত সর্ববিধ বিশেষ গুণের আত্যন্তিক বিনাশই মোক্ষ।
.
পার্থসারথি বলেন, ধর্ম ও অধর্মের বিনাশে সুখদুঃখের বিনাশ। উপভোগ, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান এবং আত্মজ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন ধর্মাধর্মের বিনাশ। নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান না করায় উৎপাদ্য ধর্মাধর্মের অনুৎপত্তি। এই অবস্থায় দেহবিনাশে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা না থাকায় জীব মুক্ত হয়ে থাকেন।
এবং আরো প্রাঞ্জল ভাষায় পার্থসারথি বলেন-
‘নিরানন্দো মোক্ষঃ; দুঃখপরিলোপাচ্চ পুরুষার্থত্বম।’- (শাস্ত্রদীপিকা)
অর্থাৎ : মোক্ষদশায় জীবের আনন্দ থাকে না, দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয় বলেই মোক্ষ পুরুষার্থ, অর্থাৎ জীবের অভিলষিত।
.
কুমারিলমতকে সহজবোধ্য করবার নিমিত্ত পার্থসারথি ‘শাস্ত্রদীপিকা’য় যা বলেছেন, তার তাৎপর্য হলো- সংসারপ্রপঞ্চের বিলয়ই মোক্ষ নয়, প্রপঞ্চের সাথে জীবের সম্বন্ধের বিলয়ই মোক্ষ। শরীর থাকলেই সুখদুঃখ ভোগ করতে হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগের সাধন এবং রূপরসাদি ভোগ্য বস্তু। শরীর, ইন্দ্রিয় ও ভোগ্য- এই তিনের বিলয় মোক্ষেই প্রতিষ্ঠিত। কর্মজনিত পাপপুণ্যের ফল ভোগ করবার নিমিত্ত জীবের শরীরধারণ। ভোগের দ্বারা পাপপুণ্য নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হলে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। শরীরাদি প্রপঞ্চের সাথে জীবের সম্বন্ধকে ‘বন্ধ’ বলে, আর চিরতরে এই বন্ধের নাশই মোক্ষ।
মীমাংসার মূল আলোচ্য-বিষয় অবশ্যই বৈদিক যাগযজ্ঞ বা ক্রিয়াকর্ম- আধুনিক অর্থে যা দার্শনিক আলোচনা নয়। অর্থাৎ, মীমাংসকরা তত্ত্ব-লাভের উদ্দেশ্যে দর্শন-চর্চা করেননি। তবুও তাঁরা যে অনিবার্যভাবেই দার্শনিক সমস্যা উত্থাপন ও আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন তার কারণ এই যাগযজ্ঞে চরম বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবিক প্রচেষ্টাদি সংক্রান্ত একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিও অবলম্বন করা প্রয়োজন। অনুমান হয়, সুপ্রাচীন কালে যাজ্ঞিকদের মধ্যে যজ্ঞকর্মের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে বিভেদ ও বিতর্ক থাকলেও যে-মূল বিশ্বাসের ভিত্তিতে যজ্ঞের চরম গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত সে-সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ ছিলো না; সে-বিশ্বাস তাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ অতএব প্রমাণ-সাপেক্ষ না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কালক্রমে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় গড়ে উঠার প্রেক্ষিতে সেগুলির দিক থেকে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রচেষ্টাদি প্রসঙ্গে যে-সব মত প্রস্তাবিত হয়েছে তার সঙ্গে যাজ্ঞিকদের মূল বিশ্বাসের অনিবার্য সংঘাতও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। ফলে প্রয়োজন হয়েছে সেই মূল বিশ্বাসের যুক্তিতর্কমূলক সমর্থন ও সংরক্ষণ এবং তার সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন- অন্তত অন্যান্য সম্প্রদায়ের সেই দাবিগুলি খন্ডন করবার প্রয়োজন হয়েছে যার সঙ্গে যাজ্ঞিকদের মূল বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সংহতি সম্ভব নয়। এভাবেই দার্শনিকতত্ত্ব মীমাংসার মূখ্য বিষয়বস্তু না হলেও মীমাংসকরা ক্রমশই দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে মীমাংসকরা যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তা বেদান্তশান্ত্রের মধুসূদন সরস্বতীর ‘অদ্বৈতসিদ্ধি’ গ্রন্থেও উল্লেখ পাওয়া যায়-
‘নাস্তি সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্যুপেতং ব্রহ্মেতি মীমাংসকাঃ।’- (অদ্বৈতসিদ্ধি)
অর্থাৎ : মীমাংসকগণ বলেন যে, সর্বজ্ঞতাদিবিশিষ্ট ঈশ্বর নেই।
বেদের চরম প্রামাণ্যই মীমাংসার ভিত্তি। মীমাংসা-মত ও তার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, স্রষ্টা হিসেবে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলে যাজ্ঞিকদের মূল বিশ্বাস ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। ফলে নিরীশ্বরবাদী মীমাংসকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার তো করেনই নি, বরং ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডনে বিস্ময়কর যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে সুপ্রাচীন অগ্রদূত হিসেবে যে দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে ঈশ্বরকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন, আধুনিক মননের কাছে তার অসাধারণ দার্শনিক মূল্য কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় নয়। যদিও জৈমিনি তাঁর মীমাংসাসূত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ করেননি তবুও ভাষ্যকার শবরস্বামী অনুভব করেছেন স্রষ্টার কথা স্বীকার করতে গেলে বেদ-এর প্রামাণ্য ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা থাকে। তাই শবরভাষ্যেই (শাবরভাষ্য: মীমাংসাসূত্র-১/১/৫) প্রথম যুক্তিপূর্ণভাবে ঈশ্বর-প্রত্যাখ্যানের সূত্রপাত। এবং পরবর্তী মীমাংসকদের রচনাতে আরো পল্লবিত হয়ে সুস্পষ্ট যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ঈশ্বর-প্রত্যাখ্যানের পূর্ণ আয়োজন লক্ষ্য করা যায়।
.
শবরস্বামীর ঈশ্বর-খণ্ডন
শবরস্বামীর কাছে সমস্যা উঠেছে মূলত বেদ-নিত্যতায় শব্দপ্রমাণের জের ধরে। বেদ যে নিত্য তা প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে শবর বলছেন, শব্দও নিত্য, শব্দার্থও নিত্য এবং শব্দ ও শব্দার্থের মধ্যে সম্বন্ধও নিত্য। কিন্তু ঈশ্বর বা স্রষ্টার কথা স্বীকার করলে শব্দার্থ-সম্বন্ধের এই নিত্যতা হানি হবার কথা; কেননা তাহলে মানতে হবে ঈশ্বর বা স্রষ্টাই এই শব্দার্থ-সম্বন্ধ সৃষ্টি করেছিলেন, অর্থাৎ সে-সম্বন্ধ নিত্য নয়। এই আশঙ্কাতেই শবর স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন।
এ-জাতীয় কোনো স্রষ্টার কল্পনা যে অবাস্তব সে-বিষয়ে শবরের যুক্তি হলো, তৎ-সম্বন্ধে প্রমাণাভাব- অর্থাৎ, কোনো প্রমাণের সাহায্যেই স্রষ্টার সত্তা সিদ্ধ হতে পারে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব সিদ্ধ নয়, কেননা এ-জাতীয় স্রষ্টারা প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নয় বলেই অন্য কোনো প্রমাণও তাঁর সত্তার প্রতিপাদক হতে পারে না, কারণ অপরাপর প্রমাণ প্রত্যক্ষমূলক। কেননা, যুক্তিন্যায় মতে- ‘সাধ্যের সাথে নিয়ত সম্বন্ধবিশিষ্ট কোনোও ধর্ম যদি প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য না হয়, তাহলে সেই সাধ্য প্রমাণান্তরের বিষয় হতে পারে না।’
.
এখানে তর্ক তুলে হয়তো বলা হবে, বর্তমান কালে স্রষ্টা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হলেও অতীত কালে তাঁর প্রত্যক্ষ হয়েছিলো।
উত্তরে শবর বলছেন, তাহলে তাঁর কথা সকলের স্মরণ থাকতো; কিন্তু ( বৈদিক) শব্দ এবং শব্দার্থের সম্বন্ধ-স্রষ্টার কথা কেউই স্মরণ করতে পারে না।
তর্ক তুলে হয়তো আবার বলা হবে, সুদূর অতীতে এই স্রষ্টা প্রত্যক্ষত উপলব্ধ হলেও বহুকাল অতীত হওয়ায় তা এখন স্মরণেরও বিষয় নয়; যেমন স্থলবিশেষে কূপ, উপবন প্রভৃতি দৃষ্ট হলেও তার স্রষ্টা যে কে তা কারুর স্মৃতিতে নেই।
উত্তরে শবর বলছেন, অধিককালের ব্যবধান হলেই অস্মরণ অনিবার্য নয়; কূপ, উপবন প্রভৃতির দৃষ্টান্তে বুঝতে হবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হেতু স্থানটি জনশূন্য হয়েছে এবং এইভাবে পূর্বেও পারম্পর্য লোপ পাওয়ায় এগুলির-স্রষ্টা বিস্মৃত হয়েছে; কিন্তু বৈদিক শব্দার্থ নিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে গুরু-শিষ্যের একটি পারম্পর্য চলে আসছে, তাই যদি বৈদিক শব্দার্থ-সম্বন্ধের কোনো স্রষ্টা থাকতেন তাহলে তাঁর স্মৃতিও বর্তমান থাকতো; কিন্তু এ-জাতীয় কোনো স্মৃতি বর্তমানে নেই।
.
তর্ক তুলে আবারও হয়তো বলা হবে, ঘট শরাবাদি দ্রব্য সকলে ব্যবহার করলেও এগুলির যে কুম্ভকার তার নাম কি সকলের স্মরণে থাকে ?
উত্তরে শবর বলছেন, এ-তুলনা সমীচীন নয়। কেননা ব্যবহার-নির্বাহের জন্য সেগুলির স্রষ্টা কুম্ভকারের নাম স্মরণের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু বেদের আপ্তত্ব অবধারিত না হলে বৈদিক ব্যবহার অসম্ভব। কারণ, যাঁর আপ্তত্ব অবধারিত নয়- অর্থাৎ যাঁর সম্বন্ধে এ-কথা জানা নেই যে ইনি ভ্রম-প্রমাদ-প্রতারণাবুদ্ধিশূন্য- তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে কেউই কোনো কষ্টসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয় না; অথচ বেদবাক্য শুনেই বৈদিকেরা যজ্ঞকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। অতএব, বেদবাক্যের যদি কোনো স্রষ্টা থাকতেন এবং তিনিই যদি শব্দার্থের স্রষ্টা হতেন তাহলে অবশ্যই তাঁর স্মরণও থাকতো; কেননা বেদবিহিত ব্যবহারের জন্য তা অপরিহার্য।
পূর্বপক্ষ হয়তো বলবেন, অর্থাপত্তির দ্বারা এই স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়। বেদান্ত এবং মীমাংসা সম্প্রদায়ে অর্থাপত্তি নামের একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে যে, অন্য একটি বিষয় স্বীকার না করে যখন একটি জ্ঞাত বিষয়ের ব্যাখ্যা হয় না তখন এই জ্ঞাতবিষয়টির ব্যাখ্যাকল্পে উক্ত বিষয়টির যে প্রমাণ তারই নাম অর্থাপত্তি। যেমন দেবদত্ত দিনে খায় না অথচ মোটা হচ্ছে; এই ঘটনার ব্যাখ্যাকল্পে প্রমাণ হয় যে দেবদত্ত রাতে খায়। অতএব পূর্বপক্ষ বলতে পারেন, ঘট-শরাবাদির স্রষ্টা অজ্ঞাত হলেও কর্তা ব্যতীত এগুলির উৎপত্তি সম্ভব নয় বলেই অর্থাপত্তির দ্বারা যেমন কর্তার প্রমাণ হয়, তেমনি শব্দ ও শব্দার্থের সম্বন্ধ সৃষ্টি না হলে শব্দ থেকে অর্থবোধ সম্ভব হতো না,- অতএব শব্দ থেকে অর্থবোধ হয় এই ঘটনাই অর্থাপত্তি হিসেবে শব্দ ও শব্দার্থের স্রষ্টা প্রমাণ করে।
উত্তরে শবর বলছেন, এ-কথা স্বীকার করতে হলে মানতে হয় শব্দার্থ-সম্বন্ধের স্রষ্টা ব্যতীত শব্দের অর্থবোধ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। কিন্তু সে-কথা স্বীকার করবার কারণ নেই। কেননা, শব্দের অর্থবোধ অন্যভাবেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। শব্দ ও শব্দার্থের সংকেতে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই; বৃদ্ধগণের সংকেত-নির্দেশ এই শব্দার্থ-সম্পর্কের জ্ঞাপক, যদিও কারক নয়; এবং এই বৃদ্ধগণ যখন অব্যুৎপন্ন ছিলেন তখন তাঁদের পূর্ববর্তীরা ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সেই পূর্ববর্তীদের উপদেশানুসারে বৃদ্ধগণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। এই ভাবেই সেই পূর্ববর্তীগণ- এবং তাঁদের পূর্ববর্তীগণও- ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তাই শব্দার্থের সম্বন্ধ-জ্ঞানের আদি নির্দেশ অসম্ভব; অর্থাৎ তা অনাদি বা নিত্য। এবং এই ব্যাখ্যা সম্ভব বলেই শব্দার্থ-সম্বন্ধ প্রসঙ্গে কোনো এক স্রষ্টার অর্থাপত্তি অবান্তর।
.
এখানে লক্ষ্যণীয় যে, শবরভাষ্যে শব্দার্থ প্রসঙ্গে আলোচনা উত্থাপিত হলেও শবরের যুক্তির মূল তাৎপর্য হলো শব্দ ও শব্দার্থের সম্বন্ধকে প্রবাহ-নিত্যতা বা ‘অনিদংপ্রথমত্ব’ (অর্থাৎ ইনিই প্রথম বেদবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, এই হলো বেদের আবির্ভাব- এমন কথা কেউ বলতে পারে না, তাই বেদ নিত্য অপৌরুষেয়) জাতীয় দুর্বল যুক্তির মাধ্যমে স্রষ্টা অর্থে ঈশ্বর-প্রত্যাখ্যান। কেননা, ঈশ্বর স্বীকার করলে আরও স্বীকার করতে হবে যে শব্দ, শব্দার্থ এবং উভয়ের সম্বন্ধ তাঁরই সৃষ্টি। কিন্তু মীমাংসকরা তা স্বীকার করতে পারেন না। তাঁরা প্রমাণ করতে চান শব্দ, শব্দার্থ এবং উভয়ের সম্বন্ধ অনাদি বা নিত্য। তা না হলে বেদের আপ্তত্ব ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা- বেদকে যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি বলেও মানা হয় তাহলে বেদের আপ্তত্ব ঈশ্বরের আপ্তত্বের উপরই নির্ভরশীল হবে, অর্থাৎ বেদের আপ্তত্ব স্বকীয় ও চরম হবে না। বলা বাহুল্য, এভাবে বেদের চরম বা চূড়ান্ত আপ্তত্ব প্রতিপাদনের প্রচেষ্টা মীমাংসা-দর্শনের চরম সংরক্ষণশীলতারই পরিচায়ক। তবে এটাও মনে রাখা আবশ্যক, এই তাগিদ থেকে উদ্ভূত হলেও পরবর্তীকালের মীমাংসকরা ক্রমশ যে-ভাবে ঈশ্বর-প্রত্যাখ্যানের যুক্তি অবতারণা করেছেন সেগুলির স্বকীয় গুরুত্বের দিক থেকে এই মীমাংসা-দর্শনই অন্যদিকে অত্যন্ত মৌলিকভাবে রীতি-বিরুদ্ধ এবং রক্ষণশীলতা-বিরুদ্ধ অভাবনীয় দর্শনে পরিণত হয়।
.
মীমাংসা-দর্শনের প্রধান দুটি সম্প্রদায়ের প্রবক্তা প্রভাকর মিশ্র ও কুমারিল ভট্টের মধ্যে মীমাংসা-ব্যাখ্যায় যথেষ্ট মৌলিক মতান্তর সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায়ই ঈশ্বর-প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই একমত পোষণ করেছেন। শবর পরবর্তী এসব দার্শনিকদের রচনায় ঈশ্বর-খণ্ডন প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক যুক্তি বিস্তার ক্রমশ এমন অসাধারণ জোরালো হয়ে উঠেছে যে অন্যান্য দর্শন-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় পরবর্তীকালের দার্শনিকদের অনেক সতর্কী করে তোলেছে।
.
প্রাভাকর-মতে ঈশ্বর-খণ্ডন
এ-বিষয়ে প্রাভাকর-মীমাংসক শালিকনাথ মিশ্রের ‘প্রকরণপঞ্চিকা’ গ্রন্থটি মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা প্রমুখ আধুনিক বিদ্বানদের কাছে প্রাভাকরমতের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিচেচিত হয়েছে বলে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘ভারতীয় দর্শন’ গ্রন্থে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং ঈশ্বর-খণ্ডনে প্রাভাকর-মতের সুগ্রাহী আলোচনা করেছেন (পৃষ্ঠা-২৩৯)। এই প্রকরণপঞ্চিকা গ্রন্থে শুধু যে শব্দার্থ-সম্বন্ধের স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বর অস্বীকৃত তা-ই নয়- জগৎ-স্রষ্টা অর্থে ঈশ্বর স্বীকার করা সম্ভব নয়, এই কথাটিই বিশেষভাবে প্রমাণ করবার আয়োজন হয়েছে। কেননা ইতোমধ্যে নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনার্থে নানা যুক্তিতর্কের অবতারণ করেছেন।
.
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনার্থে নৈয়ায়িকদের উপস্থাপিত যুক্তির মধ্যে প্রধান যুক্তি হলো, জগৎ-স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরের সত্তা অবশ্য-স্বীকার্য; কারণ ক্ষিতি, জল প্রভৃতি সমস্ত সংহত বা জটিল বস্তুই কার্যাত্মক, কেননা এগুলি অবয়বদ্বারা গঠিত; এবং কার্য বলেই এগুলির কারণ থাকতে বাধ্য এবং সেই কারণ কোনো বুদ্ধিমান কর্তা না হয়ে পারেন না। বলা হয়ে থাকে, অবয়ব দ্বারা গঠিত সমস্ত বস্তুই কার্য এবং কার্য বলেই কার্য-কারণ তত্ত্ব অনুযায়ী তার কারণও থাকবে। যেহেতু মাটি, জল প্রভৃতি পরমাণু নামের অবয়ব দ্বারা গঠিত সেহেতু এগুলিও কার্য। তাই পরমাণুপুঞ্জ থেকে সুসমঞ্জস্য ও নির্দিষ্ট আকারে ক্ষিতি, জল প্রভৃতি সংহত বা জটিল বস্তুগুলি কোনো বুদ্ধিমান কর্তার নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত উৎপন্ন হতে পারে না; অতএব এই বুদ্ধিমান কর্তা অর্থে জগতের নিমিত্তকারণ হিসেবে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অনুমেয়- তাঁরই নিয়ন্ত্রণে সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটে।
এর উত্তরে প্রাভাকররা বলেন, জাগতিক বস্তুগুলি অবশ্যই অবয়ব দ্বারা গঠিত, অতএব এগুলির উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু তাই বলে সামগ্রিকভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো সৃষ্টি বা প্রলয়ের কথা কল্পনামাত্র; অতএব জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিয়ন্ত্রণকর্তা ঈশ্বরের পরিকল্পনাও অবান্তর। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক বস্তুগুলির দৃষ্টান্তে সুস্পষ্টভাবেই অভিজ্ঞতা হয় যে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণেই সেগুলির জন্ম হচ্ছে- যেমন মানুষ ও জীবজন্তুর দেহ শুধুমাত্র তাদের পিতামাতার দরুনই উৎপন্ন হয়। এবং এ-জাতীয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে অতীত ও ভবিষ্যতের বস্তুগুলিরও উৎপাদন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অতএব, জাগতিক বস্তুগুলির স্রষ্টা হিসেবে কোনো অতি-প্রাকৃত নিয়ন্ত্রাতার কথা অনুমিত হয় না।
.
নৈয়ায়িকরা আরো দাবি করেছেন, ব্যক্তির ধর্মাধর্ম পরিচালনা করার জন্য সাধারণভাবে কোনো পরিচালক- অর্থাৎ ঈশ্বর- স্বীকারযোগ্য।
তার উত্তরে প্রাভাকররা বলেন, প্রথমত যার ধর্মাধর্ম সেই এ-জাতীয় পরিচালক হতে পারে, অতএব ঈশ্বর বলে স্বতন্ত্র পরিচালকের প্রসঙ্গ অবান্তর। দ্বিতীয়ত, একের ধর্মাধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান অপর কারুর পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়; অতএব তথাকথিত ঈশ্বরের পক্ষে কোনো মানবের ধর্মাধর্ম জানাই সম্ভব নয়।
প্রাভাকররা আরো বলেন, তথাকথিত ঈশ্বরের পক্ষে মানবাদির ধর্মাধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞানই যদি সম্ভব না হয় তাহলে তাঁর পক্ষে এই ধর্মাধর্মের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া, উক্ত জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকলেও ঈশ্বরের পক্ষে ধর্মাধর্ম পরিচালনা করা সম্ভব হতো না। কেননা, পরিচালনার জন্য সম্বন্ধ প্রয়োজন; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাদির ধর্মাধর্মের কোনো সম্বন্ধ অসম্ভব। ন্যায়মতেই সম্বন্ধ মাত্র দুরকম হতে পারে- সংযোগ ও সমবায়। ঈশ্বরের সঙ্গে ধর্মাধর্মর সংযোগ সম্ভব নয়; কারণ ধর্মাধর্ম হলো গুণ এবং ন্যায়-মতেই শুধুমাত্র দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের সংযোগ সম্ভব। ঈশ্বরের সঙ্গে ধর্মাধর্মের সমবায়ও সম্ভব নয়; কারণ এই ধর্মাধর্ম মানবাদিরই গুণ, অতএব মানবাদির সঙ্গেই তার সমবায় হতে পারে- মানবাদির গুণের সঙ্গে ঈশ্বরের সমবায় অসম্ভব।
.
এক্ষেত্রে নৈয়ায়িকরা সূত্রধর বা ছুতোরের উপমা দিতে পারেন। অবশ্যই দেহবিশিষ্ট বলে এই ছুতোরের সঙ্গে তার যন্ত্রপাতির এবং যন্ত্রপাতির সঙ্গে কাষ্ঠাদি বস্তুর সংযোগ সম্ভব; কিন্তু তথাকথিত ঈশ্বর দেহবিহীন বলেই পরিকল্পিত, অতএব তাঁর দৃষ্টান্তে এ জাতীয় প্রশ্ন ওঠে না।
প্রাভাকরা আরো বলেন, নৈয়ায়িকরা এ কথাও বলতে পারেন না যে পরমাণুসমূহ ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করে। কারণ এ-জাতীয় নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনার কোনো দৃষ্টান্তই অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, একমাত্র দেহস্থ আত্মাই দেহকে পরিচালনা করতে পারে; কিন্তু পরমাণুসমূহ বা মানবীয় ধর্মাধর্মও ঈশ্বরের দেহ নয়, অতএব ঈশ্বরের পক্ষে এগুলির পরিচালনাও সম্ভব নয়। আর যদিই বা তর্কের খাতিরে এগুলিকে ঈশ্বরের দেহ বলেই পরিকল্পনা করা হয় তাহলেও এগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টার কথা স্বীকার করতে হবে এবং সে ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা যদি নিত্য হয় তাহলে পরমাণুসমূহের সৃষ্টিকার্যকেও, অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিকেও, নিত্য বা নিয়ত ঘটনা বলে স্বীকার করতে হবে।
.
ন্যায়-বৈশেষিকরা বলে থাকেন, মানবদেহ বুদ্ধিহীন বলেই তার নিয়ন্ত্রণের জন্য এক বুদ্ধিমান স্রষ্টা বা ঈশ্বর অনুমেয়।
উত্তরে প্রাভাকররা বলছেন, নিয়ন্ত্রণ-কার্য উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না; কিন্তু এই তথাকথিত নিয়ন্ত্রণের পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী হতে পারে ? তাছাড়া, নৈয়ায়িকরা যে যুক্তিবলে বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণকর্তা প্রমাণ করতে চান সেই যুক্তি অনুসারেই উক্ত নিয়ন্ত্রণকর্তা দেহ-বিশিষ্ট বলেই প্রমাণিত হবেন। কেননা, কাষ্ঠাদি বস্তুর উপর সূত্রধর-এর নিয়ন্ত্রণ-কার্যর দৃষ্টান্ত অনুসারেই তাঁরা জগৎ-স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণ প্রমাণ করতে চান; কিন্তু সূত্রধর দেহবিশিষ্ট, তারই উপমান অনুসারে কল্পিত ঈশ্বরও দেহবিশিষ্ট বলে প্রমাণিত হবেন। কিন্তু দেহবিশিষ্ট কারুর পক্ষেই পরমাণু বা ধর্মাধর্মের মতো সূক্ষ্ম বিষয়কে বুদ্ধিসম্মত এবং কার্যকরিভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এবং যদিই বা তা সম্ভব হয় তাহলে দেহবিশিষ্ট বলেই তাঁর পরিচালনার জন্য আরো কোনো স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ-কর্তার কথা স্বীকৃত হতে বাধ্য, আবার এই স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ-কর্তার পরিচালনার জন্য অপর কোনো এক নিয়ন্ত্রণ-কর্তার কথা স্বীকৃত হতে বাধ্য- এবং এইভাবে অনবস্থা-দোষ ঘটবে।
এইভাবে প্রাভাকররা স্রষ্টা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। এবং তাঁরা সৃষ্টি বা প্রলয় মানেন নি বলেই বিশ্বজগৎ তাঁদের কাছে নিয়ত পরিবর্তনশীল ঘটনাস্রোত বলেই প্রতীত হয়েছে।
.
কুমারিলের নিরীশ্বরবাদ
ভাট্ট-সম্প্রদায়েও বেদের চরম আপ্তত্ব প্রতিপাদন করবার উদ্দেশ্যেই শব্দ, শব্দার্থ এবং উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য বলে স্বীকৃত এবং এই মত প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই ভাট্ট-মীমাংসকরাও সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এ জাতীয় সংরক্ষণশীল চাহিদায় উদ্ভাবিত হলেও স্বকীয় দার্শনিক গুরুত্বের দিক থেকে ভাট্ট-মীমাংসকদের- বিশেষত কুমারিলের- যুক্তিগুলি সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শনের পটভূমিতে প্রায় বৈপ্লবিক বলে প্রতীত হতে পারে ( দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-২৪০)।
কুমারিল ভট্ট তাঁর ‘শ্লোকবার্তিক’ গ্রন্থে সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার:৪১-১১৬-এ এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দেবীপ্রসাদের মতে, এগুলির তর্জমায় মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা সুচরিত মিশ্র এবং পার্থসারথি মিশ্রের টীকা অবলম্বনে যে-পাদটীকা দিয়েছেন, কুমারিল মতের প্রকৃত তাৎপর্য অবগতির জন্য সেগুলি বিশেষ মূল্যবান।
.
কুমারিল বস্তুত নিরীশ্বরবাদের সূচনা করেছেন সর্বজ্ঞতা-খণ্ডনের দ্বারা। মহামহোপাধ্যায় হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘বৈদিকধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৭৯) বলেন, কুমারিল চার্বাকপন্থীদের কাছ থেকে একটা আপত্তি আশঙ্কা করেছেন- বৌদ্ধরা বুদ্ধকে সর্বজ্ঞ মনে করেন, আর মীমাংসকরা মনে করেন বেদ অপৌরুষেয়। দুই মতই সমান নির্যুক্তিক। তা হলে বুদ্ধবাণী ত্যাগ করে বেদবাণী গ্রহণ করবো কেন ? তাই কুমারিলকে একদিকে সর্বজ্ঞতা খণ্ডন করতে হয়েছে। অন্যদিকে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করতে হয়েছে।
যদিও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা বুদ্ধিমান মীমাংসকদের যুক্তিহীন গোঁড়ামির একটা বড় নজির বলে মনে করা হয়, তবু সর্বজ্ঞতা খণ্ডনে কুমারিলের সাফল্য অসামান্য। কুমারিলের সর্বজ্ঞত্ব-খণ্ডন প্রণালি গভীরভাবে অনুধাবন করলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে উপস্থাপিত সর্বজ্ঞত্ব-সমর্থক যুক্তিগুলি অত্যন্ত দুর্বল বলে প্রতিপন্ন হয়। তাই কুমারিলের যুক্তিগুলি বিশ্লেষণনির্ভর।
.
কুমারিলের সর্বজ্ঞতা-খণ্ডন :
সর্বজ্ঞ মানে যিনি বিশ্বজগতের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবকিছু জানেন। কী করে জানেন ? আমরা মানুষ, তাই মানুষ যেভাবে জানে, সেভাবে জানার বাইরে অন্য কোনো অতিমানবিক উপায় যদি থাকে তা আমরা কী করে জানবো, আর না জানলে কী করে বলবো আমাদের মানববুদ্ধির অগোচরে এক সবজান্তা অতিমানব আছেন যিনি কোনো অতিমানবিক উপায়ে বিশ্বের প্রতিটি ধূলিকণা প্রতিটি অণুপরমাণু ও প্রতিটি বীজাণু পর্যন্ত আপন নখদর্পণে প্রত্যক্ষ করেন। জানার উপায়কে বলে প্রমাণ, যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপায় আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়, চোখ, কান, জিহ্বা প্রভৃতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে বলে প্রত্যক্ষপ্রমাণ যা দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমানগ্রাহী, যেমন চক্ষু শুধু বর্তমান বস্তুকেই গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অতিদূর স্থিত, অন্তরালিত, অতীত বা ভবিষ্যৎ বস্তুকে গ্রহণ করতে পারে না। এখন যদি কেউ সর্বজ্ঞ হন, তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু প্রত্যক্ষ করবেন ?
.
মানুষের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা প্রকৃতির নিয়মে সীমাবদ্ধ। তাই কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সবকিছুই বিশ্বের সবকিছু জানা সম্ভব নয়। ‘সব’ ইন্দ্রিয়ের ‘অবিষয়’ অর্থাৎ অগোচর- এটাই স্বভাবনিয়ম বা প্রাকৃতিক নিয়ম। কেউ সর্বজ্ঞ হলে তাকে হতে হবে এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম। আমরা কিন্তু ব্যতিক্রম নই। তাহলে আমরা কী করে বুঝবো যে এমন কোনো মহাপুরুষ আছেন যিনি স্বভাবনিয়মের ব্যতিক্রম ? বুঝতে হলে আমাদেরও ব্যতিক্রম হতে হবে। তাই কুমারিল বিদ্রূপ করে বলেছেন ( শ্লোকবার্তিক-২/১২২)- যিনি কোনো সর্বজ্ঞ পুরুষ আছে বলে কল্পনা করেন তিনি বোধহয় চোখ দিয়ে বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ চোখের দ্বারা দেখে, কানের দ্বারা শোনে, জিহ্বার দ্বারা রসগ্রহণ- এই প্রাকৃতিক নিয়মের উর্ধ্বে তিনি বিচরণ করেন। একথাই কুমারিল আরেকটি সাধারণ সূত্রাকারে উপস্থিত করেছেন-
‘য এব স্যাদসর্বজ্ঞঃ স সর্বজ্ঞং ন বুধ্যতে।’- ( শ্লোকবার্তিক- ২/১৩৫)
অর্থাৎ : যে নিজে অসর্বজ্ঞ সে অন্য কাউকে সর্বজ্ঞ বলে সাব্যস্ত করতে পারে না।
কুমারিল বলতে চাইছেন- অমুক মহাপুরুষ চোখ দিয়ে তামাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখতে পান, কথাটা আমি কী করে জানবো যদি না আমিও মহাপুরুষের মতো দেখতে পাই। তাহলে আমাকেও প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হতে হবে। এখানে কুমারিলের আলোচনার প্রসঙ্গ অবশ্য বুদ্ধের সর্বজ্ঞত্ব। তাই বলছেন- ধরে নিলাম বুদ্ধ ছিলেন সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ। শিষ্যরা কী করে জানলেন যে গুরু সব কিছু জানেন। শিষ্য নিজে সর্বজ্ঞ নন। সকল অণু, পরমাণু, বীজাণু ও কীটপতঙ্গের সংখ্যা সহ বিশ্বের সবকিছু যদি শিষ্যের জ্ঞানগোচর না হয় তবে শিষ্য কী করে সাব্যস্ত করলেন যে ঐ সকল বস্তুই গুরুর জ্ঞানগোচর। যে সকল বস্তু মিলে ‘সর্ব’-ব্রহ্মাণ্ড হয়, সে ‘সব’ যদি শিষ্য না জানেন তা হলে শিষ্য কী করে নির্ণয় করবেন যে তার গুরু সবটাই জানেন অথবা ‘সব’-এর চেয়ে কিছু কম জানেন। ধরুন শিষ্যটিও সর্বজ্ঞ। এখন শিষ্যটিকে সর্বজ্ঞ বলে জানতে হলে আর একজন সর্বজ্ঞের দরকার হবে। এভাবে একে একে আমাদের সকলকেই সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ হতে হবে। বুদ্ধবিদ্বেষী কুমারিল আসলে ‘সর্বজ্ঞ’-শব্দটির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করে বুদ্ধশিষ্যদের উপহাস করেছেন।
.
নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধমতে সর্বজ্ঞেয় শব্দটির প্রকৃত অর্থ ভিন্ন। সুবিখ্যাত বৌদ্ধদার্শনিকরা কিন্তু ‘সর্বজ্ঞ’ শব্দটি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেননি। এ সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধদার্শনিক ধর্মকীর্তির ‘প্রমাণবার্তিক’ গ্রন্থের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য-
‘সর্বজ্ঞ হতে হলে বিশ্বে কত হাজার কোটি কীট আছে তা জানার প্রয়োজন নেই। মানুষের কল্যাণের জন্য কী করা উচিত, এ জ্ঞান যার আছে তিনিই সর্বজ্ঞ। বিচার করুন, ভগবান তথাগতের এ জ্ঞান আছে কিনা, এবং এ জ্ঞানকে তিনি মানুষের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত করেছেন কিনা। মানুষের দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ প্রতিরোধের উপায় এবং দুঃখের প্রতিরোধ- এই চারটি ‘আর্যসত্য’ হলো ধর্মের মূল তত্ত্ব। এই তত্ত্ব আয়ত্ব করে যিনি মানুষের সুখ ও হিতসাধনে ব্যাপৃত হন সেই কল্যানব্রতী মহাপুরুষকেই আমরা বলি ‘সর্বজ্ঞ’। তথাগতের দৃষ্টি কতোটা দূরভেদী তা জানার প্রয়োজন নেই, মানুষের মঙ্গলের মূল তত্ত্বটি তার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে কিনা সেটাই আসল কথা। দূরদর্শী বলেই যদি কোনো ব্যক্তি প্রমাণ হন তাহলে শকুনের মতো প্রমাণপুরুষ আর কে আছে ? শূন্যে ভেসে ভেসে কতো উঁচু থেকে ডাঙায় বা জলে পড়ে থাকা মড়াটাকে দেখতে পায়। তবে আসুন আমরা সবাই মিলে শকুনের উপাসনা করি।’ (সূত্র: হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়/ বৈদিকধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন, পৃষ্ঠা-১৮১)
.
তবে ঈশ্বরবিশ্বাসীরা কিন্তু ঈশ্বরকে আক্ষরিক অর্থেই সর্বজ্ঞ মনে করেন, অর্থাৎ তাদের মতে ঈশ্বর বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রত্যক্ষ করেন। যোগভাষ্যকার বেদব্যাস ঈশ্বরানুমান প্রণালী প্রমাণ করেন বিচিত্রভাবে-
কেউ স্বল্পজ্ঞানী, কেউ তার তুলনায় অধিকতর জ্ঞানী, কেউ আরও অধিকতর জ্ঞানী; সুতরাং এমন একজন আছেন যিনি অধিকতম জ্ঞানী। ইনি হলেন নিরতিশয় জ্ঞানী, যার জ্ঞানের চেয়ে বেশি জ্ঞান আর সম্ভব নয়; সুতরং তিনি সর্বজ্ঞ। সবজান্তার ওপর আর কোনো জ্ঞানী থাকা সম্ভব নয়। এহেন সর্বজ্ঞ পুরুষই হলেন ঈশ্বর। দশ বিশজন সর্বজ্ঞ থাকতে বাধা কী ? বাধা শাস্ত্র। শাস্ত্র এক ঈশ্বরের কথাই বলেছে।- (যোগভাষ্য-১/২৫)
.
মানুষের জ্ঞানের তারতম্য থেকে ‘অমানুষ’ সর্বজ্ঞ পুরুষে পৌঁছানোর অনুমান-প্রণালীটি কুমারিলের দৃষ্টি এড়ায়নি। (জ্ঞাতা মানুষের) প্রমাতৃভেদে প্রত্যক্ষদর্শনের তারতম্য দেখা যায়। কেউ কেউ অধিক দূরস্থিত বা অধিক সূক্ষ্ম বস্তুও দেখতে পায়, কেউ আবার তা পারে না। তেমনি লৌকিক বা শাস্ত্রীয় বিষয়ে কারুর জ্ঞান অপরের তুলনায় অনেক বেশি। এই তারতম্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে এমন কোনো বরিষ্ঠ পুরুষ আছেন যার জ্ঞান সর্বাধিক। সর্বাধিক জ্ঞান হলো সর্ববিষয়ক জ্ঞান। এহেন সর্ববিষয়ক-জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষই হলেন সর্বজ্ঞ।
ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা যে প্রাকৃতিক নিয়মে সীমাবদ্ধ, স্বাভাবিক অবস্থায় তার ব্যত্যয় ঘটে না, সর্বজ্ঞত্ব-খণ্ডনে কুমারিল এই স্বভাবনিয়ম প্রয়োগ করেই বলেন-
‘যথাপ্যতিশয়ো দৃষ্টঃ স স্বার্থানতিলঙ্ঘনাত্ ।
দূরসূক্ষ্মাদিদৃষ্টেঃ স্যান্ন রূপে শ্রোত্রবৃত্তিতা।।’- ( শ্লোকবার্তিক-২/১১৪, পার্থসারথির টীকা)
অর্থাৎ : দূরসূক্ষ্মাদি বস্তুদর্শনে কোনো ব্যক্তির যে জ্ঞানাধিক্য পরিলক্ষিত হয় তা কিন্তু জ্ঞান ও বিষয়ের সুনির্দিষ্ট স্বাভাবিক সম্বন্ধকে লঙ্ঘন করে না, যেমন কোনো সমধিক জ্ঞানী ব্যক্তিও কর্ণের দ্বারা বস্তুর রূপ গ্রহণ করে না।
এরপর কুমারিলের যুক্তি হলো, যদি বলেন সর্বজ্ঞ পুরুষ প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা নন, তিনি সব নিয়ম লঙ্ঘন করে সবকিছু দেখতে পান তা হলেও একটা দুরুত্তর প্রশ্ন থেকে যায়। সর্বজ্ঞ পুরুষ নাকি অন্তহীন ভবিষ্যৎকেও বর্তমানের মতো স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেন। এ ধরনের উদ্ভট দাবি কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারাও সমর্থিত হতে পারে না। যা এখন পর্যন্ত বিশ্বে কোথাও জন্মগ্রহণই করেনি, যা এখনও কোথাও নেই সেই না-থাকা বস্তুগুলিকেও এখনই কেউ আক্ষরিক অর্থে প্রত্যক্ষ করছে, কেবল কল্পনা করছে না- এরকমের বক্তব্য প্রমত্তের প্রলাপ ছাড়া আর কী হতে পারে ? তাই কুমারিল বলছেন- ‘ভবিষ্যৎ বস্তুর জ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিন্দুমাত্র সামর্থ্যও পরিদৃষ্ট হয় না’- (শ্লোকবার্তিক-২/২১৫)।
যদি কোন সর্বজ্ঞ-বিশ্বাসী বলেন- সমগ্র ভবিষ্যৎ সর্বজ্ঞ পুরুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ধরা না পড়ুক, তিনি অনুমানের দ্বারা অনন্ত ভবিষ্যতের অনন্ত বস্তু জানতে পারেন, তবু কিন্তু সর্বজ্ঞতা সম্ভব নয়। অনুমান জ্ঞান হয় সামান্যাকারে। আমরা বিশ্বাস করি সকল মানুষ মরণশীল। এই সাধারণ সূত্র দেখে আমরাও অনুমান করতে পারি বর্তমানে জীবিত কোনো ব্যক্তিবিশেষও অমর নয়, একদিন তাকে মরতেই হবে। ‘সকল মানুষ মরণশীল’ এই সাধারণ সূত্রটি যখন আমরা জানি তখন অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষের অনন্ত কোটি চিতার আগুন সারিবদ্ধভাবে একে একে আমাদের কল্পনার আকাশে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে না। তিনকালের কোন লোকটি কীভাবে কোথায় কখন মরেছে বা মরবে তা কিন্তু আমাদের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। আমরা প্রত্যেকেই একদিন মরবো, কারণ আমরা মানুষ এবং মানুষমাত্রেই মরণশীল- এ ধারণাটা হয় সামান্যাকারে বা সাধারণভাবে। প্রত্যেকটি মানুষকে আলাদা করে একে একে গুনে গুনে হয় না, কে কোথায় কখন কীভাবে মরবে তাও জানা যায় না। সর্বজ্ঞ হতে হলে কিন্তু এসব কিছুই বিশেষভাবে, বিভক্তরূপে আলাদা আলাদা করে জানতে হবে। না হলে আমাদেরই বা সর্বজ্ঞ হতে বাধা কোথায়। একথাই কুমারিল সংক্ষেপে বলেছেন-
‘ভবিষ্যতি ন দৃষ্টং চ প্রত্যক্ষস্য মনাগপি।
সামর্থ্যং, নানুমানাদের্লিঙ্গাদিরহিতে ক্বচিত্ ।।’- (শ্লোকবার্তিক-২/১১৫)
অর্থাৎ : ভবিষ্যৎ বস্তুর জ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিন্দুমাত্র সামর্থ্যও পরিদৃষ্ট হয় না। বিশ্বের সকল বস্তু সম্বন্ধে অনুমান করার কোনো ‘হেতু’ বা সূচক চিহ্ন নেই।
.
কুমারিলের এ সকল আপত্তির পিছনে রয়েছে আসলে ন্যায়শাস্ত্রেও অনুমানতত্ত্বের অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা। আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানা থেকে অজানার দিকে কতোটা উল্লম্ফন করা যুক্তিগত এই পরিমিতিবোধটুকু না থাকলে যে কোনো অসম্ভবকে সম্ভব বলে প্রতিপন্ন করার জন্য বল্গাহীন কল্পনার আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। যে কোনো আজব কল্পনাকে সজীব করে তোলা যেতে পারে।
মানুষের জ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। কিন্তু এই উৎকর্ষ থেকে কোনো সর্বজ্ঞ পুরুষে পৌঁছানোর যৌক্তিক প্রয়োজন নেই।… বুদ্ধের সর্বজ্ঞতার বিরুদ্ধে কুমারিল যে কঠোর যুক্তিসমূহ উপস্থিত করেছেন ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার বিরুদ্ধেও সে যুক্তিসমূহ সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই সর্বজ্ঞতা খণ্ডনের দ্বারা পরোক্ষভাবে বা প্রকারান্তরে ঈশ্বরও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, কারণ সর্বজ্ঞ পুরুষ না হলে ঈশ্বর ঈশ্বর হতে পারে না।– (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়/ বৈদিকধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন, পৃষ্ঠা-১৮৩)
তাই কুমারিল যখন সরাসরি ঈশ্বর খণ্ডন করেছেন তখন আর তিনি আলাদা করে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা খণ্ডন করেন নি। সেখানে তিনি নতুন নতুন যুক্তির অবতারণা করেছেন, যে যুক্তির গুরুত্ব অসাধারণ।
.
কুমারিলের ঈশ্বর-খণ্ডন :
কুমারিল কর্তৃক ঈশ্বর খণ্ডনের প্রসঙ্গ হলো শব্দার্থ সম্বন্ধের নিত্যতা প্রতিপাদন। বর্ণের কূটস্থ বা বিকারবিহীন নিত্যতা থেকে শব্দ ও বেদবাক্যের নিত্যতায় উত্তরণের বিষয়টি শব্দ-প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে। শব্দ-প্রমাণের মাধ্যমে বেদকে অপৌরুষেয় প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কুমারিলের যুক্তি অনুসরণ করলে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব শুধুমাত্র প্রবাহ-নিত্যতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য, যে নিত্যতাকে পার্থসারথি মিশ্র বলেছেন ‘অনিদংপ্রাথম্য’, অর্থাৎ ইনিই প্রথম বেদবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, এই হলো বেদের প্রথম আবির্ভাব- এমন কথা কেউ বলতে পারে না, তাই বেদ নিত্য অপৌরুষেয়। মীমাংসা-মতে বেদের অভ্রান্তত্ব নির্ভর করছে অপৌরুষেয়ত্বের ওপর। এই অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণ করবার জন্য মীমাংসকরা প্রবাহ-নিত্যতার নিতান্ত ভঙ্গুর যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করলেও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধির অন্যদিকে কুমারিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুক্তিতে কঠোর ও অবিচল। এক্ষেত্রে বেদ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের রচনা বলে মেনে নিলে কী হতো ?
এ বিষয়ে কুমারিল বলছেন, পূর্বপক্ষবাদী হয়তো দাবি করতে পারেন যে জগৎ-স্রষ্টার কথা স্বীকার করলেও বেদের প্রামাণ্য ক্ষুণ্ন হয় না; কিন্তু তবুও এ জাতীয় স্রষ্টা বা ঈশ্বরের কথা স্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না, কেননা তাঁর সত্তা সম্ভব নয় এবং সৃষ্টির কল্পনাও অসম্ভব। অতএব আমরা মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর এবং সৃষ্টি স্বীকার করি না।
.
কুমারিল বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির পরিকল্পনা নিয়ে নানা রকম বিদ্রূপ করেছেন। তিনি বলেন, যদি বলো কোনো এককালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিলো তাহলে প্রশ্ন করবো, সৃষ্টির আগে বিশ্বের অবস্থা কী ছিলো ?
ঈশ্বরবাদী তখন বলবেন, তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বলা আছে ‘সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতি একাই ছিলেন’- (তৈত্তিরীয়-সংহিতা-২/১/১)। আবার ঋগ্বেদের প্রজাপতি-সূক্তেও বলা হয়েছে-
‘হিরণ্যগর্ভঃসমবর্ততাগ্রে ভূবস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।’- (ঋগ্বেদ-১০/১২১/১)
অর্থাৎ : সর্ব প্রথমে কেবল (প্রজাপতি) হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত মাত্রই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হলেন। তিনি এ পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করলেন।
কুমারিলের প্রশ্ন, সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বই যদি তখন না থাকে তাহলে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিই বা কোথায় ছিলেন ? তাঁর রূপই বা কী রকম ছিলো ? থাকার জন্য কোনো অধিকরণ বা আশ্রয় প্রয়োজন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কুমারিল এই যে গুরুতর আপত্তি তুললেন সে আপত্তি ঋগ্বেদেই রয়েছে (১০/৮১)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একাশি সূক্তে (বিশ্বকর্মা-সূক্ত) বলা হয়েছে-
‘কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ।
ষতো ভূমিং জনয়ন্বিশ্বকর্মা বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ।।’- (ঋগ্বেদ-১০/৮১/২)
অর্থাৎ : সৃষ্টিকালে তাঁর অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়স্থল কী ছিলো ? কোন স্থান হতে কিরূপে তিনি সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করলেন ? সে বিশ্বকর্মা, বিশ্বদর্শনকারী দেব কোন স্থান থেকে পৃথিবী নির্মাণ-পূর্বক প্রকাণ্ড আকাশকে উপরে বিস্তারিত করে দিলেন ?
তা ছাড়া সৃষ্টির জন্য উপাদানগুলি তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন ? তিনি ছাড়া আর কিছুই তো ছিলো না-
‘কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ।।’- (ঋগ্বেদ-১০/৮১/৪)
অর্থাৎ : সে কোন বন ? কোন বৃক্ষের কাষ্ঠ ? যা হতে দ্যুলোক ও ভূলোক গঠন করা হয়েছে ? হে বিদ্বানগণ ! তোমরা একবার আপন আপন মনে জিজ্ঞাসা করে দেখ, দেখ তিনি কিসের উপর দাঁড়িয়ে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন ?
তবে ঈশ্বরবাদীর পক্ষ হয়ে বৈদিক ঋষিই তার উত্তর দেন-
‘বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ।।’- (ঋগ্বেদ-১০/৮১/৩)
অর্থাৎ : সে এক প্রভু, তাঁর সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ, ইনি দু হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্বক নির্বাণ করেন, তাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা হয়।
তাহলেও প্রশ্ন, এই যে সর্বত্র তার চক্ষু, সর্বত্র তার মুখ, সর্বত্র তার বাহু, সর্বত্র তার পদ, কথাগুলি যদি আলংকারিক প্রয়োগ বলেও ধরা হয় তাহলেও ‘সর্বব্যাপী’ কথাটি নিরর্থক অথবা বিকল্পমাত্রে পর্যবসিত হতে বাধ্য। কারণ ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত ‘সর্ব’ বলে কিছুই ছিলো না। সুতরাং ‘সর্বব্যাপী’ কথাটি বন্ধ্যাপুত্রের মতো সমগোত্রীয় অর্থহীন।
কুমারিল বলেন, যদি বলো ঈশ্বর তার ইচ্ছাবলেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, দেহবিশিষ্ট চেতনপদার্থেরই ইচ্ছা থাকতে পারে। ঈশ্বর তো অশরীরী। যদি বলো ঈশ্বরেরও দেহ আছে, তবে শরীরের উপাদানগুলি কোথা থেকে এলো ? তবে কি ঈশ্বরের দেহ তৈরি করার উপাদানগুলি আগে থেকেই ছিলো ? অর্থাৎ ঈশ্বরের পূর্বেই জগৎ ছিলো ? তাহলে বলতে হবে জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করেনি।
.
কুমারিল আবার প্রশ্ন করেন, সৃষ্টির পূর্বে তো কোনো মানুষেরই অবস্থান সম্ভব নয়; তাই তোমাদের মতে প্রজাপতি তখন যে উপস্থিত ছিলেন এ কথা কার পক্ষেই বা জানা সম্ভব ? এবং কেই বা পরবর্তীকালে সৃষ্ট মানুষদের কাছে প্রজাপতির কথা পৌঁছে দিতে পারেন ? যদি বলো, প্রজাপতির পক্ষে কোনো মানুষেরই প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্ভব নয়, তাহলে প্রশ্ন করবো তাঁর যে একান্তই কোনো রকম অস্তিত্ব আছে সে কথাই বা জানা গেলো কীভাবে ? তোমাদের মতে কোনো এককালে বিশ্বের সৃষ্টি বা শুরু হয়েছিলো; কিন্তু তা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে ? প্রজাপতির ইচ্ছায় সৃষ্টি শুরু হলো ? কিন্তু সে-কথা তোমরা কী করে বলবে ? কেননা, তোমাদের মতেই স্রষ্টা দেহ-বিশিষ্ট নন; এবং দেহ ছাড়া ইচ্ছা সম্ভবই নয়। তাই দেহহীন স্রষ্টার পক্ষে সৃষ্টি করার ইচ্ছাও অসম্ভব। যদি বলো, স্রষ্টার দেহ আছে, তাহলে সেই দেহটিকেও তো তাঁরই সৃষ্টি বলতে পারো না। অতএব তাঁর দেহ সৃষ্টির জন্য আর একটি স্রষ্টার কথা, আবার তাঁরও দেহ সৃষ্টির জন্য আর একটি স্রষ্টার কথা- এইভাবে অবিশ্রাম ভেবে যেতে হবে। স্রষ্টার দেহকে নিত্য বা অনাদিও বলতে পারো না, কেননা সৃষ্টির পূর্বে ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি দেহের উপাদানই যখন নেই তখন কী দিয়ে তাঁর দেহ নির্মিত হতে পারে ?
তাছাড়া, প্রাণীদের পক্ষে নানা রকম জ্বালা-যন্ত্রণায় পূর্ণ এই পৃথিবীটি সৃষ্টি করবার ইচ্ছেই বা তাঁর হলো কেন ? এ-কথাও বলতে পারো না যে প্রাণীদের কর্মফলের দরুনই পৃথিবীতে এই সব জ্বালা-যন্ত্রণা। কেননা, সৃষ্টির পূর্বে এ জাতীয় কর্মফল সম্ভবই নয়। অতএব প্রাণীদের কর্মফল অনুসারে স্রষ্টার পক্ষে পৃথিবী সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়।
.
কুমারিল বলেন, উপকরণাদি ব্যতিরেকেও সৃষ্টি সম্ভব নয় এবং সৃষ্টির পূর্বে এ-জাতীয় উপকরণ বলে কিছুর অস্তিত্ব অসম্ভব। উর্ণনাভ বা মাকড়সার জালও উপাদানহীন সৃষ্টি নয়, কেননা ভক্ষিত পতঙ্গ থেকে মাকড়সার লালা উৎপাদন হয় এবং জালের উপাদান হিসেবে এই লালা ব্যবহৃত। আর এ কথাও বলা যায় না যে, করুণা বা দায় থেকেই স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন; কেননা, সৃষ্টির আগে কোনো প্রাণীই ছিলো না, অতএব করুণা বা অনুকম্পা দেখাবার মতো কোনো জীবই ছিলো না, কাকে অনুকম্পা দেখাবেন ? যখন করুণার কোনো পাত্রই নেই তখন করুণাও সম্ভব নয়। তাছাড়া করুণা বা দয়া-পরবশ হয়ে সৃষ্টি করলে তিনি শুধুমাত্র সুখী ব্যক্তিই সৃষ্টি করতেন। যদি বলো, কিছুটা দুঃখ না থাকলে জগতের সৃষ্টি বা স্থিতি সম্ভব নয়, তাহলে উত্তরে বলবো, তোমাদের মতে সবই তো স্রষ্টার শুধুমাত্র ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল, তাই তার পক্ষে আবার অসম্ভব কী হতে পারে ? আর সৃষ্টির জন্য তাঁকেও যদি নিয়মাদির উপর নির্ভরশীলই হতে হয় তাহলে তাঁর আবার স্বাধীনতা কোথায় ? তোমাদের মতে তাঁর মধ্যে সৃষ্টির ইচ্ছা জেগেছিলো; কিন্তু বলতে পারো কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য তাঁর এই ইচ্ছা জেগেছিলো- এমন কোন্ উদ্দেশ্যই বা সম্ভব হতে পারে যা কিনা সৃষ্টি-ব্যতিরেকে চরিতার্থ হওয়া অসম্ভব ? নির্বোধও উদ্দেশ্যবিহীন কাজ করে না। অতএব তিনি যদি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে তাঁর বুদ্ধিকে নিষ্ফল বলতে হবে। যদি বলো, এই সৃষ্টি তাঁর লীলা- প্রমোদ বা বিলাসমাত্র, তাহলে তাঁকে আর সদানন্দ বা চিরসন্তুষ্ট বলতে পারো না, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে তিনি নিশ্চয়ই প্রমোদের অভাব অনুভব করেছিলেন, অতএব তখন তাঁর সন্তুষ্টির অভাব ছিলো। তাছাড়া সৃষ্টি-ব্যাপারে যে পরিমাণ দুর্ভোগ ও পরিশ্রম প্রয়োজন তার তুলনায় প্রমোদ আর কতটুকুই বা ? আর সৃষ্টি যদি প্রমোদের জন্যই হয় তাহলে তোমরা যে প্রলয়ের কথা বলো তারই বা ব্যাখ্যা কী ?
আর সর্বোপরি কথা হলো, কারুর পক্ষেই এ জাতীয় স্রষ্টাকে জানা সম্ভব নয়। যদিই মানা যায় যে তাঁর রূপ সংক্রান্ত অবগতি সম্ভব, তবুও তিনিই যে স্রষ্টা এ বিষয়ে জ্ঞান অসম্ভব। সৃষ্টির শৈশবে যে সব প্রাণীদের আবির্ভাব তাদের পক্ষে কতটুকুই বা বোধ সম্ভবপর ? অতএব, কীভাবে তাদের জন্ম হলো এবং সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা কী ছিলো- এ সব কথা তাদের পক্ষে বুঝতে পারা অসম্ভব, অর্থাৎ বুঝতে পারা অসম্ভব যে প্রজাপতিই সৃষ্টি করেছিলেন। যদি বলো, প্রজাপতিই সেই প্রাণীদের বলে দিয়েছিলেন যে, তিনিই স্রষ্টা তাহলেও তাদের পক্ষে তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন সম্ভব নয়; কেননা, এমনও তো হতে পারে যে, তিনি নিজের শক্তিসংক্রান্ত শুধু দম্ভই প্রকাশ করেছেন।
.
সাধারণ লোকের ধারণায়, প্রজাপতি যে স্রষ্টা এ-কথা বেদ-এ আছে। কিন্তু কুমারিল বলছেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আসলে কয়েকটি বিধির প্রশংসামূলক বাক্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা থেকে এ ধারণার উদ্ভব- কোনো একটি বাক্যের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে সঙ্গতি ব্যতিরেকে ব্যাখ্যা করতে গেলে এ জাতীয় ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। কুমারিল আরো দাবি করছেন, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী থেকেও প্রমাণ হয় না যে, প্রজাপতিই স্রষ্টা। আসলে নিছক কাহিনী হিসেবে কোনো কাহিনীই সার্থক নয়; অতএব তথাকথিত কাহিনীগুলিকে নিছক কাহিনী হিসেবে না বুঝে প্রকৃতপক্ষে বিধি বা যজ্ঞকর্মের প্রশংসা বা অর্থবাদ হিসেবেই বুঝবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।
.
উপরিউক্ত যুক্তিগুলির পর কুমারিল বিশেষ করে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি-প্রলয় সংক্রান্ত ন্যায়-বৈশেষিক মতের সমালোচনা করেছেন।
.
কুমারিল-কর্তৃক ঈশ্বর-অস্তিত্ব-সংক্রান্ত ন্যায়-বৈশেষিক মত খণ্ডন :
ন্যায়-বৈশেষিকরা ঈশ্বরকে কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ বলে স্বীকার করেন। তাদের মতে, জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বনির্ভরতা নেই। জীবের কর্ম ও অদৃষ্টের ওপর ঈশ্বরকে নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া নিমিত্ত-কারণ কখনো উপাদান-কারণ হতে পারে না। ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা। কুম্ভকার মাটি দিয়ে ঘট তৈরি করে, কুম্ভকার কখনো নিজেই মৃত্তিকা হতে পারে না। কুম্ভকার ঘটের নির্মাতা, মাটি উপাদান। জগতের উপাদান পরমাণু, ঈশ্বর পরমাণুর সাহায্যে জগৎ নির্মাণ করেন জীবের কর্ম ও অদৃষ্ট অনুসারে।
.
কুমারিল এখানে বলতে চান যে, প্রথমত, বৈশেষিকরা যে মনে করেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় অকস্মাৎ সৃষ্টি হয় তা সম্ভব নয়; কেননা ঘট প্রভৃতি নির্মাণের দৃষ্টান্তে দেখা যায় একটি বস্তুর নির্মাণ ক্রমপদ্ধতি মাত্র। দ্বিতীয়ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় স্বীকার করা যায় না, কেননা তার কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া প্রলয়ের কথা স্বীকার করলে মানতে হবে যে ঈশ্বরের মনে প্রলয়ের ইচ্ছা জাগে; কিন্তু এ জাতীয় ইচ্ছায় লাভ কী ? অর্থাৎ বুদ্ধিমান স্রষ্টার পক্ষেই নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করবার ইচ্ছা জাগা সম্ভব নয়।
বৈশেষিকরা বলেন, প্রলয়কালে মানবাত্মার ধর্মাধর্ম নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কুমারিল বলছেন, তা কোনোমতেই সম্ভব নয়। প্রথমত কৃতকর্মের ফলাফল অবশ্যম্ভাবী; তাই এমন কোনো অবস্থা সম্ভবই নয় যখন কৃতকর্মের পরিণাম স্থগিত থাকবে। বৈশেষিকরা বলবেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা নামক কর্মটির দরুন বাকি সকলের কর্মফল এইভাবে স্থগিত থাকে; কিন্তু তাও সম্ভব নয়, কারণ একজনের একটি কর্মের ফলে বাকি সকলের কর্মফল স্থগিত থাকতে পারে না।
যদি বলা হয়, প্রলয়কালে সকলের ধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহলে কুমারিল বলছেন, আর কখনো সৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকবে না, কেননা সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কর্মগুলিকে আবার কীভাবে সঞ্জীবিত করা যাবে ?
বৈশেষিকরা যদি বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তা সম্ভব হতে পারে, তাহলে, কুমারিল বলছেন, শুধু এই ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলাই তো যথেষ্ট- বৈশেষিকরা আবার কেন সৃষ্টির জন্য ধর্মাধর্মের কথা তোলেন ? তাছাড়া, ঈশ্বরের ইচ্ছাও সম্পূর্ণ অকারণ হতে পারে না; এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার কারণ হিসেবে যদি কিছু স্বীকার করা হয় তাহলে সেই কারণটির সাহায্যেই তো সৃষ্টির ব্যাখ্যা সম্ভব, তদুপরি ঈশ্বর মানার প্রয়োজন কী ?
.
ন্যায়-বৈশেষিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে বলেন, গৃহাদির দৃষ্টান্তে দেখা যায় বিভিন্ন অবয়ব দ্বারা গঠিত বস্তুর উৎপত্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণব্যতীত সম্ভব নয়; অতএব অবয়ব-বিশিষ্ট মানবদেহের নিয়ন্তা বা নিয়ন্ত্রণ-কর্তা হিসেবেও বুদ্ধিমান ঈশ্বর অনুমেয়।
কিন্তু কুমারিল বলছেন, এই বুদ্ধিমান নিয়ন্তা অর্থে ঈশ্বরের কথা বাহুল্য মাত্র। কেননা সকলেই জানে যে মানবাদি বুদ্ধিমান জীবের নিয়ন্ত্রণ ফলেই পৃথিবীতে যাবতীয় উৎপাদন সম্ভব হয়; অতএব তার জন্য ঈশ্বর মানবার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া বৈশেষিকরা যে বলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় আকস্মিকভাবে বা হঠাৎ জগৎ সৃষ্ট হয় তাও মানবার কারণ নেই; কেননা গৃহাদি নির্মাণের দৃষ্টান্তেই দেখা যায় কোনো কিছুই নির্মাণকর্তার ইচ্ছা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয় না।
.
বৈশেষিকরা বলেন, সকলের দেহই বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। কুমারিল বলছেন, কিন্তু এই যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর-দেহের নিয়ন্ত্রণকর্তা কে হবেন ? তথাকথিত ঈশ্বরের দেহও দেহ, এবং আমাদের দেহের মতোই অবয়ব-গঠিত; অতএব তারও কোনো নিয়ন্তা স্বীকার্য। যদি বলো, ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই নিয়ন্ত্রণের কারণ, তাহলে তোমাদের নিজেদেরই মূল যুক্তির বিরুদ্ধে যেতে হবে; কেননা তোমাদের মূল যুক্তি হলো, অবয়ব-গঠিত বস্তুর নিয়ন্তা হিসেবে স্বতন্ত্র কোনো বুদ্ধিমান অনুমেয়। তাছাড়া, ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারাই বা কীভাবে তাঁর দেহ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে ? কেননা, ঈশ্বর যদি তাঁর দেহ সৃষ্টি করতে চান তাহলে তাঁকে দেহীপূর্ব বা দেহবিহীন অবস্থাতেই এ প্রয়াস করতে হবে,- উক্ত প্রয়াসের পূর্বে তাঁর দেহের অস্তিত্বই সম্ভব নয়। এবং দেহবিহীন অবস্থায় ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়।
.
ঈশ্বরানুমানের জন্য বৈশেষিকরা কুম্ভকারের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেন- অবয়ব-বিশিষ্ট ঘট যেমন কুম্ভকারের সৃষ্টি, অবয়ব-বিশিষ্ট সমগ্র জাগতিক বস্তুও তেমনি ঈশ্বরের সৃষ্টি।
কিন্তু কুমারিল বলছেন, ঘটাদি যদি প্রকৃতপক্ষে কুম্ভকারের সৃষ্টি হয় তাহলে তা ঈশ্বরের সৃষ্টি হতে পারে না, অর্থাৎ সমস্ত জাগতিক বস্তুর স্রষ্টা ঈশ্বর হতে পারেন না; অপরপক্ষে যদি বলো, ঘটাদি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই সৃষ্টি- অর্থাৎ কুম্ভকারের সৃষ্টি নয়, তাহলে যে দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে তোমরা ঈশ্বর অনুমান করো সেইটিই প্রত্যাখ্যান করতে হবে- অর্থাৎ ঈশ্বরানুমানের দৃষ্টান্তাভাব ঘটবে। তাছাড়া, ঘটাদির সৃষ্টি সাধারণত যেভাবে কুম্ভকারাদির কীর্তি বলে স্বীকৃত হয়, বৈশেষিকরাও যদি তা স্বীকার করেন তাহলে তাঁদের সিদ্ধান্তই খণ্ডিত হবে; কেননা, তাহলে মানতে হবে জীবদেহ প্রভৃতিও মরলোকের জীবদেরই সৃষ্টি- ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়।
উত্তরে বৈশেষিকরা বলবেন, ঈশ্বরের সৃষ্টিকাজ কুম্ভকারাদির মতো নয়; বস্তুত ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হয়ে পরমাণুসমূহই সৃষ্টিকাজ সম্পাদন করে।
এক্ষেত্রে কুমারিল বলছেন, এ কথাও যুক্তিযুক্ত হবে না; কারণ পরমাণুসমূহ জড় বা অচেতন, অতএব তাদের পক্ষে ঈশ্বরেচ্ছা অনুসারে কোনো কাজ করাই সম্ভব নয়; কেননা অচেতন পরমাণুর পক্ষে ঈশ্বরেচ্ছার অবগতিই সম্ভব নয়।
.
ঈশ্বর এবং সৃষ্টি-প্রলয় সংক্রান্ত ন্যায়-বৈশেষিক মত খণ্ডন করেই কুমারিল ক্ষান্ত নন; এই প্রসঙ্গে তিনি বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্বও খণ্ডন করতে অগ্রসর হয়েছেন।
.
কুমারিল-কর্তৃক বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব খণ্ডন :
বৈদান্তিক-মতে নিত্য শুদ্ধ বা পরম পবিত্র পুরুষ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা থেকে জগতের সৃষ্টি। এ জগৎ ব্রহ্মময়। ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তবে বৈদান্তিকরা বলেন, পারমার্থিকভাবে সৃষ্টি-জগৎ মিথ্যা, জগতের কোন সত্তা নেই। তবুও উপাদানরূপ ব্যবহারিক সত্তা হিসেবে এই জগৎ যে আমরা দেখি তা অবিদ্যা বা মায়ার অধ্যাস, যার কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মতো জগৎ মিথ্যা অবভাস মাত্র। এই মতে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে জীবাত্মার পরমাত্মার সাথে একাত্ম হওয়াই মোক্ষ।
.
এ প্রেক্ষিতে কুমারিল বলেন, নিত্য শুদ্ধ বা পরম পবিত্র পুরুষ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা থেকেই যদি জগতের সৃষ্টি হয় তাহলে জগৎটিও তো পরম পবিত্র বা বিশুদ্ধ হবার কথা; কিন্তু জগতে পাপাদি দোষ বা অশুদ্ধতা বর্তমান। যদি বলা হয়, জগতের পাপাদি মানুষের অতীত অধর্মের ফল অতএব এগুলির জন্য নিত্যশুদ্ধ পরমাত্মা দায়ী নন, তাহলে মানুষের এই অধর্মও তো বিশুদ্ধ পরমাত্মারই নিয়ন্ত্রণাধীন; অতএব পরম পবিত্র পরমাত্মার পক্ষে মানবীয় ধর্মাধর্মকে সুনিয়ন্ত্রিত করে একটি পরম নিষ্কলুষ জগৎই সৃষ্টি করা উচিত ছিলো।
বৈদান্তিকরা যদি বলেন, জগৎ সৃষ্টির মূলে অবিদ্যা বা মায়া; কিন্তু একথা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। কেননা তাঁদের মতে সৃষ্টির সময় ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই সত্তা ছিলো না; আর যদি তাই-ই হয় তাহলে কিসের প্রভাবে এই অবিদ্যার পক্ষে কার্যকরি হওয়া সম্ভব ? একথা বলা যায় না যে ব্রহ্মই অবিদ্যাকে সৃষ্টিকার্যে প্রণোদিত করেন; কেননা মায়া হলো স্বপ্নের মতো মিথ্যা এবং ব্রহ্ম বিশুদ্ধ, অতএব মিথ্যা মায়ার পক্ষে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সম্ভব নয়।
.
বৈদান্তিকরা যদি বলেন, মায়ার উপর এই প্রভাব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মর নয়, তাহলে তাঁদের পক্ষে ব্রহ্ম ছাড়াও মায়াকে প্রভাবিত করবার জন্য আরো কিছুর সত্তা স্বীকার করতে হবে এবং এইভাবে অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করে দ্বৈতবাদী হতে হবে।
অপরপক্ষে, বৈদান্তিকরা যদি বলেন, মায়ার কার্যকারিতা স্বাভাবিক ও স্বতঃ-পরিচালিত অতএব তার উপর আর কিছুর প্রভাব নিষ্প্রয়োজন, তাহলে কিন্তু বৈদান্তিকদের পক্ষে মুক্তি বা মোক্ষর পরিকল্পনাই পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা, মায়া যদি স্বাভাবিক ও স্বাধীন অর্থাৎ অপর কিছুর প্রভাব-নিরপেক্ষ হয় তাহলে তার বিনাশও অসম্ভব বিবেচিত হতে বাধ্য। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অবিদ্যা-নিবৃত্তির একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞান; কিন্তু আত্মজ্ঞানই বা কীভাবে স্বাভাবিক ও স্বাধীন মায়াকে ধ্বংস করতে পারে ?
এই প্রসঙ্গে কুমারিল প্রচলিত সাংখ্য মতেরও সমালোচনা করেছেন।
.
কুমারিলের সাংখ্য-মত খণ্ডন :
সাংখ্যমতে জগতের মূল হচ্ছে পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ নিত্য ও উদাসীন, প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল। এই মতে বস্তু বা প্রকৃতির মূল উপাদান তিনটি গুণ- সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ- এই তিন গুণের সাম্যাবস্থায় থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষের যখন সংযোগ ঘটে তখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থার অবসান ঘটে। প্রকৃতির সাম্যাবস্থার অবসান না হলে জগতের অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। প্রকৃতি ও পুরুষের গুণ ভিন্নরূপ। প্রকৃতি অচেতন ও বোধ শক্তিহীন। অপরদিকে পুরুষ সচেতন বুদ্ধিমান কিন্তু নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি অচেতন ও বোধশক্তিহীন বলে সচেতন ও বুদ্ধিমান সত্তার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া তার কাজ করা সম্ভব নয়। পুরুষও নিষ্ক্রিয় বলে তার পক্ষে একা জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সে জন্য প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের যখন সংযোগ হয় তখনই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে জগতের অভিব্যক্তি ঘটে।
কুমারিল এই মতের আভ্যন্তরীণ অসম্ভাবনা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, প্রকৃতির সাম্যাবস্থা-বিচ্যুতি কীভাবে স্বীকৃত হতে পারে ? পুরুষ উদাসীন বলেই এ বিচ্যুতি তাঁর প্রভাবজনিত হতে পারে না। সাংখ্যমতাবলম্বীরা এ কথাও বলতে পারেন না যে, প্রকৃতির এই পরিবর্তনের মূলে জীবাত্মাদের কর্মের প্রভাব আছে; কেননা প্রথম সৃষ্টির পূর্বে এ জাতীয় কোনো কর্ম সম্ভব নয়, অতএব তার প্রভাবে প্রকৃতিতে পরিবর্তনও সম্ভব নয়।
.
উল্লেখ্য সাংখ্যমতের প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে মোক্ষতত্ত্বের দিক থেকে সাংখ্য ও বেদান্তর মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই; সাংখ্যমতেও সম্যক্জ্ঞান উপলব্ধিহেতুই মুক্তি বা মোক্ষ। তাই সাংখ্য-সমালোচনায় কুমারিল সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব সমালোচনা করলেও তিনি বিশেষ করে মোক্ষতত্ত্বই প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন এবং এ বিষয়ে কুমারিলের মূল যুক্তি হলো সম্যক্-জ্ঞানের উপলব্ধি থেকে মুক্তি সম্ভব নয়, কেননা বন্ধনের কারণ যদি কর্ম হয় তাহলে জ্ঞান কীভাবে এই কর্ম ধ্বংস করতে পারে ? স্বভাবতই এ-জাতীয় যুক্তি প্রচলিত সাংখ্যের সমালোচনা ছাড়াও বেদান্তমতেরও সমালোচনা।
.
পরিশেষে, মীমাংসকদের ঈশ্বর-খণ্ডন প্রসঙ্গে এ কথা বলা যায় যে, প্রভাকর ও কুমারিল উভয়েই সামগ্রিকভাবে জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় স্বীকার করেননি; বিভিন্ন জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ের মতে জাগতিক কারণ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। অতএব উভয়েই সৃষ্টি-প্রলয়ের কর্তা হিসেবে তথাকথিত সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বও সুদীর্ঘভাবে খণ্ডন করেছেন। বাহ্যবস্তুবাদী হিসেবে মীমাংসকরা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য তত্ত্বকে অস্বীকার করলেও ভারতীয় দর্শনে অন্যতম বাহ্যবস্তুবাদী দর্শন ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ে ঈশ্বর-প্রমাণের প্রচেষ্টা প্রসিদ্ধ হওয়ায় নিরীশ্বরবাদী মীমাংসকদের ঈশ্বর-খণ্ডন বিষয়ক যুক্তিগুলি প্রধানত ন্যায়-বৈশেষিকদের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য হয়েছে বেশি।
মীমাংসাশাস্ত্র দর্শন হলেও অনেকাংশে তা ব্যাকরণ এবং ন্যায়শাস্ত্রের বাদার্থ বা শব্দখণ্ডের মতো। পদশাস্ত্র হলো ব্যাকরণ এবং প্রমাণশাস্ত্র হলো ন্যায়। এই পদবাক্যপ্রমাণ-তত্ত্বজ্ঞ না হলে প্রাচীনকালে কেউ সুপণ্ডিত বলে বিবেচিত হতেন না। তাই প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও ব্যাখ্যায় এগুলির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। এ প্রেক্ষিতে আচার্যরা মীমাংসাকে বাক্যশাস্ত্রও বলে থাকেন। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের তাৎপর্যবোধে মীমাংসাশাস্ত্র উপায়স্বরূপ বলে এই শাস্ত্রকে ‘ন্যায়’ও বলা হতো। আচার্য্যরা বলে থাকেন-
‘নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিরনেনেতি ন্যায়ঃ।’
‘তত্ত্বপ্রকাশনং যুক্ত্যা ন্যায় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।’
অর্থাৎ : যে-শাস্ত্রের বা যুক্তির দ্বারা বিবক্ষিত অর্থ বুঝতে পারা যায়, তা-ই ‘ন্যায়’।
.
একারণেই হয়তো মীমাংসাশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ ন্যায়নামেও অভিহিত হয়েছে। যেমন- ‘ন্যায়কণিকা’, ‘ন্যায়মালা’, ‘ন্যায়প্রকাশ’ প্রভৃতি। পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসার এক একটি অধিকরণ বা বিচারের সিদ্ধান্তকেও ন্যায় বলা হতো। মীমাংসা এবং ন্যায়- এই দুটি শব্দই প্রাচীনকাল থেকে মীমাংসাদর্শনরূপ অর্থে প্রচলিত ছিলো। তার্কিক আচার্য্যরা ন্যায় শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে গ্রহণ করে তাঁদের দর্শনের নামই করেছিলেন ন্যায়দর্শন। পরবর্তীকালে যুক্তিমূলক দর্শনের একটি ভিন্ন প্রস্থান হিসেবে ন্যায়দর্শনের উৎপত্তি হওয়ায় ন্যায় বলতে এখন আর মীমাংসাদর্শনকে বোঝায় না।
একারণেই হয়তো মীমাংসাশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ ন্যায়নামেও অভিহিত হয়েছে। যেমন- ‘ন্যায়কণিকা’, ‘ন্যায়মালা’, ‘ন্যায়প্রকাশ’ প্রভৃতি। পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসার এক একটি অধিকরণ বা বিচারের সিদ্ধান্তকেও ন্যায় বলা হতো। মীমাংসা এবং ন্যায়- এই দুটি শব্দই প্রাচীনকাল থেকে মীমাংসাদর্শনরূপ অর্থে প্রচলিত ছিলো। তার্কিক আচার্য্যরা ন্যায় শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে গ্রহণ করে তাঁদের দর্শনের নামই করেছিলেন ন্যায়দর্শন। পরবর্তীকালে যুক্তিমূলক দর্শনের একটি ভিন্ন প্রস্থান হিসেবে ন্যায়দর্শনের উৎপত্তি হওয়ায় ন্যায় বলতে এখন আর মীমাংসাদর্শনকে বোঝায় না।
ব্যুৎপত্তিগতভাবে পাণিনিব্যাকরণ অনুসারে সংস্কৃত ‘মীমাংসা’ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে বিচারার্থক ‘মান্’-ধাতুর সাথে ‘সন্’ প্রত্যয় যোগে। ফলে ‘মীমাংসা’ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ‘বিচার’ বা ‘বিচারপূর্বক তত্ত্বনির্ণয়’। বিচার মানে কোন বিষয়ের বিচার। সেই বিষয়টি কী? মীমাংসক আচার্য্য কুমারিলভট্ট তাঁর শ্লোকবার্ত্তিকের শুরুতেই বলেছেন-
‘সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে?’- (শ্লোকবার্ত্তিক)
অর্থাৎ : সমস্ত শাস্ত্রেরই এবং যে-কোন কর্মেরই প্রয়োজন যে পর্যন্ত বলা না হয়, সে পর্যন্ত কে তা গ্রহণ করেন? প্রয়োজন না বুঝলে কেউ কোন কাজে প্রবৃত্ত হন না, কোন শাস্ত্রের চর্চাও করেন না।
এরপর কুমারিল আরও বলেন-
‘জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজন।।’- (শ্লোকবার্ত্তিক)
অর্থাৎ : যে শাস্ত্রের প্রয়োজন ও সম্বন্ধ জানা হয়েছে, সেই শাস্ত্র শ্রবণ করতে শ্রোতা প্রবৃত্ত হন। তাই গ্রন্থকারগণ শাস্ত্রের প্রারম্ভে শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং প্রয়োজনের সাথে সেই শাস্ত্রের সম্বন্ধও বলে থাকেন।
.
মীমাংসাশাস্ত্র বেদার্থের বিচারাত্মক ধর্মশাস্ত্রস্বরূপ। অর্থাৎ, মীমাংসা দর্শনে বিচারের কেন্দ্রস্থল হলো ধর্ম অর্থাৎ বেদপ্রতিপাদ্য অর্থ বা বিষয়। তাই মীমাংসা দর্শনের দর্শনের সূত্রকার জৈমিনি’র ‘মীমাংসাসূত্র’-এর শুরুতেই বলা হয়েছে-
মীমাংসাশাস্ত্র বেদার্থের বিচারাত্মক ধর্মশাস্ত্রস্বরূপ। অর্থাৎ, মীমাংসা দর্শনে বিচারের কেন্দ্রস্থল হলো ধর্ম অর্থাৎ বেদপ্রতিপাদ্য অর্থ বা বিষয়। তাই মীমাংসা দর্শনের দর্শনের সূত্রকার জৈমিনি’র ‘মীমাংসাসূত্র’-এর শুরুতেই বলা হয়েছে-
‘অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা’।- (মীমাংসাসূত্র : ১/১/১)
অর্থাৎ : এবার ধর্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হচ্ছে।
এখানে ধর্ম বলতে কোন ধর্মমত বোঝানো হয়নি বা সমাজকে ধারণ করে যে সব আচার-আচরণ, আইন-কানুন তাও নয়। জৈমিনি তাঁর দ্বিতীয় সূত্রে এই ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। আর ‘জিজ্ঞাসা’ শব্দের মুখ্য অর্থ ‘জানার ইচ্ছা’ হলেও এখানে গৃহীত হয়েছে গৌণ অর্থ ‘বিচার’। অর্থাৎ মীমাংসার মূল সুর হলো ধর্ম বা বেদার্থের বিচার। জৈমিনির দ্বিতীয় সূত্রটি হলো-
‘চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্ম’।- (মীমাংসাসূত্র : ১/১/২)অর্থাৎ : চোদনা লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন বা জ্ঞাপক যার সেই বিষয়ই ধর্ম।
‘চোদনা’ শব্দের মীমাংসাসম্মত অবিসংবাদিত অর্থ হলো প্রবর্তক বাক্য। তবে যে কোন প্রবর্তক বাক্য নয়, প্রবর্তক বেদবাক্য দ্বারা সূচিত বিষয়ই ধর্ম। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অংশে যে সব যোগ ও উপাসনামূলক কর্মবাক্যের অর্থ নিয়ে বিরোধ হতে পারে তাদের যথার্থ ব্যাখ্যা দেয়াই মীমাংসাশাস্ত্রের কাজ। পূর্বমীমাংসায় প্রধানতঃ বেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যাপদ্ধতি এবং অনুষ্ঠানক্রম, আর উত্তরমীমাংসায় (বেদান্তে) প্রধানতঃ জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতির ব্যাখ্যাপদ্ধতি উপদিষ্ট হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, যে-সকল বিষয়ে জৈমিনি পরিষ্কার কিছু বলেন নি, সে-সকল বিষয়ে ব্যাসের (বাদরায়ণের) দর্শনই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হবে। তাই মীমাংসাশাস্ত্র অবশ্যই শ্রুতিমূলক, তা পরাশর-উপপুরাণের একটি উদ্ধৃতি থেকেও বোঝা যায়-
‘জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ।।’- (পরাশর-উপপুরাণ)
অর্থাৎ : জৈমিনীয়দর্শন ও (ব্যাস) বেদান্তদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন কথা নেই। উত্তমরূপে বেদার্থ জানবার নিমিত্তে জৈমিনি ও ব্যাস শ্রুতির সম্যক অনুশীলন করেছিলেন।
এখানে উল্লেখ্য, সাধারণ প্রসিদ্ধি অনুসারে ‘মন্ত্র’ শব্দটি বৈদিক বাক্য বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। পারিভাষিক প্রসিদ্ধি অনুসারে জৈমিনি বেদকে দুভাগে ভাগ করেছেন- মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। কিন্তু ঠিক ঠিক কোন্ অংশ মন্ত্র ও কোন্ অংশ ব্রাহ্মণ তা সুনির্দিষ্টভাবে বলার উপায় নেই। মন্ত্রাংশ সাধারণত সংহিতা নামে পরিচিত। সংহিতা ব্যতিরিক্ত অংশ ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।
‘ব্রাহ্মণ বলতে কি বোঝায় তা বোঝাবার জন্য শবরস্বামী সংক্ষেপে ব্রাহ্মণের আলোচ্য বিষয়গুলি এভাবে নির্ধারণ করেছেন- যজ্ঞের উপকরণ ( হেতু), যজ্ঞে প্রয়োজনীয় বস্তুর লক্ষণনির্দেশ (নির্বচন); যা অনুচিত বা নিষিদ্ধ তার নিন্দা; বিধেয় কর্মের প্রশংসা; কোন কাজ দুরকমে হতে পারে, কিন্তু কোনটি গ্রহণীয় এ বিষয়ে সন্দেহ (সংশয়); যিনি অমুক বস্তু কামনা করেন তিনি অমুক যজ্ঞ করবেন এভাবে যজ্ঞীয় বিধান (বিধি); বিধেয় কর্মের প্রশস্তির জন্য এবং নিষেধ্যের নিন্দার জন্য প্রচলিত পুরাতন উপাখ্যান (পরকৃতি ও পুরাকল্প); প্রসঙ্গ অনুসারে কোন শব্দের স্পষ্ট ব্যাকরণগত অর্থের স্থলে অন্য অর্থ নির্ধারণ (ব্যবধারণ)- যে বৈদিক বাক্যগুলি দ্বারা এই বিষয়গুলি জ্ঞাপিত হয় সেই বাক্যাত্মক বেদভাগকে ব্রাহ্মণ বলে। এই সমস্ত বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান হল বিধি বা কোনযজ্ঞের কর্তব্যতা নির্দেশক বাক্য, কারণ এই যজ্ঞকর্মেই সমস্ত বেদের তাৎপর্য পর্যবসিত। বাকি বিষয়গুলি বিধির সহায়ক। তাই বেদের ব্রাহ্মণভাগকে ‘বিধি’ এই একটি শব্দের দ্বারাও নির্দেশ করা যেতে পারে (সূ: ২/১/৩৩ শাবরভাষ্য ও তন্ত্রবার্তিক দ্রষ্টব্য)। ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত বৈদিক গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধানত এই বিষয়গুলিই দেখা যায়। আরণ্যক ও উপনিষৎকে ব্রাহ্মণের অংশ বলে ধরা হয়। কিন্তু লক্ষণীয় যে, শবরস্বামী ব্রাহ্মণের যে প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবাদের কোন স্থান নেই। শবরস্বামী স্বীকার করেছেন যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের কোন নিখুঁত লক্ষণ (definition) বলার উপায় নেই। যা বলা হল তা ‘প্রায়িক’ (approximate) মাত্র। উল্লিখিত বিষয়গুলি মন্ত্ররূপে পরিচিত সংহিতাগুলিতেও পাওয়া যাবে, যেমন যজুর্বেদে। ঋকবেদের অধিক অংশই দেবতার স্তুতিবন্দনা। মীমাংসক মতে দেবস্তুতির দ্বারা প্রকারান্তরে, যে যজ্ঞে দেব স্তুতিবাচক মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হবে সেই যজ্ঞেরই প্রশংসা করা হয়েছে। দেবতা গৌণ, যজ্ঞই প্রধান (অপি বা শব্দপূর্বত্বাদ যজ্ঞকর্ম প্রধানং স্যাত্, গুণত্বে দেবতাশ্রুতিঃ। মী: সূ: ৯/১/৯) আবার মন্ত্রপ্রধান সংহিতাগুলিতে প্রচুর উপাখ্যান পাওয়া যাচ্ছে। ব্রাহ্মণভাগের মধ্যেও দেবস্তুতিপ্রভৃতি প্রচুর রয়েছে যে বাক্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত নয়। এভাবে মন্ত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছে আবার ব্রাহ্মণের মধ্যেও মন্ত্র আছে। যজ্ঞে প্রযুক্ত বিষয়বস্তু স্মরণ করিয়ে দেয় যে বেদবাক্য, তাকে মন্ত্র বলে; বাকী অংশকে বলে ব্রাহ্মণ (মী: সূ: ২/১/৩১-৩৩) কিন্তু এভাবে মন্ত্র-ব্রাহ্মণ ভাগ করা যায় না।’ (সূত্র: বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা দর্শন/ হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৯২)
বস্তুত বৈদিক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর বৈদিক বাক্যের অর্থ এবং বৈদিক বিধান নিয়ে নানা ধরনের বিবাদ ও অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে-
‘উপনিষদ যুগের কাছাকাছি সময়ে (৭০০-৬০০ খৃঃ পূঃ) স্বর্গ ও ধর্মের নানা ক্রিয়াকলাপ পশুহত্যা, মন্ত্রতন্ত্র, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি ক্রিয়ার সঙ্গে বুদ্ধির সংঘর্ষ শুরু হয়েছিলো। উপনিষদে যজ্ঞ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানকে উচ্চস্থান দিয়ে ব্রাহ্মণকে নতুন ধর্মের (=ব্রহ্মবাদ) পুরোহিতের স্থানই শুধু দেয়নি, এমনকি প্রাচীন যাগযজ্ঞকে পিতৃযানের সাধন (উপায়) বলে মেনে নিয়ে প্রাচীন পুরোহিতদের হাতে রেখেছিল। এরপর এলো বুদ্ধের যুগ। জাতপাত এবং আর্থিক বৈষম্য থেকে উৎপন্ন অসন্তোষ ধর্ম-বিদ্রোহের রূপ নিল। অজিত কেশকম্বলের মতো বস্তুবাদী তথা বুদ্ধের ন্যায় প্রতীত্য-সমুৎপাদ প্রচারক যুক্তিবাদীগণ প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের ওপর কঠিন আঘাত করলেন। ভৌগোলিক ও বৌদ্ধিক জগৎ থেকে সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডুকতা দূর হতে লাগল, অতঃপর এদেশে বসবাসকারী গ্রীক, শক প্রভৃতি আগন্তুক জাতিগণ এই বুদ্ধিবাদী সংগ্রামকে আরও প্রবল করে দিলেন। এখন আর (উপনিষদের) যাজ্ঞবল্ক্য অথবা আরুণির শিক্ষা থেকে, অথবা গার্গীকে মুণ্ডচ্যুত হওয়ার ভয় দেখানোর উপমা দিয়ে প্রশ্ন ও সন্দেহের সীমাকে রুদ্ধ করা গেলো না। নবাগত জাতিসমূহ যখন ভারতীয় হতে লাগল তখন তারা আবার স্ব-স্ব ধর্মকে বৌদ্ধিক ভিত্তিতে যুক্তিসম্মতভাবে সিদ্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলো।’- (দর্শন-দিগদর্শন, পৃষ্ঠা-১৪৭)
এ সময়ে বেদ-বিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অতি প্রবল আকার ধারণ করলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বেদবাক্য ও বেদবিধি নিয়ে নানা ধরনের সংশয় দেখা যায়। বেদের উপজীব্য যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ড নামক ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানের অসারতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধারক-বাহক যজমান পুরোহিত ব্রাহ্মণদের জীবিকা সংশয় দেখা দেওয়ার প্রেক্ষিতে এ ধর্মসংকট কাটিয়ে উঠার জন্য স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্র বেদবাক্যের তাৎপর্য নির্ধারণে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও প্রবল সংকটকে কাটিয়ে উঠতে পারে না। কেননা ইতোমধ্যে ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ পরিশ্রমলব্ধ কর্মানুষ্ঠানের চাইতে জ্ঞানযোগের মাধ্যমে ধর্ম ও মোক্ষের সন্ধানে প্রবৃত্ত বিভিন্ন জ্ঞান-দর্শনের আবির্ভাব হওয়ায় যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ডের জ্ঞানতাত্ত্বিক দার্শনিক ভিত্তিশূন্যতা দেখা দেয়। মহর্ষি জৈমিনি বৈদিক কর্মকাণ্ডের এই গভীর সংকটকে দূর করার জন্য বেদবাক্যের যথার্থ ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন কর্মের স্বরূপ ও অনুষ্ঠানপ্রণালী স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার অভিপ্রায়ে মীমাংসাসূত্র রচনা করেন।
মূলত মীমাংসা দর্শনের প্রধান উপজীব্য হলো বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈদিক কর্মকাণ্ডের স্বতসিদ্ধতা প্রমাণ করা। যজ্ঞকর্ম যে নিষ্ফল নয় তার আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এ জন্য প্রয়োজন হয় দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার। ভারতীয় দর্শনের নিয়ম অনুযায়ী যে কোন দর্শনই প্রচলিত কিছু বিষয়কে যেমন বস্তু, জগত, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, পাপ-পূণ্য, স্বর্গ-নরক, মোক্ষ, ধর্ম, প্রমাণ-প্রমেয় ইত্যাদি বিষয়কে নিজ নিজ মত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে হয়। আর তা করতে গিয়ে দার্শনিক বিচারে অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের তত্ত্বের যেখান থেকে যেটুকু স্বীকার করা আবশ্যক তা নিজের মতো করে স্বীকার করা এবং যেখানে বিরোধিতার প্রয়োজন সেখানে বিরোধী যুক্তি উপস্থান করতে মীমাংসকরা কার্পণ্য করলেন না। ফলে একদিকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রচণ্ড অবিশ্বাসী এ দর্শনের বস্তুবাদী বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিস্রোতের পাশাপাশি যজ্ঞানুষ্ঠানের মতো একটি আদিম কুসংস্কারের মধ্যে যাদুক্ষমতা আরোপ প্রচেষ্টার চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন দর্শনটিকে জটিল স্ববিরোধিতায় ঠেলে দিয়েছে বলে একালের বিদ্বানেরা মনে করেন।
মীমাংসাদর্শন সাংখ্য বৌদ্ধ বা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মতো একটা সুশৃঙ্খল সুসংহত দার্শনিক প্রস্থানরূপে গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছে যাগযজ্ঞসম্পৃক্ত মন্ত্ররাশির অর্থবিচারকে উপলক্ষ করে। এই দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য কোন বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভাবন ও প্রচার নয়। মুখ্য উদ্দেশ্য যাগযজ্ঞের সামাজিক প্রয়োজন অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত রাখার জন্য মন্ত্রার্থবিচার। এই বিচারের প্রসঙ্গেই প্রয়োজনানুরূপ দার্শনিক যুক্তিতর্ক বিক্ষিপ্তভাবে উপস্থিত হয়েছে। অথচ এই উপস্থিতি বিপুল ও বিস্ময়কর ! মীমাংসার বহু সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচার ও সিদ্ধান্ত আধুনিক সমাজ-দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
মীমাংসা দর্শন অবশ্যই আস্তিক দর্শন। কেননা ভারতীয় দর্শনে আস্তিক মানে বেদ-পন্থী। আস্তিক্য বিচারে তাই ঈশ্বর মানা-না-মানার প্রসঙ্গ অবান্তর। বস্তুত আস্তিকদের পক্ষেও যে ঈশ্বর অস্বীকারের পরিপূর্ণ সুযোগ ছিলো তারই নজির হিসেবে সাধারণত সাংখ্য ও মীমাংসার উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এদিক থেকে সাংখ্যের চেয়ে মীমাংসা চিত্তাকর্ষক বলে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে-
‘…সাংখ্যকে বেদমূলক বলে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে শঙ্কর, রামানুজ প্রমুখ অগ্রণী আস্তিকেরা তীব্র আপত্তি তুলেছেন এবং সে আপত্তি ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু মীমাংসা-প্রসঙ্গে এ-জাতীয় সামান্যতম সংশয়ও কল্পনাতীত। কেননা, বেদের চরম প্রামাণ্যই– বেদের অপৌরুষেয়ত্ব এবং নিত্যত্ব– এ সম্প্রদায়ের মূল প্রতিপাদ্য এবং “এই কর্মমীমাংসার মধ্যে দুইটি কার্য করা হইয়াছে। প্রথম, –বেদবাক্যের প্রকারভেদ নির্ণয় এবং দ্বিতীয়, –বেদ-বাক্যের মধ্যে আপাতবিরোধের পরিহারপূর্বক একবাক্যতাসাধন। আর এইজন্য একসহস্র বিচার বা ন্যায় রচিত হইয়াছে।”- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-২৩০)
অন্যদিকে মীমাংসা চরম নিরীশ্বরবাদী দর্শন। প্রাচীন সাংখ্যকে নিরীশ্বরবাদী বলা হলেও পরবর্তীকালে বিজ্ঞানভিক্ষুর মতো ঈশ্বরবাদী দার্শনিকদের সুকৌশল ব্যাখ্যাবলে সাংখ্যের ঈশ্বর-প্রত্যাখ্যান কিছুটা হলেও অস্পষ্টতায় পর্যবসিত হয়েছে। সেদিক থেকে মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর-প্রত্যাখ্যান এতোটাই চরম যে পরবর্তীকালে তাকে ঈশ্বরবাদী বানানোর কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। এই ঈশ্বর-প্রত্যাখ্যানের দিক থেকে আস্তিক মীমাংসার সঙ্গে নাস্তিক বৌদ্ধাদি-সম্প্রদায়ের তুলনা চিত্তাকর্ষক হয় বলে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন-
‘বস্তুত, অশ্বঘোষের রচনায় যে-সব যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন সেগুলির সঙ্গে প্রাচীন মীমাংসকদের যুক্তি-তর্কের আশ্চর্য সাদৃশ্য চোখে পড়ে ! আরো আশ্চর্য কথা হলো, মীমাংসা-মতে বৈদিক দেবতারাও নেহাতই শব্দমাত্র ; অতএব তাঁদের পূজা-উপাসনা সম্পূর্ণ অর্থহীন। চরম বেদপন্থী সম্প্রদায়ের পক্ষে বৈদিক দেবতা সম্বন্ধে এ-জাতীয় মত অন্তত আপাত-অদ্ভূত মনে হবে। কিন্তু আরো বিস্ময়কর মনে হবে স্বর্গ এবং অপবর্গ সংক্রান্ত মীমাংসা-মত। কেননা নিরতিশয় সুখ বা প্রীতির নামই স্বর্গ এবং তা এই মর্ত্যলোকেই সম্ভব। আর মোক্ষ ? আধুনিক বিদ্বানদের পক্ষ থেকে মীমাংসাকে মোক্ষশাস্ত্র প্রতিপন্ন করার নানান কষ্টকল্পিত প্রয়াস সত্ত্বেও, প্রাচীন মীমাংসকেরা মোক্ষের প্রতি প্রকৃতই উদাসীন ; এবং তাঁদের দর্শনে মোক্ষ-প্রসঙ্গ কেন অবান্তর সে-কথার ব্যাখ্যা পাওয়াও কঠিন নয়।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-২৩১)।


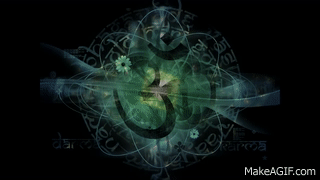




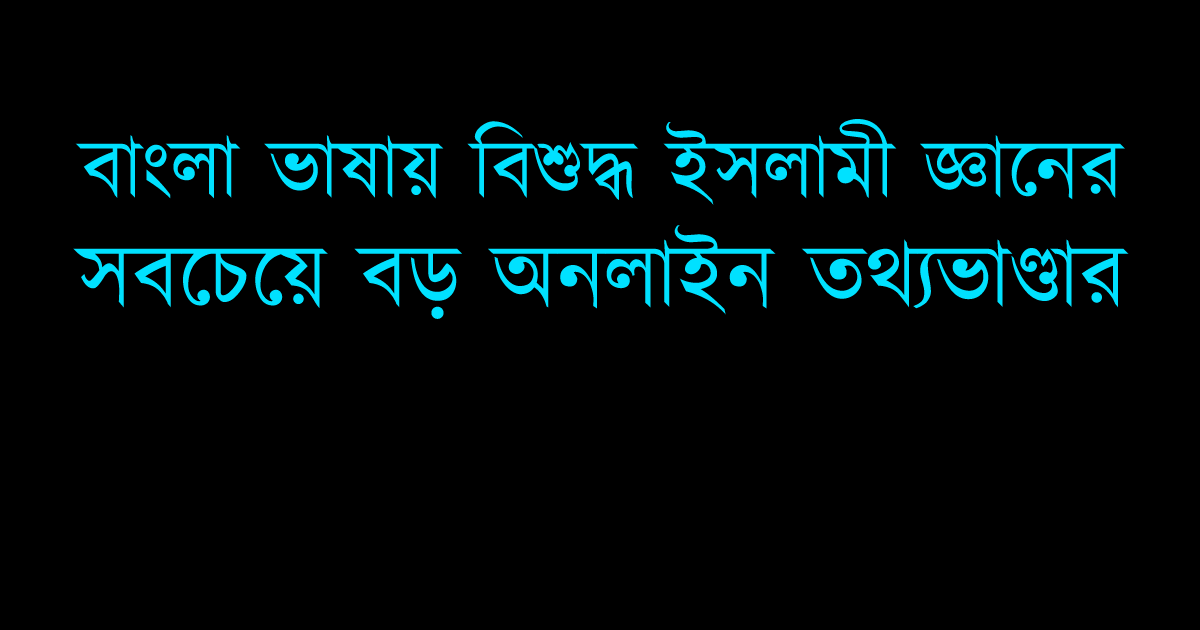


















No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ