বৌদ্ধ তন্ত্র ও তার দেবদেবী- : ভূমিকা
তন্ত্রের সাথে যে কল্পিত দেবীশক্তির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এ-বিষয়ে মনে হয় সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। আর দেবীসাধনা মানেই তো দেবীপূজা। তার মানে এখানে যে শাক্ত-প্রভাব প্রবল এটা বোধকরি অস্বীকার করা যায় না। আবার একই নামের বা বৈশিষ্ট্যের দেবীর হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় তান্ত্রিক ধর্মে উপস্থিতি থাকায় হিন্দু তন্ত্র-পুরাণাদিতে গৃহীত বহু দেবীকে বৌদ্ধ দেবী বলেও সন্দেহ করা হয়। যেমন, হিন্দু-দেবী তারাকে বহুরূপে হিন্দু উপপুরাণ-তন্ত্রাদির মধ্যে পাওয়া যায়। এই তারা-দেবী যে বৌদ্ধ তারা বা উগ্রতারা বা একজটা দেবী, সেকথাও আজ প্রায় স্বীকৃত। এ ছাড়াও–
‘হিন্দু উপপুরাণ-তন্ত্রে এবং বৌদ্ধ-তন্ত্রাদিতে এই দেবীর বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সরস্বতী হিন্দুধর্মে পূজিতা প্রসিদ্ধা দেবী; কিন্তু বৌদ্ধ-তন্ত্রে এই দেবীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দেখিতে পাই। পর্ণশবরী দেবী দুর্গার একটি প্রসিদ্ধ নাম– পর্ণ (হলুদ পাতা) পরিহিতা পর্ণশবরীর কথা আমরা বৌদ্ধ ‘সাধনমালায়’ও দেখিতে পাই। সুবন্ধুর ‘বাসবদত্তা’য় আমরা বেতালা-দেবীর মন্দিরের উল্লেখ পাই; বৌদ্ধ-তন্ত্রেও বজ্র-বেতালীর সন্ধান পাই। মার্কণ্ডেয় ‘চণ্ডী’তে শক্তির মায়ূরী, অপরাজিতা, বারাহী, ভীমা, কপালিনী, কৌবেরী প্রভৃতির নাম পাই; বৌদ্ধ ‘সাধনমালা’র মধ্যেও মহামায়ূরী, অপরাজিতা, বজ্রবারাহী, ভীমা, কপালিনী, কৌবেরী দেবীর উল্লেখ পাই। চণ্ডীতে শিবকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া দেবী ‘শিবদূতী’ নামে খ্যাতা, বৌদ্ধ-তন্ত্রে মহাকালের সহিত যুক্তা দেবীকে ‘কালদূতী’ নামে দেখিতে পাইতেছি। প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধ-তন্ত্রের ‘যমদূতী’র কথাও স্মর্তব্য। ছিন্নমস্তা হিন্দু-দশমহাবিদ্যার এক বিখ্যাত মহাবিদ্যা, ছিন্নমস্তা দেবীকে বৌদ্ধ-তন্ত্রের মধ্যেও পাইতেছি। বৌদ্ধ-তন্ত্রে কালিকা-দেবীরও সন্ধান পাইতেছি। ইনি মহাকালের সহিত সংশ্লিষ্টা; ইঁহার বর্ণনায় দেখা যায়, ইনি ভয়ঙ্করী, নীলবর্ণা, দ্বিভুজা, অগ্নিকোণস্থিতা, একহাতে কঙ্কাল ও অন্যহাতে অস্ত্র। আলীঢ় ভঙ্গিতে ইনি শবের উপর অবস্থিতা।’- (শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত/ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য/ পৃষ্ঠা-১২৯)
‘হিন্দু উপপুরাণ-তন্ত্রে এবং বৌদ্ধ-তন্ত্রাদিতে এই দেবীর বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সরস্বতী হিন্দুধর্মে পূজিতা প্রসিদ্ধা দেবী; কিন্তু বৌদ্ধ-তন্ত্রে এই দেবীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দেখিতে পাই। পর্ণশবরী দেবী দুর্গার একটি প্রসিদ্ধ নাম– পর্ণ (হলুদ পাতা) পরিহিতা পর্ণশবরীর কথা আমরা বৌদ্ধ ‘সাধনমালায়’ও দেখিতে পাই। সুবন্ধুর ‘বাসবদত্তা’য় আমরা বেতালা-দেবীর মন্দিরের উল্লেখ পাই; বৌদ্ধ-তন্ত্রেও বজ্র-বেতালীর সন্ধান পাই। মার্কণ্ডেয় ‘চণ্ডী’তে শক্তির মায়ূরী, অপরাজিতা, বারাহী, ভীমা, কপালিনী, কৌবেরী প্রভৃতির নাম পাই; বৌদ্ধ ‘সাধনমালা’র মধ্যেও মহামায়ূরী, অপরাজিতা, বজ্রবারাহী, ভীমা, কপালিনী, কৌবেরী দেবীর উল্লেখ পাই। চণ্ডীতে শিবকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া দেবী ‘শিবদূতী’ নামে খ্যাতা, বৌদ্ধ-তন্ত্রে মহাকালের সহিত যুক্তা দেবীকে ‘কালদূতী’ নামে দেখিতে পাইতেছি। প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধ-তন্ত্রের ‘যমদূতী’র কথাও স্মর্তব্য। ছিন্নমস্তা হিন্দু-দশমহাবিদ্যার এক বিখ্যাত মহাবিদ্যা, ছিন্নমস্তা দেবীকে বৌদ্ধ-তন্ত্রের মধ্যেও পাইতেছি। বৌদ্ধ-তন্ত্রে কালিকা-দেবীরও সন্ধান পাইতেছি। ইনি মহাকালের সহিত সংশ্লিষ্টা; ইঁহার বর্ণনায় দেখা যায়, ইনি ভয়ঙ্করী, নীলবর্ণা, দ্বিভুজা, অগ্নিকোণস্থিতা, একহাতে কঙ্কাল ও অন্যহাতে অস্ত্র। আলীঢ় ভঙ্গিতে ইনি শবের উপর অবস্থিতা।’- (শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত/ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য/ পৃষ্ঠা-১২৯)
প্রচলিত হিন্দু-তন্ত্রগুলি থেকে বৌদ্ধতন্ত্রগুলির রচনাকাল প্রাচীনতর হওয়ায় এভাবে বৌদ্ধ-তন্ত্রাদিতে যেসব দেবীর নাম পাওয়া যায়, হিন্দুধর্মে তাঁদেরকে গৃহীত হতে দেখলেই সাধারণভাবে ধারণা হতে পারে যে এই দেবী মূলতঃ বৌদ্ধ-দেবী এবং বৌদ্ধধর্ম থেকেই হিন্দুধর্মে তাঁরা গৃহীত হয়েছেন। এর প্রত্যুত্তরে শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন–
‘বৌদ্ধ-তন্ত্রে উল্লেখ পাইলেই কি সেই দেবী বৌদ্ধ-দেবী হইয়া যান? বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলিকে বৌদ্ধ বলিবারই বা তাৎপর্য কি? দেবদেবীর সাদৃশ্য, বর্ণিত সাধনার সাদৃশ্য এবং গুহ্য যোগবিধির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া এবং প্রচলিত হিন্দু-তন্ত্রগুলি হইতে নবাবিষ্কৃত বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলির রচনাকাল প্রাচীনতর মনে করিয়া বৌদ্ধ-তন্ত্র হইতেই হিন্দু-তন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে এইরূপ একটি মতও কেহ কেহ পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থান্তরে [An Introduction To Tantric Buddhism] আমরা এ জিনিসটি স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মূলে হিন্দু-তন্ত্র এবং বৌদ্ধ-তন্ত্র বলিয়া কোনও জিনিস নাই, মূল দর্শনে এবং সাধনায় এই উভয়বিধ তন্ত্রের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। তন্ত্র বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রবাহিত একটি স্বতন্ত্র সাধনার ধারা; এই সাধনধারার সহিত বিভিন্ন কালে হিন্দু-দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব যুক্ত হইয়া ইহাকে হিন্দু-তন্ত্রের রূপ দান করিয়াছে; আবার পরবর্তী কালের মহাযান বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি চিন্তাধারার সহিত যুক্ত হইয়া ইহা বৌদ্ধ-তন্ত্রের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আর এই মূল সাধনার কথা ছাড়িয়া তন্ত্রাদিতে বর্ণিত দেবদেবী ও পূজা-অর্চনাবিধির কথা যদি ধরা যায় তবে দেখিব– উভয়ক্ষেত্রেই দেবদেবী, উপদেবী, ডাকিনী-যোগিনী, যক্ষ-রক্ষ প্রভৃতির বর্ণনা, পূজা-বিধি বা ধ্যান-অর্চনাবিধি স্থান পাইয়াছে। এই দেবদেবীগণ কোনও ক্ষেত্রেই কোনও গভীর হিন্দু-দার্শনিক তত্ত্ব বা বৌদ্ধ-দার্শনিক তত্ত্বকে রূপায়িত করিবার জন্যই আস্তে আস্তে বিশদবর্ণনায় বিগ্রহবর্তী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সে-কথা আমরা স্বীকার করি না।… উভয়ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমাজস্তরের মানসিক প্রবণতায় বিভিন্নভাবে পরিকল্পিত স্থানীয় দেবদেবীগণ এবং প্রচার ও প্রসিদ্ধি হেতু সাধারণীকৃত দেবদেবীগণের উল্লেখ বর্ণনা ও সাধনার কথা দেখিতে পাইতেছি। বৌদ্ধ সাধনমালায় যে-সকল দেবীর উল্লেখ পাইয়াছি দেবী-হিসাবে বজ্র, শূন্যতা, করুণা, বোধিচিত্ত, প্রজ্ঞা প্রভৃতি কতকগুলি চিহ্নাঙ্কন ব্যতীত প্রচলিত হিন্দু-দেবীগণ হইতে তাঁহাদের পার্থক্য কি? সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য বিবিধ মন্ত্র-প্রয়োগের সঙ্গে যে ধ্যান-পরিকল্পনা দেখিতে পাই তাহার সহিত পরোক্ষভাবে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের ধ্যান-পরিকল্পনা এবং যোগাশ্রিত মহাযানের ধ্যান-পরিকল্পনার কিছু কিছু যোগ লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু আসলে হিন্দু-দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাস যেরূপ, বৌদ্ধ-দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাসও একান্তই অনুরূপ।’- (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৩০)
‘বৌদ্ধ-তন্ত্রে উল্লেখ পাইলেই কি সেই দেবী বৌদ্ধ-দেবী হইয়া যান? বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলিকে বৌদ্ধ বলিবারই বা তাৎপর্য কি? দেবদেবীর সাদৃশ্য, বর্ণিত সাধনার সাদৃশ্য এবং গুহ্য যোগবিধির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া এবং প্রচলিত হিন্দু-তন্ত্রগুলি হইতে নবাবিষ্কৃত বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলির রচনাকাল প্রাচীনতর মনে করিয়া বৌদ্ধ-তন্ত্র হইতেই হিন্দু-তন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে এইরূপ একটি মতও কেহ কেহ পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থান্তরে [An Introduction To Tantric Buddhism] আমরা এ জিনিসটি স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মূলে হিন্দু-তন্ত্র এবং বৌদ্ধ-তন্ত্র বলিয়া কোনও জিনিস নাই, মূল দর্শনে এবং সাধনায় এই উভয়বিধ তন্ত্রের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। তন্ত্র বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রবাহিত একটি স্বতন্ত্র সাধনার ধারা; এই সাধনধারার সহিত বিভিন্ন কালে হিন্দু-দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব যুক্ত হইয়া ইহাকে হিন্দু-তন্ত্রের রূপ দান করিয়াছে; আবার পরবর্তী কালের মহাযান বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি চিন্তাধারার সহিত যুক্ত হইয়া ইহা বৌদ্ধ-তন্ত্রের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আর এই মূল সাধনার কথা ছাড়িয়া তন্ত্রাদিতে বর্ণিত দেবদেবী ও পূজা-অর্চনাবিধির কথা যদি ধরা যায় তবে দেখিব– উভয়ক্ষেত্রেই দেবদেবী, উপদেবী, ডাকিনী-যোগিনী, যক্ষ-রক্ষ প্রভৃতির বর্ণনা, পূজা-বিধি বা ধ্যান-অর্চনাবিধি স্থান পাইয়াছে। এই দেবদেবীগণ কোনও ক্ষেত্রেই কোনও গভীর হিন্দু-দার্শনিক তত্ত্ব বা বৌদ্ধ-দার্শনিক তত্ত্বকে রূপায়িত করিবার জন্যই আস্তে আস্তে বিশদবর্ণনায় বিগ্রহবর্তী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সে-কথা আমরা স্বীকার করি না।… উভয়ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমাজস্তরের মানসিক প্রবণতায় বিভিন্নভাবে পরিকল্পিত স্থানীয় দেবদেবীগণ এবং প্রচার ও প্রসিদ্ধি হেতু সাধারণীকৃত দেবদেবীগণের উল্লেখ বর্ণনা ও সাধনার কথা দেখিতে পাইতেছি। বৌদ্ধ সাধনমালায় যে-সকল দেবীর উল্লেখ পাইয়াছি দেবী-হিসাবে বজ্র, শূন্যতা, করুণা, বোধিচিত্ত, প্রজ্ঞা প্রভৃতি কতকগুলি চিহ্নাঙ্কন ব্যতীত প্রচলিত হিন্দু-দেবীগণ হইতে তাঁহাদের পার্থক্য কি? সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য বিবিধ মন্ত্র-প্রয়োগের সঙ্গে যে ধ্যান-পরিকল্পনা দেখিতে পাই তাহার সহিত পরোক্ষভাবে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের ধ্যান-পরিকল্পনা এবং যোগাশ্রিত মহাযানের ধ্যান-পরিকল্পনার কিছু কিছু যোগ লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু আসলে হিন্দু-দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাস যেরূপ, বৌদ্ধ-দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাসও একান্তই অনুরূপ।’- (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৩০)
বলা বাহুল্য, বৌদ্ধধর্মের জটিল আবহে এই তান্ত্রিক-দেবীবাদের সৃষ্টি বা অনুপ্রবেশের ক্রমবিকাশ বুঝতে হলে আমাদেরকে বোধকরি প্রথমেই বৌদ্ধ-দেবমণ্ডল বা মূর্তিশাস্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পূর্ব-ধারণা নিয়ে রাখা আবশ্যক।
বৌদ্ধ দেবমণ্ডলের আদি দেবতা আদিবুদ্ধ। তিনিই সৃষ্টির আদি কারণ শূন্য বা বজ্র। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বকারণ, সর্বশক্তির আধার এবং সর্বজ্ঞ। সৃষ্টির প্রত্যেক অণুপরমাণুতে তিনি বিদ্যমান, সেজন্য সৃষ্টির সমস্ত বস্তুই স্বভাবশুদ্ধ, শূন্যরূপ, নিঃস্বভাব ও বুদবুদস্বরূপ। কেবল শূন্যই নিত্য। আদিবুদ্ধ সেই শূন্যের রূপকল্পনা। আদিবুদ্ধ থেকেই পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের উদ্ভব। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধেরা পাঁচটি স্কন্ধের অধিষ্ঠাতা।
‘আদিবুদ্ধ যখন দেবতাকারে কল্পিত হন তখন তাঁহার নাম হয় বজ্রধর এবং তিনি কমলের উপর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট থাকেন। তাঁহার দুইটি হস্ত বক্ষের উপর বজ্রহূঁকার মুদ্রায় সজ্জিত হয় এবং হাত দুইটিতে বজ্র ও ঘণ্টা থাকে। বজ্র থাকে দক্ষিণ হস্তে ও ঘণ্টা থাকে বাম হস্তে। পরিধানে থাকে বিচিত্র বস্ত্রাদি এবং তিনি সকল প্রকার অলংকারে ভূষিত হন। তাঁহার শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতার সহিত কোনো কোনো স্থানে তাঁহাকে যুগনদ্ধ মূর্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে শক্তির দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি ও বামে কপাল থাকে। বজ্রধরের মূর্তি দুই প্রকারে কল্পিত হইয়া থাকে।– একটি একক মূর্তি ও অপরটি যুগনদ্ধ মূর্তি। একটি শূন্যমূর্তি ও অপরটি বোধিচিত্ত-মূর্তি। একটি শূন্যতা ও অপরটি করুণা। একটি পরমাত্মা, অপরটি জীবাত্মা। যতক্ষণ দ্বয়ভাব বর্তমান থাকে ততক্ষণ দুইটি মূর্তি দেখা যায়। এই দ্বয়ভাব যখন অদ্বয়ে পরিণত হয় তখন দুইটি মিলিয়া এক হইয়া যায়, যেমন লবণ জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া একমাত্র জলে পরিণত হয়।’- ( ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য/ বৌদ্ধদের দেবদেবী, পৃষ্ঠা-২৮)
‘আদিবুদ্ধ যখন দেবতাকারে কল্পিত হন তখন তাঁহার নাম হয় বজ্রধর এবং তিনি কমলের উপর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট থাকেন। তাঁহার দুইটি হস্ত বক্ষের উপর বজ্রহূঁকার মুদ্রায় সজ্জিত হয় এবং হাত দুইটিতে বজ্র ও ঘণ্টা থাকে। বজ্র থাকে দক্ষিণ হস্তে ও ঘণ্টা থাকে বাম হস্তে। পরিধানে থাকে বিচিত্র বস্ত্রাদি এবং তিনি সকল প্রকার অলংকারে ভূষিত হন। তাঁহার শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতার সহিত কোনো কোনো স্থানে তাঁহাকে যুগনদ্ধ মূর্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে শক্তির দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি ও বামে কপাল থাকে। বজ্রধরের মূর্তি দুই প্রকারে কল্পিত হইয়া থাকে।– একটি একক মূর্তি ও অপরটি যুগনদ্ধ মূর্তি। একটি শূন্যমূর্তি ও অপরটি বোধিচিত্ত-মূর্তি। একটি শূন্যতা ও অপরটি করুণা। একটি পরমাত্মা, অপরটি জীবাত্মা। যতক্ষণ দ্বয়ভাব বর্তমান থাকে ততক্ষণ দুইটি মূর্তি দেখা যায়। এই দ্বয়ভাব যখন অদ্বয়ে পরিণত হয় তখন দুইটি মিলিয়া এক হইয়া যায়, যেমন লবণ জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া একমাত্র জলে পরিণত হয়।’- ( ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য/ বৌদ্ধদের দেবদেবী, পৃষ্ঠা-২৮)
ধ্যানীবুদ্ধ পাঁচ জন– বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। এক-একজন ধ্যানীবুদ্ধকে এক-একটি স্কন্ধের অধিষ্ঠাতা হিসেবে কল্পনা করা হয়। বৌদ্ধমূর্তি-শাস্ত্রে ধ্যানীবুদ্ধের স্থান সর্বোচ্চ, কারণ ধ্যানীবুদ্ধ থেকেই বুদ্ধশক্তির উৎপত্তি এবং বুদ্ধশক্তি থেকে বোধিসত্ত্বদের উৎপত্তি। পাঁচ ধ্যানীবুদ্ধের শক্তি যথাক্রমে লোচনা বা রোচনা, বজ্রধাত্বীশ্বরী, পাণ্ডরা, তারা ও মামকী। বোধিসত্ত্বেরা কোন-না-কোন ধ্যানীবুদ্ধ-কুলের অন্তর্গত। বোধিসত্ত্ব মূর্তির মাথার উপরে কুল-জ্ঞাপক ধ্যানীবুদ্ধের একটি ছোট মূর্তি দেওয়া হতো। এই ক্ষুদ্র ধ্যানীবুদ্ধকে দেখতে পেলে বোধিসত্ত্বের মূর্তি চেনা সহজসাধ্য হয়ে থাকে।
বৌদ্ধমতে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান– এই পাঁচটি উপাদান পুঞ্জ বা স্কন্ধের সমবায়ে পুদ্গল বা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। ধ্যানীবুদ্ধ কল্পনার ভিত্তি এই পঞ্চস্কন্ধ। তবে পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি-কল্পনা একই প্রকারের। সকলেই ধ্যানাসনে সমাধি অবস্থায় বসে থাকেন। আসনের নিচে কমল থাকে। সকলেরই একটি মুখ এবং দুটি হাত। তাঁদের নেত্র ধ্যানস্তিমিত এবং অর্ধনিমীলিত। তাঁদের পরিধানে ত্রিচীবর থাকে এবং সকলেই অলংকাররহিত হন।
তাঁদের কেবল রং আলাদা এবং মুদ্রা আলাদা। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানীবুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন বাহন ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকচিহ্ন হয়। মুদ্রা থেকেই প্রধানত ধ্যানীবুদ্ধ-মূর্তি চিনতে হয়। ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর ‘বৌদ্ধদের দেবদেবী’ গ্রন্থে প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন।
রূপ-স্কন্ধ থেকে ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের উৎপত্তি। ‘জিনজিক’ মন্ত্রপদ থেকে মন্ত্রপুরুষরূপে বৈরোচনের আবির্ভাব হয়। তাঁর বর্ণ সাদা এবং তিনি ধর্মচক্র বা বোধ্যঙ্গীমুদ্রা ধারণ করেন। তাঁর বাহন হলো দুটি ভীষণাকৃতি সর্প এবং প্রতীকচিহ্ন চক্র।
বেদনা-স্কন্ধ থেকে ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের উৎপত্তি। ‘রত্নধৃক’ মন্ত্রপদ থেকে মন্ত্রপুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব হয়। তাঁর বর্ণ পীত এবং তিনি বরদমুদ্রা প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁর বাহন দুটি সিংহ এবং প্রতীকচিহ্ন রত্ন।
ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের উৎপত্তি সংজ্ঞা-স্কন্ধ থেকে। ‘আরোলিক্’ মন্ত্রপদ থেকে অমিতাভ-রূপ মন্ত্রপুরুষের আবির্ভাব। তাঁর বর্ণ লাল এবং মুদ্রা সমাধি। তাঁর বাহন দুই ময়ূর এবং প্রতীকচিহ্ন পদ্ম।
অমোঘসিদ্ধির উৎপত্তি সংস্কার-স্কন্ধ থেকে। ‘প্রজ্ঞাধৃক’ মন্ত্রপদ থেকে মন্ত্রপুরুষরূপে অমোঘসিদ্ধির আবির্ভাব। গুহ্যসমাজতন্ত্রে তাঁর নাম অমোঘবজ্র। তাঁর বর্ণ সবুজ এবং তিনি অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করেন। তাঁর বাহন হলো দুটি গরুড় এবং প্রতীকচিহ্ন বিশ্ববজ্র।
অক্ষোভ্য ধ্যানীবুদ্ধের উৎপত্তি বিজ্ঞান-স্কন্ধ থেকে। ‘বজ্রধৃক’ মন্ত্রপদ থেকে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর বর্ণ নীল এবং মুদ্রা ভূমিস্পর্শ। তাঁর বাহন দুটি হস্তী এবং প্রতীকচিহ্ন বজ্র।
বৌদ্ধমতে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান– এই পাঁচটি উপাদান পুঞ্জ বা স্কন্ধের সমবায়ে পুদ্গল বা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। ধ্যানীবুদ্ধ কল্পনার ভিত্তি এই পঞ্চস্কন্ধ। তবে পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি-কল্পনা একই প্রকারের। সকলেই ধ্যানাসনে সমাধি অবস্থায় বসে থাকেন। আসনের নিচে কমল থাকে। সকলেরই একটি মুখ এবং দুটি হাত। তাঁদের নেত্র ধ্যানস্তিমিত এবং অর্ধনিমীলিত। তাঁদের পরিধানে ত্রিচীবর থাকে এবং সকলেই অলংকাররহিত হন।
তাঁদের কেবল রং আলাদা এবং মুদ্রা আলাদা। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানীবুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন বাহন ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকচিহ্ন হয়। মুদ্রা থেকেই প্রধানত ধ্যানীবুদ্ধ-মূর্তি চিনতে হয়। ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর ‘বৌদ্ধদের দেবদেবী’ গ্রন্থে প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন।
রূপ-স্কন্ধ থেকে ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের উৎপত্তি। ‘জিনজিক’ মন্ত্রপদ থেকে মন্ত্রপুরুষরূপে বৈরোচনের আবির্ভাব হয়। তাঁর বর্ণ সাদা এবং তিনি ধর্মচক্র বা বোধ্যঙ্গীমুদ্রা ধারণ করেন। তাঁর বাহন হলো দুটি ভীষণাকৃতি সর্প এবং প্রতীকচিহ্ন চক্র।
বেদনা-স্কন্ধ থেকে ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের উৎপত্তি। ‘রত্নধৃক’ মন্ত্রপদ থেকে মন্ত্রপুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব হয়। তাঁর বর্ণ পীত এবং তিনি বরদমুদ্রা প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁর বাহন দুটি সিংহ এবং প্রতীকচিহ্ন রত্ন।
ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের উৎপত্তি সংজ্ঞা-স্কন্ধ থেকে। ‘আরোলিক্’ মন্ত্রপদ থেকে অমিতাভ-রূপ মন্ত্রপুরুষের আবির্ভাব। তাঁর বর্ণ লাল এবং মুদ্রা সমাধি। তাঁর বাহন দুই ময়ূর এবং প্রতীকচিহ্ন পদ্ম।
অমোঘসিদ্ধির উৎপত্তি সংস্কার-স্কন্ধ থেকে। ‘প্রজ্ঞাধৃক’ মন্ত্রপদ থেকে মন্ত্রপুরুষরূপে অমোঘসিদ্ধির আবির্ভাব। গুহ্যসমাজতন্ত্রে তাঁর নাম অমোঘবজ্র। তাঁর বর্ণ সবুজ এবং তিনি অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করেন। তাঁর বাহন হলো দুটি গরুড় এবং প্রতীকচিহ্ন বিশ্ববজ্র।
অক্ষোভ্য ধ্যানীবুদ্ধের উৎপত্তি বিজ্ঞান-স্কন্ধ থেকে। ‘বজ্রধৃক’ মন্ত্রপদ থেকে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর বর্ণ নীল এবং মুদ্রা ভূমিস্পর্শ। তাঁর বাহন দুটি হস্তী এবং প্রতীকচিহ্ন বজ্র।
কখনও কখনও এই পাঁচজন ছাড়াও আরেকজন ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধের কল্পনা করা হয়। তাঁর নাম বজ্রসত্ত্ব এবং তিনি পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পুরোহিতরূপে পরিগণিত হয়ে থাকেন। বজ্রসত্ত্বের বিগ্রহ দুই প্রকারের হয়ে থাকে– একক এবং যুগনদ্ধ।
তাঁর বর্ণ সাদা, তিনি মনঃস্বভাব এবং হুঁকার শব্দ থেকে উৎপন্ন হন। তিনি একমুখ ও দ্বিভুজ এবং রাজোচিত বেশভূষা ও অলংকারাদিতে শোভিত। তিনি কমলের উপর ধ্যানাসনে বসে থাকেন। বক্ষের নিকট দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ করেন এবং বাম হস্তে কটিদেশে ঘণ্টা ধারণ করেন।
যুগনদ্ধরূপে তিনি শক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত হন। সেই শক্তির নাম বজ্রসত্ত্বাত্মিকা। তাঁর দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি এবং বামে কপাল থাকে।
তাঁর বর্ণ সাদা, তিনি মনঃস্বভাব এবং হুঁকার শব্দ থেকে উৎপন্ন হন। তিনি একমুখ ও দ্বিভুজ এবং রাজোচিত বেশভূষা ও অলংকারাদিতে শোভিত। তিনি কমলের উপর ধ্যানাসনে বসে থাকেন। বক্ষের নিকট দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ করেন এবং বাম হস্তে কটিদেশে ঘণ্টা ধারণ করেন।
যুগনদ্ধরূপে তিনি শক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত হন। সেই শক্তির নাম বজ্রসত্ত্বাত্মিকা। তাঁর দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি এবং বামে কপাল থাকে।
প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের একটি করে বিভিন্ন শক্তি কল্পিত হয়েছে। গুহ্যসমাজতন্ত্রে তাঁদের বিবরণ পাওয়া যায়। ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ‘বৌদ্ধদের দেবদেবী’ গ্রন্থে এই বুদ্ধশক্তি-মূর্তির বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন। তাঁদের সকলকেই দেখতে প্রায় এক। সকলেই সুন্দর রূপ ও লাবণ্যবতী, চন্দ্রের উপর ললিতাসনে বসে থাকেন। তাঁদের বর্ণ ও বাহন তাঁদের নিজ নিজ ধ্যানীবুদ্ধের অনুরূপ। তাঁরা সকলেই সাধারণত স্ব স্ব ধ্যানীবুদ্ধের এক-একটি ক্ষুদ্র মূর্তি মস্তকে ধারণ করেন। তাঁরা সকলেই এক মুখ ও দুই হস্ত বিশিষ্ট। তাঁরা দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বাম হস্ত বক্ষের নিকট রক্ষিত হয়। দুই হস্তে পদ্মের নাল থাকে এবং সেই নাল থেকে দুটি পদ্ম দুই পার্শ্বে উত্থিত হয়। পদ্মের উপর স্ব স্ব ধ্যানীবুদ্ধের প্রতীকচিহ্ন রক্ষিত হয়।
বুদ্ধশক্তি লোচনা বা রোচনা ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের শক্তিরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। ‘মোহরতি’ মন্ত্রপদ থেকে ঘনীভূত হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র বৈরোচন মূর্তি ধারণ করে নিজ কুলের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁর বর্ণ সাদা এবং তিনি দুই পার্শ্বস্থিত দুটি পদ্মের উপর দুটি চক্র কুলচিহ্ন স্বরূপ প্রদর্শন করেন।
বজ্রধাত্বীশ্বরী ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের শক্তিরূপে গণ্য হন। গুহ্যসমাজতন্ত্র অনুযায়ী ‘ঈর্ষ্যারতি’ মন্ত্রপদ থেকে ঘনীভূত হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র রত্নসম্ভব-মূর্তি ধারণ করে স্বকুলের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁর বর্ণ পীত বা হলদে এবং তাঁর দুই পার্শ্বস্থিত দুটি পদ্মের উপর দুটি রত্নচ্ছটা কুলচিহ্ন স্বরূপ প্রদর্শন করে থাকেন।
বুদ্ধশক্তি পাণ্ডরা বা পাণ্ডরবাসিনী ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের শক্তিরূপে গণ্য হন। ‘রাগরতি’ মন্ত্রপদ থেকে ঘনীভূত হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র অমিতাভ-মূর্তি ধারণ করে স্বকুলের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁর বর্ণ লাল এবং দুই পার্শ্বস্থিত প্রস্ফুটিত কমলের উপর কুলচিহ্নস্বরূপ দুটি পদ্ম প্রদর্শন করে থাকেন।
বুদ্ধশক্তি তারা ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির শক্তিরূপে গণ্য হন। গুহ্যসমাজের মতে ‘বজ্ররতি’ মন্ত্রপদ থেকে ঘনীভূত হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র অমোঘসিদ্ধির মূর্তি ধারণ করে স্বকুলের পরিচয় প্রদান করে থাকেন। তাঁর বর্ণ হরিত বা সবুজ এবং দুই পার্শ্বস্থিত দুটি পদ্মের উপর কুলচিহ্নস্বরূপ দুটি বিশ্ববজ্র প্রদর্শন করে থাকেন।
বুদ্ধশক্তি মামকী ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের শক্তিরূপে পরিগণিত হন। ‘দ্বেষরতি’ মন্ত্রপদ থেকে ঘনীভূত হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব। তিনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্য মূর্তি ধারণ করে স্বকুলের পরিচয় দেন এবং দুই পার্শ্বস্থিত পদ্মের উপর অক্ষোভ্যের প্রতীকচিহ্ন বজ্র প্রদর্শন করেন।
বজ্রসত্ত্বাত্মিকা ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধ বজ্রসত্ত্বের শক্তিরূপে পরিগণিত হন। তাঁর মন্ত্রপদ গুহ্যসমাজে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁর বর্ণ সাদা এবং তিনি দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি ও বাম হস্তে কপাল ধারণ করেন। তাঁর মূর্তি প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না, তবে বজ্রসত্ত্বের যুগনদ্ধ মূর্তিতে তাঁর রূপ কখনও কখনও দেখা যায়।
বুদ্ধশক্তি লোচনা বা রোচনা ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের শক্তিরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। ‘মোহরতি’ মন্ত্রপদ থেকে ঘনীভূত হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র বৈরোচন মূর্তি ধারণ করে নিজ কুলের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁর বর্ণ সাদা এবং তিনি দুই পার্শ্বস্থিত দুটি পদ্মের উপর দুটি চক্র কুলচিহ্ন স্বরূপ প্রদর্শন করেন।
বজ্রধাত্বীশ্বরী ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের শক্তিরূপে গণ্য হন। গুহ্যসমাজতন্ত্র অনুযায়ী ‘ঈর্ষ্যারতি’ মন্ত্রপদ থেকে ঘনীভূত হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র রত্নসম্ভব-মূর্তি ধারণ করে স্বকুলের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁর বর্ণ পীত বা হলদে এবং তাঁর দুই পার্শ্বস্থিত দুটি পদ্মের উপর দুটি রত্নচ্ছটা কুলচিহ্ন স্বরূপ প্রদর্শন করে থাকেন।
বুদ্ধশক্তি পাণ্ডরা বা পাণ্ডরবাসিনী ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের শক্তিরূপে গণ্য হন। ‘রাগরতি’ মন্ত্রপদ থেকে ঘনীভূত হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র অমিতাভ-মূর্তি ধারণ করে স্বকুলের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁর বর্ণ লাল এবং দুই পার্শ্বস্থিত প্রস্ফুটিত কমলের উপর কুলচিহ্নস্বরূপ দুটি পদ্ম প্রদর্শন করে থাকেন।
বুদ্ধশক্তি তারা ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির শক্তিরূপে গণ্য হন। গুহ্যসমাজের মতে ‘বজ্ররতি’ মন্ত্রপদ থেকে ঘনীভূত হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র অমোঘসিদ্ধির মূর্তি ধারণ করে স্বকুলের পরিচয় প্রদান করে থাকেন। তাঁর বর্ণ হরিত বা সবুজ এবং দুই পার্শ্বস্থিত দুটি পদ্মের উপর কুলচিহ্নস্বরূপ দুটি বিশ্ববজ্র প্রদর্শন করে থাকেন।
বুদ্ধশক্তি মামকী ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের শক্তিরূপে পরিগণিত হন। ‘দ্বেষরতি’ মন্ত্রপদ থেকে ঘনীভূত হয়ে মন্ত্রপুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব। তিনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্য মূর্তি ধারণ করে স্বকুলের পরিচয় দেন এবং দুই পার্শ্বস্থিত পদ্মের উপর অক্ষোভ্যের প্রতীকচিহ্ন বজ্র প্রদর্শন করেন।
বজ্রসত্ত্বাত্মিকা ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধ বজ্রসত্ত্বের শক্তিরূপে পরিগণিত হন। তাঁর মন্ত্রপদ গুহ্যসমাজে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁর বর্ণ সাদা এবং তিনি দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি ও বাম হস্তে কপাল ধারণ করেন। তাঁর মূর্তি প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না, তবে বজ্রসত্ত্বের যুগনদ্ধ মূর্তিতে তাঁর রূপ কখনও কখনও দেখা যায়।
এখানে উল্লেখ্য যে, কুল বা বংশ হিসেবে বজ্রযানে পাঁচটি কুলই প্রচলিত ছিলো। বজ্রসত্ত্বের কোন কুল ছিলো না। কুলপ্রবর্তক ধ্যানীবুদ্ধের একটি করে বিশেষ বর্ণ ছিলো এবং তাঁদের এক-একটি দিশা নির্দিষ্ট ছিলো। যে দেবতা যে বর্ণের প্রায়শ সেই বর্ণের ধ্যানীবুদ্ধের সন্ততিরূপে পরিগণিত। কিংবা মণ্ডলান্তর্বর্তী যে দিশায় যে দেবতা থাকেন, সেই দিশার ধ্যানীবুদ্ধের সন্ততি বলে তিনি গণ্য হন। এক্ষেত্রে বজ্রসত্ত্বের বর্ণ সাদা হওয়ায় তিনিও বৈরোচনের রূপান্তর বা তাঁর কুলভুক্ত বলে অনুমিত হয়।
পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পাঁচটি কুলের নাম যথাক্রমে মোহকুল, চিন্তামণিকুল, রাগকুল, সময়কুল ও দ্বেষকুল। মোহকুলের অধিপতি বৈরোচন, চিন্তামণিকুল রত্নসম্ভবের, রাগকুল অমিতাভের, সময়কুল অমোঘসিদ্ধির এবং দ্বেষকুলের অধিপতি অক্ষোভ্য। যাঁরা এই কুলের পূজাপদ্ধতি আচার-ব্যবহার মানেন, তাঁদেরকে কৌল বলা হয় এবং তাঁদের পূজাপদ্ধতিকে কুলাচার বলে।
পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পাঁচটি কুলের নাম যথাক্রমে মোহকুল, চিন্তামণিকুল, রাগকুল, সময়কুল ও দ্বেষকুল। মোহকুলের অধিপতি বৈরোচন, চিন্তামণিকুল রত্নসম্ভবের, রাগকুল অমিতাভের, সময়কুল অমোঘসিদ্ধির এবং দ্বেষকুলের অধিপতি অক্ষোভ্য। যাঁরা এই কুলের পূজাপদ্ধতি আচার-ব্যবহার মানেন, তাঁদেরকে কৌল বলা হয় এবং তাঁদের পূজাপদ্ধতিকে কুলাচার বলে।
প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের যেমন একটি শক্তি থাকে, তেমনই একটি বোধিসত্ত্ব থাকে। এই বোধিসত্ত্বগুলি মস্তকের উপর ক্ষুদ্র ধ্যানীবুদ্ধ-মূর্তি ধারণ করে নিজরে পরিচয় প্রদান করেন এবং স্ব স্ব কুলচিহ্ন ধারণ করেন। তাঁদের বর্ণভুজাদি ধ্যানীবুদ্ধেরই মতো, কিন্তু সাধারণত তাঁরা হয় দাঁড়িয়ে থাকেন নাহয় ললিতাসনে উপবিষ্ট থাকেন। তাঁদের বিশেষত্ব হলো, তাঁরা রাজোচিত বেশভূষাদিতে বিভূষিত থাকেন।
ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের বোধিসত্ত্বের নাম সমন্তভদ্র। তিনি যে কুল থেকে উৎপন্ন হন তার নাম মোহকুল। এই কুলের অন্য নাম তথাগতকুল। এই কুলের উৎপাদক বৈরোচন এবং তাঁর শক্তি লোচনা বা রোচনা। এই কুলোদ্ভব দেবতাদের রং সাদা এবং তাঁদের কুলচিহ্ন চক্র। সমন্তভদ্র সেজন্য চক্র ধারণ করেন এবং তাঁর বর্ণ সাদা। তিনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র বৈরোচন-মূর্তি ধারণ করে স্বকুলের পরিচয় প্রদান করে থাকেন।
ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের বোধিসত্ত্ব রত্নপাণি। তাঁদের কুলের নাম রত্নকুল। বুদ্ধশক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরী রত্নপাণির মাতৃরূপে পরিগণিত হন। এই কুলোৎপন্ন সকল দেবতার বর্ণ পীত বা হলদে এবং তাঁদের কুলচিহ্ন রত্ন। এই রত্ন হয় তাঁদের হাতে অঙ্কিত থাকে, কিংবা তাঁরা রত্ন হস্তে ধারণ করেন। আবার কখনও এই রত্ন পদ্মের উপর রক্ষিত থাকে। সমন্তভদ্রের বর্ণ পীত, তিনি হাতে রত্ন ধরে থাকেন এবং মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র রত্নসম্ভব-মূর্তি ধারণ করে নিজের পরিচয় দেন।
ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের বোধিসত্ত্বের নাম পদ্মপাণি। তিনি হস্তে পদ্ম ধরে থাকেন এবং তা থেকেই বুঝা যায় তিনি পদ্মকুলের অন্তর্গত। অমিতাভের ন্যায় তাঁরও বর্ণ লাল এবং তিনি কুলেশের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি মস্তকে ধারণ করেন। বুদ্ধশক্তি পাণ্ডরা বা পাণ্ডরবাসিনী তাঁর মাতৃরূপে গণ্য।
ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির বোধিসত্ত্বের নাম বিশ্বপাণি। তিনি কর্মকুলের অন্তর্গত এবং বুদ্ধশক্তি তারা তাঁর মাতৃরূপে গণ্য। তিনি হস্তে কুলচিহ্ন বিশ্ববজ্র প্রদর্শন করেন এবং স্বীয় পিতা অমোঘসিদ্ধির ক্ষুদ্র মূর্তি মস্তকে ধারণ করেন। তাঁর রং সবুজ। তাঁর কুলের আরেকটি নাম সময়কুল।
বজ্রপাণি ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের বোধিসত্ত্ব। তিনি হস্তে কুলচিহ্নরূপে বজ্র ধারণ করেন এবং মস্তকে একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্য-মূর্তিও ধারণ করেন। বুদ্ধশক্তি মামকী তাঁর মাতৃরূপে পরিগণিত। তিনি বজ্রকুলের অন্তর্গত।
এছাড়া ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধ বজ্রসত্ত্বের বোধিসত্ত্বের নাম ঘণ্টাপাণি। ঘণ্টাপাণির মায়ের নাম বজ্রশত্ত্বাত্মিকা। তাঁদের বর্ণ সাদা, কিন্তু তাঁদের কোনো বিশেষ কুল নেই। সম্ভবত সকলেই বৈরোচন কুলের অন্তর্গত। ঘণ্টাপাণি হতে ঘণ্টা ধারণ করে থাকেন। তবে এই বোধিসত্ত্বের মূতি বিরল।
ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের বোধিসত্ত্বের নাম সমন্তভদ্র। তিনি যে কুল থেকে উৎপন্ন হন তার নাম মোহকুল। এই কুলের অন্য নাম তথাগতকুল। এই কুলের উৎপাদক বৈরোচন এবং তাঁর শক্তি লোচনা বা রোচনা। এই কুলোদ্ভব দেবতাদের রং সাদা এবং তাঁদের কুলচিহ্ন চক্র। সমন্তভদ্র সেজন্য চক্র ধারণ করেন এবং তাঁর বর্ণ সাদা। তিনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র বৈরোচন-মূর্তি ধারণ করে স্বকুলের পরিচয় প্রদান করে থাকেন।
ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের বোধিসত্ত্ব রত্নপাণি। তাঁদের কুলের নাম রত্নকুল। বুদ্ধশক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরী রত্নপাণির মাতৃরূপে পরিগণিত হন। এই কুলোৎপন্ন সকল দেবতার বর্ণ পীত বা হলদে এবং তাঁদের কুলচিহ্ন রত্ন। এই রত্ন হয় তাঁদের হাতে অঙ্কিত থাকে, কিংবা তাঁরা রত্ন হস্তে ধারণ করেন। আবার কখনও এই রত্ন পদ্মের উপর রক্ষিত থাকে। সমন্তভদ্রের বর্ণ পীত, তিনি হাতে রত্ন ধরে থাকেন এবং মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র রত্নসম্ভব-মূর্তি ধারণ করে নিজের পরিচয় দেন।
ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের বোধিসত্ত্বের নাম পদ্মপাণি। তিনি হস্তে পদ্ম ধরে থাকেন এবং তা থেকেই বুঝা যায় তিনি পদ্মকুলের অন্তর্গত। অমিতাভের ন্যায় তাঁরও বর্ণ লাল এবং তিনি কুলেশের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি মস্তকে ধারণ করেন। বুদ্ধশক্তি পাণ্ডরা বা পাণ্ডরবাসিনী তাঁর মাতৃরূপে গণ্য।
ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির বোধিসত্ত্বের নাম বিশ্বপাণি। তিনি কর্মকুলের অন্তর্গত এবং বুদ্ধশক্তি তারা তাঁর মাতৃরূপে গণ্য। তিনি হস্তে কুলচিহ্ন বিশ্ববজ্র প্রদর্শন করেন এবং স্বীয় পিতা অমোঘসিদ্ধির ক্ষুদ্র মূর্তি মস্তকে ধারণ করেন। তাঁর রং সবুজ। তাঁর কুলের আরেকটি নাম সময়কুল।
বজ্রপাণি ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের বোধিসত্ত্ব। তিনি হস্তে কুলচিহ্নরূপে বজ্র ধারণ করেন এবং মস্তকে একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্য-মূর্তিও ধারণ করেন। বুদ্ধশক্তি মামকী তাঁর মাতৃরূপে পরিগণিত। তিনি বজ্রকুলের অন্তর্গত।
এছাড়া ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধ বজ্রসত্ত্বের বোধিসত্ত্বের নাম ঘণ্টাপাণি। ঘণ্টাপাণির মায়ের নাম বজ্রশত্ত্বাত্মিকা। তাঁদের বর্ণ সাদা, কিন্তু তাঁদের কোনো বিশেষ কুল নেই। সম্ভবত সকলেই বৈরোচন কুলের অন্তর্গত। ঘণ্টাপাণি হতে ঘণ্টা ধারণ করে থাকেন। তবে এই বোধিসত্ত্বের মূতি বিরল।
বোধিসত্ত্ব শব্দের দুইটি অংশ, একটি বোধি ও অপরটি সত্ত্ব। বোধি বলতে জগৎকারণ অনাদি অনন্ত শূন্যের জ্ঞান বুঝায় এবং সত্ত্ব বলতে সার বা মূল উপাদান বুঝায়। সে কারণে বোধিসত্ত্ব শব্দের অর্থ যে-সকল দেবতার শূন্যই হলো আসল উপাদান। বোধিসত্ত্ব শূন্যেরই অশেষ গুণের এক-একটি গুণের প্রতিমূর্তি স্বরূপ। যেমন, একজন বোধিসত্ত্বের নাম অক্ষয়মতি বা যে মতির ক্ষয় নেই, আরেক জনের নাম অমিতপ্রভ অর্থাৎ অপরিমিত প্রভাবিশিষ্ট, অপরের নাম সমন্তভদ্র অর্থাৎ সম্পূর্ণ মঙ্গলময় ইত্যাদি। তা থেকে বোঝা যায় বোধিসত্ত্ব জগৎ-কারণ শূন্যের একেকটি গুণের প্রতিরূপ।
মূর্তিশাস্ত্রে বোধিসত্ত্ব একটি বিশেষ শ্রেণির দেবতা। তাঁরা সকলেই পুং দেবতা। স্ত্রী দেবতাদের শক্তি নামে অভিহিত করা হয়। বোধিসত্ত্বের প্রত্যেকের একটি কুল আছে এবং তাঁরা সকলেই এক-একজন ধ্যানীবুদ্ধ থেকে উৎপন্ন। যখন তাঁদের মূর্তি প্রস্তুত করা হয় কিংবা রূপ কল্পনা করা হয় তখন তাঁদের মস্তকে একটি ধ্যানীবুদ্ধের ক্ষুদ্রমূর্তি দেয়া হয়। এই ক্ষুদ্রমূর্তি দেখেই তাঁদের উৎপত্তি ও কুল স্থির করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও বোধিসত্ত্বেরা তাঁদের নিজ নিজ শক্তির সাথে বিরাজমান থাকেন।
সাধারণত বোধিসত্ত্বের সংখ্যা ষোলটি। নিষ্পন্নযোগাবলী গ্রন্থে তিনটি বোধিসত্ত্বের তালিকা দেওয়া আছে। তবে নামগুলি অনুধাবন করলে দেখা যায় বোধিসত্ত্বের সংখ্যা ষোলটিরও অধিক। যেমন সমন্তভদ্র, অক্ষয়মতি, ক্ষিতিগর্ভ, আকাশগর্ভ, গগনগঞ্জ, রত্নপাণি, সাগরমতি, বজ্রগর্ভ, অবলোকিতেশ্বর, মহাস্থামপ্রাপ্ত, চন্দ্রপ্রভ, জালিনীপ্রভ, অমিতপ্রভ, প্রতিভানকূট, সর্বশোকত-মোনির্ঘাতমতি, সর্বনিবরণ-বিষ্কম্ভী, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, গন্ধহস্তী, জ্ঞানকেতু, ভদ্রপাল, সর্বাপায়ঞ্জহ, অমোঘদর্শী, সুরঙ্গম, বজ্রপাণি। এই বোধিসত্ত্বদের প্রত্যেকের আবার বিভিন্ন ধ্যানভেদে বিভিন্ন নামে বিচিত্র রূপকল্পনা করতে দেখা যায়। একইভাবে তাঁদের শক্তি হিসেবেও বিভিন্ন নামে অসংখ্য দেবীর কল্পনা বোধিসত্ত্ব মণ্ডলে দেখতে পাওয়া যায়।
মূর্তিশাস্ত্রে বোধিসত্ত্ব একটি বিশেষ শ্রেণির দেবতা। তাঁরা সকলেই পুং দেবতা। স্ত্রী দেবতাদের শক্তি নামে অভিহিত করা হয়। বোধিসত্ত্বের প্রত্যেকের একটি কুল আছে এবং তাঁরা সকলেই এক-একজন ধ্যানীবুদ্ধ থেকে উৎপন্ন। যখন তাঁদের মূর্তি প্রস্তুত করা হয় কিংবা রূপ কল্পনা করা হয় তখন তাঁদের মস্তকে একটি ধ্যানীবুদ্ধের ক্ষুদ্রমূর্তি দেয়া হয়। এই ক্ষুদ্রমূর্তি দেখেই তাঁদের উৎপত্তি ও কুল স্থির করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও বোধিসত্ত্বেরা তাঁদের নিজ নিজ শক্তির সাথে বিরাজমান থাকেন।
সাধারণত বোধিসত্ত্বের সংখ্যা ষোলটি। নিষ্পন্নযোগাবলী গ্রন্থে তিনটি বোধিসত্ত্বের তালিকা দেওয়া আছে। তবে নামগুলি অনুধাবন করলে দেখা যায় বোধিসত্ত্বের সংখ্যা ষোলটিরও অধিক। যেমন সমন্তভদ্র, অক্ষয়মতি, ক্ষিতিগর্ভ, আকাশগর্ভ, গগনগঞ্জ, রত্নপাণি, সাগরমতি, বজ্রগর্ভ, অবলোকিতেশ্বর, মহাস্থামপ্রাপ্ত, চন্দ্রপ্রভ, জালিনীপ্রভ, অমিতপ্রভ, প্রতিভানকূট, সর্বশোকত-মোনির্ঘাতমতি, সর্বনিবরণ-বিষ্কম্ভী, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, গন্ধহস্তী, জ্ঞানকেতু, ভদ্রপাল, সর্বাপায়ঞ্জহ, অমোঘদর্শী, সুরঙ্গম, বজ্রপাণি। এই বোধিসত্ত্বদের প্রত্যেকের আবার বিভিন্ন ধ্যানভেদে বিভিন্ন নামে বিচিত্র রূপকল্পনা করতে দেখা যায়। একইভাবে তাঁদের শক্তি হিসেবেও বিভিন্ন নামে অসংখ্য দেবীর কল্পনা বোধিসত্ত্ব মণ্ডলে দেখতে পাওয়া যায়।
সবাই জানেন গৌতম বুদ্ধ শাক্যসিংহ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। কিন্তু তা হলেই ধর্মটি আধুনিক ও অর্বাচীন হয়ে যায়। তাই বৌদ্ধেরা বলতো বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের পূর্বেও ছিলো। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন শেষ বুদ্ধ। তাঁর পূর্বে অন্তত চব্বিশ জন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিলো। ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে, ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধের তালিকা দেখলে প্রায় বত্রিশটি নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে শেষ সাতটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং তাঁদেরকে মানুষী বুদ্ধ আখ্যা দেওয়া হয়।
মানুষী বুদ্ধ সাতটি। তাঁদের নাম সময়ের অনুক্রমে বিপশ্যী, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কশ্যপ ও শাক্যসিংহ। এই সাতটি নামের মধ্যে শেষ তিন জন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে হয়। প্রত্যেক মানুষী বুদ্ধের এক-একটি বিশেষ বোধিবৃক্ষ ছিলো। মূর্তিতে প্রতিবিম্বিত হলে সাতজনকেই দেখতে এক রকম। তাঁদের বর্ণ এক এবং তাঁরা ধ্যানাসনে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকেন কিংবা দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁদের একটি মুখ ও দুটি হাত। উপবিষ্ট মূর্তিতে একটি হাত কোলের উপর থাকে, আরেকটিতে দক্ষিণে ভূমিস্পর্শমুদ্রা প্রদর্শিত হয়। সাধারণত তাঁদের রং পীত স্বর্ণের ন্যায়। তাঁদের প্রত্যেকের উপর একটি বোধিবৃক্ষ থাকে। কোনো কোনো মূর্তিতে সাতজনকেই দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো মূর্তিতে ভাবিবুদ্ধ মৈত্রেয়কেও বোধিসত্ত্বরূপে দেখতে পাওয়া যায়।
মানুষী বুদ্ধেরও শক্তি কল্পিত হয়েছিলো। রূপ-কল্পনা হয়েছিলো কি না তা জানা যায় না। তাঁদের নাম যথাক্রমে– বিপশ্যন্তী, শিখিমালিনী, বিশ্বধরা, ককুদ্বতী, কণ্ঠমালিনী, মহীধরা ও যশোধরা।
সাতটি মানুষী বুদ্ধের সাতটি বোধিসত্ত্বও কল্পিত হয়েছিলো। তাদের মধ্যে আনন্দ ও তাঁর মাতা যশোধরা পণ্ডিতদের নিকট পরিচিত। সাতটি বোধিসত্ত্বের নাম যথাক্রমে– মহামতি, রত্নধর, আকাশগঞ্জ, শকমঙ্গল, কনকরাজ, ধর্মধর ও আনন্দ। তবে তাঁদের মূর্তি অলভ্য।
বজ্রযান দেবসংঘে গৌতম বুদ্ধের স্থান প্রায় নেই বললেই চলে। ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে, যদি তাঁকে কখনও প্রতিমূর্তিত করা হয় তাহলে তিনি দেখতে অক্ষোভ্যের ন্যায় হন। তাঁর তখন নাম হয় বজ্রাসন। নিষ্পন্নযোগাবলীতে দুর্গতিপরিশোধন মণ্ডলেও তাঁর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে ভগবান বুদ্ধকে ‘শ্রীশাক্যসিংহো ভগবান্ মহাবৈরোচনঃ’ অর্থাৎ বৈরোচন রূপে কল্পনা করা হয়েছে।
মানুষী বুদ্ধ সাতটি। তাঁদের নাম সময়ের অনুক্রমে বিপশ্যী, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কশ্যপ ও শাক্যসিংহ। এই সাতটি নামের মধ্যে শেষ তিন জন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে হয়। প্রত্যেক মানুষী বুদ্ধের এক-একটি বিশেষ বোধিবৃক্ষ ছিলো। মূর্তিতে প্রতিবিম্বিত হলে সাতজনকেই দেখতে এক রকম। তাঁদের বর্ণ এক এবং তাঁরা ধ্যানাসনে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকেন কিংবা দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁদের একটি মুখ ও দুটি হাত। উপবিষ্ট মূর্তিতে একটি হাত কোলের উপর থাকে, আরেকটিতে দক্ষিণে ভূমিস্পর্শমুদ্রা প্রদর্শিত হয়। সাধারণত তাঁদের রং পীত স্বর্ণের ন্যায়। তাঁদের প্রত্যেকের উপর একটি বোধিবৃক্ষ থাকে। কোনো কোনো মূর্তিতে সাতজনকেই দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো মূর্তিতে ভাবিবুদ্ধ মৈত্রেয়কেও বোধিসত্ত্বরূপে দেখতে পাওয়া যায়।
মানুষী বুদ্ধেরও শক্তি কল্পিত হয়েছিলো। রূপ-কল্পনা হয়েছিলো কি না তা জানা যায় না। তাঁদের নাম যথাক্রমে– বিপশ্যন্তী, শিখিমালিনী, বিশ্বধরা, ককুদ্বতী, কণ্ঠমালিনী, মহীধরা ও যশোধরা।
সাতটি মানুষী বুদ্ধের সাতটি বোধিসত্ত্বও কল্পিত হয়েছিলো। তাদের মধ্যে আনন্দ ও তাঁর মাতা যশোধরা পণ্ডিতদের নিকট পরিচিত। সাতটি বোধিসত্ত্বের নাম যথাক্রমে– মহামতি, রত্নধর, আকাশগঞ্জ, শকমঙ্গল, কনকরাজ, ধর্মধর ও আনন্দ। তবে তাঁদের মূর্তি অলভ্য।
বজ্রযান দেবসংঘে গৌতম বুদ্ধের স্থান প্রায় নেই বললেই চলে। ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে, যদি তাঁকে কখনও প্রতিমূর্তিত করা হয় তাহলে তিনি দেখতে অক্ষোভ্যের ন্যায় হন। তাঁর তখন নাম হয় বজ্রাসন। নিষ্পন্নযোগাবলীতে দুর্গতিপরিশোধন মণ্ডলেও তাঁর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে ভগবান বুদ্ধকে ‘শ্রীশাক্যসিংহো ভগবান্ মহাবৈরোচনঃ’ অর্থাৎ বৈরোচন রূপে কল্পনা করা হয়েছে।
বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মূর্তির প্রত্ন-নিদর্শন ও মূর্তি-প্রমাণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই বৌদ্ধ দেবদেবী প্রসঙ্গে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের যে গবেষণামূলক গভীর পর্যবেক্ষণ রয়েছে তার কিছু কিছু উদ্ধৃতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।–
‘বজ্রযানের দেবদেবীর আয়তন বহু বিস্তৃত…। নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালী সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা যে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার স্বল্পমাত্র অংশই আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাঁহারা বহু দেবদেবীর স্তুতি ও অর্চনা করিয়া এই সব গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বজ্রসত্ত্ব, হেবজ্র, হেরুক, মহামায়া, ত্রৈলোক্যবশঙ্কর, নীলাম্বরধর-বজ্রপাণি, যমারি, কৃষ্ণযমারি, জম্ভল, হয়গ্রীব, সম্বর, চক্রসম্বর, চক্রেশ্বরালী, কালি, মহামায়া, বজ্রযোগিনী, সিদ্ধবজ্রযোগিনী, কুলুকুল্লা, বজ্রভৈরব, বজ্রধর, হেবজ্রোদ্ভব, সিতাতপত্রা-অপরাজিতা, উষ্ণীষ-বিজয়া প্রভৃতিরাই প্রধান। উল্লিখিত সকল দেবদেবীর মূর্তি-প্রমাণ যেমন বাঙলাদেশে পাওয়া যায় নাই তেমনই আবার এমন অনেক বজ্রযানী দেবদেবীদের প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাঁহাদের উল্লেখ এই সব গ্রন্থে দেখিতেছি না। যাহা হউক যথার্থ বজ্রযানী দেবদেবীদের কথা বলিবার আগে মহাযানী ও সাধারণভাবে বুদ্ধযানী দুই চারিটি মূর্তি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কথা বলিয়া লই।’
‘গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের…প্রায় সব বৌদ্ধ-প্রতিমাই মহাযান-বজ্রযান তন্ত্রের সন্দেহ নাই; তবে সাধারণ বুদ্ধযানী প্রতিমাও কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধরনের প্রতিমার কেন্দ্রে অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া শাক্যসিংহ বা বোধিসত্ত্ব গৌতম বা বুদ্ধ ভূমিস্পর্শ বা ধ্যান বা ধর্মচক্র-প্রবর্তন মুদ্রায় উপবিষ্ট; এবং তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বুদ্ধায়নের (অর্থাৎ বুদ্ধের জীবনের) প্রধান প্রধান কয়েকটি কাহিনীর প্রতিকৃতি রূপায়িত।… যতগুলি বুদ্ধমূর্তি বাঙলায় পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে অভয়, ব্যাখ্যান, ভূমিস্পর্শ ও ধর্মচক্র-মুদ্রায় উপবিষ্ট প্রতিমাই বেশি। ফরিদপুর জেলার উজানী গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) একাদশ শতকীয় একটি ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ-প্রতিমার পাদপীঠে বজ্র ও সপ্তরত্ন উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; এই দুইটি লক্ষণই যেন গভীর অর্থবহ।’
‘মহাযানী দেবায়তন আদিবুদ্ধ ও তাঁহার শক্তি (?) আদিপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতার ধ্যান-কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি এই পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধ বা পঞ্চ তথাগত এবং ষষ্ঠ আর একটি দেবতা বজ্রসত্ত্ব এই আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত। ধ্যানীবুদ্ধরা সকলেই যোগরত; কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক এক জন সক্রিয় বোধিসত্ত্ব এবং এক একজন মানুষীবুদ্ধ বিরাজমান। মহাযানীদের মতে বর্তমান কাল ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের কাল; তাঁহার বোধিসত্ত্ব হইতেছেন অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ এবং মানুষীবুদ্ধ হইতেছেন বুদ্ধ গৌতম। অবলোকিতেশ্বর ছাড়া মহাযান দেবায়তনে পঞ্চ বোধিসত্ত্বের মধ্যে আরও দুইটি বোধিসত্ত্বের– মঞ্জুশ্রী এবং মৈত্রেয়ের– প্রতিপত্তি প্রবল। তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একটি শক্তি; এই শক্তিময়ীরা সকলেই তারা নামে খ্যাতা এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দেশকালপ্রভেদে বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি। বোধিসত্ত্বদের সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য; বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন তাঁহাদের নাম।’
‘ধ্যানীবুদ্ধদের দুই একটি মূর্তি বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বিক্রমপুরে, এখন তাহা রাজশাহী-চিত্রশালায়। ঢাকা জেলার সুখবাসপুর গ্রামে একটি লিপি-উৎকীর্ণ দশম-শতকীয় বজ্রধারী বজ্রসত্ত্ব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দুইটি প্রতিমাই উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ধ্যানীবুদ্ধের প্রতিমা খুব সহজলভ্য নয়। আদিবুদ্ধের কোনো প্রতিমাও এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, কিন্তু দুই একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাহাদের আদিপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতিমা বলা যাইতে পারে; একটি ঢাকা-চিত্রশালায় ও আর একটি রাজশাহী-চিত্রশালায় রক্ষিত। ধর্মশ্রীপাল নামক এক ভিক্ষু বনবাসী (কর্ণাট-দেশ) হইতে উত্তরবঙ্গে আসিয়া একটি প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এই মূর্তিটি এখন কলিকাতা-চিত্রশালায়।’
‘বাঙলাদেশে যত মহাযানী-বজ্রযানী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে নানা রূপের অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথের প্রতিমাই সবচেয়ে বেশি। প্রতিমা-প্রমাণ হইতে মনে হয়, বৌদ্ধ বাঙালীর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় দেবতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের এবং সূর্যের রূপ ও গুণ লইয়া বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথ এবং তাঁহার বিচিত্র রূপ ও গুণাবলী লইয়া অসংখ্য বিচিত্র তাঁহার প্রতিমারূপ। কিন্তু বাঙলাদেশে তাঁহার যত রূপ দেখিতেছি তাহার মধ্যে পদ্মপাণি, সিংহনাদ, ষড়ক্ষরী ও খসর্পণ রূপই প্রধান। আসন ও স্থানক দুই রকমের পদ্মপাণি-মূর্তিই গোচর।’
‘অবলোকিতেশ্বরের পরই যে-বোধিসত্ত্ব বাঙালীর প্রিয় ছিলেন তিনি ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের অধ্যাত্মপুত্র, জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভার দেবতা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী। মঞ্জুশ্রীরও বিচিত্র রূপ।… বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের মূর্তি পাওয়া যায় নাই বলিলেই চলে।’
‘মহাযান-বজ্রযানের আরও যে কয়েকটি নিম্নস্তরের দেবতা বাঙলাদেশে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জম্ভল, হেরুক ও হেবজ্রই প্রধান। জম্ভল ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের সঙ্গে যুক্ত, হেরুক অক্ষোভ্য হইতে উদ্ভূত এবং হেবজ্র স্পষ্টতই তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবতা। জম্ভল ব্রাহ্মণ্য কুবেরের বৌদ্ধ প্রতিরূপ এবং তাঁহার প্রতিমা বাঙলাদেশের, বিশেষত পূর্ব ও উত্তর-বাঙলার, নানা জায়গা হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধন ও ঐশ্বর্যের এই দেবতা যে জনসাধারণের খুব প্রিয় ছিলেন, অসংখ্য মূর্তি-প্রমাণেই তাহা সুস্পষ্ট।… জম্ভলের তুলনায় হেরুকের মূর্তি কিন্তু কমই পাওয়া গিয়াছে।… শক্তির দৃঢ়ালিঙ্গনবদ্ধ হেবজ্রের মূর্তি একাধিক পাওয়া গিয়াছে।…’
‘দেবতাদের কথা শেষ হইল; এইবার মহাযান-বজ্রযান আয়তনের দেবীদের কথা বলা যাইতে পারে। এই দেবীদের মধ্যে তারা সর্বশ্রেষ্ঠা। তারার অনেক রূপভেদ; বিভিন্নরূপ বিভিন্ন ধ্যানীবুদ্ধ হইতে উৎপন্ন। বাঙলাদেশে যত প্রকারের তারামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে খদিরবনী-তারা (খয়ের বনের তারা ?) বজ্র-তারা এবং ভৃকুটী-তারাই প্রধান। খদিরবনী-তারার অপর নাম শ্যাম-তারা; তাঁহার ধ্যানীবুদ্ধ হইতেছেন অমোঘসিদ্ধি; বজ্র-তারার ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভব এবং ভৃকুটী-তারার, অমিতাভ। অশোককান্তা (মারীচী) ও একজটাসহ খদিরবনী বা শ্যাম-তারার মূর্তিই সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়াছে। নীলোৎপলধৃতা এই দেবী কখনও উপবিষ্টা, কখনও দণ্ডায়মানা।… ঢাকা জেলার ভবানীপুর গ্রামে ত্রি-শির, অষ্টহস্ত, বীরাসনোপবিষ্ট, পাদপীঠে গণেশের মূর্তি উৎকীর্ণ এবং মৌলিতে অমিতাভ মূর্তিযুক্ত একটি দেবীমূতি পাওয়া গিয়াছে। ভট্টশালী-মহাশয় বলিয়াছেন, প্রতিমাটি ভৃকুটী-তারার। কিন্তু এই প্রতিমাটির সঙ্গে ঢাকা-চিত্রশালার আর একটি প্রতিমার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, শেষোক্ত প্রতিমাটি পঞ্চরক্ষামণ্ডলভুক্ত দেবী মহাপ্রতিসরার। প্রথমোক্ত প্রতিমাটির বাম দিকে ঝাঁটা ও কুলা হস্তে যে দেবীটি দাঁড়াইয়া আছেন তিনি তো একটি গ্রাহ্য দেবী (বোধ হয় শীতলা বলিয়াই মনে হইতেছে)।… অষ্টভূজা সিতাতপত্রার একটি ধাতব মূর্তি ঢাকা-চিত্রশালায় আছে।’
‘বজ্রযানী অন্যান্য দেবী মূর্তির মধ্যে মারীচী, পর্ণশবরী, হারীতী এবং চুণ্ডাই প্রধান। ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন-সম্ভূত মারীচীর কয়েকটি প্রতিমা বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ত্রিমুখ (বাম মুখ শঙ্করীর), সপ্তশূকরবাহিত এবং রাহুসারথি, রথে প্রত্যালীঢ়ভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা এই দেবীটি ব্রাহ্মণ্য সূর্যেরই বৌদ্ধ প্রতিরূপ।… পর্ণশবরীর ধ্যানীবুদ্ধ বোধ হয় অমোঘসিদ্ধি। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে দুইটি ত্রি-শির, ষড়ভূজা, পর্ণাচ্ছাদন-পরিহিতা পর্ণশবরী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। ধ্যানে তাঁহাকে বলা হইয়াছে ‘পিশাচী’। রাজশাহী জেলার নিয়ামতপুরে অষ্টাদশভূজা চুণ্ডা দেবীর একটি নবম-শতকীয় প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে (রাজশাহী-চিত্রশালা)।… বজ্রযানী দেবী উষ্ণীষ-বিজয়ার একটি ভগ্ন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বীরভূম জেলায়। হারীতী জম্ভলের শক্তি, তিনি ধনৈশ্চর্যের দেবী এবং ব্রাহ্মণ্য ষষ্ঠীর বৌদ্ধ প্রতিরূপ। ঢাকা ও রাজশাহী-চিত্রশালায় চার পাঁচটি হারীতীর প্রতিমা রক্ষিত আছে।’
‘এই সব অসংখ্য মহাযানী দেবদেবীর পূজার্চনার জন্য মন্দিরও অবশ্যই অসংখ্য রচিত হইয়াছিল বাঙলার নানা জায়গায়। বিভিন্ন বিহারগুলির সঙ্গে সঙ্গেও মন্দির নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বাঙলার কোন্ প্রান্তে কোথায় কোন্ দেবদেবীর মন্দির ছিল, কোথায় কে পূজা পাইতেন, আজ আর তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে, একাদশ শতকের অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে বাঙলাদেশের কয়েকটি মহাযানী বজ্রযানী বৌদ্ধ মন্দিরের একং কোন্ মন্দিরে কাহার পূজা হইত তাহার একটু ইঙ্গিত আছে। তাহা হইতে বুঝা যায়, চন্দ্রদ্বীপে (নিম্নবঙ্গের খুলনা-বরিশাল অঞ্চলে) ভগবতী-তারার একটি মন্দির, সমতটে লোকনাথের দুইটি এবং বুদ্ধর্ধি-তারার একটি, পট্টিকেরক রাজ্যে চুণ্ডাবর ভবনে চুণ্ডা-দেবীর একটি এবং হরিকেলদেশে লোকনাথের একটি মন্দির ছিল।’
‘এ-পর্যন্ত যত মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদির কথা বলিলাম সেগুলির প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, উত্তর ও পূর্ব-বাঙলা (গঙ্গার পূর্বতীর হইতে), বিশেষভাবে রাজশাহী-দিনাজপুর-বগুড়া জেলায় এবং ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরা জেলায় যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বাঙলার অন্যত্র কোথাও তেমন নয়। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বজ্রযানী-তন্ত্রের প্রতিমা পাওয়া প্রায় যায় নাই বলিলেই চলে, এক বাঁকুড়া-বীরভূমের কিয়দংশ ছাড়া। মনে হয়, মহাযান-বজ্রযান তন্ত্রের প্রসার ও প্রতিপত্তি উত্তর ও পূর্ব-বাঙলায় যতটা ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমে ততটা ছিল না, দক্ষিণ-রাঢ়ে তো নয়ই। প্রায় দশম শতক হইতেই নালন্দার প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতে থাকে এবং বিক্রমশীল-সোমপুর প্রভৃতি তাহার স্থান অধিকার করে। বিক্রমশীল-বিহার এবং ফুল্লহরি-বিহার বাঙলাদেশে না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু সোমপুর, জগদ্দল এবং দেবীকোট বিহার ছিল নিঃসংশয়ে উত্তর-বঙ্গে; পণ্ডিত-বিহার, পট্টিকেরক-বিহার ও বিক্রমপুরী-বিহার নিঃসংশয়ে পূর্ববঙ্গে। রাঢ়দেশের একটি মাত্র বিহারের নাম পাইতেছি, ত্রৈকূটক বিহার, কিন্তু তাহাও নিঃসংশয়ে রাঢ়দেশে কিনা বলা যায় না। সিদ্ধাচার্যদের জন্মস্থান ও আদি পরিবেশ বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, তাঁহারা অধিকাংশই উত্তর ও পূর্ববঙ্গের লোক। অথচ, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ-রাঢ়ে সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমা মিলিতেছে প্রচুর। মনে হয়, এক বাঁকুড়া-বীরভূমের কিয়দংশ ছাড়া রাঢ়ের অন্যত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমন ছিল না। এই তথ্য সমসাময়িক ও মধ্যযুগীয় বাঙলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক হইতে গভীর অর্থবহ। ইহাও লক্ষণীয় যে, বাঁকুড়া-বীরভূমের যে অংশে মহাযান-বজ্রযান সক্রিয় সেই অংশেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রসার, প্রভাব ও প্রতিপত্তি।’
‘লিপি-প্রমাণ ও শৈলী-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বৌদ্ধ প্রতিমাগুলির তারিখ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, পাল-পূর্ব যুগের বৌদ্ধ মূর্তি খুব বেশি পাওয়া যায় নাই; যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই– দুই চারিটি বিক্ষিপ্ত মূর্তি ছাড়া– মোটামুটি নবম হইতে একাদশ শতকের এবং এই তিনশত বৎসরই বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণযুগ।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৫৩৩-৩৭)
‘বজ্রযানের দেবদেবীর আয়তন বহু বিস্তৃত…। নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালী সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা যে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার স্বল্পমাত্র অংশই আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাঁহারা বহু দেবদেবীর স্তুতি ও অর্চনা করিয়া এই সব গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বজ্রসত্ত্ব, হেবজ্র, হেরুক, মহামায়া, ত্রৈলোক্যবশঙ্কর, নীলাম্বরধর-বজ্রপাণি, যমারি, কৃষ্ণযমারি, জম্ভল, হয়গ্রীব, সম্বর, চক্রসম্বর, চক্রেশ্বরালী, কালি, মহামায়া, বজ্রযোগিনী, সিদ্ধবজ্রযোগিনী, কুলুকুল্লা, বজ্রভৈরব, বজ্রধর, হেবজ্রোদ্ভব, সিতাতপত্রা-অপরাজিতা, উষ্ণীষ-বিজয়া প্রভৃতিরাই প্রধান। উল্লিখিত সকল দেবদেবীর মূর্তি-প্রমাণ যেমন বাঙলাদেশে পাওয়া যায় নাই তেমনই আবার এমন অনেক বজ্রযানী দেবদেবীদের প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাঁহাদের উল্লেখ এই সব গ্রন্থে দেখিতেছি না। যাহা হউক যথার্থ বজ্রযানী দেবদেবীদের কথা বলিবার আগে মহাযানী ও সাধারণভাবে বুদ্ধযানী দুই চারিটি মূর্তি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কথা বলিয়া লই।’
‘গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের…প্রায় সব বৌদ্ধ-প্রতিমাই মহাযান-বজ্রযান তন্ত্রের সন্দেহ নাই; তবে সাধারণ বুদ্ধযানী প্রতিমাও কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধরনের প্রতিমার কেন্দ্রে অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া শাক্যসিংহ বা বোধিসত্ত্ব গৌতম বা বুদ্ধ ভূমিস্পর্শ বা ধ্যান বা ধর্মচক্র-প্রবর্তন মুদ্রায় উপবিষ্ট; এবং তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বুদ্ধায়নের (অর্থাৎ বুদ্ধের জীবনের) প্রধান প্রধান কয়েকটি কাহিনীর প্রতিকৃতি রূপায়িত।… যতগুলি বুদ্ধমূর্তি বাঙলায় পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে অভয়, ব্যাখ্যান, ভূমিস্পর্শ ও ধর্মচক্র-মুদ্রায় উপবিষ্ট প্রতিমাই বেশি। ফরিদপুর জেলার উজানী গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) একাদশ শতকীয় একটি ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ-প্রতিমার পাদপীঠে বজ্র ও সপ্তরত্ন উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; এই দুইটি লক্ষণই যেন গভীর অর্থবহ।’
‘মহাযানী দেবায়তন আদিবুদ্ধ ও তাঁহার শক্তি (?) আদিপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতার ধ্যান-কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি এই পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধ বা পঞ্চ তথাগত এবং ষষ্ঠ আর একটি দেবতা বজ্রসত্ত্ব এই আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত। ধ্যানীবুদ্ধরা সকলেই যোগরত; কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক এক জন সক্রিয় বোধিসত্ত্ব এবং এক একজন মানুষীবুদ্ধ বিরাজমান। মহাযানীদের মতে বর্তমান কাল ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের কাল; তাঁহার বোধিসত্ত্ব হইতেছেন অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ এবং মানুষীবুদ্ধ হইতেছেন বুদ্ধ গৌতম। অবলোকিতেশ্বর ছাড়া মহাযান দেবায়তনে পঞ্চ বোধিসত্ত্বের মধ্যে আরও দুইটি বোধিসত্ত্বের– মঞ্জুশ্রী এবং মৈত্রেয়ের– প্রতিপত্তি প্রবল। তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একটি শক্তি; এই শক্তিময়ীরা সকলেই তারা নামে খ্যাতা এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দেশকালপ্রভেদে বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি। বোধিসত্ত্বদের সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য; বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন তাঁহাদের নাম।’
‘ধ্যানীবুদ্ধদের দুই একটি মূর্তি বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বিক্রমপুরে, এখন তাহা রাজশাহী-চিত্রশালায়। ঢাকা জেলার সুখবাসপুর গ্রামে একটি লিপি-উৎকীর্ণ দশম-শতকীয় বজ্রধারী বজ্রসত্ত্ব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দুইটি প্রতিমাই উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ধ্যানীবুদ্ধের প্রতিমা খুব সহজলভ্য নয়। আদিবুদ্ধের কোনো প্রতিমাও এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, কিন্তু দুই একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাহাদের আদিপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতিমা বলা যাইতে পারে; একটি ঢাকা-চিত্রশালায় ও আর একটি রাজশাহী-চিত্রশালায় রক্ষিত। ধর্মশ্রীপাল নামক এক ভিক্ষু বনবাসী (কর্ণাট-দেশ) হইতে উত্তরবঙ্গে আসিয়া একটি প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এই মূর্তিটি এখন কলিকাতা-চিত্রশালায়।’
‘বাঙলাদেশে যত মহাযানী-বজ্রযানী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে নানা রূপের অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথের প্রতিমাই সবচেয়ে বেশি। প্রতিমা-প্রমাণ হইতে মনে হয়, বৌদ্ধ বাঙালীর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় দেবতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের এবং সূর্যের রূপ ও গুণ লইয়া বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথ এবং তাঁহার বিচিত্র রূপ ও গুণাবলী লইয়া অসংখ্য বিচিত্র তাঁহার প্রতিমারূপ। কিন্তু বাঙলাদেশে তাঁহার যত রূপ দেখিতেছি তাহার মধ্যে পদ্মপাণি, সিংহনাদ, ষড়ক্ষরী ও খসর্পণ রূপই প্রধান। আসন ও স্থানক দুই রকমের পদ্মপাণি-মূর্তিই গোচর।’
‘অবলোকিতেশ্বরের পরই যে-বোধিসত্ত্ব বাঙালীর প্রিয় ছিলেন তিনি ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের অধ্যাত্মপুত্র, জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভার দেবতা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী। মঞ্জুশ্রীরও বিচিত্র রূপ।… বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের মূর্তি পাওয়া যায় নাই বলিলেই চলে।’
‘মহাযান-বজ্রযানের আরও যে কয়েকটি নিম্নস্তরের দেবতা বাঙলাদেশে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জম্ভল, হেরুক ও হেবজ্রই প্রধান। জম্ভল ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের সঙ্গে যুক্ত, হেরুক অক্ষোভ্য হইতে উদ্ভূত এবং হেবজ্র স্পষ্টতই তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবতা। জম্ভল ব্রাহ্মণ্য কুবেরের বৌদ্ধ প্রতিরূপ এবং তাঁহার প্রতিমা বাঙলাদেশের, বিশেষত পূর্ব ও উত্তর-বাঙলার, নানা জায়গা হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধন ও ঐশ্বর্যের এই দেবতা যে জনসাধারণের খুব প্রিয় ছিলেন, অসংখ্য মূর্তি-প্রমাণেই তাহা সুস্পষ্ট।… জম্ভলের তুলনায় হেরুকের মূর্তি কিন্তু কমই পাওয়া গিয়াছে।… শক্তির দৃঢ়ালিঙ্গনবদ্ধ হেবজ্রের মূর্তি একাধিক পাওয়া গিয়াছে।…’
‘দেবতাদের কথা শেষ হইল; এইবার মহাযান-বজ্রযান আয়তনের দেবীদের কথা বলা যাইতে পারে। এই দেবীদের মধ্যে তারা সর্বশ্রেষ্ঠা। তারার অনেক রূপভেদ; বিভিন্নরূপ বিভিন্ন ধ্যানীবুদ্ধ হইতে উৎপন্ন। বাঙলাদেশে যত প্রকারের তারামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে খদিরবনী-তারা (খয়ের বনের তারা ?) বজ্র-তারা এবং ভৃকুটী-তারাই প্রধান। খদিরবনী-তারার অপর নাম শ্যাম-তারা; তাঁহার ধ্যানীবুদ্ধ হইতেছেন অমোঘসিদ্ধি; বজ্র-তারার ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভব এবং ভৃকুটী-তারার, অমিতাভ। অশোককান্তা (মারীচী) ও একজটাসহ খদিরবনী বা শ্যাম-তারার মূর্তিই সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়াছে। নীলোৎপলধৃতা এই দেবী কখনও উপবিষ্টা, কখনও দণ্ডায়মানা।… ঢাকা জেলার ভবানীপুর গ্রামে ত্রি-শির, অষ্টহস্ত, বীরাসনোপবিষ্ট, পাদপীঠে গণেশের মূর্তি উৎকীর্ণ এবং মৌলিতে অমিতাভ মূর্তিযুক্ত একটি দেবীমূতি পাওয়া গিয়াছে। ভট্টশালী-মহাশয় বলিয়াছেন, প্রতিমাটি ভৃকুটী-তারার। কিন্তু এই প্রতিমাটির সঙ্গে ঢাকা-চিত্রশালার আর একটি প্রতিমার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, শেষোক্ত প্রতিমাটি পঞ্চরক্ষামণ্ডলভুক্ত দেবী মহাপ্রতিসরার। প্রথমোক্ত প্রতিমাটির বাম দিকে ঝাঁটা ও কুলা হস্তে যে দেবীটি দাঁড়াইয়া আছেন তিনি তো একটি গ্রাহ্য দেবী (বোধ হয় শীতলা বলিয়াই মনে হইতেছে)।… অষ্টভূজা সিতাতপত্রার একটি ধাতব মূর্তি ঢাকা-চিত্রশালায় আছে।’
‘বজ্রযানী অন্যান্য দেবী মূর্তির মধ্যে মারীচী, পর্ণশবরী, হারীতী এবং চুণ্ডাই প্রধান। ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন-সম্ভূত মারীচীর কয়েকটি প্রতিমা বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ত্রিমুখ (বাম মুখ শঙ্করীর), সপ্তশূকরবাহিত এবং রাহুসারথি, রথে প্রত্যালীঢ়ভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা এই দেবীটি ব্রাহ্মণ্য সূর্যেরই বৌদ্ধ প্রতিরূপ।… পর্ণশবরীর ধ্যানীবুদ্ধ বোধ হয় অমোঘসিদ্ধি। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে দুইটি ত্রি-শির, ষড়ভূজা, পর্ণাচ্ছাদন-পরিহিতা পর্ণশবরী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। ধ্যানে তাঁহাকে বলা হইয়াছে ‘পিশাচী’। রাজশাহী জেলার নিয়ামতপুরে অষ্টাদশভূজা চুণ্ডা দেবীর একটি নবম-শতকীয় প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে (রাজশাহী-চিত্রশালা)।… বজ্রযানী দেবী উষ্ণীষ-বিজয়ার একটি ভগ্ন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বীরভূম জেলায়। হারীতী জম্ভলের শক্তি, তিনি ধনৈশ্চর্যের দেবী এবং ব্রাহ্মণ্য ষষ্ঠীর বৌদ্ধ প্রতিরূপ। ঢাকা ও রাজশাহী-চিত্রশালায় চার পাঁচটি হারীতীর প্রতিমা রক্ষিত আছে।’
‘এই সব অসংখ্য মহাযানী দেবদেবীর পূজার্চনার জন্য মন্দিরও অবশ্যই অসংখ্য রচিত হইয়াছিল বাঙলার নানা জায়গায়। বিভিন্ন বিহারগুলির সঙ্গে সঙ্গেও মন্দির নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বাঙলার কোন্ প্রান্তে কোথায় কোন্ দেবদেবীর মন্দির ছিল, কোথায় কে পূজা পাইতেন, আজ আর তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে, একাদশ শতকের অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে বাঙলাদেশের কয়েকটি মহাযানী বজ্রযানী বৌদ্ধ মন্দিরের একং কোন্ মন্দিরে কাহার পূজা হইত তাহার একটু ইঙ্গিত আছে। তাহা হইতে বুঝা যায়, চন্দ্রদ্বীপে (নিম্নবঙ্গের খুলনা-বরিশাল অঞ্চলে) ভগবতী-তারার একটি মন্দির, সমতটে লোকনাথের দুইটি এবং বুদ্ধর্ধি-তারার একটি, পট্টিকেরক রাজ্যে চুণ্ডাবর ভবনে চুণ্ডা-দেবীর একটি এবং হরিকেলদেশে লোকনাথের একটি মন্দির ছিল।’
‘এ-পর্যন্ত যত মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদির কথা বলিলাম সেগুলির প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, উত্তর ও পূর্ব-বাঙলা (গঙ্গার পূর্বতীর হইতে), বিশেষভাবে রাজশাহী-দিনাজপুর-বগুড়া জেলায় এবং ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরা জেলায় যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বাঙলার অন্যত্র কোথাও তেমন নয়। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বজ্রযানী-তন্ত্রের প্রতিমা পাওয়া প্রায় যায় নাই বলিলেই চলে, এক বাঁকুড়া-বীরভূমের কিয়দংশ ছাড়া। মনে হয়, মহাযান-বজ্রযান তন্ত্রের প্রসার ও প্রতিপত্তি উত্তর ও পূর্ব-বাঙলায় যতটা ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমে ততটা ছিল না, দক্ষিণ-রাঢ়ে তো নয়ই। প্রায় দশম শতক হইতেই নালন্দার প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতে থাকে এবং বিক্রমশীল-সোমপুর প্রভৃতি তাহার স্থান অধিকার করে। বিক্রমশীল-বিহার এবং ফুল্লহরি-বিহার বাঙলাদেশে না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু সোমপুর, জগদ্দল এবং দেবীকোট বিহার ছিল নিঃসংশয়ে উত্তর-বঙ্গে; পণ্ডিত-বিহার, পট্টিকেরক-বিহার ও বিক্রমপুরী-বিহার নিঃসংশয়ে পূর্ববঙ্গে। রাঢ়দেশের একটি মাত্র বিহারের নাম পাইতেছি, ত্রৈকূটক বিহার, কিন্তু তাহাও নিঃসংশয়ে রাঢ়দেশে কিনা বলা যায় না। সিদ্ধাচার্যদের জন্মস্থান ও আদি পরিবেশ বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, তাঁহারা অধিকাংশই উত্তর ও পূর্ববঙ্গের লোক। অথচ, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ-রাঢ়ে সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমা মিলিতেছে প্রচুর। মনে হয়, এক বাঁকুড়া-বীরভূমের কিয়দংশ ছাড়া রাঢ়ের অন্যত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমন ছিল না। এই তথ্য সমসাময়িক ও মধ্যযুগীয় বাঙলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক হইতে গভীর অর্থবহ। ইহাও লক্ষণীয় যে, বাঁকুড়া-বীরভূমের যে অংশে মহাযান-বজ্রযান সক্রিয় সেই অংশেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রসার, প্রভাব ও প্রতিপত্তি।’
‘লিপি-প্রমাণ ও শৈলী-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বৌদ্ধ প্রতিমাগুলির তারিখ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, পাল-পূর্ব যুগের বৌদ্ধ মূর্তি খুব বেশি পাওয়া যায় নাই; যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই– দুই চারিটি বিক্ষিপ্ত মূর্তি ছাড়া– মোটামুটি নবম হইতে একাদশ শতকের এবং এই তিনশত বৎসরই বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণযুগ।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৫৩৩-৩৭)
অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের উপরের বর্ণনা থেকে বৌদ্ধ-সাধনচর্চার একটা মোটামুটি ছায়া-মানচিত্র পাওয়া যায়। তবে বৌদ্ধ-তন্ত্র ও তৎসম্পর্কিত দেবদেবী প্রসঙ্গটি এতোটাই জটিলতায় পরিকীর্ণ যে তার পর্যালোচনা করতে হলে বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রাথমিক ধারণা হিসেবে ছোট্ট একটু ভূমিকা থাকাও আবশ্যক মনে হয়।
বলা হয়ে থাকে যে, দুঃখতত্ত্বই বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্ব এবং আদিতম বৌদ্ধধর্মের বিকাশ এই তত্ত্বকে আশ্রয় করেই হয়েছিল। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে বৌদ্ধধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা রীতিমতো জটিল ও পল্লবিত। বুদ্ধকথিত চারটি আর্যসত্য হচ্ছে– দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব, এবং তার জন্য সঠিক পথ জানা চাই যাকে বলা হয় দুঃখ-নিবৃত্তি-মার্গ। এক্ষেত্রে এটাও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, সকল ভারতীয় দর্শনই এই দুঃখতত্ত্বকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে। যেমন, সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী দুঃখ তিন প্রকার– আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। বিদ্বান গবেষক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, কার্যকারণ সম্পর্কের প্রতি বুদ্ধের নির্ভরতা সম্ভবত তাঁর গুরু আঢ়ার কালামের নিকট সাংখ্যদর্শন পাঠের ফল, যার মূল কথা একই বস্তু কার্যে ও কারণে বিদ্যমান। কার্যে যা ব্যক্ত তা কারণে অব্যক্ত। বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের এটাই হচ্ছে ভিত্তি।
‘বুদ্ধের মতে দুঃখের বারোটি কারণ-পরম্পরা আছে যেগুলিকে বলা হয় প্রতীত্যসমুৎপাদ। এগুলি হলো অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরামরণ ইত্যাদি। দুঃখের ধারণা যেমন সকল ভারতীয় দর্শনেই স্বীকৃত, দুঃখের মূল কারণ হিসাবে অজ্ঞানতা বা অবিদ্যার উপর সকল মতই সমান গুরুত্ব আরোপ করে। অবিদ্যা, অর্থাৎ সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা এবং সংস্কার বা মানসজাত ধারণাসমূহ জন্মান্তরে চৈতন্য (বিজ্ঞান), মানসিক ও দৈহিক উপাদানসমূহ (নামরূপ), ছয়টি ইন্দ্রিয় (ষড়ায়তন), সংযোগ (স্পর্শ), অনুভূতি (বেদনা) ও আকাঙ্ক্ষার (তৃষ্ণা) কারণ হয় যেগুলি আবার পুনরস্তিত্বের (ভব), তীব্র ইচ্ছার (উপাদান) উদ্ভব ঘটিয়ে জন্ম (জাতি) ও দুঃখের (জরামরণ ইত্যাদি) কারণ হয়।’
‘দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধ জীবনাচর্যার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা (মজঝিম পটিপদা) এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ (মগ্গ) অনুসরণের ব্যবস্থা দিয়েছেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল সম্মা বাচা (সদ্বাক্য), সম্মা কম্মন্ত (সৎ কর্ম), সম্মা আজীবা (সৎ জীবিকা), সম্মা বায়াম (যথার্থ শ্রম), সম্মা মতি (যথার্থ মনন), সম্মা সমাধি (যথার্থ ধ্যান), সম্মা সংকপ্প (যথার্থ সংকল্প) এবং সম্মা দিটঠি (যথার্থ দৃষ্টি)। অনুমান করা যেতে পারে যে দুঃখের কারণ হিসাবে বুদ্ধ যে অবিদ্যার কথা বলেছেন তার মূল কথা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটা যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। জগৎ বা জাগতিক সুখদুঃখ কারও ইচ্ছাধীন নয়, একজন যা চায় তা না পেতেও পারে, এ জন্য আক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন, তাতে দুঃখ ও হতাশারই বৃদ্ধি ঘটে। প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ কার্যকারণ পরম্পরার তত্ত্বটি পরবর্তীকালের পল্লবিত সৃষ্টি। মধ্যপন্থা বলতে বুদ্ধ বলেছেন চরম সুখভোগ ও চরম কৃচ্ছ্রসাধন বা আত্মনিগ্রহের মাঝামাঝি পথ, এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিছকই কয়েকটি নৈতিক উপদেশ যা সর্বযুগে সর্বত্রই সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সম্ভবত গৌতম বুদ্ধের মূল শিক্ষা ছিল যে মানুষের কামনাবাসনার শেষ নেই এবং সেগুলি কোনও দিনই পূর্ণ হওয়ার নয়। এই সোজা কথাটা উপলব্ধি করতে না পারাটাই অবিদ্যা। কাজেই মোটামুটি ভদ্র জীবনযাপন ও সদ্বৃত্তিসমূহের অনুশীলনই যথার্থ পুরুষার্থ। বিষয়তৃষ্ণা, ভোগের আকাঙ্ক্ষা, অপরের উপর প্রভুত্ব করার মনোবৃত্তি ইত্যাদিকে পরিহার করলেই দুঃখের বিনাশ ঘটানো যাবে।’- (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/ ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭)
‘বুদ্ধের মতে দুঃখের বারোটি কারণ-পরম্পরা আছে যেগুলিকে বলা হয় প্রতীত্যসমুৎপাদ। এগুলি হলো অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরামরণ ইত্যাদি। দুঃখের ধারণা যেমন সকল ভারতীয় দর্শনেই স্বীকৃত, দুঃখের মূল কারণ হিসাবে অজ্ঞানতা বা অবিদ্যার উপর সকল মতই সমান গুরুত্ব আরোপ করে। অবিদ্যা, অর্থাৎ সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা এবং সংস্কার বা মানসজাত ধারণাসমূহ জন্মান্তরে চৈতন্য (বিজ্ঞান), মানসিক ও দৈহিক উপাদানসমূহ (নামরূপ), ছয়টি ইন্দ্রিয় (ষড়ায়তন), সংযোগ (স্পর্শ), অনুভূতি (বেদনা) ও আকাঙ্ক্ষার (তৃষ্ণা) কারণ হয় যেগুলি আবার পুনরস্তিত্বের (ভব), তীব্র ইচ্ছার (উপাদান) উদ্ভব ঘটিয়ে জন্ম (জাতি) ও দুঃখের (জরামরণ ইত্যাদি) কারণ হয়।’
‘দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধ জীবনাচর্যার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা (মজঝিম পটিপদা) এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ (মগ্গ) অনুসরণের ব্যবস্থা দিয়েছেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল সম্মা বাচা (সদ্বাক্য), সম্মা কম্মন্ত (সৎ কর্ম), সম্মা আজীবা (সৎ জীবিকা), সম্মা বায়াম (যথার্থ শ্রম), সম্মা মতি (যথার্থ মনন), সম্মা সমাধি (যথার্থ ধ্যান), সম্মা সংকপ্প (যথার্থ সংকল্প) এবং সম্মা দিটঠি (যথার্থ দৃষ্টি)। অনুমান করা যেতে পারে যে দুঃখের কারণ হিসাবে বুদ্ধ যে অবিদ্যার কথা বলেছেন তার মূল কথা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটা যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। জগৎ বা জাগতিক সুখদুঃখ কারও ইচ্ছাধীন নয়, একজন যা চায় তা না পেতেও পারে, এ জন্য আক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন, তাতে দুঃখ ও হতাশারই বৃদ্ধি ঘটে। প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ কার্যকারণ পরম্পরার তত্ত্বটি পরবর্তীকালের পল্লবিত সৃষ্টি। মধ্যপন্থা বলতে বুদ্ধ বলেছেন চরম সুখভোগ ও চরম কৃচ্ছ্রসাধন বা আত্মনিগ্রহের মাঝামাঝি পথ, এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিছকই কয়েকটি নৈতিক উপদেশ যা সর্বযুগে সর্বত্রই সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সম্ভবত গৌতম বুদ্ধের মূল শিক্ষা ছিল যে মানুষের কামনাবাসনার শেষ নেই এবং সেগুলি কোনও দিনই পূর্ণ হওয়ার নয়। এই সোজা কথাটা উপলব্ধি করতে না পারাটাই অবিদ্যা। কাজেই মোটামুটি ভদ্র জীবনযাপন ও সদ্বৃত্তিসমূহের অনুশীলনই যথার্থ পুরুষার্থ। বিষয়তৃষ্ণা, ভোগের আকাঙ্ক্ষা, অপরের উপর প্রভুত্ব করার মনোবৃত্তি ইত্যাদিকে পরিহার করলেই দুঃখের বিনাশ ঘটানো যাবে।’- (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/ ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭)
নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধধর্মের দুটি মুখ্য বিভাগ হলো– হীনযান ও মহাযান। কালক্রমে এই দুইটি যান প্রায় দুইটি ভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিলো। হীনযান পুরাতন এবং মহাযান আধুনিক। হীনযান বুদ্ধের বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মহাযান দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুইটি পন্থের ভিতর নানারূপ বিভেদ আছে। তবে অন্যতম মুখ্য বিভেদটি হলো– হীনযানে নিজের মুক্তিই প্রধান লক্ষ্যবস্তু, কিন্তু মহাযানে নিজের মুক্তির স্থান নেই। জগতের সকল মানুষ পশুপক্ষি ইত্যাদির মুক্তি আগে, তারপর নিজের মুক্তি। জগৎ যতক্ষণ বন্ধনাবস্থায় থাকে ততক্ষণ তাদের মুক্তির জন্য প্রয়াস ও সর্বপ্রকারে ত্যাগস্বীকার করাই বোধিসত্ত্বের প্রধান কার্য।
উল্লেখ্য, হীনযান ও মহাযান উভয় মতেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হচ্ছে নির্বাণ। ভারতীয় অন্যান্য দর্শনেও নির্বাণ নামক পরিভাষাটি বিদ্যমান, যার ভিন্ন নাম মুক্তি ও মোক্ষ।
‘বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণের কোনও সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। তবে বলা হয়েছে যে তা অব্যাকৃত, অজর, অব্যাধি, অমৃত, অশোক, অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর (তুলানারহিত) যোগক্ষেম। যে পাঁচটি উপাদান কোনও সত্তাকে গঠন করে– যেগুলি হল রূপ (বস্তুগত উপাদান), বেদনা (অনুভূতিগত উপাদান), সংজ্ঞা (অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদান), সংস্কার (মানসিক উপাদান) এবং বিজ্ঞান (চৈতন্যময় উপাদান)– সেগুলি আত্মাবিহীন (অনাত্ম), অচিরস্থায়ী (অনিত্য) এবং অকাম্য (দুঃখ)। যিনি উপাদানসমূহের মধ্যে আত্মার অনুপস্থিতি উপলব্ধি করেন, তিনি জানেন যে ব্যক্তি হিসাবে তাঁর কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, এবং সেই কারণেই তাঁর সঙ্গে তাঁর চারপাশের বস্তুনিচয়ের কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠা অসম্ভব। কাজেই জগতে এমন কিছুই নেই যা তাঁকে আনন্দিত অথবা দুঃখিত করতে পারে, এবং সেই কারণেই তিনি বিমুক্ত এবং সম্পূর্ণ (অর্হৎ)। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা থেকেই তৃষ্ণা বা আসক্তির উৎপত্তি, এই তৃষ্ণাই কর্মের দ্রষ্টা, আর কর্মই মানুষকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু এই জন্মান্তরের শৃঙ্খল তখনই ভেঙে যায় যখনই জগতের অনিত্যতার পরিপূর্ণ উপলব্ধি ঘটে, যখনই এই বোধ জাগে যে অস্তিত্ব মানেই ক্ষণিক অস্তিত্ব।’
‘…হীনযান বৌদ্ধধর্মে (যেটি বৌদ্ধধর্মের দ্বিতীয় পর্যায়) বলা হয়েছে যে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের দরুনই দুঃখের উৎপত্তি, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের ধারণা অবিদ্যাপ্রসূত, তার অনিত্যতা ও ক্ষণিকতা উপলব্ধি করতে পারলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটবে। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্রের থেকে পৃথক নয়, অথচ অবোধ মানুষ কয়েকটি হেতু-প্রত্যয়ের (কারণ ও শর্ত) বশবর্তী হয়ে পৃথক দেখে, সেই রকম দৃশ্যমান জগতেরও কোনও চিরন্তন অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা ক্ষণিক অস্তিত্ব। মহাযানে আরও একধাপ এগিয়ে বলা হয়েছে দৃশ্যমান বাহ্যবস্তু মাত্রেই অলীক, অস্তিত্বের অর্থ শূন্য অস্তিত্ব।’
‘শূন্য বা অনাত্ম বলতে যেখানে হীনযানে পুদ্গলশূন্যতা বোঝায়, অর্থাৎ আত্মা বা ওই ধরনের কোনও পদার্থের অনস্তিত্ব, সেখানে শূন্য বলতে মহাযান মতে পুদ্গলশূন্যতা ছাড়াও ধর্মশূন্যতা বোঝায় যার অর্থ বস্তুরও অস্তিত্বহীনতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হীনযানে একটি মাটির পাত্রের কোনও অন্তর্নিহিত সারবস্তু এবং তজ্জন্য তার আত্মত্ব বা স্বকীয়ত্ব অস্বীকৃত, কেন না মাটির পাত্রকে মাটির ঘোড়ায় রূপদান করা সম্ভব। কিন্তু সেখানে মূল বস্তুটি, অর্থাৎ যে মাটি দিয়ে পাত্র বা ঘোড়া তৈরি হয়, অস্বীকৃত নয়। কিন্তু মহাযানে মাটির অস্তিত্বও অস্বীকৃত। মাটির পাত্রত্ব এবং অশ্বত্ব যেমন মিথ্যা, মাটিত্বও তেমনই মিথ্যা। প্রথমটি পুদ্গলশূন্যতা, দ্বিতীয়টি ধর্মশূন্যতা। মহাযানীদের মতে দুটি আবরণ সত্যকে আড়াল করে রাখে– ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ। পুদ্গলশূন্যতার দ্বারা প্রথমটির অপসারণ হয়, এবং ধর্মশূন্যতার দ্বারা দ্বিতীয়টির। মহাযানী শিক্ষার সারবস্তু হচ্ছে জাগতিক ব্যক্তি একটি ভুল ধারণার জগতে বিচরণ করে, যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় ছয়টি অপূর্ণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা, আর তার নির্বাণ তখনই ঘটে যখন সে বুঝতে পারে সব কিছুই শূন্য, স্বপ্নবৎ মিথ্যা। এই উপলব্ধিই হচ্ছে দুঃখের নিবৃত্তি।’- (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/ ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট)
উল্লেখ্য, হীনযান ও মহাযান উভয় মতেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হচ্ছে নির্বাণ। ভারতীয় অন্যান্য দর্শনেও নির্বাণ নামক পরিভাষাটি বিদ্যমান, যার ভিন্ন নাম মুক্তি ও মোক্ষ।
‘বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণের কোনও সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। তবে বলা হয়েছে যে তা অব্যাকৃত, অজর, অব্যাধি, অমৃত, অশোক, অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর (তুলানারহিত) যোগক্ষেম। যে পাঁচটি উপাদান কোনও সত্তাকে গঠন করে– যেগুলি হল রূপ (বস্তুগত উপাদান), বেদনা (অনুভূতিগত উপাদান), সংজ্ঞা (অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদান), সংস্কার (মানসিক উপাদান) এবং বিজ্ঞান (চৈতন্যময় উপাদান)– সেগুলি আত্মাবিহীন (অনাত্ম), অচিরস্থায়ী (অনিত্য) এবং অকাম্য (দুঃখ)। যিনি উপাদানসমূহের মধ্যে আত্মার অনুপস্থিতি উপলব্ধি করেন, তিনি জানেন যে ব্যক্তি হিসাবে তাঁর কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, এবং সেই কারণেই তাঁর সঙ্গে তাঁর চারপাশের বস্তুনিচয়ের কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠা অসম্ভব। কাজেই জগতে এমন কিছুই নেই যা তাঁকে আনন্দিত অথবা দুঃখিত করতে পারে, এবং সেই কারণেই তিনি বিমুক্ত এবং সম্পূর্ণ (অর্হৎ)। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা থেকেই তৃষ্ণা বা আসক্তির উৎপত্তি, এই তৃষ্ণাই কর্মের দ্রষ্টা, আর কর্মই মানুষকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু এই জন্মান্তরের শৃঙ্খল তখনই ভেঙে যায় যখনই জগতের অনিত্যতার পরিপূর্ণ উপলব্ধি ঘটে, যখনই এই বোধ জাগে যে অস্তিত্ব মানেই ক্ষণিক অস্তিত্ব।’
‘…হীনযান বৌদ্ধধর্মে (যেটি বৌদ্ধধর্মের দ্বিতীয় পর্যায়) বলা হয়েছে যে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের দরুনই দুঃখের উৎপত্তি, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের ধারণা অবিদ্যাপ্রসূত, তার অনিত্যতা ও ক্ষণিকতা উপলব্ধি করতে পারলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটবে। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্রের থেকে পৃথক নয়, অথচ অবোধ মানুষ কয়েকটি হেতু-প্রত্যয়ের (কারণ ও শর্ত) বশবর্তী হয়ে পৃথক দেখে, সেই রকম দৃশ্যমান জগতেরও কোনও চিরন্তন অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা ক্ষণিক অস্তিত্ব। মহাযানে আরও একধাপ এগিয়ে বলা হয়েছে দৃশ্যমান বাহ্যবস্তু মাত্রেই অলীক, অস্তিত্বের অর্থ শূন্য অস্তিত্ব।’
‘শূন্য বা অনাত্ম বলতে যেখানে হীনযানে পুদ্গলশূন্যতা বোঝায়, অর্থাৎ আত্মা বা ওই ধরনের কোনও পদার্থের অনস্তিত্ব, সেখানে শূন্য বলতে মহাযান মতে পুদ্গলশূন্যতা ছাড়াও ধর্মশূন্যতা বোঝায় যার অর্থ বস্তুরও অস্তিত্বহীনতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হীনযানে একটি মাটির পাত্রের কোনও অন্তর্নিহিত সারবস্তু এবং তজ্জন্য তার আত্মত্ব বা স্বকীয়ত্ব অস্বীকৃত, কেন না মাটির পাত্রকে মাটির ঘোড়ায় রূপদান করা সম্ভব। কিন্তু সেখানে মূল বস্তুটি, অর্থাৎ যে মাটি দিয়ে পাত্র বা ঘোড়া তৈরি হয়, অস্বীকৃত নয়। কিন্তু মহাযানে মাটির অস্তিত্বও অস্বীকৃত। মাটির পাত্রত্ব এবং অশ্বত্ব যেমন মিথ্যা, মাটিত্বও তেমনই মিথ্যা। প্রথমটি পুদ্গলশূন্যতা, দ্বিতীয়টি ধর্মশূন্যতা। মহাযানীদের মতে দুটি আবরণ সত্যকে আড়াল করে রাখে– ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ। পুদ্গলশূন্যতার দ্বারা প্রথমটির অপসারণ হয়, এবং ধর্মশূন্যতার দ্বারা দ্বিতীয়টির। মহাযানী শিক্ষার সারবস্তু হচ্ছে জাগতিক ব্যক্তি একটি ভুল ধারণার জগতে বিচরণ করে, যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় ছয়টি অপূর্ণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা, আর তার নির্বাণ তখনই ঘটে যখন সে বুঝতে পারে সব কিছুই শূন্য, স্বপ্নবৎ মিথ্যা। এই উপলব্ধিই হচ্ছে দুঃখের নিবৃত্তি।’- (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/ ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট)
প্রসঙ্গত এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, ‘হীনযান’ অভিধাটি মহাযানী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রাচীনপন্থি বৌদ্ধদের প্রতি উদ্দেশ্যমূলক আরোপিত। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে শ্রাবকযান এবং প্রত্যেক-বুদ্ধযানের উল্লেখ আছে। আগে এই দুটি যান ছিলো। শ্রাবকযানের সাধক বা শ্রাবকের অন্বিষ্ট হলো অর্হত্ব। এঁরা নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করেন না। অন্যপক্ষে প্রত্যেক-বুদ্ধযানের সাধক বা প্রত্যেক-বুদ্ধের লক্ষ্য ব্যক্তিগত নির্বাণ। তাঁরা প্রত্যেকে নিজে বোধি লাভ করেন কিন্তু শাস্তা বা লোকসাধারণের মুক্তির পথপ্রদর্শক হন না। তাই মহাযানীদের মতে ‘প্রত্যেক’ ও ‘শ্রাবক’ এই দুই যানই হীন, কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর। নিজের উদ্ধার হলেই হলো, তাঁরা জগতের কথা ভাবেন না, তাঁদের কাছে যেন জগৎ নাই, তাই মহাযানীরা তাঁদেরকে ‘হীন’ বলে নিন্দা করে থাকেন। আর নিজেদেরকে তাঁরা মহাযান বলেন, যেহেতু তাঁরা নিজেদের উদ্ধারের জন্য তত ভাবেন না, জগৎ উদ্ধারই তাঁদের মহাব্রত।
‘মহাযান বৌদ্ধধর্মের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান– বুদ্ধের দেবত্ব, শূন্যবাদ ও বোধিসত্ত্ববাদ। মহাসংঘিক ও তাদের অনুরূপ সম্প্রদায়সমূহ হীনযানপন্থী হলেও তাদের চিন্তাধারার মধ্যেই মহাযানের বীজ বর্তমান ছিল। মহাসংঘিকদের মতে বুদ্ধগণ লোকোত্তর, তাঁরা সাস্রবধর্ম বা যে কোনও মলিন উপাদান থেকে মুক্ত, নিদ্রা বা স্বপ্ন বিরহিত, সদা সমাধিস্থ এবং মুহূর্তেই সকল কিছু উপলব্ধি করেন। মহাযানীদের চোখে বুদ্ধ সর্বোচ্চ দেবতা। যিনি অনন্ত, উৎপত্তি ও বিলয়হীন, পরম সত্য ও সকল প্রকার বর্ণনার অতীত। বুদ্ধের তিনটি কায় বা দেহ বর্তমান– ধর্মকায়, সম্ভোগকায় এবং রূপকায় বা নির্মাণকায়। ধর্মকায় বুদ্ধের আসল দেহ যা বিশ্বচরাচরব্যাপী, আকারবিহীন, অনন্ত ও চিরন্তন। উচ্চমার্গের ভক্তদের জন্য এই বুদ্ধ দেবতার আকারে মহাপুরুষদের চিহ্নসহ দেখা দেন। এটি বুদ্ধের সম্ভোগকায় যা দর্শনের জন্য জন্মজন্মান্তরের সাধনা প্রয়োজন। সাধারণ লোকের কল্যাণের জন্য বুদ্ধ মাঝে মাঝে মানবরূপ ধারণ করেন, যে রূপ মানবীয় জন্ম-মৃত্যুর অধীন। এটি বুদ্ধের নির্মাণকায় (সৃষ্ট দেহ) বা রূপকায় (বস্তুগত দেহ)। গৌতমবুদ্ধ আসলে বুদ্ধের নির্মাণকায়। অসংখ্য জগতে অসংখ্য নির্মাণকায়ের বুদ্ধ মানবহিতায় জন্মগ্রহণ করেন, যেমন গৌতমবুদ্ধ আমাদের এই জগতে (সহা-লোকধাতু) জন্মগ্রহণ করেছেন।’
‘হীনযান বৌদ্ধধর্মে অর্হৎ-এর ধারণা বর্তমান। অর্হৎ হলেন আদর্শ মানুষ যিনি সকল প্রকার জাগতিক মোহ থেকে মুক্ত। অর্হৎ-এর সাধনা চরিত্রের সাধনা যা একান্তই ব্যক্তিনির্ভর। মহাযানে অর্হৎ-এর পরিবর্তে বোধিসত্ত্বের ধারণা গৃহীত হয়েছে। এই বোধিসত্ত্ব দেবতা হতে পারেন, গৃহীও হতে পারেন, সন্ন্যাসী হতে পারেন, এমনকি মানুষ নাও হতে পারেন। এঁদের কাজ হচ্ছে মানুষকে মুক্তিলাভে সাহায্য করা। সুকঠোর অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই, কয়েকটি সৎকর্ম (পারমিতা) করলেই যথেষ্ট। মহাযান মতে যিনি বোধিচিত্তের বিকাশ ঘটান তিনিই বোধিসত্ত্ব। তত্ত্বের দিক থেকে প্রতিটি মহাযানপন্থীই সম্ভাবনাময় বোধিসত্ত্ব। যদিও গোড়ার দিকে বোধিসত্ত্ব হওয়াই মহাযানীদের লক্ষ্য ছিল, কালক্রমে বোধিসত্ত্ব নামক এক ধরনের দেবতার সৃষ্টি হয় যাঁরা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এবং যাঁদের আরাধনা করলে প্রার্থিত ফল পাওয়া যায়। এই সকল আরাধ্য বোধিসত্ত্বদের অগ্রগণ্য হলেন অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, বজ্রপাণি, সমন্তভদ্র, আকাশগর্ভ, মহাস্থামপ্রাপ্ত, ভৈষজ্যরাজ এবং মৈত্রেয়। এঁরা আধ্যাত্মিক দিকে রীতিমত অগ্রসর, ইচ্ছা করলেই বুদ্ধ হতে পারেন, কিন্তু মানুষের কল্যাণের জন্য সে ইচ্ছা করেন না। এঁদের মধ্যে আবার অবলোকিতেশ্বর এবং মঞ্জুশ্রী প্রধান। অবলোকিতেশ্বর করুণার প্রতিমূর্তি, তাঁর সঙ্গিনী তারা প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি, যিনি দুঃখময় জগৎ অতিক্রম করতে মানুষকে সাহায্য করেন। মঞ্জুশ্রী চিরনবীন। তিনিও জ্ঞানের দেবতা যিনি মানুষকে ধর্মশিক্ষা দেন এবং ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়ের শিক্ষক।’- (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/ ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-১১১)
‘মহাযান বৌদ্ধধর্মের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান– বুদ্ধের দেবত্ব, শূন্যবাদ ও বোধিসত্ত্ববাদ। মহাসংঘিক ও তাদের অনুরূপ সম্প্রদায়সমূহ হীনযানপন্থী হলেও তাদের চিন্তাধারার মধ্যেই মহাযানের বীজ বর্তমান ছিল। মহাসংঘিকদের মতে বুদ্ধগণ লোকোত্তর, তাঁরা সাস্রবধর্ম বা যে কোনও মলিন উপাদান থেকে মুক্ত, নিদ্রা বা স্বপ্ন বিরহিত, সদা সমাধিস্থ এবং মুহূর্তেই সকল কিছু উপলব্ধি করেন। মহাযানীদের চোখে বুদ্ধ সর্বোচ্চ দেবতা। যিনি অনন্ত, উৎপত্তি ও বিলয়হীন, পরম সত্য ও সকল প্রকার বর্ণনার অতীত। বুদ্ধের তিনটি কায় বা দেহ বর্তমান– ধর্মকায়, সম্ভোগকায় এবং রূপকায় বা নির্মাণকায়। ধর্মকায় বুদ্ধের আসল দেহ যা বিশ্বচরাচরব্যাপী, আকারবিহীন, অনন্ত ও চিরন্তন। উচ্চমার্গের ভক্তদের জন্য এই বুদ্ধ দেবতার আকারে মহাপুরুষদের চিহ্নসহ দেখা দেন। এটি বুদ্ধের সম্ভোগকায় যা দর্শনের জন্য জন্মজন্মান্তরের সাধনা প্রয়োজন। সাধারণ লোকের কল্যাণের জন্য বুদ্ধ মাঝে মাঝে মানবরূপ ধারণ করেন, যে রূপ মানবীয় জন্ম-মৃত্যুর অধীন। এটি বুদ্ধের নির্মাণকায় (সৃষ্ট দেহ) বা রূপকায় (বস্তুগত দেহ)। গৌতমবুদ্ধ আসলে বুদ্ধের নির্মাণকায়। অসংখ্য জগতে অসংখ্য নির্মাণকায়ের বুদ্ধ মানবহিতায় জন্মগ্রহণ করেন, যেমন গৌতমবুদ্ধ আমাদের এই জগতে (সহা-লোকধাতু) জন্মগ্রহণ করেছেন।’
‘হীনযান বৌদ্ধধর্মে অর্হৎ-এর ধারণা বর্তমান। অর্হৎ হলেন আদর্শ মানুষ যিনি সকল প্রকার জাগতিক মোহ থেকে মুক্ত। অর্হৎ-এর সাধনা চরিত্রের সাধনা যা একান্তই ব্যক্তিনির্ভর। মহাযানে অর্হৎ-এর পরিবর্তে বোধিসত্ত্বের ধারণা গৃহীত হয়েছে। এই বোধিসত্ত্ব দেবতা হতে পারেন, গৃহীও হতে পারেন, সন্ন্যাসী হতে পারেন, এমনকি মানুষ নাও হতে পারেন। এঁদের কাজ হচ্ছে মানুষকে মুক্তিলাভে সাহায্য করা। সুকঠোর অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই, কয়েকটি সৎকর্ম (পারমিতা) করলেই যথেষ্ট। মহাযান মতে যিনি বোধিচিত্তের বিকাশ ঘটান তিনিই বোধিসত্ত্ব। তত্ত্বের দিক থেকে প্রতিটি মহাযানপন্থীই সম্ভাবনাময় বোধিসত্ত্ব। যদিও গোড়ার দিকে বোধিসত্ত্ব হওয়াই মহাযানীদের লক্ষ্য ছিল, কালক্রমে বোধিসত্ত্ব নামক এক ধরনের দেবতার সৃষ্টি হয় যাঁরা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এবং যাঁদের আরাধনা করলে প্রার্থিত ফল পাওয়া যায়। এই সকল আরাধ্য বোধিসত্ত্বদের অগ্রগণ্য হলেন অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, বজ্রপাণি, সমন্তভদ্র, আকাশগর্ভ, মহাস্থামপ্রাপ্ত, ভৈষজ্যরাজ এবং মৈত্রেয়। এঁরা আধ্যাত্মিক দিকে রীতিমত অগ্রসর, ইচ্ছা করলেই বুদ্ধ হতে পারেন, কিন্তু মানুষের কল্যাণের জন্য সে ইচ্ছা করেন না। এঁদের মধ্যে আবার অবলোকিতেশ্বর এবং মঞ্জুশ্রী প্রধান। অবলোকিতেশ্বর করুণার প্রতিমূর্তি, তাঁর সঙ্গিনী তারা প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি, যিনি দুঃখময় জগৎ অতিক্রম করতে মানুষকে সাহায্য করেন। মঞ্জুশ্রী চিরনবীন। তিনিও জ্ঞানের দেবতা যিনি মানুষকে ধর্মশিক্ষা দেন এবং ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়ের শিক্ষক।’- (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/ ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-১১১)
বলা বাহুল্য, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর মহাযান অধিবিদ্যার একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব। নির্বাণ অর্জন করেও জগতের দুঃখে অভিভূত অবলোকিতেশ্বর জগতের সমস্ত প্রাণীর দুঃখ মোচন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা, যে জীব যেভাবে যাঁকে পূজা করে তিনি সেই রূপ ধারণ করে উপদেশ দেবেন। যারা তথাগতকে মানে তাদের তথাগত রূপে, মহেশ্বর বা বিষ্ণু বা বায়ু ইত্যাদির উপাসকদের মহেশ্বর বিষ্ণু বা বায়ু ইত্যাদি রূপ ধারণ করে ধর্মদেশনা করবেন।
মহাযান মতের একটি মূল তত্ত্ব মহাকরুণা। অবলোকিতেশ্বর মহাকরুণা-বিগ্রহ। বহু বোধিসত্ত্বের মধ্যে প্রজ্ঞা-বিগ্রহ মঞ্জুশ্রী এবং করুণা-বিগ্রহ অবলোকিতেশ্বর প্রধান। মহাযান ধর্মে ক্রমে ‘করুণা’ তত্ত্বের গুরুত্ব বাড়ায় অবলোকিতেশ্বর প্রধানতম বোধিসত্ত্বের মর্যাদা পান। অন্য সব বোধিসত্ত্বের গুণ অবলোকিতেশ্বরে আরোপ করা হয়। এমন-কি হিন্দু দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের চারিত্র বৈশিষ্ট্যও মিশে যায় অবলোকিতেশ্বরে। কোথাও কোথাও অবলোকিতেশ্বরকে বুদ্ধের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। অবলোকিতেশ্বর ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ ও পাণ্ডরা থেকে উৎপন্ন। অমিতাভ কুলের নাম পদ্মকুল। প্রতীক চিহ্ন পদ্ম। শাক্যসিংহের নির্বাণের পর থেকে ভবিষ্যতে মৈত্রেয় বুদ্ধ আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত অবলোকিতেশ্বরই সৃষ্টিরক্ষা এবং ধর্মপ্রচারের অধিকারী।
অবলোকিতেশ্বরের শক্তি তারা। তন্ত্রের প্রভাবে অবলোকিতেশ্বর কল্পনায় বিচিত্র বিবর্তন ঘটেছিলো। অবলোকিতেশ্বর মূর্তিতে মাথা ও হাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মূর্তির রঙ, প্রতীক চিহ্ন, অস্ত্র ও যান কল্পনায় বৈচিত্র্য দেখা দেয়। শক্তির সংখ্যাও বাড়ে। নেপালের মছন্দর বাহালের দেয়ালে অবলোকিতেশ্বরের একশ’ আট রূপ আঁকা আছে। অবলোকিতেশ্বরের ধ্যানমন্ত্রগুলিতে কল্পিত রূপের মধ্যে প্রধান ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর, সিংহনাদ, খসর্প-লোকনাথ, হালাহল, পদ্মনর্তেশ্বর, হরিহরিহরিবাহনোদ্ভব, ত্রৈলোক্যবশংকর, রত্নলোকেশ্বর, মায়াজালক্রম, নীলকণ্ঠ, সুগতিসন্দর্শন, প্রেতসন্তর্পিত, সুখাবতী, বজ্রধর্ম। ‘ওঁ মণিপদ্মে হুঁ’ এই ছয় অক্ষরের মন্ত্রটি অবলোকিতেশ্বরের সবচেয়ে শক্তিশালী সিদ্ধ-মন্ত্র। ভারত ও নেপাল ছাড়া তিব্বত সহ চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে অবলোকিতেশ্বরের বহু মূর্তি পাওয়া গেছে।
মহাযান মতের একটি মূল তত্ত্ব মহাকরুণা। অবলোকিতেশ্বর মহাকরুণা-বিগ্রহ। বহু বোধিসত্ত্বের মধ্যে প্রজ্ঞা-বিগ্রহ মঞ্জুশ্রী এবং করুণা-বিগ্রহ অবলোকিতেশ্বর প্রধান। মহাযান ধর্মে ক্রমে ‘করুণা’ তত্ত্বের গুরুত্ব বাড়ায় অবলোকিতেশ্বর প্রধানতম বোধিসত্ত্বের মর্যাদা পান। অন্য সব বোধিসত্ত্বের গুণ অবলোকিতেশ্বরে আরোপ করা হয়। এমন-কি হিন্দু দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের চারিত্র বৈশিষ্ট্যও মিশে যায় অবলোকিতেশ্বরে। কোথাও কোথাও অবলোকিতেশ্বরকে বুদ্ধের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। অবলোকিতেশ্বর ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ ও পাণ্ডরা থেকে উৎপন্ন। অমিতাভ কুলের নাম পদ্মকুল। প্রতীক চিহ্ন পদ্ম। শাক্যসিংহের নির্বাণের পর থেকে ভবিষ্যতে মৈত্রেয় বুদ্ধ আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত অবলোকিতেশ্বরই সৃষ্টিরক্ষা এবং ধর্মপ্রচারের অধিকারী।
অবলোকিতেশ্বরের শক্তি তারা। তন্ত্রের প্রভাবে অবলোকিতেশ্বর কল্পনায় বিচিত্র বিবর্তন ঘটেছিলো। অবলোকিতেশ্বর মূর্তিতে মাথা ও হাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মূর্তির রঙ, প্রতীক চিহ্ন, অস্ত্র ও যান কল্পনায় বৈচিত্র্য দেখা দেয়। শক্তির সংখ্যাও বাড়ে। নেপালের মছন্দর বাহালের দেয়ালে অবলোকিতেশ্বরের একশ’ আট রূপ আঁকা আছে। অবলোকিতেশ্বরের ধ্যানমন্ত্রগুলিতে কল্পিত রূপের মধ্যে প্রধান ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর, সিংহনাদ, খসর্প-লোকনাথ, হালাহল, পদ্মনর্তেশ্বর, হরিহরিহরিবাহনোদ্ভব, ত্রৈলোক্যবশংকর, রত্নলোকেশ্বর, মায়াজালক্রম, নীলকণ্ঠ, সুগতিসন্দর্শন, প্রেতসন্তর্পিত, সুখাবতী, বজ্রধর্ম। ‘ওঁ মণিপদ্মে হুঁ’ এই ছয় অক্ষরের মন্ত্রটি অবলোকিতেশ্বরের সবচেয়ে শক্তিশালী সিদ্ধ-মন্ত্র। ভারত ও নেপাল ছাড়া তিব্বত সহ চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে অবলোকিতেশ্বরের বহু মূর্তি পাওয়া গেছে।
হীনযানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, হীনযানে দেবদেবীর বালাই নেই। এমনকি বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের মূর্তি পর্যন্ত বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় চারশ’ বৎসরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়নি। গৌতম বুদ্ধ নিজেই মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন বলে জানা যায়। তথাপি পরবর্তীকালের বৌদ্ধসাধনায় কী করে হিন্দু-বিশ্বাসানুরূপ অজস্র দেবদেবী কল্পনা ও মূর্তি বানিয়ে উপাসনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। বৌদ্ধবিদ্যার অগ্রবর্তী গবেষক পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলছেন–
‘নেপালীরা বলে ধর্ম দুই প্রকার হইতে পারে। খাঁটি ধর্ম দু রকম ছাড়া তিন রকম হইতে পারে না। সেই দুই প্রকার ধর্ম– ১. দেবভাজু ২. গুভাজু। হয় দেবতাকে ভজনা করো, না হয় গুরুকে ভজনা করো। ব্রাহ্মণেরা দেবভাজু, বৌদ্ধেরা গুভাজু, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিছুতেই মিশিতে পারে না। বৌদ্ধধর্মের শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযান দুই-ই গুভাজু, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। মহাযানও সম্পূর্ণরূপে গুভাজু, তাহারা বুদ্ধকেই মানে, বুদ্ধই তাদের গুরু, বুদ্ধকেই তাহারা মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করে, কোনো দেবতাকেই তাহারা উপাসনা করে না, তবে তাহাদিগকে হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য বলিয়া কেমন করিয়া মনে করিব?’- (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ তৃতীয় খন্ড, মহাযান কোথা হইতে আসিল? পৃষ্ঠা-৩৪৪)
‘নেপালীরা বলে ধর্ম দুই প্রকার হইতে পারে। খাঁটি ধর্ম দু রকম ছাড়া তিন রকম হইতে পারে না। সেই দুই প্রকার ধর্ম– ১. দেবভাজু ২. গুভাজু। হয় দেবতাকে ভজনা করো, না হয় গুরুকে ভজনা করো। ব্রাহ্মণেরা দেবভাজু, বৌদ্ধেরা গুভাজু, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিছুতেই মিশিতে পারে না। বৌদ্ধধর্মের শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযান দুই-ই গুভাজু, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। মহাযানও সম্পূর্ণরূপে গুভাজু, তাহারা বুদ্ধকেই মানে, বুদ্ধই তাদের গুরু, বুদ্ধকেই তাহারা মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করে, কোনো দেবতাকেই তাহারা উপাসনা করে না, তবে তাহাদিগকে হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য বলিয়া কেমন করিয়া মনে করিব?’- (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ তৃতীয় খন্ড, মহাযান কোথা হইতে আসিল? পৃষ্ঠা-৩৪৪)
তবে মহাযান পন্থার পরবর্তী সাধনা-পরম্পরায় উৎপত্তি হওয়া বিভিন্ন যান যেমন– মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতির ধারাবাহিকতার মধ্যেই যে এই দেবদেবী রহস্য লুকিয়ে আছে সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই বলেই মনে হয়। অথচ তাঁরাও নিজেদের মহাযানপন্থী বলে প্রচার করে থাকে। এইসব সাধনপন্থার সাথে প্রাচীন তন্ত্রসাধনার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টিও এখন আর অপ্রকাশিত নয়। তবে মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও তা থেকে উদ্ভূত অন্যান্য বৌদ্ধ যান (মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান এবং নাথধর্ম, কৌলধর্ম প্রভৃতি) সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রধান যে সমস্যার উদ্ভব হয় তা নির্দেশ করে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় বলেন–
‘বলা বাহুল্য, এই সব বিভিন্ন যান ও ধর্মমত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; অধিকাংশ গ্রন্থ এখনও অনূদিত ও আলোচিতই হয় নাই। অনুবাদ এবং আলোচনার বাধাও বিস্তর। প্রথমত, যে সংস্কৃত ভাষায় মূল গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়াছিল, সে সংস্কৃত অত্যন্ত ব্যাকরণদোষদুষ্ট শুদ্ধ সুবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষাব্যবহারের কোনও বালাই-ই যেমন বৌদ্ধ আচার্যদের ছিল না। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেন, বুঝিতে পারিলেই হইল; ছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার শব্দ বা পদরীতি ইত্যাদি অশুদ্ধ বা অপ্রচলিত হইলেও কিছু ক্ষতি নাই। কালচক্রযানের বিমলপ্রভা নামে একটি টীকায় বলা হইয়াছে, বৌদ্ধ আচার্যরা স্বেচ্ছাপূর্বক সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি-পদ্ধতি, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি অমান্য করিতেন; যাঁহারা মানিয়া চলিতেন তাঁহাদের বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন! ঠিক এই কারণেই তিব্বতী অনুবাদও বহুক্ষেত্রে দুর্বোধ্য এবং তাহা হইতে সংস্কৃতে পুর্ননুবাদ খুব সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, এই সব প্রত্যেকটি ধর্ম গুরুনির্ভর ধর্ম, গুরু ছাড়া এই ধর্মের গুহ্য সাধন প্রক্রিয়ার রহস্য ভেদ করা অসম্ভব বলিলেই চলে, এবং দীক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া গুরুরা অন্য কাহারও নিকট সে রহস্য ভেদ ও ব্যাখ্যা করিতেন না। সেই হেতু এই সব ধর্মের বিস্তৃতি দীক্ষিত চক্র বা মণ্ডলের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ; সর্বসাধারণ সেই সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতেই পারিত না। গুরুরা দীক্ষিতদের নিকট এবং দীক্ষিতরা পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের গুহ্যসাধনা সম্বন্ধে যে-ভাষায় কথা বলিতেন সে-ভাষাও ছিল গুহ্যভাষা। যে-ভাষার নাম ছিল সন্ধাভাষা (সন্ধিভাষা), যে ভাষার শুধু ‘মৌলিক’ ‘সম্পূর্ণ’ ‘নিগূঢ়’ সত্যের কথা বলে; কিন্তু যত মৌলিক, সম্পূর্ণ এবং নিগূঢ়ই হোক না কেন সে-ভাষা, অদীক্ষিত জনের কাছে তাহা ছিল দুর্বোধ্য। এ-ভাষায় যাহা ‘অভিপ্রায়িক’, অর্থাৎ আপাত যে-অর্থ কোনও বাক্যের বা পদের, তাহাই তাহার নিগূঢ় অর্থাৎ মৌলিক, সম্পূর্ণ অর্থ নয়; মৌলিক সম্পূর্ণ উদ্দিষ্ট অর্থের দিকে তাহা ইঙ্গিত করে মাত্র। কাজেই, সে ভাষার মৌলিক উদ্দিষ্ট অর্থ ধরিতে পারা সহজ নয়। তৃতীয়ত, ইঁহাদের সাধনপন্থা এবং প্রক্রিয়াও ছিল অত্যন্ত গুহ্য। নানা প্রকারের যাদুমন্ত্র, যাদুপ্রক্রিয়া, নানা বিধিবিধান, সাধনমন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, ধারণী, যোগ, সমাধি প্রভৃতি লইয়া এই বৌদ্ধাচার্যরা এমন একটি রহস্যময় জগৎ গড়িয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র-জগতের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও সর্বত্র সর্বথা তাহা আমাদের অধিগম্য নয়। সে-জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচিত সাধন-রীতি-পদ্ধতি, নীতি ও প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ কমই। গুহ্য রহস্যময় সন্ধাভাষায় বৌদ্ধ আচার্যরা গুহ্যতর সাধন-প্রক্রিয়া ও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। চতুর্থত, যে-সব ছায়া, রূপক, উপমা, প্রতীক এবং যোগারূঢ় শব্দ আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের সাধন-নীতি ও আদর্শ, রীতি ও প্রক্রিয়া এবং অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে, সে-গুলি সমসাময়িক সাধারণ নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, যৌন-জীবন এবং যৌন-প্রক্রিয়া হইতেই আহৃত, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই জীবন ও প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে তাহারা যে অর্থ ও ইঙ্গিত বহন করে তাহা একান্তই আপাত অর্থ ও ইঙ্গিত, এবং সে অর্থ ও ইঙ্গি আমাদের বর্তমান রুচি ও সংস্কারকে আঘাত করে। কাজেই স্বচ্ছ ও নির্মোহ বিজ্ঞান-দৃষ্টি লইয়া এই সুবিস্তৃত সাহিত্য অনুশীলন না করিলে পরিচিত ছায়া-উপমারূপক প্রতীকের পশ্চাতে, আপাত অর্থের পশ্চাতে, যে নিগূঢ় অর্থ বিদ্যমান তাহা সহজে ধরা পড়ে না।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, পৃষ্ঠা-৫৮৬)
অতএব, মহাযানের উচ্চকোটির দার্শনিক ধারণার সাথে এই তন্ত্রাশ্রিত সাধনপন্থার মিশ্রণ জনিত সামগ্রিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা প্রকৃতই কৌতুহলোদ্দীপক।
‘বলা বাহুল্য, এই সব বিভিন্ন যান ও ধর্মমত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; অধিকাংশ গ্রন্থ এখনও অনূদিত ও আলোচিতই হয় নাই। অনুবাদ এবং আলোচনার বাধাও বিস্তর। প্রথমত, যে সংস্কৃত ভাষায় মূল গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়াছিল, সে সংস্কৃত অত্যন্ত ব্যাকরণদোষদুষ্ট শুদ্ধ সুবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষাব্যবহারের কোনও বালাই-ই যেমন বৌদ্ধ আচার্যদের ছিল না। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেন, বুঝিতে পারিলেই হইল; ছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার শব্দ বা পদরীতি ইত্যাদি অশুদ্ধ বা অপ্রচলিত হইলেও কিছু ক্ষতি নাই। কালচক্রযানের বিমলপ্রভা নামে একটি টীকায় বলা হইয়াছে, বৌদ্ধ আচার্যরা স্বেচ্ছাপূর্বক সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি-পদ্ধতি, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি অমান্য করিতেন; যাঁহারা মানিয়া চলিতেন তাঁহাদের বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন! ঠিক এই কারণেই তিব্বতী অনুবাদও বহুক্ষেত্রে দুর্বোধ্য এবং তাহা হইতে সংস্কৃতে পুর্ননুবাদ খুব সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, এই সব প্রত্যেকটি ধর্ম গুরুনির্ভর ধর্ম, গুরু ছাড়া এই ধর্মের গুহ্য সাধন প্রক্রিয়ার রহস্য ভেদ করা অসম্ভব বলিলেই চলে, এবং দীক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া গুরুরা অন্য কাহারও নিকট সে রহস্য ভেদ ও ব্যাখ্যা করিতেন না। সেই হেতু এই সব ধর্মের বিস্তৃতি দীক্ষিত চক্র বা মণ্ডলের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ; সর্বসাধারণ সেই সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতেই পারিত না। গুরুরা দীক্ষিতদের নিকট এবং দীক্ষিতরা পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের গুহ্যসাধনা সম্বন্ধে যে-ভাষায় কথা বলিতেন সে-ভাষাও ছিল গুহ্যভাষা। যে-ভাষার নাম ছিল সন্ধাভাষা (সন্ধিভাষা), যে ভাষার শুধু ‘মৌলিক’ ‘সম্পূর্ণ’ ‘নিগূঢ়’ সত্যের কথা বলে; কিন্তু যত মৌলিক, সম্পূর্ণ এবং নিগূঢ়ই হোক না কেন সে-ভাষা, অদীক্ষিত জনের কাছে তাহা ছিল দুর্বোধ্য। এ-ভাষায় যাহা ‘অভিপ্রায়িক’, অর্থাৎ আপাত যে-অর্থ কোনও বাক্যের বা পদের, তাহাই তাহার নিগূঢ় অর্থাৎ মৌলিক, সম্পূর্ণ অর্থ নয়; মৌলিক সম্পূর্ণ উদ্দিষ্ট অর্থের দিকে তাহা ইঙ্গিত করে মাত্র। কাজেই, সে ভাষার মৌলিক উদ্দিষ্ট অর্থ ধরিতে পারা সহজ নয়। তৃতীয়ত, ইঁহাদের সাধনপন্থা এবং প্রক্রিয়াও ছিল অত্যন্ত গুহ্য। নানা প্রকারের যাদুমন্ত্র, যাদুপ্রক্রিয়া, নানা বিধিবিধান, সাধনমন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, ধারণী, যোগ, সমাধি প্রভৃতি লইয়া এই বৌদ্ধাচার্যরা এমন একটি রহস্যময় জগৎ গড়িয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র-জগতের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও সর্বত্র সর্বথা তাহা আমাদের অধিগম্য নয়। সে-জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচিত সাধন-রীতি-পদ্ধতি, নীতি ও প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ কমই। গুহ্য রহস্যময় সন্ধাভাষায় বৌদ্ধ আচার্যরা গুহ্যতর সাধন-প্রক্রিয়া ও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। চতুর্থত, যে-সব ছায়া, রূপক, উপমা, প্রতীক এবং যোগারূঢ় শব্দ আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের সাধন-নীতি ও আদর্শ, রীতি ও প্রক্রিয়া এবং অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে, সে-গুলি সমসাময়িক সাধারণ নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, যৌন-জীবন এবং যৌন-প্রক্রিয়া হইতেই আহৃত, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই জীবন ও প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে তাহারা যে অর্থ ও ইঙ্গিত বহন করে তাহা একান্তই আপাত অর্থ ও ইঙ্গিত, এবং সে অর্থ ও ইঙ্গি আমাদের বর্তমান রুচি ও সংস্কারকে আঘাত করে। কাজেই স্বচ্ছ ও নির্মোহ বিজ্ঞান-দৃষ্টি লইয়া এই সুবিস্তৃত সাহিত্য অনুশীলন না করিলে পরিচিত ছায়া-উপমারূপক প্রতীকের পশ্চাতে, আপাত অর্থের পশ্চাতে, যে নিগূঢ় অর্থ বিদ্যমান তাহা সহজে ধরা পড়ে না।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, পৃষ্ঠা-৫৮৬)
অতএব, মহাযানের উচ্চকোটির দার্শনিক ধারণার সাথে এই তন্ত্রাশ্রিত সাধনপন্থার মিশ্রণ জনিত সামগ্রিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা প্রকৃতই কৌতুহলোদ্দীপক।
তান্ত্রিক-বৌদ্ধধর্মে দেবীবাদ
এ প্রসঙ্গে এমন প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে, বৌদ্ধদর্শনের মতো একটি নৈরাত্ম্যবাদী দর্শনের ছায়াতলে গড়ে ওঠা বৌদ্ধধর্মের পরম্পরায় এই যে আত্মা ও বিভিন্ন কাল্পনিক দেবসংঘের আবির্ভাব, তাকে কি প্রকৃতই বুদ্ধ অনুসারী সাধক-সম্প্রদায় বলা যায়? নাকি প্রাচীন কোনো লোকায়তিক ঘরানার গুহ্য সাধক-সম্প্রদায়ের সাধনপন্থার মধ্যে প্রাচীন হিন্দুতান্ত্রিক শাক্ত ধারণা ও মহাযানী বৌদ্ধমতের দার্শনিক প্রপঞ্চ মিলেমিশে নতুন কোনো সাধনপন্থার স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে এগিয়ে গেছে? কিন্তু এই প্রশ্নের নিরসন আদৌ সহজসাধ্য নয় বলেই মনে হয়। কেননা, বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ সাধনমালায় উড্ডিয়ান (ধারণা করা হয় বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রাম), (অসমের) কামাখ্যা, সিরিহট্ট (বর্তমানের শ্রীহট্ট) ও পূর্ণগিরি এই চারটি তন্ত্রের মুখ্য পীঠস্থান বলে উল্লেখ আছে, যেগুলো বৌদ্ধদেবী বজ্রযোগিনীর পূজার জন্য বিখ্যাত ছিলো। তাছাড়া নালন্দা, বিক্রমশিলা, সারনাথ, ওদন্তপুরী, জগদ্দল ইত্যাতি প্রাচীন বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠগুলোতে বজ্রযানের অনুশীলন হতো বলেও জানা যায়–
‘কামাখ্যা সিরিহট্ট পূর্ণগিরি ও উড্ডিয়ানই তন্ত্রের আদি পীঠ। পূর্ববঙ্গ ও আসামই তন্ত্রের আদি স্থান। এই স্থানে তান্ত্রিক বজ্রযানের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং এই স্থান হইতেই নিকটবর্তী প্রদেশগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নালন্দা বিক্রমশিলা সারনাথ ওদন্তপুরী জগদ্দল ইত্যাদি বিদ্যাপীঠগুলিতে বজ্রযানের অনুশীলন হইত। সেসকল স্থানে তন্ত্র ও যোগমার্গের উপদেশ দেওয়া হইত এবং ছাত্রও তৈয়ারি করা হইত। সমগ্র বাংলায় বিহারে এবং উড়িষ্যায় বজ্রযানের প্রভাব অত্যধিক ছিল এবং এইসকল স্থানেই বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি সর্বাপেক্ষা বেশি পাওয়া যায়।’
‘বৌদ্ধ সাহিত্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর সাধনার কথা গুহ্যসমাজতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই তন্ত্রখানির রচনায় অসঙ্গের কিছু হাত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। অসঙ্গ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বসুবন্ধু বৌদ্ধ জগতে সুপরিচিত। লামা তারানাথ নামক এক তিব্বতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতের মতে তন্ত্রের উৎপত্তি পূর্বেই হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় তিন শত বৎসর সুপ্ত অবস্থায় ছিল এবং গোপনভাবে গুরুশিষ্যপরম্পরায় লুক্কায়িত ছিল, পাল-রাজত্বের সময় সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা উহা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বজ্রযানের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবলভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের আদিতে মুসলমান-আক্রমণ হয় এবং সে সময়ে অনেক মঠ ও বিদ্যাপীঠ ধ্বংস হয়। তাহার পর হইতেই বজ্রযান ভারতে নিষ্প্রভ হইয়া যায় এবং কিছুকাল পরে বিলুপ্ত হয়। বজ্রযানের অনুসারীরা হয় হিন্দু সমাজে মিলাইয়া যায়, নয় মুসলমান হইয়া যায়। চৈতন্যদেব অনেককে বৈষ্ণব করিয়া নেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ধারণা ছিল, বৌদ্ধদের ভিতর তন্ত্র ছিল না এবং তাহারা দেবদেবীর উপাসনা করিত না। কিন্তু এখন তন্ত্রসাহিত্যের গ্রন্থ কিছুকিছু প্রকাশ হওয়ায় সে ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনও সহস্র সহস্র বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। এইগুলি যতদিন না প্রকাশিত হয় ততদিন বজ্রযানের পূর্ণ স্বরূপ জানা সম্ভব হইবে না।’- (ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বৌদ্ধদের দেবদেবী, পৃষ্ঠা-২৬)
‘কামাখ্যা সিরিহট্ট পূর্ণগিরি ও উড্ডিয়ানই তন্ত্রের আদি পীঠ। পূর্ববঙ্গ ও আসামই তন্ত্রের আদি স্থান। এই স্থানে তান্ত্রিক বজ্রযানের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং এই স্থান হইতেই নিকটবর্তী প্রদেশগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নালন্দা বিক্রমশিলা সারনাথ ওদন্তপুরী জগদ্দল ইত্যাদি বিদ্যাপীঠগুলিতে বজ্রযানের অনুশীলন হইত। সেসকল স্থানে তন্ত্র ও যোগমার্গের উপদেশ দেওয়া হইত এবং ছাত্রও তৈয়ারি করা হইত। সমগ্র বাংলায় বিহারে এবং উড়িষ্যায় বজ্রযানের প্রভাব অত্যধিক ছিল এবং এইসকল স্থানেই বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি সর্বাপেক্ষা বেশি পাওয়া যায়।’
‘বৌদ্ধ সাহিত্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর সাধনার কথা গুহ্যসমাজতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই তন্ত্রখানির রচনায় অসঙ্গের কিছু হাত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। অসঙ্গ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বসুবন্ধু বৌদ্ধ জগতে সুপরিচিত। লামা তারানাথ নামক এক তিব্বতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতের মতে তন্ত্রের উৎপত্তি পূর্বেই হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় তিন শত বৎসর সুপ্ত অবস্থায় ছিল এবং গোপনভাবে গুরুশিষ্যপরম্পরায় লুক্কায়িত ছিল, পাল-রাজত্বের সময় সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা উহা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বজ্রযানের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবলভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের আদিতে মুসলমান-আক্রমণ হয় এবং সে সময়ে অনেক মঠ ও বিদ্যাপীঠ ধ্বংস হয়। তাহার পর হইতেই বজ্রযান ভারতে নিষ্প্রভ হইয়া যায় এবং কিছুকাল পরে বিলুপ্ত হয়। বজ্রযানের অনুসারীরা হয় হিন্দু সমাজে মিলাইয়া যায়, নয় মুসলমান হইয়া যায়। চৈতন্যদেব অনেককে বৈষ্ণব করিয়া নেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ধারণা ছিল, বৌদ্ধদের ভিতর তন্ত্র ছিল না এবং তাহারা দেবদেবীর উপাসনা করিত না। কিন্তু এখন তন্ত্রসাহিত্যের গ্রন্থ কিছুকিছু প্রকাশ হওয়ায় সে ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনও সহস্র সহস্র বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। এইগুলি যতদিন না প্রকাশিত হয় ততদিন বজ্রযানের পূর্ণ স্বরূপ জানা সম্ভব হইবে না।’- (ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বৌদ্ধদের দেবদেবী, পৃষ্ঠা-২৬)
এ-বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলছেন– ‘মহাযান বৌদ্ধধর্ম নিজেকে জনপ্রিয় করার অভিপ্রায়ে স্থানীয় লৌকিক ধর্মবিশ্বাসসমূহের সঙ্গে আপোষ করেছিল যার ফলে অসংখ্য স্থানীয় দেবদেবী বৌদ্ধধর্মে গৃহীত হয়েছিল। ভারতের গ্রাম্য কৃষিজীবী সমাজে স্বাভাবিকভাবে দেবীপ্রাধান্যমূলক ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ছিল। কৃষিজীবী সমাজের সুপ্রাচীন মাতৃদেবীর ধারণাই কালক্রমে সকল জাগতিক উপাদানের প্রতিরূপ বা প্রকৃতি এবং সেগুলির কার্যকারিতার মূল প্রেরণা বা শক্তি হিসাবে কল্পিত হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মে এই শক্তিই বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী বা কৃষ্ণের শক্তি রাধা হিসাবে কল্পিত হয়েছে; শৈবধর্মে এই শক্তিই শিবের শক্তি দেবী ; বৌদ্ধধর্মে এই শক্তিই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের শক্তিস্বরূপা নানা নামের দেবী, দার্শনিক পর্যায়ে যা প্রজ্ঞা বা শূন্যতা। এইভাবে শক্তির ধারণার অনুপ্রবেশের ফলে আদিম তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ মহাযান বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়। বৌদ্ধ গুহ্যসমাজতন্ত্রে মুদ্রা, মাংস ও মৈথুনকে সাধনার অঙ্গ বলা হয়েছে। যুগনদ্ধ বা নারীপুরুষের সম্মিলিত মিথুনমূর্তির দ্বারা বুদ্ধগণ, বোধিসত্ত্বগণ ও তাঁদের শক্তিসমূহ উপস্থাপিত হতে শুরু করেন। অনঙ্গবজ্রের প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি গ্রন্থে মিথুনতত্ত্ব ও মহামুদ্রাতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।’- (ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-১১৩)
অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্বের ‘ধর্মকর্ম : ধ্যান-ধারণা’ অধ্যায়ে মহাযানের বিবর্তন প্রসঙ্গে বলেন–
‘অষ্টম ও নবম শতকে মহাযান বৌদ্ধধর্মে নূতনতর তান্ত্রিক ধ্যান-কল্পনার স্পর্শ লাগিয়াছিল এবং তাহার ফলে দশম শতক হইতেই বৌদ্ধ ধর্মে গুহ্য সাধনতত্ত্ব, নীতিপদ্ধতি ও পূজাচারের প্রসার দেখা দিয়াছিল। এই গুহ্য সাধনার ধ্যান-কল্পনা কোথা হইতে কী করিয়া মহাযান-দেহে প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর ঘটাইল এবং বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি করিল বলা কঠিন। মহাযানের মধ্যে তাহার বীজ সুপ্ত ছিল কিনা তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে আচার্য অসঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, পর্বত-কান্তারবাসী সুবৃহৎ কৌম-সমাজকে বৌদ্ধধর্মের সীমার মধ্যে আকর্ষণ করিবার জন্য ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, যোগিনী, ডাকিনী, পিশাচ ও মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবী প্রভৃতিকে অসঙ্গ মহাযান-দেবায়তনে স্থান দান করিয়াছিলেন। নানা গুহ্য, মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী (গূঢ়ার্থক অক্ষর) প্রভৃতিও প্রবেশ করিয়াছিল মহাযান ধ্যান-কল্পনায়, পূজাচারে, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে এবং তাহাও অসঙ্গেরই অনুমোদনে। এই ঐহিত্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, বলা কঠিন। তবে, বলা বাহুল্য, এই সব গুহ্য, রহস্যময়, গূঢ়ার্থক মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী বীজ, মণ্ডল প্রভৃতি সমস্তই আদিম কৌম সমাজের যাদুশক্তিতে বিশ্বাস হইতেই উদ্ভূত। সহজ সমাজতান্ত্রিক যুক্তিতেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম উভয়েরই ভাব-কল্পনায় ও ধর্মগত আচারানুষ্ঠানে ইহাদের প্রবেশ লাভ কিছু অস্বাভাবিক নয়। উভয়কেই নিজ নিজ প্রভাবের সীমা বিস্তৃত করিবার চেষ্টায় আদিম কৌম-সমাজের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; তাহা ছাড়া উভয় ধর্ম সম্প্রদায়েরই নিম্নতর স্তরগুলিতে যে সুবৃহৎ মানবগোষ্ঠী ক্রমশ আসিয়া ভিড় করিতেছিল তাঁহারা তো ক্রমহ্রস্বায়মান আদিবাসী সমাজেরই জনসাধারণ। তাঁহারা তো নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, দেবদেবী লইয়াই বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আসিয়া আশ্রয় লইতেছিলেন। অন্যদিকে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও চেষ্টা ছিল নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও ভাব-কল্পনা অনুযায়ী, নিজ নিজ শক্তি ও প্রয়োজনানুযায়ী সদ্যোক্ত আদিম ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, দেবদেবী ইত্যাদির রূপ ও মর্ম কিছু রাখিয়া কিছু ছাড়িয়া, শোধিত ও রূপান্তরিত করিয়া লওয়া। অসঙ্গের সময় হইতেই হয়তো বৌদ্ধধর্মে এই রূপান্তরের সূচনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, সন্দেহ নাই যে, বাঙলা-বিহারের, এক কথায় পূর্ব-ভারতের বৌদ্ধ ধর্মে এই ধরনের রূপান্তরের একটা গতি অষ্টম-নবম শতকেই ধরা পড়িয়াছিল। ইহার মূলে ঐতিহাসিক একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ছিল ; সে-কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই, এই মাত্র। তবু এই পর্বের বাঙলা-বিহারে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেরই এই বিরাট বিবর্তনের (যাহাকে সাধারণ কথায় তান্ত্রিক বিবর্তন বলা চলে) কারণ সম্বন্ধে একটু অনুমান বোধ হয় করা চলে।’- (নীহাররঞ্জন রায়/ বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব/ পৃষ্ঠা-৫২৫-২৬)
এ প্রেক্ষিতে খ্রিস্টোত্তর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকেই যে হিমালয়ক্রোড়স্থিত পার্বত্য-কান্তাময় দেশগুলির সঙ্গে গাঙ্গেয় প্রদেশের প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে মধ্য ও পূর্ব-ভারতের আদান-প্রদান বেড়ে যাওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে, রাষ্ট্রীয় দৌত্যবিনিময়, সমরাভিযান প্রভৃতি আশ্রয় করে এই সব পার্বত্য দেশের আদিম সংস্কার ও সংস্কৃতির স্রোত বাঙলা-বিহারে প্রবাহিত হতে শুরু করে, সেদিকেও নীহাররঞ্জন রায়ের বিশ্লেষণী দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তিনি বলেন– ‘সপ্তম শতকের পূর্ব-বাঙলার খড়্গ-রাজবংশ বোধ হয় এই স্রোতেরই দান। ধর্মপাল ও দেবপালের কালে এই যোগাযোগ আরও বাড়িয়াই গিয়াছিল। পরবর্তীকালে আমরা যাহাকে বলিয়াছি তান্ত্রিক ধর্ম তাহার একটা দিক এই যোগাযোগের ফল হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক হয়তো নয়। তন্ত্রধর্মের প্রসারের ভৌগোলিক লীলাক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে এ-অনুমান একেবারে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।’
‘অষ্টম ও নবম শতকে মহাযান বৌদ্ধধর্মে নূতনতর তান্ত্রিক ধ্যান-কল্পনার স্পর্শ লাগিয়াছিল এবং তাহার ফলে দশম শতক হইতেই বৌদ্ধ ধর্মে গুহ্য সাধনতত্ত্ব, নীতিপদ্ধতি ও পূজাচারের প্রসার দেখা দিয়াছিল। এই গুহ্য সাধনার ধ্যান-কল্পনা কোথা হইতে কী করিয়া মহাযান-দেহে প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর ঘটাইল এবং বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি করিল বলা কঠিন। মহাযানের মধ্যে তাহার বীজ সুপ্ত ছিল কিনা তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে আচার্য অসঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, পর্বত-কান্তারবাসী সুবৃহৎ কৌম-সমাজকে বৌদ্ধধর্মের সীমার মধ্যে আকর্ষণ করিবার জন্য ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, যোগিনী, ডাকিনী, পিশাচ ও মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবী প্রভৃতিকে অসঙ্গ মহাযান-দেবায়তনে স্থান দান করিয়াছিলেন। নানা গুহ্য, মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী (গূঢ়ার্থক অক্ষর) প্রভৃতিও প্রবেশ করিয়াছিল মহাযান ধ্যান-কল্পনায়, পূজাচারে, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে এবং তাহাও অসঙ্গেরই অনুমোদনে। এই ঐহিত্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, বলা কঠিন। তবে, বলা বাহুল্য, এই সব গুহ্য, রহস্যময়, গূঢ়ার্থক মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী বীজ, মণ্ডল প্রভৃতি সমস্তই আদিম কৌম সমাজের যাদুশক্তিতে বিশ্বাস হইতেই উদ্ভূত। সহজ সমাজতান্ত্রিক যুক্তিতেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম উভয়েরই ভাব-কল্পনায় ও ধর্মগত আচারানুষ্ঠানে ইহাদের প্রবেশ লাভ কিছু অস্বাভাবিক নয়। উভয়কেই নিজ নিজ প্রভাবের সীমা বিস্তৃত করিবার চেষ্টায় আদিম কৌম-সমাজের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; তাহা ছাড়া উভয় ধর্ম সম্প্রদায়েরই নিম্নতর স্তরগুলিতে যে সুবৃহৎ মানবগোষ্ঠী ক্রমশ আসিয়া ভিড় করিতেছিল তাঁহারা তো ক্রমহ্রস্বায়মান আদিবাসী সমাজেরই জনসাধারণ। তাঁহারা তো নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, দেবদেবী লইয়াই বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আসিয়া আশ্রয় লইতেছিলেন। অন্যদিকে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও চেষ্টা ছিল নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও ভাব-কল্পনা অনুযায়ী, নিজ নিজ শক্তি ও প্রয়োজনানুযায়ী সদ্যোক্ত আদিম ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, দেবদেবী ইত্যাদির রূপ ও মর্ম কিছু রাখিয়া কিছু ছাড়িয়া, শোধিত ও রূপান্তরিত করিয়া লওয়া। অসঙ্গের সময় হইতেই হয়তো বৌদ্ধধর্মে এই রূপান্তরের সূচনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, সন্দেহ নাই যে, বাঙলা-বিহারের, এক কথায় পূর্ব-ভারতের বৌদ্ধ ধর্মে এই ধরনের রূপান্তরের একটা গতি অষ্টম-নবম শতকেই ধরা পড়িয়াছিল। ইহার মূলে ঐতিহাসিক একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ছিল ; সে-কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই, এই মাত্র। তবু এই পর্বের বাঙলা-বিহারে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেরই এই বিরাট বিবর্তনের (যাহাকে সাধারণ কথায় তান্ত্রিক বিবর্তন বলা চলে) কারণ সম্বন্ধে একটু অনুমান বোধ হয় করা চলে।’- (নীহাররঞ্জন রায়/ বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব/ পৃষ্ঠা-৫২৫-২৬)
এ প্রেক্ষিতে খ্রিস্টোত্তর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকেই যে হিমালয়ক্রোড়স্থিত পার্বত্য-কান্তাময় দেশগুলির সঙ্গে গাঙ্গেয় প্রদেশের প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে মধ্য ও পূর্ব-ভারতের আদান-প্রদান বেড়ে যাওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে, রাষ্ট্রীয় দৌত্যবিনিময়, সমরাভিযান প্রভৃতি আশ্রয় করে এই সব পার্বত্য দেশের আদিম সংস্কার ও সংস্কৃতির স্রোত বাঙলা-বিহারে প্রবাহিত হতে শুরু করে, সেদিকেও নীহাররঞ্জন রায়ের বিশ্লেষণী দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তিনি বলেন– ‘সপ্তম শতকের পূর্ব-বাঙলার খড়্গ-রাজবংশ বোধ হয় এই স্রোতেরই দান। ধর্মপাল ও দেবপালের কালে এই যোগাযোগ আরও বাড়িয়াই গিয়াছিল। পরবর্তীকালে আমরা যাহাকে বলিয়াছি তান্ত্রিক ধর্ম তাহার একটা দিক এই যোগাযোগের ফল হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক হয়তো নয়। তন্ত্রধর্মের প্রসারের ভৌগোলিক লীলাক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে এ-অনুমান একেবারে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।’
এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এখানে আরও কিছু তথ্য লক্ষ্যণীয়। শশিভূষণ দাশগুপ্তের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রচুর প্রসার ঘটেছিলো মহাচীনে– অর্থাৎ বিহার-বঙ্গ-আসামের কিছু অঞ্চল এবং নেপাল-তিব্বত-ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলে। ফলে এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধা কিছু কিছু দেবী বৌদ্ধ-তন্ত্রে স্থান পেয়েছিলেন, তাঁরাই সম্ভবত বৌদ্ধতন্ত্রের মারফতে হিন্দু-তন্ত্রাদিতেও দেবী বলে গৃহীতা এবং স্বীকৃতা হয়েছেন। তারা বা উগ্রতারা বা একজটা দেবী মূলত তিব্বতের দেবী বলে ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বিশ্বাস [Evolution of the Tantras]। পর্ণশবরী দেবীও এভাবে বৌদ্ধ-তন্ত্র থেকেই গৃহীত বলে ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মত [সাধনমালার ভূমিকা এবং Buddhist Iconography]। হিন্দু-তন্ত্রে বর্ণিত ষট্চক্রের অধিষ্ঠাত্রী ডাকিনী, হাকিনী, লাকিনী, রাকিণী, শাকিনী দেবীগণের সবাই না হলেও কেউ কেউ মহাচীনাঞ্চল থেকে গৃহীত বলে শশিভূষণ দাশগুপ্তের অভিমত। তবে তিনি মনে করেন,–
‘বাঙলাদেশ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান ঘাঁটি ছিল, এ সত্য আজ ঐতিহাসিক তথ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই তন্ত্রসমূহ এবং তাঁহাদের উপরে রচিত অনেক টীকা-টীপ্পনীর বাঙলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন দেশেই রচিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইবার তথ্য আমাদের যথেষ্ট নাই। পরবর্তী কালের যে বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙলাদেশেই লিখিত বলিয়া আমরা একেবারে নিশ্চিত হইতে পারি তাহা হইল বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণ-রচিত দোহা ও চর্যাগীতিগুলি। এই দোহা ও চর্যাগীতিগুলি যদিও প্রধানতঃ সহজিয়া বৌদ্ধ-মতবাদ ও সাধন-পন্থা-অবলম্বনেই লিখিত তথাপি পরোক্ষভাবে ইহার ভিতরে তৎকালীন দেবীবাদ-সম্বন্ধে কিছু কিছু লক্ষণীয় তথ্য লাভ করা যায়। এই দোহা ও গীতিগুলি মোটামুটিভাবে খ্রীস্টীয় দশম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতরে রচিত বলিয়া গৃহীত; সুতরাং এইগুলির ভিতরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিতর দিয়া তৎকালীন প্রচলিত দেবীবাদ বা শক্তিবাদের একটি বিশেষ দিককে আমরা গভীর এবং ব্যাপকভাবে বুঝিতে সমর্থ হই।’
‘বৌদ্ধ-দোহা ও গীতিগুলির মধ্যে আমরা এক ‘দেবী’র উল্লেখ দেখিতে পাই; এই দেবী নৈরাত্মা, নৈরামণি, ডোম্বী, চণ্ডালী, মাগঙ্গী, শবরী প্রভৃতি নানারূপে অভিহিত। সাধনতত্ত্বের মধ্যে এই দেবীকে রূপকচ্ছলেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই ব্যাখ্যাদ্বারা সিদ্ধাচার্যগণের মনঃসংগঠনের সবখানি পরিচয় পাওয়া যায় না। তৎকালে প্রচলিত ভারতীয় দেবীতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্বের সহিত এই বৌদ্ধ-দেবীর নিগূঢ় যোগ আছে বলিয়া মনে করি।’- (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৩১)
‘বাঙলাদেশ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান ঘাঁটি ছিল, এ সত্য আজ ঐতিহাসিক তথ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই তন্ত্রসমূহ এবং তাঁহাদের উপরে রচিত অনেক টীকা-টীপ্পনীর বাঙলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন দেশেই রচিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইবার তথ্য আমাদের যথেষ্ট নাই। পরবর্তী কালের যে বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙলাদেশেই লিখিত বলিয়া আমরা একেবারে নিশ্চিত হইতে পারি তাহা হইল বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণ-রচিত দোহা ও চর্যাগীতিগুলি। এই দোহা ও চর্যাগীতিগুলি যদিও প্রধানতঃ সহজিয়া বৌদ্ধ-মতবাদ ও সাধন-পন্থা-অবলম্বনেই লিখিত তথাপি পরোক্ষভাবে ইহার ভিতরে তৎকালীন দেবীবাদ-সম্বন্ধে কিছু কিছু লক্ষণীয় তথ্য লাভ করা যায়। এই দোহা ও গীতিগুলি মোটামুটিভাবে খ্রীস্টীয় দশম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতরে রচিত বলিয়া গৃহীত; সুতরাং এইগুলির ভিতরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিতর দিয়া তৎকালীন প্রচলিত দেবীবাদ বা শক্তিবাদের একটি বিশেষ দিককে আমরা গভীর এবং ব্যাপকভাবে বুঝিতে সমর্থ হই।’
‘বৌদ্ধ-দোহা ও গীতিগুলির মধ্যে আমরা এক ‘দেবী’র উল্লেখ দেখিতে পাই; এই দেবী নৈরাত্মা, নৈরামণি, ডোম্বী, চণ্ডালী, মাগঙ্গী, শবরী প্রভৃতি নানারূপে অভিহিত। সাধনতত্ত্বের মধ্যে এই দেবীকে রূপকচ্ছলেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই ব্যাখ্যাদ্বারা সিদ্ধাচার্যগণের মনঃসংগঠনের সবখানি পরিচয় পাওয়া যায় না। তৎকালে প্রচলিত ভারতীয় দেবীতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্বের সহিত এই বৌদ্ধ-দেবীর নিগূঢ় যোগ আছে বলিয়া মনে করি।’- (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৩১)
সহজিয়া বৌদ্ধ-সাধকদের এই দেবীতত্ত্বকে বুঝতে হলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এই দেবদেবীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পরিচয় থাকা আবশ্যক মনে হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দেবীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস লক্ষ্য করতে গিয়ে শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন–
‘উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে– অর্থাৎ নেপাল-ভূটান-তিব্বত এবং কতকভাবে চীনদেশের কিছু কিছু অংশে আমরা এক আদিবুদ্ধ এবং তাঁহার নিত্যা শক্তি আদিদেবী বা আদিশক্তির কথা জানিতে পারি। এই আদিবুদ্ধের ধারণা বহু স্থলে পরবর্তী মহাযানের ধর্মকায়-বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন। যেরূপ বুদ্ধ সমস্ত প্রপঞ্চাত্মক বহুর পরমাধিষ্ঠান কারণাত্মক একরূপে বিরাজিত, সেই কারণাত্মক অদ্বয়তত্ত্বই পরিকল্পিত হইয়াছে আদি-বুদ্ধরূপে। তিনি নিজে নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিরাকার; কিন্তু সকল বিশেষ গুণ ও আকারের তিনিই পরমাধিষ্ঠান। অতএব তাঁহা হইতেই নিখিল বিশ্ব প্রসৃত। কিন্তু সকল বিকারের মূল কারণ হইয়াও তিনি নিজে নিত্য অবিকারী। কোনও কোনও স্থলে আবার দেখিতে পাই, ধর্মকায়-বুদ্ধই আদিবুদ্ধ নহেন; মহাযানের ত্রিকায়ের শেষকায় ধর্মকায়কেই তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বুদ্ধের চরমকায় বলিয়া স্বীকার করে নাই– ধর্মকায়-বুদ্ধও যেন খানিকটা অব্যক্ত হিরণ্যগর্ভ-তত্ত্ব; তাঁহারও উর্ধ্বে হইল বুদ্ধের চরম স্থিতি– তাহাকে বলা হইয়াছে স্বভাবকায় বুদ্ধ; এই স্বভাবকায়ই হইল অবিকারী শূন্যতায়– ইহাই বুদ্ধের বজ্রকায়। এই স্বভাবকায় বা বজ্রকায় বুদ্ধই আদিবুদ্ধ, তিনিই হইলেন তন্ত্রের পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বরের শক্তি যেমন পরমেশ্বরী– তেমনই আদিবুদ্ধের নিত্যা শক্তি হইলেন আদিদেবী। এক্ষেত্রে হিন্দু-তন্ত্রগুলি তাঁহাদের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীকে আদিবুদ্ধ বা আদিদেবী বা আদিপ্রজ্ঞা হইতে গ্রহণ করিয়াছে, না বৌদ্ধ আদিবুদ্ধ ও আদিদেবী হিন্দু-তন্ত্রের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীর আদর্শ লইয়া বৌদ্ধরূপে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছেন? এই জিজ্ঞাসা এবং এ সম্বন্ধে এ পক্ষে বা সে পক্ষে সিদ্ধান্তকে মূলেই ভুল বলিয়া মনে করি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই শক্তিমান্ ও শক্তির অভেদত্বের মধ্যেই একটা ভেদকল্পনা করিয়া যে শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব দেখিতে পাই, হিন্দু-তান্ত্রিক পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী এবং বৌদ্ধ আদিবুদ্ধ-আদিপ্রজ্ঞা বা আদিদেবীর পরিকল্পনায় আমরা সেই একই প্রাচীন শক্তিতত্ত্বের বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রহণ মাত্র দেখিতে পাই।’
‘প্রাচীন বৈষ্ণব ও শৈব শাস্ত্রে যে শক্তিতত্ত্ব দেখিতে পাই, তাহাতে দেখি প্রপঞ্চাত্মক যে বহিঃসৃষ্টি তাহা পরমেশ্বরের স্বরূপে সহিত অভিন্না সমবায়িনী শক্তি হইতে হয় না; সৃষ্টি হয় বিক্ষেপ-শক্তি বা পরিগ্রহ-শক্তি হইতে। এই তত্ত্বটি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে অন্যরূপে। আদিবুদ্ধ ও আদিদেবী হইতে সৃষ্টি হয় না; সৃষ্টি হয় সশক্তিক ধ্যানিবুদ্ধ বা পঞ্চ তথাগত হইতে। আদিবুদ্ধের সিসৃক্ষাত্মক পঞ্চ প্রকারের ধ্যান আছে, ইহার প্রত্যেকটি ধ্যান হইতে প্রসৃত হন এক এক জন ধ্যানিবুদ্ধ। ইঁহারা হইলেন বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধই হইলেন যথাক্রমে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের দেবতা; সৃষ্টি এই পঞ্চস্কন্ধাত্মক। এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধের পঞ্চশক্তি,– তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে তারা বা বজ্রধাত্বীশ্বরী, মামকী, পাণ্ডরা, আর্যতারা এবং লোচনা। সশক্তিক পঞ্চ-তথাগত মনুষ্যদেহের মস্তক, মুখ, হৃদয়, নাভী ও পাদদেশ এই পঞ্চস্থানে অধিষ্ঠান করেন। দেহ-অবলম্বনে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধনার প্রারম্ভে দেহশুদ্ধির দ্বারা যোগদেহ লাভ করিতে হইলে প্রথমে এই সশক্তিক পঞ্চতথাগতকে দেহের বিভিন্ন দেশে অধিষ্ঠিত করিতে হয়। তাহাদ্বারাই তথাগত-দেহ লাভ হয়। তথাগত-দেহ ব্যতীত সাধনা হয় না।’- (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৩২-৩৩)
‘উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে– অর্থাৎ নেপাল-ভূটান-তিব্বত এবং কতকভাবে চীনদেশের কিছু কিছু অংশে আমরা এক আদিবুদ্ধ এবং তাঁহার নিত্যা শক্তি আদিদেবী বা আদিশক্তির কথা জানিতে পারি। এই আদিবুদ্ধের ধারণা বহু স্থলে পরবর্তী মহাযানের ধর্মকায়-বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন। যেরূপ বুদ্ধ সমস্ত প্রপঞ্চাত্মক বহুর পরমাধিষ্ঠান কারণাত্মক একরূপে বিরাজিত, সেই কারণাত্মক অদ্বয়তত্ত্বই পরিকল্পিত হইয়াছে আদি-বুদ্ধরূপে। তিনি নিজে নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিরাকার; কিন্তু সকল বিশেষ গুণ ও আকারের তিনিই পরমাধিষ্ঠান। অতএব তাঁহা হইতেই নিখিল বিশ্ব প্রসৃত। কিন্তু সকল বিকারের মূল কারণ হইয়াও তিনি নিজে নিত্য অবিকারী। কোনও কোনও স্থলে আবার দেখিতে পাই, ধর্মকায়-বুদ্ধই আদিবুদ্ধ নহেন; মহাযানের ত্রিকায়ের শেষকায় ধর্মকায়কেই তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বুদ্ধের চরমকায় বলিয়া স্বীকার করে নাই– ধর্মকায়-বুদ্ধও যেন খানিকটা অব্যক্ত হিরণ্যগর্ভ-তত্ত্ব; তাঁহারও উর্ধ্বে হইল বুদ্ধের চরম স্থিতি– তাহাকে বলা হইয়াছে স্বভাবকায় বুদ্ধ; এই স্বভাবকায়ই হইল অবিকারী শূন্যতায়– ইহাই বুদ্ধের বজ্রকায়। এই স্বভাবকায় বা বজ্রকায় বুদ্ধই আদিবুদ্ধ, তিনিই হইলেন তন্ত্রের পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বরের শক্তি যেমন পরমেশ্বরী– তেমনই আদিবুদ্ধের নিত্যা শক্তি হইলেন আদিদেবী। এক্ষেত্রে হিন্দু-তন্ত্রগুলি তাঁহাদের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীকে আদিবুদ্ধ বা আদিদেবী বা আদিপ্রজ্ঞা হইতে গ্রহণ করিয়াছে, না বৌদ্ধ আদিবুদ্ধ ও আদিদেবী হিন্দু-তন্ত্রের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীর আদর্শ লইয়া বৌদ্ধরূপে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছেন? এই জিজ্ঞাসা এবং এ সম্বন্ধে এ পক্ষে বা সে পক্ষে সিদ্ধান্তকে মূলেই ভুল বলিয়া মনে করি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই শক্তিমান্ ও শক্তির অভেদত্বের মধ্যেই একটা ভেদকল্পনা করিয়া যে শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব দেখিতে পাই, হিন্দু-তান্ত্রিক পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী এবং বৌদ্ধ আদিবুদ্ধ-আদিপ্রজ্ঞা বা আদিদেবীর পরিকল্পনায় আমরা সেই একই প্রাচীন শক্তিতত্ত্বের বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রহণ মাত্র দেখিতে পাই।’
‘প্রাচীন বৈষ্ণব ও শৈব শাস্ত্রে যে শক্তিতত্ত্ব দেখিতে পাই, তাহাতে দেখি প্রপঞ্চাত্মক যে বহিঃসৃষ্টি তাহা পরমেশ্বরের স্বরূপে সহিত অভিন্না সমবায়িনী শক্তি হইতে হয় না; সৃষ্টি হয় বিক্ষেপ-শক্তি বা পরিগ্রহ-শক্তি হইতে। এই তত্ত্বটি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে অন্যরূপে। আদিবুদ্ধ ও আদিদেবী হইতে সৃষ্টি হয় না; সৃষ্টি হয় সশক্তিক ধ্যানিবুদ্ধ বা পঞ্চ তথাগত হইতে। আদিবুদ্ধের সিসৃক্ষাত্মক পঞ্চ প্রকারের ধ্যান আছে, ইহার প্রত্যেকটি ধ্যান হইতে প্রসৃত হন এক এক জন ধ্যানিবুদ্ধ। ইঁহারা হইলেন বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধই হইলেন যথাক্রমে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের দেবতা; সৃষ্টি এই পঞ্চস্কন্ধাত্মক। এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধের পঞ্চশক্তি,– তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে তারা বা বজ্রধাত্বীশ্বরী, মামকী, পাণ্ডরা, আর্যতারা এবং লোচনা। সশক্তিক পঞ্চ-তথাগত মনুষ্যদেহের মস্তক, মুখ, হৃদয়, নাভী ও পাদদেশ এই পঞ্চস্থানে অধিষ্ঠান করেন। দেহ-অবলম্বনে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধনার প্রারম্ভে দেহশুদ্ধির দ্বারা যোগদেহ লাভ করিতে হইলে প্রথমে এই সশক্তিক পঞ্চতথাগতকে দেহের বিভিন্ন দেশে অধিষ্ঠিত করিতে হয়। তাহাদ্বারাই তথাগত-দেহ লাভ হয়। তথাগত-দেহ ব্যতীত সাধনা হয় না।’- (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৩২-৩৩)
অন্যদিকে ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ দেবদেবীর উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেন, বৌদ্ধতন্ত্র মতে সৃষ্টির আদি ও অকৃত্রিম উৎপত্তিস্থল একমাত্র শূন্য। এই শূন্যের অর্থ সৎ বিজ্ঞান ও মহাসুখ, অর্থাৎ শূন্য চিৎসদৃশ ও আনন্দস্বরূপ। এই শূন্য ঘনীভূত হয়ে প্রথমে শব্দরূপে দেখা দেন এবং পরে শব্দ থেকে পুনরায় ঘনীভূত হয়ে দেবতারূপ গ্রহণ করে থাকেন। আদি বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ গুহ্যসমাজতন্ত্রে এই বিবর্তনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, কায়বাকচিত্তবজ্র সমাধি গ্রহণ করছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাধিতে সমাধিস্থ হবার পর এক-একটি শব্দ উত্থিত হচ্ছে। এবং এই ধ্বনি ক্রমশ গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে এক-একটি ধ্যানীবুদ্ধ-আকারে পরিণত হচ্ছে। সংক্ষেপে বৌদ্ধ দেবতার উৎপত্তি প্রসঙ্গে ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের ‘বৌদ্ধদের দেবদেবী’ গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে–
‘জগতের কারণ রূপে শূন্য আপনাকে প্রথমে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। এইগুলিই স্কন্ধ নামে পরিচিত এবং হিন্দুদিগের পঞ্চভূতের ন্যায় জগৎকারণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এই পঞ্চস্কন্ধের নাম– রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই পঞ্চস্কন্ধও অনাদি অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান এবং স্বভাব তাহাদের শূন্যাত্মক। কর্মবশে যখন এই পঞ্চস্কন্ধ একত্র হয় তখনই দৃশ্যমান জীবে পরিণত হইয়া থাকে।’
‘শূন্যকে বজ্রযানে ‘বজ্র’ আখ্যা দেওয়া হয়। তাহার কারণ শূন্য বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, সারবান, ছিদ্ররহিত, অচ্ছেদ্য, অদাহী ও অবিনাশী। শূন্যের নামই বজ্র এবং যে মার্গে শূন্যের সহিত মিলিত হওয়া যায় তাহাকেই শূন্যযান বা বজ্রযান বলা হয়। বজ্রযানের অনুগামীরা এক পৃথক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিগণিত হইয়াছিলেন।’
‘দেবমূর্তির দর্শন ও দেবদেবীর পূজা বজ্রযানের এক বিশেষত্ব। যেহেতু দেবতার দর্শন না হইলে তাঁহার রূপ জানা যায় না, তাই তাঁরা দেবতার দর্শনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু, দেবতার দর্শন সহজসাধ্য নয়। ইহার জন্য দরকার অধ্যাত্মজ্ঞান আত্মোন্নতি এবং আধ্যাত্মিক সাধনা। সেই জন্য সাধন-মার্গে বজ্রযানীরা এককালে ব্রতী হইয়াছিলেন। সাধনার জন্য দরকার হয় শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা। এবং দেবতা-দর্শনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ। জগৎ শূন্যময় বলিয়া সতত ভাবনা, এবং জগতের কল্যাণের জন্য সতত করুণার্দ্রচিত্ত হওয়াও এই সাধনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহাদের এই গুণগুলি আছে তাঁহারা বৌদ্ধই হউন বা অন্য ধর্মাবলম্বীই হউন, দেবতা দর্শন করিতে সক্ষম হন।’
‘প্রথমত, শরীর শুদ্ধি করিয়া একটি পবিত্র ও নির্জন স্থানে বসিয়া সাধনা করিতে হয়। যে দেবতার দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষা হয় সেই দেবতার মন্ত্র জপ করিতে হয় এবং তাহার বীজমন্ত্র হৃদয়দেশে চিন্তা করিতে হয়। কিছুদিন অভ্যাসের পর চিত্ত স্থির হয় এবং সাধনার সময় দেবতা ছাড়া ও তাহার মন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো দিকে মন ধাবিত হয় না। তাহার পর দৃঢ়চিত্তে একান্ত মনে ধ্যান ও জপ করিতে করিতে জাপক ক্রমশ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যান। যখন ইন্দ্রিয়াদির বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় তখন তাহাকে সমাধি বলে। এই সমাধিতে সম্পূর্ণ সুষুপ্তি অবস্থা আনয়ন করে। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় মানব তাহার সময় যাপন করিয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয় বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রাখিয়া থাকে; স্বপ্ন অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সকল সক্রিয় থাকে; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় কোনোরূপ চেতনা থাকে না। এই সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয় এবং সেই সময় মানব শক্তির ভাণ্ডার পরমাত্মার নিকট হইতে নিজের প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করিয়া থাকে। বৌদ্ধদের কথায় জীবাত্মা বোধিচিত্ত বা করুণা ও পরমাত্মা শূন্য বজ্র বা আদিবুদ্ধ।’
‘যখন সাধক দেবতা-দর্শনের উদ্দেশে ধ্যান ও জপ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যান, তখন তাঁহার বোধিচিত্ত শূন্যের সহিত মিলিত হয়। শূন্যের সহিত মিলিত হইবার পর ক্রমশ পাঁচ প্রকারের নিমিত্তের দর্শন হইয়া থাকে। প্রথমে চিত্তাকাশে মরীচিকার দর্শন হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে ধূমের আকার দর্শন হইয়া থাকে; তৃতীয় পর্যায়ে খদ্যোতিকার ন্যায় আলোকবিন্দুর দর্শন হয়, চতুর্থ পর্যায়ে একটি দীপালোকের ন্যায় দৃশ্য দেখা যায় এবং পঞ্চম বা শেষ পর্যায়ে সতত আলোক দেখিতে পাওয়া যায়– সেটা দেখিতে সম্পূর্ণ মেঘশূন্য আকাশের ন্যায়।’
‘এইরূপে ক্রমশ ধ্যানমার্গে অগ্রসর হইলে পূর্ণসমাধি আসে এবং সেই সময়ে সাধক হঠাৎ যে দেবতার সাধনা করিতেছেন সেই দেবতার দর্শন লাভ করেন। আরও এই মার্গে অগ্রসর হইলে দেবতাকে সর্বদাই দেখিতে পান এবং নিজেকেও সেই দেবতারূপে অনুভব করিতে পারেন। এবং এই দেবতা-যোগের ফলে উত্তরোত্তর শক্তিসঞ্চয় করেন এবং নানাপ্রকার লৌকিক ও অনুত্তর সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।’
‘জগৎ কারণ শূন্য সদাসর্বদা পবিত্র ও শুদ্ধ স্বভাব। তাহার কোনোরূপ বাসনা নাই। বোধিচিত্ত বাসনাযুক্ত এবং অনেক প্রকারের। বাসনার তীব্রতায় শূন্য ভাবনা করিলে শূন্যের যে বিকার হয় তাহা সেই বাসনা অনুযায়ীই হইয়া থাকে। এক বাসনায় যেমন এক দেবতার দর্শন হয় সেইরূপ অন্য প্রকারের বাসনায় অন্য প্রকার দেবতার উদ্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ নানাপ্রকারের বোধিচিত্ত হইতে নানাপ্রকার দেবদেবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাসনার যেহেতু অন্ত নাই, সেইহেতু দেবতাও অনন্ত। এই অনন্ত দেবতা লইয়াই দেবসংঘ গঠিত হয়।’
‘কিন্তু দেবতা যতই হউক-না কেন তাঁহাদের উৎপত্তিস্থান কিন্তু এক অনাদি অনন্ত শূন্যতা বা বজ্র। ভাবনাবশে শূন্যে স্ফোট বা বুদবুদ হইয়া থাকে এবং তাহাকে বৌদ্ধেরা ‘স্ফূর্তি’ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শূন্যের এই স্ফূর্তিই দেবতারূপে দেখা দেয়, কিন্তু তাহারা স্বভাবতই নিঃস্বভাব, ঠিক শূন্যেরই মতো। তাই দেবতারা শূন্যাত্মিকা। বৌদ্ধতন্ত্রে বলে সাধনা করিলে প্রথমে শূন্যতার বোধ হয়, দ্বিতীয়ে বীজমন্ত্রের দর্শন হয়, তৃতীয়ে বীজমন্ত্র হইতে বিম্ব অথবা দেবতার অস্পষ্ট আকার দেখা যায় এবং অবশেষে দেবতার সুস্পষ্ট মূর্তি দর্শন হইয়া থাকে। সে মূর্তি অতি মনোহর সর্বাঙ্গসুন্দর কল্পনার অতীত, স্বর্গীয় বর্ণে রঞ্জিত এবং নানাপ্রকার দিব্য বস্ত্র অলংকার ও অস্ত্রশস্ত্রে শোভিত। একবার দেখিলে তাহা আর জীবনে বিস্মৃত হওয়া যায় না।’- ( বৌদ্ধদের দেবদেবী, উপোদ্ঘাত, পৃষ্ঠা- ১৮-২১)
‘জগতের কারণ রূপে শূন্য আপনাকে প্রথমে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। এইগুলিই স্কন্ধ নামে পরিচিত এবং হিন্দুদিগের পঞ্চভূতের ন্যায় জগৎকারণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এই পঞ্চস্কন্ধের নাম– রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই পঞ্চস্কন্ধও অনাদি অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান এবং স্বভাব তাহাদের শূন্যাত্মক। কর্মবশে যখন এই পঞ্চস্কন্ধ একত্র হয় তখনই দৃশ্যমান জীবে পরিণত হইয়া থাকে।’
‘শূন্যকে বজ্রযানে ‘বজ্র’ আখ্যা দেওয়া হয়। তাহার কারণ শূন্য বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, সারবান, ছিদ্ররহিত, অচ্ছেদ্য, অদাহী ও অবিনাশী। শূন্যের নামই বজ্র এবং যে মার্গে শূন্যের সহিত মিলিত হওয়া যায় তাহাকেই শূন্যযান বা বজ্রযান বলা হয়। বজ্রযানের অনুগামীরা এক পৃথক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিগণিত হইয়াছিলেন।’
‘দেবমূর্তির দর্শন ও দেবদেবীর পূজা বজ্রযানের এক বিশেষত্ব। যেহেতু দেবতার দর্শন না হইলে তাঁহার রূপ জানা যায় না, তাই তাঁরা দেবতার দর্শনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু, দেবতার দর্শন সহজসাধ্য নয়। ইহার জন্য দরকার অধ্যাত্মজ্ঞান আত্মোন্নতি এবং আধ্যাত্মিক সাধনা। সেই জন্য সাধন-মার্গে বজ্রযানীরা এককালে ব্রতী হইয়াছিলেন। সাধনার জন্য দরকার হয় শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা। এবং দেবতা-দর্শনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ। জগৎ শূন্যময় বলিয়া সতত ভাবনা, এবং জগতের কল্যাণের জন্য সতত করুণার্দ্রচিত্ত হওয়াও এই সাধনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহাদের এই গুণগুলি আছে তাঁহারা বৌদ্ধই হউন বা অন্য ধর্মাবলম্বীই হউন, দেবতা দর্শন করিতে সক্ষম হন।’
‘প্রথমত, শরীর শুদ্ধি করিয়া একটি পবিত্র ও নির্জন স্থানে বসিয়া সাধনা করিতে হয়। যে দেবতার দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষা হয় সেই দেবতার মন্ত্র জপ করিতে হয় এবং তাহার বীজমন্ত্র হৃদয়দেশে চিন্তা করিতে হয়। কিছুদিন অভ্যাসের পর চিত্ত স্থির হয় এবং সাধনার সময় দেবতা ছাড়া ও তাহার মন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো দিকে মন ধাবিত হয় না। তাহার পর দৃঢ়চিত্তে একান্ত মনে ধ্যান ও জপ করিতে করিতে জাপক ক্রমশ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যান। যখন ইন্দ্রিয়াদির বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় তখন তাহাকে সমাধি বলে। এই সমাধিতে সম্পূর্ণ সুষুপ্তি অবস্থা আনয়ন করে। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় মানব তাহার সময় যাপন করিয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয় বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রাখিয়া থাকে; স্বপ্ন অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সকল সক্রিয় থাকে; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় কোনোরূপ চেতনা থাকে না। এই সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয় এবং সেই সময় মানব শক্তির ভাণ্ডার পরমাত্মার নিকট হইতে নিজের প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করিয়া থাকে। বৌদ্ধদের কথায় জীবাত্মা বোধিচিত্ত বা করুণা ও পরমাত্মা শূন্য বজ্র বা আদিবুদ্ধ।’
‘যখন সাধক দেবতা-দর্শনের উদ্দেশে ধ্যান ও জপ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যান, তখন তাঁহার বোধিচিত্ত শূন্যের সহিত মিলিত হয়। শূন্যের সহিত মিলিত হইবার পর ক্রমশ পাঁচ প্রকারের নিমিত্তের দর্শন হইয়া থাকে। প্রথমে চিত্তাকাশে মরীচিকার দর্শন হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে ধূমের আকার দর্শন হইয়া থাকে; তৃতীয় পর্যায়ে খদ্যোতিকার ন্যায় আলোকবিন্দুর দর্শন হয়, চতুর্থ পর্যায়ে একটি দীপালোকের ন্যায় দৃশ্য দেখা যায় এবং পঞ্চম বা শেষ পর্যায়ে সতত আলোক দেখিতে পাওয়া যায়– সেটা দেখিতে সম্পূর্ণ মেঘশূন্য আকাশের ন্যায়।’
‘এইরূপে ক্রমশ ধ্যানমার্গে অগ্রসর হইলে পূর্ণসমাধি আসে এবং সেই সময়ে সাধক হঠাৎ যে দেবতার সাধনা করিতেছেন সেই দেবতার দর্শন লাভ করেন। আরও এই মার্গে অগ্রসর হইলে দেবতাকে সর্বদাই দেখিতে পান এবং নিজেকেও সেই দেবতারূপে অনুভব করিতে পারেন। এবং এই দেবতা-যোগের ফলে উত্তরোত্তর শক্তিসঞ্চয় করেন এবং নানাপ্রকার লৌকিক ও অনুত্তর সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।’
‘জগৎ কারণ শূন্য সদাসর্বদা পবিত্র ও শুদ্ধ স্বভাব। তাহার কোনোরূপ বাসনা নাই। বোধিচিত্ত বাসনাযুক্ত এবং অনেক প্রকারের। বাসনার তীব্রতায় শূন্য ভাবনা করিলে শূন্যের যে বিকার হয় তাহা সেই বাসনা অনুযায়ীই হইয়া থাকে। এক বাসনায় যেমন এক দেবতার দর্শন হয় সেইরূপ অন্য প্রকারের বাসনায় অন্য প্রকার দেবতার উদ্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ নানাপ্রকারের বোধিচিত্ত হইতে নানাপ্রকার দেবদেবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাসনার যেহেতু অন্ত নাই, সেইহেতু দেবতাও অনন্ত। এই অনন্ত দেবতা লইয়াই দেবসংঘ গঠিত হয়।’
‘কিন্তু দেবতা যতই হউক-না কেন তাঁহাদের উৎপত্তিস্থান কিন্তু এক অনাদি অনন্ত শূন্যতা বা বজ্র। ভাবনাবশে শূন্যে স্ফোট বা বুদবুদ হইয়া থাকে এবং তাহাকে বৌদ্ধেরা ‘স্ফূর্তি’ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শূন্যের এই স্ফূর্তিই দেবতারূপে দেখা দেয়, কিন্তু তাহারা স্বভাবতই নিঃস্বভাব, ঠিক শূন্যেরই মতো। তাই দেবতারা শূন্যাত্মিকা। বৌদ্ধতন্ত্রে বলে সাধনা করিলে প্রথমে শূন্যতার বোধ হয়, দ্বিতীয়ে বীজমন্ত্রের দর্শন হয়, তৃতীয়ে বীজমন্ত্র হইতে বিম্ব অথবা দেবতার অস্পষ্ট আকার দেখা যায় এবং অবশেষে দেবতার সুস্পষ্ট মূর্তি দর্শন হইয়া থাকে। সে মূর্তি অতি মনোহর সর্বাঙ্গসুন্দর কল্পনার অতীত, স্বর্গীয় বর্ণে রঞ্জিত এবং নানাপ্রকার দিব্য বস্ত্র অলংকার ও অস্ত্রশস্ত্রে শোভিত। একবার দেখিলে তাহা আর জীবনে বিস্মৃত হওয়া যায় না।’- ( বৌদ্ধদের দেবদেবী, উপোদ্ঘাত, পৃষ্ঠা- ১৮-২১)
দেবতাদর্শনের এই বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে দেবতাদর্শন একটা আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপার। এর জন্য অনেক সময় দিতে হয়, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, সংযম করতে হয়, অনেক যোগযাগাদি অভ্যাস করতে হয়। নইলে তাতে সিদ্ধিলাভ হয় না। বলা হয়, এই সাধনমার্গের পেছনে এক বিরাট দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে, যা সকলের জন্য প্রশস্ত নয়। এটি কেবলই সাধকের মার্গ, যোগীর মার্গ। এই দেবদেবী প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাসঙ্গিক কিছু বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য মনে হয়। তিনি বলছেন–
‘বৌদ্ধধর্মে দেবতার সংস্রব নাই– দেবতার পূজা-অর্চা হীনযানে ছিলই না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কতদিন পরে বুদ্ধদেবের মূর্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহা লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এখনো মতভেদ আছে– কেহ বলেন, চারি শত বৎসর পরে, কেহ বলেন, পাঁচ শত বৎসর পরে। ইন্ডিয়ান মিউজিয়মে গেলে গান্ধার-শিল্পের কুঠরিতে প্রথম বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি বুদ্ধের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পরে নির্মিত হয়। মহাযানেও শাক্যসিংহের মূর্তি বিহারে বিহারে থাকিত। তাঁহারা উহাকে নির্বাণ লাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমে একটি-একটি করিয়া ধ্যানীবুদ্ধ আসিতে লাগিলেন। প্রথম ‘অমিতাভ’, তারপর ‘অক্ষোভ্য’, তারপর ‘বৈরোচন’, তারপর ‘রত্নসম্ভব’, তারপর ‘অমোঘসিদ্ধি’ আসিয়া জমিলেন। ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের মগধ-কুঠরিতে অনেকগুলি চৈত্য বা স্তূপ আছে। তাহার চারি দিকে চারিটি ‘তথাগতের’ মূর্তি আছে। প্রথম তথাগত ‘বৈরোচন’ স্তূপের মধ্যেই থাকিতেন। তাঁহার জন্য স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গি কাটা হইত না। ক্রমে তিনিও আসিয়া অগ্নিকোণে জমিলেন। শাক্যসিংহ তখন একেবারে উপায় হইয়া গিয়াছেন– স্তূপে তাঁহার স্থান নাই– তাঁহার স্থান বিহারের মধ্যস্থলে যে মন্দির– তাহাতে। তখনকার বৌদ্ধরা বলিতেন, তিনি ‘পঞ্চ তথাগতে’র অথবা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের কলম মাত্র– তিনি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মত কলমবন্দি করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে এই পঞ্চ তথাগতের পাঁচটি শক্তি দাঁড়াইল। শক্তিগণের নাম– ‘লোচনা’, ‘মামকী’, ‘তারা’, ‘পাণ্ডরা’, ‘আর্যতারিকা’। বহুকাল অবধি তাঁহারা যন্ত্রে (যন্ত্র দেবতার প্রতীক) থাকিতেন, তাঁহাদের মূর্তি ছিল না– ক্রমে তাঁহাদেরও মূর্তি হইল। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের পঞ্চ শক্তিতে পাঁচ জন ‘বোধিসত্ত্ব’ হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ‘মঞ্জুশ্রী’ ও ‘অবলোকিতেশ্বর’ প্রধান। বর্তমান কল্পে অর্থাৎ ভদ্রকল্পে ‘অমিতাভ’ প্রধান ধ্যানীবুদ্ধ। তাঁহার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর– প্রধান বোধিসত্ত্ব। অবলোকিতেশ্বর করুণার মূর্তি। তিনি মহোৎসাহে জীব উদ্ধার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার পূজা খুব আরম্ভ হইল। সেবকের উৎসাহ অনুসারে তাঁহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল– অনেক পদ হইতে লাগিল– অনেক মস্তক হইতে লাগিল; তাঁহার পূজা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তারাদেবীও নানা রূপ ধারণ করিয়া বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী, ভৈরব, বুদ্ধগণের উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল। এক ‘অভিধ্যানাত্তরতন্ত্রে’ ‘সম্বরবজ্র’ ‘পীঠপর্ব’ ‘বজ্রসত্ত্ব’ ‘পীঠদেবতা’ ‘ভেরুক’ [হেরুক?] ‘যোগবীর’ ‘পীঠমালা’ ‘বজ্রবীর-ষড়যোগসম্বর’ ‘অমৃতসঞ্জীবনী’ ‘যোগিনী’ ‘কুলডাক’ ‘যোগিনী যোগ-হৃদয়’ ‘বুদ্ধকাপালিকযোগ’ ‘মঞ্জুবজ্র’ ‘নবাক্ষরালীডাক’ ‘বজ্রডাক’ ‘চোমক’ প্রভৃতি অনেক ভৈরব ও যোগিনীর পূজাপদ্ধতি আছে। বোধিসত্ত্ব ও যোগিনীগণের ধ্যানকে সাধন বলে। যে পুস্তকে অনেক ধ্যান লেখা আছে তাহাকে ‘সাধনমালা’ বলে। একখানি ‘সাধনমালা’য় দুই শত ছাপ্পান্নটি সাধন আছে। ‘বজ্রবারাহী’, ‘বজ্রযোগিনী’, ‘কুরুকুল্লা’, ‘মহাপ্রতিসরা’, ‘মহামায়ূরী’, ‘মহাসাহস্র প্রমর্দ্দিনী’ প্রভৃতি অনেক যোগিনীর ধ্যান ইহাতে আছে। এই-সকল সাধন লইয়া মূর্তি নির্মাণে বৌদ্ধকারিগরেরা এক সময়ে যথেষ্ট বাহাদুরি দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরবীর পূজা লইয়া ও তাঁহাদের মূর্তি লইয়া বৌদ্ধধর্ম চলিতে লাগিল, তখন আর অধঃপতনের বাকি কী রহিল?’
‘বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ‘গুহ্যপূজা’ আরম্ভ হইল। লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিব– কাহাকেও দেখিতে দিব না; এ পূজার অর্থ কী? অর্থ এই যে, সে-সকল দেবমূর্তি লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না। ঐ-সকল মূর্তির নাম– উহারা বলিত শম্বর। একে তো অশ্লীল মূর্তি– তাহাতে ভালো কারিগরের হাতের তৈয়ারি– তাহাতে অশ্লীলতার মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। সেই-সকল মূর্তি যখন বুদ্ধদের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল– তখন আর অধঃপাতের বাকি রহিল কী? সে-সকল উপাসনার প্রকার আরো অশ্লীল– সভ্যসমাজে বর্ণনা করা যায় না।’- (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড, বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত, পৃষ্ঠা- ৩৭৫-৭৬)
‘বৌদ্ধধর্মে দেবতার সংস্রব নাই– দেবতার পূজা-অর্চা হীনযানে ছিলই না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কতদিন পরে বুদ্ধদেবের মূর্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহা লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এখনো মতভেদ আছে– কেহ বলেন, চারি শত বৎসর পরে, কেহ বলেন, পাঁচ শত বৎসর পরে। ইন্ডিয়ান মিউজিয়মে গেলে গান্ধার-শিল্পের কুঠরিতে প্রথম বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি বুদ্ধের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পরে নির্মিত হয়। মহাযানেও শাক্যসিংহের মূর্তি বিহারে বিহারে থাকিত। তাঁহারা উহাকে নির্বাণ লাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমে একটি-একটি করিয়া ধ্যানীবুদ্ধ আসিতে লাগিলেন। প্রথম ‘অমিতাভ’, তারপর ‘অক্ষোভ্য’, তারপর ‘বৈরোচন’, তারপর ‘রত্নসম্ভব’, তারপর ‘অমোঘসিদ্ধি’ আসিয়া জমিলেন। ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের মগধ-কুঠরিতে অনেকগুলি চৈত্য বা স্তূপ আছে। তাহার চারি দিকে চারিটি ‘তথাগতের’ মূর্তি আছে। প্রথম তথাগত ‘বৈরোচন’ স্তূপের মধ্যেই থাকিতেন। তাঁহার জন্য স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গি কাটা হইত না। ক্রমে তিনিও আসিয়া অগ্নিকোণে জমিলেন। শাক্যসিংহ তখন একেবারে উপায় হইয়া গিয়াছেন– স্তূপে তাঁহার স্থান নাই– তাঁহার স্থান বিহারের মধ্যস্থলে যে মন্দির– তাহাতে। তখনকার বৌদ্ধরা বলিতেন, তিনি ‘পঞ্চ তথাগতে’র অথবা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের কলম মাত্র– তিনি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মত কলমবন্দি করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে এই পঞ্চ তথাগতের পাঁচটি শক্তি দাঁড়াইল। শক্তিগণের নাম– ‘লোচনা’, ‘মামকী’, ‘তারা’, ‘পাণ্ডরা’, ‘আর্যতারিকা’। বহুকাল অবধি তাঁহারা যন্ত্রে (যন্ত্র দেবতার প্রতীক) থাকিতেন, তাঁহাদের মূর্তি ছিল না– ক্রমে তাঁহাদেরও মূর্তি হইল। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের পঞ্চ শক্তিতে পাঁচ জন ‘বোধিসত্ত্ব’ হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ‘মঞ্জুশ্রী’ ও ‘অবলোকিতেশ্বর’ প্রধান। বর্তমান কল্পে অর্থাৎ ভদ্রকল্পে ‘অমিতাভ’ প্রধান ধ্যানীবুদ্ধ। তাঁহার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর– প্রধান বোধিসত্ত্ব। অবলোকিতেশ্বর করুণার মূর্তি। তিনি মহোৎসাহে জীব উদ্ধার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার পূজা খুব আরম্ভ হইল। সেবকের উৎসাহ অনুসারে তাঁহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল– অনেক পদ হইতে লাগিল– অনেক মস্তক হইতে লাগিল; তাঁহার পূজা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তারাদেবীও নানা রূপ ধারণ করিয়া বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী, ভৈরব, বুদ্ধগণের উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল। এক ‘অভিধ্যানাত্তরতন্ত্রে’ ‘সম্বরবজ্র’ ‘পীঠপর্ব’ ‘বজ্রসত্ত্ব’ ‘পীঠদেবতা’ ‘ভেরুক’ [হেরুক?] ‘যোগবীর’ ‘পীঠমালা’ ‘বজ্রবীর-ষড়যোগসম্বর’ ‘অমৃতসঞ্জীবনী’ ‘যোগিনী’ ‘কুলডাক’ ‘যোগিনী যোগ-হৃদয়’ ‘বুদ্ধকাপালিকযোগ’ ‘মঞ্জুবজ্র’ ‘নবাক্ষরালীডাক’ ‘বজ্রডাক’ ‘চোমক’ প্রভৃতি অনেক ভৈরব ও যোগিনীর পূজাপদ্ধতি আছে। বোধিসত্ত্ব ও যোগিনীগণের ধ্যানকে সাধন বলে। যে পুস্তকে অনেক ধ্যান লেখা আছে তাহাকে ‘সাধনমালা’ বলে। একখানি ‘সাধনমালা’য় দুই শত ছাপ্পান্নটি সাধন আছে। ‘বজ্রবারাহী’, ‘বজ্রযোগিনী’, ‘কুরুকুল্লা’, ‘মহাপ্রতিসরা’, ‘মহামায়ূরী’, ‘মহাসাহস্র প্রমর্দ্দিনী’ প্রভৃতি অনেক যোগিনীর ধ্যান ইহাতে আছে। এই-সকল সাধন লইয়া মূর্তি নির্মাণে বৌদ্ধকারিগরেরা এক সময়ে যথেষ্ট বাহাদুরি দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরবীর পূজা লইয়া ও তাঁহাদের মূর্তি লইয়া বৌদ্ধধর্ম চলিতে লাগিল, তখন আর অধঃপতনের বাকি কী রহিল?’
‘বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ‘গুহ্যপূজা’ আরম্ভ হইল। লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিব– কাহাকেও দেখিতে দিব না; এ পূজার অর্থ কী? অর্থ এই যে, সে-সকল দেবমূর্তি লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না। ঐ-সকল মূর্তির নাম– উহারা বলিত শম্বর। একে তো অশ্লীল মূর্তি– তাহাতে ভালো কারিগরের হাতের তৈয়ারি– তাহাতে অশ্লীলতার মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। সেই-সকল মূর্তি যখন বুদ্ধদের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল– তখন আর অধঃপাতের বাকি রহিল কী? সে-সকল উপাসনার প্রকার আরো অশ্লীল– সভ্যসমাজে বর্ণনা করা যায় না।’- (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড, বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত, পৃষ্ঠা- ৩৭৫-৭৬)
এখানে উল্লেখ্য, পালিতে কল্পকে কপ্প বলা হয়। কল্প হলো কাল পরিধি। মহাযান মতে কল্পের দুই প্রকারভেদ– শূন্য-কল্প এবং অশূন্য-কল্প বা বুদ্ধ-কল্প। শূন্য-কল্পে কোনো বুদ্ধ বর্তমান থাকেন না। অশূন্য বা বুদ্ধ-কল্পে এক বা একাধিক বুদ্ধ বর্তমান থাকেন। আবির্ভূত বুদ্ধের সংখ্যার হিসাব অনুযায়ী অশূন্য-কল্পের পাঁচ প্রকারভেদ কল্পনা করা হয়। সারকপ্পো’য় একজন বুদ্ধ আবির্ভূত হন। মণ্ডকপ্পো’য় দু’জন, বরকপ্পো’য় তিন জন, সারমণ্ডকপ্পো’য় চার জন এবং ভদ্দকপ্প– ভদ্রকল্প বা মহাভদ্রকল্পে পাঁচ জন বুদ্ধ আবির্ভূত হন।
বর্তমান চলতি কল্পকে ভদ্রকল্প ধরা হয়। এই কল্পে ককুসন্ধ, কোণাগমন, কস্সপ এবং গোতম– চার জন বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছেন। মেত্তেয় বা মৈত্রেয় বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন। বৌদ্ধধর্মে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। বিশেষ করে মহাযানে অগণিত বুদ্ধের অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে।
বর্তমান চলতি কল্পকে ভদ্রকল্প ধরা হয়। এই কল্পে ককুসন্ধ, কোণাগমন, কস্সপ এবং গোতম– চার জন বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছেন। মেত্তেয় বা মৈত্রেয় বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন। বৌদ্ধধর্মে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। বিশেষ করে মহাযানে অগণিত বুদ্ধের অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে।
শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য থেকে ‘অশ্লীলতার’ যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তাতে ধারণা করি, তার লক্ষ্যস্থল দু’টি– প্রথমত মূর্তির রূপ, দ্বিতীয়ত উপাসনা বা সাধন পদ্ধতি। সে যাই হোক, আলোচনাক্রমে বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট হবে আশা করি। তবে শাস্ত্রী মহাশয় যাকে ‘অধঃপাত’ বলেছেন তা আদৌ একপেশে বক্তব্য কিনা সে পর্যালোচনায় না গিয়েও বলা চলে যে, সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এক দীর্ঘ সাধন-পরম্পরার পেছনে কোন আচার-মার্গীয় দর্শন-তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তা না থাকলে তা টিকে থাকার পক্ষে অন্য কী কারণ থাকতে পারে? তন্ত্রে শাক্ত-প্রভাব অনস্বীকার্য, তাছাড়া এতদঞ্চলের সবকটি ধর্ম বা সাধনাচারও যে এই প্রভাবের বাইরে নেই তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। শক্তির ধারণার অনুপ্রবেশের ফলে যে আদিম তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ মহাযান বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয় তা এখন সর্বমহলেই স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের– মঞ্জুশ্রীমূলকল্প এবং গুহ্যসমাজ বা তথাগতগুহ্যক (পঞ্চম-ষষ্ট শতক)– কথা বলা যায়। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ভাষ্যে–
‘মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে মুদ্রা, মণ্ডল, মন্ত্র, ক্রিয়া ও চর্যা আলোচিত হয়েছে, গুহ্যসমাজে যোগ ও অনুত্তরযোগ। উভয় গ্রন্থেরই বক্তব্য মুদ্রা এবং মণ্ডল দেবী ও যোগমনস্কা নারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই নারীরা যে কোনও জাতি থেকেই আসতে পারে। সাধককে বুঝতে হবে যে সৃষ্টিকার্য নারী ও পুরুষ উভয় আদর্শের সংযোগের ফল। এই দুটি আদর্শ প্রজ্ঞা এবং উপায় অথবা শূন্যতা এবং করুণা। প্রজ্ঞা এবং উপায়ের মিলনই হচ্ছে যুগনদ্ধ বা সমরস, এবং নিজের ক্ষেত্রে যিনি তা ঘটাতে পারেন তিনিই পূর্ণজ্ঞান এবং পরম সুখ লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হন। এই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধত্ব। এই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা পেতে হলে পুরুষ ও নারীকে প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে যে তারা যথাক্রমে উপায় ও প্রজ্ঞার প্রকাশ। প্রজ্ঞা নারী আদর্শ, সেই হিসাবে ভগবতী। তিনি বজ্রকন্যা এবং যুবতী হিসাবেও কথিত। সাধনার জন্য যে ষোল বছরের সুন্দরী মেয়েকে গ্রহণ করা হবে সে প্রজ্ঞা। এ ছাড়া প্রজ্ঞা বলতে নারীর যৌনাঙ্গ বোঝায়। পুরুষ আদর্শ উপায়ের আর একটি নাম বজ্র, যার অর্থ পুরুষাঙ্গ। প্রজ্ঞা ও উপায়, নারী ও পুরুষের সংসর্গে অনন্ত পুলকের উপলব্ধি ঘটে, যাতে সকল মানসিক ক্রিয়া হারিয়ে যায়। চারদিকের জগৎ এক আনন্দময় সর্বব্যাপী একত্বের মধ্যে অবলুপ্ত হয়। এই হল মহাসুখ বা নির্বাণ, বোধিচিত্তের যথার্থ বিকাশ।’- (ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-১১৪)
নরনারীর দৈহিক মিলনের উপর বৌদ্ধতন্ত্রে এই যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এর মূলে সেই পুরাতন বিশ্বাসটিই কার্যকর, যা নেই দেহভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে। এই প্রাচীন বিশ্বাসই কায়সাধনের মূল কথা, যা হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় তন্ত্রেরই বিষয়বস্তু।
‘মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে মুদ্রা, মণ্ডল, মন্ত্র, ক্রিয়া ও চর্যা আলোচিত হয়েছে, গুহ্যসমাজে যোগ ও অনুত্তরযোগ। উভয় গ্রন্থেরই বক্তব্য মুদ্রা এবং মণ্ডল দেবী ও যোগমনস্কা নারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই নারীরা যে কোনও জাতি থেকেই আসতে পারে। সাধককে বুঝতে হবে যে সৃষ্টিকার্য নারী ও পুরুষ উভয় আদর্শের সংযোগের ফল। এই দুটি আদর্শ প্রজ্ঞা এবং উপায় অথবা শূন্যতা এবং করুণা। প্রজ্ঞা এবং উপায়ের মিলনই হচ্ছে যুগনদ্ধ বা সমরস, এবং নিজের ক্ষেত্রে যিনি তা ঘটাতে পারেন তিনিই পূর্ণজ্ঞান এবং পরম সুখ লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হন। এই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধত্ব। এই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা পেতে হলে পুরুষ ও নারীকে প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে যে তারা যথাক্রমে উপায় ও প্রজ্ঞার প্রকাশ। প্রজ্ঞা নারী আদর্শ, সেই হিসাবে ভগবতী। তিনি বজ্রকন্যা এবং যুবতী হিসাবেও কথিত। সাধনার জন্য যে ষোল বছরের সুন্দরী মেয়েকে গ্রহণ করা হবে সে প্রজ্ঞা। এ ছাড়া প্রজ্ঞা বলতে নারীর যৌনাঙ্গ বোঝায়। পুরুষ আদর্শ উপায়ের আর একটি নাম বজ্র, যার অর্থ পুরুষাঙ্গ। প্রজ্ঞা ও উপায়, নারী ও পুরুষের সংসর্গে অনন্ত পুলকের উপলব্ধি ঘটে, যাতে সকল মানসিক ক্রিয়া হারিয়ে যায়। চারদিকের জগৎ এক আনন্দময় সর্বব্যাপী একত্বের মধ্যে অবলুপ্ত হয়। এই হল মহাসুখ বা নির্বাণ, বোধিচিত্তের যথার্থ বিকাশ।’- (ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-১১৪)
নরনারীর দৈহিক মিলনের উপর বৌদ্ধতন্ত্রে এই যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এর মূলে সেই পুরাতন বিশ্বাসটিই কার্যকর, যা নেই দেহভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে। এই প্রাচীন বিশ্বাসই কায়সাধনের মূল কথা, যা হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় তন্ত্রেরই বিষয়বস্তু।
বৌদ্ধ-তন্ত্রে আদিবুদ্ধকে অবলম্বন করে যেভাবে সর্বেশ্বরী মহাদেবী আদিদেবীকে পাওয়া যায়, অন্যভাবে আবার সর্বেশ্বর ভগবান্ এবং সর্বেশ্বরী ভগবতীকে পাওয়া যায়। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন–
‘বৌদ্ধ-তন্ত্র মহাযান-বৌদ্ধধর্মেরই একটি বিশেষ পরিণতি। মহাযানী বৌদ্ধেরা যাঁহাদিগকে হীনযানী বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের যান বা মত এবং পথকে হীন বলিবার কারণ এই যে, তাঁহারা শূন্যতার উপরেই একমাত্র জোর দিয়াছেন এবং শূন্যতাজ্ঞানের সাধনার দ্বারা ব্যক্তিগত মুক্তি– অর্থাৎ অর্হত্ত্বলাভের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। মহাযানীরা সেখানে আনিলেন বিশ্ব-মুক্তির প্রশ্ন– সুতরাং মুক্তিদাত্রী শূন্যতার সহিত তাঁহারা যুক্ত করিলেন কুশলকর্মের প্রেরণাদায়ক মহাকরুণা। এই শূন্যতা হইল নেতিবাচক প্রজ্ঞা, আর করুণা হইল ইতিবাচক উপায় অর্থাৎ কুশল-কর্মপ্রেরণা। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ মহাযানের এই শূন্যতা-করুণার মিলনের উপরই সমস্ত সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তাঁহাদের সাধনা হইল বোধিসত্ত্ব হইয়া বোধিচিত্তলাভের সাধনা, আর বোধিচিত্তের তাঁহারা সংজ্ঞা নির্ণয় করিলেন, ‘শূন্যতা-করুণাভিন্নং বোধিচিত্তং তদুচ্যতে’– শূন্যতা এবং করুণার অভিন্নত্বই হইল বোধিচিত্ত। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ ধর্মমত ও সাধনার ক্ষেত্রে এই বোধিচিত্ত এবং শূন্যতা-করুণাকে নানাভাবে বহু দূরে টানিয়া লইতে লাগিলেন। বোধিচিত্ততত্ত্বই হইল তন্ত্রের যুগল– বা যামল-তত্ত্ব; ইহাই মূল সামরস্য, ইহাই মিথুনতত্ত্ব। শূন্যতা প্রজ্ঞারূপিণী ভগবতী– উপায় নিখিল ক্রিয়াত্মক ভগবান্ । এই ভগবান্-ভগবতী সামরস্য-রূপ মিথুনতত্ত্বই হইল অদ্বয় বোধিচিত্ত-তত্ত্ব। প্রজ্ঞারূপে শূন্যতা নিবৃত্তি-লক্ষণা, শূন্যতাই পরম-সংহৃতি, শূন্যতাই বিন্দু; কর্মচোদনারূপে উপায় প্রবৃত্তি-লক্ষণ, উপায় পরম-প্রকাশ, উপায়ই নাদতত্ত্ব। শূন্যতা-রূপিণী প্রজ্ঞানই নৈরাত্মা-রূপিণী নির্বাণ– উপায়ই সর্ববুদ্ধরূপ ভব। এই ভব এবং নির্বাণের সামরস্যই হইল যুগনদ্ধতত্ত্ব– সেই অদ্বয় যুগনদ্ধতত্ত্বই হইল পরম কাম্য।’
‘তন্ত্রশাস্ত্রের (তাহা হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ হোক অথবা হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণব হোক বা শৈব হোক বা শাক্ত হোক) মূল দার্শনিক দৃষ্টি হইল অদ্বয়বাদ। পরম সত্য অদ্বয়-স্বরূপ। কিন্তু এই অদ্বয়তত্ত্ব শুধু দ্বয়ের অভাব নয়– তাহা দ্বয়ের মিথুনতত্ত্ব, দ্বয়ের নিঃশেষ সমরসতা। যে দ্বয়ের সমরসতায় অদ্বয়সিদ্ধি হিন্দুতত্ত্ব-মতে সে দ্বয়তত্ত্বই হইল শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব– একই উৎসের যেন দুইটি ধারা; একটি জ্ঞানমাত্রতনু নিবৃত্তিমূলক– অপরটি ত্রিগুণাত্মিক প্রকাশাত্মিকা প্রবৃত্তিমূলা। দার্শনিক ভাষায় শিবত্ত্বই জ্ঞাতৃত্ব– শক্তিতত্ত্বই জ্ঞেয়ত্ব; শিবই পরম সঙ্কুচিত বিন্দু– শক্তিই পরম প্রসারিতা নাদরূপিণী।’
‘তন্ত্রের এই যে অদ্বয়তত্ত্ব এবং অদ্বয়ের মধ্যে অবিনাভাবে মিথুনীকৃত দ্বয়তত্ত্বের দ্বি-ধারা এই মৌলিক তত্ত্বটি বৌদ্ধ-তন্ত্রে প্রকাশ লাভ করিয়াছে বোধিচিত্ত এবং শূন্যতা-করুণাকে লইয়া। শুধু তফাত এই– বৌদ্ধ-তন্ত্রে ভগবতী-ই হইলেন নির্বাণরূপিণী বা বিন্দুরূপিণী প্রজ্ঞা আর সর্ববুদ্ধাত্মক ভগবান্ই হইলেন ক্রিয়াত্মক এবং প্রকাশাত্মক।’- (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৩৩-৩৪)
‘বৌদ্ধ-তন্ত্র মহাযান-বৌদ্ধধর্মেরই একটি বিশেষ পরিণতি। মহাযানী বৌদ্ধেরা যাঁহাদিগকে হীনযানী বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের যান বা মত এবং পথকে হীন বলিবার কারণ এই যে, তাঁহারা শূন্যতার উপরেই একমাত্র জোর দিয়াছেন এবং শূন্যতাজ্ঞানের সাধনার দ্বারা ব্যক্তিগত মুক্তি– অর্থাৎ অর্হত্ত্বলাভের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। মহাযানীরা সেখানে আনিলেন বিশ্ব-মুক্তির প্রশ্ন– সুতরাং মুক্তিদাত্রী শূন্যতার সহিত তাঁহারা যুক্ত করিলেন কুশলকর্মের প্রেরণাদায়ক মহাকরুণা। এই শূন্যতা হইল নেতিবাচক প্রজ্ঞা, আর করুণা হইল ইতিবাচক উপায় অর্থাৎ কুশল-কর্মপ্রেরণা। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ মহাযানের এই শূন্যতা-করুণার মিলনের উপরই সমস্ত সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তাঁহাদের সাধনা হইল বোধিসত্ত্ব হইয়া বোধিচিত্তলাভের সাধনা, আর বোধিচিত্তের তাঁহারা সংজ্ঞা নির্ণয় করিলেন, ‘শূন্যতা-করুণাভিন্নং বোধিচিত্তং তদুচ্যতে’– শূন্যতা এবং করুণার অভিন্নত্বই হইল বোধিচিত্ত। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ ধর্মমত ও সাধনার ক্ষেত্রে এই বোধিচিত্ত এবং শূন্যতা-করুণাকে নানাভাবে বহু দূরে টানিয়া লইতে লাগিলেন। বোধিচিত্ততত্ত্বই হইল তন্ত্রের যুগল– বা যামল-তত্ত্ব; ইহাই মূল সামরস্য, ইহাই মিথুনতত্ত্ব। শূন্যতা প্রজ্ঞারূপিণী ভগবতী– উপায় নিখিল ক্রিয়াত্মক ভগবান্ । এই ভগবান্-ভগবতী সামরস্য-রূপ মিথুনতত্ত্বই হইল অদ্বয় বোধিচিত্ত-তত্ত্ব। প্রজ্ঞারূপে শূন্যতা নিবৃত্তি-লক্ষণা, শূন্যতাই পরম-সংহৃতি, শূন্যতাই বিন্দু; কর্মচোদনারূপে উপায় প্রবৃত্তি-লক্ষণ, উপায় পরম-প্রকাশ, উপায়ই নাদতত্ত্ব। শূন্যতা-রূপিণী প্রজ্ঞানই নৈরাত্মা-রূপিণী নির্বাণ– উপায়ই সর্ববুদ্ধরূপ ভব। এই ভব এবং নির্বাণের সামরস্যই হইল যুগনদ্ধতত্ত্ব– সেই অদ্বয় যুগনদ্ধতত্ত্বই হইল পরম কাম্য।’
‘তন্ত্রশাস্ত্রের (তাহা হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ হোক অথবা হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণব হোক বা শৈব হোক বা শাক্ত হোক) মূল দার্শনিক দৃষ্টি হইল অদ্বয়বাদ। পরম সত্য অদ্বয়-স্বরূপ। কিন্তু এই অদ্বয়তত্ত্ব শুধু দ্বয়ের অভাব নয়– তাহা দ্বয়ের মিথুনতত্ত্ব, দ্বয়ের নিঃশেষ সমরসতা। যে দ্বয়ের সমরসতায় অদ্বয়সিদ্ধি হিন্দুতত্ত্ব-মতে সে দ্বয়তত্ত্বই হইল শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব– একই উৎসের যেন দুইটি ধারা; একটি জ্ঞানমাত্রতনু নিবৃত্তিমূলক– অপরটি ত্রিগুণাত্মিক প্রকাশাত্মিকা প্রবৃত্তিমূলা। দার্শনিক ভাষায় শিবত্ত্বই জ্ঞাতৃত্ব– শক্তিতত্ত্বই জ্ঞেয়ত্ব; শিবই পরম সঙ্কুচিত বিন্দু– শক্তিই পরম প্রসারিতা নাদরূপিণী।’
‘তন্ত্রের এই যে অদ্বয়তত্ত্ব এবং অদ্বয়ের মধ্যে অবিনাভাবে মিথুনীকৃত দ্বয়তত্ত্বের দ্বি-ধারা এই মৌলিক তত্ত্বটি বৌদ্ধ-তন্ত্রে প্রকাশ লাভ করিয়াছে বোধিচিত্ত এবং শূন্যতা-করুণাকে লইয়া। শুধু তফাত এই– বৌদ্ধ-তন্ত্রে ভগবতী-ই হইলেন নির্বাণরূপিণী বা বিন্দুরূপিণী প্রজ্ঞা আর সর্ববুদ্ধাত্মক ভগবান্ই হইলেন ক্রিয়াত্মক এবং প্রকাশাত্মক।’- (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৩৩-৩৪)
এভাবেই দেখা যায়, হিন্দু-তন্ত্রে যেমন শিব-শক্তিকে অবলম্বন করে মিথুন-সাধনা গড়ে উঠেছে, তেমনই বৌদ্ধ-তন্ত্রেও করুণারূপী ভগবান্ ও প্রজ্ঞারূপিণী দেবী ভগবতীকে নিয়ে তান্ত্রিক মিথুন-সাধনা গড়ে উঠেছে। যোগ-সাধনায় এই ভগবতী এবং ভগবান্ ইড়া-পিঙ্গলা, গঙ্গা-যমুনা, বাম-দক্ষিণের রূপ গ্রহণ করেছেন। এই অদ্বয়তত্ত্বই অর্ধনারীশ্বর তত্ত্ব– বামে দেবী ভগবতী, দক্ষিণে ভগবান্, দুই মিলে এক। একে দুই– দুইয়ে এক; হিন্দু-তন্ত্রেও এই কথা– বৌদ্ধ-তন্ত্রেও সেই একই কথা।
তন্ত্রসাধনার এই ভগবান্ এবং ভগবতী পূর্বে বর্ণিত আদিবুদ্ধ ও আদিদেবীর সাথে মিলে-মিশে গেলেন। ফলে– ‘বৌদ্ধ-তন্ত্রেও আমরা এক সর্বেশ্বর ভগবান্ এবং সর্বেশ্বরী ভগবতীর কথা প্রচুরভাবে দেখিতে পাই। এই সর্বেশ্বর দেবতা সাধারণতঃ শ্রীহেবজ্র, শ্রীহেরুক, শ্রীবজ্রধর, শ্রীবজ্রেশ্বর, শ্রীবজ্রসত্ত্ব, মহাসত্ত্ব, শ্রীমন্মহাসুখ, শ্রীচণ্ডরোষণ প্রভৃতি রূপে দেখা দিয়াছেন, সর্বেশ্বরী দেবী দেখা দিয়াছেন তাঁহারই অঙ্কবিহারিণীরূপে অথবা মিথুনাবস্থায় তাঁহার সহিত যুক্তরূপে। তিনি কোথাও বজ্রধাত্বীশ্বরী, বজ্রবারাহী, কোথাও ভগবতীপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতা অথবা দেবী নৈরাত্মা। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু মহেশ্বর-মহেশ্বরী এবং বৌদ্ধ সর্বেশ্বর-সর্বেশ্বরী বহু স্থানে মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছেন।’- (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৩৪)
তন্ত্রসাধনার এই ভগবান্ এবং ভগবতী পূর্বে বর্ণিত আদিবুদ্ধ ও আদিদেবীর সাথে মিলে-মিশে গেলেন। ফলে– ‘বৌদ্ধ-তন্ত্রেও আমরা এক সর্বেশ্বর ভগবান্ এবং সর্বেশ্বরী ভগবতীর কথা প্রচুরভাবে দেখিতে পাই। এই সর্বেশ্বর দেবতা সাধারণতঃ শ্রীহেবজ্র, শ্রীহেরুক, শ্রীবজ্রধর, শ্রীবজ্রেশ্বর, শ্রীবজ্রসত্ত্ব, মহাসত্ত্ব, শ্রীমন্মহাসুখ, শ্রীচণ্ডরোষণ প্রভৃতি রূপে দেখা দিয়াছেন, সর্বেশ্বরী দেবী দেখা দিয়াছেন তাঁহারই অঙ্কবিহারিণীরূপে অথবা মিথুনাবস্থায় তাঁহার সহিত যুক্তরূপে। তিনি কোথাও বজ্রধাত্বীশ্বরী, বজ্রবারাহী, কোথাও ভগবতীপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতা অথবা দেবী নৈরাত্মা। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু মহেশ্বর-মহেশ্বরী এবং বৌদ্ধ সর্বেশ্বর-সর্বেশ্বরী বহু স্থানে মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছেন।’- (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৩৪)
তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যগণ
বলার অপেক্ষা রাখে না, বৌদ্ধধর্মের আওতায় একটি বিশেষ ধরনের তান্ত্রিক জীবনচর্যার পুনরুজ্জীবন হয় যার মূল আদর্শ সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতালাভ। এই আদর্শের ধারকেরা ছিলেন জাতিপ্রথা বিরোধী, অনেকেই ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ, এবং এই আদর্শ কবীর-পন্থা, নাথ-পন্থা প্রভৃতি পরবর্তী লৌকিক ধর্মগুলিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে ঋদ্ধি বা অভিজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রেও অষ্টসিদ্ধির উল্লেখ আছে, যেমন– অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, প্রাপ্তি, বশিত্ব, ঈশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব।
শাক্ত তান্ত্রিক ললিতাসহস্রনামে তিন রকম সাধনার উল্লেখ আছে– দিব্য, মানব এবং সিদ্ধ। এই সাধন পরম্পরা অনুযায়ীই হয়তো বিভিন্ন তান্ত্রিক গ্রন্থে সিদ্ধকুল, সিদ্ধামৃত ইত্যাদি সম্প্রদায় এবং সিদ্ধদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ঐতিহ্য অনুযায়ী সিদ্ধদের সংখ্যা চুরাশিজন যাঁরা যোগের দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। জ্যোতিরীশ্বর বিরচিত বর্ণরত্নাকরে চুরাশিজন সিদ্ধের উল্লেখ আছে। তিব্বতী তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে এঁদের জীবনী দেওয়া আছে বলে জানা যায়। এই সিদ্ধাচার্যরা হলেন–
‘লুহি, লীলা, বিরু, ডোম্বী, শবরী, সরহ, কঙ্কালী, মীন, গোরক্ষ, চৌরঙ্গী, বীণা, শান্তি, তান্তি, চর্মরী, খড়গ, নাগার্জুন, কাণ্হ, কাণরী, থগন, নাড়, শালি, তিলো, ছত্র, ভদ্র, দ্বিখণ্ডী, অযোগী, কড়, ধোবি, কংকন, কম্বল, তেঙ্কি, ভাদে, তদ্ধি, কুক্কুরী, চুজ্বী, ধর্ম, মহী, অচিন্ত্য, বভহি, নলিন, ভুসুকু, ইন্দ্রভূতি, মেঘ, কুঠারী, কর্মার, জালন্ধী, রাহুল, গর্ভরী, ধকরী, মেদিনী, পঙ্কজ, ঘণ্টা, যোগী, চেলুক, বাগুরী, লুঞ্চক, নির্গুণ, জয়ানন্দ, চর্যটি, চম্পক, বিষাণ, ভলি বা তেলি, কুমরী, চার্পটি, মণিভদ্রা, মেখলা, মংখালা, কলকল, কন্থডি, দৌধি, উধলি, কপাল, কিল, পুষ্কর, সর্বভক্ষ্য, নাগবোধি, দারিক, পুত্তলি, পনহ, কোকিলা, অনঙ্গ, লক্ষ্মীঙ্করা, সামুদ্র ও ভলি।’
শাক্ত তান্ত্রিক ললিতাসহস্রনামে তিন রকম সাধনার উল্লেখ আছে– দিব্য, মানব এবং সিদ্ধ। এই সাধন পরম্পরা অনুযায়ীই হয়তো বিভিন্ন তান্ত্রিক গ্রন্থে সিদ্ধকুল, সিদ্ধামৃত ইত্যাদি সম্প্রদায় এবং সিদ্ধদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ঐতিহ্য অনুযায়ী সিদ্ধদের সংখ্যা চুরাশিজন যাঁরা যোগের দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। জ্যোতিরীশ্বর বিরচিত বর্ণরত্নাকরে চুরাশিজন সিদ্ধের উল্লেখ আছে। তিব্বতী তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে এঁদের জীবনী দেওয়া আছে বলে জানা যায়। এই সিদ্ধাচার্যরা হলেন–
‘লুহি, লীলা, বিরু, ডোম্বী, শবরী, সরহ, কঙ্কালী, মীন, গোরক্ষ, চৌরঙ্গী, বীণা, শান্তি, তান্তি, চর্মরী, খড়গ, নাগার্জুন, কাণ্হ, কাণরী, থগন, নাড়, শালি, তিলো, ছত্র, ভদ্র, দ্বিখণ্ডী, অযোগী, কড়, ধোবি, কংকন, কম্বল, তেঙ্কি, ভাদে, তদ্ধি, কুক্কুরী, চুজ্বী, ধর্ম, মহী, অচিন্ত্য, বভহি, নলিন, ভুসুকু, ইন্দ্রভূতি, মেঘ, কুঠারী, কর্মার, জালন্ধী, রাহুল, গর্ভরী, ধকরী, মেদিনী, পঙ্কজ, ঘণ্টা, যোগী, চেলুক, বাগুরী, লুঞ্চক, নির্গুণ, জয়ানন্দ, চর্যটি, চম্পক, বিষাণ, ভলি বা তেলি, কুমরী, চার্পটি, মণিভদ্রা, মেখলা, মংখালা, কলকল, কন্থডি, দৌধি, উধলি, কপাল, কিল, পুষ্কর, সর্বভক্ষ্য, নাগবোধি, দারিক, পুত্তলি, পনহ, কোকিলা, অনঙ্গ, লক্ষ্মীঙ্করা, সামুদ্র ও ভলি।’
লক্ষ্যণীয় যে, ‘এঁদের অনেকেই নীচ জাতীয়, নাম থেকেই বোঝা যায় কেউ ডোম, কেউ শবর, কেউ ধোপা, কেউ তেলী, কেউ তাঁতী। এদের উপাধি পা অর্থাৎ বাবা, অর্থাৎ ডোম বাবা, কুড়ুল বাবা, তাঁতী বাবা। এই তালিকায় কোন কোন বৌদ্ধ আচার্য আছেন। যেমন নাগার্জুন, কাণরী বা আর্যদেব প্রভৃতি। নাথধর্মের প্রবক্তারা যেমন মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, জালন্ধরী, প্রভৃতিও এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন। চর্যাগীতিকোশ বা চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে নিম্নলিখিত সিদ্ধদের উল্লেখ পাওয়া যায় : কাণরী, ভাদে, ভুসুকু, দারিক, ধর্ম, ডোম্বী, গুণ্ডরী, জয়ানন্দ, জালন্ধর, কম্বল, কুক্কুরী, কঙ্কন, লুহি, মহী, শান্তি, শবর, তান্তি, তেণ্টনা, বীণা, কাণ্হ ও সরহ। এই সকল সিদ্ধদের খবর ও তাঁদের কারো কারো রচনার অনুবাদ তিব্বতী তাঞ্জুরগ্রন্থমালায় বর্তমান। যাঁদের বিষয় সেখানে উল্লিখিত হয়েছে তাঁরা হলেন ইন্দ্রভূতি, কেরলী, অজ মহাসুখ, সরহ, মহাশবর, নারো, আর্যদেব, কৃষ্ণ (কাণ্হ), বিরু, কর্ম, কিলো, শান্তিদেব, লুহি, থগন, ভাদে (ভাঙদে), ধর্ম, মহী, শবরী, কম্বল, চাতে, কঙ্কালী, মীন, অচিন্দ, গোরক্ষ, চোরংঘি (চৌরঙ্গী), বীণা, তান্তি, শিয়ালী, আজাকি, পঙ্কজ, ডোম্বী, কুক্কুরী, কর্মরী, চার্পটি, জালন্ধরী, কন্থরি, লুঞ্চক, গর্ভরি প্রভৃতি। এই সকল সিদ্ধদের অধিকাংশই দশম ও একাদশ শতকের মানুষ।’- (ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)
এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ে বলেন– ‘এই সব মহাযানী-কালচক্রযানী-মন্ত্রযানী-বজ্রযানী-সহজযানী আচার্যদের দেশ ও কাল সম্বন্ধে এবং ইঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। ইঁহাদের মধ্যে যাহারা দেশ ছাড়িয়া দূরে অন্যত্র নিজেদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়াছিলেন তাঁহাদের সমস্ত তথ্যই প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকায় অনেকের জন্ম ও কর্মভূমি উল্লেখিত আছে, কিন্তু অনেকের নাইও। কিন্তু যাঁহাদের আছে তাঁহাদেরও জন্ম-কর্মভূমির স্থান-নাম সর্বদা এবং সর্বত্র শনাক্ত করা সহজ নয়; এ-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যাঁহাদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ বিদ্যমান এবং যে-সব স্থান-নামের শনাক্তকরণ সুনির্ধারিত, তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিঃসংশয়ে বলা চলে, এই সব আচার্যরা অধিকাংশই ছিলেন বাঙলা দেশের অধিবাসী, স্বল্পসংখ্যক কয়েকজনের জন্মভূমি ছিল কামরূপ, ওড্রদেশ, বিহার এবং কাশ্মীর। এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই ইহাও বলা চলে যে, এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের লীলাভূমি ছিল প্রাচ্য-ভারত, বিশেষ ভাবে বাঙলা দেশ। যে-সব মহাবিহারে বসিয়া বৌদ্ধ আচার্যরা অগণিত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের ভিতর নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীল ছাড়া অন্য প্রত্যেকটি মহাবিহারই ছিল বাঙলা দেশে। সমসাময়িক বাঙালীল শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যান্য সুবৃহৎ কেন্দ্র ছিল জগদ্দল, সোমপুরী, পাণ্ডুভূমি, ত্রৈকুটক, বিক্রমপুরী, দেবীকোট, সন্নগর, ফুল্লহরি, পণ্ডিত, পট্টিকেরক প্রভৃতি বিহারে; এ-সংবাদও পাইতেছি তিব্বতী বৌদ্ধ গ্রন্থতালিকা হইতেই। এই পর্বের নালন্দা, ওদন্তপুরী এবং বিক্রমশীল মহাবিহারও বাঙালী ও বাঙলা দেশের রাষ্ট্রীয় ও সংস্কৃতি সীমার অন্তর্গত। বিক্রমশীল বিহারের প্রতিষ্ঠাতাই তো ছিলেন পাল-রাজ ধর্মপাল স্বয়ং এবং ওদন্তপুরী ও নালন্দায় এ-পর্বের বিদ্যার্থী ও আচার্যদের অধিকাংশই বাঙালী। নালন্দা ও ওদন্তপুরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষকও বাঙলার পাল-বংশ। এই সব বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার্যদের স্থিতিকাল সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সন-তারিখ নির্ণয় কঠিন হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। কোনও কোনও গ্রন্থ-রচনার তারিখ উল্লিখিত আছে; সমসাময়িক বা পূর্বতন আচার্যদের ও রাজা-রাজবংশের উল্লেখের এবং গুরুপরম্পরানির্ধারণের সাহায্যে মোটামুটি ইঁহাদের কালনির্ণয়ের একাধিক চেষ্টা হইয়াছে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা চলে, উল্লিখিত বৌদ্ধ আচার্যদের স্থিতিকাল এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থাদির রচনাকাল মোটামুটি অষ্টম শতক হইতে একাদশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশেষভাবে পাল-পর্বই যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের উদ্ভব, প্রসার ও প্রভাব কাল তাহা তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকা, তারনাথের ইতিহাস এবং সুম্পার পাগ্-সাম্-জোন্-জাঙ্-গ্রন্থের সাক্ষ্যেও সুপ্রমাণিত।’
‘উল্লিখিত বৌদ্ধ আচার্যরা যে শুধু অবলোকিতেশ্বর, তারা, মঞ্জুশ্রী, লোকনাথ, হেরুক, হেবজ্র, প্রভৃতি বিচিত্র দেবদেবীর সাধনমন্ত্র, স্তোত্র, সংগীতি, মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, যোগ, ধারণী, সমাধি প্রভৃতি লইয়াই গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন তাহাই নয়, যোগ ও দর্শন হেতুবিদ্যা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও শব্দবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই, এই সব গ্রন্থের মধ্যেই সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-দীক্ষাও প্রতিফলিত।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, পৃষ্ঠা-৫৮৮)
‘উল্লিখিত বৌদ্ধ আচার্যরা যে শুধু অবলোকিতেশ্বর, তারা, মঞ্জুশ্রী, লোকনাথ, হেরুক, হেবজ্র, প্রভৃতি বিচিত্র দেবদেবীর সাধনমন্ত্র, স্তোত্র, সংগীতি, মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, যোগ, ধারণী, সমাধি প্রভৃতি লইয়াই গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন তাহাই নয়, যোগ ও দর্শন হেতুবিদ্যা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও শব্দবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই, এই সব গ্রন্থের মধ্যেই সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-দীক্ষাও প্রতিফলিত।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, পৃষ্ঠা-৫৮৮)
সিদ্ধরা মূলত গুরুবাদী। গুরুই শিষ্যকে সাধনায় দীক্ষিত করেন তার গ্রহণশক্তি অনুযায়ী। এই হিসেবে সাধনার পাঁচটি কুল বর্তমান– ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী, এবং ব্রাহ্মণী– যেগুলি যথাক্রমে পাঁচটি আকারের প্রতীক। সিদ্ধিলাভের সাধনা মূলত কায়-সাধনা। এই মত অনুযায়ী দেহে বত্রিশটি নাড়ী বর্তমান যেগুলির মধ্য দিয়ে শক্তি প্রবাহিত হয়, যার মূলকেন্দ্র নাভির নিম্নদেশ। শক্তির সর্বোচ্চ আধার মহাসুখস্থান নামে কল্পিত। ওই বত্রিশটি নাড়ীর নানারকম নাম আছে– ললনা, রমণা, অবধূতী, প্রবণা, কৃষ্ণরূপিণী, সামান্যা, পাবকী, সুমনা, কামিনী প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে তিনটি– ললনা, রমণা ও অবধূতী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তন্ত্রে সেগুলিকে বলা হয়েছে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। সর্বোচ্চ স্থানটি যা মহাসুখস্থান নামে পরিচিত একটি সহস্রদল পদ্মরূপে কল্পিত। কয়েকটি বিরতিস্থান অতিক্রম করে শক্তি সেখানে পৌঁছায়। এই বিরতিস্থানগুলি তান্ত্রিক পীঠস্থানসমূহের নামে পরিচিত, যেমন– উড্ডীয়ান, জালন্ধর, পূর্ণগিরি, কামরূপ। সাধকের লক্ষ্য সহজের উপলব্ধি। সহজ সব কিছুর উৎস, যা চিরন্তন সুখ ও অনির্বচনীয় আনন্দের আকর, যেখানে সকল অনুভূতিকে মিশিয়ে দিলেই চরম অদ্বয়বোধের উপলব্ধি ঘটে। সাধক তখন নিজেকে অন্য কিছুর থেকে পৃথক করে দেখেন না। অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথের ভাষ্যে–
‘মুক্তির পর আত্মার মুক্তি নয়, মুক্তি ইহজীবনেই, তাই সিদ্ধিপন্থার সাধকরা জীবন্মুক্তি শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। কায়সাধনের দ্বারা অমরত্ব লাভ করা যায়। জীবনদায়িকা শুক্র বা বীর্য বোধিচিত্তরূপে কল্পিত, যাকে পরাবৃত্তি বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিপরীত প্রবৃত্তি অনুসরণে ঊর্ধ্বমুখী করতে পারলে অমরত্বের পথ সুগম হয়। বোধিচিত্ত চর্চা রসায়নের সঙ্গেও সম্পর্কিত এবং সেই কারণেই রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। দেহের মধ্যে যে অস্থির রসস্রোত বইছে তাকে কঠিন করা, অর্থাৎ বজ্রে পরিণত করার দরকার, তবেই সকল বৃত্তির স্থিরতা আসবে। এই উদ্দেশ্যে পারদঘটিত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন, কেননা সাধারণ মরণশীল দেহকে দিব্য দেহে পরিণত করার দরকার। তত্ত্বের দিক থেকে বলা হয় মানবদেহ অশুদ্ধ মায়া বা অশুদ্ধ বস্তু দিয়ে গঠিত, কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা সেগুলিকে শুদ্ধ মায়া বা শুদ্ধ বস্তুতে পরিণত করতে হবে। দেহের তিন রকম রূপান্তর হতে পারে মন্ত্র-তনু, প্রবণ বা বৈন্দব তনু এবং দিব্য তনু। পাকাপাকিভাবে জীবন্মুক্তি ঘটলে সেই অবস্থাকে পরমুক্তি বলা হয়।’- (ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস)
‘মুক্তির পর আত্মার মুক্তি নয়, মুক্তি ইহজীবনেই, তাই সিদ্ধিপন্থার সাধকরা জীবন্মুক্তি শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। কায়সাধনের দ্বারা অমরত্ব লাভ করা যায়। জীবনদায়িকা শুক্র বা বীর্য বোধিচিত্তরূপে কল্পিত, যাকে পরাবৃত্তি বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিপরীত প্রবৃত্তি অনুসরণে ঊর্ধ্বমুখী করতে পারলে অমরত্বের পথ সুগম হয়। বোধিচিত্ত চর্চা রসায়নের সঙ্গেও সম্পর্কিত এবং সেই কারণেই রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। দেহের মধ্যে যে অস্থির রসস্রোত বইছে তাকে কঠিন করা, অর্থাৎ বজ্রে পরিণত করার দরকার, তবেই সকল বৃত্তির স্থিরতা আসবে। এই উদ্দেশ্যে পারদঘটিত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন, কেননা সাধারণ মরণশীল দেহকে দিব্য দেহে পরিণত করার দরকার। তত্ত্বের দিক থেকে বলা হয় মানবদেহ অশুদ্ধ মায়া বা অশুদ্ধ বস্তু দিয়ে গঠিত, কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা সেগুলিকে শুদ্ধ মায়া বা শুদ্ধ বস্তুতে পরিণত করতে হবে। দেহের তিন রকম রূপান্তর হতে পারে মন্ত্র-তনু, প্রবণ বা বৈন্দব তনু এবং দিব্য তনু। পাকাপাকিভাবে জীবন্মুক্তি ঘটলে সেই অবস্থাকে পরমুক্তি বলা হয়।’- (ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস)
সিদ্ধগণসহ কায়সাধনকারী সকল সম্প্রদায় এই তান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী যে দেহই হচ্ছে বস্তুজগতের সংক্ষিপ্ত রূপ। পর্বত, সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য, নদী, বস্তুজগতের সবকিছুই দেহের মধ্যে অবস্থিত। হঠযোগের দ্বারা দেহ ও মনের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব অর্জন করা যায়। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, শিব ও শক্তি দেহে বাস করেন, শিব থাকেন সহস্রারে, শক্তি থাকেন মূলাধারে। দেহের দক্ষিণার্ধ শিব, বামার্ধ শক্তি। ডান দিকের নাড়ী পিঙ্গলা দিয়ে শিবের আদর্শস্বরূপ অপান বায়ু প্রবাহিত হয়, বামদিকের নাড়ী ইড়া দিয়ে শক্তির আদর্শরূপ প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়। সাধক যৌগিক পদ্ধতির সাহায্যে এই দুই প্রবাহকে মধ্য অঞ্চলে বা সুষুম্না কাণ্ডে নিয়ে আসবেন এবং তাহলে দুই ধারার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সাম্যাবস্থা ঘটবে। পুরুষ শিবের প্রতীক, নারী শক্তির, তাদের যৌগিক মিলন চরম অদ্বয়বোধজনিত মহাসুখের কারণ হবে। এটাই সিদ্ধপন্থী সাধকের লক্ষ্য।
বৌদ্ধ-তন্ত্রের ক্রমবিকাশ
মহাযান সাহিত্যে ধারণী বা রক্ষামূলক মন্ত্রশাস্ত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণে,–
‘অল্পাক্ষরাপ্রজ্ঞাপারমিতার মতো রচনা এই মন্ত্রশাস্ত্রের প্রাথমিক রূপ। ধারণী নামক বিশেষ পরিভাষাটি গোড়ার দিকে অবশ্য খুবই ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হত। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রসমূহ ছাড়াও অন্যান্য মহাযান সূত্রও কখনও কখনও ধারণী বলে উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে ধারণী বলতে বিশেষ করে দেবীদের উদ্দেশে নানাপ্রকার সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য ব্যবহৃত মন্ত্রাবলীকে বুঝিয়েছে। এই রকম একটি ধারণীর সঙ্কলনের নাম পঞ্চরক্ষা যার প্রথমটি পাপ, রোগ এবং অপরাপর অঘটনের প্রতিরোধ কল্পে মহাপ্রতিসরার উদ্দেশে, দ্বিতীয়টি ভূতপ্রেত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহাসহস্রপ্রমর্দিনীর উদ্দেশে, তৃতীয়টি সর্পবিষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহামায়ূরীর উদ্দেশে, চতুর্থটি প্রতিকূল গ্রহশান্তি, বন্য পশু ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মহাসীতবতীর উদ্দেশে এবং পঞ্চমটি রোগশান্তির জন্য মহামন্ত্রানুসারিণীর উদ্দেশে রচিত। তিব্বতী তাঞ্জুর ও কাঞ্জুর গ্রন্থমালায়, চৈনিক ত্রিপিটকে এবং মহাযানের উপর রচিত নানা গ্রন্থে এই রকম অসংখ্য ধারণীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই মন্ত্রশাস্ত্র মন্ত্র নয় বা মন্ত্রযানের পথিকৃৎ যা অবলম্বনে বজ্রযান প্রমুখ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম গড়ে ওঠে। বৌদ্ধ তন্ত্র চার প্রকার– ক্রিয়াতন্ত্র যেখানে মন্দির নির্মাণ, মূর্তিস্থাপন ও নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, চর্যাতন্ত্র যা সাধনার ব্যবহারিক দিক্গুলিকে প্রদর্শন করায়, যোগতন্ত্র যা যৌগিক নানা প্রক্রিয়া শিক্ষা দেয় এবং অনুত্তরযোগতন্ত্র যা উচ্চতর অতীন্দ্রিয়বাদের কথা বলে।’
‘বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানমূলক সাহিত্যে সাধনা ও সিদ্ধি, মুদ্রা ও ধ্যান, পূজা ও দেবদেবীদের মূর্তিকল্পনা, বিভিন্ন ধরনের যোগ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন লেখক রচিত এই ধরনের সাধনশাস্ত্রের একটি বিশেষ সঙ্কলন সাধনমালা নামে পরিচিত। একাদশ শতকে সঙ্কলিত এই গ্রন্থে ৩১২টি সাধন আছে, যেগুলির মধ্যে কিছু অশুদ্ধ সংস্কৃত গদ্যে রচিত এবং কিছু ছন্দে রচিত। কয়েকটি সাধন নাগার্জুনের নামে প্রচলিত যিনি অবশ্য মাধ্যমিক দর্শনের প্রবক্তা নাগার্জুনের থেকে ভিন্ন। কথিত আছে তিনি ভোটদেশ বা তিব্বত থেকে কিছু সাধন নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি তান্ত্রিক গ্রন্থের উল্লেখ তিব্বতী তাঞ্জুর সংগ্রহে পাওয়া যায়। অপর একজন তান্ত্রিক আচার্য ইন্দ্রভূতি গৌতম সপ্তম-অষ্টম শতকে উড্ডিয়ানে রাজত্ব করতেন যিনি তিব্বতীয় লামাবর্গের প্রবক্তা পদ্মসম্ভবের পিতা ছিলেন। তাঁর রচিত জ্ঞানসিদ্ধি একটি বিশিষ্ট বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ। ইন্দ্রভূতির সমকালীন ছিলেন পদ্মবজ্র যাঁর সন্ধ্যাভাষায় রচিত গুহ্যসিদ্ধি গ্রন্থে বজ্রযান বৌদ্ধমতের তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইন্দ্রভূতির ভগিনী ছিলেন লক্ষ্মীঙ্করা যাঁর অদ্বয়সিদ্ধি গ্রন্থে পরবর্তীকালের সহজযানের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। আরও একজন তান্ত্রিক লেখিকা ছিলেন সহজযোগিনী চিন্তা যিনি অষ্টম শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।’- (ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-১০২-১০৩)
‘অল্পাক্ষরাপ্রজ্ঞাপারমিতার মতো রচনা এই মন্ত্রশাস্ত্রের প্রাথমিক রূপ। ধারণী নামক বিশেষ পরিভাষাটি গোড়ার দিকে অবশ্য খুবই ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হত। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রসমূহ ছাড়াও অন্যান্য মহাযান সূত্রও কখনও কখনও ধারণী বলে উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে ধারণী বলতে বিশেষ করে দেবীদের উদ্দেশে নানাপ্রকার সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য ব্যবহৃত মন্ত্রাবলীকে বুঝিয়েছে। এই রকম একটি ধারণীর সঙ্কলনের নাম পঞ্চরক্ষা যার প্রথমটি পাপ, রোগ এবং অপরাপর অঘটনের প্রতিরোধ কল্পে মহাপ্রতিসরার উদ্দেশে, দ্বিতীয়টি ভূতপ্রেত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহাসহস্রপ্রমর্দিনীর উদ্দেশে, তৃতীয়টি সর্পবিষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহামায়ূরীর উদ্দেশে, চতুর্থটি প্রতিকূল গ্রহশান্তি, বন্য পশু ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মহাসীতবতীর উদ্দেশে এবং পঞ্চমটি রোগশান্তির জন্য মহামন্ত্রানুসারিণীর উদ্দেশে রচিত। তিব্বতী তাঞ্জুর ও কাঞ্জুর গ্রন্থমালায়, চৈনিক ত্রিপিটকে এবং মহাযানের উপর রচিত নানা গ্রন্থে এই রকম অসংখ্য ধারণীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই মন্ত্রশাস্ত্র মন্ত্র নয় বা মন্ত্রযানের পথিকৃৎ যা অবলম্বনে বজ্রযান প্রমুখ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম গড়ে ওঠে। বৌদ্ধ তন্ত্র চার প্রকার– ক্রিয়াতন্ত্র যেখানে মন্দির নির্মাণ, মূর্তিস্থাপন ও নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, চর্যাতন্ত্র যা সাধনার ব্যবহারিক দিক্গুলিকে প্রদর্শন করায়, যোগতন্ত্র যা যৌগিক নানা প্রক্রিয়া শিক্ষা দেয় এবং অনুত্তরযোগতন্ত্র যা উচ্চতর অতীন্দ্রিয়বাদের কথা বলে।’
‘বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানমূলক সাহিত্যে সাধনা ও সিদ্ধি, মুদ্রা ও ধ্যান, পূজা ও দেবদেবীদের মূর্তিকল্পনা, বিভিন্ন ধরনের যোগ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন লেখক রচিত এই ধরনের সাধনশাস্ত্রের একটি বিশেষ সঙ্কলন সাধনমালা নামে পরিচিত। একাদশ শতকে সঙ্কলিত এই গ্রন্থে ৩১২টি সাধন আছে, যেগুলির মধ্যে কিছু অশুদ্ধ সংস্কৃত গদ্যে রচিত এবং কিছু ছন্দে রচিত। কয়েকটি সাধন নাগার্জুনের নামে প্রচলিত যিনি অবশ্য মাধ্যমিক দর্শনের প্রবক্তা নাগার্জুনের থেকে ভিন্ন। কথিত আছে তিনি ভোটদেশ বা তিব্বত থেকে কিছু সাধন নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি তান্ত্রিক গ্রন্থের উল্লেখ তিব্বতী তাঞ্জুর সংগ্রহে পাওয়া যায়। অপর একজন তান্ত্রিক আচার্য ইন্দ্রভূতি গৌতম সপ্তম-অষ্টম শতকে উড্ডিয়ানে রাজত্ব করতেন যিনি তিব্বতীয় লামাবর্গের প্রবক্তা পদ্মসম্ভবের পিতা ছিলেন। তাঁর রচিত জ্ঞানসিদ্ধি একটি বিশিষ্ট বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ। ইন্দ্রভূতির সমকালীন ছিলেন পদ্মবজ্র যাঁর সন্ধ্যাভাষায় রচিত গুহ্যসিদ্ধি গ্রন্থে বজ্রযান বৌদ্ধমতের তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইন্দ্রভূতির ভগিনী ছিলেন লক্ষ্মীঙ্করা যাঁর অদ্বয়সিদ্ধি গ্রন্থে পরবর্তীকালের সহজযানের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। আরও একজন তান্ত্রিক লেখিকা ছিলেন সহজযোগিনী চিন্তা যিনি অষ্টম শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।’- (ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-১০২-১০৩)
এখানে উল্লেখ্য, তিব্বতে ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের অনুবাদের একটি বিপুল সংগ্রহ বর্তমান। এই সংগ্রহ দুই ভাগে বিভক্ত– কাঞ্জুর ও তাঞ্জুর। প্রথম সংগ্রহ অর্থাৎ কাঞ্জুরে আছে ১১০৮টি গ্রন্থ, বিষয়বস্তু অনুযায়ী যেগুলিকে বিনয়, প্রজ্ঞাপারমিতা, বুদ্ধাবতংসক, রত্নকূট, সূত্র, নির্বাণ ও তন্ত্র এই সাত ভাগে ভাগ করা হয়। আর দ্বিতীয় সংগ্রহ অর্থাৎ তাঞ্জুরে আছে ৩৪৫৮টি গ্রন্থ, বিষয়বস্তু অনুযায়ী যেগুলি তন্ত্র ও সূত্র এই দুই ভাগে বিভক্ত। একাদশ শতকে বিক্রমশিলা মহাবিহারের আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সেখানে তিনি বৌদ্ধধর্মকে নতুনভাবে প্রচার করেন।
বস্তুত মহাযান মতের দর্শনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহারিক সাধন পরম্পরার বিবর্তনের মধ্য দিয়েই যে বৌদ্ধতন্ত্রের বিকাশ এ বিষয়ে বোধকরি কারও কোন দ্বিমত নেই। এ প্রেক্ষিতে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ভাষ্য হলো–
‘আদি বৌদ্ধ তন্ত্রসমূহের আকর কিন্তু মহাযান সূত্রসমূহের মধ্যে পাওয়া যায়। সপ্তম শতকে রচিত তথাগতগুহ্যক বা গুহ্যসমাজে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পরিচয় পাই। এই গ্রন্থটিকে পূর্বোক্ত ইন্দ্রভূতি প্রামাণ্য বলে মনে করেছেন। শান্তিদেব তাঁর শিক্ষাসমুচ্চয় গ্রন্থে বহুবার তথাগতগুহ্যসূত্রের উল্লেখ করেছেন। যন্ত্র ও মন্ত্র নিয়ে বিশেষ আলোচনা ছাড়াও গুহ্যসমাজে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে মৈথুনতত্ত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অপর একটি তন্ত্র পঞ্চক্রম গুহ্যসমাজেরই সংক্ষিপ্তসার যেখানে যোগ, মন্ত্র, মণ্ডল ও উপলব্ধিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। অপর একটি বিখ্যাত তান্ত্রিক গ্রন্থের নাম মঞ্জুশ্রীমূলকল্প, অন্য নাম মহাবৈপুল্যমহাযানসূত্র, যাতে মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডল তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি ৯৮০-১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চীনাভাষায় এবং একাদশ শতকে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। একল্লবীর-চণ্ড-মহারোষণতন্ত্র একদিকে যেমন মহাযানমতে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসাবে প্রসিদ্ধ, অপর দিকে এটি যোগিনী উপাসনার উপর বিশেষ আলোকপাত করে। শাক্ত দেবীরা এখানে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন। শ্রীচক্রসম্ভারতন্ত্রের তিব্বতী সংস্করণ কেবল পাওয়া যায় যেখানে প্রজ্ঞারূপিণী নারী এবং উপায়রূপ পুরুষের যৌনমিলন ইয়াব-ইউম বা যুগনদ্ধ নামে পরিচিত। অভয়কর গুপ্ত কর্তৃক একাদশ শতকে রচিত নিষ্পন্নযোগাবলী গ্রন্থে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীদের ধ্যানমূর্তির বর্ণনা ছাড়াও ছাব্বিশটি মণ্ডল সম্পর্কেও নানা তথ্য আছে। অনঙ্গবজ্রের প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি গ্রন্থে তান্ত্রিক বৌদ্ধ দর্শন ও প্রজ্ঞাভিষেক প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। অপরাপর বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের মধ্যে হেবজ্রতন্ত্র, অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ ও সেকোদ্দেশটীকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।’- (ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-১০৩)
‘আদি বৌদ্ধ তন্ত্রসমূহের আকর কিন্তু মহাযান সূত্রসমূহের মধ্যে পাওয়া যায়। সপ্তম শতকে রচিত তথাগতগুহ্যক বা গুহ্যসমাজে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পরিচয় পাই। এই গ্রন্থটিকে পূর্বোক্ত ইন্দ্রভূতি প্রামাণ্য বলে মনে করেছেন। শান্তিদেব তাঁর শিক্ষাসমুচ্চয় গ্রন্থে বহুবার তথাগতগুহ্যসূত্রের উল্লেখ করেছেন। যন্ত্র ও মন্ত্র নিয়ে বিশেষ আলোচনা ছাড়াও গুহ্যসমাজে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে মৈথুনতত্ত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অপর একটি তন্ত্র পঞ্চক্রম গুহ্যসমাজেরই সংক্ষিপ্তসার যেখানে যোগ, মন্ত্র, মণ্ডল ও উপলব্ধিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। অপর একটি বিখ্যাত তান্ত্রিক গ্রন্থের নাম মঞ্জুশ্রীমূলকল্প, অন্য নাম মহাবৈপুল্যমহাযানসূত্র, যাতে মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডল তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি ৯৮০-১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চীনাভাষায় এবং একাদশ শতকে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। একল্লবীর-চণ্ড-মহারোষণতন্ত্র একদিকে যেমন মহাযানমতে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসাবে প্রসিদ্ধ, অপর দিকে এটি যোগিনী উপাসনার উপর বিশেষ আলোকপাত করে। শাক্ত দেবীরা এখানে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন। শ্রীচক্রসম্ভারতন্ত্রের তিব্বতী সংস্করণ কেবল পাওয়া যায় যেখানে প্রজ্ঞারূপিণী নারী এবং উপায়রূপ পুরুষের যৌনমিলন ইয়াব-ইউম বা যুগনদ্ধ নামে পরিচিত। অভয়কর গুপ্ত কর্তৃক একাদশ শতকে রচিত নিষ্পন্নযোগাবলী গ্রন্থে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীদের ধ্যানমূর্তির বর্ণনা ছাড়াও ছাব্বিশটি মণ্ডল সম্পর্কেও নানা তথ্য আছে। অনঙ্গবজ্রের প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি গ্রন্থে তান্ত্রিক বৌদ্ধ দর্শন ও প্রজ্ঞাভিষেক প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। অপরাপর বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের মধ্যে হেবজ্রতন্ত্র, অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ ও সেকোদ্দেশটীকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।’- (ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-১০৩)
এখানে স্মর্তব্য যে, মহাযান বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করে দুটি দার্শনিক মতবাদ গড়ে ওঠেছিলো– বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার এবং শূন্যবাদ বা মাধ্যমিক। যোগাচার মতে চৈতন্য বা বিজ্ঞান স্বয়ং ক্রিয়াশীল, সর্বস্রষ্টা এবং পরম সত্য, যার বাইরে কিছু নেই, বিজ্ঞান বা চৈতন্য ব্যতিরেকে কোনও বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব নেই। এ প্রেক্ষিতে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মন্তব্য হলো, পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে যে অদ্বৈত বেদান্ত বিশেষ প্রাধান্যলাভ করেছিল, তার অন্যতম উৎস এই বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার। বিজ্ঞানবাদীরা অস্তিত্বের মূল সত্তাসমূহকে সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত, এই দুই ভাগে ভাগ করেন। এই সত্তাসমূহ রূপ বা বস্তু নয়, চিত্ত বা মানসজাত। যোগাচার মতে বাহ্যবস্তুর কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, যেহেতু আমরা চৈতন্য ছাড়া অন্য কোনও মাধ্যমই পেতে পারি না যা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ করতে পারে।
‘এইভাবে যখন যোগাচার দর্শন সমস্ত বস্তুকেই মানসসঞ্জাত বলে ঘোষণা করে এবং পরিদৃশ্যমান সমস্ত কিছুকেই নিছক ধারণা বলেই খারিজ করে দেয় মাধ্যমিক দর্শন বা শূন্যবাদ আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলে যে ওই চৈতন্যও অলীক। নাগার্জুন বলেন যে অভিজ্ঞতার জগৎ একটা দৃশ্যাভাস মাত্র, কয়েকটি অবোধ্য সম্পর্কের জালবুনানি। সংস্কৃত তথাকথিত অস্তিত্বের সত্তাসমূহ, যেগুলির সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আছে বলে আমাদের ধারণা, আসলে শূন্য, কেন না সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কোনও সত্তার মধ্যে একই সঙ্গে থাকতে পারে না। অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বকে কোনও বস্তুর মূল সত্তা হিসাবে প্রমাণ করা যায় না। একটি বস্তু তার গুণাবলীর দ্বারাই পরিচিত, এবং সেই হিসাবেই আমরা মাটি, জল ইত্যাদি উপাদানগুলিকে বুঝি, কিন্তু গুণাবলী স্বয়ং অস্তিত্ববান হতে পারে না। চক্ষু ব্যতিরেকে রং নেই, কাজেই গুণাবলীর আপেক্ষিক অস্তিত্ব শূন্য অস্তিত্ব, এবং সেই কারণেই যে সকল বস্তুর মধ্যে সেগুলি অবস্থান করে বলে কল্পিত, সে সকল বস্তুর কোনও সত্যকারের অস্তিত্ব নেই। দ্রব্য এবং গুণ পরস্পরনির্ভর এবং দুটির কোনটিকেই বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না। পারমার্থিকভাবে দ্রব্য ও গুণ দুই-ই অলীক, কিন্তু আপেক্ষিকভাবে মনে হয় যেন তারা বর্তমান। কোনও কার্য নেই, কোনও কারণ নেই। একটি বস্তু নিজের থেকে সৃষ্ট হয় না, অপরের থেকেও নয়, আসলে সৃষ্টি বা উৎপাদন ব্যাপারটাই অসম্ভব। জগতের কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, বস্তুসমূহ ক্ষণস্থায়ীও নয়, চিরন্তনও নয়, উৎপন্ন হয় না, বিলয়প্রাপ্তও হয় না, একও নয়, পৃথকও নয়। যা ক্রমিক কারণের দ্বারা উদ্ভূত, তা স্ব-উদ্ভূত নয়, কাজেই তার কোনও নিজস্ব অস্তিত্ব নেই।’- (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/ ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-১১২)
‘এইভাবে যখন যোগাচার দর্শন সমস্ত বস্তুকেই মানসসঞ্জাত বলে ঘোষণা করে এবং পরিদৃশ্যমান সমস্ত কিছুকেই নিছক ধারণা বলেই খারিজ করে দেয় মাধ্যমিক দর্শন বা শূন্যবাদ আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলে যে ওই চৈতন্যও অলীক। নাগার্জুন বলেন যে অভিজ্ঞতার জগৎ একটা দৃশ্যাভাস মাত্র, কয়েকটি অবোধ্য সম্পর্কের জালবুনানি। সংস্কৃত তথাকথিত অস্তিত্বের সত্তাসমূহ, যেগুলির সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আছে বলে আমাদের ধারণা, আসলে শূন্য, কেন না সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কোনও সত্তার মধ্যে একই সঙ্গে থাকতে পারে না। অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বকে কোনও বস্তুর মূল সত্তা হিসাবে প্রমাণ করা যায় না। একটি বস্তু তার গুণাবলীর দ্বারাই পরিচিত, এবং সেই হিসাবেই আমরা মাটি, জল ইত্যাদি উপাদানগুলিকে বুঝি, কিন্তু গুণাবলী স্বয়ং অস্তিত্ববান হতে পারে না। চক্ষু ব্যতিরেকে রং নেই, কাজেই গুণাবলীর আপেক্ষিক অস্তিত্ব শূন্য অস্তিত্ব, এবং সেই কারণেই যে সকল বস্তুর মধ্যে সেগুলি অবস্থান করে বলে কল্পিত, সে সকল বস্তুর কোনও সত্যকারের অস্তিত্ব নেই। দ্রব্য এবং গুণ পরস্পরনির্ভর এবং দুটির কোনটিকেই বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না। পারমার্থিকভাবে দ্রব্য ও গুণ দুই-ই অলীক, কিন্তু আপেক্ষিকভাবে মনে হয় যেন তারা বর্তমান। কোনও কার্য নেই, কোনও কারণ নেই। একটি বস্তু নিজের থেকে সৃষ্ট হয় না, অপরের থেকেও নয়, আসলে সৃষ্টি বা উৎপাদন ব্যাপারটাই অসম্ভব। জগতের কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, বস্তুসমূহ ক্ষণস্থায়ীও নয়, চিরন্তনও নয়, উৎপন্ন হয় না, বিলয়প্রাপ্তও হয় না, একও নয়, পৃথকও নয়। যা ক্রমিক কারণের দ্বারা উদ্ভূত, তা স্ব-উদ্ভূত নয়, কাজেই তার কোনও নিজস্ব অস্তিত্ব নেই।’- (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/ ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-১১২)
কিন্তু সত্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিক অনুমান হলো, বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার এবং শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকের এসব জটিল দার্শনিক তত্ত্ব হয়তো স্বল্পসংখ্যক পণ্ডিতদের চর্চার মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো। কেননা, নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত হলো– ‘বৌদ্ধ জনসাধারণ শূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদ, যোগাচার বা মাধ্যমিকদের গভীর পারমার্থিক তত্ত্ব ও সাধনমার্গের বিচিত্র স্তরের কিছুই বুঝিত না, বুঝিতে পারা সহজও ছিল না। তাঁহাদের পক্ষে যাদুশক্তিমূল মন্ত্র ও মণ্ডল, ধারণী ও বীজ অনেক বেশি সত্য ও সহজ বলিয়া ধরা দিল এবং ক্রমবর্ধমান ধর্ম-সমাজের জন্য এক শ্রেণীর বৌদ্ধ আচার্যরা মহাযানের নূতন ধ্যান-কল্পনা গড়িয়া তুলিবার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। মন্ত্রই হইল তাঁহাদের মূল প্রেরণা এবং মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ধারণী ও বীজ। ইহাদের রচিত নয়ই মন্ত্র-নয়, ইহাদের প্রদর্শিত যান বা পথই মন্ত্র-যান। এই মন্ত্রযানই মহাযানের বিবর্তনের প্রথম স্তর।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৫২৬)
বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে বজ্রযান। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ভাষায়– ‘মহাযান বৌদ্ধধর্মে দুটি বিশিষ্ট সাধনপদ্ধতির উদ্ভব হয়– মন্ত্রযান ও পারমিতাযান। মন্ত্রযান হল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক পর্যায় যেখানে মন্ত্র, ধারণী, মুদ্রা, মণ্ডল, অভিষেক প্রভৃতির প্রাধান্য বর্তমান। বজ্রযান মন্ত্রযানেরই বিবর্তিত রূপ যেখানে শূন্যতার স্থানে বজ্র শব্দটির ব্যবহার হয়। বজ্র বলতে বোঝায় আত্ম ও ধর্মসমূহের, অর্থাৎ অস্তিত্বের মূল সত্তাসমূহের, অপরিবর্তনীয় শূন্য প্রকৃতি। এখানে পরম সত্য হলেন বজ্রসত্ত্ব বা বজ্রধর যিনি বোধিচিত্তের সঙ্গে অভিন্ন এবং শূন্যতা ও করুণার অদ্বয় অবস্থার প্রতীক। তিনিই আদিবুদ্ধ যাঁর থেকে পঞ্চস্কন্ধের (রূপ, বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান) প্রতীক পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধের উদ্ভব হয়েছে যাঁরা হলেন বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। এঁদের প্রত্যেকেরই সঙ্গিনী হিসাবে একজন করে শক্তি আছেন যাঁরা হলেন বজ্রধাত্বীশ্বরী, লোচনা, মামকা, পাণ্ডরা ও আর্য তারা। প্রত্যেকের পুত্র হিসাবে একজন করে বোধিসত্ত্ব এবং একজন করে মানুষী বুদ্ধ আছেন। বজ্রসত্ত্বের সঙ্গিনী হচ্ছেন বজ্রসত্ত্বাত্মিকা, যিনি বজ্রবারাহী, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি নামেও পরিচিত। তাঁকে পূজা বা ধ্যান করতে হয় তাঁর শক্তি বা প্রজ্ঞার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অথবা যৌনমিলিত অবস্থায়, যা যুগনদ্ধ বা অদ্বয়ের আদর্শের প্রতীক।’- (ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-১১৪)
বজ্রযান সম্পর্কে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় বলেন,– ‘বজ্রযানের ধ্যান-কল্পনা গভীর ও জটিল। বজ্রযানীদের মতে নির্বাণের পর তিন অবস্থা : শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। শূন্যতত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা নাগার্জুন; তাঁহার মতে দুঃখ, কর্ম, কর্মফল, সংসার সমস্তই শূন্য, শূন্যতার এই পরম জ্ঞানই নির্বাণ। বজ্রযানীরা এই নির্বিকল্প জ্ঞানের নামকরণ করিলেন নিরাত্মা; বলিলেন, জীবের আত্মা নির্বাণ লাভ করিলে এই নিরাত্মাতেই বিলীন হয়। নিরাত্মা কল্পিতা হইলেন দেবীরূপে এবং বলা হইল, বোধিচিত্ত যখন নিরাত্মার আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া নিরাত্মাতেই বিলীন হন তখনই উৎপত্তি হয় মহাসুখের। বোধিচিত্তের অর্থ হইতেছে চিত্তের এক বিশেষ বৃত্তি বা অবস্থা যাহাতে সম্যক জ্ঞান বা বোধিলাভের সংকল্প বর্তমান। বজ্রযানীরা বলেন, মৈথুনযোগে চিত্তের যে পরম আনন্দময় ভাব, যে এককেন্দ্রিক ধ্যান তাহাই বোধিচিত্ত। এই বোধিচিত্তই বজ্র, কারণ কঠোর যোগসাধনার ফলে ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পূর্ণ দমিত চিত্ত বজ্রের মতো দৃঢ় ও কঠিন হয়। বোধিচিত্তের বজ্রভাব লাভ ঘটিলে তবে বোধিজ্ঞান লাভ হয়। চিত্তের এই বজ্রভাবকে আশ্রয় করিয়া সাধনার যে পথ তাহাই বজ্রযান। ইন্দ্রিয়শক্তিকে, কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণ দমিত করিবার কথা এই মাত্র বলা হইল। বজ্রযানীরা বলেন, ইন্দ্রিয় দমন করিতে হইলে আগে সেগুলিকে জাগরিত করিতে হয়; মিথুন সেই জাগরণের উপায়। মিথুনজাত আনন্দকে অর্থাৎ বোধিচিত্তকে স্থায়ী করা যায় মন্ত্রশক্তির সাহায্যে এবং সেই অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়শক্তি দমিত হয়। সাধকের সাধনার শক্তিতে মন্ত্র বা ধ্যান অর্থাৎ তাহার ধ্বনি রূপমূর্তি লাভ করে; এই রূপমূর্তিরাই বিভিন্ন দেবদেবী। মিথুনাবস্থার আনন্দোদ্ভূত বিভিন্ন দেবদেবী সাধকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে নিজ নিজ স্থানে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়া এক একটি মণ্ডল সৃষ্টি করেন। এই মণ্ডলের নিঃশব্দ ধ্যান করিতে করিতেই বোধিচিত্ত স্থায়ী ও স্থির হইয়া বজ্রের মতো কঠিন হয় এবং ক্রমে বোধিজ্ঞান লাভ ঘটে। বলা বাহুল্য, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বজ্রযানের এই সমস্ত সাধন-পদ্ধতিটাই অত্যন্ত গুহ্য এবং যে-ভাষায় ও শব্দে এই পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হয় তাহাও গুহ্য। গুরুদীক্ষিত-সাধক ছাড়া সে শব্দ ও ভাষার গূঢ়ার্থ আর কেহ বুঝিতে পারেন না এবং গুরুর নির্দেশ ও উপদেশ ছাড়া আর কাহারও পক্ষে এই সাধন-পদ্ধতি অনুসরণ করাও প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। বজ্রযানে গুরু অপরিহার্য। বজ্রযানে প্রজ্ঞার সার যে বোধিচিত্ত, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের ভাষায় তাহাই শক্তি।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৫২৭)
আনুমানিক দশম শতকে বজ্রযানেরই আরেক সাধনপন্থা হিসেবে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আর একটি শাখা গড়ে ওঠে যা কালচক্রযান নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ দেবতা হলেন শ্রীকালচক্র। এখানে কাল শব্দটির অর্থ প্রজ্ঞা বা শূন্য অস্তিত্ব এবং চক্র হচ্ছে জাগতিক পদ্ধতি বা উপায়। অতএব কালচক্র হলো প্রজ্ঞা ও উপায়ের অদ্বয়াবস্থা এবং সেই সঙ্গে বোধিচিত্ত এবং বজ্রসত্ত্ব তথা আদিবুদ্ধের সঙ্গে এক ও অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন,– ‘কালচক্রযানে অনেক ভয়ঙ্কর ধরনের দেবদেবী বর্তমান যাঁদের মন্ত্র, মণ্ডল ও বলিদানের দ্বারা তৃপ্ত করতে হয়। প্রজ্ঞা ছাড়াও কাল সময়ের দ্যোতক যার বিভাগ প্রাণবায়ুর দ্বারা সম্ভব হয় এবং যা স্নায়ুচক্রের মধ্যে বিস্তৃত থাকে। যোগাভ্যাসের দ্বারা এই প্রাণবায়ুকে সংযত করতে পারলে মানুষও সময়ের চক্রকে এড়াতে পারবে, ফলে তার সকল দুঃখের অবসান ঘটবে। কালচক্রযান বঙ্গদেশ, মগধ, কাশ্মীর ও নেপালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।’
অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের বর্ণনায়– ‘কালচক্রযানীদের মতে শূন্যতা ও কালচক্র এক এবং অভিন্ন। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ লইয়া অবিরাম প্রবহমান কালস্রোত চক্রাকারে ঘূর্ণ্যমান। এই কালচক্র সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ; এই কালচক্রই আদিবুদ্ধ ও সকল বুদ্ধের জন্মদাতা। কালচক্র প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হইয়া এই জন্মদান কার্যটি সম্পন্ন করেন। কালচক্রযানীদের উদ্দেশ্যই হইতেছে কালচক্রের এই অবিরাম গতিকে নিরস্ত করা অর্থাৎ নিজেদের সেই কাল-প্রভাবের ঊর্ধ্বে উন্নীত করা। কিন্তু কালকে নিরস্ত করা যায় কিরূপে? কালের গতির লক্ষণ হইতেছে একের পর এক কার্যের মালা; কার্যপরম্পরা অর্থাৎ গতির বিবর্তন দেখিয়াই আমরা কালের ধারণায় উপনীত হই। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই কার্যপরম্পরা মূলত প্রাণক্রিয়ার পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই, প্রাণক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই কালকে নিরস্ত করা যায়। কালচক্রযানীরা বলেন, যোগসাধনার বলে দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ী ও নাড়ীকেন্দ্রগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই পঞ্চবায়ুকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই প্রাণক্রিয়া নিরুদ্ধ করা যায় এবং তাহাতেই কাল নিরস্ত হয়। কাল নিরস্ত করাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে কালচক্রযানীদের সাধন-পদ্ধতিতে তিথি, বার, নক্ষত্র, রাশি, যোগ প্রভৃতি একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয় ! এই জন্যই কালচক্রযানীদের মধ্যে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রচলন ছিল খুব বেশি। তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে কালচক্রযানের উদ্ভব ভারতবর্ষের বাহিরে, সম্ভল নামক কোনো স্থানে। পাল-পর্বের কোনও সময়ে নাকি তাহা বাঙলাদেশে প্রবেশ লাভ করে। প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী অভয়াকরগুপ্ত এই মতবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন রামপালের সমসাময়িক।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৫২৯)
অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের বর্ণনায়– ‘কালচক্রযানীদের মতে শূন্যতা ও কালচক্র এক এবং অভিন্ন। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ লইয়া অবিরাম প্রবহমান কালস্রোত চক্রাকারে ঘূর্ণ্যমান। এই কালচক্র সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ; এই কালচক্রই আদিবুদ্ধ ও সকল বুদ্ধের জন্মদাতা। কালচক্র প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হইয়া এই জন্মদান কার্যটি সম্পন্ন করেন। কালচক্রযানীদের উদ্দেশ্যই হইতেছে কালচক্রের এই অবিরাম গতিকে নিরস্ত করা অর্থাৎ নিজেদের সেই কাল-প্রভাবের ঊর্ধ্বে উন্নীত করা। কিন্তু কালকে নিরস্ত করা যায় কিরূপে? কালের গতির লক্ষণ হইতেছে একের পর এক কার্যের মালা; কার্যপরম্পরা অর্থাৎ গতির বিবর্তন দেখিয়াই আমরা কালের ধারণায় উপনীত হই। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই কার্যপরম্পরা মূলত প্রাণক্রিয়ার পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই, প্রাণক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই কালকে নিরস্ত করা যায়। কালচক্রযানীরা বলেন, যোগসাধনার বলে দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ী ও নাড়ীকেন্দ্রগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই পঞ্চবায়ুকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই প্রাণক্রিয়া নিরুদ্ধ করা যায় এবং তাহাতেই কাল নিরস্ত হয়। কাল নিরস্ত করাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে কালচক্রযানীদের সাধন-পদ্ধতিতে তিথি, বার, নক্ষত্র, রাশি, যোগ প্রভৃতি একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয় ! এই জন্যই কালচক্রযানীদের মধ্যে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রচলন ছিল খুব বেশি। তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে কালচক্রযানের উদ্ভব ভারতবর্ষের বাহিরে, সম্ভল নামক কোনো স্থানে। পাল-পর্বের কোনও সময়ে নাকি তাহা বাঙলাদেশে প্রবেশ লাভ করে। প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী অভয়াকরগুপ্ত এই মতবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন রামপালের সমসাময়িক।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৫২৯)
বজ্রযান গুহ্য সাধনারই সূক্ষ্মতর স্তর সহজযান নামে খ্যাত। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বর্ণনায়– ‘সহজযান বঙ্গদেশসহ উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সহজযানী বৌদ্ধগণ মনে করেন সত্যোপলব্ধি একটা অন্তর্দর্শনের ব্যাপার, এই জন্য সহজ অর্থাৎ স্বাভাবিক পথ গ্রহণ করার দরকার। এই সহজ পথ হল বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির অনুবর্তী হওয়া। যা নেই দেহভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে, অতএব দেহই সকল সাধনার উৎস, লক্ষ্য ও মাধ্যম। যৌগিক পদ্ধতিতে কায়সাধনা, নাভিমূলে অবস্থিত নির্মাণচক্রের নারীশক্তিকে জাগিয়ে তোলা, প্রভৃতি সহজযানী মার্গ। সহজিয়া সম্প্রদায়ের রচিত চর্যাপদ ও দোহাসমূহে তাদের সাধনপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণিত হয়েছে। বজ্রযানীদের মত সহজযানীরাও যুগনদ্ধে বিশ্বাসী। সাধক স্বয়ং বুদ্ধ এবং তাঁর সঙ্গিনী বুদ্ধের শক্তি, উভয়ের মিলনেই পূর্ণজ্ঞান ও মহাসুখ। সহজযানের বিকাশ শুধু বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই হয়নি, বৈষ্ণবদের মধ্যেও এই মার্গের বিকাশ ঘটেছিল।’- (ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট/ পৃষ্ঠা-১১৫)
এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় বলেন,– ‘বজ্রযানে মন্ত্রের মূর্তি রূপের ছড়াছড়ি সুতরাং তাহার দেবায়তনও সুপ্রশস্ত; মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানে বজ্রযানের সাধনমার্গ আকীর্ণ। সহজযানে দেবদেবীর স্বীকৃতি যেমন নাই, তেমনই নাই মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি। সহজযানীরা বলেন, কাঠ, মাটি বা পাথরের তৈরি দেবদেবীর কাছে প্রণত হওয়া বৃথা। বাহ্যানুষ্ঠানের কোনো মূল্যই তাঁহাদের কাছে ছিল না। ব্রাহ্মণদের নিন্দা তো তাঁহারা করিতেনই; যে-সব বৌদ্ধ মন্ত্রজপ, পূজার্চনা, কৃচ্ছ্রসাধন প্রব্রজ্যা ইত্যাদি করিতেন তাঁহাদেরও নিন্দা করিতেন; বলিতেন সিদ্ধিলাভ, বৌদ্ধত্বলাভ তাঁহাদের ঘটে না। সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ দোহাকোষের অনেকগুলি দোহায় স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৫২৭)
এক্ষেত্রে তিনি দোহাকোষ থেকে সহজযানের দৃষ্টান্তমূলক দু’টি দোহা’র নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন–
এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় বলেন,– ‘বজ্রযানে মন্ত্রের মূর্তি রূপের ছড়াছড়ি সুতরাং তাহার দেবায়তনও সুপ্রশস্ত; মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানে বজ্রযানের সাধনমার্গ আকীর্ণ। সহজযানে দেবদেবীর স্বীকৃতি যেমন নাই, তেমনই নাই মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি। সহজযানীরা বলেন, কাঠ, মাটি বা পাথরের তৈরি দেবদেবীর কাছে প্রণত হওয়া বৃথা। বাহ্যানুষ্ঠানের কোনো মূল্যই তাঁহাদের কাছে ছিল না। ব্রাহ্মণদের নিন্দা তো তাঁহারা করিতেনই; যে-সব বৌদ্ধ মন্ত্রজপ, পূজার্চনা, কৃচ্ছ্রসাধন প্রব্রজ্যা ইত্যাদি করিতেন তাঁহাদেরও নিন্দা করিতেন; বলিতেন সিদ্ধিলাভ, বৌদ্ধত্বলাভ তাঁহাদের ঘটে না। সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ দোহাকোষের অনেকগুলি দোহায় স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৫২৭)
এক্ষেত্রে তিনি দোহাকোষ থেকে সহজযানের দৃষ্টান্তমূলক দু’টি দোহা’র নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন–
কিং তো দীবে কিং তো নিবেজ্জঁ
কিং তো কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ।
কিং তো তিত্থ তপোবন জাই
মোক্খ কি লব্ ভই পানী হ্নাই।।
অর্থাৎ : কী (হইবে) তোর দীপে, কী (হইবে) তোর নৈবেদ্যে, কী করা হইবে তোর মন্ত্রের সেবায়, কী তোর (হইবে) তীর্থ-তপোবনে যাইয়া ! জলে নাহিলেই কি মোক্ষ লাভ হয় ?এস জপহোমে মণ্ডল কম্মে
অনুদিন আচ্ছসি বাহিউ ধম্মে।
তো বিনু তরুণি নিরন্তর ণেহে
বোধি কি লব্ ভই প্রণ বি দেহেঁ।
অর্থাৎ : এই জপ-হোম-মণ্ডল কর্ম লইয়া অনুদিন বাহ্যধর্মে (লিপ্ত) আছিস্ । তোর নিরন্তর স্নেহ বিনা, হে তরুণি, এই দেহে কি বোধিলাভ হয় ?
‘সহজযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গূঢ় সাধন-পদ্ধতি ও ধ্যান-ধারণার সূক্ষ্ম গভীর পরিচয় দোহাকোষের দোহা এবং চর্যাগীতির গীতগুলিতে বিধৃত হইয়া আছে। সহজযানীরা বলেন, বোধি বা পরমজ্ঞান লাভের খবর অন্য সাধারণ লোকের তো দূরের কথা, বুদ্ধদেবও জানিতেন না– বুদ্ধোহপি ন তথা বেত্তি যথায়মিতরো নরঃ। ঐতিহাসিক বা লৌকিক বুদ্ধের স্থানই বা কোথায় ? সকলেই তো বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী এবং এই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে– দেহস্থিতং বুদ্ধত্ব ; দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই। কোথায় কতদূরে গেলে শূন্যতাবাদ, কতদূরে সরিয়া গেল বিজ্ঞানবাদ। জাগিয়া রহিল শুধু দেহবাদ, শুধু কায়সাধন। সহজিয়াদের মতে শূন্যতা হইল প্রকৃতি, করুণা হইল পুরুষ ; শূন্যতা ও করুণা অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে, অর্থাৎ নারী ও নরের মিথুন-মিলনযোগে বোধিচিত্তের যে পরমানন্দময় অবস্থার সৃষ্টি লাভ হয় তাহাই মহাসুখ। এই মহাসুখই ধ্রুবসত্য ; এই ধ্রুবসত্যের উপলব্ধি ঘটিলে ইন্দ্রিয়গ্রাম বিলুপ্ত হইয়া যায়, সংসারজ্ঞান তিরোহিত হয়, আত্মপরভেদ লোপ পায়, সংস্কার বিনষ্ট হয়। ইহাই সহজ অবস্থা। রাজা হরিকালদেব রণবঙ্কমল্লের ত্রয়োদশ শতকীয় একটি লিপিতে দেখিতেছি, জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী পট্টিকেরক নগরীতে সহজধর্মকর্মে লিপ্ত ছিলেন।’- (নীহাররঞ্জন রায়/ বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৫২৮)
কায়সাধক সহজযানীরা নিঃসন্দেহে বেদ-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা যে বেদ-আগমের কথা বলেছেন তা শুধু বেদ বা আগম মাত্র নয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রামাণিক শাস্ত্র মাত্রই তাঁদের দৃষ্টিতে বেদ, আগম প্রভৃতি। এককালের আর্যাবর্তের বাইরের বাঙলায় যে কোনকালেই যথার্থ বেদচর্চা, বৈদিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি খুব বেশি প্রচলিত ছিল না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেন-বর্মণ আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার যখন খুব বেশি, তখনও হলায়ুধ, জীমূতবাহন প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা বেদচর্চার অবহেলা দেখে দুঃখ প্রকাশ করতেন বলে নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেন। তবু প্রধানত পশ্চিমাগত ক্রিয়াত্বিত ব্রাহ্মণদেরই সাহায্যে ও প্রেরণায় উচ্চকোটির বর্ণ-হিন্দুরা যে কিছু কিছু যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বেদপাঠ ইত্যাদি করাতেন, তাঁদের লক্ষ্য করে দোহাকোষে সিদ্ধাচার্য সরহপাদ বলেছেন–
বহ্মণো হি ম জানন্ত হি ভেউ।
এবই পড়িঅউ এ চ্চউ বেউ।।
মট্টী (পাণী) কুস লই পড়ন্ত।
ঘরহিঁ [বইসী] অগ্গি হুণন্তঁ।।
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ।
অক্খি উহাবিঅ কুড় এ ধুমের্ঁ।।
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণেরা তো যথার্থ ভেদ জানে না; চতুর্বেদ এই ভাবেই পড়া হয়। তাঁহারা মাটি, জল, কুশ লইয়া (মন্ত্র) পড়ে, ঘরে বসিয়া আগুনে আহুতি দেয়; কার্যবিরহিত (অর্থাৎ ফলহীন) অগ্নিহোমের কটু ধোঁয়ায় চোখ শুধু পীড়িত হয়।
আবার দণ্ডী সন্ন্যাদীদের সম্বন্ধে সরহপাদ অন্যত্র বলছেন–
একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী ভঅবঁবেসেঁ।
বিণুআ হোই হংহউএসেঁ।।
মিচ্ছেহিঁ জগে বাহিঅ ভুল্লে।
ধম্মাধম্ম ণ জানিঅ তুল্লে।।
অর্থাৎ : একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী প্রভৃতি ভগবানের বেশে (সকলেই) ঘুরিয়া বেড়ায়; হংসের উপদেশে জ্ঞানী হয়। মিথ্যাই জগৎ ভুলে বহিয়া চলে; তাহারা ধর্মাধর্ম তুল্যরূপেই জানে না (অর্থাৎ ধর্মাধর্মের মূল্য তাহাদের কাছে সমান)।
দোহাকোষে শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রাভিমানী এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবপূজক ব্রাহ্মণদের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে সহজযানী সিদ্ধাচার্যেরা তাঁদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। যেমন–
জাহের বাণচিহ্ন রুব ণ জানী।
সে কোইসে আগম বেএঁ বখাণী।।
অর্থাৎ : যাঁহার বর্ণ, চিহ্ন ও রূপ কিছুই জানা যায় না, তাহা আগমে বেদে কিরূপে ব্যাখ্যাত হইবে?
সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মের মধ্যে থেরবাদী, মহাযানী, কালচক্রযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম, দিগম্বর জৈনধর্ম, কাপালিকধর্ম, রসসিদ্ধ তথা নাথসিদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি কিছু কিছু উল্লেখ সহজযানীদের চর্যাগীতি ও দোহাকোষে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের প্রতি সহজযাীরা শ্রদ্ধিত ছিলেন বলে মনে হয় না। যেমন চর্যাগীতিতে মহাযানীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে–
সঅল সমাহিঅ কাহি করি অই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি অই।।
অর্থাৎ : সরল (ধ্যান) সমাধি দ্বারা কী করিবে? সুখ দুঃখের হাত হইতে তাহাতে মুক্তি পাওয়া যায় না।
মহাযানী-বজ্রযানী-কালচক্রযানী প্রভৃতিদের সম্বন্ধে দোহাকোষে আছে–
অণ্ন তহি মহাজাণহিঁ ধাবই।
তহিঁ সুতন্তু তক্কসত্থ হই।।
কোই মণ্ডলচক্ক ভাবই।
অন্ন চউত্থতত্ত দীসই।।
অর্থাৎ : অন্যেরা ধাবিত হইতেছে মহাযানের দিকে, সেখানে আছে সূত্রান্ত ও তর্কশাস্ত্র। কেহ কেহ ভাবিতেছে মণ্ডল ও চক্র; দিশা দিতেছে চতুর্থ তত্ত্বে।
আবার জৈন-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে দোহাকোষে সরহপাদ বলছেন–
দীহণক্খ জই মলিণেঁ বেসেঁ।
ণগ্গল হোই উপাড়ি অ কেসেঁ।।
খবণেহি জাণ বিড়ংবিঅ বেসেঁ।
অপ্পণ বাহিঅ মোক্খ উবেসেঁ।।
অর্থাৎ : দীর্ঘনখ যোগী মলিন বেশে নগ্ন হইয়া কেশ উপড়ায়। ক্ষপণকেরা (জৈন-সন্ন্যাসীরা) বিড়ম্বিত বেশে মোক্ষের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাহির লইয়া চলে।জই নগ্গা বিঅ হোই মুক্তি তা সুণহ সিআলহ।
লোমুপাড়ণো অত্থি সিদ্ধি তা জুবই নিতম্বহ।।
পিচ্ছী গণহে দিঠ্ঠ মোক্খ [তা মোরহ চমরহ]।
উঞ্ছেঁ ভো অণোঁ হোই জাণ তা করিহ তুরঙ্গাহ।।
অর্থাৎ : নগ্ন হইলেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে কুকুর-শেয়ালেও হইত; লোম উপড়াইলেই যদি সিদ্ধি আসিত তাহা হইলে যুবতীর নিতম্বেরও সিদ্ধিলাভ ঘটিত; পুচ্ছ গ্রহণেই যদি মোক্ষ দেখা যাইত, তাহা হইলে ময়ূর-চামরেরও মোক্ষ দেখা হইত; উচ্ছ্বিষ্ট ভোজনে যদি জ্ঞান হইত, তাহা হইলে হাতি ঘোড়ারও হইত।
প্রাচীন বাঙলায় দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকে এক শ্রেণির সাধক ছিলেন যাঁরা মুত্যুর পর মুক্তি লাভে বিশ্বাস করতেন না; তাঁরা ছিলেন জীবন্মুক্তির সাধক। রস-রসায়নের সাহায্যে কায়সিদ্ধি লাভ করে এই স্থূল জড়দেহকেই সিদ্ধদেহ এবং সিদ্ধদেহকে দিব্যদেহে রূপান্তরিত করা সম্ভব এবং তা হলেই শিবত্ব লাভ ঘটে– এই মতে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। তাঁদেরকে বলা হতো রসসিদ্ধ যোগী। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় সুস্পষ্ট প্রমাণ করেছেন যে, এই রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ই পরবর্তী নাথসিদ্ধ যোগী সম্প্রদায়ের প্রাচীনতর রূপ। যা হোক, তাঁদের সম্বন্ধেও সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা যে শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিলেন না, বরং কঠোর সমালোচনাই করতেন, তা সরহপাদের দোহাতেই বোঝা যায়,–
অহ্মে ণ জাণহু অচিন্ত জোই।
জামমরণভব কইসণ হোই।।
জাইসো জাম মরণ বি তোইসো।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেসো।।
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কক্সক্ষা।।
অর্থাৎ : অচিন্ত্যযোগী আমরা, জানি না জন্ম মরণ সংসার কিরূপে হয়। জন্ম যেমন মরণও তেমনই; জীবিতে ও মৃতে বিশেষ (কোনো) পার্থক্য নাই। এখানে (এই সংসারে) যাহারা জন্ম-মরণে বিশঙ্কিত (ভীত), তাহারাই রস রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুন।
সাধারণ যোগী-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধেও সহজযানীদের ছিল নিদারুণ অবজ্ঞা। সরহপাদের একটি দোহায় আছে–
অহরি এহিঁ উদ্দুলিঅ চ্ছারেঁ।
সীসসু বাহিঅ এ জড়ভারেঁ।।
ঘরহী বইসী দীবা জালী।
কোনহিঁ বইসী ঘণ্টা চালী।।
অক্খি ণিবেসী আসণ বন্ধী।
কণ্নেহিঁ খুসুখুসাই জণ ধন্ধী।।
অর্থাৎ : আর্য যোগীরা ছাই মাখে দেহে, শিরে বহ করে জটাভার; ঘরে বসিয়া দীপ জ্বালে, কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে; চোখ বুঁজিয়া আসন বাঁধে, আর কান খুসখুস করিয়া জনসাধারণকে ধাঁধা লাগায়!
উপরের উদাহরণগুলো অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের ‘বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব’ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ-তন্ত্রগ্রন্থ গুহ্যসমাজতন্ত্র, যোগরত্নমালা, হেবজ্রতন্ত্র ইত্যাদিতেও আমরা উপরে বর্ণিত বক্তব্যের সুস্পষ্ট ছায়া দেখতে পাই। তবে কথিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক ঘরানার এই যে বিভিন্ন যান, যেমন– মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান ইত্যাদির গুহ্য সাধনপন্থার বিশেষ কোন পার্থক্য ছাড়া তাত্ত্বিক পর্যায়ে মৌলিক কোনো পার্থক্য রয়েছে বলে মনে হয় না। এ প্রেক্ষিতে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য–
‘মহাযানোদ্ভূত মন্ত্রযান, কালচক্রযান ও বজ্রযানে সীমানির্দিষ্ট পার্থক্য বিশেষ কিছু কখনো ছিল না। একই বৌদ্ধাচার্য বিভিন্ন যান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন, এবং একাধিক যান কর্তৃক গুরু এবং আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। শান্তিদেব, শান্তিরক্ষিত, দীপঙ্কর প্রভৃতি আচার্যরা মহাযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান প্রভৃতি সকল যানেই স্বীকৃত, এবং বজ্রযানী-মন্ত্রযানীরা ইঁহাদের আপন গুরু বলিয়া দাবিও করিয়াছেন। ঠিক একই কথা বলা চলে সহজযান, নাথধর্ম, কৌলধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে। এই সব ধর্ম মত ও সম্প্রদায় সমস্তই সমসাময়িক, এবং এক সম্প্রদায়ের আচার্যরা অন্য সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃতিও লাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বজ্রযান ও মন্ত্রযানের অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠাবান আচার্যরা তো সকলেই সহজযান, নাথধর্ম এবং কৌলধর্মের আদি গুরু বলিয়া স্বীকৃত। সরহ বা সরহপাদ, কৃষ্ণ বা কাহ্নপাদ, শবরপাদ, লুইপাদ-মীননাথ ইঁহারা প্রত্যেকেই বজ্রযানে যেমন স্বীকৃত, তেমনই সহজযানী-নাথপন্থী-কৌলমার্গী প্রভৃতিরাও ইঁহাদের আচার্য, বা গুরু, বা প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া দাবি করিয়াছেন। শান্তিদেব, শান্তি বা শান্তরক্ষিত, দীপঙ্কর প্রমুখ আচার্যরা গোড়ায় ছিলেন মহাযানী, পরে ক্রমশ বিবর্তিত হইয়াছিলেন বজ্রযানীরূপে, এবং যেহেতু বজ্রযান মহাযান হইতেই উদ্ভূত এবং তাহারই বিবর্তিত রূপ সেই হেতু ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক বা অনৈতিহাসিক কিছু নাই। এই কারণেই নাথপন্থী বা কৌলমার্গীদের গুরু লুইপাদ-মীননাথ এবং সহজযানীদের লুইপাদ দুই ব্যক্তি, এমন মনে করিবারও কোনও কারণ নাই। বজ্রযানোদ্ভূত এই সব ধর্মমার্গ ও সম্প্রদায় গোড়ায়ই আপনাপন বৈশিষ্ট্য লইয়া সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমিত হয় নাই; সে-সব বৈশিষ্ট্য ক্রমশ পরে গড়িয়া উঠিয়াছে। বরং, সূচনায় ইঁহাদের একই ছিল ধ্যান ও আদর্শ, একই ছিল ভাব-পরিমণ্ডল, এবং যাহারা সেই ধ্যান, আদর্শ ও ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন তাঁহারা পরে প্রত্যেক স্ব-স্বতন্ত্র মত ও সম্প্রদায় কর্তৃক গুরু এবং আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাহা ছাড়া, মন্ত্রযান-বজ্রযান ধর্মের মন্ত্র, মণ্ডল প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠানের প্রতি সহজযানী সিদ্ধাচার্যের মনোভাব যত বিরূপই হোক না কেন, নাথ ও কৌলধর্মের প্রতি বিরূপ হইবার তেমন কারণ কিছু ছিলনা; ইহাদের মধ্যে, মৌলিক বিরোধ স্বল্পই। ইহাদের মধ্যে, বিশেষভাবে নাথধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া সমানেই চলিতেছিল। নাথধর্ম ছিল কতকটা লোকায়ত ধর্ম, সহজযানও কতকটা তাই। কাজেই ইহাদের মধ্যে এবং অন্যান্য লোকায়ত ধর্মের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগ কিছুটা ছিলই, এবং ছিল বলিয়াই ইহাদের ভিতর হইতে এবং ইহাদেরই ধ্যানাদর্শ লইয়া পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়া-ধর্ম, শৈব, নাথযোগী সম্প্রদায়, আউল-বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় ও মতামতের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, পৃষ্ঠা-৫৮৭)
‘মহাযানোদ্ভূত মন্ত্রযান, কালচক্রযান ও বজ্রযানে সীমানির্দিষ্ট পার্থক্য বিশেষ কিছু কখনো ছিল না। একই বৌদ্ধাচার্য বিভিন্ন যান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন, এবং একাধিক যান কর্তৃক গুরু এবং আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। শান্তিদেব, শান্তিরক্ষিত, দীপঙ্কর প্রভৃতি আচার্যরা মহাযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান প্রভৃতি সকল যানেই স্বীকৃত, এবং বজ্রযানী-মন্ত্রযানীরা ইঁহাদের আপন গুরু বলিয়া দাবিও করিয়াছেন। ঠিক একই কথা বলা চলে সহজযান, নাথধর্ম, কৌলধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে। এই সব ধর্ম মত ও সম্প্রদায় সমস্তই সমসাময়িক, এবং এক সম্প্রদায়ের আচার্যরা অন্য সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃতিও লাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বজ্রযান ও মন্ত্রযানের অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠাবান আচার্যরা তো সকলেই সহজযান, নাথধর্ম এবং কৌলধর্মের আদি গুরু বলিয়া স্বীকৃত। সরহ বা সরহপাদ, কৃষ্ণ বা কাহ্নপাদ, শবরপাদ, লুইপাদ-মীননাথ ইঁহারা প্রত্যেকেই বজ্রযানে যেমন স্বীকৃত, তেমনই সহজযানী-নাথপন্থী-কৌলমার্গী প্রভৃতিরাও ইঁহাদের আচার্য, বা গুরু, বা প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া দাবি করিয়াছেন। শান্তিদেব, শান্তি বা শান্তরক্ষিত, দীপঙ্কর প্রমুখ আচার্যরা গোড়ায় ছিলেন মহাযানী, পরে ক্রমশ বিবর্তিত হইয়াছিলেন বজ্রযানীরূপে, এবং যেহেতু বজ্রযান মহাযান হইতেই উদ্ভূত এবং তাহারই বিবর্তিত রূপ সেই হেতু ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক বা অনৈতিহাসিক কিছু নাই। এই কারণেই নাথপন্থী বা কৌলমার্গীদের গুরু লুইপাদ-মীননাথ এবং সহজযানীদের লুইপাদ দুই ব্যক্তি, এমন মনে করিবারও কোনও কারণ নাই। বজ্রযানোদ্ভূত এই সব ধর্মমার্গ ও সম্প্রদায় গোড়ায়ই আপনাপন বৈশিষ্ট্য লইয়া সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমিত হয় নাই; সে-সব বৈশিষ্ট্য ক্রমশ পরে গড়িয়া উঠিয়াছে। বরং, সূচনায় ইঁহাদের একই ছিল ধ্যান ও আদর্শ, একই ছিল ভাব-পরিমণ্ডল, এবং যাহারা সেই ধ্যান, আদর্শ ও ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন তাঁহারা পরে প্রত্যেক স্ব-স্বতন্ত্র মত ও সম্প্রদায় কর্তৃক গুরু এবং আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাহা ছাড়া, মন্ত্রযান-বজ্রযান ধর্মের মন্ত্র, মণ্ডল প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠানের প্রতি সহজযানী সিদ্ধাচার্যের মনোভাব যত বিরূপই হোক না কেন, নাথ ও কৌলধর্মের প্রতি বিরূপ হইবার তেমন কারণ কিছু ছিলনা; ইহাদের মধ্যে, মৌলিক বিরোধ স্বল্পই। ইহাদের মধ্যে, বিশেষভাবে নাথধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া সমানেই চলিতেছিল। নাথধর্ম ছিল কতকটা লোকায়ত ধর্ম, সহজযানও কতকটা তাই। কাজেই ইহাদের মধ্যে এবং অন্যান্য লোকায়ত ধর্মের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগ কিছুটা ছিলই, এবং ছিল বলিয়াই ইহাদের ভিতর হইতে এবং ইহাদেরই ধ্যানাদর্শ লইয়া পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়া-ধর্ম, শৈব, নাথযোগী সম্প্রদায়, আউল-বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় ও মতামতের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল।’- (বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, পৃষ্ঠা-৫৮৭)
সে যাক্, আমরা দেখি, বজ্রযান সাধন-পদ্ধতিতে বজ্রযান সাধন-পদ্ধতিতে গুরু যে অপরিহার্য তা বৌদ্ধতন্ত্রের আদি গ্রন্থ গুহ্যসমাজতন্ত্রে বলা হয়েছে–
‘ন বিনা বজ্রগুরুণা সর্ব্বক্লেশপ্রমাণকম্ ।
নির্ব্বাণঞ্চ পদং শান্তমবৈবর্ত্তিকমাপ্নুয়াৎ।।’- (গুহ্যসমাজতন্ত্র)
অর্থাৎ : বজ্রগুরু ব্যতিরেকে নির্বাণপদ পাওয়া যায় না। যে নির্বাণে সকল ক্লেশের নাশ হয়, শান্তি যে নির্বাণের চরম ফল, যে নির্বাণে আর “বিবর্ত” থাকে না, অর্থাৎ কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, সে পদ গুরুর কৃপা ভিন্ন পাওয়া যায় না।
সহজযানের মূল কথাও– সদ্গুরুর উপদেশ। কিন্তু সে গুরুকে বজ্রগুরু বলা হয় কেন? বজ্র বলতে শূন্যতা বোঝায়। বজ্রযানের অন্যতম মূল শাস্ত্র ‘হেবজ্রতন্ত্র’র টীকাগ্রন্থ ‘যোগরত্নমালা’য় বলা হয়েছে–
‘দৃঢ়ং সারমশৌষীর্য্যমচ্ছেদ্যঃ অভেদ্যলক্ষণম্ ।
অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে।।’- ( যোগরত্নমালা)
অর্থাৎ : শূন্যতাই বজ্র। তাকে ছেদ করা যায় না, ভেদ করা যায় না, দগ্ধ করা যায় না, বিনাশ করা যায় না, এতে ছিদ্র করা যায় না– তা অতি দৃঢ় ও সারবান। যে গুরু এই শূন্যতাবজ্রের উপদেশ দেন, তিনিই বজ্রগুরু।
সহজযান মতে, গুরুর উপদেশে যা লাভ হয়, সে লাভ শতসহস্র সমাধিতে হয় না। তার আরেকটি অর্থ হয়তো এরকম যে, ইন্দ্রিয় নিরোধের চেষ্টা করা বৃথা, কঠোর ব্রত ধারণের চেষ্টা বৃথা, কঠিন কঠিন নিয়মপালন করাও বৃথা হয়তো। কেননা, গুহ্যসমাজতন্ত্রেই বলা হয়েছে–
‘দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈমূর্ত্তিঃ শুষ্যতি দুঃখিতা।
দুঃখাদ্ধি ক্ষিপ্যতে চিত্তং বিক্ষেপাৎ সিদ্ধিরন্যথা।।’- (গুহ্যসমাজতন্ত্র)
অর্থাৎ : যদি তুমি কঠোর নিয়ম পালন করো, তাহলে তোমার শরীর শুষ্ক হবে ও তোমার নানারূপ দুঃখ উপস্থিত হবে। দুঃখ উপস্থিত হলে মন স্থির থাকবে না, মন স্থির না থাকলে কখনোই সিদ্ধিলাভ হয় না।
কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, বুদ্ধ যেহেতু সাধনমার্গে মধ্যপন্থা মেনে চলতেন এবং অন্যকেও মধ্যপন্থা অনুসরণের উপদেশ দিয়েছেন, উপরিউক্ত উপদেশে বুঝি তারই প্রতিফলন রয়েছে। কিন্তু ‘হেবজ্রতন্ত্রে’ উক্ত নিচের শ্লোকটিতে আমরা হয়তো অন্য কিছুর ইঙ্গিত পেয়ে যাই–
‘রাগেণ বধ্যতে লোকো রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ।।’- ( হেবজ্রতন্ত্র)
অর্থাৎ : বিষয়ের আসক্তিতেই লোকে বদ্ধ হয়, আবার সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয়। আসক্তির এই যে বিপরীত ফলদানের ক্ষমতা বুদ্ধতীর্থিকেরা এটা জানতো না, (অর্থাৎ, অন্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোকেরা তা জানে না, আমরা, সহজপন্থীরাই কেবল জানি।)
অন্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের তীর্থিকেরা কী জানতো না? হয়তো তার উত্তর ‘গুহ্যসমাজতন্ত্রে’ই দেয়া হয়েছে এভাবে–
‘পঞ্চকামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্নৈব পীড়য়েৎ।
সুখেন সাধয়েদ্বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ।।’- (গুহ্যসমাজতন্ত্র)
অর্থাৎ : পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, বিষয়কেই ভোগ বলে, বিষয়কেই কাম বলে। সেই পঞ্চকাম বা পাঁচটি ভোগ ত্যাগ করে তপস্যার দ্বারা নিজেকে পীড়া দেবে না। যোগতন্ত্রানুসারে সুখভোগ করতে করতে বোধির সাধনা করবে।
তাই হয়তো হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর সহজযান নিবন্ধে কটাক্ষ করেই বলেছেন– ‘এই-সকল সহজপন্থীর শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, যদি তোমার বোধিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে পঞ্চকাম উপভোগ করো।’- (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৯)
অতএব, একান্ত দ্বিরুক্তি হলেও শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের সেই অভিমতটি আবারো উল্লেখ করে বলা যেতে পারে– ‘মাতৃপূজা এবং শক্তিসাধনার প্রচলন বাঙলাদেশে অনেক পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা এখানে একটা নবরূপ লাভ করিয়াছে এবং এই নবরূপেই বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতিকে তাহা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কিন্তু বাঙলাদেশে তন্ত্রসাধনার প্রচলন এবং প্রভাব অনেক পূর্ব হইতে। বাঙলাদেশে এবং তৎসংলগ্ন পূর্বভারতীয় অঞ্চলসমূহে এই তন্ত্রপ্রভাব খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মকে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল। আমার ধারণা, বাঙলাদেশে যত হিন্দুতন্ত্র প্রচলিত আছে তাহা মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। বাঙলাদেশে এই হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র বলিয়া যে দুইটি জাতিভেদ করা হয় সেই ভেদলক্ষণ আমার কাছে খুব স্পষ্ট এবং নিঃসন্দিগ্ধ মনে হয় না। সংস্কারবর্জিতভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষের তন্ত্রসাধনা মূলতঃ একটি সাধনা। তন্ত্রের মধ্যে দার্শনিক মতবাদগুলি বড় কথা নয়– বড় হইল দেহকেই যন্ত্রস্বরূপ করিয়া কতকগুলি গুহ্য সাধনপদ্ধতি। এই সাধনপদ্ধতিগুলি পরবর্তী কালের লোকায়ত বৌদ্ধধর্মের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, আবার হিন্দুধর্মের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া হিন্দুতন্ত্রের রূপ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু আসলে বৌদ্ধ ‘প্রজ্ঞা-উপায়ে’র পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনাশ্রিত সাধনা, আর হিন্দু শিব-শক্তির পরিকল্পনা এবং তদাশ্রিত সাধনার মধ্যে বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ দোঁহাকোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজিয়া রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতি বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।’ -(ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য)


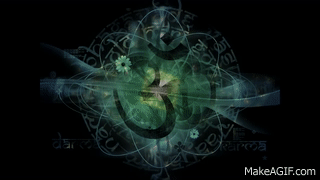




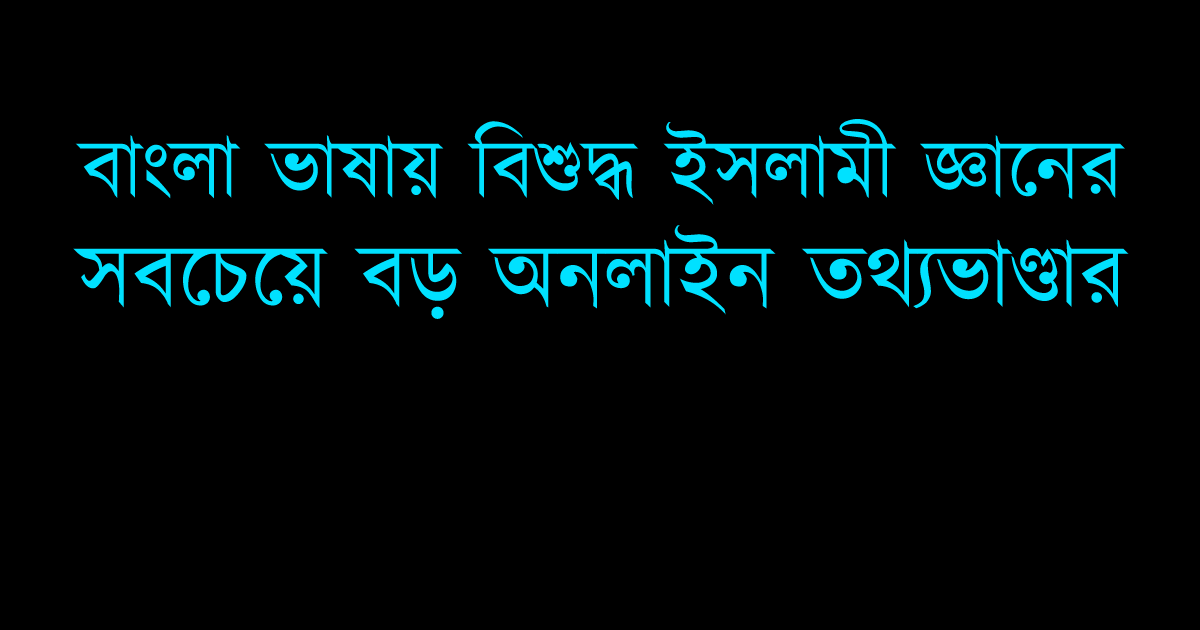



















No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ