নীতিশাস্ত্র দর্শনের একটি শাখা যেখানে নৈতিকতা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাত্ত্বিক দিকগুলো, যেমন - ভাল-মন্দের সংজ্ঞা এর সাথে প্রায়োগিক দিক, যেমন - মানুষের ভাল বা মন্দ ব্যবহারের সংজ্ঞা-ও এর আলোচ্য বিষয়। মানুষের ব্যবহারগত সম্পর্কের তাৎপর্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্র বিকাশ লাভ করেছে।
যুক্তিহীন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার এই শাস্ত্রসম্মত প্রাচীন নজির একালেও বিরল তো নয়ই, বরং ভিন্ন রূপে ভিন্ন মোড়কে তাকে আরো বেশি মাত্রায় সক্রিয় হতে দেখা যায় এখনো। তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্তঃসারশূন্য শান্ত্র-দর্শনের বিপরীতে জড়বাদী লোকায়ত চার্বাক দর্শনের এইযে বাস্তববাদী শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে গেলো, তাকে প্রতিরোধ করতেই সে-সময়কার শাসকদের নিয়োজিত করতে হয়েছিলো তাদের সর্বময় শক্তি। তাদের দর্শনের প্রধান কাজই হয়ে দাঁড়ালো ওই লোকায়তের বাস্তব যুক্তি খণ্ডনের উপায় অন্বেষণ। আর এই শক্তির বলয় তৈরি করতে সৃষ্টি করতে হয়েছে সম্পূর্ণ এক পরভোজী সম্প্রদায়, উৎপাদন সংশ্লিষ্টতাহীন আরাম-আয়েশ-বিলাস-ব্যসনে মত্ত অঢেল সময় থেকে যাদের একমাত্র কাজ হলো নতুন নতুন ধর্মশাস্ত্রীয় কল্পনা, যুক্তি, তর্ক ইত্যাদির সমৃদ্ধিতে নিজেদের সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রাখা। রাজশক্তির সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের অঢেল ভোগলিপ্সা পরিতৃপ্তির পাশাপাশি এরা রচনা করবে রাজশক্তিকে নিরাপদ রাখার যাবতীয় কলাকৌশল। এরাই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, ক্ষত্রিয় শাসনে তাদেরকে দেয়া হলো সর্বোচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত বিদ্যাগুরুর পদ। এরাই চর্চা করবে যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের, তৈরি করবে সামাজিক আইন, তাদের মুখনিঃসৃত বাণীই হবে নীতিশাস্ত্র, সংবিধান, পালনীয় আচার। কারণ তাঁরাই জ্ঞানী বা বিদ্বান হিসেবে স্বীকৃত। তাঁদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব নির্দেশ করে মনুশাস্ত্রে তাই বলা হচ্ছে-
ত্রয়ী অর্থ বেদ। ঋগে¦দ, সামবেদ, যজুর্বেদ এই তিনটি একত্রে বেদ। সেকালে তখনো চতুর্থ বেদ অর্থাৎ অথর্ববেদ সংগৃহীত হয়নি বা তখনো তা বেদ হিসেবে গুরুত্ববহ স্বীকৃতি পায়নি বলে প্রাচীন শাস্ত্রে বেদকে ত্রয়ী হিসেবেই উল্লেখ করা হয়। দণ্ডনীতি হলো রাজকার্য পরিচালনার বিধান। বার্তা হলো কৃষি ইত্যাদি অর্থনীতিসংক্রান্ত বিদ্যা। আর আন্বীক্ষিকী হলো তর্কবিদ্যা। এ সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রেই বলা হচ্ছে-
বুঝাই যাচ্ছে, প্রচলিত ধর্মকে রার করার উপায় হিসেবে সৃষ্ট ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, মীমাংসা ইত্যাদি ধর্মীয় শাস্ত্রকে হেতু বা যুক্তির মাধ্যমে ধর্ম-অধর্ম, অর্থ-অনর্থ, ফলাফল ইত্যাদির বিচার করে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করাই আন্বীক্ষিকীর উদ্দেশ্য। আর এজন্যেই লোকায়ত বার্হষ্পত্যরা আন্বীক্ষিকীকে প্রামাণ্য বিদ্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেন না। আর ত্রয়ী বা বেদকে তো প্রামাণ্য মানতেই নারাজ। কারণ তাঁদের মতে-
লোকায়তিকরা প্রত্যক্ষের বাইরে কোন কিছুকেই প্রমাণ হিসেবে মানেন না। তাই কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বার্হস্পত্যদের সম্পর্কে উক্তি করেছেন-
কৌটিল্য যে বার্হস্পত্যদের সাথে কোনভাবেই একমত নন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা তিনি তো বিদ্যা অর্থে চারটি শাস্ত্রকেই নির্দেশ করেছেন। অতএব, কৌটিল্য তথা চাণক্যের নীতিশ্লোকে বর্ণিত বিদ্বানের আয়ত্তে কোন্ কোন্ বিদ্যা থাকবে তা পরিষ্কার। সমাজকে তাঁদের চাওয়া অনুযায়ী এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনে যেসব শাস্ত্রে বুৎপত্তি, দক্ষতা ও লক্ষ্যনিষ্ঠ সক্রিয়তা থাকা দরকার মনে করেছেন, সেটাই নীতিশাস্ত্রের মাধ্যমে সমাজকে জানিয়ে দিয়েছেন। মোড়কের বাইরে বিদ্যা নাম নিয়ে কোন আপত্তি না-থাকলেও বিদ্যার সংজ্ঞা, কাঠামো, উৎস বা লক্ষ্য নিয়ে তৎকালীন দার্শনিক চিন্তকদের মধ্যে যে প্রচণ্ড অন্তর্বিরোধের সাংঘর্ষিক উপাদান সক্রিয় ছিলো তাও নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছি আমরা। আর আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার সমাজ ও তার ভৌগোলিক অবস্থা, যোগাযোগ কাঠামো, জীবনধারণ পরিবেশ ইত্যকার বিষয় বিবেচনায় নিলে সে-সময় প্রবাস বলতে নিশ্চয়ই অত্যাধুনিক উড়োজাহাজে চড়ে সুদূর মার্কিনদেশ বা পাশ্চাত্যের ইউরোপ ভ্রমণ বোঝাতো না। খুব স্বাভাবিকভাবে আশেপাশের কোন গমনযোগ্য রাজ্য বা অঞ্চল কিংবা তৎকালীন বৃহত্তর ভারতবর্ষকেই বোঝানো হতো। ফলে বিদ্বান সর্বত্র পূজনীয় বলা হলেও এই সর্বত্রেরও যে একটা সীমিত ভৌগলিক কাঠামো ছিলো তাও বোঝার বাকি থাকে না। ওই কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়ন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যবহারিক মূল্যের আলোকেই বিদ্যাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ঠিক এই বিষয়টিকে মাথায় রাখলেই আমরা নীতিশাস্ত্রের সেই চিরায়ত সুরের খোঁজটি পেয়ে যাই। যেখানে প্রয়োজনীয় সমকালীন তান সংযুক্ত করে দিলেই তা যুগোপযোগী হয়ে ওঠতে পারে। আর তাই এই নীতিকথাকে আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না তো বটেই, বরং সময়ের তরতাজা ক্রমানুক্রমিক রসে সিক্ত হয়ে তা আমাদের জন্য কালোত্তীর্ণ এক চিরকালীন অমূল্য রত্ন হিসেবেই আগ্রহের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে।
.
এবার তাহলে আমরা ফিরে যাই নীতিশ্লোকটির কাছে। কোন রাজাধিরাজ নয়, বিদ্বানই সর্বত্র পূজিত হন। কারণ তিনিই বিদ্বান্ যিনি সেই বিদ্যাটিই আয়ত্ত করেন যা দিয়ে সমাজ-সভ্যতার অগ্রযাত্রা আরো বেগবান, সৃষ্টিশীল ও বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। আর যা আঁকড়ে থাকলে সমাজ স্থবিরতায় আক্রান্ত হয়, সম্মুখগতি হারিয়ে পেছনমুখি হয় সেটা কোন বিদ্যাই নয়। তাই ওইসব প্রাগৈতিহাসিক জঞ্জালবিদ্যায় পাণ্ডিত্যের পাহাড় জমিয়ে তাকে রিসাইক্লিং না করে কেবলি ঘাটাঘুটি করলে পচা-গলা-বাসি অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধই ছড়াবে শুধু, সমাজ আক্রান্ত হবে অথর্বতায়, কিন্তু কোন বিদ্যা বা বিদ্বান বেরুবে না যিনি মানুষকে সামনে যাবার পথটা দেখিয়ে দেবেন। সর্বত্র পূজিত বিদ্বান তিনিই যিনি যে-সমাজের অধিবাসীই হোন না কেন বৃহত্তর মানবসমাজকে সামনে এগিয়ে যাবার পথটা তৈরি করে দেন তার সমকালীন বিদ্যার সৃষ্টিশীলতা দিয়ে। দেশ-কাল অতিক্রম করে মানবসভ্যতা যাদের কাছে ঋণী, সভ্যতার প্রারম্ভিক কাল থেকে একাল পর্যন্ত এরকম বহু বহু বিদ্বানের নাম যুগে যুগে মানবেতিহাসের অত্যুজ্জ্বল পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে। কিন্তু এরা কেউ ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। ধর্মের কূপমণ্ডূকতায় আবদ্ধও ছিলেন না এরা।
.
মূর্খ ব্যক্তির চেয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি অধিকতর গুণবান হবেন, সম্ভাব্যতার বিচারে তা মেনে নিতেই পারি আমরা। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি সকল দোষের আধার- (নিজে মূর্খ বলেই) এরকম একটা সন্দেহাতীত ঘোষিত নিশ্চিত সিদ্ধান্তকে হজম করার আগে কিঞ্চিৎ ভাবনার দরকার নয় কি ? প্রথমত মূর্খ বলতে চাণক্য কাদের বুঝিয়েছেন, আর পণ্ডিতই বা কারা ? সাধারণ জ্ঞানে বলা হয়, বিভিন্ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে যিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তিনিই পণ্ডিত। কিন্তু সাধারণ জ্ঞান আর বিশেষ জ্ঞানের মধ্যে যে ব্যাপক ফারাক ! বিশেষ করে নীতিশ্লোক রচয়িতা চাণক্যের সময়কালও বিবেচনায় রাখাটা জরুরি বটে। সেক্ষেত্রে তৎকালীন সকল শাস্ত্রের আধার সমাজের অবশ্যপালনীয় স্মৃতিশাস্ত্র ‘মনুসংহিতা’য় মনু কী বলেছেন দেখি-
পণ্ডিত ব্রাহ্মণের কাছে যে সুরতলাভ বা কাম চরিতার্থ করা তুচ্ছবিষয় ছিলো না তা মনুশাস্ত্রের দুটো ক্রমিক শাস্ত্রবিধানের উদ্ধৃতি থেকে না-বুঝার কথা নয়। প্রায় আড়াই-হাজার বছরের প্রাচীন কীর্তি চাণক্যের যে-কোন নীতিশ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে সেই সমাজের সার্বিক আবহ ও দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা তাই জরুরি বলে মনে হয়। এবং এতোকাল পরে এসে এখনো এসব নীতিশ্লোকের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করলে আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার নাড়ির স্পন্দনটাও টের পাওয়ার যায় সহজেই। তবে এ ধরনের নীতিশ্লোকের সবচাইতে বড় প্রভাববিস্তারী সামর্থটা হলো সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েও এর চিরায়ত রূপ গ্রহণের ক্ষমতা। সময়ের সাথে মানবসমাজের জীবনাচার ও ভাবনাস্রোতে যে ইতিবাচক বিবর্তন ঘটে যায় তার সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করলেও এই নীতিশ্লোকগুলির গ্রহণযোগ্যতা একটুও ক্ষুণ্ন হয় না। তাই বর্তমান নীতিশ্লোকটির উল্লিখিত পণ্ডিত ব্যক্তি যদি সেকালের কূপমণ্ডূক শাস্ত্রবেত্তা কোন একচক্ষু পণ্ডিত না হয়ে সমাজ-সভ্যতাকে সামনে এগিয়ে নেয়ার নতুন নতুন পথ সৃষ্টিকারী মানবদরদী কোন বিজ্ঞানমনস্ক সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব হন, এবং মূর্খ বলতে যদি প্রাগৈতিহাসিক ধ্যান-ধারণা স্থবিরতায় আক্রান্ত সৃজনশীলজ্ঞান-বিমুখ কূপমণ্ডূক ব্যক্তিবর্গকে বোঝায়, তাহলে মানবসভ্যতার যে-কোন সময়কালের জন্যেই চাণক্যের এই নীতিশ্লোক আমাদের কাছে চিরকালীন প্রাসঙ্গিক হয়ে ধরা দেয়। জ্ঞান-অন্বেষায় সামনে এগিয়ে যেতে নিজের অবস্থান চিহ্নিত করতে পেছনে ফিরে তাকানো যেতে পারে, কিন্তু পেছনে হাঁটার প্রয়োগসিদ্ধতা আদৌ কি আছে ?
.
আর শাস্ত্রজ্ঞ বা বিদ্বান ব্যক্তি যে তিনিই যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে নিজ ধর্মে নিবিষ্ট হবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জন করবেন (মনুসংহিতা : ২/৮) তা ইতঃপূর্বে (নীতিবাক্য-০১-এ) বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তাই সে প্রেক্ষিত এখানে পুনরায় ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। তবে এই প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জনের লক্ষ্যে ধর্মের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অবগত হওয়ার উপায়টাও যে শাস্ত্রে বলে দেয়া হয়েছে তা আলোচনার সুবিধার্থে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে মনুশাস্ত্রে বলা হচ্ছে-
.
উল্লেখ্য, এখানে ধর্ম শব্দটির অর্থ হলো বেদার্থ অর্থাৎ বেদবাক্যের তাৎপর্যবিষয়ীভূত অর্থ। অতএব আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, ধর্ম অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করার যে শাস্ত্রবিহিত জ্ঞান, সেটুকু যিনি আয়ত্ত করবেন তিনিই শাস্ত্রজ্ঞ। এবং তিনিই হবেন গুণবান। ধর্মভিত্তিক গোঁড়ামিপূর্ণ বৃত্তাবদ্ধ একটা সমাজে মানুষের মানবিক ও নৈতিক গুণাবলী গৌন হয়ে যুক্তিহীনভাবে কেবলমাত্র ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থা ও নিষ্ঠা থাকাই যে মহৎ গুণের পরিচায়ক হয়ে ওঠা, এটাই তাৎপর্যপূর্ণ এবং অনুধাবনেরও বিষয়। নীতিপ্রবক্তা পণ্ডিত চাণক্য যে আসলে এ বৃত্তের বাইরের কেউ নন, এটা বোধ করি বোঝার বাকি রাখে না। এবং আড়াই হাজার বছর পেরিয়ে একালের এই আমরা এখনো এ গণ্ডিটা কতোটা মুক্ত হতে পেরেছি তা নিজেদের জন্যেও বোঝাপড়ার বিষয়।
.
এখানে বুদ্ধিমান পাঠকের জ্ঞাতার্থে এটাও জানিয়ে রাখা আবশ্যক যে, প্রতিটা বিষয়ের উৎস সন্ধানে আমাদেরকে যেহেতু বারে বারে শাস্ত্রীয়-বিধানের আকরগ্রন্থ মনুসংহিতার দ্বারস্থ হতে হচ্ছে, তাই বেদবিহিত এই মনুশাস্ত্রের যথার্থতা নিয়ে যাতে কারো কোন সন্দেহের অবকাশ না-থাকে সে লক্ষ্যে মনুশাস্ত্রেই নির্দেশিত হয়েছে-
.
তাই এই মনুশাস্ত্রের প্রতি আস্থা অগাধ হলে নিশ্চয়ই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য বিষয় চাণক্য-কথিত কুল বা বংশমর্যাদার প্রাচীন উৎসটাও খুঁজে পেতে সহায়ক হবে। আর তা খুঁজতে হলে প্রথমত আমাদেরকে এ ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত হতে হবে যে বংশের সাথে জন্মের সম্পর্কটা অবিচ্ছেদ্য। সে সন্দেহ থাকার কথাও নয়, কেননা বংশ মানে হচ্ছে জন্ম-পরম্পরায় উত্তরাধিকার বহন। একবার জন্ম নিয়ে বংশের যে তিলকটা কপালে সেঁটে গেছে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি জন্মপ্রক্রিয়ার বাইরে অন্য কোন উপায়ে আরেকটি বংশে অনুপ্রবেশও কোনোভাবে সম্ভব নয়। প্রকৃতির একটা উল্লেখযোগ্য প্রধান জাতিগোষ্ঠি এই মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও বংশ নামের আরেকটি অদ্ভুত খাঁচায় নিজেকে আবিষ্কারের এই বিস্ময়টা আমাদেরকে আসলে তথাকথিত পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ নামের কিছু ধর্মীয় ধারণার মুখোমুখি করে দেয়। আর এই শাস্ত্রের মাহাত্ম্যই বলি কি রহস্যই বলি তা নিয়ন্ত্রণের সূত্রটা সুকৌশলে রাখা হয়েছে এক অদৃশ্য স্রষ্টা ব্রহ্মার রহস্যময় লীলার মধ্যে। আপাতত সেই রহস্য বাদ রেখে বরং বংশ লীলাটাই খোঁজা যাক। এ বিষয়ে প্রথমেই মনু বলছেন-
.
কিন্তু ব্রহ্মা কর্তৃক এই বর্ণ সৃষ্টি তো আর এমনি এমনি হয়নি। পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী এজন্মে তার ফল ভোগ করার নিমিত্তেই ব্রহ্মা কর্তৃক মানবকুলে এই বর্ণসৃষ্টি। তাই শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুনির্দিষ্ট কার্যেরও ঘোষণা করা হলো-
.
অর্থাৎ উপরিউক্ত শ্লোকগুলো থেকে আমরা এটা বুঝে যাই যে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা গোটা বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করে তা সুষ্ঠুভাবে রক্ষাকল্পে চারটি বর্ণ সৃষ্টি করলেন- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের আবার দুটো ভাগ- এক ভাগে প্রথম তিনটি যথাক্রমে উচ্চতম, উচ্চতর ও উচ্চ বর্ণ, আর দ্বিতীয় ভাগে চতুর্থটি অর্থাৎ শূদ্র হচ্ছে নিম্নবর্ণ, যে কিনা উচ্চবর্ণীয়দের সেবাদাস। আবার ব্রাহ্মণ, যে কিনা কোন শারীরিক শ্রমের সাথে কোনভাবেই জড়িত নয়, সকল বর্ণের শীর্ষে। শুধু শীর্ষেই নয়, ক্ষমতার এতোটাই কল্পনাতীত উচ্চ অবস্থানে অবস্থিত যে, জগতের সবকিছুর মালিক বা প্রভুও হচ্ছে ব্রাহ্মণ-
.
উদ্ধৃত পবিত্র শ্লোকগুলো থেকে নিশ্চয়ই কুল অর্থাৎ বংশ বা বর্ণের ক্রমিক শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায় আমাদের। তবু অজ্ঞানী বা মূর্খ-দৃষ্টিতে শরীরের অবস্থান অনুযায়ী মুখ, বাহু, উরু ও পায়ের পবিত্রতার রকমফের নিয়ে যাতে সন্দেহের কোনরূপ অবকাশই না-থাকে, সে লক্ষ্যে মনুশাস্ত্র সবার মঙ্গলার্থে তা স্পষ্ট করে দিয়েছে এভাবে-
.
উল্লেখ্য, এখানে পুরুষ বলতে কিন্তু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকেই বোঝানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে নাভির উর্ধ্বপ্রদেশ পবিত্রতর অংশ। তাহলে নাভির নিম্নপ্রদেশ ? পাদ বা পায়ের অবস্থান তো নিম্নেই। সবখানে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে হয় না, কারণ শাস্ত্রগ্রন্থ তো নিম্নবর্ণীয় মূর্খদের জন্যে নয়। পুরুষ ব্রহ্মা আপাদ-মস্তক সর্বতোভাবে পবিত্র হলেও তাঁর পা থেকে উৎপন্ন শূদ্রের বংশ বা বর্ণের নিচত্বে যে কোন সন্দেহ থাকা চলবে না, সেটাও শাস্ত্র-বিধানে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে-
.
বড় ভয়ঙ্কর কথা ! অতএব আশা করা যায় এতোসব শাস্ত্র-উদ্ধৃতির ভারে ভারাক্রান্ত হতে হতে নিশ্চয়ই আমরা মানবকুলে বংশমর্যাদা নামের সৃষ্ট প্রপঞ্চ বা রহস্যের উৎস-সূত্রটা একটু হলেও অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছি। আমাদের আপাত প্রয়োজন এটুকুই। আর তা সম্বল করেই আরেকটু ভালোভাবে অনুধাবনের উদ্দেশ্যে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের রচিত চাণক্যের উদ্ধৃত নীতিবাক্যটির কাছে আবার ফিরে যেতে পারি আমরা।
নীতিবাক্যে বলা হচ্ছে- যে ব্যক্তি গুণহীন, তার উচ্চবংশে জন্মগ্রহণেও সার্থকতা কোথায় ? বিপরীতপক্ষে, যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ না করলেও দেবতাদের দ্বারা পূজিত (সমাদৃত) হন।
.
অর্থাৎ কোন ব্যক্তির উচ্চবংশে জন্ম নিয়ে বংশ-নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় বেদবিহিত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বুৎপত্তি অর্জন করার মাধ্যমে গুণবান হওয়ার যে কর্তব্যকাজ নির্দিষ্ট করা আছে, তা যথাযথ না-হলে ওই গুণহীন ব্যক্তির উচ্চবংশে জন্মগ্রহণের কোন সার্থকতা থাকে না। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী চাণক্যের প্রথমাংশের সাথে আমাদের মতানৈক্য হওয়ার সুযোগ নেই বলতে হবে। কিন্তু অন্যদিকে উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম না-হয়ে শূদ্রজাত নীচ-বংশে জন্ম নিয়ে কোন ব্যক্তির শাস্ত্রজ্ঞ হওয়ার সুযোগ আদৌ কি শাস্ত্রগ্রন্থে রাখা হয়েছে ? শাস্ত্রবাক্য শোনাও তো তার জন্যে অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। কিভাবে সে গুণবান শাস্ত্রজ্ঞ হবে ? সেক্ষেত্রে চাণক্যের দ্বিতীয়াংশের এই বিভ্রমের উত্তর হতে পারে এরকম যে, ব্রাহ্মণ না-হয়ে হয়তোবা শাস্ত্র অধ্যয়নের অনুমোদপ্রাপ্ত অন্য কোন দ্বিজ যেমন ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেও শাস্ত্রজ্ঞ হওয়ার সুযোগ রয়েছে। মোটকথা ব্রহ্মার উর্ধ্বাঙ্গের যেকোন অঙ্গ থেকে উৎপন্ন উচ্চবর্ণীয় দ্বিজদের নিজেদের মধ্যেই এই সুবিধা ভাগাভাগির একটা কৌশলই এই নীতিবাক্যে প্রতিবিম্বিত হতে দেখি আমরা। এখানে আসলে নিচ-জাত নিম্নবংশীয় শূদ্র ও অন্যান্য অন্ত্যজদের গুণবান হওয়ার উপায় বা স্বীকৃতির কোন সুযোগই রাখা হয়নি। এটাকেই যদি এ নীতিবাক্যের গোপন মর্মার্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাতে কি খুব অন্যায় হবে ?
.
এই বংশবত্তার জয়গান কেবল যে চাণক্য বা ভর্তৃহরির ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা নয়, পরবর্তীকালের ধর্মের পট্টি বাঁধা চোখের অন্যান্য নীতিকথকদের মধ্যেও সমভাবে দৃষ্ট হয় তা। যেমন ‘উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহে’র একটি শ্লোকেও এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-
.
আসলে এই ভূখণ্ডের পুরনো জনগোষ্ঠির প্রাচীন জনসংস্কৃতিতে পরবর্তীকালে বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির মিশেল ঘটলেও আশরাফ-আতরাফ বা উচ্চ-নীচ বংশ-মর্যাদা বা মর্যাদাহীনতার বহু কল্পকাহিনী ও প্রচলিত সমাজ-মনস্কতায় এই সামাজিক বিভেদটা বিলুপ্ত না হয়ে বরং আরো জোরালো হয়েই জেঁকে বসেছে বিভিন্ন চেহারায় বিভিন্ন মোড়কে। তাই হয়তো চাণক্যের এই ধর্মীয় সামাজিক বৈষম্যদায়ী নীতিশ্লোকটা বর্তমান জনমানসের কাছে আগ্রহ হারায় নি এখনো। এর প্রধান কারণ হয়তো এটাই যে, ধর্মীয় আধিপত্যবাদী মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার আগল থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি আজো।
.
কিন্তু বর্তমানকালের অগ্রবর্তী জ্ঞান ও সামাজিক সাম্যতার ধর্ম নিরপেক্ষ বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই নীতিশ্লোকটিতে কোনোভাবে সমকালীন ব্যাখ্যা আরোপ করা আদৌ কি সম্ভব ? নিশ্চয়ই তা ভাবনার বিষয়। কেননা, বংশমর্যাদার মতো একটা পশ্চাৎপদ হীন দৃষ্টিসম্পন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকায় চাণক্যের এই নীতিশ্লোকটিকে আসলে মুক্ত মানবিক চিন্তা কাঠামোয় এখন আর কোনভাবেই যুগোপযোগী হবার উপায় নেই বলেই প্রতীয়মান হয়।
বিক্রমাদিত্যের মা ছিলেন মালব দেশের তৎকালীন রাজধানী ধারা নগরের রাজকন্যা। ধারারাজের কোন পুত্র সন্তান না-থাকায় উভয় দৌহিত্র অর্থাৎ ভর্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্যকে তিনি তুল্যস্নেহে পরিপালন করেন এবং যথাসময়ে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী করে তোলেন।
.
স্বাভাবিক স্নেহবশতই ধারাপতি একসময় আপন দৌহিত্র বিক্রমাদিত্যকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করার অভিলাষ করেন এবং বিক্রমাদিত্যকে তাঁর সংকল্পের কথা জানান। জ্যেষ্ঠ বর্তমানে তিনি সিংহাসনে বসতে অনিহা প্রকাশ করায় তাঁর যুক্তি ও ঔদার্যে মুগ্ধ হয়ে ধারাপতি ভর্তৃহরিকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন অনুজ বিক্রমাদিত্য। এর কিছুকাল পরে তাঁরা মালবের রাজধানী ধারানগর থেকে উজ্জৈন-এ স্থানান্তর করেন।
.
বিক্রমাদিত্যের সুযোগ্য মন্ত্রণায় রাজ্য নির্বিঘ্নেই চলছিলো এবং প্রজারা সুখেই দিনাতিপাত করছিলো। বিক্রমাদিত্যের সঠিক ও সফল পরিচালনার জন্য ভর্তৃহরিকে প্রায় কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টি দিতে হতো না বলে এই সুযোগে ভর্তৃহরি মদ ও নারীতে আসক্ত হয়ে অন্তঃপুরে নারীসঙ্গ ও নারীসম্ভোগেই দিন কাটাতে লাগলেন। বিক্রমাদিত্য এ বিষয়ে তাঁকে বহুবার সাবধান করে রাজকার্যের প্রতি মনোসংযোগ করতে পরামর্শ দিলেনও তিনি তাতে কর্ণপাত না করে উল্টো বিক্রমাদিত্যের প্রতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠতে লাগলেন। এমনিভাবে ভর্তৃহরি অনন্ত বিলাসের মধ্য দিয়ে ক্রমশ অধঃপাতের দিকে এগিয়ে গেলেন। অবস্থা সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছলে কোনও এক নারীঘটিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ফলে পরস্পরের সৌভ্রাতৃত্ব শত্রুতায় পর্যবসিত হয় এবং স্ত্রী (বা প্রেমিকা)-র পরামর্শে ভর্তৃহরি বিক্রমাদিত্যকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত ও নির্বাসিত করেন।
.
বিক্রমাদিত্যকে পদচ্যুত ও নির্বাসিত করে ভর্তৃহরি নির্বাধায় সুরা ও নারীভোগে নিমজ্জিত হন। এদিকে বিক্রমাদিত্যকে অপসারণ করায় এবং তাঁর অপশাসনে প্রজারা তাঁর প্রতি বিক্ষুব্ধ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রজাদের স্বেচ্ছাচারিতায় সমগ্র মালবদেশ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় ছেয়ে যায়।
.
অন্য এক তথ্যে ‘অর্বাচিনকোষ’ মতে ভর্তৃহরির পিতা ছিলেন একজন গন্ধর্ব। তাঁর নাম বীরসেন। বীরসেনের স্ত্রী অর্থাৎ ভর্তৃহরির মা সুশীলা ছিলেন জম্বুদ্বীপরাজের একমাত্র কন্যা। ভর্তৃহরিরা ছিলেন চার ভাই-বোন, যথাক্রমে- ভর্তৃহরি, বিক্রমাদিত্য, সুভতবীর্য এবং ময়নাবতী। ধারণা করা হয় এই ময়নাবতীই ছিলেন বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা গোপিচন্দের জননী। ভর্তৃহরির মাতামহ জম্বুদ্বীপরাজের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র ভর্তৃহরিকে তিনি তাঁর রাজ্য দান করেন। ভর্তৃহরি তাঁর রাজধানী জম্বুদ্বীপ হতে উজ্জৈন-এ স্থানান্তরিত করে বিক্রমাদিত্যকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং সুভতবীর্যকে তাঁর প্রধান সেনাপতি করেন।
.
পণ্ডিত শশগিরি শাস্ত্রী প্রবর্তিত অন্য এক প্রচলিত মতানুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত নামে জনৈক ব্রাহ্মণের চারবর্ণের চারজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে- ব্রাহ্মণ জাতীয়া ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ভানুমতী, বৈশ্যা ভাগ্যবতী এবং শূদ্রা সিন্ধুমতী। এই চার স্ত্রীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের চারজন পুত্র জন্মে, যথাক্রমে- বররুচি, বিক্রমার্ক, ভট্টি ও ভর্তৃহরি। বিক্রমার্ক রাজা হন এবং ভট্টি (মতান্তরে ভট্টি ও ভর্তৃহরি) তাঁর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত হন।
.
উপরোক্ত এই তিন ধরনের পরস্পর-সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যময় তথ্যপুঞ্জি থেকে এখন পর্যন্ত কোন্ তথ্যটি সঠিক তা নির্ধারণ করা দুরুহ হলেও সাদৃশ্যটুকু থেকে আমরা অন্তত এটুকু ধারণা করতে পারি যে- ভর্তৃহরি হয়তো মাতামহের রাজ্য পেয়ে একজন রাজা বা রাজপুরুষ ছিলেন, ফলে রাজ্য বা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বিক্রমার্ক বা বিক্রমাদিত্য তাঁর ভাই ছিলেন।
.
ভর্তৃহরির দাম্পত্যজীবন নিরঙ্কুশ সুখের ছিলো না। দাম্পত্য জীবনে তিনি যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিনী স্ত্রীর দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন তা তাঁর নামে প্রচলিত চমৎকার একটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায়-
একদিন জনৈক ব্রাহ্মণ পুত্রলাভের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রসন্ন চিত্তে রাজা ভর্তৃহরিকে একটি দৈব ফল দান করেন- যে ফল ভক্ষণে আয়ু বৃদ্ধি পাবে। রাজা এই অসাধারণ ফলটি নিজে না খেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী অনঙ্গসেনাকে দিলেন। অনঙ্গসেনার আবার এক গোপন প্রেমিক ছিলো- ফলটি তিনি তাকে দিলেন। সেই প্রেমিক আবার এক পতিতার প্রণয়াসক্ত ছিলো- তাই ফলটি সে ওই পতিতাকে দিলো। সেই পতিতা আবার মনে মনে রাজা ভর্তৃহরিকে ভালোবাসতো। ‘এই ফল ভক্ষণে রাজা দীর্ঘায়ু হলে রাজ্যের লাভ’- এরকম চিন্তা করে সে তাই ফলটি রাজাকেই দিয়ে দিলো। স্ত্রীকে দেয়া ফলটি পুনরায় পতিতার হাত থেকে ফিরে পেয়ে ভর্তৃহরি যারপর নেই বিস্মিত হলেন। স্ত্রী অনঙ্গসেনাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। এতে ভর্তৃহরি হৃদয়ে মর্মান্তিক বেদনা বোধ করলেন। প্রাণাধিক প্রিয়তমা স্ত্রীর এরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত ভর্তৃহরি ভাবলেন-
.
ভর্তৃহরি স্ত্রীকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। অনঙ্গসেনাও এই কলঙ্কিত জীবনের ভার বইতে না পেরে আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি লাভ করেন। স্ত্রীর এই আত্মহত্যার ঘটনায় ভর্তৃহরির হৃদয় পুনরায় আহত হয়। ভর্তৃহরির এই দুঃসময়ে সত্যিকারের পতিভক্তি ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের আধার হয়ে এগিয়ে আসেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী কোমলহৃদয়া পিঙ্গলা। পিঙ্গলার অসাধারণ সেবাযত্নে ভর্তৃহরি ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং আবার যেন নতুন জীবনে পদার্পণ করে পরম সুখে কাটতে থাকে তাঁর দাম্পত্য জীবন।
.
কিন্তু বিধি বাম ! এ সময়ে ঘটে তাঁর দ্বিতীয় মর্মান্তিক ঘটনা, যার কারণে তিনি সংসার-বিবাগী হয়ে যান এবং রচনা করেন ‘বৈরাগ্যশতক’। জনশ্রুতি অনুযায়ী ঘটনাটি হলো-
ভর্তৃহরি একদিন শিকার সন্ধানে বনে যান। সেখানে গিয়ে তিনি সাংঘাতিক এক দৃশ্য দেখতে পান। দেখেন- জনৈক ব্যাধ (শিকারী) বাণ দ্বারা একটি হরিণকে বধ করে সে নিজেও সেখানেই সর্পাঘাতে মৃত্যুবরণ করে। তিনি আশ্চর্য বিস্ময়ে দেখলেন- কিছুক্ষণ পর হরিণীটি এসে মৃত হরিণটির নিস্তব্ধ অসার দেহের উপর পতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। শুধু তা-ই নয়, আরও কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলো- ওই শিকারীর স্ত্রী এসে চিতাগ্নিতে স্বামীসহ ভস্মীভূত হয়ে যায়।
.
এই দৃশ্য ভর্তৃহরির হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে এবং তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়েন। মৃগয়া পরিত্যাগ করে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাণী পিঙ্গলাকে অরণ্যের সেই বিস্ময়কর ঘটনা সবিস্তারে শোনান। রাণী পিঙ্গলা সমস্ত ঘটনা শুনে বলেন- পতির বিরহে সতী নারী আত্মাহুতি দেবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, বরং প্রকৃত সতী যে- এরূপ আত্মাহুতিতে তার আগুনেরও প্রয়োজন হয় না।
পিঙ্গলার এ কথায় রাজা আরও বিস্মিত হন। তাঁর মনে একটু সন্দেহেরও সৃষ্টি হয়। তাই তিনি সঙ্কল্প করেন- পিঙ্গলার পতিভক্তির পরীক্ষা নেবেন।
.
পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজা কয়েকদিন পরে পুনরায় মৃগয়ায় বের হলেন। মৃগয়ায় গিয়ে নিজের পোশাক-পরিচ্ছদে রক্ত মাখিয়ে স্বীয় অনুচর দ্বারা রাজধানীতে রাণী পিঙ্গলার কাছে পাঠিয়ে দেন। অনুচর রাণীকে রাজার রক্তাপ্লুত পোশাক অর্পণ করে নিবেদন করে যে- বাঘের হাতে রাজার মৃত্যু হয়েছে, এই তাঁর রক্তাক্ত পরিচ্ছদ। সরলপ্রাণা পিঙ্গলা আকস্মিক এ মর্মান্তিক সংবাদে প্রথমে স্তব্ধ হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর শান্তভাবে রাজার রক্তমাখা পরিচ্ছদ হাতে নিয়ে সেগুলি মাটিতে রেখে অন্তিম প্রণতি জানান এবং ভূমিতে শায়িত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
.
রাজধানীতে ফিরে এসে ভর্তৃহরি এই হৃদয় বিদারক ঘটনা শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। আপন দোষে তিনি পিঙ্গলাকে হারিয়েছেন- এ কারণেই তাঁর ব্যথা আরও বেশি করে অনুভূত হতে লাগলো। তিনি বারবার নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। পরপর দু’বার প্রিয়তমা স্ত্রীদের দ্বারা এভাবে মর্মাহত হয়ে সংসারের প্রতি ভর্তৃহরির মোহ কেটে যায়। শেষপর্যন্ত সংসার ছেড়ে বৈরাগ্য গ্রহণ করে তিনি অরণ্যে গমন করেন।
.
ভর্তৃহরি বিতর্ক
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ‘ভট্টি’ ও ‘ভর্তৃ-হরি’ নামে তিনজন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং এ তিনজনই কবি। ভট্টির রচনা ‘ভট্টকাব্য’ বা ‘রাবণবধ’ একটি মহাকাব্য। প্রথম ভর্তৃহরির রচনা ‘শতকত্রয়’- শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক। আর দ্বিতীয় ভর্তৃহরির রচনা হলো পতঞ্জলির মহাভাষ্যের উপর ব্যাকরণদর্শন জাতীয় গ্রন্থ ‘বাক্যপদীয়’। এ তিনজনই একই ব্যক্তি না কি পৃথক তিনজন কবি ছিলেন- এ নিয়ে পণ্ডিত-গবেষকদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক রয়েছে।
.
কেউ বলেন এঁরা তিনজন পৃথক ব্যক্তি ((-M.R.Kale), কেউ বলেন এঁরা তিনজন একই ব্যক্তি (-A.A.Mackonell ও ড. রামেশ্বর শ’)। আবার কারো মতে ভট্টি এবং শতকরচয়িতা ভর্তৃহরি এক এবং বাক্যপাদীয়কার ভর্তৃহরি ভিন্ন ব্যক্তি (-ড. বিধানচন্দ্র ভট্টাচার্য)। এ মতের বিরোধিতা করে আবার কেউ কেউ বলেন- ভট্টি এবং শতককার ভর্তৃহরি এক নন (-S.N.Dasgupta, S.K.De, Krishna Chitanya, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী এবং জাহ্নবীচরণ ভৌমিক)। শতককার ভর্তৃহরি এবং বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি একই ব্যক্তি বলেও মতামত প্রকাশ করেন কেউ কেউ (-জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী এবং Krishna Chitanya)। আবার দুই ভর্তৃহরি এক- এই মতকেও স্বীকার করেন নি কেউ কেউ- (Prof,K.B.Pathak Ges K.T.Telang)। এভাবে বর্তমান সময় পর্যন্ত আরও অনেক গবেষকই এ বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন।
.
চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং (I-tsing) ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভ্রমণে আসেন। জানা যায়, তিনি তাঁর বিবরণীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে গেছেন যে, তাঁর আগমনের ৪০ বৎসর পূর্বে (৬৫১ খ্রিঃ) বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি (ভর্তৃহরি) ছিলেন একজন বৌদ্ধ এবং ‘বাক্যপদীয়’ নামক গ্রন্থটি তাঁরই রচিত। এই পরিব্রাজকের বিবরণীতে জনৈক ভর্তৃহরি সম্পর্কে এক চমৎকার ঘটনা যায়। তিনি (ভর্তৃহরি) নাকি সংসার ছেড়েও সংসারের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। সন্ন্যাসজীবনে তিনি এক সময় বৌদ্ধ সঙ্ঘে আশ্রয় নেন। কিন্তু যখনই সংসারের সুখ-দুঃখের কথা মনে পড়তো তখনই ছুটে যেতেন সংসার জীবনে। এজন্য একটি গাড়িও না-কি সর্বদা প্রস্তুত থাকতো যাতে ইচ্ছে মতো তিনি সংসারে ফিরে যেতে পারেন। এমনিভাবে ভর্তৃহরি না-কি সাতবার বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগ দিয়েছেন এবং সাতবার সঙ্ঘের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। এই ভর্তৃহরি শতককার ভর্তৃহরি না হয়ে বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, কারণ শতককার ভর্তৃহরি বৌদ্ধ ছিলেন না, ছিলেন শৈব।
.
ভট্টি বা শতককার ভর্তৃহরি কেউ-ই বৌদ্ধ ছিলেন না। তাঁদের রচনায় এমন কথা বা প্রামাণ্য তথ্য নেই যার দ্বারা এটা অনুমিত হতে পারে যে, তাঁদের রচয়িতা বৌদ্ধ কবি। ভট্টির মহাকাব্যের (ভট্টিকাব্য বা রাবণবধ) ঘটনা রামায়ণাশ্রয়ী এবং তার নায়ক স্বয়ং রাম- হিন্দু ধর্মের একজন আদর্শ পুরুষ। রাম হিন্দুদের কাছে বিষ্ণুর অবতার বলেই খ্যাত। তাছাড়া ভট্টির কাব্য-রচনার পেছনে প্রচলিত কিংবদন্তী থেকেও বুঝা যায় যে তিনি একজন বেদজ্ঞ হিন্দু ছিলেন। অন্যদিকে বৌদ্ধরা বেদবিরোধী নাস্তিক।
.
আর শতককার ভর্তৃহরি যে হিন্দু ছিলেন এর বড় প্রমাণ তাঁর শতকত্রয়। নীতিশতকের শুরুতেই তিনি ব্রহ্মকে নমস্কার জানিয়েছেন ‘নম শান্তায় তেজসে’ বলে-
.
নীতিশতকের এই নান্দীশ্লোক ছাড়াও আরও অনেক শ্লোকেই তিনি ব্রহ্মসহ অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবতা এবং অবতার সম্পর্কে বলেছেন। নীতিশতকে ভর্তৃহরি মানুষের আরাধ্য দেবতা হয় শিব অথবা কেশব (বিষ্ণু) বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন-
.
এভাবে শতককার ভর্তৃহরি তাঁর অন্য রচনা শৃঙ্গারশতকের শুরুতে স্মরণ করেছেন হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে ‘শম্ভুস্বয়ম্ভূহরয়ঃ’, এবং নান্দী ব্যতীত আরও অনেক জায়গায় তিনি ‘ব্রহ্মা’ সহ হিন্দু দেব-দেবীর কথা বলেছেন। আর বৈরাগ্যশতকে তিনি প্রথমেই আত্মনিবেদন করেছেন সমস্ত ‘অজ্ঞান-অন্ধকারের… জ্ঞানালোকস্বরূপ ভগবান শিব’-এর পায়ে ‘…মোহতিমি… জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ’। এছাড়াও বৈরাগ্যশতকের বিভিন্ন জায়গায় শ্লোকে শিবের অর্চনা ও তৎপদে আত্মনিবেদনের কথা বলেছেন।
.
আবার গবেষকদের মতে শতকত্রয় এবং ভট্টিকাব্যের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকেও এটা প্রতীয়মান হয় না যে, এগুলি একই ব্যক্তির রচনা। ভট্টিকাব্যের রচয়িতা একজন বৈয়াকরণ হওয়ায় ব্যাকরণের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় ভট্টিকাব্য একটি সার্থক রচনা, সাহিত্যের দিক থেকেও একই কথা প্রযোজ্য। এছাড়া কবি নিজেই তাঁর কাব্যপাঠের ব্যাপারে চমৎকার হুশিয়ারী জ্ঞাপন করেছেন এ বলে যে- ব্যাকরণে উৎসাহী পাঠকের কাছে এই কাব্য উজ্জ্বল দীপতুল্য কিন্তু ব্যাকরণ-জ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে এটি অন্ধের হাতে দর্পণের মতো- ‘দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোয়ং শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্’। কিংবা-
.
ভট্টিকাব্য রচয়িতার এই হুঁশিয়ারি হয়তো যথার্থই। কিন্তু শতকত্রয় সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। ভট্টিকাব্যের তুলনায় শতকত্রয় নিতান্তই কাঁচা হাতের লেখা বলে মনে হয়। শতকত্রয়ের ভাষা সহজ-সরল ও সহজবোধ্য, সকলেরই এতে প্রবেশাধিকার রয়েছে। শতকত্রয়ে ব্যাকরণিক নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য নয়। এসব কারণেই সহজে স্বীকার করার উপায় নেই যে, শতকত্রয় এবং ভট্টিকাব্য একই ব্যক্তির রচনা।
.
আবার কিংবদন্তীপ্রসূত জীবনচরিত এবং শতকত্রয়ের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, ভর্তৃহরি ছিলেন একজন ক্ষত্রিয়, পক্ষান্তরে ভট্টি ছিলেন ব্রাহ্মণ। ভর্তৃহরি ছিলেন রাজা বা রাজপুরুষ, কিন্তু ভট্টি ছিলেন বলভীরাজের পোষ্য কবি। বলভীর রাজা শ্রীধরসেনের কিংবা তাঁর পুত্র নরেন্দ্রের সভাকবি ছিলেন ভট্টি (খ্রিঃ ৪৯৫-৬৪১-এর মধ্যে যে-কোন এক সময়ে), এবং সেখানে থেকেই তিনি ভট্টিকাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু ভর্তৃহরি নিজেই উজ্জৈন বা উজ্জয়িনীর রাজা থেকে থাকলে এবং পরবর্তীকালে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হয়ে থাকলে তিনি অন্য রাজার সভাকবি হতে যাবেন এমনটা কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।
.
শতকত্রয় বিশেষত বৈরাগ্যশতক থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভর্তৃহরি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন এবং বাকি জীবন অরণ্যে-আশ্রমেই অতিবাহিত করেছিলেন। নীতিশতকের একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে-
.
মর্মার্থ দাঁড়ালো- সংসারে যারা সুখ না পায় তাদের জন্য অরণ্যই একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাই বোধ করি সমগ্র বৈরাগ্যশতক জুড়ে এই আকুতি দেখা যায়- অরণ্যে গঙ্গাতীরে কিংবা হিমালয়ের কোন গুহাগহ্বরে বসে ‘শিব শিব’ মন্ত্র জপ করতে করতে শিবত্ব অর্জন করার। তাছাড়া বৈরাগ্যশতকের একটি শ্লোকে তাঁর স্পষ্ট উক্তি দেখতে পাই-
অর্থাৎ যে-রাজ্য ত্যাগ করে তিনি দিগম্বর বা সন্ন্যাসী হয়েছেন পুনরায় সে-রাজ্যে তাঁর প্রয়োজন কী ?
.
তাই অন্য কোন চূড়ান্ত প্রমাণ না-পাওয়াতক ভট্টিকাব্যের ভট্টি আর শতককার ভর্তৃহরি যে এক নয়, তেমনি বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি আর শতককার ভর্তৃহরিও এক নয়, এ ব্যাপারে আপাত সিদ্ধান্ত নেয়া অনুচিৎ হবে না বলেই মনে হয়। তাঁদের প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র একেকজন কবি হিসেবেই আমরা ধরে নিতে পারি।
.
ভর্তৃহরির রচনাবলী
শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক- এই শতকত্রয়ের কোথাও ভর্তৃহরির নাম লেখা না-থাকলেও তিনিই যে শতকত্রয়ের রচয়িতা- এ ব্যাপারে সকলেই প্রায় একমত। তবে কারো কারো মতে অবশ্য ভর্তৃহরি শতকত্রয়ের রচয়িতা নন, সঙ্কলয়িতা মাত্র। তিনি অন্য কবিদের রচিত এবং লোকমুখে প্রচলিত শ্লোকসমূহ বিষয়বস্তু অনুসারে তিনটি শিরোনামে বিন্যাস করেছেন বলে তাঁদের অভিমত (-Dr.Bohlen Ges Abraham Roger)।
.
এছাড়া শতকত্রয় ব্যতীত ভর্তৃহরির নামের সঙ্গে আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম যুক্ত করেছেন কেউ কেউ তাঁদের গ্রন্থে। সেগুলো হচ্ছে- ভট্টিকাব্য (বা রাবণবধ), বাক্যপদীয়, মহাভাষ্যদীপিকা, মীমাংসাভাষ্য, বেদান্তসূত্রবৃত্তি, শব্দধাতুসমীক্ষা ও ভাগবৃত্তি। এগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি যে শতককার ভর্তৃহরির রচনা নয় সে সম্পর্কে ইতঃপূর্বেই আলোচনায় এসেছে। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি সম্পর্কে পক্ষে বা বিপক্ষে যথার্থ কোন যুক্তি বা তথ্য এখনো অজ্ঞাত বলে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা এখনি সম্ভব নয়।
তবে শতকত্রয় ভর্তৃহরির মৌলিক রচনা কি-না, এ সম্পর্কে তিনটি মত প্রচলিত আছে বলে জানা যায়। প্রথম মত হলো- শতকত্রয় ভর্তৃহরির মৌলিক রচনা নয়, সঙ্কলিত। দ্বিতীয় মত হলো- অন্য কোন কবি বা কবিরা শতকত্রয় রচনা করে ভর্তৃহরির নামে উৎসর্গ করেছেন। এবং তৃতীয় মত- শতকত্রয় ভর্তৃহরির নিজের রচনা।
.
প্রথম মতের প্রবক্তাদের যুক্তি হলো- শতকত্রয়ের শ্লোকগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যসূত্র নেই এবং বিভিন্ন কবিদের রচিত শ্লোক এতে দেখা যায়। শতকত্রয়ের শ্লোকগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যসূত্র নেই সত্য, কিন্তু প্রতিটি শতকের মোট শ্লোকগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় এবং এই ভাগগুলোর অন্তর্গত শ্লোকসমূহের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ভাব-সঙ্গতি বা বক্তব্যের ঐক্য বর্তমান। প্রতিটি শতকের শ্লোকগুলিকে তাই দেখা যায় ভাব বা বক্তব্যভিত্তিতে দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অতএব শতকত্রয়ের শ্লোকগুলো যে একেবারেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন একথা স্বীকার্য নয়। তাছাড়া সংস্কৃত কাব্যের নিয়মে শতককাব্যের শ্রেণীই হচ্ছে ‘মুক্তক’. যার বৈশিষ্ট্যই হলো প্রতিটি শ্লোক হবে পরস্পর অর্থনিরপেক্ষ। এতে কোন কাহিনী থাকবে না, থাকবে না ঘটনার ঐক্য। তাই একটির সঙ্গে অন্যটির ঐক্যসূত্র নেই বলেই যে শতকত্রয় মৌলিক রচনা না হয়ে সঙ্কলিত গ্রন্থ হবে- এ অনুমানের বাস্তব ভিত্তি নেই বলেই মনে হয়।
.
শতকত্রয়ের মধ্যে অন্য কবিদের রচিত শ্লোক যে পাওয়া যায় তা সত্য। যেমন- কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলে’র (পঞ্চম অঙ্ক-১২) শ্লোকটি দেখা যায় নীতিশতকের এই শ্লোকে-
.
এবং বিশাখদত্তের ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকের (দ্বিতীয় অঙ্ক-১৭) শ্লোকটি পাওয়া যায় নীতিশতকের এই শ্লোকে-
.
এরকম উদাহরণ আরো আছে। এ ধরনের শ্লোকগুলি যে নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে লিপিকরদের হাতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। কেননা শতককাব্যের নামের সার্থকতা বিচার করতে গেলে শতকত্রয়ের প্রত্যেকটিতে একশত করে মোট তিনশত শ্লোক থাকাই বাঞ্ছনীয় ছিলো। কিন্তু সেখানে আছে চারশোর কাছাকাছি। জানা যায়, M.R.Kale সম্পাদিত নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতকে মূল শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ১০৮ ও ১০১টি। এ ছাড়াও দুটি শতকে অতিরিক্ত শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ২৫ ও ৪৪টি। এই অতিরিক্ত শ্লোকসমূহেরই কোন কোনটি আবার শতকদ্বয়ের অপর অপর সংস্করণে মূল শ্লোকসমূহের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। তাই কোনটা যে ভর্তৃহরির আর কোনটা প্রক্ষিপ্ত তা নিরূপণ কষ্টকর বলে গবেষকদের মন্তব্য। সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (তৃতীয় খণ্ড)-এ শৃঙ্গারশতকে শ্লোক সংখ্যা ১০০টি। এ হিসেবে তিনটি শতকে মোট শ্লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭৮।
.
ভর্তৃহরি হয়তো তিনটি কাব্যে তিনশত শ্লোকই রচনা করেছিলেন, কিন্তু কালে কালে লিপিকর ও অন্যান্যদের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে তাদের কলেবর আজ এতোটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রক্ষেপণের কাজটি পরবর্তীকালের কোন কোন অখ্যাত কবিদের দ্বারাও হতে পারে। কারণ শ্লোকসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যসূত্রই যখন নেই তখন ভাবগত ঐক্য বজায় রেখে একটি দুটি রচিত শ্লোক এর সঙ্গে যোগ হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। শতকত্রয়ে অন্যান্য যে সব কবির রচনা পাওয়া যায় তাঁদের দু-একজন ছাড়া বাকিরা অজ্ঞাত অখ্যাতই শুধু নয়, সময়ের মানদণ্ডে তাদের অধিকাংশই ভর্তৃহরির অর্বাচীন। যেমন সর্বজন-নন্দিত ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকের স্রষ্টা সংস্কৃতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিশাখদত্তের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তিনি খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকের বলে ধরা হয়। সে বিবেচনায় সম্ভাব্য খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের কবি ভর্তৃহরি নিজে এই সব শ্লোক তাঁর কাব্যে গ্রহণ করেন নি- পরবর্তীকালের প্রক্ষেপণকারীদেরই কাজ এটা।
.
ভর্তৃহরির রচনা সম্পর্কে অন্য যে মত- অন্য কবি বা কবিরা শতকত্রয় রচনা করে ভর্তৃহরির নামে প্রকাশ করেছে কিংবা ভর্তৃহরিই অন্যদের দ্বারা লিখিয়ে নিজের নামে প্রকাশ করেছেন। এ মতের কারণ হয়তো ভর্তৃহরি রাজা ছিলেন বলে। এরূপ প্রবাদ বা অপবাদ সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক কবির বেলায়ই প্রচলিত রয়েছে বলে জানা যায়। কিন্ত পণ্ডিত মহলে এ মত সমাদর লাভ করে নি। কাজেই সবকিছু বিবেচনায় পণ্ডিতদের তৃতীয় মত অর্থাৎ শতকত্রয় ভর্তৃহরির নিজের মৌলিক রচনা- এটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।
.
ভর্তৃহরির রচনাক্রম
ভর্তৃহরির শতকত্রয়ের মধ্যে কোনটি আগে এবং কোনটি পরে এ নিয়েও বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলেন প্রথমে নীতিশতক, তারপর শৃঙ্গারশতক এবং শেষে বৈরাগ্যশতক। কেউ এতে ভিন্নমত পোষণ করেন। তবে বৈরাগ্যশতক যে শেষে তা নিয়ে কারও দ্বিমত নেই, এবং সম্ভবত মতভেদের অবকাশও নেই। কারণ বৈরাগ্যের পর কারও জীবনে আর কিছু অর্থাৎ নীতি-অনীতি, শৃঙ্গার-প্রেম-কাম-ভালোবাসা বলতে কিছু থাকতে পারে না। তাছাড়া বৈরাগ্যশতকে কবির যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তাতে এটাই প্রতীত হয় যে, কবি ইতোমধ্যে নীতি বা সংসারনীতি এবং শৃঙ্গাররাজ্য অতিক্রম করে এসেছেন এবং সে-রাজ্যের অসারতা, বিশ্বাসহীনতা এবং আনন্দহীনতা তাঁকে পীড়িত করেছে। তাই বুঝি বৈরাগ্যশতকে নির্দ্বিধায় তিনি বলেন-
.
কাজেই এ থেকেই বুঝা যায় যে, বৈরাগ্যশতক শেষে অর্থাৎ কবির বৈরাগ্য অবলম্বনের পরেই রচিত হয়েছে। আর শৃঙ্গারশতক ও নীতিশতকের কোনটা আগে-পরের রচনা তা অনুমান করতে ভর্তৃহরির জনশ্রুত জীবন-চরিত বিশ্লেষণ করাই সঙ্গত। দেখা যায়- ভর্তৃহরি রাজা হওয়ার পরপরই রাজকার্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন থেকে সারাক্ষণই আকণ্ঠ সুরা আর নারীসম্ভোগে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর এই নারীসম্ভোগের অপূর্ব বর্ণনাই বিধৃত হয়েছে তাঁর শৃঙ্গারশতকে। এ বর্ণনা যে তাঁর স্বীয় অভিজ্ঞতারই ফল তা কাব্য-পাঠেই অনুধাবন করা যায়। শৃঙ্গারসাগরে সন্তরণ করতে করতে তিনি বলছেন-
.
শৃঙ্গার সম্পর্কে কবির এই নিখুঁত বর্ণনা যে জীবন-অভিজ্ঞতা ব্যতীত সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অন্য এক আকর্ষণীয় কিংবদন্তী অনুযায়ী, শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য ‘অমরুশতক’-এর রচয়িতাও (শংকরাচার্য) নাকি জনৈক মণ্ডনমিশ্রের বিদূষী পত্নী ভারতীর সঙ্গে একবার রতিবিষয়ক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে জনৈক মৃতরাজা অমরুর দেহ আশ্রয় করে তার অন্তঃপুরে যান এবং তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে বহুদিন যাপন করে রতিশাস্ত্রবিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে উক্ত মহিলাকে বিতর্কে পরাজিত করেন। রতিবিষয়ক তাঁর সেই জ্ঞানই ‘অমরুশতক’ নামে পরবর্তীকালে খ্যাতিলাভ করে। কবি ভর্তৃহরির বেলায়ও হয়তো তা-ই হয়েছিলো।
.
নারীর প্রতি তাঁর এই ঘৃণা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিতৃষ্ণা চরমে উঠে পত্নী অনঙ্গসেনার বিশ্বাসঘাতকতায়। তাই নীতিশতকের শুরুতেই তিনি বলেন-
এরপর সমগ্র নীতিশতকেই দেখি আমরা অন্য এক ভর্র্তৃহরিকে- যেন তিনি শৃঙ্গারশতকের কবি ভর্তৃহরি নন, সম্পূর্ণ অন্য এক ভর্তৃহরি। যেখানে তিনি শুধুই নীতির প্রচার করেছেন। নিজের মূর্খতা, অজ্ঞতা ও স্থূল বুদ্ধিবৃত্তির কুপরিণাম প্রচার এবং এসব হতে লোকে যাতে দূরে থাকে এবং আত্মমর্যাদা রক্ষা করে সবার শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে সংসারে টিকে থাকতে পারে, সেসব উপদেশ-নির্দেশনাই তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর নীতিশতকে। হয়তো আপন জীবনের শিক্ষা দিয়ে তিনি অপরের জীবন-চলার পথ সুগম করতে চেয়েছেন। তাই সংসারে টিকে থাকতে মানুষের করণীয় কী হবে তা সম্পর্কে বলেন-
শৃঙ্গারশতকে যাঁর সম্ভোগক্রিয়ার চমৎকার বিবরণ পরিলক্ষিত হয়, নীতিশতকে তারই মধ্যে দেখা যায় নীতিবোধের জাগরণ, নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা। শৃঙ্গারশতকেই নারীদের প্রতি কবির মোহাচ্ছন্নতা কেটে ক্রমে যে ঘৃণার বাষ্প দেখা দিয়েছিলো, নীতিশতকে দেখা যায় তা মেঘ হয়ে বৃষ্টিপাতের ফলে তাঁর মনকে ধুয়ে মুছে একেবারে পূত-পবিত্র করে দিয়েছে। এবং বৈরাগ্যশতকে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে সংসার ত্যাগ করেন। এই তিনটি কাব্যের মৌল চেতনার রূপান্তরের মধ্যেই মূলত স্রষ্টা ভর্তৃহরির ক্রমবিবর্তিত মানস-চেতনার স্বাক্ষরই সমুজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে।
.
ভর্তৃহরির নীতিশতক
ভর্তৃহরির রচনাশৈলী এমনিতেই অনুপম। তাঁর কাব্যে অর্থাৎ শ্লোকে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ খুবই অল্প দেখা যায়। এ কারণে তার ভাষা সহজ-সরল ও সর্বজনবোধ্য এবং ভাবগ্রাহীও। কাব্যের পরতে পরতে গভীর তাৎপর্য ব্যক্ত হয়েছে। বাক্য-গঠন সহজ ও স্বাভাবিক হলেও অর্থের দিক থেকে তা খুবই তাৎপর্যময় হওয়ায় ভর্তৃহরির শতকত্রয় বিশেষ করে নীতিশতক সকলেরই সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠেছে। মানবজীবনের বিচিত্র বিষয়ের যথার্থ চিত্রণ করতে গিয়ে ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের উপর তাঁর প্রশংসনীয় অধিকারের স্বাক্ষর তাঁর রচনাকে অনুপম সাহিত্যকর্মে পরিণত করেছে। সংস্কৃত শতককাব্যের জগতে তাই ভর্তৃহরির শতকত্রয় সর্বোচ্চ আসন দখল করে আছে বলে রসগ্রাহী পাঠকরা মনে করেন।
.
শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভাব ও বক্তব্যের ঐক্য বিবেচনায় ভর্তৃহরির নীতিশতকের শ্লোকসমূহকে দশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে যথাক্রমে- অজ্ঞনিন্দা (বা মূর্খপদ্ধতি), বিদ্বৎপদ্ধতি, মানশোর্যপদ্ধতি, অর্থপদ্ধতি, দুর্জনপদ্ধতি, সুজনপদ্ধতি, পরোপকারপদ্ধতি, ধৈর্যপদ্ধতি, দৈবপদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতি।
.
অজ্ঞনিন্দা বা মূর্খপদ্ধতি : মূর্খপদ্ধতির রচনাগুলিতে মূর্খদের সম্পর্কে কবির উপলব্ধি ও মতামত উপদেশাকারে বিধৃত হয়েছে। যেমন-
.
বিদ্বৎপদ্ধতি : এই বিদ্বৎপদ্ধতির রচনায় বিদ্যা ও বিদ্বানের সুখ্যাতি ও প্রশংসা ধ্বনিত হয়েছে। যেমন-
.
মানশৌর্যপদ্ধতি : আত্মগৌরবে যাঁরা গর্বিত এবং আত্মশক্তিতে যারা আস্থাবান তারা কোন কারণেই হীন কাজে উদ্যোগী হন না- এ উপলব্ধির সারাৎসারই এই মানশৌর্যপদ্ধতির রচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। যেমন-
.
অর্থপদ্ধতি : প্রচলিত সমাজে যে অর্থই সব কিছুর মূল, সেই অর্থের জয়গানই অর্থপদ্ধতির রচনায় প্রতিপাদ্য হয়েছে। কখনো হয়তো শ্লোকের অন্তর্গত সূক্ষ্ম কটাক্ষও ধরা পড়ে। যেমন-
.
দুর্জনপদ্ধতি : দুর্জন ব্যক্তি স্বভাবতই নির্দয় হয়ে থাকে। দুর্জনের দুর্জনত্ব কোন কারণের অপেক্ষা করে না। বিনা কারণেই তারা শত্রুতা করে। এ বিষয়ক রচনাই দুর্জনপদ্ধতির শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-
.
সুজনপদ্ধতি : সজ্জনের সমাদর সর্বত্র- সবাই তাঁদের শ্রদ্ধা করে। সজ্জনের গুণ ও প্রশংসাসূচক রচনাই সুজনপদ্ধতির প্রতিপাদ্য হয়েছে। যেমন-
.
পরোপকারপদ্ধতি : যারা পরোপকারী সজ্জন ব্যক্তি তাঁরা বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেও অবিনীত হন না, বিনয়ই যেন তাঁদের অঙ্গভূষণ। দয়া তাঁদের পরম ধর্ম। এ ধরনের প্রশস্তিই পরোপকারপদ্ধতির শ্লোকগুলিতে উক্ত হয়েছে। যেমন-
.
ধৈর্যপদ্ধতি : ধৈর্য মনস্বী ব্যক্তিদের প্রধান গুণ। অভীষ্ট বস্তু লাভ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ধৈর্য ত্যাগ করেন না। এই ধৈর্যগুণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ধৈর্যপদ্ধতির শ্লোকের অভীষ্ট হয়েছে। যেমন-
.
দৈবপদ্ধতি : দৈব মানুষের নিয়ন্ত্রক, রক্ষক। দৈবের কাছে পৌরুষ নিষ্ক্রিয়। এরকম অদৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দৈবপদ্ধতির শ্লোকগুলিতে অনুরণিত হতে দেখা যায়। যেমন-
.
কর্মপদ্ধতি : কর্মই সবচেয়ে শক্তিশালী, কারণ দেখা যায় বিধি মানুষকে যে ফল দান করে তার উপর বিধির কোন নিয়ন্ত্রণ নেই- কর্মের দ্বারাই তা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই কর্মই সবার শ্রেষ্ঠ। এই অনুধাবনই কর্মপদ্ধতির শ্লোকগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন-
.
ভর্তৃহরির নীতিশতকে এরকম অনেক শ্লোক আছে যা শুধু শুষ্ক নীতিকথাই প্রচার করছে না- বরং ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও অর্থ সমন্বয়ে সেগুলো সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের একেকটি অমূল্য রত্নরূপে পরিগণিত। আর এ কারণেই ভর্তৃহরির নীতিশতক সংস্কৃত সাহিত্য-জগতে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে আছে।
…
[ অনুসৃত সূত্রগ্রন্থ : ভর্তৃহরির নীতিশতক / দুলাল ভৌমিক / বাংলা একাডেমী ঢাকা, মার্চ ১৯৮৯ ]
প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ‘নীতিশাস্ত্রম’ নামে একটি বিভাগ স্বীকার করা হয়। যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়- নীতিশাস্ত্র। নামের মধ্যেই যেহেতু শাস্ত্র কথাটি যুক্ত রয়েছে, তার উপর আবার সংস্কৃত ভাষা, তাই ধারণা হয় নিশ্চয়ই এতে মারাত্মক সব জটিল তত্ত্বের সমাহারে ভয়ঙ্কর সব শাস্ত্রীয় কপচানিই থাকবে। এবং যার ফলে, এ বিষয়ে বিরাট পাণ্ডিত্য ধারণ করা না-গেলে এই শাস্ত্র উপভোগের শুরুতেই সহজ-সরল সাধারণ পাঠক-মনে প্রথম যে ইচ্ছেটাই গজিয়ে ওঠা স্বাভাবিক, তা হলো- থাক্ বাবা! এ রাস্তায় এগোনোর চাইতে পাথর চিবানোও বুঝি সহজ কর্ম ! ভাগ্যিস এগুলো আসলে সে জাতীয় ভয়ঙ্কর কিছু নয়। এবং এগুলো যে মোটেও রসকষহীন কিছু নয়, বরং অধিকাংশই মনোগ্রাহী কাব্যধর্মী রচনা, এর উদ্দেশ্য থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, এর উদ্দেশ্য হলো আকর্ষণীয় উপায়ে কিছু সদুপদেশ বিতরণ বা কাঙ্ক্ষিত কিছু নীতির প্রচার।
.
স্বভাবতই প্রশ্ন আসে- কিসের নীতি ? তা নির্ভর করে এই নীতিগুলোর রচয়িতা বা প্রচারকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সামাজিক অবস্থান এবং তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সামাজিক প্রয়োজনের উপর। সংস্কৃত সাহিত্যে এরকম বহু নীতিকাব্যের নাম জানা যায়। এক্ষেত্রে প্রথমেই যার নাম আসে তা হলো চাণক্যের নীতিশাস্ত্র। এরপরেই আসে ভর্তৃহরির শতকত্রয় (শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক এবং বৈরাগ্যশতক)। সুধীসমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এ ধরনের অন্যান্য নীতিমূলক কাব্যগুলো হচ্ছে- ভল্লটের শতক, সদানন্দের নীতিমালা, শম্ভুরাজের নীতিমঞ্জরী, বেঙ্কটরায়ের নীতিশতক, ঘটকর্পরের নীতিসার, স্বামী দয়ানন্দের নীতিচন্দ্রিকা, সুন্দরাচার্যের নীতিশতক, সোমদেবসূরির নীতিবাক্যামৃত, ব্রজরাজ শুক্লের নীতিবিলাস, বররুচির নামে প্রচলিত আর্যামঞ্জরী, অমরুর অমরুশতক, বাণভট্টের চণ্ডীশতক, ময়ূরের সূর্যশতক, শিহ্লনের শান্তিশতক, আনন্দবর্ধনের দেবীশতক, নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের সভারঞ্জকশতক ও অন্যোক্তিশতক, বল্লালসেনের বল্লালশতক, রামচন্দ্র কবিভারতীর ভক্তিশতক, বজ্রদত্তের লোকেশ্বরশতক ইত্যাদি। এসব গ্রন্থ বর্তমানে খুবই দুষ্প্রাপ্য বলে উদাহরণ হিসেবে শুধু নামগুলোই সংযুক্ত করা হলো।
.
তবে বর্তমান পাঠে আমাদের পর্যায়ক্রমিক আলোচনার সুবিধার্থে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার রচিত চাণক্যের নীতিশাস্ত্রকেই মূল অবলম্বন হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। বঙ্গানুবাদসহ সংস্কৃত মূল শ্লোকগুলোকে ব্যবহার করে এর উপর যথাসাধ্য আলোকপাতের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক বিষয়ানুক্রমে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের অন্যতম প্রধান সংস্কৃত কবি ভর্তৃহরির নীতিশতকের সবগুলো না হলেও যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় শ্লোকও উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্যে অন্যান্য সূত্রগ্রন্থের পাশাপাশি যে-দুটো ছোট্ট বইয়ের ব্যাপক সহযোগিতা নেয়ার কারণে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, সেই বই দুটো হলো- সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার কলকাতা থেকে প্রকাশিত শ্রী সত্যনারায়ণ চক্রবর্তীর ‘চাণক্য-নীতি-শাস্ত্র-সমীক্ষা’ এবং বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রকাশিত দুলাল ভৌমিকের ‘ভর্তৃহরির নীতিশতক’।
.
.
স্বভাবতই প্রশ্ন আসে- কিসের নীতি ? তা নির্ভর করে এই নীতিগুলোর রচয়িতা বা প্রচারকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সামাজিক অবস্থান এবং তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সামাজিক প্রয়োজনের উপর। সংস্কৃত সাহিত্যে এরকম বহু নীতিকাব্যের নাম জানা যায়। এক্ষেত্রে প্রথমেই যার নাম আসে তা হলো চাণক্যের নীতিশাস্ত্র। এরপরেই আসে ভর্তৃহরির শতকত্রয় (শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক এবং বৈরাগ্যশতক)। সুধীসমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এ ধরনের অন্যান্য নীতিমূলক কাব্যগুলো হচ্ছে- ভল্লটের শতক, সদানন্দের নীতিমালা, শম্ভুরাজের নীতিমঞ্জরী, বেঙ্কটরায়ের নীতিশতক, ঘটকর্পরের নীতিসার, স্বামী দয়ানন্দের নীতিচন্দ্রিকা, সুন্দরাচার্যের নীতিশতক, সোমদেবসূরির নীতিবাক্যামৃত, ব্রজরাজ শুক্লের নীতিবিলাস, বররুচির নামে প্রচলিত আর্যামঞ্জরী, অমরুর অমরুশতক, বাণভট্টের চণ্ডীশতক, ময়ূরের সূর্যশতক, শিহ্লনের শান্তিশতক, আনন্দবর্ধনের দেবীশতক, নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের সভারঞ্জকশতক ও অন্যোক্তিশতক, বল্লালসেনের বল্লালশতক, রামচন্দ্র কবিভারতীর ভক্তিশতক, বজ্রদত্তের লোকেশ্বরশতক ইত্যাদি। এসব গ্রন্থ বর্তমানে খুবই দুষ্প্রাপ্য বলে উদাহরণ হিসেবে শুধু নামগুলোই সংযুক্ত করা হলো।
.
তবে বর্তমান পাঠে আমাদের পর্যায়ক্রমিক আলোচনার সুবিধার্থে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার রচিত চাণক্যের নীতিশাস্ত্রকেই মূল অবলম্বন হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। বঙ্গানুবাদসহ সংস্কৃত মূল শ্লোকগুলোকে ব্যবহার করে এর উপর যথাসাধ্য আলোকপাতের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক বিষয়ানুক্রমে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের অন্যতম প্রধান সংস্কৃত কবি ভর্তৃহরির নীতিশতকের সবগুলো না হলেও যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় শ্লোকও উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্যে অন্যান্য সূত্রগ্রন্থের পাশাপাশি যে-দুটো ছোট্ট বইয়ের ব্যাপক সহযোগিতা নেয়ার কারণে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, সেই বই দুটো হলো- সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার কলকাতা থেকে প্রকাশিত শ্রী সত্যনারায়ণ চক্রবর্তীর ‘চাণক্য-নীতি-শাস্ত্র-সমীক্ষা’ এবং বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রকাশিত দুলাল ভৌমিকের ‘ভর্তৃহরির নীতিশতক’।
.
সংস্কৃত সাহিত্য
আমাদের বর্তমান আলোচনা সংস্কৃত কাব্যের কোনরূপ সাহিত্য বিচার বা পর্যালোচনা না হলেও প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপিতব্য প্রাচীন জ্ঞানের বিষয় আস্বাদনের সুবিধার্থে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের সামান্য দুয়েকটা লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য জেনে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধ করি।
.
তার আগে বলে নেয়া ভালো, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্য হচ্ছে সংস্কৃত। বেদ থেকে শুরু করে রামায়ণ মহাভারতের কবিগণ এবং কালিদাসের মতো সংস্কৃত সাহিত্যের কবিশ্রেষ্ঠগণ সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারকে অমূল্য রত্নরাজিতে পূর্ণ করে গেছেন। কিন্তু এতো কিছু দিলেও আরেকটা যে অনুচিত কাজ করে গেছেন তাঁরা, উত্তরসূরীদের কাছে নিজেদেরকে রেখে গেছেন গোপন করে। কেননা অধিকাংশ কবিরই জীবন-চরিত আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গেছে এজন্যেই যে, আমরা জানি না তাঁদের সঠিক পিতৃ-মাতৃ পরিচয়, বংশ বা জন্মস্থানের কথা। এমনকি তাঁরা কেউ কেউ তাঁদের রচনার পাতায় নিজের নামটিও উহ্য রেখেছেন। ফলে অজ্ঞাত পরিচয় রচনাকর্মের স্রষ্টা নির্ধারণেই দূরপনেয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। একারণে অধিকাংশ কবির বেলাতেই সৃষ্টি হয়েছে একের পর এক জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীর। কারো কারো পরিচয় উদ্ধার করতে এসব জনশ্রুতিকেই একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। ফলে নিশ্চয় করে কোন তথ্যকেই অভ্রান্ত হিসেবে মেনে নিয়ে যেমন সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় না, তেমনি অবহেলা করারও উপায় থাকে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের এটাও বোধ করি একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। এ দায় মাথায় নিয়েই এই কবিশ্রেষ্টদের সম্পর্কে কোন তথ্য উপস্থাপন করতে হয় বৈকি।
.
সে যাক্, সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যকে প্রথমতঃ দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে- দৃশ্যকাব্য এবং শ্রব্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য হলো দেখার উপযোগী নাটক বা নাটক জাতীয় রচনা যা অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের দেখানো যায়। আর শ্রব্যকাব্য শোনার উপযোগী যা কেবল পাঠের দ্বারা শ্রোতাদের শোনানো যায়, কিন্তু অভিনয় করে দেখানো যায় না।
.
শ্রব্যকাব্য আবার তিন ভাগে বিভক্ত- গদ্যকাব্য, পদ্যকাব্য ও চম্পূকাব্য। গদ্যকাব্য গদ্যে রচিত। যা ‘কথা’ ও ‘আখ্যায়িকা’ এই দুই প্রকার। এদের পার্থক্য মূলত বিষয়বস্তুতে। ‘কথা’ হলো কবিকল্পিত বা কল্পনাশ্রয়ী রচনা, এবং ‘আখ্যায়িকা’র কাহিনী হবে ঐতিহাসিক বা বস্তুনিষ্ঠ। অন্যদিকে পদ্যকাব্য পদ্যে রচিত। আর গদ্য-পদ্য মিশ্রিত কাব্যকে বলা হয় চম্পূকাব্য।
.
পদ্যকাব্যের আবার তিনটি ভাগ- মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং গীতিকাব্য। লোকপ্রসিদ্ধ, ঐতিহাসিক মহাপুরুষ কিংবা কোন দেব-দেবীর কাহিনী নিয়ে আটের অধিক সর্গে রচিত বিশাল কাব্যই মহাকাব্য। এতে মানবজীবনের একটি পূর্ণ চিত্র প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে খণ্ডকাব্য এর বিপরীত। যেখানে ধর্ম, নীতি, প্রেম, বিরহ ইত্যাদি যে-কোন বিষয়ে মানবজীবনের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র অঙ্কিত হয়। আর গীতিধর্মী রচনাশৈলীর যে কাব্য গীত হবার যোগ্য তা-ই গীতিকাব্য।
.
গীতিকাব্যের দুটো ভাগ- প্রবন্ধকাব্য এবং মুক্তককাব্য বা কোষকাব্য। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু সম্বলিত পরস্পর-সাপেক্ষ শ্লোকসমূহকে বলে প্রবন্ধকাব্য। অর্থ প্রকাশের দিক থেকে প্রবন্ধকাব্যের শ্লোকগুলো পরস্পর-নিরপেক্ষ হবার সুযোগ নেই। অন্যদিকে মুক্তককাব্য বা কোষকাব্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থ প্রকাশের দিক থেকে প্রতিটি শ্লোকই পরস্পর নিরপেক্ষ। প্রত্যেক শ্লোকই স্বতন্ত্র, বিশেষ ভাবনার বাহক।
.
তার আগে বলে নেয়া ভালো, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্য হচ্ছে সংস্কৃত। বেদ থেকে শুরু করে রামায়ণ মহাভারতের কবিগণ এবং কালিদাসের মতো সংস্কৃত সাহিত্যের কবিশ্রেষ্ঠগণ সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারকে অমূল্য রত্নরাজিতে পূর্ণ করে গেছেন। কিন্তু এতো কিছু দিলেও আরেকটা যে অনুচিত কাজ করে গেছেন তাঁরা, উত্তরসূরীদের কাছে নিজেদেরকে রেখে গেছেন গোপন করে। কেননা অধিকাংশ কবিরই জীবন-চরিত আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গেছে এজন্যেই যে, আমরা জানি না তাঁদের সঠিক পিতৃ-মাতৃ পরিচয়, বংশ বা জন্মস্থানের কথা। এমনকি তাঁরা কেউ কেউ তাঁদের রচনার পাতায় নিজের নামটিও উহ্য রেখেছেন। ফলে অজ্ঞাত পরিচয় রচনাকর্মের স্রষ্টা নির্ধারণেই দূরপনেয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। একারণে অধিকাংশ কবির বেলাতেই সৃষ্টি হয়েছে একের পর এক জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীর। কারো কারো পরিচয় উদ্ধার করতে এসব জনশ্রুতিকেই একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। ফলে নিশ্চয় করে কোন তথ্যকেই অভ্রান্ত হিসেবে মেনে নিয়ে যেমন সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় না, তেমনি অবহেলা করারও উপায় থাকে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের এটাও বোধ করি একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। এ দায় মাথায় নিয়েই এই কবিশ্রেষ্টদের সম্পর্কে কোন তথ্য উপস্থাপন করতে হয় বৈকি।
.
সে যাক্, সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যকে প্রথমতঃ দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে- দৃশ্যকাব্য এবং শ্রব্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য হলো দেখার উপযোগী নাটক বা নাটক জাতীয় রচনা যা অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের দেখানো যায়। আর শ্রব্যকাব্য শোনার উপযোগী যা কেবল পাঠের দ্বারা শ্রোতাদের শোনানো যায়, কিন্তু অভিনয় করে দেখানো যায় না।
.
শ্রব্যকাব্য আবার তিন ভাগে বিভক্ত- গদ্যকাব্য, পদ্যকাব্য ও চম্পূকাব্য। গদ্যকাব্য গদ্যে রচিত। যা ‘কথা’ ও ‘আখ্যায়িকা’ এই দুই প্রকার। এদের পার্থক্য মূলত বিষয়বস্তুতে। ‘কথা’ হলো কবিকল্পিত বা কল্পনাশ্রয়ী রচনা, এবং ‘আখ্যায়িকা’র কাহিনী হবে ঐতিহাসিক বা বস্তুনিষ্ঠ। অন্যদিকে পদ্যকাব্য পদ্যে রচিত। আর গদ্য-পদ্য মিশ্রিত কাব্যকে বলা হয় চম্পূকাব্য।
.
পদ্যকাব্যের আবার তিনটি ভাগ- মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং গীতিকাব্য। লোকপ্রসিদ্ধ, ঐতিহাসিক মহাপুরুষ কিংবা কোন দেব-দেবীর কাহিনী নিয়ে আটের অধিক সর্গে রচিত বিশাল কাব্যই মহাকাব্য। এতে মানবজীবনের একটি পূর্ণ চিত্র প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে খণ্ডকাব্য এর বিপরীত। যেখানে ধর্ম, নীতি, প্রেম, বিরহ ইত্যাদি যে-কোন বিষয়ে মানবজীবনের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র অঙ্কিত হয়। আর গীতিধর্মী রচনাশৈলীর যে কাব্য গীত হবার যোগ্য তা-ই গীতিকাব্য।
.
গীতিকাব্যের দুটো ভাগ- প্রবন্ধকাব্য এবং মুক্তককাব্য বা কোষকাব্য। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু সম্বলিত পরস্পর-সাপেক্ষ শ্লোকসমূহকে বলে প্রবন্ধকাব্য। অর্থ প্রকাশের দিক থেকে প্রবন্ধকাব্যের শ্লোকগুলো পরস্পর-নিরপেক্ষ হবার সুযোগ নেই। অন্যদিকে মুক্তককাব্য বা কোষকাব্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থ প্রকাশের দিক থেকে প্রতিটি শ্লোকই পরস্পর নিরপেক্ষ। প্রত্যেক শ্লোকই স্বতন্ত্র, বিশেষ ভাবনার বাহক।
.
জীবন চলার পথে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে কোষকাব্যশৈলীর এধরনের শ্লোক-সংকলন প্রয়োজনীয় নির্দেশনার কাজ করে। এগুলো সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য রত্নবিশেষ। কোন কোন সংকলন বিভিন্ন কবির কাব্য বা নাটকের বা যেকোন সাহিত্যকীর্তির উদ্ধৃতিমাত্র অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। আবার লৌকিক প্রবাদ-বাক্যকে সম্বল করেও মনোরম শ্লোক রচিত হয়েছে, যার উদাহরণ ‘ভর্তৃহরির নীতিশতক’। অথবা কেবলমাত্র উপদেশমালা নিয়েও এরকম সুভাষিতসংগ্রহ রচিত হয়েছে। ‘চাণক্য-নীতিশাস্ত্র’ সেরকমই উপদেশমালা বিশেষ।
.
যেহেতু নীতিমূলক শাস্ত্র বা কাব্য রচনায় রচয়িতার সমকালীনতাই মূল অনুসঙ্গ হয়ে থাকে, তাই রচয়িতার উৎস-সন্ধানের মধ্য দিয়ে সেকালের সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলেই এই নীতিশাস্ত্রগুলোর প্রকৃত উপযোগিতাটুকু উপলব্ধি করা সহজ হতে পারে। তাছাড়া সভ্যতার ক্রমবিবর্তিত ধারায় কয়েক হাজার বছর পেরিয়ে একালে এসেও বহু নীতিবচন যেভাবে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মিলেমিশে কখনো পূর্বের অবয়বে কখনো বা নতুন অবয়বে সমকালীন উপযোগিতায় জ্বলজ্বল করছে, তাতে করে এই নীতিবচনগুলো থেকে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির একটি ধারাবাহিক চারুপাঠ করে ফেলাও অসম্ভব নয় বলে মনে হয়। সেই চারুপাঠে প্রবেশের আগে সংশ্লিষ্ট সময়কালটাকে উপলব্ধির প্রয়োজনে আমাদের আলোচ্য ওই নীতিকাব্য স্রষ্টাদের পরিচয়টা অন্তত একটু খুঁজে নিতে পারি।
জীবন চলার পথে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে কোষকাব্যশৈলীর এধরনের শ্লোক-সংকলন প্রয়োজনীয় নির্দেশনার কাজ করে। এগুলো সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য রত্নবিশেষ। কোন কোন সংকলন বিভিন্ন কবির কাব্য বা নাটকের বা যেকোন সাহিত্যকীর্তির উদ্ধৃতিমাত্র অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। আবার লৌকিক প্রবাদ-বাক্যকে সম্বল করেও মনোরম শ্লোক রচিত হয়েছে, যার উদাহরণ ‘ভর্তৃহরির নীতিশতক’। অথবা কেবলমাত্র উপদেশমালা নিয়েও এরকম সুভাষিতসংগ্রহ রচিত হয়েছে। ‘চাণক্য-নীতিশাস্ত্র’ সেরকমই উপদেশমালা বিশেষ।
.
যেহেতু নীতিমূলক শাস্ত্র বা কাব্য রচনায় রচয়িতার সমকালীনতাই মূল অনুসঙ্গ হয়ে থাকে, তাই রচয়িতার উৎস-সন্ধানের মধ্য দিয়ে সেকালের সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলেই এই নীতিশাস্ত্রগুলোর প্রকৃত উপযোগিতাটুকু উপলব্ধি করা সহজ হতে পারে। তাছাড়া সভ্যতার ক্রমবিবর্তিত ধারায় কয়েক হাজার বছর পেরিয়ে একালে এসেও বহু নীতিবচন যেভাবে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মিলেমিশে কখনো পূর্বের অবয়বে কখনো বা নতুন অবয়বে সমকালীন উপযোগিতায় জ্বলজ্বল করছে, তাতে করে এই নীতিবচনগুলো থেকে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির একটি ধারাবাহিক চারুপাঠ করে ফেলাও অসম্ভব নয় বলে মনে হয়। সেই চারুপাঠে প্রবেশের আগে সংশ্লিষ্ট সময়কালটাকে উপলব্ধির প্রয়োজনে আমাদের আলোচ্য ওই নীতিকাব্য স্রষ্টাদের পরিচয়টা অন্তত একটু খুঁজে নিতে পারি।
বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।। ০১।। (চাণক্য নীতিশাস্ত্র)।
অর্থাৎ : বিদ্যাবত্তা এবং রাজপদ কখনোই সমান হয় না। রাজা কেবলমাত্র নিজ রাজ্যেই সম্মান পান, বিদ্বান (স্বদেশ-বিদেশ) সর্বত্র সম্মান পান।
.
চাণক্য নীতিশাস্ত্রের প্রথম শ্লোক এটি। শ্লোকটির বহুল ব্যবহৃত দ্বিতীয় চরণটা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত মনে হওয়ার কথা। কারণ, ‘স্বদেশে পূজিত রাজা, বিদ্বান সর্বত্র’- এরকম একটা ভাবসম্প্রসারণের বিষয় মাধ্যমিক ক্লাসের জন্য যথার্থই বলা চলে। এবং মজার বিষয় হলো, এরকম একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে বসলে আমরা যে-যত বিদ্যাদিগ্গজই হয়ে উঠি না কেন, বিশেষ ব্যতিক্রম বাদ দিলে, আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ের জ্ঞানটাই খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে আমাদের নির্দ্বিধ ব্যাখ্যাটা এগিয়ে যেতে থাকবে এভাবে- বিদ্বানের সম্মান সর্বত্রই। নিজের দেশে বিদ্বান ও রাজা দুজনেই সম্মান ও মর্যাদা পেলেও বিদ্বানের সম্মান কিন্তু নিজ দেশের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। রাজা স্বদেশে ক্ষমতা ও আধিপত্যের জোরে যে সম্মান আদায় করে নেন, বিদেশে এই সম্মান না-ও পেতে পারেন। এখানেই বিদ্বান ও রাজার মধ্যে পার্থক্য এবং ইত্যাদি ইত্যাদি…।
.
কেন ? নিরবচ্ছিন্ন কথার মাঝখানে এরকম দুর্মুখের মতো ছোট্ট একটা প্রশ্ন আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ের জ্ঞানস্রোতকে মুহূর্তের জন্যে থমকে দেয়াটা অসম্ভব নয়। কিঞ্চিৎ বিরক্তি নিয়েই এর উত্তর দেয়ার একটা চেষ্টা করবো নিশ্চয়ই। হয়তো এভাবেই বলবো তখন- যিনি সম্যক বিদ্যা অর্জন করেন তিনিই বিদ্বান। যেহেতু বিদ্যা সকল দেশেই প্রার্থিত, তাই বিদ্যার সম্মান সর্বত্রই রয়েছে। কিন্তু রাজা হলেই যে তিনি বিদ্বান হবেন এমন তো কথা নেই ! অতএব রাজা এবং বিদ্বানের মধ্যে পার্থক্য তো একটা রয়েছেই !
.
একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে, আমাদের চিন্তাস্রোত কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায় ছেড়ে আরেকটু উপরের দিকে উড্ডীন হয়ে গেছে। এবং এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে তখনই যখন মূর্খের মতো আরেকটা বেয়ারা প্রশ্ন এসে খাড়ার মতো সামনে দাঁড়িয়ে যাবে- বিদ্যা কী ? তাই তো ! পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে জুতসই উত্তর লিখার জন্য কয়েক গাদা বইয়ের পাতা মুখস্ত করাই কি বিদ্যা ? কিন্তু তা কেন হবে ! তাহলে বিদ্যা কি বড় বড় কিছু সনদ বা প্রশংসাপত্র ? তাও নিশ্চয়ই নয়। তাহলে কী ? ফাঁক গলে কেউ হয়তো এরকম একটা উত্তর নিয়ে হাজির হয়ে যেতে পারেন যে- কোনো বিষয়ে বিশেষ যে জ্ঞান তা-ই বিদ্যা। কিন্তু এতেও কি স্থির থাকার উপায় আছে ? প্রশ্নের সমস্যাটাই হলো একবার শুরু হয়ে গেলে তা থামানো মোটেও সহজ হয় না। কোন্ বিষয়ে জ্ঞান, কী ধরনের জ্ঞান, কেন এ জ্ঞান, এ জ্ঞান কোন্ পর্যায়ে আহরিত হলে তাকে বিদ্যা বলা হবে, কেন এ বিদ্যাকে সর্বত্র পূজিত হতে হবে, এ বিদ্যা কি চিরায়ত ? ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচুর ডালপালা বিস্তৃত হতেই থাকবে যতক্ষণ না তাকে একটা সন্তোষজনক সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা যায়। এবং এখানেও সন্দেহ, আদৌ কি কোনো সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা সম্ভব ?
.
ফাঁকতালে আরেকটা কথা বলে রাখা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এককালে জ্যোতিষশাস্ত্র নামক ভয়ানক গুরুত্ববহ একটা বিদ্যাকে একালের আলোকে মুক্তচিন্তক জ্ঞানপিপাসুরা সম্পূর্ণ প্রতারণা ও ভাওতাবাজিপূর্ণ একটি অপবিদ্যা হিসেবেই চিহ্নিত করেন। অতএব যুগে যুগে বিদ্বান বা জ্ঞানীর সংজ্ঞাতেও যে এরকম অনেক মোহন হেঁয়ালির বিভ্রম মিশে থাকতে পারে, সেদিকেও সতর্ক থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না কখনোই।
.
তাহলে শুরুতেই আমরা যে নীতিবাক্যটিকে আমাদের জটিলতামুক্ত ভাবনায় স্রেফ সহজ সরল একটা মনোরম বাক্য বলেই ধরে নিয়েছিলাম, আদতে কি তা ? আর কূটতর্ক জুড়ে গেলে আসলে কোন কিছুই যে জটিলতামুক্ত থাকে না, সেটাও ভাবনার বিষয়। তবে এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উদ্ধৃত শ্লোকটি শুধুমাত্র একটি বচনই নয়। মানবসভ্যতার প্রাচীন জ্ঞানজগতের এক অসামান্য প্রতিভাধর বিদ্বান ও প্রাজ্ঞ দার্শনিক কৌটিল্য তথা চাণক্যের নীতিশাস্ত্রের অন্যতম শ্লোক এটি। এরকম অনেকগুলো শ্লোকের সমাহার হলো সেই নীতিশাস্ত্র, প্রায় আড়াইহাজার বছর পেরিয়ে এসেও আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতায় অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে যার অতুলনীয় অবদান। কী এমন আশ্চর্য জারকরস নিহিত এসব শ্লোকের মধ্যে, তা উপলব্ধিরও বিষয় বৈ কি। অন্তত পরবর্তী শ্লোকগুলোর যথার্থ মাহাত্ম্য অনুধাবনের প্রয়োজনেই এ পর্যায়ে প্রাথমিক কিছু সুলুকসন্ধান করা অনুচিত হবে না বোধ করি।
.
আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, নীতিবাক্যের উদ্দেশ্য হলো আকর্ষণীয় উপায়ে কিছু উপদেশ বিতরণ বা নীতির প্রচার। আর তা নির্ভর করে এই নীতিগুলোর রচয়িতা বা প্রচারকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সামাজিক অবস্থান এবং তৎকালীন প্রেক্ষাপটের উপর। কোন প্রক্ষিপ্ত সংযুক্তি না হয়ে প্রকৃতই এটা যদি চাণক্যের শ্লোক হয়ে থাকে, তাহলে চাণক্যের অধিষ্ঠানকাল বিবেচনায় শ্লোকটির রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকই বলতে হবে। তখনকার সামাজিক আবহটা কী ছিলো তবে ?
.
ধর্মীয় বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল আধিপত্যের যাতাকলে পিষ্ট তৎকালীন সমাজ তখন খণ্ড-বিখণ্ডে বিভাজিত। একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের স্বঘোষিত মুখপাত্র উচ্চবর্ণীয় আর্য ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সম্প্রদায়ের হাতে শাসনদণ্ড, অন্যদিকে সমাজের সরাসরি উৎপাদন-সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর সাধারণ জনগোষ্ঠী যাদেরকে শুধু অনার্য বানিয়েই ক্ষান্ত হতে পারেনি এরা, তথাকথিত এক স্রষ্টা ব্রহ্মার আজগুবি গল্প ফেঁদে কাল্পনিক পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ধর্মীয় দোহাই তোলে সুকৌশলে তাদেরকে নিম্নবর্গীয় শূদ্র বানিয়ে রাখা হয়েছে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত করে আক্ষরিক অর্থেই ভয়ঙ্কর এক ক্রিতদাস্যের শৃঙ্খলে। এবং এরা যাতে কখনোই একাট্টা বিদ্রোহী হয়ে এই অপশাসন-ব্যবস্থার জন্যে হুমকী হয়ে উঠতে না পারে সে লক্ষ্যে এই ব্রাত্য জনগোষ্ঠীকে আরো অনেক অনেক সামাজিক বিভাজনে পরস্পর বিভাজিত করে ভেঙে দিতে চেয়েছে তাদের মেরুদণ্ডের সবকটা কশেরুকা। আর এই ধর্মবাদী নিরঙ্কুশ শাসন নির্বিঘ্নে পরিচালনার লক্ষ্যে উপনিষদীয় ঋষি-ব্রাহ্মণদের হাতে রচিত হয়ে গেছে বেশ কিছু মোহনীয় শাস্ত্র, দর্শন এবং এর ভূরিভূরি ভাববাদী ব্যাখ্যাও। আর নিকৃষ্ট শূদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ রয়েছে সকল ধরনের বিদ্যার্জন, শাস্ত্রপাঠ বা জ্ঞান অর্জনের যেকোন নগন্য সুযোগও। কেননা এরা এই সুযোগ পেলে বুঝে যাবে শাস্ত্রীয় ভণ্ডামির ফোকর-ফাকর, তছনছ হয়ে যাবে এতোকালের পরনির্ভরশীলতায় গড়ে তোলা যথেচ্ছ ভোগের অবারিত সাম্রাজ্য-সৌধ।
.
কিন্তু তাতেও কি নিরাপদ থেকেছে তারা ? খুব স্বাভাবিকভাবেই শ্রমে-ঘামে ভেজা ব্রাত্য জনগোষ্ঠী কখনোই মেনে নিতে চায়নি তা। তারা তাদের জীবনচর্চার প্রত্যক্ষ উপাদান লোকায়ত আচার-বিচারকে অবলম্বন করেই গড়ে তুলেছে এক অন্যরকম বিদ্রোহের দেয়াল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভণ্ডামির অন্তঃসারশূন্যতাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সৃষ্টি করেছে এক প্রতিবাদী দর্শন- যার নাম লোকায়ত দর্শন। মাটির সন্তান বলেই মৃত্তিকার রসসিঞ্চিত প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিতে এরা পরাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাওতাবাজির সমস্ত কাল্পনিক উৎসকে সরাসরি অস্বীকার করে লোকায়ত চার্বাক দর্শনের নামে যুক্তির যে ধারালো বল্লম তুলে নিয়েছে হাতে, তা যে আর হেলাফেলার নয়, বড় শক্ত ভিতের উপর দাঁড়ানো, তা বুঝতে একটুও দেরি হয়নি ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্র, ধর্ম, দর্শনেও এসেছে নতুন ঢাল। তাদের চোখে সেই লোকায়তিকরা হয়েছে নাস্তিক, কারণ ওরা বেদ মানে না। প্রত্যক্ষের বাইরে কোন কিছুই বিশ্বাস করে না ওরা, তাই ব্রাহ্মণ্যবাদের চোখে ওদের শানিত যুক্তি চিহ্নিত হয়েছে হেতুবিদ্যা বা অসৎ-তর্ক নামে।
.
এখন প্রশ্ন আসে, যুক্তির ধারে শানিত এই হেতুবিদ্যা কি প্রকৃতই কোন অজ্ঞ শাস্ত্রবিমুখ মূর্খের দ্বারা সৃষ্ট হওয়া সম্ভব ছিলো ? ব্রাহ্মণের অষ্টপ্রহর সেবায় নিয়োজিত আক্ষরিক গাধার মতো খেটে যাওয়া কোনরূপ শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগহীন ক্রিতদাস শূদ্রদের দ্বারা নিশ্চয়ই এরকম সুশিক্ষিত উচ্চকোটির শাস্ত্র রচিত হওয়া সম্ভব ছিলো না। অর্থাৎ যে কোন অবস্থান থেকেই যুগে যুগে মানবদরদী মানবতাবাদী মুক্তচিন্তক কিছু মানুষের উত্থান সর্বকালেই হয়েছে যাঁরা মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন সবকিছু তুচ্ছ করে কেবলই মানবজন্মের দায়ভার কাঁধে নিয়ে। তাঁদের শরীরেও মাটির সোঁদা গন্ধই ছিলো নিশ্চয়ই। প্রাথমিক চার্বাকরা সেই বিরল গোত্রেরই মানুষ। অন্য দৃষ্টিতে তাঁদেরকে বার্হষ্পত্যও বলা হয়। এরা নাস্তিক। নইলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সকল শাস্ত্রের সাংবিধানিক আকরগ্রন্থ ‘মনুসংহিতা’য় কেন স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে এভাবে-
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।। ০১।। (চাণক্য নীতিশাস্ত্র)।
অর্থাৎ : বিদ্যাবত্তা এবং রাজপদ কখনোই সমান হয় না। রাজা কেবলমাত্র নিজ রাজ্যেই সম্মান পান, বিদ্বান (স্বদেশ-বিদেশ) সর্বত্র সম্মান পান।
.
চাণক্য নীতিশাস্ত্রের প্রথম শ্লোক এটি। শ্লোকটির বহুল ব্যবহৃত দ্বিতীয় চরণটা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত মনে হওয়ার কথা। কারণ, ‘স্বদেশে পূজিত রাজা, বিদ্বান সর্বত্র’- এরকম একটা ভাবসম্প্রসারণের বিষয় মাধ্যমিক ক্লাসের জন্য যথার্থই বলা চলে। এবং মজার বিষয় হলো, এরকম একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে বসলে আমরা যে-যত বিদ্যাদিগ্গজই হয়ে উঠি না কেন, বিশেষ ব্যতিক্রম বাদ দিলে, আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ের জ্ঞানটাই খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে আমাদের নির্দ্বিধ ব্যাখ্যাটা এগিয়ে যেতে থাকবে এভাবে- বিদ্বানের সম্মান সর্বত্রই। নিজের দেশে বিদ্বান ও রাজা দুজনেই সম্মান ও মর্যাদা পেলেও বিদ্বানের সম্মান কিন্তু নিজ দেশের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। রাজা স্বদেশে ক্ষমতা ও আধিপত্যের জোরে যে সম্মান আদায় করে নেন, বিদেশে এই সম্মান না-ও পেতে পারেন। এখানেই বিদ্বান ও রাজার মধ্যে পার্থক্য এবং ইত্যাদি ইত্যাদি…।
.
কেন ? নিরবচ্ছিন্ন কথার মাঝখানে এরকম দুর্মুখের মতো ছোট্ট একটা প্রশ্ন আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ের জ্ঞানস্রোতকে মুহূর্তের জন্যে থমকে দেয়াটা অসম্ভব নয়। কিঞ্চিৎ বিরক্তি নিয়েই এর উত্তর দেয়ার একটা চেষ্টা করবো নিশ্চয়ই। হয়তো এভাবেই বলবো তখন- যিনি সম্যক বিদ্যা অর্জন করেন তিনিই বিদ্বান। যেহেতু বিদ্যা সকল দেশেই প্রার্থিত, তাই বিদ্যার সম্মান সর্বত্রই রয়েছে। কিন্তু রাজা হলেই যে তিনি বিদ্বান হবেন এমন তো কথা নেই ! অতএব রাজা এবং বিদ্বানের মধ্যে পার্থক্য তো একটা রয়েছেই !
.
একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে, আমাদের চিন্তাস্রোত কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায় ছেড়ে আরেকটু উপরের দিকে উড্ডীন হয়ে গেছে। এবং এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে তখনই যখন মূর্খের মতো আরেকটা বেয়ারা প্রশ্ন এসে খাড়ার মতো সামনে দাঁড়িয়ে যাবে- বিদ্যা কী ? তাই তো ! পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে জুতসই উত্তর লিখার জন্য কয়েক গাদা বইয়ের পাতা মুখস্ত করাই কি বিদ্যা ? কিন্তু তা কেন হবে ! তাহলে বিদ্যা কি বড় বড় কিছু সনদ বা প্রশংসাপত্র ? তাও নিশ্চয়ই নয়। তাহলে কী ? ফাঁক গলে কেউ হয়তো এরকম একটা উত্তর নিয়ে হাজির হয়ে যেতে পারেন যে- কোনো বিষয়ে বিশেষ যে জ্ঞান তা-ই বিদ্যা। কিন্তু এতেও কি স্থির থাকার উপায় আছে ? প্রশ্নের সমস্যাটাই হলো একবার শুরু হয়ে গেলে তা থামানো মোটেও সহজ হয় না। কোন্ বিষয়ে জ্ঞান, কী ধরনের জ্ঞান, কেন এ জ্ঞান, এ জ্ঞান কোন্ পর্যায়ে আহরিত হলে তাকে বিদ্যা বলা হবে, কেন এ বিদ্যাকে সর্বত্র পূজিত হতে হবে, এ বিদ্যা কি চিরায়ত ? ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচুর ডালপালা বিস্তৃত হতেই থাকবে যতক্ষণ না তাকে একটা সন্তোষজনক সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা যায়। এবং এখানেও সন্দেহ, আদৌ কি কোনো সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা সম্ভব ?
.
ফাঁকতালে আরেকটা কথা বলে রাখা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এককালে জ্যোতিষশাস্ত্র নামক ভয়ানক গুরুত্ববহ একটা বিদ্যাকে একালের আলোকে মুক্তচিন্তক জ্ঞানপিপাসুরা সম্পূর্ণ প্রতারণা ও ভাওতাবাজিপূর্ণ একটি অপবিদ্যা হিসেবেই চিহ্নিত করেন। অতএব যুগে যুগে বিদ্বান বা জ্ঞানীর সংজ্ঞাতেও যে এরকম অনেক মোহন হেঁয়ালির বিভ্রম মিশে থাকতে পারে, সেদিকেও সতর্ক থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না কখনোই।
.
তাহলে শুরুতেই আমরা যে নীতিবাক্যটিকে আমাদের জটিলতামুক্ত ভাবনায় স্রেফ সহজ সরল একটা মনোরম বাক্য বলেই ধরে নিয়েছিলাম, আদতে কি তা ? আর কূটতর্ক জুড়ে গেলে আসলে কোন কিছুই যে জটিলতামুক্ত থাকে না, সেটাও ভাবনার বিষয়। তবে এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উদ্ধৃত শ্লোকটি শুধুমাত্র একটি বচনই নয়। মানবসভ্যতার প্রাচীন জ্ঞানজগতের এক অসামান্য প্রতিভাধর বিদ্বান ও প্রাজ্ঞ দার্শনিক কৌটিল্য তথা চাণক্যের নীতিশাস্ত্রের অন্যতম শ্লোক এটি। এরকম অনেকগুলো শ্লোকের সমাহার হলো সেই নীতিশাস্ত্র, প্রায় আড়াইহাজার বছর পেরিয়ে এসেও আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতায় অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে যার অতুলনীয় অবদান। কী এমন আশ্চর্য জারকরস নিহিত এসব শ্লোকের মধ্যে, তা উপলব্ধিরও বিষয় বৈ কি। অন্তত পরবর্তী শ্লোকগুলোর যথার্থ মাহাত্ম্য অনুধাবনের প্রয়োজনেই এ পর্যায়ে প্রাথমিক কিছু সুলুকসন্ধান করা অনুচিত হবে না বোধ করি।
.
আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, নীতিবাক্যের উদ্দেশ্য হলো আকর্ষণীয় উপায়ে কিছু উপদেশ বিতরণ বা নীতির প্রচার। আর তা নির্ভর করে এই নীতিগুলোর রচয়িতা বা প্রচারকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সামাজিক অবস্থান এবং তৎকালীন প্রেক্ষাপটের উপর। কোন প্রক্ষিপ্ত সংযুক্তি না হয়ে প্রকৃতই এটা যদি চাণক্যের শ্লোক হয়ে থাকে, তাহলে চাণক্যের অধিষ্ঠানকাল বিবেচনায় শ্লোকটির রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকই বলতে হবে। তখনকার সামাজিক আবহটা কী ছিলো তবে ?
.
ধর্মীয় বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল আধিপত্যের যাতাকলে পিষ্ট তৎকালীন সমাজ তখন খণ্ড-বিখণ্ডে বিভাজিত। একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের স্বঘোষিত মুখপাত্র উচ্চবর্ণীয় আর্য ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সম্প্রদায়ের হাতে শাসনদণ্ড, অন্যদিকে সমাজের সরাসরি উৎপাদন-সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর সাধারণ জনগোষ্ঠী যাদেরকে শুধু অনার্য বানিয়েই ক্ষান্ত হতে পারেনি এরা, তথাকথিত এক স্রষ্টা ব্রহ্মার আজগুবি গল্প ফেঁদে কাল্পনিক পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ধর্মীয় দোহাই তোলে সুকৌশলে তাদেরকে নিম্নবর্গীয় শূদ্র বানিয়ে রাখা হয়েছে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত করে আক্ষরিক অর্থেই ভয়ঙ্কর এক ক্রিতদাস্যের শৃঙ্খলে। এবং এরা যাতে কখনোই একাট্টা বিদ্রোহী হয়ে এই অপশাসন-ব্যবস্থার জন্যে হুমকী হয়ে উঠতে না পারে সে লক্ষ্যে এই ব্রাত্য জনগোষ্ঠীকে আরো অনেক অনেক সামাজিক বিভাজনে পরস্পর বিভাজিত করে ভেঙে দিতে চেয়েছে তাদের মেরুদণ্ডের সবকটা কশেরুকা। আর এই ধর্মবাদী নিরঙ্কুশ শাসন নির্বিঘ্নে পরিচালনার লক্ষ্যে উপনিষদীয় ঋষি-ব্রাহ্মণদের হাতে রচিত হয়ে গেছে বেশ কিছু মোহনীয় শাস্ত্র, দর্শন এবং এর ভূরিভূরি ভাববাদী ব্যাখ্যাও। আর নিকৃষ্ট শূদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ রয়েছে সকল ধরনের বিদ্যার্জন, শাস্ত্রপাঠ বা জ্ঞান অর্জনের যেকোন নগন্য সুযোগও। কেননা এরা এই সুযোগ পেলে বুঝে যাবে শাস্ত্রীয় ভণ্ডামির ফোকর-ফাকর, তছনছ হয়ে যাবে এতোকালের পরনির্ভরশীলতায় গড়ে তোলা যথেচ্ছ ভোগের অবারিত সাম্রাজ্য-সৌধ।
.
কিন্তু তাতেও কি নিরাপদ থেকেছে তারা ? খুব স্বাভাবিকভাবেই শ্রমে-ঘামে ভেজা ব্রাত্য জনগোষ্ঠী কখনোই মেনে নিতে চায়নি তা। তারা তাদের জীবনচর্চার প্রত্যক্ষ উপাদান লোকায়ত আচার-বিচারকে অবলম্বন করেই গড়ে তুলেছে এক অন্যরকম বিদ্রোহের দেয়াল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভণ্ডামির অন্তঃসারশূন্যতাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সৃষ্টি করেছে এক প্রতিবাদী দর্শন- যার নাম লোকায়ত দর্শন। মাটির সন্তান বলেই মৃত্তিকার রসসিঞ্চিত প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিতে এরা পরাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাওতাবাজির সমস্ত কাল্পনিক উৎসকে সরাসরি অস্বীকার করে লোকায়ত চার্বাক দর্শনের নামে যুক্তির যে ধারালো বল্লম তুলে নিয়েছে হাতে, তা যে আর হেলাফেলার নয়, বড় শক্ত ভিতের উপর দাঁড়ানো, তা বুঝতে একটুও দেরি হয়নি ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্র, ধর্ম, দর্শনেও এসেছে নতুন ঢাল। তাদের চোখে সেই লোকায়তিকরা হয়েছে নাস্তিক, কারণ ওরা বেদ মানে না। প্রত্যক্ষের বাইরে কোন কিছুই বিশ্বাস করে না ওরা, তাই ব্রাহ্মণ্যবাদের চোখে ওদের শানিত যুক্তি চিহ্নিত হয়েছে হেতুবিদ্যা বা অসৎ-তর্ক নামে।
.
এখন প্রশ্ন আসে, যুক্তির ধারে শানিত এই হেতুবিদ্যা কি প্রকৃতই কোন অজ্ঞ শাস্ত্রবিমুখ মূর্খের দ্বারা সৃষ্ট হওয়া সম্ভব ছিলো ? ব্রাহ্মণের অষ্টপ্রহর সেবায় নিয়োজিত আক্ষরিক গাধার মতো খেটে যাওয়া কোনরূপ শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগহীন ক্রিতদাস শূদ্রদের দ্বারা নিশ্চয়ই এরকম সুশিক্ষিত উচ্চকোটির শাস্ত্র রচিত হওয়া সম্ভব ছিলো না। অর্থাৎ যে কোন অবস্থান থেকেই যুগে যুগে মানবদরদী মানবতাবাদী মুক্তচিন্তক কিছু মানুষের উত্থান সর্বকালেই হয়েছে যাঁরা মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন সবকিছু তুচ্ছ করে কেবলই মানবজন্মের দায়ভার কাঁধে নিয়ে। তাঁদের শরীরেও মাটির সোঁদা গন্ধই ছিলো নিশ্চয়ই। প্রাথমিক চার্বাকরা সেই বিরল গোত্রেরই মানুষ। অন্য দৃষ্টিতে তাঁদেরকে বার্হষ্পত্যও বলা হয়। এরা নাস্তিক। নইলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সকল শাস্ত্রের সাংবিধানিক আকরগ্রন্থ ‘মনুসংহিতা’য় কেন স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে এভাবে-
যোহবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভি র্বহিষ্কার্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।। ২ / ১১।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অর্থাৎ অসৎ-তর্ককে অবলম্বন ক’রে ধর্মের মূলস্বরূপ এই শাস্ত্রদ্বয়ের (শ্রুতি ও স্মৃতির) প্রাধান্য অস্বীকার করে (বা অনাদর করে), সাধু ব্যক্তিদের কর্তব্য হবে- তাকে সকল কর্তব্য কর্ম এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা (অর্থাৎ অপাংক্তেয় ক’রে রাখা)। কারণ, সেই ব্যক্তি বেদের নিন্দাকারী, অতএব নাস্তিক।
যুক্তিহীন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার এই শাস্ত্রসম্মত প্রাচীন নজির একালেও বিরল তো নয়ই, বরং ভিন্ন রূপে ভিন্ন মোড়কে তাকে আরো বেশি মাত্রায় সক্রিয় হতে দেখা যায় এখনো। তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্তঃসারশূন্য শান্ত্র-দর্শনের বিপরীতে জড়বাদী লোকায়ত চার্বাক দর্শনের এইযে বাস্তববাদী শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে গেলো, তাকে প্রতিরোধ করতেই সে-সময়কার শাসকদের নিয়োজিত করতে হয়েছিলো তাদের সর্বময় শক্তি। তাদের দর্শনের প্রধান কাজই হয়ে দাঁড়ালো ওই লোকায়তের বাস্তব যুক্তি খণ্ডনের উপায় অন্বেষণ। আর এই শক্তির বলয় তৈরি করতে সৃষ্টি করতে হয়েছে সম্পূর্ণ এক পরভোজী সম্প্রদায়, উৎপাদন সংশ্লিষ্টতাহীন আরাম-আয়েশ-বিলাস-ব্যসনে মত্ত অঢেল সময় থেকে যাদের একমাত্র কাজ হলো নতুন নতুন ধর্মশাস্ত্রীয় কল্পনা, যুক্তি, তর্ক ইত্যাদির সমৃদ্ধিতে নিজেদের সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রাখা। রাজশক্তির সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের অঢেল ভোগলিপ্সা পরিতৃপ্তির পাশাপাশি এরা রচনা করবে রাজশক্তিকে নিরাপদ রাখার যাবতীয় কলাকৌশল। এরাই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, ক্ষত্রিয় শাসনে তাদেরকে দেয়া হলো সর্বোচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত বিদ্যাগুরুর পদ। এরাই চর্চা করবে যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের, তৈরি করবে সামাজিক আইন, তাদের মুখনিঃসৃত বাণীই হবে নীতিশাস্ত্র, সংবিধান, পালনীয় আচার। কারণ তাঁরাই জ্ঞানী বা বিদ্বান হিসেবে স্বীকৃত। তাঁদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব নির্দেশ করে মনুশাস্ত্রে তাই বলা হচ্ছে-
সর্বং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্মে নিবিশেত বৈ।। ২ / ৮।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : বিদ্বান্ ব্যক্তি সমস্ত বিষয়ে [যা কৃত্রিম অর্থাৎ উৎপত্তিযুক্ত এবং যা অকৃত্রিম অর্থাৎ উৎপত্তিবিহীন, যা প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য এবং যা অনুমানাদি প্রমাণগম্য- এই সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থ] জ্ঞানরূপ চক্ষুর দ্বারা [অর্থাৎ তর্ক, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, মীমাংসা প্রভৃতি বিদ্যাবিষয় আচার্যের মুখ থেকে শুনে এবং নিজে তা চিন্তা করে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তার দ্বারা] ভালোভাবে বিচারপূর্বক নিরূপণ করে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে নিজ ধর্মে নিবিষ্ট হবেন।
অতএব, বিদ্বানের তৎকালীন শাস্ত্রবিহিত সংজ্ঞাটা স্পষ্টভাবেই নির্দেশিত হয়ে গেছে। গুরু চাণক্য যে সেকালের সর্বশ্রেষ্ট বিদ্বান ছিলেন তা তাঁর জীবন চরিত থেকেই আমরা জানতে পারি। তিনি একাধারে শাস্ত্রজ্ঞ দার্শনিক, কূটনীতিজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, রতিশাস্ত্রবিদ, ন্যায়ভাষ্যকার, ভারতবর্ষের প্রথম সাম্রাজ্যবিস্তারকারী সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উপদেষ্টা গুরু ও প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ রাজপুরুষও এবং আরো অনেককিছু। ফলে তাঁর রচিত নীতিশাস্ত্রে বর্ণিত নীতিশ্লোকের মাহাত্ম্য অনেক গভীরেই প্রোথিত আছে বলাবাহুল্য।
.
সমাজে বিদ্বানের পরিচয় আমরা ইতোমধ্যে পেয়ে গেলেও বিদ্যা বলতে প্রকৃতই কী বোঝানো হয়েছে তা মনুসংহিতার অবশ্যপালনীয় বিধান থেকে মোটামুটি একটা চিত্র আমরা পেয়ে যাই। তবু এ ব্যাপারে যাতে কোন অস্পষ্টতা না থাকে সেজন্যেই সাম্রাজ্য পরিচালনার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে রাষ্ট্রনায়কদের পালনীয় নীতিকোষ হিসেবে কৌটিল্য ছদ্মনামে রচিত চাণক্যের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থ ‘অর্থশাস্ত্রে’ প্রয়োজনীয় বিদ্যা বলতে কী বোঝায় তা তিনি স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন-
.
সমাজে বিদ্বানের পরিচয় আমরা ইতোমধ্যে পেয়ে গেলেও বিদ্যা বলতে প্রকৃতই কী বোঝানো হয়েছে তা মনুসংহিতার অবশ্যপালনীয় বিধান থেকে মোটামুটি একটা চিত্র আমরা পেয়ে যাই। তবু এ ব্যাপারে যাতে কোন অস্পষ্টতা না থাকে সেজন্যেই সাম্রাজ্য পরিচালনার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে রাষ্ট্রনায়কদের পালনীয় নীতিকোষ হিসেবে কৌটিল্য ছদ্মনামে রচিত চাণক্যের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থ ‘অর্থশাস্ত্রে’ প্রয়োজনীয় বিদ্যা বলতে কী বোঝায় তা তিনি স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন-
‘আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ। ১/২/১ (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র)।
অর্থাৎ : আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি- এই চারটিই বিদ্যা।
ত্রয়ী অর্থ বেদ। ঋগে¦দ, সামবেদ, যজুর্বেদ এই তিনটি একত্রে বেদ। সেকালে তখনো চতুর্থ বেদ অর্থাৎ অথর্ববেদ সংগৃহীত হয়নি বা তখনো তা বেদ হিসেবে গুরুত্ববহ স্বীকৃতি পায়নি বলে প্রাচীন শাস্ত্রে বেদকে ত্রয়ী হিসেবেই উল্লেখ করা হয়। দণ্ডনীতি হলো রাজকার্য পরিচালনার বিধান। বার্তা হলো কৃষি ইত্যাদি অর্থনীতিসংক্রান্ত বিদ্যা। আর আন্বীক্ষিকী হলো তর্কবিদ্যা। এ সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রেই বলা হচ্ছে-
‘প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মনাম্ ।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মানাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।। ১/২/১১।। (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র)
অর্থাৎ : সব রকম বিদ্যার প্রদীপ, সব কাজের উপায় এবং সকল ধর্মের আশ্রয় হলো আন্বীক্ষিকী।
বুঝাই যাচ্ছে, প্রচলিত ধর্মকে রার করার উপায় হিসেবে সৃষ্ট ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, মীমাংসা ইত্যাদি ধর্মীয় শাস্ত্রকে হেতু বা যুক্তির মাধ্যমে ধর্ম-অধর্ম, অর্থ-অনর্থ, ফলাফল ইত্যাদির বিচার করে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করাই আন্বীক্ষিকীর উদ্দেশ্য। আর এজন্যেই লোকায়ত বার্হষ্পত্যরা আন্বীক্ষিকীকে প্রামাণ্য বিদ্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেন না। আর ত্রয়ী বা বেদকে তো প্রামাণ্য মানতেই নারাজ। কারণ তাঁদের মতে-
‘তদপ্রামাণ্যমনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্ত-দোষেভ্যঃ’। ৫৮। (বার্হস্পত্যসূত্র)
অর্থাৎ : এতে (বেদে) অনৃত দোষ বা মিথ্যে কথা, ব্যাঘাত দোষ বা পরস্পর বিরুদ্ধ কথা এবং পুনরুক্ত দোষ পূর্ণ।.
‘ধূর্ত্ত-প্রলাপস্ত্রয়ী’। ৫৯। (বার্হস্পত্যসূত্র)
অর্থাৎ : (বেদের কর্তা) ভণ্ড, ধূর্ত, নিশাচর ত্রয়ী।
লোকায়তিকরা প্রত্যক্ষের বাইরে কোন কিছুকেই প্রমাণ হিসেবে মানেন না। তাই কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বার্হস্পত্যদের সম্পর্কে উক্তি করেছেন-
‘বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বার্হস্পত্যাঃ। ১/২/৪। (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র)
অর্থাৎ : বার্হস্পত্যদের মতে বিদ্যা হলো দুটি- দণ্ডনীতি এবং বার্তা।
কৌটিল্য যে বার্হস্পত্যদের সাথে কোনভাবেই একমত নন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা তিনি তো বিদ্যা অর্থে চারটি শাস্ত্রকেই নির্দেশ করেছেন। অতএব, কৌটিল্য তথা চাণক্যের নীতিশ্লোকে বর্ণিত বিদ্বানের আয়ত্তে কোন্ কোন্ বিদ্যা থাকবে তা পরিষ্কার। সমাজকে তাঁদের চাওয়া অনুযায়ী এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনে যেসব শাস্ত্রে বুৎপত্তি, দক্ষতা ও লক্ষ্যনিষ্ঠ সক্রিয়তা থাকা দরকার মনে করেছেন, সেটাই নীতিশাস্ত্রের মাধ্যমে সমাজকে জানিয়ে দিয়েছেন। মোড়কের বাইরে বিদ্যা নাম নিয়ে কোন আপত্তি না-থাকলেও বিদ্যার সংজ্ঞা, কাঠামো, উৎস বা লক্ষ্য নিয়ে তৎকালীন দার্শনিক চিন্তকদের মধ্যে যে প্রচণ্ড অন্তর্বিরোধের সাংঘর্ষিক উপাদান সক্রিয় ছিলো তাও নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছি আমরা। আর আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার সমাজ ও তার ভৌগোলিক অবস্থা, যোগাযোগ কাঠামো, জীবনধারণ পরিবেশ ইত্যকার বিষয় বিবেচনায় নিলে সে-সময় প্রবাস বলতে নিশ্চয়ই অত্যাধুনিক উড়োজাহাজে চড়ে সুদূর মার্কিনদেশ বা পাশ্চাত্যের ইউরোপ ভ্রমণ বোঝাতো না। খুব স্বাভাবিকভাবে আশেপাশের কোন গমনযোগ্য রাজ্য বা অঞ্চল কিংবা তৎকালীন বৃহত্তর ভারতবর্ষকেই বোঝানো হতো। ফলে বিদ্বান সর্বত্র পূজনীয় বলা হলেও এই সর্বত্রেরও যে একটা সীমিত ভৌগলিক কাঠামো ছিলো তাও বোঝার বাকি থাকে না। ওই কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়ন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যবহারিক মূল্যের আলোকেই বিদ্যাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ঠিক এই বিষয়টিকে মাথায় রাখলেই আমরা নীতিশাস্ত্রের সেই চিরায়ত সুরের খোঁজটি পেয়ে যাই। যেখানে প্রয়োজনীয় সমকালীন তান সংযুক্ত করে দিলেই তা যুগোপযোগী হয়ে ওঠতে পারে। আর তাই এই নীতিকথাকে আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না তো বটেই, বরং সময়ের তরতাজা ক্রমানুক্রমিক রসে সিক্ত হয়ে তা আমাদের জন্য কালোত্তীর্ণ এক চিরকালীন অমূল্য রত্ন হিসেবেই আগ্রহের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে।
.
এবার তাহলে আমরা ফিরে যাই নীতিশ্লোকটির কাছে। কোন রাজাধিরাজ নয়, বিদ্বানই সর্বত্র পূজিত হন। কারণ তিনিই বিদ্বান্ যিনি সেই বিদ্যাটিই আয়ত্ত করেন যা দিয়ে সমাজ-সভ্যতার অগ্রযাত্রা আরো বেগবান, সৃষ্টিশীল ও বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। আর যা আঁকড়ে থাকলে সমাজ স্থবিরতায় আক্রান্ত হয়, সম্মুখগতি হারিয়ে পেছনমুখি হয় সেটা কোন বিদ্যাই নয়। তাই ওইসব প্রাগৈতিহাসিক জঞ্জালবিদ্যায় পাণ্ডিত্যের পাহাড় জমিয়ে তাকে রিসাইক্লিং না করে কেবলি ঘাটাঘুটি করলে পচা-গলা-বাসি অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধই ছড়াবে শুধু, সমাজ আক্রান্ত হবে অথর্বতায়, কিন্তু কোন বিদ্যা বা বিদ্বান বেরুবে না যিনি মানুষকে সামনে যাবার পথটা দেখিয়ে দেবেন। সর্বত্র পূজিত বিদ্বান তিনিই যিনি যে-সমাজের অধিবাসীই হোন না কেন বৃহত্তর মানবসমাজকে সামনে এগিয়ে যাবার পথটা তৈরি করে দেন তার সমকালীন বিদ্যার সৃষ্টিশীলতা দিয়ে। দেশ-কাল অতিক্রম করে মানবসভ্যতা যাদের কাছে ঋণী, সভ্যতার প্রারম্ভিক কাল থেকে একাল পর্যন্ত এরকম বহু বহু বিদ্বানের নাম যুগে যুগে মানবেতিহাসের অত্যুজ্জ্বল পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে। কিন্তু এরা কেউ ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। ধর্মের কূপমণ্ডূকতায় আবদ্ধও ছিলেন না এরা।
.
এসব নীতিশ্লোককে কেন্দ্র করে যুগে যুগে অনুসন্ধিৎসু জ্ঞানপিপাসুরা হয়েছেন প্রাণিত, বহু কবি তাঁদের সৃষ্টিকর্মকে করেছেন উজ্জ্বল। সাহিত্যে কাব্যে উপকথায় পল্লবিত হয়েছে অপরূপ বর্ণচ্ছটায়। আড়াই হাজার বছর পেরিয়ে আমরাও এখনো স্মরণ করছি এসব। এবং এ থেকেই এসব নীতিশ্লোকের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সুদূরপ্রসারি প্রভাবটুকু অনুধাবন করা যায় সহজেই। চাণক্যের এই নীতিশ্লোক রচনার প্রায় তিনশ বছর পরের খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের আরেক সংস্কৃত কবিশ্রেষ্ঠ ভর্তৃহরির নীতিকাব্যেও দেখি তাই চাণক্যেজনের ছায়া-
বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশঃসুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্য পরা দেবতা
বিদ্যা রাজসু পূজিতা ন তু ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ।। ২০।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)।
অর্থাৎ : বিদ্যা মানুষের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য ও গোপনে রক্ষিত (বহুমূল্য) ধন। বিদ্যা (মানুষকে) ভোগ দেয়, দেয় সুখ ও সুখ্যাতি। বিদ্যা গুরুর(-ও) গুরু। প্রবাসে বিদ্যা(-ই) বন্ধু। বিদ্যা পরম দেবতা। রাজসভায় বিদ্যা(-ই) সমাদৃত হয়, ধন নয়। (তাই) বিদ্যা যার নেই সে পশু(তুল্য)।
পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বে মূর্খে দোষা হি কেবলম্ ।
তস্মান্মূর্খসহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে।। ০২।। (চাণক্য নীতিশাস্ত্র)।
অর্থাৎ : পণ্ডিত ব্যক্তি সকল গুণের আর মূর্খ ব্যক্তি সকল দোষের আধার- এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই সহস্র মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিত বিশিষ্ট বা অধিকতর গ্রাহ্য রূপে পরিগণিত হন।
তস্মান্মূর্খসহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে।। ০২।। (চাণক্য নীতিশাস্ত্র)।
অর্থাৎ : পণ্ডিত ব্যক্তি সকল গুণের আর মূর্খ ব্যক্তি সকল দোষের আধার- এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই সহস্র মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিত বিশিষ্ট বা অধিকতর গ্রাহ্য রূপে পরিগণিত হন।
.
মূর্খ ব্যক্তির চেয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি অধিকতর গুণবান হবেন, সম্ভাব্যতার বিচারে তা মেনে নিতেই পারি আমরা। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি সকল দোষের আধার- (নিজে মূর্খ বলেই) এরকম একটা সন্দেহাতীত ঘোষিত নিশ্চিত সিদ্ধান্তকে হজম করার আগে কিঞ্চিৎ ভাবনার দরকার নয় কি ? প্রথমত মূর্খ বলতে চাণক্য কাদের বুঝিয়েছেন, আর পণ্ডিতই বা কারা ? সাধারণ জ্ঞানে বলা হয়, বিভিন্ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে যিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তিনিই পণ্ডিত। কিন্তু সাধারণ জ্ঞান আর বিশেষ জ্ঞানের মধ্যে যে ব্যাপক ফারাক ! বিশেষ করে নীতিশ্লোক রচয়িতা চাণক্যের সময়কালও বিবেচনায় রাখাটা জরুরি বটে। সেক্ষেত্রে তৎকালীন সকল শাস্ত্রের আধার সমাজের অবশ্যপালনীয় স্মৃতিশাস্ত্র ‘মনুসংহিতা’য় মনু কী বলেছেন দেখি-
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ।। ২ / ১৫৫।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব হয় জ্ঞানের আধিক্যের দ্বারা, ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠত্ব অধিক বীর্যবত্তার দ্বারা, বৈশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ধন-ধান্যাদি প্রভৃতি বেশি সম্পত্তির দ্বারা এবং শূদ্রদের শ্রেষ্ঠত্ব হয় তাদের জন্মের অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার উপর (অর্থাৎ কেবল বয়সে বৃদ্ধ হলেই কোনও শূদ্র তার জাতির অন্য লোকদের কাছে মান্য হয়)।
বর্ণাশ্রম প্রথায় বিভাজিত তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জন্মমাত্রই জগতকে কৃতার্থ করে দেন, কারণ জন্মসূত্রেই তিনি অন্য তিন বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে।। ১ / ৯৯।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করা মাত্রই পৃথিবীর সকল লোকের উপরিবর্তী হন অর্থাৎ সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। কারণ, ব্রাহ্মণই সকলের ধর্মকোষ অর্থাৎ ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য প্রভূসম্পন্ন হয়ে থাকেন [কারণ, ব্রাহ্মণের উপদেশেই অন্য সকলের ধর্মের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে]।
অতএব তিনি অন্য সবার জন্যেই অবশ্য-সম্মানীয়। এমনকি তাঁর মহান কাজও নির্দিষ্ট করা আছে শাস্ত্রে- শাস্ত্র-অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং জগতের সকল বিষয়ে শুভ-অশুভ, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি নির্ধারণ। অর্থাৎ জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈধ অধিকারী কেবল ব্রাহ্মণই। তবে ব্রাহ্মণের মুখ থেকে শাস্ত্র শ্রবণের অধিকার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের থাকলেও বর্ণদাস শূদ্র সেখানে গুনাতেই আসে না। বরং লুকিয়ে বা অসতর্কভাবেও শাস্ত্রবাক্য শূদ্রের কানে পৌঁছে গেলে তার কানে গরম সীসা ঢেলে দেয়ার বিধান শাস্ত্রেই নির্দেশ করা আছে। ফলে পাণ্ডিত্যের পাল্লাটা যে ব্রাহ্মণের দিকেই হেলে পড়বে তাতে আর সন্দেহ কী ! তাহলে ব্রাহ্মণ হলেই কি তিনি পণ্ডিতের খেতাব পেয়ে যাচ্ছেন ? তাও নয়। শাস্ত্রানুযায়ী ব্রাহ্মণদের নিজেদের মধ্যেও মান্যতার মাপকাঠিতে পর্যায়ক্রমিক একটা রকমফের রয়েছে-
বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরম্ ।। ২ / ১৩৬।। (মনুসংহিতা)
অর্থাৎ : (সজাতীয় লোকেদের মধ্যে) ন্যায়ার্জিত ধন, পিতৃব্যাদি রক্তসম্মন্ধ, বয়সের আধিক্য, শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত কর্ম, এবং বেদার্থতত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানরূপ বিদ্যা- এই পাঁচটি মান্যতার কারণ; এদের মধ্যে পর পরটি অধিকতর সম্মানের হেতু বলে জানবে [অর্থাৎ ধনী অপেক্ষা পিতৃব্যাদি-রক্তসম্বন্ধযুক্ত বন্ধু, বন্ধু অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ অপেক্ষা শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানকারী, এবং অনুষ্ঠানকারী অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে বেশি মান্য বলে জানবে]।.ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ।। ১ / ৯৭।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণগণের মধ্যে (মহাফলপ্রদ জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞাধিকারী) বিদ্বানেরা শ্রেষ্ঠ; বিদ্বানদের মধ্যে যাঁরা কৃতবুদ্ধি (অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্রে নিষ্ঠাবান বা শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠানে যাঁদের কর্তব্যবুদ্ধি আছে), তাঁরাই শ্রেষ্ঠ; কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিদের মধ্যে আবার যাঁরা শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠাতা, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ; আবার শাস্ত্রোক্তকর্মানুষ্ঠানকারীদের মধ্যে ব্রহ্মবিদগণ (অর্থাৎ জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী লোকেরা) শ্রেষ্ঠ।
অতএব আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় অধিকতম সম্মানের অধিকারী ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণরা যাঁরা বেদকে প্রামাণ্য মেনে শাস্ত্রবিহিত কর্ম পালন করে বেদার্থতত্ত্ব বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। তাঁরাই ছিলেন সমাজের চোখে তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত। অন্যদিকে মূর্খ তো ওরাই, যারা কোনরূপ বিদ্যার্জন থেকে দূরে রয়েছে। সে বিবেচনায় শূদ্ররা যে মহামূর্খ তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে ! কিন্তু সমাজ-কাঠামোর জীয়নযন্ত্র তথা সামগ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সচল ও সক্রিয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠি এই শূদ্রদেরকে কারা বেদ ও ব্রহ্মার দোহাই দিয়ে সুকৌশলে মূর্খ বানিয়ে রাখতে চেয়েছে- সে প্রশ্নটি নির্দ্বিধায় করে ফেলে যারা এর প্রতিকার চেয়েছেন, তারা তো বেদের নিন্দাকারী নাস্তিক। তাদেরকে সম্মান করার প্রশ্নই আসে না ! নইলে কি এরা এভাবে বলে-
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ী তন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকম্ ।
প্রজ্ঞাপৌরুষনিঃস্বানাং জীবো জল্পতি জীবিকাম্ ।। ৩।। (চার্বাকষষ্ঠী)।
অর্থাৎ : (বৃহস্পতি বলেন)- হোম, বেদবিহিত কার্যকলাপ, পাশুপত ব্রত ও ভস্ম তিলক হলো প্রজ্ঞাশক্তিহীন ব্যক্তিদের জীবিকা।
মনুসংহিতায় (২ / ১১) এইসব বেদনিন্দুক নাস্তিকদেরকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করার কথা স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে। ফলে এরা যত শাস্ত্র-অধ্যয়নকারী প্রাজ্ঞ যুক্তিশীলই হোন না কেন, তাঁদেরকে ওই ব্রাহ্মণ্যশাসনের যুগে পণ্ডিত হিসেবে মান্য করার কোন দৃষ্টিভঙ্গি চাণক্যশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। তখনকার সমাজ-শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো এমনই, অন্তত নীতিশাস্ত্রের সমাজচিত্র তা-ই বলে। এই শাস্ত্রবিহিত পণ্ডিত হতে হলে অন্য গুণ যা-ই হোক, বেদাদি শাস্ত্রে আগ্রহ ও বিশ্বাস থাকতেই হবে। এই গুণ না-থাকলে মহাত্মা হওয়া যায় না। তাই তো সেকালের কবিশ্রেষ্ঠ ভর্তৃহরির নীতিশতকেও আমরা দেখতে পাই-
বিপদি ধৈর্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা
সদসি বাক্পটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরতিব্যসনং শ্রুতৌ
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্ ।। ৬৩।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)।
অর্থাৎ : বিপদে ধৈর্য (ধারণ), সম্পদে অনৌদ্ধত্য, সভায় বাকপটুতা, সংগ্রামে শৌর্য, খ্যাতির প্রতি অভীপ্সা এবং বেদাদি শাস্ত্রের প্রতি আসক্তি- এসব (হচ্ছে) মহাত্মাদের স্বভাবসিদ্ধ (গুণ)।
দৃষ্টিভঙ্গির এই ধারা দু’হাজার বছর পেরিয়ে একালে এসেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মধ্যে খুব একটা হেরফের হতে আজো কি দেখতে পাই আমরা ? বর্তমান সমাজেও দেখি কোন ব্যক্তির চারিত্রিক সদাচারের অন্যতম উজ্জ্বল ও আবশ্যক গুণ হিসেবে বিবেচিত হয় ধর্মচর্চায় তিনি কতোটা নিষ্ঠা দেখাচ্ছেন তার উপর। কিন্তু ধর্মচর্চায় ব্রতী হলেই তিনি যে উন্নত চরিত্রের হবেন এমন নিশ্চয়তা কি কেউ দিতে পারে ? বরং ধর্মশাস্ত্র-পুরাণেই দেখি ধর্মনীতির নামে যুগে যুগে মানবেতিহাসের কতো অমানবিক অনৈতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ধর্মের দোহাই তুলে। শাস্ত্রবিধিতেও রয়েছে যতো পক্ষপাতদুষ্ট চতুরতার ভূরিভূরি নিদর্শন। অপ্রাসঙ্গিক না-হলে এ প্রেক্ষিতে নমুনা হিসেবে পরিপূরক দুটো শাস্ত্রবিধি উদ্ধৃত করা যায়, যেমন-
ন বৃথা শপথং কুর্যাৎ স্বল্লেহপ্যর্থে নরো বুধঃ।
বৃথা হি শপথং কুর্বন্ প্রেত্য চেহ চ নশ্যতি।। ৮ / ১১১।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : পণ্ডিত ব্যক্তি তুচ্ছবিষয়ের জন্য বৃথা শপথ করবেন না। বৃথা শপথকারীর ইহলোকে কীর্তি নষ্ট হয় এবং পরলোকে নরকভোগ করতে হয়।
.
কামিনীষু বিবাহেষু গবাং ভক্ষ্যে তথেন্ধনে।
ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকম্ ।। ৮ / ১১২।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : ‘আমি অন্য কোনও নারীকে চাই না, তুমিই আমার প্রাণেশ্বরী’- সুরতলাভের জন্য অর্থাৎ কাম চরিতার্থ করার জন্য কামিনীবিষয়ে (অর্থাৎ স্ত্রী, বেশ্যা প্রভৃতির কাছে) মিথ্যা শপথ করা হলে পাপ হয় না। ‘তুমি অন্য কোনও নারীকে বিবাহ করতে পারবে না কিংবা তুমি অন্য কোনও পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে না’- এই প্রকারে স্বীকার করা সত্ত্বেও নিজের জন্য বা বন্ধুবান্ধবের জন্য বিবাহবিষয়ে মিথ্য বলায় দোষ নেই। গরুর ঘাস প্রভৃতি খাদ্য বিষয়ে, যজ্ঞ হোমের জন্য কাষ্ঠাদি আহরণ বিষয়ে, এবং ব্রাহ্মণের উপকার করার জন্য মিথ্যা বললে দোষ হয় না।
মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।। ০৩।। (চাণক্য নীতিশাস্ত্র)।
অর্থাৎ : যে ব্যক্তি পরের স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে দেখেন, পরের দ্রব্যকে মাটির ঢেলার মতো জ্ঞান করেন (অর্থাৎ নির্লোভ থাকেন) এবং সকল জীবে আত্মজ্ঞান পোষণ করেন- তিনিই যথার্থ পণ্ডিত বা জ্ঞানী।
.
চমৎকার এই মোহনীয় নীতিবাক্যটি মুগ্ধ হয়ে শুনতে ভালোই লাগে। কিন্তু একটু ভাবতে বসলেই ভিরমি খেতে হয়- পরের স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে দেখার সাথে যথার্থ পাণ্ডিত্যের বা জ্ঞানের সম্পর্কটা কোথায় ! কেউ কেউ অবশ্য এই নীতিবাক্যের মনোমুগ্ধকর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন এভাবে-
‘সমাজে বাস করতে গেলে কতগুলি সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ সামাজিক গর্হিত অপরাধ। স্বাভাবিক কামনাবশতঃ সৃষ্ট এইসব প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে ব্যভিচার হয়, সামাজিক বন্ধন নষ্ট হয়। পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ পরিহারের শ্রেষ্ঠ পন্থা হ’ল তাঁকে নিজের মা বলে ভাবা। নিজের মা যেমন ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র- পরস্ত্রীও সেরকমই। এই জ্ঞান এলে সমস্ত অসৎবুদ্ধি দূর হয়- ব্যবহারে কালিমা আসে না। পরের জিনিষের প্রতিও কোন লোভ পোষণ করা উচিত নয়। লোভ মানুষকে অনেক সময় অমানুষ করে তোলে। মাটির ঢেলাকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি সেই দৃষ্টিতে যদি পরের জিনিষ দেখা যায় তবে আর কোন মোহ আসে না। ফলে তা পাওয়ার বাসনাও লুপ্ত হয়। সকল প্রাণীতে আত্মজ্ঞান যথার্থ পণ্ডিতের লক্ষণ। সকল জীবের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের সুখ-দুঃখের অনুভূতির সাম্যজ্ঞান আসলে কখন দুঃখে শোকে অভিভূত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।’
.
খুবই সুন্দর ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে। তবে এটা একালের ব্যাখ্যা। শ্লোকটি রচিত হওয়ার কালে কি এরকম কোন ব্যাখ্যা রচয়িতার ভাবনায় সক্রিয় ছিলো ? আমরা না-হয় পরে আবার এ ব্যাখ্যায় ফিরে আসবো। কিন্তু সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় চাণক্য হঠাৎ মানুষের চারিত্রিক কিছু মৌলিক ঝোঁককে যথার্থ পাণ্ডিত্যের সাথে যেভাবে সূত্রাবদ্ধ করে দিলেন, তাতে করে এই সম্পর্কসূত্রটা খোঁজার একটা কৌতুহল জেগে ওঠে বৈকি। সেক্ষেত্রে শ্লোক রচনার সময়টাতে একটু ঘুরে আসাটাই ভালো হবে মনে হয়। এবং এক্ষেত্রে আমাদেরকে অনিবার্যভাবে শাস্ত্রীয় বিধানের জটিল জগতেই ঢু মারতে হবে ফের।
.
প্রশ্নটা যেহেতু পণ্ডিত বা জ্ঞানী বিষয়ক, তাই আমাদের ইতঃপূর্বের (নীতিকথা-০২) আলোচনার সূত্রে এটা অন্তত বুঝা যায় যে, বিতর্কটা একান্তই সেসব বিদ্যার জাহাজি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যাদের নারী বিষয়ক মনোরঞ্জনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থে কোন সীমা বেঁধে দেয়া হয় নি বলেই প্রতীয়মান হয়। যেমন-
‘সমাজে বাস করতে গেলে কতগুলি সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ সামাজিক গর্হিত অপরাধ। স্বাভাবিক কামনাবশতঃ সৃষ্ট এইসব প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে ব্যভিচার হয়, সামাজিক বন্ধন নষ্ট হয়। পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ পরিহারের শ্রেষ্ঠ পন্থা হ’ল তাঁকে নিজের মা বলে ভাবা। নিজের মা যেমন ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র- পরস্ত্রীও সেরকমই। এই জ্ঞান এলে সমস্ত অসৎবুদ্ধি দূর হয়- ব্যবহারে কালিমা আসে না। পরের জিনিষের প্রতিও কোন লোভ পোষণ করা উচিত নয়। লোভ মানুষকে অনেক সময় অমানুষ করে তোলে। মাটির ঢেলাকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি সেই দৃষ্টিতে যদি পরের জিনিষ দেখা যায় তবে আর কোন মোহ আসে না। ফলে তা পাওয়ার বাসনাও লুপ্ত হয়। সকল প্রাণীতে আত্মজ্ঞান যথার্থ পণ্ডিতের লক্ষণ। সকল জীবের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের সুখ-দুঃখের অনুভূতির সাম্যজ্ঞান আসলে কখন দুঃখে শোকে অভিভূত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।’
.
খুবই সুন্দর ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে। তবে এটা একালের ব্যাখ্যা। শ্লোকটি রচিত হওয়ার কালে কি এরকম কোন ব্যাখ্যা রচয়িতার ভাবনায় সক্রিয় ছিলো ? আমরা না-হয় পরে আবার এ ব্যাখ্যায় ফিরে আসবো। কিন্তু সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় চাণক্য হঠাৎ মানুষের চারিত্রিক কিছু মৌলিক ঝোঁককে যথার্থ পাণ্ডিত্যের সাথে যেভাবে সূত্রাবদ্ধ করে দিলেন, তাতে করে এই সম্পর্কসূত্রটা খোঁজার একটা কৌতুহল জেগে ওঠে বৈকি। সেক্ষেত্রে শ্লোক রচনার সময়টাতে একটু ঘুরে আসাটাই ভালো হবে মনে হয়। এবং এক্ষেত্রে আমাদেরকে অনিবার্যভাবে শাস্ত্রীয় বিধানের জটিল জগতেই ঢু মারতে হবে ফের।
.
প্রশ্নটা যেহেতু পণ্ডিত বা জ্ঞানী বিষয়ক, তাই আমাদের ইতঃপূর্বের (নীতিকথা-০২) আলোচনার সূত্রে এটা অন্তত বুঝা যায় যে, বিতর্কটা একান্তই সেসব বিদ্যার জাহাজি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যাদের নারী বিষয়ক মনোরঞ্জনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থে কোন সীমা বেঁধে দেয়া হয় নি বলেই প্রতীয়মান হয়। যেমন-
সবর্ণাহগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।। ৩/১২।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য- এই দ্বিজাতিগণের দারপরিগ্রহ ব্যাপারে সর্বপ্রথমে (অর্থাৎ অন্য নারীকে বিবাহ করার আগে) সমানজাতীয়া কন্যাকেই বিবাহ করা প্রশস্ত। কিন্তু কামনাপরায়ণ হয়ে পুনরায় বিবাহে প্রবৃত্ত হলে (অর্থাৎ সবর্ণাকে বিবাহ করা হয়ে গেলে তার উপর যদি কোনও কারণে প্রীতি না জন্মে অথবা পুত্রের উৎপাদনের জন্য ব্যাপার নিষ্পন্ন না হলে যদি কাম-প্রযুক্ত অন্যস্ত্রী-অভিলাষ জন্মায় তাহলে) দ্বিজাতির পক্ষে ব্ক্ষ্যমাণ নারীরা প্রশস্ত হবে। (পরবর্তী শ্লোকে তা বর্ণিত হয়েছে)
.
শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজম্মনঃ।। ৩/১৩।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : একমাত্র শূদ্রকন্যাই শূদ্রের ভার্যা হবে; বৈশ্য সজাতীয়া বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করতে পারে; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সবর্ণা ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্যা হতে পারে; আর ব্রাহ্মণের পক্ষে সবর্ণা ব্রাহ্মণকন্যা এবং ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্যা হতে পারে।
.
ভালোই ! একজনে তৃপ্ত না হয়ে কামনাপরায়ণ হলে যেকোন বর্ণ থেকে পুনঃ পুনঃ নারী গ্রহণের বৈধ উপায় উন্মুক্ত থাকলেও পরস্ত্রীর প্রতি বর্ণশ্রেষ্ঠদের এই কামদৃষ্টি নিক্ষেপ বা পরস্ত্রী-গমন নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্ত দোষ হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকবে, অপরাধ হিসেবে নয়। কেননা, অপরাধের জন্য দণ্ডের বিধান থাকে। আর দোষ থেকে পাপ হয়, যা মোচনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয়। দেখা যাক্ শাস্ত্রবিধান কী বলে-
অকামতঃ কৃতং পাপং বেদাভ্যাসেন শুধ্যতি।
কামতস্তু কৃতং মোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।। ১১/৪৬।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : অনিচ্ছাপূর্বক যে পাপ করা হয়, তা পুনঃপুনঃ বেদপাঠ দ্বারা ক্ষয় হয়, কিন্তু মূঢ়তাবশতঃ ইচ্ছাপূর্বক যে পাপ করা হয় তা বিশিষ্ট প্রায়শ্চিত্তসমূহের দ্বারাই শুদ্ধ হয়ে থাকে।
.
তবে পরস্ত্রীগমন বিষয়ক পাপগুলো যে পণ্ডিত প্রবরদের জন্য কোন গুরু পাপ নয়, লঘু পাপ, শাস্ত্রীয় বিধানই তা আশ্বস্ত করে-
গোবধোহযাজ্যসংযাজ্য-পারদার্যাত্মবিক্রয়াঃ।
গুরুমাতৃপিতৃত্যাগঃ স্বাধ্যায়াগ্ন্যোঃ সুতস্য চ।। ১১/৬০।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : গোহত্যা, অযাজ্যসংযাজ্য [অযাজ্য অর্থাৎ অবিরুদ্ধ অপাতকী শূদ্র প্রভৃতি, তাদের সংযাজ্য অর্থাৎ যাজন অর্থাৎ পূজা প্রভৃতি ধর্মকর্ম করে দেওয়া], পরস্ত্রী-গমন, আত্মবিক্রয় [অর্থাৎ গবাদি পশুর মতো নিজেকেও পরের দাসত্বে বিলিয়ে দেওয়া], গুরুত্যাগ [অধ্যাপনা করতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের অধ্যাপক-গুরুকে ত্যাগ করে অন্য অধ্যাপকের আশ্রয়-নেওয়া], পতিত না হওয়া সত্ত্বেও মাতাকে ও পিতাকে পরিত্যাগ [তাঁরা যদি পতিত হন তাহলে তাদের ত্যাগ করা শাস্ত্র সম্মত], স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ, অগ্নিত্যাগ অর্থাৎ গৃহ্য বা স্মার্তাগ্নিত্যাগ এবং পতিত নয় এমন গুণবান প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে ত্যাগ- এগুলি সব উপপাতক।
.
আর সাথে এটাও জেনে রাখা অনুচিত হবে না যে, ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের জন্য গুরুতর পাপ বা মহাপাতক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে পাঁচটি বিষয়কে-
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়াং গুর্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ।। ১১/৫৫।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : ব্রহ্মহত্য, নিষিদ্ধ সুরাপান, ব্রাহ্মণের সোনা অপহরণ ও গুরুপত্নীগমন- এইগুলিকে ঋষিগণ মহাপাতক বলেছেন; ঐসব মহাপাতকগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে ক্রমিক একবৎসর সংসর্গ করাও মহাপাতক অতএব এই পাঁচটিকে মহাপাতক বলা হয়।
তবে এর চাইতে অধিকতর লঘু পাপ হলো নিচেরগুলো-
রেতঃসেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষ্বন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ।। ১১/৫৯।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : সহোদরা ভগিনী, কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিত নারী, অন্ত্যজনারী অর্থাৎ চণ্ডালজাতীয়া নারী, সখা এবং পুত্রের স্ত্রী- এদের যোনিতে রেতঃপাত করলে তা গুরুপত্নীগমনতুল্য পাতক বলে বুঝতে হবে। [তবে এগুলো অনুপাতক। মহাপাতকের তুলনায় কম প্রায়শ্চিত্ত হবে।]
.
যুবক শিষ্যকর্তৃক গুরুপত্নীগমনকে কেন এমন প্রণিধানযোগ্য মহাপাপ হিসেবে বিবেচনা করা হলো সে ব্যাখ্যায় না যাই। বরং বয়োবৃদ্ধ শাস্ত্রগুরুরা এসব পাতকের জন্য উপযুক্ত দণ্ডবিধান না-করে প্রয়োজনীয় প্রায়শ্চিত্তের যে বিস্তৃত বিধান শাস্ত্রগ্রন্থের পাতার পর পাতা জুড়ে রচনা করেছেন, তাতে করে প্রতীয়মান হয়, যে-পাপ পরস্পর সম্মতি সাপেক্ষে নির্বিচার ঘটে চলেছে সম্ভ্রান্ত সমাজদেহের অন্তরালে, তাকে প্রমাণযোগ্য করা যতোটা না জটিল, তার চেয়ে জটিলতর ছিলো হয়তো সমাজপতিদের আত্মগ্লানির মুখোমুখি হওয়ার ভয়াবহ পরিস্থিতি। তাই পাপ আর প্রায়শ্চিত্তের ভীতি আরোপের শাস্ত্রীয় বিধির পাশাপাশি নীতিশাস্ত্রের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণই অধিকতর বিজ্ঞ কৌশল হিসেবে গণ্য হয়েছে। পরের স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে দেখার সাথে পণ্ডিত ব্যক্তির যথার্থ পাণ্ডিত্যের সম্মন্ধসূত্রটা কি এখানেই ?
.
কিন্তু যথার্থ পণ্ডিত বা জানীর লক্ষণে পরের দ্রব্যকে মাটির ঢেলার রূপে দেখার আগে আমাদেরকে বোধয় আবারো কিছু শাস্ত্রীয় বিভ্রম চেখে আসতে হবে। যেমন-
.
কিন্তু যথার্থ পণ্ডিত বা জানীর লক্ষণে পরের দ্রব্যকে মাটির ঢেলার রূপে দেখার আগে আমাদেরকে বোধয় আবারো কিছু শাস্ত্রীয় বিভ্রম চেখে আসতে হবে। যেমন-
সর্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোহর্হতি।। ১/১০০।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : জগতে যা কিছু ধনসম্পত্তি সে সমস্তই ব্রাহ্মণের নিজ ধনের তুল্য; অতএব সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তিরই প্রাপ্তির যোগ্য হয়েছেন।
.
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ।। ১/১০১। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণ যে পরের অন্ন ভোজন করেন, পরকীয় বসন পরিধান করেন, পরের ধন গ্রহণ করে অন্যকে প্রদান করেন, সে সবকিছু ব্রাহ্মণের নিজেরই। কারণ, ব্রাহ্মণেরই আনৃশংস্য অর্থাৎ দয়া বা করুণাতেই অন্যান্য যাবতীয় লোক ভোজন-পরিধানাদি করতে পারছে।
.
এরপরেও পরিতৃপ্তিহীন পোড়াচক্ষে যখন পরের দ্রব্য কিছুতেই মাটির ঢেলায় পরিণত না-হয়ে অপহরণের বস্তু হয়ে যায়, তখন উপায়ান্তর না-পেয়েই হয়তো উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে (মনুসংহিতা ১১/৫৫) ব্রাহ্মণের সোনা অপহরণকে মহাপাতক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পণ্ডিতেরা তো আর চুরি করেন না, করেন অপহরণ।
.
অন্যদিকে সকল জীবে আত্মজ্ঞান পোষণ কেবল পণ্ডিত কেন, সবার জন্যেই তো একটা শ্রেষ্ঠ মহৎ গুণ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। শাস্ত্র মানেই তো অতি পবিত্র মহৎ জীবন বিধান। একজন শাস্ত্রবেত্তা গুণী ব্যক্তি যেসব শাস্ত্রীয় বিধান অধ্যয়ন উপলব্ধির মাধ্যমে স্বীকৃত আত্মজ্ঞানী পণ্ডিত হয়ে ওঠেন এবং তা তাঁদের জীবনাচরণে কঠোরভাবে মান্য করে থাকেন, মনুশাস্ত্র থেকে তার আর ব্যাখ্যা না-করে কেবল কিছু উদ্ধৃতিই তুলে ধরা যাক্। তাহলেই আমাদেরও সম্যক উপলব্ধি হবে চাণক্য কথিত যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তির সকল জীবে আত্মজ্ঞান পোষণের মাহাত্ম্য প্রকৃতই কোন্ পর্যায়ে ছিলো। যেমন-
.
অন্যদিকে সকল জীবে আত্মজ্ঞান পোষণ কেবল পণ্ডিত কেন, সবার জন্যেই তো একটা শ্রেষ্ঠ মহৎ গুণ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। শাস্ত্র মানেই তো অতি পবিত্র মহৎ জীবন বিধান। একজন শাস্ত্রবেত্তা গুণী ব্যক্তি যেসব শাস্ত্রীয় বিধান অধ্যয়ন উপলব্ধির মাধ্যমে স্বীকৃত আত্মজ্ঞানী পণ্ডিত হয়ে ওঠেন এবং তা তাঁদের জীবনাচরণে কঠোরভাবে মান্য করে থাকেন, মনুশাস্ত্র থেকে তার আর ব্যাখ্যা না-করে কেবল কিছু উদ্ধৃতিই তুলে ধরা যাক্। তাহলেই আমাদেরও সম্যক উপলব্ধি হবে চাণক্য কথিত যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তির সকল জীবে আত্মজ্ঞান পোষণের মাহাত্ম্য প্রকৃতই কোন্ পর্যায়ে ছিলো। যেমন-
এতমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রƒষামনসূয়য়া।। ১/৯১।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : প্রভু ব্রহ্মা শূদ্রের জন্য একটি কাজই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন,- তা হলো কোনও অসূয়া অর্থাৎ নিন্দা না করে (অর্থাৎ অকপটভাবে) এই তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষা করা।
.
মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্।। ২/৩১।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণের নাম হবে মঙ্গলবাচক শব্দ (‘মঙ্গল’ শব্দের অর্থ ‘ধর্ম’; সেই ধর্মের সাধক ‘মঙ্গল্য’; ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাবাচক শব্দ বা ঋষিবাচক শব্দ মঙ্গলের সাধন, তাই ‘মঙ্গল্য’; যেমন- ইন্দ্র, বায়ু, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি); ক্ষত্রিয়ের নাম হবে বলসূচক শব্দ (যেমন, প্রজাপাল, দুর্যোধন, নৃসিংহ প্রভৃতি); বৈশ্যের নাম হবে ধনবাচক অর্থাৎ পুষ্টিবৃদ্ধিসমন্বিত (যেমন ধনকর্মা, গোমান, ধনপতি প্রভৃতি) এবং শূদ্রের নাম হবে জুগুপ্সিত (নিন্দা বা হীনতাবোধক, যেমন- কৃপণক, দীন, শবরক ইত্যাদি)।
.
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ ধর্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ।। ৪/৮০।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : (ব্রাহ্মণ) শূদ্রকে কোন মন্ত্রণা-পরামর্শ দেবে না। শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দান করবে না। যজ্ঞের হবির জন্য যা ‘কৃত’ অর্থাৎ সঙ্কল্পিত এমন দ্রব্য শূদ্রকে দেবে না; শূদ্রকে কোনও ধর্মোপদেশ করবে না এবং কোনও ব্রত বা প্রায়শ্চিত্ত করতেও উপদেশ দেবে না।
.
শূদ্রং তু কারয়েদ্ দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা।। ৮/৪১৩।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : ক্রীত অর্থাৎ অন্নাদির দ্বারা প্রতিপালিত হোক্ বা অক্রীতই হোক্ শূদ্রের দ্বারা ব্রাহ্মণ দাসত্বের কাজ করিয়ে নেবেন। যেহেতু, বিধাতা শূদ্রকে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।
.
ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ ধনম্।। ৮/৪১৬।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : স্মৃতিকারদের মতে ভার্যা, পুত্র ও দাস- এরা তিনজনই অধম (বিকল্পে অধন); এরা তিনজনেই যা কিছু অর্থ উপার্জন করবে তাতে এদের কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, পরন্তু এরা যার অধীন ঐ ধন তারই হবে।
.
উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ।। ১০/১২৫।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণ-পরিত্যক্ত বস্ত্র, ধানের পুলাক অর্থাৎ আগড়া (অসার ধান) এবং জীর্ণ পুরাতন ‘পরিচ্ছদ’ অর্থাৎ শয্যা-আসন প্রভৃতি আশ্রিত শূদ্রকে দেবেন।
.
শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে।। ১০/১২৯।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : ‘ধন অর্জনে সমর্থ হলেও শূদ্রকে কিছুতেই ধন সঞ্চয় করতে দেওয়া চলবে না, কেননা ধন সঞ্চয় করলে ব্রাহ্মণদের কষ্ট হয়৷ শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের পরিচর্যা না করে অবমাননা করতে পারে৷’
.
বৈদিক সংস্কৃতির অনিবার্য জীবনবিধান হিসেবে অবশ্যপালনীয় শাস্ত্রগ্রন্থ মনুসংহিতায় এরকম শাস্ত্রবিধানের অভাব নেই। ভূরিভূরি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আবার একইভাবে সংঘটিত কোন অপরাধের দণ্ড আরোপের ক্ষেত্রেও মনুশাস্ত্রে তীব্র বৈষম্য আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় না। যেমন-
পঞ্চাশদ্ ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধপঞ্চাশৎ শূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ।। ৮/২৬৮।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : (উত্তমর্ণ) ব্রাহ্মণ যদি (অধমর্ণ অনুসারে) ক্ষত্রিয়ের প্রতি আক্রোশন বা গালিগালাজ করে তা হলে তার পঞ্চাশ দণ্ড হবে, বৈশ্যের প্রতি করলে পঁচিশ পণ এবং শূদ্রের প্রতি করলে বারো পণ দণ্ড হবে।
অন্যদিকে-
যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেৎ শ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্।। ৮/২৭৯।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : শূদ্র কিংবা অন্ত্যজ ব্যক্তি (শূদ্র থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত নিকৃষ্ট জাতি) দ্বিজাতিগণকে (ব্রাহ্মণ, ক্সত্রিয়, বৈশ্য) যে অঙ্গের দ্বারা পীড়ন করবে তার সেই অঙ্গ ছেদন করে দেবে, এটি মনুর নির্দেশ।
.
স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, কোন অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে খুবই অল্পমাত্রায় অর্থদণ্ডের বিধান থাকলেও সেই একই অপরাধে বর্ণদাস শূদ্রের অপরাধী অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ কর্তনের কঠোর নির্দেশ খোদ মনুশাস্ত্রেই রয়েছে। এভাবে জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোতেও শাস্ত্রের অনিবার্য বিধানের বাইরে গিয়ে প্রচলিত সামাজিক শৃঙ্খলা ও স্থিতির স্বার্থে চাণক্য তার নীতিশ্লোকের কোথাও শাস্ত্রবিধানের পরিপন্থি কোন উপদেশ দান করেছেন কিনা তা কৌতুহলি গবেষকদের আগ্রহের বিষয় হতে পারে। তবে ব্রাহ্মণ্যশাসনাধীন তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় মনুশাস্ত্রের উপরিউক্ত অবশ্যপালনীয় শ্লোকগুলোর খুব দৃঢ় উপস্থিতির পরও আবার তৎকালীন এবং বর্তমানেও বৈদিক হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্য আরেক অবশ্যমান্য অতি পবিত্র ধর্মপুস্তক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অন্যরকম অমর ললিত বাণীও দেখা যায়-
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।। ৫/১৮।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)।
অর্থাৎ : বিদ্বান ও বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে ব্রহ্মজ্ঞানীগণ সমদর্শী হন (অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন করেন)।
কিংবা-
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।। ৬/৩২।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)।
অর্থাৎ : হে অর্জুন, যিনি সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।
.
প্রসঙ্গত এখানে ভুলে গেলে চলবে না যে, মনুশাস্ত্র হলো তৎকালীন সমাজ-শাসনের কঠোর ব্যবহারিক বিধান, যার আওতা থেকে বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু সংস্কৃতি ও সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় আইন এখনো মুক্ত হতে পারে নি কোনভাবেই। আর শ্রী শ্রী গীতা হলো সেইসব ভাগ্যবানদের কোন আয়েশী অলস মুহূর্তের পূণ্য কামানোর গদগদ মাহাত্ম্য নিয়ে পরম তৃপ্তির সাথে পঠিত ও নিজের মতো করে বিশ্লেষিত হবার এক অপূর্ব ভাবুক ধর্মগ্রন্থ। ইতিহাসই বলে দেয় আমাদের চাণক্য পণ্ডিতের কর্মযজ্ঞ ঘিরে ছিলো মনুরই বিধান শুধু। কিন্তু তাঁর নীতিশাস্ত্রে দেখি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাবুক মুহূর্তেরই ছায়া। তাই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আরোপ না করেও সকল জীবে আত্মজ্ঞান পোষণের এই নৈতিক উপদেশ তাত্ত্বিক আলোচনায় কতোটা গ্রহণযোগ্য কে জানে, কিন্তু ব্যবহারিক প্রপঞ্চে তা কেবলই এক বিভ্রম বলেই মনে হয়।
.
অবস্থা বৈগুন্যে আদিবাসী গারোদের একটা প্রবাদের কথা মনে পড়ে-
অবস্থা বৈগুন্যে আদিবাসী গারোদের একটা প্রবাদের কথা মনে পড়ে-
‘আনথাং নাদে ছিজং পিদ্দক
গিব্বিন নাদে বগা পিদ্দক।’
(নিজের বেলায় কাছিম গলা, পরের বেলায় বগের গলা)।
.
আর তৎকালীন সাধারণ জনগোষ্ঠি তথা শূদ্রদের অবস্থা তো কুড়িগ্রাম অঞ্চলের প্রচলিত সেই প্রবাদটির মতোই- ‘গরম ভাতোত নুন জোটে না, পান্তা ভাতোত ঘি !’
.
নির্মোহ সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণে চাণক্যের এই নীতিশ্লোকটি পরবর্তীকালের নীতিসাহিত্যে যথেষ্ট ছায়া ফেললেও এর সমকালীন ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ ধাঁ-ধাঁয়ই ফেলে বৈকি। তবে তৎকালীন প্রায় সমসাময়িক সামাজিক পরিস্থিতিতে বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত নীতিসাহিত্য হিসেবে ভর্তৃহরির নিম্নোক্ত নীতিশ্লোকটিকেই গ্রহণযোগ্যতার বিবেচনায় অধিকতর মোহনীয় মনে হতে পারে। কেননা বর্তমান ভাবনা-কাঠামোর আলোকে সমকালীন ব্যাখ্যা আরোপ করে এটাকে অন্তত যুগোপযোগী নীতিকথায় রূপান্তর করা সহজতর মনে হয়-
অর্থাৎ : নির্দয়তা, বিনাকারণে কলহ, পরধন ও পরস্ত্রীতে আসক্তি, সজ্জন ও সুহৃজ্জনে ঈর্ষা- এগুলো (হচ্ছে) দুর্জনদের স্বভাবসিদ্ধ (প্রবৃত্তি)।অকরুণত্বমকারণবিগ্রঃ
পরধনে পরযোষিতি চ স্পৃহা।
সুজনবন্ধুজনেষ্বসহিষ্ণুতা
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি দুরাত্মনাম্ ।। ৫২।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)।
কিং কুলেন বিশালেন গুণহীনস্তু যো নরঃ।
অকুলীনোহপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে।। ০৪।। (চাণক্যের নীতিশাস্ত্র)।
অর্থাৎ : যে ব্যক্তি গুণহীন, তার উচ্চবংশে জন্মগ্রহণেও সার্থকতা কোথায় ? বিপরীতপক্ষে, যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ না করলেও দেবতাদের দ্বারা পূজিত (সমাদৃত) হন।
.
প্রথম পাঠেই নীতিবাক্যটিতে কোন জটিলতার কারণ খুঁজে পাওয়া দুরুহ বৈকি। কেননা আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান থেকেই এর একটা সহজ সরল ব্যাখ্যা মনের মধ্যে এমনিই হাজির হয়ে যায়। কী সেই ব্যাখ্যা ? তা হলো, কেবলমাত্র উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করলেই কেউ সম্মান বা শ্রদ্ধাভাজন হয়ে যায় না। মানুষকে সে সম্মান যোগ্যতার মাধ্যমেই অর্জন করতে হয়। আর সেই যোগ্যতা অর্জন করতে হয় শাস্ত্রজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে। ফলে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ না-করেও যিনি শাস্ত্রজ্ঞ হন, লোকে তাঁকে সম্মান করে, এমনকি দেবতারাও তাঁর সমাদর করেন। অতএব উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করলে সেই বংশের যোগ্য হওয়ার জন্য নিশ্চয়ই তাঁকে প্রয়োজনীয় চর্চার মধ্য দিয়ে গুণাবলী অর্জন করতে হবে।
.
কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় সেসব অনুভূতিপ্রবণ পাঠকের জন্যে। যাঁদের সংবেদনশীল মনে এ নীতিবাক্যটির অন্তত তিনটি বিষয় কিঞ্চিৎ কড়া নাড়তে থাকে। কেননা চাণক্য তাঁর এ নীতিশ্লোকটিতে কুল বা উচ্চবংশ কথাটা গুরুত্বের সাথে আরোপ করার মাধ্যমে তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষিতে মূলত বংশমর্যাদার বিষয়টিকে গুরুত্ববহ করে তুলেছেন। অর্থাৎ সামাজিক আবহে বংশমর্যাদা একটি উল্লেখযোগ্য প্রপঞ্চ। আর এই ধারণা বা প্রপঞ্চটিকে একালে এসেও আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় পূর্ণ শক্তিতে বহাল থাকতে দেখছি আমরা। আমাদের শ্রুতিবাহুল্যে উচ্চবংশ বা উঁচু জাত ও নিম্নবংশ বা নিচু জাত শব্দ দুটো এতোটাই বহুল প্রচলিত হয়ে গেছে যে, মধ্যবংশ বা মধ্য জাত বলে কোন শব্দের ব্যবহারিক অস্তিত্ব আদৌ রয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, বংশ পরম্পরায় আমাদের সমাজটা আসলে দুটো ভাগে বিভাজিত সেই প্রাচীনকাল থেকেই। পরবর্তীকালে আমাদের এই জনবসতিতে বহু ধর্মাধর্মের আগমন-নির্গমন ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সেই বিভাজনটা রয়েই গেছে। তাই প্রাসঙ্গিক কারণেই এর উৎস খোঁজাটা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না।
.
এছাড়া আর যে দুটো বিষয় এ নীতিশ্লোকে স্থান পেয়েছে, তা হলো ব্যক্তির গুণের প্রসঙ্গ এবং শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া না-হওয়ার বিষয়টি। তবে এখানে গুণের সাথে শাস্ত্রের একটা চমৎকার একরৈখিক সম্পর্ক দেখতে পাই আমরা। অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রজ্ঞ তিনিই গুণবান হবেন, আর এর বিপরীতে শাস্ত্রে অজ্ঞ বা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি অবশ্যই গুণহীন এবং তিনি পরমার্থের অযোগ্য। এজন্যেই হয়তো সেই প্রাচীনকাল হতেই বৈদিক সমাজ-সংস্কৃতিতে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বহুল পূজিত গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে এভাবে-
.
কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় সেসব অনুভূতিপ্রবণ পাঠকের জন্যে। যাঁদের সংবেদনশীল মনে এ নীতিবাক্যটির অন্তত তিনটি বিষয় কিঞ্চিৎ কড়া নাড়তে থাকে। কেননা চাণক্য তাঁর এ নীতিশ্লোকটিতে কুল বা উচ্চবংশ কথাটা গুরুত্বের সাথে আরোপ করার মাধ্যমে তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষিতে মূলত বংশমর্যাদার বিষয়টিকে গুরুত্ববহ করে তুলেছেন। অর্থাৎ সামাজিক আবহে বংশমর্যাদা একটি উল্লেখযোগ্য প্রপঞ্চ। আর এই ধারণা বা প্রপঞ্চটিকে একালে এসেও আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় পূর্ণ শক্তিতে বহাল থাকতে দেখছি আমরা। আমাদের শ্রুতিবাহুল্যে উচ্চবংশ বা উঁচু জাত ও নিম্নবংশ বা নিচু জাত শব্দ দুটো এতোটাই বহুল প্রচলিত হয়ে গেছে যে, মধ্যবংশ বা মধ্য জাত বলে কোন শব্দের ব্যবহারিক অস্তিত্ব আদৌ রয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, বংশ পরম্পরায় আমাদের সমাজটা আসলে দুটো ভাগে বিভাজিত সেই প্রাচীনকাল থেকেই। পরবর্তীকালে আমাদের এই জনবসতিতে বহু ধর্মাধর্মের আগমন-নির্গমন ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সেই বিভাজনটা রয়েই গেছে। তাই প্রাসঙ্গিক কারণেই এর উৎস খোঁজাটা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না।
.
এছাড়া আর যে দুটো বিষয় এ নীতিশ্লোকে স্থান পেয়েছে, তা হলো ব্যক্তির গুণের প্রসঙ্গ এবং শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া না-হওয়ার বিষয়টি। তবে এখানে গুণের সাথে শাস্ত্রের একটা চমৎকার একরৈখিক সম্পর্ক দেখতে পাই আমরা। অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রজ্ঞ তিনিই গুণবান হবেন, আর এর বিপরীতে শাস্ত্রে অজ্ঞ বা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি অবশ্যই গুণহীন এবং তিনি পরমার্থের অযোগ্য। এজন্যেই হয়তো সেই প্রাচীনকাল হতেই বৈদিক সমাজ-সংস্কৃতিতে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বহুল পূজিত গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে এভাবে-
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।। ৪/৪০।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)।
অর্থাৎ : অজ্ঞ, শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন, (জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠানবিষয়ে) সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি পরমার্থের অযোগ্য হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই এবং ঐহিক সুখও নাই।
.
আর শাস্ত্রজ্ঞ বা বিদ্বান ব্যক্তি যে তিনিই যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে নিজ ধর্মে নিবিষ্ট হবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জন করবেন (মনুসংহিতা : ২/৮) তা ইতঃপূর্বে (নীতিবাক্য-০১-এ) বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তাই সে প্রেক্ষিত এখানে পুনরায় ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। তবে এই প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জনের লক্ষ্যে ধর্মের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অবগত হওয়ার উপায়টাও যে শাস্ত্রে বলে দেয়া হয়েছে তা আলোচনার সুবিধার্থে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে মনুশাস্ত্রে বলা হচ্ছে-
প্রত্যঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্ ।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা।। ১২/১০৫।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : যে ব্যক্তি ধর্মশুদ্ধি অর্থাৎ ধর্মের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অবগত হতে ইচ্ছুক তাঁর পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং নানাপ্রকার বিধিনিষেধযুক্ত স্মৃতি প্রভৃতি-শাস্ত্র- এই তিনটি প্রমাণ সম্যকরূপে বিদিত হওয়া আবশ্যক।
এবং আরো বলা হচ্ছে-
আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাহবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ।। ১২/১০৬।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : যে ব্যক্তি বেদোক্ত-ধর্মোপদেশসমূহ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী অর্থাৎ অনুকূল তর্কের সাহায্যে অনুসন্ধান করেন অর্থাৎ নিরূপণ করতে চেষ্টা করেন, তিনিই বেদের ধর্ম অর্থাৎ বেদের অর্থ অবগত হন; এর বিপরীত স্বভাব ব্যক্তি বেদার্থধর্ম বোঝে না।
.
উল্লেখ্য, এখানে ধর্ম শব্দটির অর্থ হলো বেদার্থ অর্থাৎ বেদবাক্যের তাৎপর্যবিষয়ীভূত অর্থ। অতএব আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, ধর্ম অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করার যে শাস্ত্রবিহিত জ্ঞান, সেটুকু যিনি আয়ত্ত করবেন তিনিই শাস্ত্রজ্ঞ। এবং তিনিই হবেন গুণবান। ধর্মভিত্তিক গোঁড়ামিপূর্ণ বৃত্তাবদ্ধ একটা সমাজে মানুষের মানবিক ও নৈতিক গুণাবলী গৌন হয়ে যুক্তিহীনভাবে কেবলমাত্র ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থা ও নিষ্ঠা থাকাই যে মহৎ গুণের পরিচায়ক হয়ে ওঠা, এটাই তাৎপর্যপূর্ণ এবং অনুধাবনেরও বিষয়। নীতিপ্রবক্তা পণ্ডিত চাণক্য যে আসলে এ বৃত্তের বাইরের কেউ নন, এটা বোধ করি বোঝার বাকি রাখে না। এবং আড়াই হাজার বছর পেরিয়ে একালের এই আমরা এখনো এ গণ্ডিটা কতোটা মুক্ত হতে পেরেছি তা নিজেদের জন্যেও বোঝাপড়ার বিষয়।
.
এখানে বুদ্ধিমান পাঠকের জ্ঞাতার্থে এটাও জানিয়ে রাখা আবশ্যক যে, প্রতিটা বিষয়ের উৎস সন্ধানে আমাদেরকে যেহেতু বারে বারে শাস্ত্রীয়-বিধানের আকরগ্রন্থ মনুসংহিতার দ্বারস্থ হতে হচ্ছে, তাই বেদবিহিত এই মনুশাস্ত্রের যথার্থতা নিয়ে যাতে কারো কোন সন্দেহের অবকাশ না-থাকে সে লক্ষ্যে মনুশাস্ত্রেই নির্দেশিত হয়েছে-
যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতঃ।
স সর্বোহভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ।। ১/৭।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : (যেহেতু মনু সকল বেদই সম্যকরূপে অবগত আছেন) সর্বজ্ঞানময় মনু যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও ধর্মের (যেমন, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, সংস্কারধর্ম প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণাদি বিশেষ বিশেষ বর্ণের জন্য বিহিত বিশেষ বিশেষ ধর্ম) উপদেশ দিয়েছেন, সে সবগুলিই বেদে প্রতিপাদিত হয়েছে। কারণ, সেই বেদ হলো সকল প্রকার (এমনকি যে সব বিষয় লৌকিক প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না সে সবেরও) জ্ঞানের আকর।
.
তাই এই মনুশাস্ত্রের প্রতি আস্থা অগাধ হলে নিশ্চয়ই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য বিষয় চাণক্য-কথিত কুল বা বংশমর্যাদার প্রাচীন উৎসটাও খুঁজে পেতে সহায়ক হবে। আর তা খুঁজতে হলে প্রথমত আমাদেরকে এ ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত হতে হবে যে বংশের সাথে জন্মের সম্পর্কটা অবিচ্ছেদ্য। সে সন্দেহ থাকার কথাও নয়, কেননা বংশ মানে হচ্ছে জন্ম-পরম্পরায় উত্তরাধিকার বহন। একবার জন্ম নিয়ে বংশের যে তিলকটা কপালে সেঁটে গেছে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি জন্মপ্রক্রিয়ার বাইরে অন্য কোন উপায়ে আরেকটি বংশে অনুপ্রবেশও কোনোভাবে সম্ভব নয়। প্রকৃতির একটা উল্লেখযোগ্য প্রধান জাতিগোষ্ঠি এই মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও বংশ নামের আরেকটি অদ্ভুত খাঁচায় নিজেকে আবিষ্কারের এই বিস্ময়টা আমাদেরকে আসলে তথাকথিত পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ নামের কিছু ধর্মীয় ধারণার মুখোমুখি করে দেয়। আর এই শাস্ত্রের মাহাত্ম্যই বলি কি রহস্যই বলি তা নিয়ন্ত্রণের সূত্রটা সুকৌশলে রাখা হয়েছে এক অদৃশ্য স্রষ্টা ব্রহ্মার রহস্যময় লীলার মধ্যে। আপাতত সেই রহস্য বাদ রেখে বরং বংশ লীলাটাই খোঁজা যাক। এ বিষয়ে প্রথমেই মনু বলছেন-
লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ।। ১/৩১।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : পৃথিব্যাদির লোকসকলের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এই চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করলেন।
.
কিন্তু ব্রহ্মা কর্তৃক এই বর্ণ সৃষ্টি তো আর এমনি এমনি হয়নি। পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী এজন্মে তার ফল ভোগ করার নিমিত্তেই ব্রহ্মা কর্তৃক মানবকুলে এই বর্ণসৃষ্টি। তাই শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুনির্দিষ্ট কার্যেরও ঘোষণা করা হলো-
সর্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহুরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্মাণ্যকল্পয়ৎ।। ১/৮৭।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : এই সকল সৃষ্টির অর্থাৎ ত্রিভুবনের রক্ষার জন্য মহাতেজযুক্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজের মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ- এই চারটি অঙ্গ থেকে জাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের পৃথক পৃথক কার্যের ব্যবস্থা করে দিলেন।
.
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ।। ১/৮৮।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : অধ্যাপন, স্বয়ং অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (উপহার বা দান-সামগ্রি গ্রহণ)- এই ছয়টি কাজ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দেশ করে দিলেন।
.
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েম্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।। ১/৮৯।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, নৃত্যগীতবনিতাদি-বিষয়ভোগে অনাসক্তি, এই কয়েকটি কাজ ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়গণের জন্য সংক্ষেপে নিরূপিত করলেন।
.
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।। ১/৯০।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : পশুদের রক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য (স্থলপথ ও জলপথ প্রভৃতির মাধ্যমে বস্তু আদান-প্রদান করে ধন উপার্জন), কুসীদ (বৃত্তিজীবিকা- টাকা সুদে খাটানো) এবং কৃষিকাজ- ব্রহ্মা কর্তৃক বৈশ্যদের জন্য নিরূপিত হল।
.
এতমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রƒষামনসূয়য়া।। ১/৯১।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : প্রভু ব্রহ্মা শূদ্রের জন্য একটি কাজই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন,- তা হলো কোনও অসূয়া অর্থাৎ নিন্দা না করে (অর্থাৎ অকপটভাবে) এই তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষা করা।
.
অর্থাৎ উপরিউক্ত শ্লোকগুলো থেকে আমরা এটা বুঝে যাই যে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা গোটা বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করে তা সুষ্ঠুভাবে রক্ষাকল্পে চারটি বর্ণ সৃষ্টি করলেন- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের আবার দুটো ভাগ- এক ভাগে প্রথম তিনটি যথাক্রমে উচ্চতম, উচ্চতর ও উচ্চ বর্ণ, আর দ্বিতীয় ভাগে চতুর্থটি অর্থাৎ শূদ্র হচ্ছে নিম্নবর্ণ, যে কিনা উচ্চবর্ণীয়দের সেবাদাস। আবার ব্রাহ্মণ, যে কিনা কোন শারীরিক শ্রমের সাথে কোনভাবেই জড়িত নয়, সকল বর্ণের শীর্ষে। শুধু শীর্ষেই নয়, ক্ষমতার এতোটাই কল্পনাতীত উচ্চ অবস্থানে অবস্থিত যে, জগতের সবকিছুর মালিক বা প্রভুও হচ্ছে ব্রাহ্মণ-
উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।। ১/৯৩।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ মানে পবিত্রতম মুখ থেকে উৎপন্ন বলে, সকল বর্ণের আগে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হওয়ায়, এবং বেদসমূহ ব্রাহ্মণকর্তৃক রক্ষিত হওয়ার জন্য (বা বেদসমূহ ব্রাহ্মণেরাই পঠন-পাঠন করেন বলে)- ব্রাহ্মণই ধর্মের অনুশাসন অনুসারে এই সৃষ্ট জগতের একমাত্র প্রভু।
তাই-
ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে।। ১/৯৯।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করা মাত্রই পৃথিবীর সকল লোকের উপরিবর্তী হন অর্থাৎ সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। কারণ, ব্রাহ্মণই সকলের ধর্মকোষ অর্থাৎ ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য প্রভুসম্পন্ন হয়ে থাকেন।
.
উদ্ধৃত পবিত্র শ্লোকগুলো থেকে নিশ্চয়ই কুল অর্থাৎ বংশ বা বর্ণের ক্রমিক শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায় আমাদের। তবু অজ্ঞানী বা মূর্খ-দৃষ্টিতে শরীরের অবস্থান অনুযায়ী মুখ, বাহু, উরু ও পায়ের পবিত্রতার রকমফের নিয়ে যাতে সন্দেহের কোনরূপ অবকাশই না-থাকে, সে লক্ষ্যে মনুশাস্ত্র সবার মঙ্গলার্থে তা স্পষ্ট করে দিয়েছে এভাবে-
ঊর্ধ্বং নাভের্মেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্তিতঃ।
তস্মান্মেধ্যতমং ত্বস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা।। ১/৯২।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : (পুরুষ ব্রহ্মা আপাদ-মস্তক সর্বতোভাবে পবিত্র)। (তবুও) পুরুষের নাভি থেকে উর্ধ্বপ্রদেশ পবিত্রতর বলে কথিত। তা অপেক্ষাও আবার পুরুষের মুখ আরও পবিত্র- একথা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বলেছেন।
.
উল্লেখ্য, এখানে পুরুষ বলতে কিন্তু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকেই বোঝানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে নাভির উর্ধ্বপ্রদেশ পবিত্রতর অংশ। তাহলে নাভির নিম্নপ্রদেশ ? পাদ বা পায়ের অবস্থান তো নিম্নেই। সবখানে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে হয় না, কারণ শাস্ত্রগ্রন্থ তো নিম্নবর্ণীয় মূর্খদের জন্যে নয়। পুরুষ ব্রহ্মা আপাদ-মস্তক সর্বতোভাবে পবিত্র হলেও তাঁর পা থেকে উৎপন্ন শূদ্রের বংশ বা বর্ণের নিচত্বে যে কোন সন্দেহ থাকা চলবে না, সেটাও শাস্ত্র-বিধানে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে-
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোহপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি।। ৮/৪১৪।। (মনুসংহিতা)।
অর্থাৎ : প্রভু তাঁর অধীনস্থ শূদ্রকে দাসত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেও শূদ্র দাসত্ব কর্ম থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। দাসত্বকর্ম তার স্বভাবসিদ্ধ কর্ম (অর্থাৎ জন্মের সাথে আগত)। তাই ঐ শূদ্রের কাছ থেকে কে দাসত্ব কর্ম সরিয়ে নিতে পারে ?
.
বড় ভয়ঙ্কর কথা ! অতএব আশা করা যায় এতোসব শাস্ত্র-উদ্ধৃতির ভারে ভারাক্রান্ত হতে হতে নিশ্চয়ই আমরা মানবকুলে বংশমর্যাদা নামের সৃষ্ট প্রপঞ্চ বা রহস্যের উৎস-সূত্রটা একটু হলেও অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছি। আমাদের আপাত প্রয়োজন এটুকুই। আর তা সম্বল করেই আরেকটু ভালোভাবে অনুধাবনের উদ্দেশ্যে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের রচিত চাণক্যের উদ্ধৃত নীতিবাক্যটির কাছে আবার ফিরে যেতে পারি আমরা।
নীতিবাক্যে বলা হচ্ছে- যে ব্যক্তি গুণহীন, তার উচ্চবংশে জন্মগ্রহণেও সার্থকতা কোথায় ? বিপরীতপক্ষে, যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ না করলেও দেবতাদের দ্বারা পূজিত (সমাদৃত) হন।
.
অর্থাৎ কোন ব্যক্তির উচ্চবংশে জন্ম নিয়ে বংশ-নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় বেদবিহিত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বুৎপত্তি অর্জন করার মাধ্যমে গুণবান হওয়ার যে কর্তব্যকাজ নির্দিষ্ট করা আছে, তা যথাযথ না-হলে ওই গুণহীন ব্যক্তির উচ্চবংশে জন্মগ্রহণের কোন সার্থকতা থাকে না। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী চাণক্যের প্রথমাংশের সাথে আমাদের মতানৈক্য হওয়ার সুযোগ নেই বলতে হবে। কিন্তু অন্যদিকে উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম না-হয়ে শূদ্রজাত নীচ-বংশে জন্ম নিয়ে কোন ব্যক্তির শাস্ত্রজ্ঞ হওয়ার সুযোগ আদৌ কি শাস্ত্রগ্রন্থে রাখা হয়েছে ? শাস্ত্রবাক্য শোনাও তো তার জন্যে অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। কিভাবে সে গুণবান শাস্ত্রজ্ঞ হবে ? সেক্ষেত্রে চাণক্যের দ্বিতীয়াংশের এই বিভ্রমের উত্তর হতে পারে এরকম যে, ব্রাহ্মণ না-হয়ে হয়তোবা শাস্ত্র অধ্যয়নের অনুমোদপ্রাপ্ত অন্য কোন দ্বিজ যেমন ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেও শাস্ত্রজ্ঞ হওয়ার সুযোগ রয়েছে। মোটকথা ব্রহ্মার উর্ধ্বাঙ্গের যেকোন অঙ্গ থেকে উৎপন্ন উচ্চবর্ণীয় দ্বিজদের নিজেদের মধ্যেই এই সুবিধা ভাগাভাগির একটা কৌশলই এই নীতিবাক্যে প্রতিবিম্বিত হতে দেখি আমরা। এখানে আসলে নিচ-জাত নিম্নবংশীয় শূদ্র ও অন্যান্য অন্ত্যজদের গুণবান হওয়ার উপায় বা স্বীকৃতির কোন সুযোগই রাখা হয়নি। এটাকেই যদি এ নীতিবাক্যের গোপন মর্মার্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাতে কি খুব অন্যায় হবে ?
.
খুব সুস্পষ্ট না-হলেও সুপ্তভাবে এই ইঙ্গিতই পরিলক্ষিত হয় কাছাকাছি সময়কালের একই আবহের অন্য নীতিকাব্য স্রষ্টা ভর্তৃহরির নীতিশতকেও-
পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে !
স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্ ।। ৩২।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)।
অর্থাৎ : পরিবর্তনশীল (এই জগৎ) সংসারে মৃত কে-ই বা না জন্মগ্রহণ করে (অর্থাৎ কে-ই বা না মরে আর কে-ই বা না জন্মে, কিন্তু একমাত্র) সে(-ই) জন্মেছে (অর্থাৎ তার জন্মই সার্থক) যার জন্মের দ্বারা (তার) বংশ (প্রভূত) উন্নতি লাভ করেছে।
.
এই বংশবত্তার জয়গান কেবল যে চাণক্য বা ভর্তৃহরির ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা নয়, পরবর্তীকালের ধর্মের পট্টি বাঁধা চোখের অন্যান্য নীতিকথকদের মধ্যেও সমভাবে দৃষ্ট হয় তা। যেমন ‘উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহে’র একটি শ্লোকেও এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-
গুণাঃ সর্বত্র পূজ্যন্তে পিতৃবংশো নিরর্থকঃ।
বসুদেবং পরিত্যজ্য বাসুদেব উপাস্যতে।। (উদ্ভট-সাগর)।।
অর্থাৎ : মানুষের গুণই সর্বত্র বিচার্য বা পূজিত- পিতৃবংশ নয়। ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের কথা সর্বলোকমুখে; সবার উপাস্য। বসুদেবের কথা ক’জন জানে ?
.
আসলে এই ভূখণ্ডের পুরনো জনগোষ্ঠির প্রাচীন জনসংস্কৃতিতে পরবর্তীকালে বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির মিশেল ঘটলেও আশরাফ-আতরাফ বা উচ্চ-নীচ বংশ-মর্যাদা বা মর্যাদাহীনতার বহু কল্পকাহিনী ও প্রচলিত সমাজ-মনস্কতায় এই সামাজিক বিভেদটা বিলুপ্ত না হয়ে বরং আরো জোরালো হয়েই জেঁকে বসেছে বিভিন্ন চেহারায় বিভিন্ন মোড়কে। তাই হয়তো চাণক্যের এই ধর্মীয় সামাজিক বৈষম্যদায়ী নীতিশ্লোকটা বর্তমান জনমানসের কাছে আগ্রহ হারায় নি এখনো। এর প্রধান কারণ হয়তো এটাই যে, ধর্মীয় আধিপত্যবাদী মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার আগল থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি আজো।
.
ভর্তৃহরি
সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য রক্ষিত না হওয়ায় সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম কবিশ্রেষ্ঠ ভর্তৃহরির জীবন-চরিতের জন্যেও জনশ্রুতি-নির্ভর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিভিন্ন জনশ্রুতি-প্রসূত তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতককে ভর্তৃহরির অধিষ্ঠানকাল হিসেবে চিহ্নিত করেন। কিংবদন্তী অনুযায়ী- ভর্তৃহরি ছিলেন মালব দেশের অধিবাসী এবং জাতিতে ক্ষত্রিয়। রাজপরিবারে জন্মগ্রহণকারী ভর্তৃহরির পিতার নাম ছিলো গন্ধর্ব সেন। গন্ধর্ব সেনের দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রীর পুত্র ভর্তৃহরি এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুত্র বিক্রমাদিত্য- যার নামে ‘সম্বৎ’ সন বা ‘বিক্রমাব্দ’ প্রচলিত। উল্লেখ্য, বিক্রম সম্বৎ গণনা শুরু হয় ৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে।বিক্রমাদিত্যের মা ছিলেন মালব দেশের তৎকালীন রাজধানী ধারা নগরের রাজকন্যা। ধারারাজের কোন পুত্র সন্তান না-থাকায় উভয় দৌহিত্র অর্থাৎ ভর্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্যকে তিনি তুল্যস্নেহে পরিপালন করেন এবং যথাসময়ে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী করে তোলেন।
.
স্বাভাবিক স্নেহবশতই ধারাপতি একসময় আপন দৌহিত্র বিক্রমাদিত্যকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করার অভিলাষ করেন এবং বিক্রমাদিত্যকে তাঁর সংকল্পের কথা জানান। জ্যেষ্ঠ বর্তমানে তিনি সিংহাসনে বসতে অনিহা প্রকাশ করায় তাঁর যুক্তি ও ঔদার্যে মুগ্ধ হয়ে ধারাপতি ভর্তৃহরিকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন অনুজ বিক্রমাদিত্য। এর কিছুকাল পরে তাঁরা মালবের রাজধানী ধারানগর থেকে উজ্জৈন-এ স্থানান্তর করেন।
.
বিক্রমাদিত্যের সুযোগ্য মন্ত্রণায় রাজ্য নির্বিঘ্নেই চলছিলো এবং প্রজারা সুখেই দিনাতিপাত করছিলো। বিক্রমাদিত্যের সঠিক ও সফল পরিচালনার জন্য ভর্তৃহরিকে প্রায় কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টি দিতে হতো না বলে এই সুযোগে ভর্তৃহরি মদ ও নারীতে আসক্ত হয়ে অন্তঃপুরে নারীসঙ্গ ও নারীসম্ভোগেই দিন কাটাতে লাগলেন। বিক্রমাদিত্য এ বিষয়ে তাঁকে বহুবার সাবধান করে রাজকার্যের প্রতি মনোসংযোগ করতে পরামর্শ দিলেনও তিনি তাতে কর্ণপাত না করে উল্টো বিক্রমাদিত্যের প্রতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠতে লাগলেন। এমনিভাবে ভর্তৃহরি অনন্ত বিলাসের মধ্য দিয়ে ক্রমশ অধঃপাতের দিকে এগিয়ে গেলেন। অবস্থা সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছলে কোনও এক নারীঘটিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ফলে পরস্পরের সৌভ্রাতৃত্ব শত্রুতায় পর্যবসিত হয় এবং স্ত্রী (বা প্রেমিকা)-র পরামর্শে ভর্তৃহরি বিক্রমাদিত্যকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত ও নির্বাসিত করেন।
.
বিক্রমাদিত্যকে পদচ্যুত ও নির্বাসিত করে ভর্তৃহরি নির্বাধায় সুরা ও নারীভোগে নিমজ্জিত হন। এদিকে বিক্রমাদিত্যকে অপসারণ করায় এবং তাঁর অপশাসনে প্রজারা তাঁর প্রতি বিক্ষুব্ধ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রজাদের স্বেচ্ছাচারিতায় সমগ্র মালবদেশ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় ছেয়ে যায়।
.
অন্য এক তথ্যে ‘অর্বাচিনকোষ’ মতে ভর্তৃহরির পিতা ছিলেন একজন গন্ধর্ব। তাঁর নাম বীরসেন। বীরসেনের স্ত্রী অর্থাৎ ভর্তৃহরির মা সুশীলা ছিলেন জম্বুদ্বীপরাজের একমাত্র কন্যা। ভর্তৃহরিরা ছিলেন চার ভাই-বোন, যথাক্রমে- ভর্তৃহরি, বিক্রমাদিত্য, সুভতবীর্য এবং ময়নাবতী। ধারণা করা হয় এই ময়নাবতীই ছিলেন বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা গোপিচন্দের জননী। ভর্তৃহরির মাতামহ জম্বুদ্বীপরাজের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র ভর্তৃহরিকে তিনি তাঁর রাজ্য দান করেন। ভর্তৃহরি তাঁর রাজধানী জম্বুদ্বীপ হতে উজ্জৈন-এ স্থানান্তরিত করে বিক্রমাদিত্যকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং সুভতবীর্যকে তাঁর প্রধান সেনাপতি করেন।
.
পণ্ডিত শশগিরি শাস্ত্রী প্রবর্তিত অন্য এক প্রচলিত মতানুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত নামে জনৈক ব্রাহ্মণের চারবর্ণের চারজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে- ব্রাহ্মণ জাতীয়া ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ভানুমতী, বৈশ্যা ভাগ্যবতী এবং শূদ্রা সিন্ধুমতী। এই চার স্ত্রীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের চারজন পুত্র জন্মে, যথাক্রমে- বররুচি, বিক্রমার্ক, ভট্টি ও ভর্তৃহরি। বিক্রমার্ক রাজা হন এবং ভট্টি (মতান্তরে ভট্টি ও ভর্তৃহরি) তাঁর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত হন।
.
উপরোক্ত এই তিন ধরনের পরস্পর-সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যময় তথ্যপুঞ্জি থেকে এখন পর্যন্ত কোন্ তথ্যটি সঠিক তা নির্ধারণ করা দুরুহ হলেও সাদৃশ্যটুকু থেকে আমরা অন্তত এটুকু ধারণা করতে পারি যে- ভর্তৃহরি হয়তো মাতামহের রাজ্য পেয়ে একজন রাজা বা রাজপুরুষ ছিলেন, ফলে রাজ্য বা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বিক্রমার্ক বা বিক্রমাদিত্য তাঁর ভাই ছিলেন।
.
ভর্তৃহরির দাম্পত্যজীবন নিরঙ্কুশ সুখের ছিলো না। দাম্পত্য জীবনে তিনি যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিনী স্ত্রীর দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন তা তাঁর নামে প্রচলিত চমৎকার একটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায়-
একদিন জনৈক ব্রাহ্মণ পুত্রলাভের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রসন্ন চিত্তে রাজা ভর্তৃহরিকে একটি দৈব ফল দান করেন- যে ফল ভক্ষণে আয়ু বৃদ্ধি পাবে। রাজা এই অসাধারণ ফলটি নিজে না খেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী অনঙ্গসেনাকে দিলেন। অনঙ্গসেনার আবার এক গোপন প্রেমিক ছিলো- ফলটি তিনি তাকে দিলেন। সেই প্রেমিক আবার এক পতিতার প্রণয়াসক্ত ছিলো- তাই ফলটি সে ওই পতিতাকে দিলো। সেই পতিতা আবার মনে মনে রাজা ভর্তৃহরিকে ভালোবাসতো। ‘এই ফল ভক্ষণে রাজা দীর্ঘায়ু হলে রাজ্যের লাভ’- এরকম চিন্তা করে সে তাই ফলটি রাজাকেই দিয়ে দিলো। স্ত্রীকে দেয়া ফলটি পুনরায় পতিতার হাত থেকে ফিরে পেয়ে ভর্তৃহরি যারপর নেই বিস্মিত হলেন। স্ত্রী অনঙ্গসেনাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। এতে ভর্তৃহরি হৃদয়ে মর্মান্তিক বেদনা বোধ করলেন। প্রাণাধিক প্রিয়তমা স্ত্রীর এরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত ভর্তৃহরি ভাবলেন-
যাং চিন্তয়ামি সততং মরি সা বিরক্তা
সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং স জনোন্যসক্তঃ।
অস্মৎকৃতে চ পরিশুষ্যতি কাচিন্যা
ধিক্ তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ।। ০২।। (ভর্তৃহরি নীতিশতক)
অর্থাৎ : আমি যার ভজনা করি সে আমার প্রতি বিরক্ত, অন্য পুরুষ তার মনের মানুষ। সেই পুরুষ আবার অন্য (বারবণিতা) নারীর প্রতি অনুরক্ত। আমাকে পেয়েও আনন্দ পায় সেই অন্য নারী। ধিক্ সেই নারীকে, ধিক সেই পুরুষকে, ধিক সেই বারবণিতাকে, ধিক কামদেবকে যার প্রভাবে এসব সংঘটিত হচ্ছে, এবং ধিক আমাকেও।
.
ভর্তৃহরি স্ত্রীকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। অনঙ্গসেনাও এই কলঙ্কিত জীবনের ভার বইতে না পেরে আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি লাভ করেন। স্ত্রীর এই আত্মহত্যার ঘটনায় ভর্তৃহরির হৃদয় পুনরায় আহত হয়। ভর্তৃহরির এই দুঃসময়ে সত্যিকারের পতিভক্তি ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের আধার হয়ে এগিয়ে আসেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী কোমলহৃদয়া পিঙ্গলা। পিঙ্গলার অসাধারণ সেবাযত্নে ভর্তৃহরি ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং আবার যেন নতুন জীবনে পদার্পণ করে পরম সুখে কাটতে থাকে তাঁর দাম্পত্য জীবন।
.
কিন্তু বিধি বাম ! এ সময়ে ঘটে তাঁর দ্বিতীয় মর্মান্তিক ঘটনা, যার কারণে তিনি সংসার-বিবাগী হয়ে যান এবং রচনা করেন ‘বৈরাগ্যশতক’। জনশ্রুতি অনুযায়ী ঘটনাটি হলো-
ভর্তৃহরি একদিন শিকার সন্ধানে বনে যান। সেখানে গিয়ে তিনি সাংঘাতিক এক দৃশ্য দেখতে পান। দেখেন- জনৈক ব্যাধ (শিকারী) বাণ দ্বারা একটি হরিণকে বধ করে সে নিজেও সেখানেই সর্পাঘাতে মৃত্যুবরণ করে। তিনি আশ্চর্য বিস্ময়ে দেখলেন- কিছুক্ষণ পর হরিণীটি এসে মৃত হরিণটির নিস্তব্ধ অসার দেহের উপর পতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। শুধু তা-ই নয়, আরও কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলো- ওই শিকারীর স্ত্রী এসে চিতাগ্নিতে স্বামীসহ ভস্মীভূত হয়ে যায়।
.
এই দৃশ্য ভর্তৃহরির হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে এবং তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়েন। মৃগয়া পরিত্যাগ করে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাণী পিঙ্গলাকে অরণ্যের সেই বিস্ময়কর ঘটনা সবিস্তারে শোনান। রাণী পিঙ্গলা সমস্ত ঘটনা শুনে বলেন- পতির বিরহে সতী নারী আত্মাহুতি দেবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, বরং প্রকৃত সতী যে- এরূপ আত্মাহুতিতে তার আগুনেরও প্রয়োজন হয় না।
পিঙ্গলার এ কথায় রাজা আরও বিস্মিত হন। তাঁর মনে একটু সন্দেহেরও সৃষ্টি হয়। তাই তিনি সঙ্কল্প করেন- পিঙ্গলার পতিভক্তির পরীক্ষা নেবেন।
.
পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজা কয়েকদিন পরে পুনরায় মৃগয়ায় বের হলেন। মৃগয়ায় গিয়ে নিজের পোশাক-পরিচ্ছদে রক্ত মাখিয়ে স্বীয় অনুচর দ্বারা রাজধানীতে রাণী পিঙ্গলার কাছে পাঠিয়ে দেন। অনুচর রাণীকে রাজার রক্তাপ্লুত পোশাক অর্পণ করে নিবেদন করে যে- বাঘের হাতে রাজার মৃত্যু হয়েছে, এই তাঁর রক্তাক্ত পরিচ্ছদ। সরলপ্রাণা পিঙ্গলা আকস্মিক এ মর্মান্তিক সংবাদে প্রথমে স্তব্ধ হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর শান্তভাবে রাজার রক্তমাখা পরিচ্ছদ হাতে নিয়ে সেগুলি মাটিতে রেখে অন্তিম প্রণতি জানান এবং ভূমিতে শায়িত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
.
রাজধানীতে ফিরে এসে ভর্তৃহরি এই হৃদয় বিদারক ঘটনা শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। আপন দোষে তিনি পিঙ্গলাকে হারিয়েছেন- এ কারণেই তাঁর ব্যথা আরও বেশি করে অনুভূত হতে লাগলো। তিনি বারবার নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। পরপর দু’বার প্রিয়তমা স্ত্রীদের দ্বারা এভাবে মর্মাহত হয়ে সংসারের প্রতি ভর্তৃহরির মোহ কেটে যায়। শেষপর্যন্ত সংসার ছেড়ে বৈরাগ্য গ্রহণ করে তিনি অরণ্যে গমন করেন।
.
ভর্তৃহরি বিতর্ক
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ‘ভট্টি’ ও ‘ভর্তৃ-হরি’ নামে তিনজন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং এ তিনজনই কবি। ভট্টির রচনা ‘ভট্টকাব্য’ বা ‘রাবণবধ’ একটি মহাকাব্য। প্রথম ভর্তৃহরির রচনা ‘শতকত্রয়’- শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক। আর দ্বিতীয় ভর্তৃহরির রচনা হলো পতঞ্জলির মহাভাষ্যের উপর ব্যাকরণদর্শন জাতীয় গ্রন্থ ‘বাক্যপদীয়’। এ তিনজনই একই ব্যক্তি না কি পৃথক তিনজন কবি ছিলেন- এ নিয়ে পণ্ডিত-গবেষকদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক রয়েছে।
.
কেউ বলেন এঁরা তিনজন পৃথক ব্যক্তি ((-M.R.Kale), কেউ বলেন এঁরা তিনজন একই ব্যক্তি (-A.A.Mackonell ও ড. রামেশ্বর শ’)। আবার কারো মতে ভট্টি এবং শতকরচয়িতা ভর্তৃহরি এক এবং বাক্যপাদীয়কার ভর্তৃহরি ভিন্ন ব্যক্তি (-ড. বিধানচন্দ্র ভট্টাচার্য)। এ মতের বিরোধিতা করে আবার কেউ কেউ বলেন- ভট্টি এবং শতককার ভর্তৃহরি এক নন (-S.N.Dasgupta, S.K.De, Krishna Chitanya, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী এবং জাহ্নবীচরণ ভৌমিক)। শতককার ভর্তৃহরি এবং বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি একই ব্যক্তি বলেও মতামত প্রকাশ করেন কেউ কেউ (-জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী এবং Krishna Chitanya)। আবার দুই ভর্তৃহরি এক- এই মতকেও স্বীকার করেন নি কেউ কেউ- (Prof,K.B.Pathak Ges K.T.Telang)। এভাবে বর্তমান সময় পর্যন্ত আরও অনেক গবেষকই এ বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন।
.
চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং (I-tsing) ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভ্রমণে আসেন। জানা যায়, তিনি তাঁর বিবরণীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে গেছেন যে, তাঁর আগমনের ৪০ বৎসর পূর্বে (৬৫১ খ্রিঃ) বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি (ভর্তৃহরি) ছিলেন একজন বৌদ্ধ এবং ‘বাক্যপদীয়’ নামক গ্রন্থটি তাঁরই রচিত। এই পরিব্রাজকের বিবরণীতে জনৈক ভর্তৃহরি সম্পর্কে এক চমৎকার ঘটনা যায়। তিনি (ভর্তৃহরি) নাকি সংসার ছেড়েও সংসারের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। সন্ন্যাসজীবনে তিনি এক সময় বৌদ্ধ সঙ্ঘে আশ্রয় নেন। কিন্তু যখনই সংসারের সুখ-দুঃখের কথা মনে পড়তো তখনই ছুটে যেতেন সংসার জীবনে। এজন্য একটি গাড়িও না-কি সর্বদা প্রস্তুত থাকতো যাতে ইচ্ছে মতো তিনি সংসারে ফিরে যেতে পারেন। এমনিভাবে ভর্তৃহরি না-কি সাতবার বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগ দিয়েছেন এবং সাতবার সঙ্ঘের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। এই ভর্তৃহরি শতককার ভর্তৃহরি না হয়ে বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, কারণ শতককার ভর্তৃহরি বৌদ্ধ ছিলেন না, ছিলেন শৈব।
.
ভট্টি বা শতককার ভর্তৃহরি কেউ-ই বৌদ্ধ ছিলেন না। তাঁদের রচনায় এমন কথা বা প্রামাণ্য তথ্য নেই যার দ্বারা এটা অনুমিত হতে পারে যে, তাঁদের রচয়িতা বৌদ্ধ কবি। ভট্টির মহাকাব্যের (ভট্টিকাব্য বা রাবণবধ) ঘটনা রামায়ণাশ্রয়ী এবং তার নায়ক স্বয়ং রাম- হিন্দু ধর্মের একজন আদর্শ পুরুষ। রাম হিন্দুদের কাছে বিষ্ণুর অবতার বলেই খ্যাত। তাছাড়া ভট্টির কাব্য-রচনার পেছনে প্রচলিত কিংবদন্তী থেকেও বুঝা যায় যে তিনি একজন বেদজ্ঞ হিন্দু ছিলেন। অন্যদিকে বৌদ্ধরা বেদবিরোধী নাস্তিক।
.
আর শতককার ভর্তৃহরি যে হিন্দু ছিলেন এর বড় প্রমাণ তাঁর শতকত্রয়। নীতিশতকের শুরুতেই তিনি ব্রহ্মকে নমস্কার জানিয়েছেন ‘নম শান্তায় তেজসে’ বলে-
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নানন্তচিন্মাত্রমূর্তয়ে।
স্বানুভূত্যেকমানায় নমঃ শান্তায় তেজসে।। ০১।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : দিক-কালাদি দ্বারা যাঁর পরিমাপ করা যায় না, যিনি অনন্ত; জ্ঞাময় যাঁর আকৃতি (শরীর) (এবং) আপন উপলব্ধি-ই যাঁর একমাত্র প্রমাণ (অর্থাৎ আপন উপলব্ধি-ই যাঁকে জানার একমাত্র উপায়) (সেই) শমগুণবিশিষ্ট জ্যোতির্ময় (ব্রহ্ম)-কে নমস্কার।
.
নীতিশতকের এই নান্দীশ্লোক ছাড়াও আরও অনেক শ্লোকেই তিনি ব্রহ্মসহ অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবতা এবং অবতার সম্পর্কে বলেছেন। নীতিশতকে ভর্তৃহরি মানুষের আরাধ্য দেবতা হয় শিব অথবা কেশব (বিষ্ণু) বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন-
একো দেবঃ কেশবো বা শিবো বা
একং মিত্রং ভূপতির্বা যতির্বা।
একো বাসঃ পত্তনে বা বনে বা
একা ভার্যা সুন্দরী বা দরী বা।। বিবিধ-১১।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : (এ সংসারে মানুষের) দেবতা একজনই (হওয়া উচিত)- হয় বিষ্ণু, না হয় শিব; সুহৃদ একজনই- রাজা অথবা যোগী; বাসস্থান একটাই- নগর অথবা বন, (এবং) স্ত্রী একজনই- সুন্দরী যুবতী অথবা গিরিগুহা।
.
এভাবে শতককার ভর্তৃহরি তাঁর অন্য রচনা শৃঙ্গারশতকের শুরুতে স্মরণ করেছেন হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে ‘শম্ভুস্বয়ম্ভূহরয়ঃ’, এবং নান্দী ব্যতীত আরও অনেক জায়গায় তিনি ‘ব্রহ্মা’ সহ হিন্দু দেব-দেবীর কথা বলেছেন। আর বৈরাগ্যশতকে তিনি প্রথমেই আত্মনিবেদন করেছেন সমস্ত ‘অজ্ঞান-অন্ধকারের… জ্ঞানালোকস্বরূপ ভগবান শিব’-এর পায়ে ‘…মোহতিমি… জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ’। এছাড়াও বৈরাগ্যশতকের বিভিন্ন জায়গায় শ্লোকে শিবের অর্চনা ও তৎপদে আত্মনিবেদনের কথা বলেছেন।
.
আবার গবেষকদের মতে শতকত্রয় এবং ভট্টিকাব্যের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকেও এটা প্রতীয়মান হয় না যে, এগুলি একই ব্যক্তির রচনা। ভট্টিকাব্যের রচয়িতা একজন বৈয়াকরণ হওয়ায় ব্যাকরণের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় ভট্টিকাব্য একটি সার্থক রচনা, সাহিত্যের দিক থেকেও একই কথা প্রযোজ্য। এছাড়া কবি নিজেই তাঁর কাব্যপাঠের ব্যাপারে চমৎকার হুশিয়ারী জ্ঞাপন করেছেন এ বলে যে- ব্যাকরণে উৎসাহী পাঠকের কাছে এই কাব্য উজ্জ্বল দীপতুল্য কিন্তু ব্যাকরণ-জ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে এটি অন্ধের হাতে দর্পণের মতো- ‘দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোয়ং শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্’। কিংবা-
ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্ ।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া।।
অর্থাৎ : আমার এই কাব্য ব্যাখ্যা দ্বারা বোধ্য; ইহা সুধীগণের উৎসব স্বরূপ; দুর্মেধা ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
.
ভট্টিকাব্য রচয়িতার এই হুঁশিয়ারি হয়তো যথার্থই। কিন্তু শতকত্রয় সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। ভট্টিকাব্যের তুলনায় শতকত্রয় নিতান্তই কাঁচা হাতের লেখা বলে মনে হয়। শতকত্রয়ের ভাষা সহজ-সরল ও সহজবোধ্য, সকলেরই এতে প্রবেশাধিকার রয়েছে। শতকত্রয়ে ব্যাকরণিক নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য নয়। এসব কারণেই সহজে স্বীকার করার উপায় নেই যে, শতকত্রয় এবং ভট্টিকাব্য একই ব্যক্তির রচনা।
.
আবার কিংবদন্তীপ্রসূত জীবনচরিত এবং শতকত্রয়ের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, ভর্তৃহরি ছিলেন একজন ক্ষত্রিয়, পক্ষান্তরে ভট্টি ছিলেন ব্রাহ্মণ। ভর্তৃহরি ছিলেন রাজা বা রাজপুরুষ, কিন্তু ভট্টি ছিলেন বলভীরাজের পোষ্য কবি। বলভীর রাজা শ্রীধরসেনের কিংবা তাঁর পুত্র নরেন্দ্রের সভাকবি ছিলেন ভট্টি (খ্রিঃ ৪৯৫-৬৪১-এর মধ্যে যে-কোন এক সময়ে), এবং সেখানে থেকেই তিনি ভট্টিকাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু ভর্তৃহরি নিজেই উজ্জৈন বা উজ্জয়িনীর রাজা থেকে থাকলে এবং পরবর্তীকালে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হয়ে থাকলে তিনি অন্য রাজার সভাকবি হতে যাবেন এমনটা কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।
.
শতকত্রয় বিশেষত বৈরাগ্যশতক থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভর্তৃহরি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন এবং বাকি জীবন অরণ্যে-আশ্রমেই অতিবাহিত করেছিলেন। নীতিশতকের একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে-
কুসুমস্তবকস্যেব দ্বয়ী বৃত্তির্মনস্বিনঃ।
মূর্ধ্নি বা সর্বলোকস্য বিশীর্যেত বনেথবা।। ৩৩।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : ফুলের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিদেরও দুটি মাত্র গতি হয়- হয় সর্বলোকের মস্তকে অবস্থান অথবা অরণ্যে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যাওয়া।
.
মর্মার্থ দাঁড়ালো- সংসারে যারা সুখ না পায় তাদের জন্য অরণ্যই একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাই বোধ করি সমগ্র বৈরাগ্যশতক জুড়ে এই আকুতি দেখা যায়- অরণ্যে গঙ্গাতীরে কিংবা হিমালয়ের কোন গুহাগহ্বরে বসে ‘শিব শিব’ মন্ত্র জপ করতে করতে শিবত্ব অর্জন করার। তাছাড়া বৈরাগ্যশতকের একটি শ্লোকে তাঁর স্পষ্ট উক্তি দেখতে পাই-
‘আমরা ভিক্ষাণ্ন ভোজন করি, দিক বস্ত্র পরিধান করি (দিগম্বর থাকি), ভূতলে শয়ন করি, সুতরাং রাজাদের কাছে আমাদের কী প্রয়োজন ?’- ।। ৫৬।। (ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতক)
অর্থাৎ যে-রাজ্য ত্যাগ করে তিনি দিগম্বর বা সন্ন্যাসী হয়েছেন পুনরায় সে-রাজ্যে তাঁর প্রয়োজন কী ?
.
তাই অন্য কোন চূড়ান্ত প্রমাণ না-পাওয়াতক ভট্টিকাব্যের ভট্টি আর শতককার ভর্তৃহরি যে এক নয়, তেমনি বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি আর শতককার ভর্তৃহরিও এক নয়, এ ব্যাপারে আপাত সিদ্ধান্ত নেয়া অনুচিৎ হবে না বলেই মনে হয়। তাঁদের প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র একেকজন কবি হিসেবেই আমরা ধরে নিতে পারি।
.
ভর্তৃহরির রচনাবলী
শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক- এই শতকত্রয়ের কোথাও ভর্তৃহরির নাম লেখা না-থাকলেও তিনিই যে শতকত্রয়ের রচয়িতা- এ ব্যাপারে সকলেই প্রায় একমত। তবে কারো কারো মতে অবশ্য ভর্তৃহরি শতকত্রয়ের রচয়িতা নন, সঙ্কলয়িতা মাত্র। তিনি অন্য কবিদের রচিত এবং লোকমুখে প্রচলিত শ্লোকসমূহ বিষয়বস্তু অনুসারে তিনটি শিরোনামে বিন্যাস করেছেন বলে তাঁদের অভিমত (-Dr.Bohlen Ges Abraham Roger)।
.
এছাড়া শতকত্রয় ব্যতীত ভর্তৃহরির নামের সঙ্গে আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম যুক্ত করেছেন কেউ কেউ তাঁদের গ্রন্থে। সেগুলো হচ্ছে- ভট্টিকাব্য (বা রাবণবধ), বাক্যপদীয়, মহাভাষ্যদীপিকা, মীমাংসাভাষ্য, বেদান্তসূত্রবৃত্তি, শব্দধাতুসমীক্ষা ও ভাগবৃত্তি। এগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি যে শতককার ভর্তৃহরির রচনা নয় সে সম্পর্কে ইতঃপূর্বেই আলোচনায় এসেছে। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি সম্পর্কে পক্ষে বা বিপক্ষে যথার্থ কোন যুক্তি বা তথ্য এখনো অজ্ঞাত বলে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা এখনি সম্ভব নয়।
তবে শতকত্রয় ভর্তৃহরির মৌলিক রচনা কি-না, এ সম্পর্কে তিনটি মত প্রচলিত আছে বলে জানা যায়। প্রথম মত হলো- শতকত্রয় ভর্তৃহরির মৌলিক রচনা নয়, সঙ্কলিত। দ্বিতীয় মত হলো- অন্য কোন কবি বা কবিরা শতকত্রয় রচনা করে ভর্তৃহরির নামে উৎসর্গ করেছেন। এবং তৃতীয় মত- শতকত্রয় ভর্তৃহরির নিজের রচনা।
.
প্রথম মতের প্রবক্তাদের যুক্তি হলো- শতকত্রয়ের শ্লোকগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যসূত্র নেই এবং বিভিন্ন কবিদের রচিত শ্লোক এতে দেখা যায়। শতকত্রয়ের শ্লোকগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যসূত্র নেই সত্য, কিন্তু প্রতিটি শতকের মোট শ্লোকগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় এবং এই ভাগগুলোর অন্তর্গত শ্লোকসমূহের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ভাব-সঙ্গতি বা বক্তব্যের ঐক্য বর্তমান। প্রতিটি শতকের শ্লোকগুলিকে তাই দেখা যায় ভাব বা বক্তব্যভিত্তিতে দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অতএব শতকত্রয়ের শ্লোকগুলো যে একেবারেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন একথা স্বীকার্য নয়। তাছাড়া সংস্কৃত কাব্যের নিয়মে শতককাব্যের শ্রেণীই হচ্ছে ‘মুক্তক’. যার বৈশিষ্ট্যই হলো প্রতিটি শ্লোক হবে পরস্পর অর্থনিরপেক্ষ। এতে কোন কাহিনী থাকবে না, থাকবে না ঘটনার ঐক্য। তাই একটির সঙ্গে অন্যটির ঐক্যসূত্র নেই বলেই যে শতকত্রয় মৌলিক রচনা না হয়ে সঙ্কলিত গ্রন্থ হবে- এ অনুমানের বাস্তব ভিত্তি নেই বলেই মনে হয়।
.
শতকত্রয়ের মধ্যে অন্য কবিদের রচিত শ্লোক যে পাওয়া যায় তা সত্য। যেমন- কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলে’র (পঞ্চম অঙ্ক-১২) শ্লোকটি দেখা যায় নীতিশতকের এই শ্লোকে-
ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলোদ্গমৈ-
র্নবাম্বুভির্ভূরিবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্ ।। ৭০।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : ফলাগমে বৃক্ষসকল অবনত হয়, মেঘসকল নবজলভারে বিলম্বিত (নিম্নগামী হয় এবং) সজ্জনেরা সম্পত্তি (ঐশ্বর্য) লাভে বিনীত (হন)। পরোপকারীদের এটাই স্বভাব।
.
এবং বিশাখদত্তের ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকের (দ্বিতীয় অঙ্ক-১৭) শ্লোকটি পাওয়া যায় নীতিশতকের এই শ্লোকে-
প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমজনা ন পরিত্যজন্তি।। ২৭।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : অধমেরা (দুর্বলচিত্তেরা) বিঘ্নভয়ে (কোন কাজ) আরম্ভ করে না, মধ্যমেরা (সাধারণ জন) আরম্ভ করে(-ও) বাধাগ্রস্ত (হয়ে তা থেকে) বিরত থাকে, (কিন্তু) উত্তমেরা (সাহসীরা) বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েও আরম্ভকৃত (কাজ) কখনও পরিত্যাগ করেন না।
.
এরকম উদাহরণ আরো আছে। এ ধরনের শ্লোকগুলি যে নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে লিপিকরদের হাতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। কেননা শতককাব্যের নামের সার্থকতা বিচার করতে গেলে শতকত্রয়ের প্রত্যেকটিতে একশত করে মোট তিনশত শ্লোক থাকাই বাঞ্ছনীয় ছিলো। কিন্তু সেখানে আছে চারশোর কাছাকাছি। জানা যায়, M.R.Kale সম্পাদিত নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতকে মূল শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ১০৮ ও ১০১টি। এ ছাড়াও দুটি শতকে অতিরিক্ত শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ২৫ ও ৪৪টি। এই অতিরিক্ত শ্লোকসমূহেরই কোন কোনটি আবার শতকদ্বয়ের অপর অপর সংস্করণে মূল শ্লোকসমূহের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। তাই কোনটা যে ভর্তৃহরির আর কোনটা প্রক্ষিপ্ত তা নিরূপণ কষ্টকর বলে গবেষকদের মন্তব্য। সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (তৃতীয় খণ্ড)-এ শৃঙ্গারশতকে শ্লোক সংখ্যা ১০০টি। এ হিসেবে তিনটি শতকে মোট শ্লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭৮।
.
ভর্তৃহরি হয়তো তিনটি কাব্যে তিনশত শ্লোকই রচনা করেছিলেন, কিন্তু কালে কালে লিপিকর ও অন্যান্যদের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে তাদের কলেবর আজ এতোটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রক্ষেপণের কাজটি পরবর্তীকালের কোন কোন অখ্যাত কবিদের দ্বারাও হতে পারে। কারণ শ্লোকসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যসূত্রই যখন নেই তখন ভাবগত ঐক্য বজায় রেখে একটি দুটি রচিত শ্লোক এর সঙ্গে যোগ হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। শতকত্রয়ে অন্যান্য যে সব কবির রচনা পাওয়া যায় তাঁদের দু-একজন ছাড়া বাকিরা অজ্ঞাত অখ্যাতই শুধু নয়, সময়ের মানদণ্ডে তাদের অধিকাংশই ভর্তৃহরির অর্বাচীন। যেমন সর্বজন-নন্দিত ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকের স্রষ্টা সংস্কৃতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিশাখদত্তের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তিনি খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকের বলে ধরা হয়। সে বিবেচনায় সম্ভাব্য খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের কবি ভর্তৃহরি নিজে এই সব শ্লোক তাঁর কাব্যে গ্রহণ করেন নি- পরবর্তীকালের প্রক্ষেপণকারীদেরই কাজ এটা।
.
ভর্তৃহরির রচনা সম্পর্কে অন্য যে মত- অন্য কবি বা কবিরা শতকত্রয় রচনা করে ভর্তৃহরির নামে প্রকাশ করেছে কিংবা ভর্তৃহরিই অন্যদের দ্বারা লিখিয়ে নিজের নামে প্রকাশ করেছেন। এ মতের কারণ হয়তো ভর্তৃহরি রাজা ছিলেন বলে। এরূপ প্রবাদ বা অপবাদ সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক কবির বেলায়ই প্রচলিত রয়েছে বলে জানা যায়। কিন্ত পণ্ডিত মহলে এ মত সমাদর লাভ করে নি। কাজেই সবকিছু বিবেচনায় পণ্ডিতদের তৃতীয় মত অর্থাৎ শতকত্রয় ভর্তৃহরির নিজের মৌলিক রচনা- এটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।
.
ভর্তৃহরির রচনাক্রম
ভর্তৃহরির শতকত্রয়ের মধ্যে কোনটি আগে এবং কোনটি পরে এ নিয়েও বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলেন প্রথমে নীতিশতক, তারপর শৃঙ্গারশতক এবং শেষে বৈরাগ্যশতক। কেউ এতে ভিন্নমত পোষণ করেন। তবে বৈরাগ্যশতক যে শেষে তা নিয়ে কারও দ্বিমত নেই, এবং সম্ভবত মতভেদের অবকাশও নেই। কারণ বৈরাগ্যের পর কারও জীবনে আর কিছু অর্থাৎ নীতি-অনীতি, শৃঙ্গার-প্রেম-কাম-ভালোবাসা বলতে কিছু থাকতে পারে না। তাছাড়া বৈরাগ্যশতকে কবির যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তাতে এটাই প্রতীত হয় যে, কবি ইতোমধ্যে নীতি বা সংসারনীতি এবং শৃঙ্গাররাজ্য অতিক্রম করে এসেছেন এবং সে-রাজ্যের অসারতা, বিশ্বাসহীনতা এবং আনন্দহীনতা তাঁকে পীড়িত করেছে। তাই বুঝি বৈরাগ্যশতকে নির্দ্বিধায় তিনি বলেন-
‘ভোগসুখে রোগের ভয়, সদ্বংশে বিপরীত আচরণজনিত দোষে বিচ্যুতির (সম্মান নাশের) ভয়, ধনসম্পদের বৃদ্ধিতে রাজাদের ভয়, অভিমানে দীনতার ভয়, শক্তিতে শত্রুর ভয়, সৌন্দর্যে বার্ধক্যের ভয়, শাস্ত্রজ্ঞানে তার্কিক প্রতিবাদীর ভয়, বিদ্যা-বিনয় প্রভৃতি গুণের বিষয়ে দুষ্ট লোকের অপবাদের ভয়, দেহে মৃত্যুর ভয়- জগতে মানুষের কাছে সমস্ত বস্তুই ভীতিপ্রদ কেবলমাত্র বৈরাগ্যই ভয়শূন্য। (সুতরাং ভয়াবহ ভোগ্য বিষয়সমূহ ত্যাগ করে বৈরাগ্যই আশ্রয় করা উচিত)’।। ৩১।। (-ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতক/ সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ১৬শ খণ্ড)।
.
‘মৃত্যু সমস্ত প্রাণীর জীবন, বার্ধক্য উজ্জ্বল রমণীর যৌবন, ধনলাভের বাসনা সন্তুষ্টিকে, প্রগল্ভা নারীর বিলাস ইন্দ্রিয়-অনাসক্তিজনিত আনন্দকে, অসহিষ্ণু ব্যক্তিরা বিনয় প্রভৃতি গুণকে, দুষ্ট হস্তী এবং সর্প পবিত্র অরণ্যভূমিকে, কুমন্ত্রণাদাতা দুর্জনরা রাজাদের এবং নশ্বরতা ধনসম্পদকে অভিভূত করে- এই সংসারে কোন্ বস্তু অন্য কিছু দ্বারা আক্রান্ত (অভিভূত) হয় না ?’ ।। ৩২।। (-ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতক /ঐ)
.
‘হে চিত্ত ! শ্রীশিবশম্ভুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও, হৃদয়ে জন্মমৃত্যুর ভয় সর্বদা স্মরণ করো, পুত্র-পত্নী-বন্ধুর প্রতি মমতা ত্যাগ করো, কামনাজনিত বিকার অন্তরে স্থান দিয়ো না, সঙ্গদোষ শূন্য হয়ে (কাম-ক্রোধাদি প্রসঙ্গশূন্য হয়ে) নির্জন অরণ্যে বাস এই বৈরাগ্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কী প্রার্থনার যোগ্য বিষয় আছে ?’ ।। ৬৮।। (-ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতক /ঐ)
.
কাজেই এ থেকেই বুঝা যায় যে, বৈরাগ্যশতক শেষে অর্থাৎ কবির বৈরাগ্য অবলম্বনের পরেই রচিত হয়েছে। আর শৃঙ্গারশতক ও নীতিশতকের কোনটা আগে-পরের রচনা তা অনুমান করতে ভর্তৃহরির জনশ্রুত জীবন-চরিত বিশ্লেষণ করাই সঙ্গত। দেখা যায়- ভর্তৃহরি রাজা হওয়ার পরপরই রাজকার্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন থেকে সারাক্ষণই আকণ্ঠ সুরা আর নারীসম্ভোগে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর এই নারীসম্ভোগের অপূর্ব বর্ণনাই বিধৃত হয়েছে তাঁর শৃঙ্গারশতকে। এ বর্ণনা যে তাঁর স্বীয় অভিজ্ঞতারই ফল তা কাব্য-পাঠেই অনুধাবন করা যায়। শৃঙ্গারসাগরে সন্তরণ করতে করতে তিনি বলছেন-
‘সুধীজনেরা পক্ষপাতিত্ব বর্জন করে এবং বাস্তবতা বিচার করে ঠিক ঠিক বলুন তো, আমরা পর্বতের নিতম্ব (কটকদেশ) আশ্রয় করবো, না কামোচ্ছ্বাসে স্মিতহাস্যময়ী বিলাসিনীদের নিতম্ব আশ্রয় করবো ?’।। ৩৬।। (ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতক/ সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ১৬শ খণ্ড)
.
‘হয় গঙ্গার কলুষনাশী বারিতে, নয় তরুণীর হারমণ্ডিত মনোহর স্তন দুটিতে বাসস্থান রচনা করুন।। ৩৮।। (ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতক/ ঐ)
.
‘যুক্তিহীন বহুতর্কে লাভ কী ? পুরুষদের দুটি জিনিসই সর্বদা সেব্য- হয় সুন্দরীদের অভিনব কামলোলুপ স্তনভারাক্রান্ত যৌবন, নয় অরণ্য।। ৩৯।। (ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতক/ ঐ)
.
‘জনগণ ! আমি কোনরকম পক্ষপাতিত্ব না করে বলছি- সপ্তলোকে আমার এ কথা প্রযোজ্য : নিতম্বিনীদের মতো রমণীয় কিছু নেই, তাদের মতো দুঃখের মুখ্য হেতুও আর কিছু নেই।। ৪০।। (ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতক/ ঐ)
.
শৃঙ্গার সম্পর্কে কবির এই নিখুঁত বর্ণনা যে জীবন-অভিজ্ঞতা ব্যতীত সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অন্য এক আকর্ষণীয় কিংবদন্তী অনুযায়ী, শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য ‘অমরুশতক’-এর রচয়িতাও (শংকরাচার্য) নাকি জনৈক মণ্ডনমিশ্রের বিদূষী পত্নী ভারতীর সঙ্গে একবার রতিবিষয়ক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে জনৈক মৃতরাজা অমরুর দেহ আশ্রয় করে তার অন্তঃপুরে যান এবং তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে বহুদিন যাপন করে রতিশাস্ত্রবিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে উক্ত মহিলাকে বিতর্কে পরাজিত করেন। রতিবিষয়ক তাঁর সেই জ্ঞানই ‘অমরুশতক’ নামে পরবর্তীকালে খ্যাতিলাভ করে। কবি ভর্তৃহরির বেলায়ও হয়তো তা-ই হয়েছিলো।
শৃঙ্গারশতকে নারী সম্পর্কে কবি ভর্তৃহরির এমন পক্ষপাতিত্বের মধ্য দিয়েও কিন্তু নারীদের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা, অবিশ্বাস ও ঘৃণা কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। সেটাই দেখা যায় একটু পরেই-
‘সংশয়ের আবর্ত, অবিনয়ের ভুবন, সাহসের নগর, দোষের আকর, শতকপটতার আধার, অবিশ্বাসের ক্ষেত্র, স্বর্গদ্বারের বিঘ্ন, নরকের দ্বার, সমস্ত মায়ার পেটিকা, অমৃতময় বিষ, প্রাণিজগতের বন্ধন এমন স্ত্রীযন্ত্র কে সৃষ্টি করলো ?’।। ৪৫।। (ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতক/ ঐ)
.
নারীর প্রতি তাঁর এই ঘৃণা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিতৃষ্ণা চরমে উঠে পত্নী অনঙ্গসেনার বিশ্বাসঘাতকতায়। তাই নীতিশতকের শুরুতেই তিনি বলেন-
‘যাকে (যার কথা) নিরন্তর চিন্তা করেছি (অর্থাৎ যাকে প্রাণের চেয়েও অধিক ভালোবেসেছি) সে (সেই প্রিয়তমা পত্নী) আমার প্রতি নিরাসক্ত, সে ভালোবাসে (বা কামনা করে) অন্য পুরুষকে; সেই পুরুষ (আবার) অন্যাসক্ত (অর্থাৎ অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত); আবার আমার কারণেও অনুশোচনা করে (অর্থাৎ দুঃখ পায় বা ধ্বংস হচ্ছে) (সে) অন্য কোনও এক স্ত্রীলোক। (তাই) ধিক্ সেই (পরপুরুষগামিনী) স্ত্রীলোককে, ধিক্ সেই পুরুষকে (যে একাধিক স্ত্রীজনে আসক্ত), ধিক্ এই (বারবণিতা) স্ত্রীলোককে এবং ধিক্ আমাকেও, (সর্বোপরি) ধিক্ সেই মদনকে (যার প্রভাবে এসব সংঘটিত হচ্ছে)’ ।। ০২।। (ভর্তৃহরি নীতিশতক)
এরপর সমগ্র নীতিশতকেই দেখি আমরা অন্য এক ভর্র্তৃহরিকে- যেন তিনি শৃঙ্গারশতকের কবি ভর্তৃহরি নন, সম্পূর্ণ অন্য এক ভর্তৃহরি। যেখানে তিনি শুধুই নীতির প্রচার করেছেন। নিজের মূর্খতা, অজ্ঞতা ও স্থূল বুদ্ধিবৃত্তির কুপরিণাম প্রচার এবং এসব হতে লোকে যাতে দূরে থাকে এবং আত্মমর্যাদা রক্ষা করে সবার শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে সংসারে টিকে থাকতে পারে, সেসব উপদেশ-নির্দেশনাই তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর নীতিশতকে। হয়তো আপন জীবনের শিক্ষা দিয়ে তিনি অপরের জীবন-চলার পথ সুগম করতে চেয়েছেন। তাই সংসারে টিকে থাকতে মানুষের করণীয় কী হবে তা সম্পর্কে বলেন-
দাক্ষিণ্যং স্বজনে দয়া পরজনে শাঠ্যং সদা দুর্জনে
প্রীতিঃ সাধুজনে নয়ো নৃপজনে বিদ্বজ্জনেপ্যার্জবম্ ।
শৌর্যং শত্রুজনে ক্ষমা গুরুজনে নারীজনে ধূর্ততা
যে চৈবং পুরুষাঃ কলাসু কুশলাস্তেষ্যেব লোকস্থিতিঃ।। ২২।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : আত্মজনের প্রতি ঔদার্য, ভৃত্যজনের প্রতি দয়া; শঠের প্রতি সদা শাঠ্য, সজ্জনের প্রতি প্রেম; রাজজনের (রাজপুরুষদের) প্রতি নীতি, পণ্ডিতজনের প্রতি সারল্য; শত্রুদের প্রতি বীরত্ব (শৌর্য), পূজনীয়দের প্রতি সহিষ্ণুতা; নারীজনের প্রতি ছলনা (শঠতা) ইত্যাদি কলাবিদ্যায় যে-সকল পুরুষ পারদর্শী তাদের উপরই সংসারের স্থৈর্য (বা স্থিতিশীলতা নির্ভর করে, অর্থাৎ এই জগৎসংসারে তারাই সুখে বসবাস করতে পারে)।
শৃঙ্গারশতকে যাঁর সম্ভোগক্রিয়ার চমৎকার বিবরণ পরিলক্ষিত হয়, নীতিশতকে তারই মধ্যে দেখা যায় নীতিবোধের জাগরণ, নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা। শৃঙ্গারশতকেই নারীদের প্রতি কবির মোহাচ্ছন্নতা কেটে ক্রমে যে ঘৃণার বাষ্প দেখা দিয়েছিলো, নীতিশতকে দেখা যায় তা মেঘ হয়ে বৃষ্টিপাতের ফলে তাঁর মনকে ধুয়ে মুছে একেবারে পূত-পবিত্র করে দিয়েছে। এবং বৈরাগ্যশতকে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে সংসার ত্যাগ করেন। এই তিনটি কাব্যের মৌল চেতনার রূপান্তরের মধ্যেই মূলত স্রষ্টা ভর্তৃহরির ক্রমবিবর্তিত মানস-চেতনার স্বাক্ষরই সমুজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে।
.
ভর্তৃহরির নীতিশতক
ভর্তৃহরির রচনাশৈলী এমনিতেই অনুপম। তাঁর কাব্যে অর্থাৎ শ্লোকে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ খুবই অল্প দেখা যায়। এ কারণে তার ভাষা সহজ-সরল ও সর্বজনবোধ্য এবং ভাবগ্রাহীও। কাব্যের পরতে পরতে গভীর তাৎপর্য ব্যক্ত হয়েছে। বাক্য-গঠন সহজ ও স্বাভাবিক হলেও অর্থের দিক থেকে তা খুবই তাৎপর্যময় হওয়ায় ভর্তৃহরির শতকত্রয় বিশেষ করে নীতিশতক সকলেরই সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠেছে। মানবজীবনের বিচিত্র বিষয়ের যথার্থ চিত্রণ করতে গিয়ে ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের উপর তাঁর প্রশংসনীয় অধিকারের স্বাক্ষর তাঁর রচনাকে অনুপম সাহিত্যকর্মে পরিণত করেছে। সংস্কৃত শতককাব্যের জগতে তাই ভর্তৃহরির শতকত্রয় সর্বোচ্চ আসন দখল করে আছে বলে রসগ্রাহী পাঠকরা মনে করেন।
.
শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভাব ও বক্তব্যের ঐক্য বিবেচনায় ভর্তৃহরির নীতিশতকের শ্লোকসমূহকে দশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে যথাক্রমে- অজ্ঞনিন্দা (বা মূর্খপদ্ধতি), বিদ্বৎপদ্ধতি, মানশোর্যপদ্ধতি, অর্থপদ্ধতি, দুর্জনপদ্ধতি, সুজনপদ্ধতি, পরোপকারপদ্ধতি, ধৈর্যপদ্ধতি, দৈবপদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতি।
.
অজ্ঞনিন্দা বা মূর্খপদ্ধতি : মূর্খপদ্ধতির রচনাগুলিতে মূর্খদের সম্পর্কে কবির উপলব্ধি ও মতামত উপদেশাকারে বিধৃত হয়েছে। যেমন-
অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ সুখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ।
জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি।। ০৩।। (ভর্তৃহরি নীতিশতক)
অর্থাৎ : যে অজ্ঞ তাকে প্রসন্ন করা সহজ, বিজ্ঞকে প্রসন্ন করা আরও সহজ, (কিন্তু) স্বল্পজ্ঞানে গর্বিত যে পণ্ডিত তাকে ব্রহ্মাও পরিতুষ্ট করতে পারেন না।
.
বিদ্বৎপদ্ধতি : এই বিদ্বৎপদ্ধতির রচনায় বিদ্যা ও বিদ্বানের সুখ্যাতি ও প্রশংসা ধ্বনিত হয়েছে। যেমন-
হর্তুর্যাতি ন গোচরং কিমপি শং পুষ্ণাতি যৎসর্বদা
হ্যর্থিভ্যঃ প্রতিপাদ্যমানমনিশং প্রাপ্নোতি বৃদ্ধিং পরাম্ ।
কল্পান্তেষ্যপি ন প্রয়াতি নিধনং বিদ্যাখ্যমন্তর্ধনং
যেষাং তান্ প্রতি মানমুজ্ঝত নৃপাঃ কস্তৈঃসহ স্পর্ধতে।। ১৬।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : যা চোরের(-ও) দৃষ্টিগোচর হয় না, (যা) সর্বদাই কোনও এক অনির্বচনীয় আনন্দ দেয়, (যা) প্রার্থীদের (বিদ্যার্থীদের) মধ্যে নিরন্তর বিতরণ করলেও (শেষ হয় না, বরং) প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, (এমন কি পৃথিবীর) প্রলয়কালেও (যা) ধ্বংস না হয়- সেই বিদ্যা নামক গুপ্ত ধন যাঁদের (আছে), হে রাজন্! তাঁদের প্রতি অহঙ্কার পরিত্যাগ করুন; কে তাঁদের কাছে স্পর্ধা দেখাতে পারে ?
.
মানশৌর্যপদ্ধতি : আত্মগৌরবে যাঁরা গর্বিত এবং আত্মশক্তিতে যারা আস্থাবান তারা কোন কারণেই হীন কাজে উদ্যোগী হন না- এ উপলব্ধির সারাৎসারই এই মানশৌর্যপদ্ধতির রচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। যেমন-
ক্ষুৎক্ষামোপি জরাকৃশোপি শিথিলপ্রায়োপি কষ্টাং দশা-
মাপন্নোপি বিপন্নদীধিতিরপি প্রাণেষু নশ্যৎস্বপি।
মত্তেভেন্দ্রবিভিন্নকুম্ভকব লগ্রাসৈকবদ্ধস্পৃহঃ
কিং জীর্ণং তৃণমত্তি মানমহতামগ্রেসরঃ কেশরী।। ২৯।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : ক্ষুধায় কাতর হলেও, বার্ধক্যহেতু দুর্বল হলেও, প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এলেও, (জীবনের) কষ্টকর অবস্থায় উপনীত হলেও, তেজ দূরীভূত হলেও মদমত্ত গজরাজের কপোলের মাংস এক গ্রাসে খেতে (যে) লুব্ধ (এবং) আত্মসম্মানে যারা মহান্ তাদের (মধ্যে যে) অগ্রগণ্য (সেই) সিংহরাজ (মৃগরাজ) কি প্রাণপাত হলেও শুষ্ক তৃণ ভক্ষণ করে ?
.
অর্থপদ্ধতি : প্রচলিত সমাজে যে অর্থই সব কিছুর মূল, সেই অর্থের জয়গানই অর্থপদ্ধতির রচনায় প্রতিপাদ্য হয়েছে। কখনো হয়তো শ্লোকের অন্তর্গত সূক্ষ্ম কটাক্ষও ধরা পড়ে। যেমন-
যস্যাস্তি বিত্তং স নরঃ কুলীনঃ
স পণ্ডিতঃ স শ্রুতবান্ গুণজ্ঞঃ।
স এব বক্তা স চ দর্শনীয়ঃ
সর্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তে।। ৪১।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : যার ধন আছে সেই মানুষ(-ই) কুলীন, সে প্রাজ্ঞ (বা পণ্ডিত), সে শাস্ত্রজ্ঞ, সে গুণবান্, সে-ই (উত্তম) বক্তা এবং সে (সকলের) দর্শনীয় হয়; সকল প্রকার গুণ অর্থকে(-ই) ঘিরে থাকে।
.
দুর্জনপদ্ধতি : দুর্জন ব্যক্তি স্বভাবতই নির্দয় হয়ে থাকে। দুর্জনের দুর্জনত্ব কোন কারণের অপেক্ষা করে না। বিনা কারণেই তারা শত্রুতা করে। এ বিষয়ক রচনাই দুর্জনপদ্ধতির শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-
জাড্যং হ্রীমতি গণ্যতে ব্রতরুচৌ দম্ভঃ শুচৌ কৈতবং
শূরে নির্ঘৃণতা মুনৌ বিমতিতা দৈন্যং প্রিয়ালাপিনি।
তেজস্বিন্যবলিপ্ততা মুখরতা বক্তর্যশক্তিঃ স্থিরে
তৎ কো নাম গুণো ভবেৎ স গুণিনাং যো দুর্জনৈর্নাঙ্কিতঃ।। ৫৪।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : (দুর্জন ব্যক্তি) লজ্জাশীলের মধ্যে জড়তা, ব্রতচারীর মধ্যে দম্ভ, চরিত্রবানের মধ্যে কপটতা, বীরের মধ্যে হৃদয়হীনতা, মুনিদের মধ্যে প্রজ্ঞাহীনতা, প্রিয়ভাষীদের মধ্যে দুর্বলতা, বলবানের মধ্যে ঔদ্ধত্য, বক্তার মধ্যে বাচালতা (এবং) ধীরস্বভাব ব্যক্তির মধ্যে অসমর্থতা (ইত্যাদি দোষসমূহ) আবিষ্কার করে। অতএব, গুণীদের এমন কি গুণ আছে (বা থাকতে পারে) যা দুর্জন কর্তৃক (এমনিভাবে) কলঙ্কিত নয় (অথবা কলঙ্কিত হয় না) ।
.
সুজনপদ্ধতি : সজ্জনের সমাদর সর্বত্র- সবাই তাঁদের শ্রদ্ধা করে। সজ্জনের গুণ ও প্রশংসাসূচক রচনাই সুজনপদ্ধতির প্রতিপাদ্য হয়েছে। যেমন-
প্রদানং প্রচ্ছন্নং গৃহমুপগতে সম্ভ্রমবিধিঃ
প্রিয়ং কৃত্বা মৌনং সদসি কথানং চাপ্যুপকৃতেঃ।
অনুৎসেকো লক্ষ্ম্যাং নিরভিভবসারাঃ পরকথাঃ
সতাং কেনোদ্দিষ্টং বিষমমসিধারাব্রতমিদম্ ।। ৬৪।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : দানের কথা গোপন রাখা, গৃহাগত (অতিথি)-কে সাদর অভ্যর্থনা জানানো, (কারও) উপকার করে মৌন থাকা, (কিন্তু অপরের) উপকারের কথা সৎসভায় (অর্থাৎ সজ্জনদের মধ্যে) প্রচার করা, সম্পদে গর্বহীনতা (এবং) অন্যের সম্পর্কে নিন্দা না করা- খড়গধারার মতো দুশ্চর এই ব্রতের উপদেশ সদ্ব্যক্তিদের কে দিয়েছে ?
.
পরোপকারপদ্ধতি : যারা পরোপকারী সজ্জন ব্যক্তি তাঁরা বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেও অবিনীত হন না, বিনয়ই যেন তাঁদের অঙ্গভূষণ। দয়া তাঁদের পরম ধর্ম। এ ধরনের প্রশস্তিই পরোপকারপদ্ধতির শ্লোকগুলিতে উক্ত হয়েছে। যেমন-
ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলোদ্গমৈ-
র্নবাম্বুভির্ভূরিবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্ ।। ৭০।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : ফলাগমে বৃক্ষসকল অবনত হয়, মেঘসকল নবজলভারে বিলম্বিত (নিম্নগামী হয় এবং) সজ্জনেরা সম্পত্তি (ঐশ্বর্য) লাভে বিনীত (হন)। পরোপকারীদের এটাই স্বভাব।
.
ধৈর্যপদ্ধতি : ধৈর্য মনস্বী ব্যক্তিদের প্রধান গুণ। অভীষ্ট বস্তু লাভ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ধৈর্য ত্যাগ করেন না। এই ধৈর্যগুণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ধৈর্যপদ্ধতির শ্লোকের অভীষ্ট হয়েছে। যেমন-
কান্তাকটাক্ষবিশিখা ন লুনন্তি যস্য
চিত্তং ন নির্দহতি কোপকৃশানুতাপঃ।
কর্ষন্তি ভূরিবিষয়াশ্চ ন লোভপাশৈ-
র্লোকত্রয়ং জয়তি কৃৎস্নমিদং স ধীরঃ।। ৮৫।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : বণিতার কটাক্ষশর যাঁর হৃদয়কে ছিন্ন (বিদ্ধ) করতে পারে না, ক্রোধাগ্নির সন্তাপ (যাঁকে) দগ্ধ করতে পারে না, অমিত বিষয়-সম্পদ (যাঁকে) লোভের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে না- সেই ধৈর্যশীল ব্যক্তি(-ই) এই সমগ্র ত্রিভুবন জয় করতে পারেন।
.
দৈবপদ্ধতি : দৈব মানুষের নিয়ন্ত্রক, রক্ষক। দৈবের কাছে পৌরুষ নিষ্ক্রিয়। এরকম অদৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দৈবপদ্ধতির শ্লোকগুলিতে অনুরণিত হতে দেখা যায়। যেমন-
কার্যায়ত্তং ফলং পুংসাং বুদ্ধিঃ কর্মানুসারিণী।
তথাপি সুধিয়া ভাব্যং সুবিচার্যৈব কুর্বতা।। ৯২।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : পুরুষের (অর্থাৎ মানুষের সুখ-দুঃখাদি) ফল (যদিও পূর্বকৃত) কর্মের অধীন, (এবং) বুদ্ধি কর্মের অনুসারিণী, তথাপি বিজ্ঞজনের উচিত সুবিবেচনাপূর্বক কার্য নির্ধারণ করা।
.
কর্মপদ্ধতি : কর্মই সবচেয়ে শক্তিশালী, কারণ দেখা যায় বিধি মানুষকে যে ফল দান করে তার উপর বিধির কোন নিয়ন্ত্রণ নেই- কর্মের দ্বারাই তা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই কর্মই সবার শ্রেষ্ঠ। এই অনুধাবনই কর্মপদ্ধতির শ্লোকগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন-
নমস্যামো দেবান্ননু হতবিধেস্তেপি বশগা
বিধির্বন্দ্যঃ সোপি প্রতিনিয়তকর্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিং চ বিধিনা
নমস্তৎকর্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।। ৯৯।। (ভর্তৃহরির নীতিশতক)
অর্থাৎ : আমরা (কি) দেবগণকে নমস্কার করবো ? কিন্তু তারাও (যে) ঘৃণ্য বিধির বশীভূত। (তাহলে কি) বিধি বন্দনীয় ? (কিন্তু) সে-ও সদা কর্মানুযায়ী ফল দান করে থাকে। (আর) ফল যদি কর্মের(-ই) অধীন (হয় তাহলে) দেবতা কিংবা বিধাতার কী প্রয়োজন ? অতএব (সেই) কর্মকেই নমস্কার- যার উপর বিধিরও নিয়ন্ত্রণ নেই (অর্থাৎ বিধিও যার অধীন)।
.
ভর্তৃহরির নীতিশতকে এরকম অনেক শ্লোক আছে যা শুধু শুষ্ক নীতিকথাই প্রচার করছে না- বরং ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও অর্থ সমন্বয়ে সেগুলো সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের একেকটি অমূল্য রত্নরূপে পরিগণিত। আর এ কারণেই ভর্তৃহরির নীতিশতক সংস্কৃত সাহিত্য-জগতে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে আছে।
…
[ অনুসৃত সূত্রগ্রন্থ : ভর্তৃহরির নীতিশতক / দুলাল ভৌমিক / বাংলা একাডেমী ঢাকা, মার্চ ১৯৮৯ ]


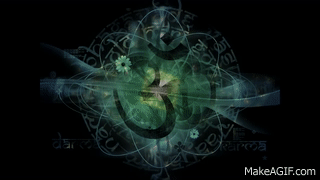




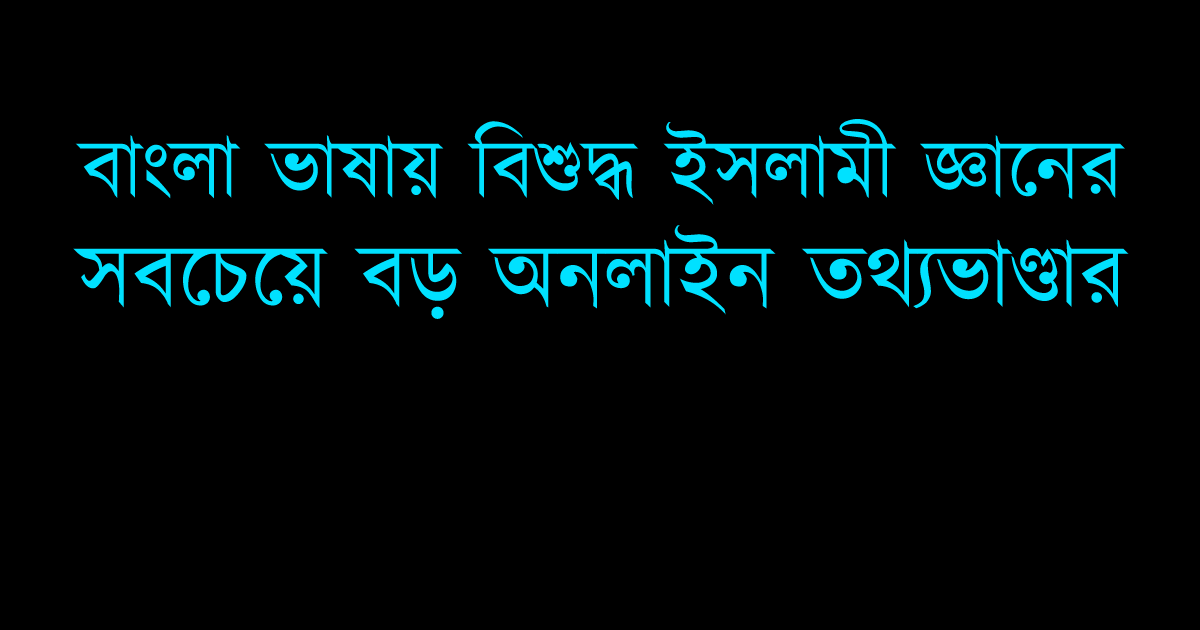


















No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ