 |
| শিব ও তাঁর বিকাশ |
বেদের রূঢ় অর্থের কারনে নানা ভুল ভ্রান্তির সূচনা।
বৈদিক যুগের প্রথম স্তরে অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যের প্রধান ও প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদে বস্তুত শিবকে পাওয়া যায় না। তাঁর প্রতিরূপ রুদ্রকে ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তে স্তূয়মান হিসেবে পাওয়া যায়। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথের মতে–
‘শিব’ শব্দ এই সময়ে কতিপয় বৈদিক দেবতার বিশেষণ রূপে ‘মঙ্গলদায়ক’ অর্থে ব্যবহৃত হইত। উত্তর বৈদিক সাহিত্যে যে ‘সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্’ পদ পাওয়া যায়, সেখানেও ইহা পরম ব্রহ্মের বিশেষণ রূপে একই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিক হইতে ইহা এক বিশেষ দেবসত্তাকে বুঝাইতে আরম্ভ করে।… কিন্তু রুদ্রই যে পৌরাণিক শিবের আদি বৈদিক প্রতিরূপ সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।’– (পঞ্চোপাসনা, পৃষ্ঠা-১২৫)
আর দীনেশ চন্দ্র সেন-এর ভাষায় বৈদিক রুদ্রের রূপ হলো– ‘বেদের রুদ্রদেব বিনাশের দেবতা, তাঁর জটাজুট অগ্নিশলাকার মতো। তাঁর নৃত্যের নাম– তাণ্ডব; তাতে বিশ্ব বিকম্পিত হয় ও গ্রহরা কক্ষচ্যুত হয়ে ব্যোমপথে বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি করে। রুদ্রের নিঃশ্বাসের জ্বালা– জগতের শ্মশান। তাঁর শূলাগ্রে বিদ্ধ হয়ে দিগ্হস্তীরা আর্তনাদ করে ওঠে। তাঁর নেত্রশাসনে চিত্ত-শ্মশানে কামদেব পুড়ে ছাই হয়। তাঁর মুখোচ্চারিত প্রণব প্রলয়ের গান– বিনাশের ঝঞ্ঝা। তা জগতকে পুঞ্জীভূত ধুলোয় পরিণত করে। তাঁর বিষাণ-বাদনের তালে তালে চতুর্দশ মৃত্যু নৃত্য করতে থাকে।’ –(বৃহৎ বঙ্গ)
‘শিব’ শব্দ এই সময়ে কতিপয় বৈদিক দেবতার বিশেষণ রূপে ‘মঙ্গলদায়ক’ অর্থে ব্যবহৃত হইত। উত্তর বৈদিক সাহিত্যে যে ‘সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্’ পদ পাওয়া যায়, সেখানেও ইহা পরম ব্রহ্মের বিশেষণ রূপে একই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিক হইতে ইহা এক বিশেষ দেবসত্তাকে বুঝাইতে আরম্ভ করে।… কিন্তু রুদ্রই যে পৌরাণিক শিবের আদি বৈদিক প্রতিরূপ সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।’– (পঞ্চোপাসনা, পৃষ্ঠা-১২৫)
আর দীনেশ চন্দ্র সেন-এর ভাষায় বৈদিক রুদ্রের রূপ হলো– ‘বেদের রুদ্রদেব বিনাশের দেবতা, তাঁর জটাজুট অগ্নিশলাকার মতো। তাঁর নৃত্যের নাম– তাণ্ডব; তাতে বিশ্ব বিকম্পিত হয় ও গ্রহরা কক্ষচ্যুত হয়ে ব্যোমপথে বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি করে। রুদ্রের নিঃশ্বাসের জ্বালা– জগতের শ্মশান। তাঁর শূলাগ্রে বিদ্ধ হয়ে দিগ্হস্তীরা আর্তনাদ করে ওঠে। তাঁর নেত্রশাসনে চিত্ত-শ্মশানে কামদেব পুড়ে ছাই হয়। তাঁর মুখোচ্চারিত প্রণব প্রলয়ের গান– বিনাশের ঝঞ্ঝা। তা জগতকে পুঞ্জীভূত ধুলোয় পরিণত করে। তাঁর বিষাণ-বাদনের তালে তালে চতুর্দশ মৃত্যু নৃত্য করতে থাকে।’ –(বৃহৎ বঙ্গ)
ঈশ্বর মঙ্গল এবং সর্ব্বকল্যাণের কর্ত্তা বলিয়া "শিব"।"যো রোদযতান্যয়কারিণো জনান্ স রুদ্রঃ"- পরমেশ্বর দুস্কর্ম্মকারিদিগকে রোদন করান এজন্য তাঁহার নাম " রুদ্র" হইয়াছে।
ড. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্যে, ‘পণ্ডিতদের অনুমান– আদিম মানব গোষ্ঠীর মধ্যে গাছ, পাথর, বিভিন্ন জন্তু পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এরূপ কোন ‘জন্’ বা গোষ্ঠী হয়তো লম্বাটে পাথরকে শিব হিসাবে পূজা করতেন, যা পরবর্তী কালে বেদের রুদ্র দেবতার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিঙ্গপূজাকে ‘ট্রাইবাল’দের থেকে আসা বলেই মনে করেন। পরবর্তীকালে প্রত্ন-নিদর্শন হিসেবে প্রাপ্ত কয়েকটি শিবলিঙ্গের গায়ে শিবমূর্তি অঙ্কিত করে বা শিবের প্রতীক ত্রিশূল, পরশু ইত্যাদি অঙ্কিত করে উভয়ের ঐক্য বোঝানো হয়েছে। মূর্তি অঙ্কিত লিঙ্গকে বলে মুখলিঙ্গ। এধরনের মুখলিঙ্গ অতি প্রাচীন কালের প্রত্ন-নিদর্শনে তত বেশি পাওয়া যায় না। কাজেই লিঙ্গ-শিব-রুদ্রের মিশ্রণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক।’– (ভূমিকা, লিঙ্গ পুরাণ, পৃষ্ঠা-৯)
তার মানে, লিঙ্গের সাথে শিবের সম্বন্ধ যেভাবেই ঘটুক, দেবতা হিসেবে শিবের চরিত্র ও রূপ-কল্পনায় বৈদিক রুদ্রের বৈশিষ্ট্য এক হয়ে মিশে গেছে বলেই পণ্ডিতদের ধারণা। এভাবে ঋগ্বেদের রুদ্র পরবর্তীকালের শিবের সঙ্গে অভিন্ন বলে ঘোষিত হলেও তিনি একটি পৃথক ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন। আমরা দেখতে পাই, ঋগ্বেদে রুদ্র হলেন অন্তরীক্ষের দেবতা। রুদ্রকে উদ্দেশ্য করে ঋগ্বেদে মাত্র তিনটি স্বতন্ত্র সূক্ত রয়েছে। তবে দেবতা হিসেবে ঋগ্বেদে তাঁর বিশেষ প্রাধান্য না থাকলেও রুদ্রের পরিকল্পনায় বিবিধ বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কোথাও তিনি উগ্র, ক্রোধপরায়ণ ও পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর, এবং এই রূপেই বিস্তীর্ণ জগতের রক্ষাকর্তা। যেমন–
হবীমভি র্র্হভতে যো হবির্ভিরব স্তোমেভী রুদ্রং দিষীয়।
ঋদূদরঃ সুহবো মা নো অস্যৈ বভ্রুঃ সুশিপ্রো রীরধন্মনায়ৈ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/৫)।
স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ।
ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভুরে র্ন বা উ যোষদ্রুদ্রাদসূর্যম্ ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/৯)।
অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্ ।
অর্হন্নিদং দয়সে বিশ্বমভ্বং ন বা ওজীয়ো রুদ্রত্বদস্তি।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/১০)।
স্তুহি শ্রতং গর্তসদং যুবানং মৃগং ন ভীমমুপহত্নুমুগ্রম্ ।
মৃলা জরিত্রে রুদ্র স্তবানোহন্যং তে অস্মন্নি বপন্তু সেনাঃ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/১১)।
অর্থাৎ :
যে রুদ্র হব্য সম্বলিত আহ্বানদ্বারা আহুত হন, আমি স্তোত্রদ্বারা তাঁকে অপগত-ক্রোধ করব। কোমলোদর, শোভন আহ্বানবিশিষ্ট বভ্রুবর্ণ ও সুনাসিক রুদ্র আমাদের যেন তাঁর জিঘাংসাবৃত্তির বিষয়ীভূত না করেন। (ঋক-২/৩৩/৫)।। দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র ও বভ্রুবর্ণ রুদ্র দীপ্ত হিরণ্ময় অলঙ্কারে শোভিত হচ্ছেন। রুদ্র সমস্ত ভুবনের অধিপতি এবং ভর্তা, তাঁর বল পৃথককৃত হয় না। (ঋক-২/৩৩/৯)।। হে অর্চনার্হ ! তুমি ধনুর্বাণধারী; হে অর্চনার্হ ! তুমি নানারূপবিশিষ্ট ও পূজনীয় নিষ্ক ধারণ করেছ; হে অর্চনার্হ ! তুমি সমস্ত বিস্তীর্ণ জগৎকে রক্ষা করছ, তোমা অপেক্ষা অধিক বলবান আর কেউ নেই। (ঋক-২/৩৩/১০)।। হে স্তোতা ! প্রখ্যাত রথস্থিত, যুবা, পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর ও শত্রুদের বিনাশক, উগ্র রুদ্রকে স্তব কর। হে রুদ্র ! আমরা স্তব করলে তুমি আমাদের সুখী কর, তোমার সেনা শত্রুকে বিনাশ করুক। (ঋক-২/৩৩/১১)।।
আবার কোন কোন দৃষ্টান্তে রুদ্রের স্তুতি সুস্পষ্ট আতঙ্কজনিত বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই ঋগ্বেদে বারবার এরকম প্রার্থনা উচ্চারিত হতে দেখা যায়–
মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা না উক্ষিতম্ ।
মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১১৪/৭)।
মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অন্বেষু রীরিষঃ।
বীরাদ্মা নো রুদ্রং ভামিতো বধী র্হবিষ্মন্তঃ সর্দামত্ত্বা হবামহে।। (ঋগ্বেদ-১/১১৪/৮)।
আরে তে গোঘ্নমুত পুরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর সুম্নমস্মে তে অস্তু।
মৃলা চ নো অধি চ ব্রুহি দেবাধা চ নঃ শর্ম যচ্ছ দ্বিবর্হাঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১১৪/১০)।
অর্থাৎ :
হে রুদ্র ! আমাদের মধ্যে বৃদ্ধকে বধ করো না, বালককে বধ করো না, সন্তান জনয়িতাকে বধ করো না, গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করো না, আমাদের পিতাকে বধ করো না, মাতাকে বধ করো না, আমাদের শরীরে আঘাত করো না। (ঋক-১/১১৪/৭)।। হে রুদ্র ! আমাদের পুত্রকে হিংসা করো না; তার পুত্রকে হিংসা করো না, আমাদের অন্য মানুষকে হিংসা করো না, আমাদের গো ও অশ্ব হিংসা করো না। হে রুদ্র ! ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের বীরদের হিংসা করো না, কেননা আমরা হব্য নিয়ে সর্বদাই তোমাকে আহ্বান করি। (ঋক-১/১১৪/৮)।। হে বীরগণের ক্ষয়কারক ! তোমার কৃত গোহত্যা ও মানুষহত্যা দূরে থাকুক, আমরা যেন তোমার দত্ত সুখ পাই। আমাদের সুখী কর, হে দীপ্তিমান রুদ্র ! আমাদের পক্ষ হয়ে কথা বলো, তুমি উভয় পৃথিবীর স্বামী, আমাদের সুখ দাও। (ঋক-১/১১৪/১০)।।
এ-প্রেক্ষিতে ড. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণিধানযোগ্য বক্তব্যটি হলো,– ‘লৌকিক শিবের মধ্যে বৈদিক রুদ্র ভাবনা এক সময় মিশে গিয়েছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে বৈদিক রুদ্রই শিবেতে মিশেছেন। প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক মূর্তিকে ঋগ্বেদে রুদ্র বলা হয়েছে। আকাশের বিদ্যুৎ তাঁর হাতের বাণ, ধ্বংসাত্মক মরুতেরা তাঁর পুত্র (মরুৎদের তাই ঋক্ সংহিতায় ‘রুদ্রিয়াসঃ’ বলা হয়েছে। ঋ.সং. ১/৩৮/৭; ১/৬৪/২; ১/১১৪/৬; ২/৩৪/১০ ইত্যাদি মন্ত্র দ্রষ্টব্য।) শুধু তাই নয়– মহামারী, রোগ, বিষ ইত্যাদি অনিষ্টকারক সব কিছুর সঙ্গেই রুদ্রকে যুক্ত করা হয়েছে। এই দেবতাকে আর্যরা এত ভয় পেতেন যে এনার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, এবং সেজন্য বেদ মন্ত্রকে বিকৃত ভাবে উচ্চারণের বিধানও দেওয়া হয়েছে। লৌকিক ধর্মে গণেশ এবং শনিদেবতা সম্পর্কে এরূপ বিধান পাওয়া যায়। বিঘ্নের দেবতা গণেশকে পুরাণে ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা দ্রষ্টব্য)। শনিকেও একই কারণে ‘বারের ঠাকুর’ বলা হয়। এই সব লৌকিক দেবতাকে লোকে যেমন ভয়ে পূজা করে, তেমনি রুদ্রকেও ভয়ে স্তুতি করা হত। এই কারণেই হয়তো ঋগ্বেদে রুদ্রের স্তুতি অত্যন্ত কম। রুদ্র দেবতা বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে যজুর্বেদে একটা বিরাট স্থান অধিকার করেছেন।’– (ভূমিকা/ লিঙ্গ পুরাণ, পৃষ্ঠা-১৩)
তবে রুদ্রের একটি কল্যাণের দিকও আছে। ঋগ্বেদে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভিষক রূপে খ্যাত। তাই তিনি শুধুই আতঙ্ক-নিরসনের আশায় নয়, পার্থিব কল্যাণ-কামনায়, বিশেষ করে রোগ-নিরাময়কারক ওষধি প্রভৃতির কামনায়ও স্তুত হয়েছেন। যেমন–
মূলা নো রুদ্রোত নো ময়ষ্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে।
যচ্ছং চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতিষু।। (ঋগ্বেদ-১/১১৪/২)।
কুমারশ্চিৎ পিতরং বন্দমানং প্রতি নানাম রুদ্রোপয়ন্তম্ ।
ভূরে র্দাতারং সৎপতি গৃণীষে স্তুভস্ত্বং ভেষজা রাস্যস্মে।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/১২)।
যা বো ভেষজা মরুতঃ শুচীনি যা শন্তমা বৃষণো যা ময়োভু।
যানি মনুরবৃণীতা পিতা নস্তা শঞ্চ যোশ্চ রুদ্রস্য রশ্মি।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/১৩)।
ত্বাদত্তেভি রুদ্র শন্তমেভিঃ শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ।
ব্যস্মদ্দ্বেষো বিতরং ব্যংহো ব্যমীবাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/২)।
অর্থাৎ :
হে রুদ্র ! তুমি সুখী হও, আমাদের সুখী কর; তুমি বীরদের ক্ষয়কারী, আমরা নমস্কারের সাথে তোমার পরিচর্যা করি। পিতা মনু যে রোগসমূহ হতে উপশম ও ভয়সমূহ হতে উদ্ধার পেয়েছিলেন, হে রুদ্র ! তোমার উপদেশ হতে যেন আমরা তা পাই। (ঋক-১/১১৪/২)।। পিতা আশির্বাদ করবার সময় পুত্র যেরূপ তাঁকে নমস্কার করে, সেরূপ হে রুদ্র ! তুমি আসবার সময় আমরা তোমাকে নমস্কার করছি। হে রুদ্র ! তুমি বহুধনদাতা এবং সাধুলোকের পালক, আমরা স্তব করলে আমাদের ঔষধ প্রদান কর। (ঋক-২/৩৩/১২)।। হে মরুৎগণ ! তোমাদের যে নির্মল ঔষধ আছে, হে অভীষ্টবর্ষিগণ, তোমাদের যে ঔষধ অত্যন্ত সুখকর ও সুখপ্রদ, যে ঔষধ আমাদের পিতা মনু মনোনীত করেছিলেন, রুদ্রের সে সুখকর ভয়হারী ঔষধ আমরা কামনা করছি। (ঋক-২/৩৩/১৩)।। হে রুদ্র ! আমরা যেন তোমার দত্ত সুখকর ওষধিদ্বারা শতবর্ষ জীবিত থাকতে পারি। তুমি আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ কর, আমার পাপ একেবারে বিদূরিত কর এবং সর্বশরীরব্যাপী ব্যাধিপুঞ্জকে বিদূরিত কর। (ঋক-২/৩৩/২)।।
ঋগ্বেদের নানা জায়গায় রুদ্রের সঙ্গে মরুৎগণের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় রুদ্রের সঙ্গে মরুৎগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মরুৎগণও অন্তরীক্ষের দেবতা, তবে একটি দেবতা নন– একদল দেবতা, এবং সর্বত্রই দল হিসেবে তাঁদের উল্লেখ। এই কারণে তাঁদের নামের সঙ্গে ‘গণ’ শব্দ সংযুক্ত। বিভিন্ন সূক্তে রুদ্রকে মরুৎগণের পিতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–
উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রাস্বা পিতর্মরুতাং সুম্মমস্মে।
ভদ্রা হি তে সুমতি র্মৃলয়ত্তমাথা বয়মব ইত্তে বৃণীমহে।। (ঋগ্বেদ-১/১১৪/৯)।
আ তে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতু মা নঃ সূর্যস্য সন্দৃশো যুযোথাঃ।
অভি নো বীরো অর্বতি ক্ষমেত প্র জায়েমহি রুদ্র প্রজাভিঃ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/১)।
ইদং পিত্রে মরূতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্ধনম্ ।
রাস্বা নো অমৃত মর্তভোজনং ত্বনে তোকায় তনয়ায় মৃল।। (ঋগ্বেদ-১/১১৪/৬)।
অর্থাৎ :
পশুপালক যেরূপ সায়ংকালে পশুস্বামীদের তাদের পশু ফিরিয়ে দেয়, হে রুদ্র ! আমি সেরূপ তোমার স্তোত্র তোমাকে অর্পণ করছি। হে মরুৎগণের পিতা ! আমাদের সুখ দান কর, তোমার অনুগ্রহ অতিশয় সুখকর এবং কল্যাণকর, আমরা তোমার ক্ষণ প্রার্থনা করি। (ঋক-১/১১৪/৯)।। হে মরুৎগণের পিতা (রুদ্র) ! তোমার প্রদত্ত সুখ আমাদের নিকট আসুক, তুমি সূর্য দর্শন হতে আমাদের পৃথক করো না, আমাদের বীর পুত্রগণ শত্রুদের অভিভূত করুক। হে রুদ্র ! আমরা যেন পুত্র পৌত্রাদিতে অনেক হয়ে উঠি। (ঋক-২/৩৩/১)।। মধু হতেও অধিক মধুর এ স্তুতি বাক্য মরুৎগণের পিতা রুদ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত হচ্ছে, এতে (স্তোতার) বৃদ্ধি সাধন হয়। হে মরণরহিত রুদ্র ! মনুষ্যদের ভোজনরূপ অন্ন আমাদের প্রদান কর এবং আমাকে আমার পুত্রকে ও তার তনয়কে সুখ দান কর। (ঋক-১/১১৪/৬)।।
ঋগ্বেদের অন্যত্র রুদ্র-পুত্র অর্থে মরুৎগণকে ‘রুদ্রাসঃ’ বলা হয়েছে এবং কোথাও আবার ‘রুদ্রিয়গণ’ হিসেবে স্তুত হয়েছে। যেমন–
নহি বঃ শত্রু র্বিবিদে অধি দ্যবি ন ভূম্যাং রিশাদসঃ।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাশো নু চিদাধৃষে।। (ঋগ্বেদ-১/৩৯/৪)।
সত্যং ত্বেষা অমবস্তো ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ। মিহং কৃণ¦স্ত্যবাতাম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/৩৮/৭)।
চিত্রং তদ্বো মরুতো ষাম চেকিতে পৃশ্ন্যা যদুধরপ্যাপয়ো দুহুঃ।
যদ্বা নিদে নবমানস্য রুদ্রিয়াস্ত্রিতং জরায় জুরতামদাভ্যাঃ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৪/১০)।
অর্থাৎ :
হে শত্রুহিংসক মরুৎগণ ! দ্যুলোকে তোমাদের শত্রু নেই, পৃথিবীতেও নেই। হে রুদ্রপুত্রগণ ! তোমরা একত্রিত হও, (শত্রুদের) ধর্ষণার্থে তোমাদের বল শীঘ্র বিস্তৃত হোক। (ঋক-১/৩৯/৪)।। দীপ্তিমান ও বলবান রুদ্রীয়গণ সত্যই মরুভূমিতেও বায়ুরহিত বৃষ্টি দান করেন। (ঋক-১/৩৮/৭)।। হে মরুৎগণ; তোমরা যখন পৃশ্নির উধঃ দোহন করেছিলে, যখন স্তুতিকারীর নিন্দুককে হিংসা করেছিলে এবং ত্রিতের শত্রুদের বধ করেছিলে, হে অহিংসনীয় রুদ্রপুত্রগণ ! সে সময়ে তোমাদের বিচিত্র ক্ষমতা সকলেই জেনেছিল। (ঋক-২/৩৪/১০)।।
আবার ঋগ্বেদের অন্যত্র এই মরুৎগণকে ‘পৃশ্নিমাতরঃ’ অর্থাৎ পৃশ্নি মাতার সন্তান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং কোথাও কোথাও মরুৎগণের মাতা পৃশ্নি উল্লেখও রয়েছে। যেমন–
বিশ্বান্দেবান্ হবামহে মরুতঃ সোমপীতয়ে। উগ্রা হি পৃশ্নিমাতরঃ।। (ঋগ্বেদ-১/২৩/১০)।
দ্যাবো ন স্তৃভিশ্চিতয়ন্ত খাদিনো ব্যভ্রিয়া ন দ্যূতয়ন্ত বৃষ্টয়ঃ।
রুদ্রো যদ্বো মরুতো রু´বক্ষসো বৃষাজনি পৃশ্ন্যাঃ শক্র ঊধনি।। (ঋগ্বেদ-২/৩৪/২)।
প্র যে মে বংধ্বেষে গাং বোচন্ত সূরয়ঃ পৃশ্নিং বোচন্তে মাতরম্ ।
অধা পিতরমিষ্মিণং রুদ্রং বোচন্ত শিক্বসঃ।। (ঋগ্বেদ-৫/৫২/১৬)।
অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সংভ্রাতরো বাবৃধূঃ সৌভগায়।
যুবা পিতা স্বপা রুদ্র এষাং সুদুঘা পৃশ্নিঃ সুদিনা মরুদ্ভ্যঃ।। (ঋগ্বেদ-৫/৬০/৫)।
অর্থাৎ :
সমস্ত মরুৎ দেবগণকে সোমপানার্থে আহ্বান করি, তাঁরা উগ্র ও পৃশ্নির সন্তান। (ঋক-১/২৩/১০)।। হে সুবর্ণবক্ষ মরুৎগণ ! যেহেতু সেচন সমর্থ রুদ্র পৃশ্নির নির্মল উদরে তোমাদের উৎপন্ন করেছেন; অতএব আকাশ যেরূপ নক্ষত্রে শোভিত হয়, তোমরা সেরূপ স্বীয় আভরণে শোভিত হও। তোমরা শত্রভক্ষক ও জলপ্রেরক, তোমরা মেঘস্থ বিদ্যুতের ন্যায় শোভিত হও। (ঋক-২/৩৪/২)।। আমি তাদের উৎপত্তিক্রম অনুসন্ধান করায়, জ্ঞানী মরুৎগণ আমাকে এ উত্তর দিয়েছেন; তাঁরা বলেছেন পৃশ্নি তাদের জননী, বলশালী মরুৎগণ বলেছেন অন্নদাতা রুদ্র তাঁদের জনক। (ঋক-৫/৫২/১৬)।। এ সমস্ত মরুৎ এক সময়ে উৎপন্ন, সুতরাং পরস্পর জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠভাব বর্জিত হয়ে ভ্রাতৃভাবে ও সমৃদ্ধি সহকারে বর্ধিত হয়েছেন। নিত্যতরুণ, সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী মরুৎগণের পিতা রুদ্র ও জননী দোহনযোগ্যা পৃশ্নি মরুৎগণের নিমিত্ত দিন সকল অনুকুল করুন। (ঋক-৫/৬০/৫)।।
ঋগ্বেদ অনুসারে পৃশ্নি একটি গরুর নাম। ফলে মরুৎগণকে ‘গোমাতরঃ’ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন–
স বহ্নিঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ পবিত্রবান্ পুনাতি ধীরো ভুবনানি মায়য়া।
ধেনুঞ্চ পৃশ্নিং বৃষভঃ সুরেতসং বিশ্বাহা শুক্রং পয়ো অস্য দুক্ষত।। (ঋগ্বেদ-১/১৬০/৩)।
গোভির্বাণো অজ্যতে সোভরীণাং রথে কোশে হিরণ্যয়ে।
গোবন্ধবঃ সুজাতাস ইষে ভুজে মহান্তো নঃ স্পরসে নু।। (ঋগ্বেদ-৮/২০/৮)।
অর্থাৎ :
আদিত্য পিতা মাতা স্বরূপ দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র। তিনি ধীর এবং ফলপ্রদায়ী তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাদ্বারা সমস্ত ভূতগণকে প্রকাশ করছেন। তিনি পৃশ্নি ধেনু ও সেচন সমর্থ বৃষকে প্রকাশ করছেন ও দ্যুলোক হতে নির্মল জল দোহন করছেন। (ঋক-১/১৬০/৩)।। সোভরি ঋষিগণের শব্দদ্বারা হিরণ্ময় রথের মধ্যদেশে মরুৎগণের বাণ ব্যক্ত হচ্ছে। গোমাতৃক সুজন্মা, মহানুভব মরুৎগণ আমাদের অন্ন ভোগ ও প্রীতিপ্রদ হোন। (ঋক-৮/২০/৮)।।
কিন্তু মরুৎগণকে গোমাতৃক জাতীয় পৌরাণিক কল্পনার কারণ কী হতে পারে? ‘পৃশ্নি’ অর্থ হলো নানা বর্ণযুক্ত। তাহলে নানা বর্ণযুক্তা মরুৎগণের এই মাতা কে? বেদ-টীকাকার সায়ণের ভাষ্যে পৃশ্নি অর্থ পৃথিবী। আবার কোথাও তিনি ‘পৃশ্নি’ শব্দের অর্থ শুক্লবর্ণ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত অভিধান ‘নিঘণ্টু’ অনুযায়ী পৃশ্নি অর্থে আকাশ। তবে আধুনিক পণ্ডিত গবেষকরা অনুমান করতে চেয়েছেন, বৈদিক কবিরা এখানে আকাশের বৃষ্টিদায়িনী মেঘকে দুগ্ধদায়িনী গরুর সঙ্গে তুলনা করেছেন, অতএব গোমাতৃক অর্থে মরুৎগণ প্রকৃতপক্ষে মেঘতনয় বলেই কল্পিত। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সুবিশাল ঋগ্বেদ সাহিত্যে বহু কবি বহুভাবে এই দেবতাদের নিয়ে বহু কল্পনা করেছেন; তাই মরুৎগণের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে কোন এক অদ্বিতীয় সিদ্ধান্তের সাহায্যে সমস্ত নজিরের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা পাওয়া সুকঠিন। কেননা, এই মরুৎগণই কোথাও ‘সিন্ধু-মাতরঃ’ বলে কল্পিত, আবার বর্ণনা-বিশেষে তাঁরা কোথাও ‘স্বয়ং-উৎপন্ন’ কিংবা কোথাও ‘স্বর্গ-তনয়’ হিসেবেও কল্পিত হয়েছেন। যেমন–
গ্রাবাণো ন সূরয়ঃ সিন্ধুমাতর আদর্দিরাসো অদ্রয়ো ন বিশ্বহা।
শিশুলা ন ক্রীলয়ঃ সুমাতরো মহাগ্রামো ন যামন্নুত ত্বিষা।। (ঋগ্বেদ-১০/৭৮/৬)।
বব্রাসো ন যে স্বজাঃ স্বতবস ইষং স্বরভিজায়ন্ত ধূতয়ঃ।
সহস্রিয়াসো অপাং নোর্ময় আসা গাবো বন্দ্যাসো নোক্ষশঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১৬৮/২)।
শ্রিয়ে মর্যাসো অঞ্জীরকৃণ্বত সুমারুতং ন পূর্বীরতি ক্ষপঃ।
দিবস্পুত্রাস এতা ন যেতির আদিত্যাসস্তে অক্রা ন বাবৃধুঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৭৭/২)।
অর্থাৎ :
জল প্রেরণকারী মেঘের ন্যায় সিন্ধুমাতার সন্তানেরা (মরুৎগণ) নদী নির্মাণ করেন। বিদীর্ণকারী অস্ত্রশস্ত্রের ন্যায় সকলি তাঁরা ধ্বংস করেন। বৎসল মাতার শিশুদের ন্যায় তাঁরা ক্রীড়া করেন। বহুলোকসমূহের ন্যায় তাঁরা দীপ্তিসহকারে গমন করেন। (ঋক-১০/৭৮/৬)।। স্বয়ং-উৎপন্ন, স্বাধীনবল, কম্পনশীল মরুৎগণ যে মূর্তিমান হয়ে অন্ন ও স্বর্গের জন্য প্রাদুর্ভূত হচ্ছেন। অসংখ্য এবং প্রশংসনীয় ধেনু যেরূপ দুগ্ধদান করে, জলোর্মির ন্যায় তাঁরা সেরূপ হয়ে জলদান করেন। (ঋক-১/১৬৮/২)।। এ মরুৎগণ পূর্বে মনুষ্য ছিলেন, পুণ্যদ্বারা দেবতা হয়েছেন, এরা শরীর শোভার্থে অলঙ্কার ধারণ করেন। বিস্তর সৈন্য একত্র হয়েও মরুৎগণকে অতিক্রম করতে পারে না। আমরা এখনও স্তব করি নি বলে এ সকল দ্যুলোকের পুত্রগণ অর্থাৎ মরুৎগণ এখনও দেখা দেন নি, মহাবল পরাক্রান্ত এ সকল অদিতি সন্তানগণ এখনও বৃদ্ধিযুক্ত হন নি। (ঋক-১০/৭৭/২)।।
তবে বৈদিক কবিদের এই কল্পনা যত বিচিত্রই হোক না কেন, রুদ্রের সাথে গরু বা গো-মাতার সম্পর্ক এবং পরবর্তীকালের শিব-কল্পনায় শিবের বাহন বা লাঞ্ছন হিসেবে যে গরু তথা বৃষ বা বলীবর্দের উপস্থিতি রয়েছে, কিংবা শিবের অন্যতম প্রধান অনুচর নন্দী যে মূলত বৃষ-কল্পনা সেটিও বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। কেননা, বৃষের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যোগী শিবের মূর্তির সঙ্গে বৃষমূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া ঋগ্বেদের একাধিক মন্ত্রেও বৃষের সঙ্গে রুদ্রের যে সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়, কয়েকটি ক্ষেত্রে রুদ্রকেই বলা হয়েছে বৃষভ। যেমন–
উন্মা মমন্দ বৃষভো মরুত্বান্ত্বক্ষীয়সা বয়সা নাধমানম্ ।
ঘৃণীব ছায়ামরপা অশীয়া বিবাসেয়ং রুদ্রস্য সুম্নম্ ।। (ঋগ্বেদ-সংহিতা-২/৩৩/৬)
অর্থাৎ : আমি প্রার্থনা করছি, অভীষ্টবর্ষী (বৃষভ) মরুৎবিশিষ্ট রুদ্র আমাকে দীপ্ত অন্নদ্বারা তৃপ্ত করুন। রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তি যেরূপ ছায়া লাভ করে, আমি সেরূপ পাপশূন্য হয়ে রুদ্রদত্ত সুখ লাভ করব এবং রুদ্রের পরিচর্যা করব।
এখানে বৃষভ-এর বেদার্থে অভীষ্টবর্ষী বলা হয়েছে। এ-প্রেক্ষিতে ড. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,– ‘কাম্যবস্তুর বর্ষক হিসাবে বৃষভ শব্দটিকে টীকাকারেরা ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকে মনে করেন যে রুদ্রের বৃষভ বা ষাঁড় রূপের কথাই এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে। দেবতাদের পশুরূপ কল্পনার ইতিহাস অতি প্রাচীন। হয়তো এর মধ্যে টোটেম বিশ্বাস বা অন্য কোন প্রকার বিশ্বাসের কথাও লুকিয়ে আছে। পরবর্তী কালের ইতিহাসে পূজিত পশুরা বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন এবং তাঁদের বাহনে পর্য্যবসিত হয়েছেন। বৃষভও এভাবেই শিবের বাহনে পরিণত হয়েছেন অনেক পরে।’
এছাড়া দেবতার বাহনদের বিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি বলেন,– ‘প্রসঙ্গত বলা চলতে পারে যে শতপথ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি গ্রন্থে রুদ্রের পশু হিসাবে আখু বা ইঁদুরের উল্লেখ আছে। এই পশুটি ছেদনের প্রতীক বা ধ্বংসের প্রতীক। শিবের পুত্র হিসাবে পরবর্তী পুরাণাদি সাহিত্যে গণেশ এই বাহনকে লাভ করেছিলেন।’– (ভূমিকা/ লিঙ্গ পুরাণ, পৃষ্ঠা-৯)
এছাড়া দেবতার বাহনদের বিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি বলেন,– ‘প্রসঙ্গত বলা চলতে পারে যে শতপথ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি গ্রন্থে রুদ্রের পশু হিসাবে আখু বা ইঁদুরের উল্লেখ আছে। এই পশুটি ছেদনের প্রতীক বা ধ্বংসের প্রতীক। শিবের পুত্র হিসাবে পরবর্তী পুরাণাদি সাহিত্যে গণেশ এই বাহনকে লাভ করেছিলেন।’– (ভূমিকা/ লিঙ্গ পুরাণ, পৃষ্ঠা-৯)
ঋগ্বেদের পর যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় নামক অংশে (যেখানে রুদ্রের শতনাম কীর্তিত আছে) তাঁর চরিত্রের প্রভূত বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই নামগুলির মধ্যে কয়েকটি তাঁর উগ্র রূপ ব্যঞ্জনা করে, কয়েকটি আবার তাঁর মঙ্গলময় সত্তার দ্যোতক। এই দুই রূপ তাঁর ঘোর ও শিব বা শান্ত তনু। যেমন, কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয়-সংহিতার চতুর্থ কাণ্ডের পঞ্চম প্রপাঠকের প্রথম মন্ত্রে বলা হয়েছে–
নমস্তে রুদ্র মন্যব উতো ত ইষবে নমঃ। নমস্তে অস্তু ধন্বনে বাহুভ্যামুত তে নমঃ। যা ত ইষুঃ শিবতমা শিবং বভূব তে ধনুঃ। শিবা শরব্যা যা তব তয়া নো রুদ্র মৃড়য়। যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাহপাপকাশিনী তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভি চাকশীহি। যামিষুম্ গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে। শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ। শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি। যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ। অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্ । অহীংশ্চ সর্ব্বান্ জম্ভয়ন্ৎ সর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যঃ। অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চেমাং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোহবৈষাং হেড় ঈমহে। অসৌ যোহবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ। উতৈনং গোপা অদৃশন্নদৃশন্নুদহার্য্যঃ উতৈনং বিশ্বা ভূতানি স দৃষ্টো মৃড়য়াতি নঃ। নমো অস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢুষে। অথো যে অস্য সত্বানোহহং তেভ্যোহকরং নমঃ। প্র মুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরার্ত্নিয়োর্জ্জ্যাম্ । যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বপ। অবতত্য ধনুস্ত্বং সহস্রাক্ষ শতেষুধে। নিশীর্ষ্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ সুমনা ভব। বিজ্যং ধনুঃ কপর্দ্দিনো বিশল্যো বাণবাম্ উত। অনেশন্নস্যেষব আভুরস্য নিষঙ্গথিঃ। যা তে হেতির্মীঢুষ্টম হস্তে বভূব তে ধনুঃ। তয়াহস্মান্বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্ময়া পরি বূভুজ। নমস্তে অস্ত্বায়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে। উভাভ্যামুত তে নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে। পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্বৃণক্তু বিশ্বতঃ। অথো য ইষুধিস্তবারে অস্মন্নি ধেহি তম্ ।। (তৈত্তিরীয়-সংহিতা-৪/৫/১)
অর্থাৎ :
হে রুদ্র, তোমার কোপকে নমস্কার করি, তোমার বাণকে নমস্কার করি এবং তোমার ধনুর্বাণ যুক্ত বাহুযুগলকে নমস্কার করি। এগুলি শত্রুর প্রতি প্রবৃত্ত হোক, আমার প্রতি নয়। হে রুদ্র, তোমার যে মঙ্গলময় ইষু আছে, তোমার যে কল্যাণপ্রদ ধনু আছে, এবং যে শান্ত ইষুধি আছে, তাদের দ্বারা আমাদের সুখী কর। হে রুদ্র, তোমার অনুগ্রহকারিণী তনু, আমাদের প্রতি যেন ঘোর রূপ না হয়। হে গিরিশ, তোমার সুখকর রূপ আমাদের কাছে প্রকাশ কর। হে গিরিশ, যে বাণ শত্রুর প্রতি নিক্ষেপের জন্য হস্তে ধারণ করেছ, হে কৈলাস-গিরির পালক রুদ্র, তোমার সে বাণ আমাদের প্রতি শান্ত কর, তোমার বাণ আমাদের পুত্রাদি ও পশুদের যেন হিংসা না করে। হে গিরিশ, তোমাকে পাবার জন্য আমরা মঙ্গলকর স্তূতিরূপ বাক্যের দ্বারা প্রার্থনা করছি, যাতে সকল মানুষ ও গব্যাদি পশু রোগরহিত হয়ে শোভন মন লাভ করে। হে রুদ্র, সকলের ভেতর আমাকে অধিক বল। তুমি দেবতাদের মধ্যে মুখ্য ও তাদের পালনে সক্ষম। ধ্যান মাত্রে সকলের রোগের উপশম কর জন্য তুমি চিকিৎসক। তুমি সর্প, ব্যাঘ্র ও রাক্ষস জাতিদের বিনাশক। আদিত্যরূপ রুদ্র উদয়কালে অত্যন্ত রক্তবর্ণ, উদয়ের পরে নানা বর্ণে অন্ধকারাদির নিবর্তক রূপে অত্যন্ত মঙ্গলরূপ রুদ্রের সহস্র সংখ্যক রশ্মি পূর্বাদি দিকে বিস্তৃত হয়েছে, সে রশ্মিরূপ রুদ্রগণের ক্রোধ-সদৃশ তীক্ষ্ণত্ব ভক্তি ও নমস্কারের দ্বারা আমরা নিবারণ করব। যে রুদ্র কালকূট বিষ ধারণে নীলগ্রীব; সে রুদ্র লোহিত বর্ণরূপে মণ্ডলবর্তী হয়ে উদয় ও অস্ত সম্পন্ন করছেন, সে রুদ্রকে গোপগণ, জল আহরণকারিণী গ্রাম্য রমণীগণ এবং গো-মহিষাদি সকল প্রাণী দর্শন করে। সকলের দর্শন দেবার জন্য রুদ্রদেব আদিত্য মূর্তি ধারণ করেছেন, তার কৈলাসবর্তী রুদ্ররূপ বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞজন দেখে থাকে। সে রুদ্র আমাদের দর্শন দানে সুখী করুন। সে নীলগ্রীব, সহস্রাক্ষ, বৃষ্টিকর্তা রুদ্রকে নমস্কার করছি। এ রুদ্রের দ্বারা ভৃত্য তাদের সকলকে নমস্কার করছি। হে ভগবান রুদ্র, ধনুর্ধারী তোমার ধনুর জ্যা খুলে ফেলে ও তীক্ষ্ণ বাণের ফলাগুলি ইষুধির মধ্যে রেখে আমাদের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক শান্ত হও। (তৈত্তিরীয়-সংহিতা-৪/৫/১)
অন্যদিকে রুদ্রের শতনাম কীর্তিত শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী-সংহিতার রুদ্রাধ্যায় নামক ষোড়শ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত (১৬/১-৫) মন্ত্রে বলা হয়েছে–
নমস্তে রুদ্র মন্যব উতো ত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যামুত তে নমঃ।। ১।। যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাহপাপকাশিনী তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভি চাকশীহি।। ২।। যামিষুম্ গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে। শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ।। ৩।। শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি। যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ।। ৪।। অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্ । অহীংশ্চ সর্ব্বান্ জম্ভয়ন্ৎ সর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যো হধরাচীঃ পরা সুব।। ৫।। (বাজসনেয়ী-সংহিতা-১৬/১-৫)
অর্থাৎ :
হে দুঃখনাশক জ্ঞানপ্রদ রুদ্র, তোমার ক্রোধের উদ্দেশে নমস্কার, তোমার বাণ ও বাহুযুগলকে নমস্কার করি। ১।। হে রুদ্র, তোমার যে মঙ্গলময়, সৌম্য, পুণ্যপ্রদ শরীর আছে, হে গিরিশ, সে সুখতম শরীরের দ্বারা আমাদের দিকে তাকাও। ২।। হে গিরিশ, শত্রুর প্রতি নিক্ষেপের জন্য তুমি হস্তে যে বাণ ধারণ করেছ, হে প্রাণিগণের ত্রাতা, তা কল্যাণকর কর, পুরুষ ও জগতের হিংসা করো না। ৩।। হে গিরিশ, মঙ্গলময় স্তুতি বাক্যে তোমায় পাবার জন্য প্রার্থনা জানাই যাতে জগতের সকলে নীরোগ ও শোভনমনস্ক হয়। ৪।। হে অধিকবদনশীল, আমায় সর্বাধিক বল, তুমি সকলের পূজ্য ও স্মরণমাত্র দেবগণের হিতকারী ভিষক। হে রুদ্র, সকল সর্প ব্যাঘ্রাদি বিনাশ করে অধোগমনশীল রাক্ষসীদের দূর করে দাও। ৫।।
বাজসনেয়ী সংহিতার শতরুদ্রীয় ১৬ অধ্যায়ের অন্য মন্ত্রগুলি বাহুল্য বিবেচনায় উদ্ধৃত করা হয়নি। তবে এই শতরুদ্রীয় অধ্যায় বর্তমান আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, পরবর্তীকালের পৌরাণিক যুগের দেহী শিবের কল্পনায় যেসব বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনীর পরস্পর সমন্বয় ঘটেছে সেগুলির কল্পবীজ যে যজুর্বেদের এসব মন্ত্রের মধ্যে উপ্ত ছিলো তা বোধকরি বলা বাহুল্য হবে না। বেদের রুদ্র যেমন ব্যাধি, মৃত্যু ও অমঙ্গলের কারক, তাঁকে তুষ্ট করলে তিনি সেগুলির প্রতিকারও করেন। ড. উদয়চন্দ্রের ভাষ্যে–
‘রুদ্র দেবতার নামকরণ প্রসঙ্গে বেদ ও বেদাঙ্গে নানা প্রকার কল্পনা করা হয়েছে। বাজসনেয় সংহিতায় তাঁর সম্বন্ধে– ‘উচ্চৈঃ ঘোষঃ’ (১৬/১৯) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যাস্ক এখানে থেকেই অনুমান করেন যে গর্জনকারী হলেন রুদ্র– ‘রুদ্রো রৌরীতি সতঃ’ (নিরুক্ত ১০/৫)। বেদ ব্যাখ্যাকার সায়ণাচার্য্য অন্যভাবে রুদ্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে যিনি অনন্তকাল সকলকে কাঁদান তিনিই রুদ্র– ‘রোদয়তি সর্বমন্তকালে ইতি রুদ্রঃ’ (১/৪৩/১ ঋক্ভাষ্য)। যিনি শত্রুদের কাঁদান তিনি রুদ্র– ‘রুৎ সংসারাখ্যং দুঃখং তং দ্রাবয়তি অপগময়তি বিনাশয়তি ইতি রুদ্রঃ’ (১/১১৪/১ ঋক্ভাষ্য)। দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে রুদ্র শব্দকে নির্বাচন করার চেষ্টা সায়ণভাষ্যে পরিলক্ষিত হয়– ‘রুৎ শব্দাত্মিকা বাণী তৎপ্রতিপাদ্যা আত্মবিদ্যা বা তমুপাসকেভ্যো রাতি দদাতি ইতি রুদ্রঃ’ (১/১১৪/১ ঋক্ভাষ্য।) অর্থাৎ রুৎ শব্দের অর্থ শব্দাত্মিকা বাণী বা আত্মবিদ্যা; যিনি উপাসকদের সেই আত্মবিদ্যা দেন তিনিই রুদ্র। ঐ মন্ত্রেরই ভাষ্যে রুদ্র শব্দের আর একটি নির্বচনে বলা হয়েছে– যা আবৃত করে, সেই অন্ধকার হল রুৎ; সেই রুৎ বা অন্ধকারকে বিজারণকারী হলেন রুদ্র (রুণদ্ধি আবৃনোতি ইতি রুৎ অন্ধকারাদি। তৎ দৃণাতি বিদারয়তি ইতি রুদ্রঃ)। এই মতটি তান্ত্রিক বেদভাষ্যকার মহীধরের ভাষ্যের প্রতিধ্বনি। বাজসনেয়ী সংহিতার ১৬/১ মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর রুদ্র সম্পর্কে বলেছেন– ‘বরণৎ রুৎ জ্ঞানং রাতি দদাতি রুদ্রঃ। অথবা পাপিনো নরান্ দুঃখভোগেন রোদয়তি রুদ্রঃ’। রুদ্র নিজে রোদন করেন বলেই তাঁর এরূপ নামকরণ হয়েছিল বলে সায়ণ ১/১১৪/১ ঋক্-মন্ত্রের ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন এবং সেই সংক্রান্ত একটি আখ্যায়িকার কথাও বলেছেন।’– (ভূমিকা/ লিঙ্গ পুরাণ, পৃষ্ঠা-১৪)
‘রুদ্র দেবতার নামকরণ প্রসঙ্গে বেদ ও বেদাঙ্গে নানা প্রকার কল্পনা করা হয়েছে। বাজসনেয় সংহিতায় তাঁর সম্বন্ধে– ‘উচ্চৈঃ ঘোষঃ’ (১৬/১৯) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যাস্ক এখানে থেকেই অনুমান করেন যে গর্জনকারী হলেন রুদ্র– ‘রুদ্রো রৌরীতি সতঃ’ (নিরুক্ত ১০/৫)। বেদ ব্যাখ্যাকার সায়ণাচার্য্য অন্যভাবে রুদ্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে যিনি অনন্তকাল সকলকে কাঁদান তিনিই রুদ্র– ‘রোদয়তি সর্বমন্তকালে ইতি রুদ্রঃ’ (১/৪৩/১ ঋক্ভাষ্য)। যিনি শত্রুদের কাঁদান তিনি রুদ্র– ‘রুৎ সংসারাখ্যং দুঃখং তং দ্রাবয়তি অপগময়তি বিনাশয়তি ইতি রুদ্রঃ’ (১/১১৪/১ ঋক্ভাষ্য)। দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে রুদ্র শব্দকে নির্বাচন করার চেষ্টা সায়ণভাষ্যে পরিলক্ষিত হয়– ‘রুৎ শব্দাত্মিকা বাণী তৎপ্রতিপাদ্যা আত্মবিদ্যা বা তমুপাসকেভ্যো রাতি দদাতি ইতি রুদ্রঃ’ (১/১১৪/১ ঋক্ভাষ্য।) অর্থাৎ রুৎ শব্দের অর্থ শব্দাত্মিকা বাণী বা আত্মবিদ্যা; যিনি উপাসকদের সেই আত্মবিদ্যা দেন তিনিই রুদ্র। ঐ মন্ত্রেরই ভাষ্যে রুদ্র শব্দের আর একটি নির্বচনে বলা হয়েছে– যা আবৃত করে, সেই অন্ধকার হল রুৎ; সেই রুৎ বা অন্ধকারকে বিজারণকারী হলেন রুদ্র (রুণদ্ধি আবৃনোতি ইতি রুৎ অন্ধকারাদি। তৎ দৃণাতি বিদারয়তি ইতি রুদ্রঃ)। এই মতটি তান্ত্রিক বেদভাষ্যকার মহীধরের ভাষ্যের প্রতিধ্বনি। বাজসনেয়ী সংহিতার ১৬/১ মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর রুদ্র সম্পর্কে বলেছেন– ‘বরণৎ রুৎ জ্ঞানং রাতি দদাতি রুদ্রঃ। অথবা পাপিনো নরান্ দুঃখভোগেন রোদয়তি রুদ্রঃ’। রুদ্র নিজে রোদন করেন বলেই তাঁর এরূপ নামকরণ হয়েছিল বলে সায়ণ ১/১১৪/১ ঋক্-মন্ত্রের ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন এবং সেই সংক্রান্ত একটি আখ্যায়িকার কথাও বলেছেন।’– (ভূমিকা/ লিঙ্গ পুরাণ, পৃষ্ঠা-১৪)
অথর্ববেদে রুদ্রের কয়েকটি নাম পাওয়া যায় যথা– রুদ্র, শর্ব, উগ্র, ভব, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথের বর্ণনায়–
‘প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহাভারতেও রুদ্র-শিব দেবতার দুই তনুর কথা একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে– দ্বে তনূ তস্য দেবস্য ব্রাহ্মণাঃ বেদজ্ঞাঃ বিদুঃ। ঘোরামন্যাং শিবামন্যাং…। অথর্ববেদে রুদ্র দেবতার সাত মুখ্য নাম যথা– রুদ্র, শর্ব, উগ্র, ভব, পশুপতি, মহাদেব এবং ঈশান; দেবতা এই সাতটি নামে বিভিন্ন দিকের প্রাণিগণের সংরক্ষক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভব নামধারী দেবতা পূর্বদিকের মধ্যভাগে স্থিত আর্যগোষ্ঠী হইতে বহিষ্কৃত ব্রাত্যদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। শতপথ ব্রাহ্মণে রুদ্র ঊষাদেবীর পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং প্রজাপতি এক এক করিয়া তাঁহাকে আটটি নাম প্রদান করেন। অথর্ববেদোক্ত সাতটি নামের সহিত অশনি (বজ্র) নাম যোগ করিয়া তালিকার সংখ্যা পূরণ করা হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে রুদ্র, শর্ব, উগ্র ও অশনি দেবতার ঘোর রূপ এবং বাকী কয়টি যথা ভব, পশুপতি, মহাদেব এবং ঈশান তাঁহার মঙ্গলময় রূপ ব্যঞ্জনা করে। শতপথ ব্রাহ্মণের কয়েকটি অংশে রুদ্রকে অগ্নির আর এক রূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত আট নাম অগ্নির এবং এই বিভিন্ন নামে দেবতা ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরিচিত ছিলেন। পূর্বদেশের লোকেরা তাঁহাকে শর্ব নামে এবং বাহীকেরা তাঁহাকে ভব নামে অভিহিত করিত। রুদ্র সম্বন্ধে এই সকল এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ আলোচনা করিয়া ইহা অনুমান করা যায় যে এই দেবতার পূর্ণ রূপায়ণে বিভিন্ন সমগোষ্ঠীয় দেবসত্তার সহিত ইঁহার সংমিশ্রণ বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল।’– (পঞ্চোপাসনা, পৃষ্ঠা-১২৬)
‘ঐতরেয়, শতপথ, তাণ্ড্য এবং গোপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতির অগম্যাগমনের জন্য রুদ্রকে তাঁর শাস্তিদাতা-রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শাংখ্যায়ন, কৌষীতকি প্রভৃতি ব্রাহ্মণেও রুদ্রের বিভিন্ন নামের উল্লেখ আছে।’– (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/ ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৯৯)
‘প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহাভারতেও রুদ্র-শিব দেবতার দুই তনুর কথা একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে– দ্বে তনূ তস্য দেবস্য ব্রাহ্মণাঃ বেদজ্ঞাঃ বিদুঃ। ঘোরামন্যাং শিবামন্যাং…। অথর্ববেদে রুদ্র দেবতার সাত মুখ্য নাম যথা– রুদ্র, শর্ব, উগ্র, ভব, পশুপতি, মহাদেব এবং ঈশান; দেবতা এই সাতটি নামে বিভিন্ন দিকের প্রাণিগণের সংরক্ষক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভব নামধারী দেবতা পূর্বদিকের মধ্যভাগে স্থিত আর্যগোষ্ঠী হইতে বহিষ্কৃত ব্রাত্যদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। শতপথ ব্রাহ্মণে রুদ্র ঊষাদেবীর পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং প্রজাপতি এক এক করিয়া তাঁহাকে আটটি নাম প্রদান করেন। অথর্ববেদোক্ত সাতটি নামের সহিত অশনি (বজ্র) নাম যোগ করিয়া তালিকার সংখ্যা পূরণ করা হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে রুদ্র, শর্ব, উগ্র ও অশনি দেবতার ঘোর রূপ এবং বাকী কয়টি যথা ভব, পশুপতি, মহাদেব এবং ঈশান তাঁহার মঙ্গলময় রূপ ব্যঞ্জনা করে। শতপথ ব্রাহ্মণের কয়েকটি অংশে রুদ্রকে অগ্নির আর এক রূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত আট নাম অগ্নির এবং এই বিভিন্ন নামে দেবতা ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরিচিত ছিলেন। পূর্বদেশের লোকেরা তাঁহাকে শর্ব নামে এবং বাহীকেরা তাঁহাকে ভব নামে অভিহিত করিত। রুদ্র সম্বন্ধে এই সকল এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ আলোচনা করিয়া ইহা অনুমান করা যায় যে এই দেবতার পূর্ণ রূপায়ণে বিভিন্ন সমগোষ্ঠীয় দেবসত্তার সহিত ইঁহার সংমিশ্রণ বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল।’– (পঞ্চোপাসনা, পৃষ্ঠা-১২৬)
‘ঐতরেয়, শতপথ, তাণ্ড্য এবং গোপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতির অগম্যাগমনের জন্য রুদ্রকে তাঁর শাস্তিদাতা-রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শাংখ্যায়ন, কৌষীতকি প্রভৃতি ব্রাহ্মণেও রুদ্রের বিভিন্ন নামের উল্লেখ আছে।’– (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/ ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৯৯)
এক্ষেত্রে ড. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিঙ্গ পুরাণের ভূমিকায় (পৃষ্ঠা-১৪-৫) বলছেন,– ‘ঋগ্বেদে বিশেষতঃ যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় রুদ্রের একটি প্রসন্ন মূর্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়। ঋক্-সংহিতার ১/৪৩/১, ১/১১৪/৫, ২/৩৩/২, ৫/৪২/১১ ইত্যাদি মন্ত্রের বিভিন্ন বিশেষণ এক্ষেত্রে স্মরণীয়। বেদের বিভিন্ন বিশেষণ পর্য্যালোচনা করলে রুদ্রের একটি শরীরী সত্ত্বার পরিচয়ও পাওয়া যায়। ইন্দ্র, অগ্নি ইত্যাদি দেবতার সঙ্গে কোথাও কোথাও রুদ্রকে এক করে দেখাবার চেষ্টা থেকে এবং পরবর্তী পুরাণগুলিতে উল্লিখিত শিবের শতনাম, সহস্র নাম ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে এই দেবতার আড়ালে অনেক লৌকিক ও বৈদিক দেবতা একাত্ম হয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে বেদেই সহস্র সহস্র রুদ্রের কথা আমরা পাই।’
‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩/৩/৯, শতপথ ব্রাহ্মণ ১/৭/৪/১-৪ প্রভৃতি অংশে কথিত রুদ্রোৎপত্তির কাহিনী এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের স্মৃতিতে আসে। প্রজাপতি পশুরূপে নিজের কন্যাকে ধর্ষণ করলে দেবতারা রেগে গেলেন এবং তাদের সম্মিলিত ক্রোধ থেকেই রুদ্রের আবির্ভাব হল। রুদ্র বাণাঘাতে প্রজাপতিকে বধ করলেন। (পরবর্তী পুরাণগুলিতে এই কাহিনীকে একটু ভিন্ন ভাবে স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে শিবের ক্রোধ থেকে উৎপন্ন হয়ে বীরভদ্র দক্ষ প্রজাপতিকে বধ করেছেন)। সমস্ত দেবতার তেজ থেকে সম্মিলিত ভাবেই যে কাত্যায়নী দেবীর এভাবেই উৎপত্তি ঘটেছিল তা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে প্রথম অধ্যায়ে বলা আছে। গীতার একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপও সমস্ত দেবতার সম্মিলিত রূপ। এভাবেই সমস্ত দেবতাকে মিলিয়ে দিয়ে একটা বিশ্বদেব কল্পনার প্রক্রিয়া বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়ে পৌরাণিক যুগ হয়ে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত যে সক্রিয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই।’
‘বিভিন্ন দেবতাকে একের মধ্যে মিশিয়ে দেবার প্রক্রিয়া যে কেবল মাত্র শৈব কাল্টেই ঘটেছিল এমন নয়, বৈষ্ণব ও শাক্ত কাল্টেও একই প্রকার প্রক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি। ভয়ংকর রুদ্রের প্রসন্ন মূর্তির কথা এবং অঘোর সৌম্য তনুর কথা বাজসনেয়ী সংহিতায় আছে (১৬/২)। এখানেই রুদ্রের শিবতর রূপের কথা আছে এবং দক্ষিণ মুখের কথা আছে। রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রকে ‘ক্ষেম্য’ (১৬/৩৩) বা সমস্ত কুশলের মধ্যে বিদ্যমান বলা হয়েছে। রুদ্রাধ্যায়ে উক্ত ১৬/৪০ মন্ত্রের ‘তার’ নামটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উবট এবং মহীধর প্রায় একই প্রকার কথা বলেছেন– সংসার থেকে তরিয়ে দেন বলেই তিনি ‘তার’। এই প্রসঙ্গেই পাঠকের তারক বা তারকেশ্বর নামটি স্মরণে আসতে পারে। রুদ্রের শিবময় তনুর অনেকগুলি রূপের কথাই বাজসনেয়ী সংহিতার নিম্নোক্ত মন্ত্রে পাওয়া যায়– ‘নমঃ শংভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।’ (বাজসনেয়ী-সংহিতা-১৬/৪১)
‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩/৩/৯, শতপথ ব্রাহ্মণ ১/৭/৪/১-৪ প্রভৃতি অংশে কথিত রুদ্রোৎপত্তির কাহিনী এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের স্মৃতিতে আসে। প্রজাপতি পশুরূপে নিজের কন্যাকে ধর্ষণ করলে দেবতারা রেগে গেলেন এবং তাদের সম্মিলিত ক্রোধ থেকেই রুদ্রের আবির্ভাব হল। রুদ্র বাণাঘাতে প্রজাপতিকে বধ করলেন। (পরবর্তী পুরাণগুলিতে এই কাহিনীকে একটু ভিন্ন ভাবে স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে শিবের ক্রোধ থেকে উৎপন্ন হয়ে বীরভদ্র দক্ষ প্রজাপতিকে বধ করেছেন)। সমস্ত দেবতার তেজ থেকে সম্মিলিত ভাবেই যে কাত্যায়নী দেবীর এভাবেই উৎপত্তি ঘটেছিল তা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে প্রথম অধ্যায়ে বলা আছে। গীতার একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপও সমস্ত দেবতার সম্মিলিত রূপ। এভাবেই সমস্ত দেবতাকে মিলিয়ে দিয়ে একটা বিশ্বদেব কল্পনার প্রক্রিয়া বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়ে পৌরাণিক যুগ হয়ে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত যে সক্রিয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই।’
‘বিভিন্ন দেবতাকে একের মধ্যে মিশিয়ে দেবার প্রক্রিয়া যে কেবল মাত্র শৈব কাল্টেই ঘটেছিল এমন নয়, বৈষ্ণব ও শাক্ত কাল্টেও একই প্রকার প্রক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি। ভয়ংকর রুদ্রের প্রসন্ন মূর্তির কথা এবং অঘোর সৌম্য তনুর কথা বাজসনেয়ী সংহিতায় আছে (১৬/২)। এখানেই রুদ্রের শিবতর রূপের কথা আছে এবং দক্ষিণ মুখের কথা আছে। রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রকে ‘ক্ষেম্য’ (১৬/৩৩) বা সমস্ত কুশলের মধ্যে বিদ্যমান বলা হয়েছে। রুদ্রাধ্যায়ে উক্ত ১৬/৪০ মন্ত্রের ‘তার’ নামটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উবট এবং মহীধর প্রায় একই প্রকার কথা বলেছেন– সংসার থেকে তরিয়ে দেন বলেই তিনি ‘তার’। এই প্রসঙ্গেই পাঠকের তারক বা তারকেশ্বর নামটি স্মরণে আসতে পারে। রুদ্রের শিবময় তনুর অনেকগুলি রূপের কথাই বাজসনেয়ী সংহিতার নিম্নোক্ত মন্ত্রে পাওয়া যায়– ‘নমঃ শংভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।’ (বাজসনেয়ী-সংহিতা-১৬/৪১)
ঐতরেয় ব্রাহ্মণে– রুদ্র অত্যন্ত উগ্রস্বভাব এবং দুর্ধর্ষ, তাঁর নাম উচ্চারণ করাও বিপজ্জনক। রুদ্র কথাটা রুদ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন যার অর্থ রোদন। রোদন করেন বা অন্তিমকালে রোদন করান, ভগিনী অম্বিকা তাঁর ধ্বংসকার্যের সহায়িকা। তিনি রীবগণকে ধ্বংস করেন বলে– ক্ষয়দ্বীয়। হাতে বজ্র তাই– বজ্রবাহু। এহেন মহাশক্তিমান দেবতার কোপানল থেকে বাঁচার তাগিদে মানুষ কাতর মিনতি জানাতো– তবে ভক্তিতে নয়, ভয়ে। কিন্তু মানুষের মন বুঝি এতে ভরে না। সে এই অমিত শক্তিধরকে চায়– কল্যাণসুন্দর রূপে পেতে। ফলে রুদ্র ধীরে ধীরে জনমানসে বিবর্তিত হন– মঙ্গলময় শিবে। আর পরিশেষে আশুতোষ রূপ পরিগ্রহ করেন যজুর্বেদে এসে।
রুদ্রাধ্যায়ের এ মন্ত্রে রুদ্রকে– ‘নমঃ উগ্রায় চ ভীমায় চ’, অর্থাৎ উগ্র ও ভীম এই দুই ভীষণত্ববোধক যেমন বলা হয়েছে, তেমনি আবার মঙ্গলবাচক বিশেষণে প্রণতি জানিয়ে বলা হয়েছে–
রুদ্রাধ্যায়ের এ মন্ত্রে রুদ্রকে– ‘নমঃ উগ্রায় চ ভীমায় চ’, অর্থাৎ উগ্র ও ভীম এই দুই ভীষণত্ববোধক যেমন বলা হয়েছে, তেমনি আবার মঙ্গলবাচক বিশেষণে প্রণতি জানিয়ে বলা হয়েছে–
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ।
নমঃ শঙ্করায় চ ময়ষ্করায় চ।
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।।
অর্থাৎ : শম্ভুকে নমস্কার, সুখভবকে নমস্কার। শঙ্করকে নমস্কার, সুখকরকে নমস্কার। শিবকে নমস্কার, শিবতরকে নমস্কার।
এখানে শম্ভব, ময়োভব, শঙ্কর, ময়ষ্কর ও শিব– প্রতিটা শব্দের একই অর্থ– কল্যাণ সুন্দর মঙ্গলময় রূপ। এ শুধু শিবই নয়। ‘শিবতর’ অর্থাৎ অধিকতার মঙ্গলদায়ক ও কল্যাণজনক।
এবং পরবর্তীতে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও ঋষি প্রার্থনা করেছেন যে– রুদ্রের যে মঙ্গলময় দক্ষিণ মুখ আছে তা যেন তাঁকে নিত্য পালন করেন– ‘রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্’ (৪/২১)।
এবং পরবর্তীতে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও ঋষি প্রার্থনা করেছেন যে– রুদ্রের যে মঙ্গলময় দক্ষিণ মুখ আছে তা যেন তাঁকে নিত্য পালন করেন– ‘রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্’ (৪/২১)।
রুদ্র শব্দটির মধ্যে যেমন ধ্বংসাত্মক তনুটির পরিচয় আছে তেমনি শিব শব্দের মধ্যে মঙ্গলময় সত্তার পরিচয় আছে। রুদ্রের বিভিন্ন রঙ ও রূপের কথা বেদ থেকেই আমরা পাই।–
‘বাজসনেয়ী সংহিতায় (১৬/৬,৭) আদিত্য রূপে রুদ্রের স্তুতি আছে। রুদ্রাধ্যায়ের মতে তিনি সহস্রাক্ষ, আদিত্য, শিপিবিষ্ট, সোম ও সূর্য। তিনি রক্তবর্ণ (১৬/৩৯), পীতবর্ণ (১৬/১৭), কপিলবর্ণ (১৬/৬)। এই স্তবেই তাঁকে নীললোহিত ও নীলগ্রীব (১৬/৭,৮) বলা হয়েছে। এই বিশেষণটিই পরবর্তী কালে সমুদ্রমন্থনে বিষ পানের ফলে শিবের নীলকণ্ঠ হবার আখ্যানের ভিত্তিভূমি হিসাবে কাজ করেছে। অনুরূপ ভাবে পশুপতি, ত্রিপুরারি (পৌরাণিক ত্রিপুর দহন বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য), ক্ষেত্রপতি (মঙ্গলকাব্যে চাষী শিবের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি বৈদিক বিশেষণগুলিও পুরাণের গল্পে পল্লবিত হয়ে শৈব পুরাণগুলিতে নতুন মাত্রা এনেছে। এইসব কারণের জন্যই প্রাচীন পুরাণ পরম্পরা বলেছে– ‘ইতিহাস-পুরাণাভ্যাম্ বেদম্ সমুপবৃংহয়েত্’। রুদ্রাধ্যায়ে উক্ত (১৬/১৮) ‘অন্নানাং পতি’ বিশেষণ থেকেই অন্নপূর্ণাপতি শিবের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেছেন।’– (ড. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/ ভূমিকা, লিঙ্গ পুরাণ, পৃষ্ঠা-১৬)
‘বাজসনেয়ী সংহিতায় (১৬/৬,৭) আদিত্য রূপে রুদ্রের স্তুতি আছে। রুদ্রাধ্যায়ের মতে তিনি সহস্রাক্ষ, আদিত্য, শিপিবিষ্ট, সোম ও সূর্য। তিনি রক্তবর্ণ (১৬/৩৯), পীতবর্ণ (১৬/১৭), কপিলবর্ণ (১৬/৬)। এই স্তবেই তাঁকে নীললোহিত ও নীলগ্রীব (১৬/৭,৮) বলা হয়েছে। এই বিশেষণটিই পরবর্তী কালে সমুদ্রমন্থনে বিষ পানের ফলে শিবের নীলকণ্ঠ হবার আখ্যানের ভিত্তিভূমি হিসাবে কাজ করেছে। অনুরূপ ভাবে পশুপতি, ত্রিপুরারি (পৌরাণিক ত্রিপুর দহন বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য), ক্ষেত্রপতি (মঙ্গলকাব্যে চাষী শিবের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি বৈদিক বিশেষণগুলিও পুরাণের গল্পে পল্লবিত হয়ে শৈব পুরাণগুলিতে নতুন মাত্রা এনেছে। এইসব কারণের জন্যই প্রাচীন পুরাণ পরম্পরা বলেছে– ‘ইতিহাস-পুরাণাভ্যাম্ বেদম্ সমুপবৃংহয়েত্’। রুদ্রাধ্যায়ে উক্ত (১৬/১৮) ‘অন্নানাং পতি’ বিশেষণ থেকেই অন্নপূর্ণাপতি শিবের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেছেন।’– (ড. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/ ভূমিকা, লিঙ্গ পুরাণ, পৃষ্ঠা-১৬)
এখানে উল্লেখ্য,– ‘যজুর্বেদের কালে রুদ্র কেবল দ্বিজাতির বা আর্যদেরই দেবতা ছিলেন তা নয়; এই সময় তিনি অনার্য জাতির অন্ত্যজ জাতিরও দেবতা ছিলেন। তাই এই (রুদ্রাধ্যায়) সূক্তে অনেক অনার্য জাতি, অন্ত্যজ ও নীচ বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়ে এই অধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনার্য জাতি, দস্যু, পার্বত্য জাতি ও অন্ত্যজ জাতির উপাস্য ও পালক বলে উল্লেখ থাকায় অধিকাংশ পণ্ডিতজন মনে করেন– রুদ্র প্রথমে অনার্য আদিবাসীদের উপাস্য দেবতা ছিলেন; পরবর্তীকালে আর্যরা তাদের থেকে এই দেবতাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন বলেই ঋগ্বেদ সংহিতায় রুদ্র ছিলেন অন্ত্যজ দেবতা। এরপর আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সংশ্লেষণের ফলে অনার্য প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এই দেবতাকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন– সর্বপূজ্য কল্যাণসুন্দর রূপে। আর এই যজুর্বেদের কালেই তিনি পরমাত্মায় পর্যবসিত হন। কারণ এই সময়ে তিনি শুধুমাত্র সাধু-সজ্জনদেরই আরাধ্য দেবতা ছিলেন তা নয়। তিনি একই সাথে অসাধু, চোর, দস্যু, গাঁটকাটা সিধেল চোর, সশস্ত্র চোর, নিশাচর দস্যু, মানুষ মারা দস্যু, উষ্ণীষধারী দস্যু (পাগড়ি পরা ডাকাত), পার্বত্য দস্যু, ধনুর্বাণধারী দস্যু ও শস্য অপহরণকারী দস্যুদেরও উপাস্য দেবতা ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ছুতোর, কামার, কুমোর, নিষাদ, যাযাবর, বেদে, ব্যাধ ইত্যাদিদেরও দেবতা ও পালক রূপে পূজিত ছিলেন। এমনকী তিনি গো, অশ্ব, কুকুর ইত্যাদি সমস্ত গৃহপালিত পশুদেরও পতি বা পালকরূপে পরিচিত– পশুপতি।’– (অশোক রায়, বিবর্তনের ধারায় শিব ও শিবলিঙ্গ, পৃষ্ঠা-১৩৯)
এভাবেই যজুর্বেদ সংহিতায় রুদ্র সগুণ দেবতার লক্ষণ অতিক্রম করে সর্বপূজ্য নির্গুণ পরমেশ্বরে পর্যবসিত হয়েছেন, যেখানে সমস্ত বিরোধের অবসান, সমস্ত দ্বন্দ্বের ঐক্যসমাবেশ, সমস্ত বৈপরীত্যের সমন্বয়। এই রুদ্রাধ্যায়েই তিনি যাবতীয় দার্শনিক রুপ-লক্ষণ, লাঞ্ছন চিহ্ন ও বিবিধ নামরূপে স্তুত হয়ে পরমেশ্বরে পর্যবসিত হলেন।
‘শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা কাব্য হিসাবেও অপূর্ব। রুদ্রাধ্যায় থেকে বহু দৃষ্টান্তই দেওয়া যায়। এই অধ্যায়ে রুদ্র দেব পশুপতি, শম্ভু, শিব, শংকর, কৃত্তিবাস, গিরিশ, ক্ষিতিকণ্ঠ, নীলগ্রীব, কপর্দী ইত্যাদি নামে স্তুত হয়েছেন। ঋগ্বেদের রুদ্র কেবল বজ্রের দেবতা, কিন্তু যজুর্বেদে তিনি কেবলমাত্র বজ্রই নন সূর্যের সাথেও তাঁর অভিন্নতা দেখানো হয়েছে। তাই সূর্যের উদয় থেকে অস্তকালীন অবস্থার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুযায়ী রুদ্রের এক একটা নাম হয়েছে। উদয় ও অস্তের সময় সূর্যের সহস্র সহস্র রশ্মি বা কিরণ সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়; তাই ঋষি কল্পনায় সূর্যের বিম্বটি মস্তকসদৃশ। আর তার চতুর্দিকে প্রসারিত কিরণমালা– দীর্ঘ জটাজুট সদৃশ। তাই জটার প্রতিশব্দ (কপর্দ) অনুযায়ী রুদ্র হলেন– কপর্দী (রুদ্রাধ্যায় ষষ্ঠ মন্ত্র)। সপ্তম মন্ত্রে তিনি নীলকণ্ঠ। যা অস্তগামী সূর্যের রূপ থেকে এসেছে। ঋষি কবি বলছেন– ‘আদিত্যদেব যখন অস্তাচলে গমন করেন তখন গগনমণ্ডল রঙের মহোৎসবে মাতিয়া ওঠে। স্বর্ণবর্ণ সূর্যবিম্বের চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত গাঢ় সিন্দুরবর্ণে পশ্চিমগগন রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয়, কেবল সূর্যবিম্বের মধ্যস্থলে নীল বর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়।’ এই মধ্যস্থলই কবি কল্পনায় কণ্ঠদেশ, আর সেই কণ্ঠদেশে নীল রং দেখায় বলেই ওই অবস্থায় সূর্যের নাম– নীলকণ্ঠ বা নীলগ্রীব। তাই ঋষি কবি বন্দনাগীত গাইছেন– ‘ওই যে নীলকণ্ঠ রক্তিমবর্ণ সূর্যরূপী রুদ্রদেব গগনপটে ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, তাঁহার অপরূপ রূপে আকৃষ্ট হইয়া গোধূলি লগ্নে মাঠ হইতে গোরুর পাল লইয়া গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তন কালে মুগ্ধ হইয়া গোপালেরা তাঁহাকে দর্শন করে। গ্রামের ললনাবৃন্দ সায়ংকালে সরোবরের জল লইতে আসিয়া মুগ্ধ হইয়া রুদ্রের এই অতুলনীয় রূপ দেখিতে থাকে।’– (অশোক রায়, বিবর্তনের ধারায় শিব ও শিবলিঙ্গ)
যজুর্বেদের দুই শাখা– কৃষ্ণ যজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্ল যজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী সংহিতা। কৃষ্ণ যজুর্বেদের পঠন-পাঠন প্রচলন ও চর্চা সাধারণভাবে দেখা যায় দাক্ষিণাত্যে, আর শুক্ল যজুর্বেদের চর্চা সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়েই (উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে)। বাংলাদেশের অধিকাংশ যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণই শুক্ল যজুর্বেদীয় গোষ্ঠীর।
‘শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা কাব্য হিসাবেও অপূর্ব। রুদ্রাধ্যায় থেকে বহু দৃষ্টান্তই দেওয়া যায়। এই অধ্যায়ে রুদ্র দেব পশুপতি, শম্ভু, শিব, শংকর, কৃত্তিবাস, গিরিশ, ক্ষিতিকণ্ঠ, নীলগ্রীব, কপর্দী ইত্যাদি নামে স্তুত হয়েছেন। ঋগ্বেদের রুদ্র কেবল বজ্রের দেবতা, কিন্তু যজুর্বেদে তিনি কেবলমাত্র বজ্রই নন সূর্যের সাথেও তাঁর অভিন্নতা দেখানো হয়েছে। তাই সূর্যের উদয় থেকে অস্তকালীন অবস্থার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুযায়ী রুদ্রের এক একটা নাম হয়েছে। উদয় ও অস্তের সময় সূর্যের সহস্র সহস্র রশ্মি বা কিরণ সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়; তাই ঋষি কল্পনায় সূর্যের বিম্বটি মস্তকসদৃশ। আর তার চতুর্দিকে প্রসারিত কিরণমালা– দীর্ঘ জটাজুট সদৃশ। তাই জটার প্রতিশব্দ (কপর্দ) অনুযায়ী রুদ্র হলেন– কপর্দী (রুদ্রাধ্যায় ষষ্ঠ মন্ত্র)। সপ্তম মন্ত্রে তিনি নীলকণ্ঠ। যা অস্তগামী সূর্যের রূপ থেকে এসেছে। ঋষি কবি বলছেন– ‘আদিত্যদেব যখন অস্তাচলে গমন করেন তখন গগনমণ্ডল রঙের মহোৎসবে মাতিয়া ওঠে। স্বর্ণবর্ণ সূর্যবিম্বের চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত গাঢ় সিন্দুরবর্ণে পশ্চিমগগন রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয়, কেবল সূর্যবিম্বের মধ্যস্থলে নীল বর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়।’ এই মধ্যস্থলই কবি কল্পনায় কণ্ঠদেশ, আর সেই কণ্ঠদেশে নীল রং দেখায় বলেই ওই অবস্থায় সূর্যের নাম– নীলকণ্ঠ বা নীলগ্রীব। তাই ঋষি কবি বন্দনাগীত গাইছেন– ‘ওই যে নীলকণ্ঠ রক্তিমবর্ণ সূর্যরূপী রুদ্রদেব গগনপটে ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, তাঁহার অপরূপ রূপে আকৃষ্ট হইয়া গোধূলি লগ্নে মাঠ হইতে গোরুর পাল লইয়া গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তন কালে মুগ্ধ হইয়া গোপালেরা তাঁহাকে দর্শন করে। গ্রামের ললনাবৃন্দ সায়ংকালে সরোবরের জল লইতে আসিয়া মুগ্ধ হইয়া রুদ্রের এই অতুলনীয় রূপ দেখিতে থাকে।’– (অশোক রায়, বিবর্তনের ধারায় শিব ও শিবলিঙ্গ)
যজুর্বেদের দুই শাখা– কৃষ্ণ যজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্ল যজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী সংহিতা। কৃষ্ণ যজুর্বেদের পঠন-পাঠন প্রচলন ও চর্চা সাধারণভাবে দেখা যায় দাক্ষিণাত্যে, আর শুক্ল যজুর্বেদের চর্চা সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়েই (উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে)। বাংলাদেশের অধিকাংশ যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণই শুক্ল যজুর্বেদীয় গোষ্ঠীর।
অথর্ববেদের যুগ বা তার আগে থেকেই রুদ্র শিবের সঙ্গে মহাকাল সংক্রান্ত একটা ধারা মিশতে থাকে বলে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা মনে করেন। রুদ্রকে সৃষ্টি ও সংহারের দেবতা বলা হয়েছে। অথর্ববেদের কালসূক্তে (উনবিংশ কাণ্ডের ষষ্ঠ অনুবাকের অষ্টম ও নবম সূক্ত) আমরা কালের স্রষ্টা রূপের পরিচয় পাই। কালেই সব কিছু উৎপন্ন হয়, আবার কালেই সব বিলীন হয়। যেমন–
স এব সং ভুবনান্যাভরৎ স এব সং ভুবনানি পর্যৈৎ। পিতা সন্নভবৎ পুত্র এষাং তস্মাৎ বৈ নান্যৎ পরমস্তি তেজঃ।। ৪।। কালোহমূং দিবমজনয়ৎ কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত। কালে হ ভূতং ভব্যং চেষিতং হ বি তিষ্ঠতে।। ৫।। কালো ভূতিমসৃজত কালে তপতি সূর্যঃ। কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বি পশ্যতি।। ৬।। কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্ । কালেন সর্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ।। ৭।। তেনেষিতং তেন জাতং তদু তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ । কালো হ ব্রহ্ম ভূত্বা বিভর্তি পরমেষ্ঠিনম্ ।। ৯।। কালঃ প্রজা অসৃজত কালো অগ্রে প্রজাপতিম্ । স্বয়ম্ভুঃ কশ্যপঃ কালাৎ তপঃ কালাদজায়ত।। ১০।। (অথর্ববেদ-১৯/৬/৮/৪,৫,৬,৭,৯,১০)
অর্থাৎ :
সে কালই এ চরাচর সর্ববস্তু উৎপন্ন করেছে (অথবা নিজের উৎপাদিত সকল প্রাণীকে তিনিই সর্বতোভাবে পোষণ করেন)। সে কালই সমস্ত ভুবন ব্যাপ্ত করেছে। সে কালই এ ভুবনের জনক হয়ে পুত্ররূপে অবস্থান করছে। সে সকলের উৎপাদক সর্বগত কাল ছাড়া অন্য উৎকৃষ্ট তেজ আর নেই। ৪।। কালরূপ পরমাত্মা ঐ দ্যুলোক সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এ পরিদৃশ্যমান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কালই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালাবচ্ছিন্ন জগৎ আশ্রয় করে আছে। ৫।। কালরূপ পরমাত্মা এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কালের প্রেরণায় সূর্য তাপ দেয় অর্থাৎ জগৎ প্রকাশ করে। কালের আশ্রয়ে সকল বিশ্ব অবস্থান করছে। কালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দর্শন করে (অথবা কালেই চক্ষুষ্মান সর্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার করে থাকে)। ৬।। সে কালরূপ পরমাত্মায় জগৎ সৃষ্টির কারণ-রূপ মন অবস্থান করছে। তাতেই সকল জগতের অন্তর্যামী সূত্রাত্মা প্রাণ অবস্থান করছে। অথবা সকল প্রাণীর মন, প্রাণ, নাম সেই কাল-স্বরূপে অবস্থান করছে। বসন্তাদি রূপে আগত সে কালের দ্বারা সকল প্রজাগণ (সৃষ্টি পদার্থ) নিজ নিজ কার্যসিদ্ধির জন্য তুষ্ট হচ্ছে। ৭।। সে কালরূপ পরমাত্মা সমস্ত স্রষ্টব্য জগতের কামনা করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট এ জগৎ সে কালেই প্রতিষ্ঠিত। সে কালই দেশকালাবচ্ছিন্ন সচ্চিৎ সুখাত্মক পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মরূপে পরমেষ্ঠীকে (পরম স্থান সত্যলোকে স্থিত চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে) পালন করেন। ৯।। কালরূপ পরমাত্মাই সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করেছিলেন। সে কালই প্রজা সৃষ্টি করেন। স্বয়ম্ভূ কশ্যপ সকলের দ্রষ্টা অষ্টম সূর্য এবং তার সন্তাপক তেজ সে কাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ১০।।
এবং–
কালাদাপঃ সমভবন্ কালাৎ ব্রহ্ম তপো দিশঃ। কালেনোদেতি সূর্যঃ কালে নি বিশতে পুনঃ।। ১।। কালেন বাতঃ পবতে কালেন পৃথিবী মহী। দৌর্মহী কাল আহিতা।। ২।। কালো হ ভূতং ভব্যং চ পুত্রো অজনয়ৎ পুরা। কালাদৃচঃ সমভবন্ যজুঃ কালদজায়ত।। ৩।। কালো যজ্ঞং সমৈরয়দ্দেবেভ্যো ভাগমক্ষিতম্ । কালে গন্ধর্বাপ্সরসঃ কালে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।। ৪।। কালেহয়মঙ্গিরা দেবোহথর্বা চাধি তিষ্ঠতঃ। ইমং চ লোকং পরমং চ লোকং পুণ্যাংশ্চ লোকান্ বিধৃতীশ্চ পুণ্যাঃ। সর্বাংল্লোকানভিজিত্য ব্রহ্মণা কালঃ স ঈয়তে পরমো নু দেবঃ।। ৫।। –(অথর্ববেদ-১৯/৬/৯/১-৫)
অর্থাৎ :
সর্বজগৎকারণ পরমাত্মা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপ জল উৎপন্ন হয়েছিল। সেরূপ সে কাল থেকে যজ্ঞাদি কর্ম, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা ও পূর্বাদি দিকসকল উৎপন্ন হয়েছিল। প্রেরক কালের দ্বারা সূর্য উদয় লাভ করে এবং আবার কালে বিলীন হয় অর্থাৎ অস্তাগমন করে। ১।। কালরূপ পরমাত্মার প্রেরণায় বায়ু প্রবাহিত হয়, তার দ্বারাই মহতী পৃথিবী দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়েছে এবং মহান দ্যুলোক কালরূপ আধারে নিহত আছে। কালরূপ পরমাত্মা থেকে ঋক্, যজুঃ ও সামমন্ত্রগুলি উৎপন্ন হয়েছে। ২-৩।। কালই ইন্দ্রাদি দেবগণের জন্য অক্ষয় ভাগরূপে যজ্ঞ (প্রকৃতি-বিকৃতিরূপ সোমযাগ) উৎপন্ন করিয়েছিলেন। বাক্যের ধারক (গায়ক) গন্ধর্বগণ ও অন্তরিক্ষচারিণী অপ্সরাগণ কালাধারে অবস্থান করছে। সমস্ত লোকই (সর্বজগৎ ও তদধিবাসী প্রাণিগণ) কালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৪।। অথর্ববেদ-স্রষ্টা দীপ্যমান পরমাত্মার অঙ্গোদ্ভূত অঙ্গিরা দেব এবং অথর্বা দেব স্বজনক কালেই অবস্থান করছে। ভূলোক, স্বর্গলোক, পুণ্যলোক ও দুঃখরহিত অন্য সকল লোক, স্বকারণ, দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সত্যজ্ঞানানন্তাদিরূপ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত করে, (এ সূক্তদ্বয় প্রতিপাদ্য) পরম কাল-দেব সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ ব্যেপে অবস্থান করছেন। ৫।।
এ-প্রেক্ষিতে ড. উদয়চন্দ্র বলেন,– ‘বেদের এই মহাকাল তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই মহাভারতকার শিব সম্পর্কে বললেন– ‘সকালঃ সোহন্তকঃ মৃত্যুঃ স যমঃ’ (৭/২০১/২০৪)। মহানির্বাণ তন্ত্রেও আদ্যাকালীকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাকাল শব্দের এই প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে–
‘কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ তমাদ্যা কালিকা পরা।।’
বেদ ও মহাভারতের সঙ্গে তন্ত্র বা শৈবাগমের মহাকালের হয়তো রূপগত পার্থক্য আছে, হয়তো আর্যেতর কোনো জনের দেবভাবনা থেকে শৈবাগমের কালচিন্তা আসতে পারে, তবে তার ওপর বৈদিক চিন্তার অভিষেক ঘটেনি এমত মনে হয় না।’
‘কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ তমাদ্যা কালিকা পরা।।’
বেদ ও মহাভারতের সঙ্গে তন্ত্র বা শৈবাগমের মহাকালের হয়তো রূপগত পার্থক্য আছে, হয়তো আর্যেতর কোনো জনের দেবভাবনা থেকে শৈবাগমের কালচিন্তা আসতে পারে, তবে তার ওপর বৈদিক চিন্তার অভিষেক ঘটেনি এমত মনে হয় না।’
বেদ-সংহিতার যুগ অর্থাৎ ঋগ্বেদ-যজুর্বেদ-অথর্ববেদ হয়ে রুদ্রের এই ক্রমবিবর্তিত ধারায় ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদের যুগে এসে রুদ্রের অন্যতম নাম মহাদেব হিসেবে বৈদিক দেবগণের মধ্যে হয়তো তাঁর প্রধানতম স্থান সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করে। যেমন, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে তাঁকে মহেশ্বর নামে অভিহিত করে বলা হয়েছে– তিনি প্রকৃতি রূপ মায়ার অধীশ্বর এবং এই বিশ্বভুবন তাঁরই বিভিন্ন রূপ বা অবয়বের দ্বারা পরিব্যাপ্ত–
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং চ মহেশ্বরম্ ।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ।। (শ্বেতাশ্বতর-৪/১০)
অর্থাৎ : প্রকৃতিকে মায়া বলে এবং মহেশ্বরকে মায়াধীশ বলে জানবে। এই বিশ্বচরাচর মহেশ্বরের দেহ।
বস্তুত, ইতোমধ্যে আমরা যা লক্ষ্য করেছি, রুদ্র ভাবনা ক্রমে একটা বিশাল ব্রহ্ম ভাবনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। অথর্বের ব্রাত্য ধারার মধ্যে দিয়ে উপনিষদে এসে এই ভাবনা পরিপূর্ণভাবে ব্রহ্মবাদে বিলীন হয়। শৈব বেদপন্থী টীকাকারেরা এই ধারার দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে– আরেকটি ধারা– বেদবিরোধী শৈব ধারার চলার পথ আবার ভিন্ন।
বস্তুত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেবতা রুদ্র ক্রমশ সর্বপ্রধান দেবতা, এবং একেশ্বর হিসেবে কীর্তিত হতে দেখা যায়। আমরা দেখতে পাই, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে রুদ্রশিব ও ব্রহ্ম এক পর্যায়ে চলে গেছেন। ঋষি বলছেন–
বস্তুত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেবতা রুদ্র ক্রমশ সর্বপ্রধান দেবতা, এবং একেশ্বর হিসেবে কীর্তিত হতে দেখা যায়। আমরা দেখতে পাই, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে রুদ্রশিব ও ব্রহ্ম এক পর্যায়ে চলে গেছেন। ঋষি বলছেন–
অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ।। (শ্বেতশ্বতর-৪/২১)
অর্থাৎ : হে রুদ্র, তুমি মৃত্যুঞ্জয়। যে জন্মাদি মৃত্যুভয়ে ভীত সেই তোমার শরণ নেয়। তোমার প্রসন্ন মুখ আমার দিকে ফেরাও এবং নিয়ত আমাকে রক্ষা কর।
উপনিষদকারের মতে একমাত্র ঈশ্বর ভগবান রুদ্র ব্যতীত আর কেউ নন। যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার ১৬/২,৩ ইত্যাদি মন্ত্রকে এখানে শ্বেতাশ্বতরে ৩/৫,৬ মন্ত্ররূপে ব্রহ্মপরত্বে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বেদান্ত মতে ব্রহ্মই যেমন এক এবং সত্য, তেমনি শ্বেতাশ্বতরের মতে রুদ্রই হলেন একতম। এক ও অদ্বিতীয় রুদ্র স্ব-শক্তির সাহায্যে বিশ্ব চরাচর নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা,– প্রলয়কালে তাঁর মধ্যেই সমস্ত ভুবন আশ্রয় গ্রহণ করে। যেমন–
একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থূঃ য ইমান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যক্ জনান্ তিষ্ঠতে সঞ্চুকোপান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বাঃ ভুবনানি গোপাঃ।। (শ্বেতাশ্বতর-৩/২)
অর্থাৎ : এক সেই পরমেশ্বর কে, যাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই ? তিনি হলেন রুদ্র। প্রতি জীব-হৃদয়ে তাঁর অবস্থান– তাই পরমাত্মা। তিনিই তাঁর সেই ঐশ্বরিক শক্তি-বুদ্ধি দিয়ে জগৎকে শাসন করছেন। সেই শক্তির কোন ব্যাখ্যা চলে না। ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করে প্রতিটি মানুষের অন্তরে তিনি অবস্থান করছেন, আবার গোপা অর্থাৎ রক্ষাও করছেন। আবার অন্তিমকালে এলে সংহার-মূর্তিতে তিনিই সব সংহার করছেন।
এখানে উল্লেখ্য, যোগী সম্প্রদায়ের শ্বেতাশ্বতর ঋষির দ্বারা রচিত এই উপনিষদটি উপনিষদ্ ভাগের শেষ পর্বের রচনা। পুরাণবর্ণিত কল্প ও কল্পযুগের কথা যেমন এখানে আছে, তেমনি যোগাচারের ও যোগসিদ্ধির প্রথমাবস্থার কথাও এখানে বলা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ব্রহ্মের রূপ হিসেবে রুদ্রকে এখানে দেখানো হলেও ‘শিব’ শব্দটি তখনো (শ্বেতাশ্বতর রচনাকালে) রুদ্রের নামে পর্যবসিত হয়নি, তা বরাবরই বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্বেতাশ্বতরে রুদ্রকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে, যেমন মহাদেব, মহর্ষি, ভগবান, ঈশ, ঈশান এবং শিব। তবে শেষোক্ত নামটি (শিব) রুদ্রের উপাধি বা বিশেষণ হিসেবেই মাত্র কয়েকটি স্থলে উল্লিখিত হয়েছে বলে মনে হয়। যেমন–
সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ।। (শ্বেতাশ্বতর-৩/১১)
অর্থাৎ : তিনি সর্বানন– জগতের সব মুখই তাঁর মুখ। জগতের প্রাণীমাত্রেরই মাথা, গলা– তাঁরই শির-গ্রীবা। প্রাণীর ভেতরে সেই গুহা, যার নাম বুদ্ধি, তিনি আছেন সেই গুহায়। সর্বব্যাপী এবং সর্বগত শিবস্বরূপ মঙ্গলময় তিনি ভগবান।
.
ঘৃতাৎ পরং মন্ডমিবাতিসূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্ ।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।। (শ্বেতাশ্বতর-৪/১৬)
অর্থাৎ : ঘিয়ের উপর হালকা সরের মতো একটা সারবস্তু ভেসে থাকে। ঈশ্বর সেই অতি সূক্ষ্ম সারবস্তুর মতো, যিনি বিশ্বের একমাত্র কর্তা, যিনি প্রতিটি জীবকে তার কর্ম অনুসারে প্রাপ্য ফল দান করেন। অন্তরাত্মা হয়ে এই পরমেশ্বর সকলের মধ্যেই লুকিয়ে আছেন। তিনিই করুণাঘন পরমেশ্বর শিব। সেই পরমেশ্বরকে জানতে পারলে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।
.
ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্ ।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ।। (শ্বেতাশ্বতর-৫/১৪)
অর্থাৎ : ভাব-গ্রাহ্য তিনি, খ্যাত তিনি অশরীরী বলে; সৃষ্টি-লয়ের কারণ যিনি পঞ্চপ্রাণ দশ-ইন্দ্রিয় এবং মন নিয়ে ষোড়শ কলার স্রষ্টা, সেই মঙ্গলময় (শিব) দেবকে যাঁরা জানেন, তাদের আর দেহাভিমান থাকে না– দেহত্যাগের পর আর দেহও ধারণ করতে হয় না।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্র এমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে যাতে তিনি যে উপনিষদকারের ভক্তি ও পূজার পাত্র ছিলেন তা অনুমান করা যায়। এতে ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক একেশ্বরবাদ এবং প্রাচীনতর গদ্য উপনিষদগুলির নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মবাদ একত্র মিলিত হলেও, ঈশ্বরবাদেরই প্রাধান্য সূচিত হয়েছে। ড. উদয়চন্দ্রের বক্তব্য অনুযায়ী, পাতঞ্জল যোগের সঙ্গে কয়েকটি ক্ষেত্রে মিল থাকায় আধুনিক পণ্ডিতেরা শৈব মতাবলম্বী এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদকে যোগোপনিষদ্গুলির আদি গ্রন্থ বলে অনুমান করেন। তিনি আরও বলেন, রুদ্রকে নিয়ে ব্রহ্মভাবনা শ্বেতাশ্বতরেতে ব্যাপক রূপ নিলেও তৈত্তিরীয় আরণ্যক থেকেই এর একটা সূত্র পাওয়া যায় (তৈ. আ. ১০/১৬)। সেখানে রুদ্রকে সর্বভূতাত্মা, বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ বলা হয়েছে। বায়বীয় সংহিতার (৪/৭০-১৪১) বিভিন্ন অংশের সঙ্গে শ্বেতাশ্বতরের প্রচণ্ড মিল। শ্বেতাশ্বতরকে সামান্য উল্টেপাল্টে এগুলি লেখা।
অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথের ভাষ্যে, এভাবেই ক্রমশ শিব নামের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আর্যেতর জাতির দ্বারা পূজিত অনুরূপ দেবতার যখন বৈদিক রুদ্রের সাথে মিলন ঘটে তখন মিশ্র দেবতা শিব নামেই পরিচিত হন।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্র শিবকে কেন্দ্র করে যে একেশ্বরবাদী প্রবণতা দেখা যায়, তার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে অনেক পরবর্তীকালে রচিত অথর্বাশিরস্ উপনিষদে।–
‘ইহাতেই সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ রুদ্র-শিব উপাসনার অন্যতম প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে রুদ্র বিভিন্ন বৈদিক দেবতা, যথা ব্রহ্মা প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, বরুণ প্রভৃতির সহিত একাত্মীভূত হইয়াছেন ত বটেই, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পৌরাণিক দেবতা, যথা স্কন্দ, বিনায়ক, উমা (কেনোপনিষদে উমার নাম প্রথম পাওয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মহাকাব্য ও পুরাণের যুগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন) প্রভৃতিও তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে সপ্ত লোক, পঞ্চ মহাভূত, অষ্ট গ্রহ (তথাকথিত গ্রহের সংখ্যা আদিতে আট, পরে কেতু এই সংখ্যায় যুক্ত হইলে নব গ্রহ পূরণ হয়), কাল, অমৃত প্রভৃতি সবই ইঁহার বিভিন্ন রূপ। তিনি বিশ্বস্রষ্টা ও জগৎপিতা এবং সংহারকর্তা। তাঁহার এই রূপ কল্পনায় সুস্পষ্টভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ দেখা না যাইলেও রুদ্রোপাসকদিগের এক বিশেষ ব্রতের কথা এখানে বলা হইয়াছে। ইহার নাম পাশুপত ব্রত, এবং এই ব্রতের অনুষ্ঠানে ‘অগ্নিরিতি ভস্য বায়ুরিতিভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম ব্যোম ইতি ভস্ম সর্বংহ বৈ ইদং ভস্ম মনঃ এতানি চক্ষুংষি ভস্মানি’ মন্ত্র পাঠ করিয়া উপাসক তাঁহার সর্বাঙ্গে ভস্ম স্পর্শ করাইতেন। এই ব্রত পালনের ফলে উপাসক পশুপাশ হইতে মুক্ত হইতেন (পশুপাশবিমোক্ষণ) এবং ঐশী শক্তির অধিকারী হইতেন।’– (জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ পঞ্চোপাসনা, পৃষ্ঠা-১২৯)
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্র শিবকে কেন্দ্র করে যে একেশ্বরবাদী প্রবণতা দেখা যায়, তার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে অনেক পরবর্তীকালে রচিত অথর্বাশিরস্ উপনিষদে।–
‘ইহাতেই সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ রুদ্র-শিব উপাসনার অন্যতম প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে রুদ্র বিভিন্ন বৈদিক দেবতা, যথা ব্রহ্মা প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, বরুণ প্রভৃতির সহিত একাত্মীভূত হইয়াছেন ত বটেই, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পৌরাণিক দেবতা, যথা স্কন্দ, বিনায়ক, উমা (কেনোপনিষদে উমার নাম প্রথম পাওয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মহাকাব্য ও পুরাণের যুগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন) প্রভৃতিও তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে সপ্ত লোক, পঞ্চ মহাভূত, অষ্ট গ্রহ (তথাকথিত গ্রহের সংখ্যা আদিতে আট, পরে কেতু এই সংখ্যায় যুক্ত হইলে নব গ্রহ পূরণ হয়), কাল, অমৃত প্রভৃতি সবই ইঁহার বিভিন্ন রূপ। তিনি বিশ্বস্রষ্টা ও জগৎপিতা এবং সংহারকর্তা। তাঁহার এই রূপ কল্পনায় সুস্পষ্টভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ দেখা না যাইলেও রুদ্রোপাসকদিগের এক বিশেষ ব্রতের কথা এখানে বলা হইয়াছে। ইহার নাম পাশুপত ব্রত, এবং এই ব্রতের অনুষ্ঠানে ‘অগ্নিরিতি ভস্য বায়ুরিতিভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম ব্যোম ইতি ভস্ম সর্বংহ বৈ ইদং ভস্ম মনঃ এতানি চক্ষুংষি ভস্মানি’ মন্ত্র পাঠ করিয়া উপাসক তাঁহার সর্বাঙ্গে ভস্ম স্পর্শ করাইতেন। এই ব্রত পালনের ফলে উপাসক পশুপাশ হইতে মুক্ত হইতেন (পশুপাশবিমোক্ষণ) এবং ঐশী শক্তির অধিকারী হইতেন।’– (জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ পঞ্চোপাসনা, পৃষ্ঠা-১২৯)
বলা বাহুল্য, শৈব ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির প্রধান দেবতা শিবের আদিম রূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে বুঝা যায় যে তা মূলত এক কাল্পনিক দেবসত্তাকে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু কিভাবে লিঙ্গ ও যোনি প্রতীক পূজা শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলো তার ইঙ্গিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাওয়া যায় বলে কেউ কেউ (রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকর মহাশয়) মনে করেন। যেমন শ্বেতাশ্বতরে বলা হয়েছে–
যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বম্ ।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি।। (শ্বেতাশ্বতর-৪/১১)
অর্থাৎ : প্রকৃতি, আকাশ ইত্যাদি সবকিছু যে কারণ (যোনি) থেকে উৎপন্ন হয়েছে, আবার প্রলয়ের সময় যে কারণে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সেই কারণেরও কারণ হলেন মায়ার অতীত পরমানন্দময় এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। সেই নিয়ন্তা, বরদা, পূজ্য দেবতাকে নিশ্চিতভাবে যে সাধক উপলব্ধি করেছেন, মনের চোখ দিয়ে হৃদয়-আকাশে দেখেছেন তিনি চিরশান্তি লাভ করেছেন।
.
যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠ্যত্যেকো বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ।। (শ্বেতাশ্বতর-৫/২)
অর্থাৎ : যিনি এক হয়েও বিশ্বের যোনিতে-যোনিতে অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুতে, সমস্ত রূপে, সমস্ত উপাদানে বা উৎপত্তির কারণে কারণ হয়ে আছে, যিনি সৃষ্টির বা কল্পের শুরুতে সর্বজ্ঞ ঋষি কপিলকে উৎপন্ন করে ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য দিয়ে পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং তাঁর জন্ম-মুহূর্তটিকেও দেখেছিলেন, তিনি জীব বা জীবাত্মা নন– পরমাত্মা, পরমেশ্বর।
এখানে কৌতুহলের বিষয় হলো, উপনিষদ ঋষি বলছেন, সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি জ্ঞানগর্ভ কপিলকে উৎপন্ন করলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও ভগবান বলেছেন, ঋষিদের মধ্যে কপিল এবং দর্শনের মধ্যে আমি সাংখ্য। তাহলে কি বুঝতে হবে যে, জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের প্রথম সৃষ্টি সাংখ্যদর্শনের দ্রষ্টা ভগবান কপিল মুনি? আবার এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই অন্যত্র বলা হয়েছে– তাঁর প্রথম সৃষ্টি হিরণ্যগর্ভ। তাহলে কি কপিল বলতে হিরণ্যগর্ভকেই বোঝানো হয়েছে? পণ্ডিতদের মতে এখানে কপিল মুনি নন, স্বয়ং কনকবর্ণ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকেই বোঝানো হয়েছে। সে যাক, তবে অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে–
‘এই দুটি শ্লোকেরই প্রথম চরণে ঈশান (শিব) দেবতাকে প্রতি যোনিতে অধিষ্ঠিত থাকিবার বর্ণনা দেখিয়া ভান্ডারকরের মনে এইরূপ সংশয় জাগিয়াছিল। কিন্তু এখানে যোনি যে স্ত্রীচিহ্ন অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া মূল কারণ বীজ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্বমূলক প্রমাণও আমাদের এই উক্তি সমর্থন করে। লিঙ্গপ্রতীকের আদিমতম ও কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের যে সব নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এগুলির কোনওটিতেই লিঙ্গ ও যোনি একত্র করিয়া দেখানো হয় নাই। এই দুইটি পূজা প্রতীকের একত্র সমাবেশ আমরা গুপ্ত ও তৎপরবর্তী যুগের নিদর্শনগুলিতেই পাই,– তখন ইহার শিশ্নাকৃতি অনেকাংশে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং ইহা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছিল। গুপ্তপূর্ব কালের এবং খৃষ্টপূর্ব যুগের যে সব শিবলিঙ্গ বা তাহার চিত্র মুদ্রায় বা শিলমোহরে দেখা যায়, সেগুলিতে পরবর্তী কালের যোনিপট্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং ইহাদিগকে ঊর্ধ্বোত্থিত মুক্তমুখচর্ম পুংলিঙ্গের আকারে রূপায়িত দেখা যায়। গোপীনাথ রাও মহাশয় খৃষ্টপূর্ব যুগের এইরূপ একটি পরশু ও মৃগধারী দ্বিভুজ শিবের আকৃতি সংযুক্ত সুদীর্ঘ শিবলিঙ্গ অন্ধ্র প্রদেশের গুডিমল্লম গ্রামে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা অদ্যাবধি পূজা পাইয়া আসিতেছে। ইহাতে কোনও যোনিপীঠ বা যোনিপট্ট নাই।’– (পঞ্চোপাসনা, পৃষ্ঠা-১৩৬)
‘এই দুটি শ্লোকেরই প্রথম চরণে ঈশান (শিব) দেবতাকে প্রতি যোনিতে অধিষ্ঠিত থাকিবার বর্ণনা দেখিয়া ভান্ডারকরের মনে এইরূপ সংশয় জাগিয়াছিল। কিন্তু এখানে যোনি যে স্ত্রীচিহ্ন অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া মূল কারণ বীজ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্বমূলক প্রমাণও আমাদের এই উক্তি সমর্থন করে। লিঙ্গপ্রতীকের আদিমতম ও কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের যে সব নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এগুলির কোনওটিতেই লিঙ্গ ও যোনি একত্র করিয়া দেখানো হয় নাই। এই দুইটি পূজা প্রতীকের একত্র সমাবেশ আমরা গুপ্ত ও তৎপরবর্তী যুগের নিদর্শনগুলিতেই পাই,– তখন ইহার শিশ্নাকৃতি অনেকাংশে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং ইহা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছিল। গুপ্তপূর্ব কালের এবং খৃষ্টপূর্ব যুগের যে সব শিবলিঙ্গ বা তাহার চিত্র মুদ্রায় বা শিলমোহরে দেখা যায়, সেগুলিতে পরবর্তী কালের যোনিপট্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং ইহাদিগকে ঊর্ধ্বোত্থিত মুক্তমুখচর্ম পুংলিঙ্গের আকারে রূপায়িত দেখা যায়। গোপীনাথ রাও মহাশয় খৃষ্টপূর্ব যুগের এইরূপ একটি পরশু ও মৃগধারী দ্বিভুজ শিবের আকৃতি সংযুক্ত সুদীর্ঘ শিবলিঙ্গ অন্ধ্র প্রদেশের গুডিমল্লম গ্রামে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা অদ্যাবধি পূজা পাইয়া আসিতেছে। ইহাতে কোনও যোনিপীঠ বা যোনিপট্ট নাই।’– (পঞ্চোপাসনা, পৃষ্ঠা-১৩৬)
বিদ্বানেরা বলেন, সাধনার দার্শনিক উপলব্ধিতে লিঙ্গ মানে সূক্ষ্ম শরীরের প্রতীকী রূপ। কেননা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেরই নিম্নোক্ত শ্লোকে সূক্ষ্ম শরীরকে লিঙ্গ শরীর বলা হয়েছে–
বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্তির্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্যস্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে।। (শ্বেতাশ্বতর-১/১৩)
অর্থাৎ : আগুনের উৎস কাঠ। অর্থাৎ কাঠের ভিতরেই আগুন আছে। কিন্তু সেই আগুন তখনি দেখা যায় যখন একটি কাঠকে আরেকটি কাঠের সঙ্গে ঘষা হয়। না ঘষলে কি সেই শক্তি কাঠের মধ্যে থাকে না? অবশ্যই থাকে। সেইরকম প্রণবের মধ্যেই আত্মা আছেন। তাই প্রণবের দ্বারা আত্মাকে মনন করলেই তার উপলব্ধি হয়।
তার মানে, পরমেশ্বর মহেশ্বর সর্বব্যাপ্ত হয়েও সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে অবস্থান করেন বলে তাঁকে দেখা যায় না, উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁকে অনুভব করতে হয়। অর্থাৎ লিঙ্গশরীর মানে সূক্ষ্ম শরীর, যা বাস্তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। কিন্তু এই উপলব্ধির জন্য যে উচ্চমার্গের ধ্যান ও গভীর সাধনার প্রয়োজন হয় তার জন্যেও প্রাথমিকভাবে দরকার হয় কোনো বাহ্যিক প্রতীকী মাধ্যম। এই মাধ্যমই কি লিঙ্গপ্রতীক? এ প্রেক্ষিতে ড. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন–
‘শিবের সূক্ষ্মমূর্তি হলেও তার বাহ্য প্রতীক হিসাবে শিবলিঙ্গকে পূজা করা হত। এক্ষেত্রে লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন। শিবপূজকরা তাঁদের দেহে বিশেষ প্রকার তিলকাদি ব্যবহার করতেন। একেও লিঙ্গ বলা হত। পৌরাণিক যুগে ত্রিপুণ্ডক, ত্রিশূল বা লিঙ্গায়েৎ-দের শিবলিঙ্গ ধারণের মতই তখনও শৈবরা বিশেষ চিহ্ন বা লিঙ্গ ধারণ করতেন। পাশুপতসূত্রের– ‘লিঙ্গধারী’ (১/৬) অংশের ব্যাখ্যা কালে কৌণ্ডিন্য বলেন– বর্ণাশ্রমীদের যেমন স্ব স্ব আশ্রমের চিহ্ন থাকে, অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর যেমন দণ্ড, কমণ্ডুল, যজ্ঞোপবীত ইত্যাদি থাকে, তেমনি পশুপতেরাও ভষ্মালেপন, নির্মাল্যধারণ ইত্যাদি লিঙ্গ ব্যবহার করবেন। শিবের চিহ্ন বা লিঙ্গ হিসাবেই তাই শিবলিঙ্গ ধারণ করা হত, কারণ শিবের প্রতীক লিঙ্গ এবং শিব প্রকৃতপক্ষে একই।’– (ভূমিকা, লিঙ্গ পুরাণ)
‘শিবের সূক্ষ্মমূর্তি হলেও তার বাহ্য প্রতীক হিসাবে শিবলিঙ্গকে পূজা করা হত। এক্ষেত্রে লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন। শিবপূজকরা তাঁদের দেহে বিশেষ প্রকার তিলকাদি ব্যবহার করতেন। একেও লিঙ্গ বলা হত। পৌরাণিক যুগে ত্রিপুণ্ডক, ত্রিশূল বা লিঙ্গায়েৎ-দের শিবলিঙ্গ ধারণের মতই তখনও শৈবরা বিশেষ চিহ্ন বা লিঙ্গ ধারণ করতেন। পাশুপতসূত্রের– ‘লিঙ্গধারী’ (১/৬) অংশের ব্যাখ্যা কালে কৌণ্ডিন্য বলেন– বর্ণাশ্রমীদের যেমন স্ব স্ব আশ্রমের চিহ্ন থাকে, অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর যেমন দণ্ড, কমণ্ডুল, যজ্ঞোপবীত ইত্যাদি থাকে, তেমনি পশুপতেরাও ভষ্মালেপন, নির্মাল্যধারণ ইত্যাদি লিঙ্গ ব্যবহার করবেন। শিবের চিহ্ন বা লিঙ্গ হিসাবেই তাই শিবলিঙ্গ ধারণ করা হত, কারণ শিবের প্রতীক লিঙ্গ এবং শিব প্রকৃতপক্ষে একই।’– (ভূমিকা, লিঙ্গ পুরাণ)
বস্তুত কখন কিভাবে শিবের প্রতীক লিঙ্গ অর্থাৎ শিশ্ন বা পুং জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক হিসেবে একীভূত হলো তার সন তারিখ সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করে বলা এখন আর সম্ভব না হলেও মহাকাব্যের যুগে এসে যে এই একীভূত ধারণা ইতোমধ্যেই দানা বেঁধে ফেলেছে তার সাক্ষ্য মহাভারতে আর অস্পষ্ট নয়।
লিঙ্গপুরাণে লিঙ্গমূর্তিতে শিব পূজার কথা যেমন আছে, তেমনি তাঁর অপর বিভিন্ন মূর্তির কথাও আছে। প্রাচীন ভারতে শিব পূজার ব্যাপক প্রচলন থাকলেও লিঙ্গমূর্তিতে তাঁর পূজার প্রচলন উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে হয়তো ততটা ছিলো না। মহাভারতের যুগে মূর্তিতে ও লিঙ্গে উভয় আধারেই শিবপূজা হতো, তবে প্রথমটিই ছিলো ব্যাপক। তার মানে খ্রিস্টপূর্ব কালেই শিব ও লিঙ্গ এই উভয় ধারণার ভিন্ন ভিন্ন উপস্থিতি ছিলো এবং উভয়কে সমন্বিত করার প্রয়াসও অস্পষ্ট নয়। কেননা, লিঙ্গার্চনাকে বিভিন্ন আখ্যানের দ্বারা প্রাধান্য দেবার চেষ্টা মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হয়। এজন্য ব্যাসদেব বিভিন্ন প্রকার অর্থবাদের সাহায্য নিয়েছেন। যেমন মহাভারতের একটি আখ্যানে দেখা যায়– দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা মহাদেবের তপস্যার দ্বারা অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করলেন। আবার কৃষ্ণার্জুনও জন্মান্তরে নরনারায়ণ রূপে তপস্যা করে মহাদেবের বর পান। অথচ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র অর্জুনের কাছে ব্যর্থ হলো কেন? একথা ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করা হলো। উত্তরে ব্যাসদেব জানালেন– কৃষ্ণার্জুন তপস্যাকালে লিঙ্গে শিবার্চন করতেন এবং অশ্বত্থামা প্রতিমায় অর্চনা করতেন, তাই ‘জন্মকর্মতপো যোগে’ অশ্বত্থামা তাদের মতো হয়েও তাদের সমান ফল পেলেন না। এভাবে লিঙ্গার্চনাকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা মহাভারতের অনেক স্থলেই পরিলক্ষিত হয়। যেমন, দ্রোণপর্বের এক স্থলে বলা হচ্ছে–
লিঙ্গপুরাণে লিঙ্গমূর্তিতে শিব পূজার কথা যেমন আছে, তেমনি তাঁর অপর বিভিন্ন মূর্তির কথাও আছে। প্রাচীন ভারতে শিব পূজার ব্যাপক প্রচলন থাকলেও লিঙ্গমূর্তিতে তাঁর পূজার প্রচলন উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে হয়তো ততটা ছিলো না। মহাভারতের যুগে মূর্তিতে ও লিঙ্গে উভয় আধারেই শিবপূজা হতো, তবে প্রথমটিই ছিলো ব্যাপক। তার মানে খ্রিস্টপূর্ব কালেই শিব ও লিঙ্গ এই উভয় ধারণার ভিন্ন ভিন্ন উপস্থিতি ছিলো এবং উভয়কে সমন্বিত করার প্রয়াসও অস্পষ্ট নয়। কেননা, লিঙ্গার্চনাকে বিভিন্ন আখ্যানের দ্বারা প্রাধান্য দেবার চেষ্টা মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হয়। এজন্য ব্যাসদেব বিভিন্ন প্রকার অর্থবাদের সাহায্য নিয়েছেন। যেমন মহাভারতের একটি আখ্যানে দেখা যায়– দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা মহাদেবের তপস্যার দ্বারা অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করলেন। আবার কৃষ্ণার্জুনও জন্মান্তরে নরনারায়ণ রূপে তপস্যা করে মহাদেবের বর পান। অথচ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র অর্জুনের কাছে ব্যর্থ হলো কেন? একথা ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করা হলো। উত্তরে ব্যাসদেব জানালেন– কৃষ্ণার্জুন তপস্যাকালে লিঙ্গে শিবার্চন করতেন এবং অশ্বত্থামা প্রতিমায় অর্চনা করতেন, তাই ‘জন্মকর্মতপো যোগে’ অশ্বত্থামা তাদের মতো হয়েও তাদের সমান ফল পেলেন না। এভাবে লিঙ্গার্চনাকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা মহাভারতের অনেক স্থলেই পরিলক্ষিত হয়। যেমন, দ্রোণপর্বের এক স্থলে বলা হচ্ছে–
সর্বরূপং ভবং জ্ঞাত্বা লিঙ্গে যোহর্চয়তি প্রভুম্ ।
আত্মযোগশ্চ তস্মিন্ বৈ শাস্ত্রযোগাশ্চ শাশ্বতাঃ।। (মহাভারত-৭/২০০/৯৩)
অর্থাৎ : ভবকে (শিবকে) সমস্ত বস্তুর মধ্যে অবস্থিত জেনে যিনি লিঙ্গে শিবার্চনা করেন তাঁরই আত্মযোগ এবং শাস্ত্রযোগ শাশ্বত হয়।
‘লিঙ্গার্চনাকে মহাভারতকার ব্যাসদেব সূক্ষ্ম জ্ঞানীর কর্ম বলে মনে করেছেন এবং মূর্তি পূজাকে অসূক্ষ্ম জ্ঞানীর কর্ম বলেছেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ উভয় পূজার দার্শনিক পার্থক্য দেখাতে গিয়ে দক্ষ সংহিতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর মতে লিঙ্গপূজক ইন্দ্রিয় এবং বিষয় থেকে মনকে প্রত্যাহার করে ব্রহ্মস্বরূপ (শিবেতে) নিবিষ্ট করে তন্ময় হন বলে শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞান পান। মূর্তিপূজক তা পান না। দক্ষ প্রজাপতি তাই শিবকে বলেছেন– ‘যা মূর্তয়ঃ সূসূক্ষ্মাস্তে ন মহং যান্তি দর্শনম্’ (মহা-১২/২৮৯/৯৫)। অর্থাৎ তোমার যেসব সুসূক্ষ্মমূর্তি তাদের আমি দর্শন পাই না।’– (ড. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/ ভূমিকা, লিঙ্গ পুরাণ)
গোড়ার দিকে লিঙ্গ ও যোনি স্বতন্ত্রভাবে পূজিত হতো তা ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা– ‘প্রাক্-গুপ্ত যুগের যে সব শিবলিঙ্গ বা তার চিত্র মুদ্রায় বা সীলে দেখা যায়, সেগুলিতে পরবর্তীকালের যোনিপট্ট অনুপস্থিত। এই যুগের একটি বিশেষ মূর্তির কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এই মূর্তিটি অন্ধ্রপ্রদেশের গুড়িমল্লম গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিটি একটি পরশু ও মৃগধারী দ্বিভুজ শিবের। সংশ্লিষ্ট লিঙ্গটি ঊর্ধ্বোত্থিত, মুক্তমুখচর্ম পুরুষাঙ্গের আকারে রূপায়িত। মথুরা ও লক্ষ্ণৌ সংগ্রহশালায় খ্রীষ্টীয় প্রথম তিন শতকের যে সকল যোনিপট্টহীন শিবলিঙ্গ রক্ষিত আছে সেগুলি মুক্তমুখচর্ম পুরুষাঙ্গের পুরোদস্তুর অনুকরণ। উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি মুদ্রার একদিকে শিবের মনুষ্য মূর্তি, অপর দিকে তাঁর লিঙ্গ মূর্তি অঙ্কিত আছে। শৈবধর্মে তান্ত্রিক প্রভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ ও যোনির যুক্তরূপ অধিকতর জনপ্রিয় হয়।’
‘শিবলিঙ্গের সঙ্গে যোনিপট্ট যুক্ত হবার পর লিঙ্গের মুক্তমুখচর্ম ধরনের কিছু পরিবর্তন ঘটে। ক্রমশ পূজাপ্রতীক রূপে লিঙ্গ আশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে দেখা যায় যে উপমন্যু কৃষ্ণের সম্মুখে এই বলে শিবের গুণগান গাইছেন যে শিবই একমাত্র দেবতা যাঁর লিঙ্গ ব্যাপকভাবে পূজিত হয়। পূজাপ্রতীক হিসাবে লিঙ্গ এতদূর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে প্রতি শিবমন্দিরের গর্ভগৃহে প্রধানতম এবং মুখ্য পূজার বস্তু হিসাবে লিঙ্গই অধিষ্ঠিত হয়। শিবের মনুষ্য মূর্তি গৌণ হয়ে ওঠে। ইলোরার কৈলাস মন্দিরের গর্ভগৃহে যে মূল দেবতাটি স্থান পেয়েছেন তিনি হচ্ছেন লিঙ্গ, মনুষ্য মূর্তিগুলির স্থান অন্যান্য গৌণ স্থানে। একথা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের ক্ষেত্রেও সত্য।’– (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/ ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৯৮-৯৯)
‘শিবলিঙ্গের সঙ্গে যোনিপট্ট যুক্ত হবার পর লিঙ্গের মুক্তমুখচর্ম ধরনের কিছু পরিবর্তন ঘটে। ক্রমশ পূজাপ্রতীক রূপে লিঙ্গ আশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে দেখা যায় যে উপমন্যু কৃষ্ণের সম্মুখে এই বলে শিবের গুণগান গাইছেন যে শিবই একমাত্র দেবতা যাঁর লিঙ্গ ব্যাপকভাবে পূজিত হয়। পূজাপ্রতীক হিসাবে লিঙ্গ এতদূর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে প্রতি শিবমন্দিরের গর্ভগৃহে প্রধানতম এবং মুখ্য পূজার বস্তু হিসাবে লিঙ্গই অধিষ্ঠিত হয়। শিবের মনুষ্য মূর্তি গৌণ হয়ে ওঠে। ইলোরার কৈলাস মন্দিরের গর্ভগৃহে যে মূল দেবতাটি স্থান পেয়েছেন তিনি হচ্ছেন লিঙ্গ, মনুষ্য মূর্তিগুলির স্থান অন্যান্য গৌণ স্থানে। একথা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের ক্ষেত্রেও সত্য।’– (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/ ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৯৮-৯৯)
প্রসঙ্গক্রমে এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য। স্মরণাতীত কাল থেকেই রুদ্র পূজকদের সাথে যাঁরা রুদ্রকে পূজা করতেন না তাঁদের একটা সংঘাত ছিলই। কারণ চিরকালই আর্যদের মধ্যে সকলেই বৈদিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। আবার কিছু লোককে বিভিন্ন সময়ে বৈদিক সংস্কৃতি থেকে বহিষ্কার করাও হয়েছিল। এদেরকে বলা হতো ‘বাহীক’ বা ‘ব্রাত্যজন’ (সে যুগে ‘ব্রাত্য’ বলতে বেদবহির্ভূত সমস্ত আর্য-অনার্য মানুষকেই বোঝানো হতো)। ফলে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজনে এইসব ব্রাত্যজনেরা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথে যথেচ্ছভাবে মেলামেশা করে এক বেদবহির্ভূত জনগোষ্ঠীর সূচনা করে। যাতে আর্য-অনার্য সকলেরই স্থান ছিল। আর তৎকালীন সমাজে এরা সংখ্যায় নিতান্ত কমও ছিল না। এছাড়া প্রাগার্য সমাজ জীবনে আদি শিবের পূজা ব্যবস্থা ছিল। সেই ধারায় অনার্য সমাজেও শিবের পূজা হতো। কিন্তু বৈদিক আর্যদের রুদ্র পূজন পদ্ধতি অবৈদিক পূজা ব্যবস্থা থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে আর্য সমাজের রুদ্র ব্রাত্য ও অনার্যদের কাছে পূজনীয় ও সম্মানীয় ছিল না; তাই সামাজিক বৈরিতা বশে ব্রাত্য ও অনার্যদের সাথে বৈদিক আর্যদের তীব্র বিরোধ থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। এ অবস্থায় প্রাগার্য পূজিত দেবতা আর্য সংস্কৃতিতে কীভাবে ও কেন অনুপ্রবেশ করলো, সে বিষয়টি নিশ্চয়ই কৌতুহলজনক। এ সম্পর্কে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন,–
‘খুব সম্ভবত আর্যগণ যখন এদেশে আসেন তখন তাঁহাদের সাথে নারীর সংখ্যা বেশী ছিল না, তাই তাঁদের এদেশীয় আর্যপূর্ব জাতির কন্যাগ্রহণে কোন আপত্তি ছিল না। ক্রমে তাঁহারা এত শূদ্র কন্যাকে ঘরে লইলেন যে হয়তো নারীদের মধ্যে অধিকাংশই হইলেন বেদে অনধিকারিণী শূদ্রা। হয়তো, এইসব শূদ্র কন্যারাও পতিগণের বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা পিতৃকুলের প্রাচীন ধর্মই বেশী পছন্দ করিতেন। তাই তাঁরা নিজেরাও যাগ-যজ্ঞাদিতে যোগ দিতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না। পরবর্তীকালে এইসব শূদ্র নারী (পত্নীরাই) আর্য সমাজে বৈদিক দেবতার পরিবর্তে অনার্য দেবগণের পূজা প্রবেশ করাইয়াছিলেন।’
এখানে শূদ্র নারী বলতে সেন মহাশয় বোধকরি অনার্য নারীকেই বুঝিয়েছেন। কেননা তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতিভেদ তথা সমাজ-বিভাজনকারী বর্ণাশ্রমের কোনরূপ সাক্ষ্য অন্তত বেদ-সংহিতার যুগে কোথাও পাওয়া যায় না। এটি পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য কায়েমীবাদী ধারণা। তবে বস্তুতই নবাগত আর্যরা যে নারীর অপ্রতুলতায় এদেশের মেয়েদের উপর ভীষণ লোভী ছিলেন তার সাক্ষ্য ঋগ্বেদ-সংহিতায় অপ্রতুল নয়। অন্ন ও বিভিন্ন ধন প্রার্থনার পাশাপাশি স্ত্রী পাওয়ার জন্য ইন্দ্রের কাছে অনবরত প্রার্থনা জানাতো, যেমন–
‘খুব সম্ভবত আর্যগণ যখন এদেশে আসেন তখন তাঁহাদের সাথে নারীর সংখ্যা বেশী ছিল না, তাই তাঁদের এদেশীয় আর্যপূর্ব জাতির কন্যাগ্রহণে কোন আপত্তি ছিল না। ক্রমে তাঁহারা এত শূদ্র কন্যাকে ঘরে লইলেন যে হয়তো নারীদের মধ্যে অধিকাংশই হইলেন বেদে অনধিকারিণী শূদ্রা। হয়তো, এইসব শূদ্র কন্যারাও পতিগণের বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা পিতৃকুলের প্রাচীন ধর্মই বেশী পছন্দ করিতেন। তাই তাঁরা নিজেরাও যাগ-যজ্ঞাদিতে যোগ দিতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না। পরবর্তীকালে এইসব শূদ্র নারী (পত্নীরাই) আর্য সমাজে বৈদিক দেবতার পরিবর্তে অনার্য দেবগণের পূজা প্রবেশ করাইয়াছিলেন।’
এখানে শূদ্র নারী বলতে সেন মহাশয় বোধকরি অনার্য নারীকেই বুঝিয়েছেন। কেননা তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতিভেদ তথা সমাজ-বিভাজনকারী বর্ণাশ্রমের কোনরূপ সাক্ষ্য অন্তত বেদ-সংহিতার যুগে কোথাও পাওয়া যায় না। এটি পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য কায়েমীবাদী ধারণা। তবে বস্তুতই নবাগত আর্যরা যে নারীর অপ্রতুলতায় এদেশের মেয়েদের উপর ভীষণ লোভী ছিলেন তার সাক্ষ্য ঋগ্বেদ-সংহিতায় অপ্রতুল নয়। অন্ন ও বিভিন্ন ধন প্রার্থনার পাশাপাশি স্ত্রী পাওয়ার জন্য ইন্দ্রের কাছে অনবরত প্রার্থনা জানাতো, যেমন–
স ঘা নো যোগ আ ভুবত্স রাযে স পুরন্ধ্যাং।
পমদ্বাজেভিরা স নঃ।। (ঋক-১/৫/৩)
আ প্র দ্রব হরিবো মা বি বেনঃ পিশঙ্গরাতে অভি নঃ সচস্ব।
নহি ত্বদিন্দ্র বস্যো অন্যদস্ত্যমেনাংশ্চিজনিবতশ্চকর্থ।। (ঋক-৫/৩১/২)
অর্থাৎ :
তিনি আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করুন, তিনি ধন প্রদান করুন, তিনি স্ত্রী প্রদান করুন, তিনি অন্ন নিয়ে আমাদের নিকটে আগমন করুন। (ঋ-১/৫/৩)।। হে অশ্ববান ইন্দ্র! তুমি আমাদের সামনে এস এবং আমাদের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করো না; হে বিবিধ ধনদাতা! আমাদের প্রতি অনুকুল হও, কারণ তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কিছুই নেই; তুমি পত্নিহীন ব্যক্তিগণকে পত্নী প্রদান করেছ। (ঋ-৫/৩১/২)।।
এই অনার্য নারীরা আর্য সমাজে কেবল যে অনার্য দেবগণের পূজা প্রবেশ করিয়েছিলেন তাই নয়, আদিম মানব সমাজে একসময়ে মেয়েরাই যেমন চাষাবাদের প্রবর্তন করেছিলো তেমনি আর্য সমাজে বস্ত্র বয়ন ও কৃষিকার্যের প্রবর্তন ও প্রচলনও করেছে এই অনার্য রমণীরা। বস্ত্রবয়ন সম্পর্কে ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে বৈদিক আর্যরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে তাঁরা বস্ত্র বয়ন করতে জানে না–
না হং তন্তু ন বি জানাম্যোতুং ন যং বয়ন্তি সমরেহতমানাঃ। (ঋ.স.-৬/৯/২)
অর্থাৎ : আমি তন্তু অথবা ওতু জানি না, কিম্বা সতত চেষ্টাদ্বারা যে বস্ত্র বয়ন করে তার কিছুই অবগত নই। (যদিও টীকাকার সায়ণ বলেন, এস্থলে তন্তু শব্দদ্বারা বৈদিক ছন্দসমূহ, ওতু শব্দদ্বারা যজুসমূহ ও বাগকার্য এবং উভয়ের সংঘটনদ্বারা বস্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞ বুঝতে হবে।)
এবং–
সাধ্বপাংশি সনতা ন উক্ষিতে উষাসানক্তা বয্যেব রশ্মিতে।
তন্তুং ততং সম্বয়ন্তী সমীচী যজ্ঞস্য পেশঃ সুদুঘে পয়স্বতী।। (ঋক-২/৩/৬)
অর্থাৎ : আমাদের সাধু কর্মফলের চিরপ্রদায়ী উষা ও নক্ত রূপ অগ্নি, বয়নকুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সাহায্যার্থে গমনাগমন করে যজ্ঞের রূপ নির্মাণার্থে পরস্পরকে আনুকূল্য করে বিস্তৃত তন্তু বয়ন করছেন। তাঁরা অত্যন্ত ফলপ্রদ এবং উদকবিশিষ্ট। (টীকাকার বলেন যে সেকালে দুজন নারী’তে টানা ও পোড়েন’ সঞ্চালন করে বস্ত্র প্রস্তুত করতো।)
এদেশে আসবার আগে আর্যদের আদিম বাসস্থান খুব সম্ভবত ছিল শীতপ্রধান দেশে। সেখানে শরীরকে গরম রাখবার জন্যে তারা মাংসাশী ছিলেন। শিকারই ছিল তাদের প্রধান কিংবা একমাত্র পেশা। হয়তো দেবতার নামে কোনও এক বিশেষ জীবকে উৎসর্গ দিয়ে আরম্ভ করেছিলো– নরমেধ যজ্ঞ। তারপর ক্রমিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে আরম্ভ হয় অশ্বমেধ, গোমেধ, মেষমেধ ও ছাগমেধ যজ্ঞও। এরপরই তারা ভূমিকর্ষণ করে শস্য উৎপাদনের জ্ঞান লাভ করে। এর সাক্ষ্য হিসেবে ‘শতপথ ব্রাহ্মণের’ প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বলিদান সম্বন্ধে এক বিস্ময়কর বর্ণনা পাওয়া যায় বলে অশোক রায় উল্লেখ করেছেন,–
‘প্রথমত, দেবতারা একটি মনুষ্যকে উৎসর্গ করলেন, তার উৎসর্গীকৃত আত্মা অশ্বদেহে প্রবেশ করল। দেবতারা অশ্বকে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন; উৎসর্গীকৃত আত্মা বলীবর্দে প্রবেশ করল। বলীবর্দকে উৎসর্গ করা হলে, ওই আত্মা মেষদেহে প্রবিষ্ট হল; মেষ উৎসর্গীকৃত হলে, উহা ছাগদেহে প্রবিষ্ট হল। ছাগ উৎসর্গীকৃত হলে, পৃথিবীতে প্রবেশ করল। দেবতারা পৃথিবী খনন করে ধান্য ও যব আকারে ওই আত্মাকে পেলেন। তদবধি সকলে এখনও ধান্যাদি কর্ষণ দ্বারা পেয়ে থাকেন।’
‘প্রথমত, দেবতারা একটি মনুষ্যকে উৎসর্গ করলেন, তার উৎসর্গীকৃত আত্মা অশ্বদেহে প্রবেশ করল। দেবতারা অশ্বকে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন; উৎসর্গীকৃত আত্মা বলীবর্দে প্রবেশ করল। বলীবর্দকে উৎসর্গ করা হলে, ওই আত্মা মেষদেহে প্রবিষ্ট হল; মেষ উৎসর্গীকৃত হলে, উহা ছাগদেহে প্রবিষ্ট হল। ছাগ উৎসর্গীকৃত হলে, পৃথিবীতে প্রবেশ করল। দেবতারা পৃথিবী খনন করে ধান্য ও যব আকারে ওই আত্মাকে পেলেন। তদবধি সকলে এখনও ধান্যাদি কর্ষণ দ্বারা পেয়ে থাকেন।’
উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রুদ্র বৈদিক সাহিত্যের শুরুতে, ঋগ্বেদ-সংহিতায়, মাত্র তিনটি সূক্তে স্তুত হয়েছেন। সেই বৈদিক সাহিত্যেরই মধ্য গগনে, কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদে তিনি রুদ্রাধ্যায় ও শতরুদ্রীয়তে দার্শনিকতার চরমোৎকর্ষতা দিয়ে স্তুত হয়ে পরমাত্মায় পর্যবসিত হয়েছেন। ঋগ্বেদে যিনি অত্যন্ত অপ্রধান দেবতা, তিনিই কেমন করে হয়ে গেলেন পরমাত্মা? বিষয়টির প্রমাণ হিসেবে ক্রমবিবর্তনিক সাহিত্য নিদর্শন ইতোমধ্যেই উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বৈদিক সাহিত্যের আকার-আয়তন প্রকৃতই সাগর সমতুল্য। মানব-সভ্যতার সমান্তরালে ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষকাল থেকে ক্রমবিকাশের যে সাহিত্য-নিদর্শন তার মধ্যে সুপ্ত ও সংরক্ষিত আছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তার যথার্থ অনুসন্ধানের মাধ্যমে বহু আপাত অব্যাখ্যেয় প্রশ্নের সন্ধান অসম্ভব নয় বলেই বিদ্বান গবেষকদের অভিমত। লিঙ্গ ও আদিশিব এবং রুদ্রের ধারণার ক্রমবিকাশ ও তাদের একাত্ম হওয়ার ধারাবাহিক পথপরিক্রমার সামান্য কিছু নিদর্শন এখানে উপস্থাপন করা হলেও আরো বহু বিচিত্র নিদর্শন যে এই সাহিত্যের ভাজে ভাজে অক্ষত ও পূর্ণরূপে লুকিয়ে আছে এ ব্যাপারে বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। যথাযথ অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সেগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি সামাজিক রূপরেখা অঙ্কন করা মোটেও অসম্ভব নয়।
এটা এখন স্বীকৃত যে, ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে আর্যরা তাঁদের আদিম বাসভূমি থেকেই ছিলেন প্রকৃতি পূজক। অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশরূপকেই তাঁরা বিভিন্ন দেবতার রূপ-কল্পনায় স্তুতি-বন্দনা করতেন। ভারতবর্ষে এসে যখন তাঁরা পঞ্চনদের অঞ্চলকে তাঁদের বিজয় অভিযানের পাদমঞ্চ করে এগিয়ে চললেন তখন এদেশ একেবারে জনশূন্য ছিল না, বরং যাঁরা ছিলেন এখানকার আদিবাসী তারা তখন তৎকালের বিচারে এক অত্যুন্নত নগর সভ্যতার চরম শিখরে। আর্য ও অনার্য এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে একটা বড় ধরনের পার্থক্য ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাগার্য সংস্কৃতি ছিল মোটামুটিভাবে বৈষয়িক সংস্কৃতি, আর আর্যদের ছিল যাজকীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। প্রাগার্যদের মধ্যেও দেব উপাসনা ও যাজকীয় ব্যাপার ছিল হয়তো, তবে তা আর্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে শুরু হলো বিরোধ ও লড়াই। যেহেতু নবাগত আর্যরা ঘোড়ার ব্যবহার জানতো, যা প্রাগার্যদের কাছে ছিল অপরিচিত, ফলে ক্ষিপ্র গতিময়তার কাছে পরাভূত হতে হলো এদেশের উন্নত সভ্যতায় সভ্য ভূমিপুত্রদের। একে একে ধ্বংস হয়ে গেলো তাঁদের দীর্ঘদিনের সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ নগর বা পুরগুলো। সর্বস্ব হারিয়ে যাঁরা বেঁচে ছিলেন খাদ্য সংগ্রাহক-যাযাবর-আরণ্যক জীবনে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন তাঁরা।
আক্রমণকারী আর্যরা তাঁদের সব কিছুকে ধ্বংস করে দিলেও কিন্তু স্ত্রীধনকে নির্দ্বিধায় লুণ্ঠন ও গ্রহণ করলো। ফলে অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিঃশব্দ অনুপ্রবেশ ঘটলো আর্য সমাজজীবনে। এইসব অনার্য নারীদের সংস্পর্শে-প্রভাবে আক্রমণকারী লুটেরা-যাযাবর-খাদ্যসংগ্রাহক আর্যরা ধীরে ধীরে সংস্কৃত হলো। সৃষ্টি হতে থাকলো বৈদিক সাহিত্যসম্ভার। যদিও একাজ তাঁরা তাঁদের আদিম বাসভূমি থেকেই শুরু করেছিলেন, তবুও অনুকূল পরিবেশে, স্থায়ী বসবাসের সুস্থতায় অর্গলমুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত নির্ঝরিণীর রূপ নিলো।
বলা বাহুল্য, সেই লুণ্ঠিত স্ত্রীধন আর্য সমাজ জীবনকে ক্রমশ সংস্কৃত করে তুললেও তাঁদের সেই অনার্য সংস্কৃতি আর্য সমাজ জীবন ও সংস্কৃতিকে উভয়-সংকটে ফেলে দিলো। কেননা আর্যরা কখনওই মূর্তি পূজক ছিলো না, কিন্তু প্রাগার্য সভ্যতার দেব-দেবীরা বিশেষত তাঁদের গণ-দেবতা ‘আদি শিব’ অনার্য সমাজজীবনে মূর্তিরূপে ও লিঙ্গ প্রতীকে সর্বদাই পূজিত হতেন। তাঁকে অস্বীকার করলে একদিকে যেমন নষ্ট হয় গৃহশান্তি, অন্যদিকে বাড়ে জনরোষ। শেষপর্যন্ত যা হলো, প্রকৃতি পূজক আর্যরা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশরূপের চৈতন্যসত্তাকে বিভিন্ন দেবতারূপে স্তুতি বন্দনা করতেন, সেই প্রকৃতির যে ভয়াল-ভয়ঙ্কর রূপ, যাঁকে স্তব-স্তুতি করে তুষ্ট করতে না-পারলে সৃষ্টি যায় রসাতলে, তারই অধীশ্বর হলেন রুদ্রদেব। ইনি ভয়ঙ্করের দেবতা, অমিত শক্তির অধিকারী, তিনিই হলেন ‘আদি শিবের’ বৈদিক সমীকরণ। এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে হয়তো একটা আপোসরফার আপাত সমাধান হলো। তাই ঋগ্বেদ সংহিতায় দেখা যায় বৈদিক রুদ্র একজন অত্যন্ত অপ্রধান দেবতা। যাঁর উদ্দেশে রচিত হলো মাত্র তিনটি শ্লোক বা সূক্ত, যেখানে ইন্দ্রের নামে রয়েছে অন্তত আড়াইশ সূক্ত।
এটা এখন স্বীকৃত যে, ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে আর্যরা তাঁদের আদিম বাসভূমি থেকেই ছিলেন প্রকৃতি পূজক। অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশরূপকেই তাঁরা বিভিন্ন দেবতার রূপ-কল্পনায় স্তুতি-বন্দনা করতেন। ভারতবর্ষে এসে যখন তাঁরা পঞ্চনদের অঞ্চলকে তাঁদের বিজয় অভিযানের পাদমঞ্চ করে এগিয়ে চললেন তখন এদেশ একেবারে জনশূন্য ছিল না, বরং যাঁরা ছিলেন এখানকার আদিবাসী তারা তখন তৎকালের বিচারে এক অত্যুন্নত নগর সভ্যতার চরম শিখরে। আর্য ও অনার্য এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে একটা বড় ধরনের পার্থক্য ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাগার্য সংস্কৃতি ছিল মোটামুটিভাবে বৈষয়িক সংস্কৃতি, আর আর্যদের ছিল যাজকীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। প্রাগার্যদের মধ্যেও দেব উপাসনা ও যাজকীয় ব্যাপার ছিল হয়তো, তবে তা আর্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে শুরু হলো বিরোধ ও লড়াই। যেহেতু নবাগত আর্যরা ঘোড়ার ব্যবহার জানতো, যা প্রাগার্যদের কাছে ছিল অপরিচিত, ফলে ক্ষিপ্র গতিময়তার কাছে পরাভূত হতে হলো এদেশের উন্নত সভ্যতায় সভ্য ভূমিপুত্রদের। একে একে ধ্বংস হয়ে গেলো তাঁদের দীর্ঘদিনের সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ নগর বা পুরগুলো। সর্বস্ব হারিয়ে যাঁরা বেঁচে ছিলেন খাদ্য সংগ্রাহক-যাযাবর-আরণ্যক জীবনে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন তাঁরা।
আক্রমণকারী আর্যরা তাঁদের সব কিছুকে ধ্বংস করে দিলেও কিন্তু স্ত্রীধনকে নির্দ্বিধায় লুণ্ঠন ও গ্রহণ করলো। ফলে অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিঃশব্দ অনুপ্রবেশ ঘটলো আর্য সমাজজীবনে। এইসব অনার্য নারীদের সংস্পর্শে-প্রভাবে আক্রমণকারী লুটেরা-যাযাবর-খাদ্যসংগ্রাহক আর্যরা ধীরে ধীরে সংস্কৃত হলো। সৃষ্টি হতে থাকলো বৈদিক সাহিত্যসম্ভার। যদিও একাজ তাঁরা তাঁদের আদিম বাসভূমি থেকেই শুরু করেছিলেন, তবুও অনুকূল পরিবেশে, স্থায়ী বসবাসের সুস্থতায় অর্গলমুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত নির্ঝরিণীর রূপ নিলো।
বলা বাহুল্য, সেই লুণ্ঠিত স্ত্রীধন আর্য সমাজ জীবনকে ক্রমশ সংস্কৃত করে তুললেও তাঁদের সেই অনার্য সংস্কৃতি আর্য সমাজ জীবন ও সংস্কৃতিকে উভয়-সংকটে ফেলে দিলো। কেননা আর্যরা কখনওই মূর্তি পূজক ছিলো না, কিন্তু প্রাগার্য সভ্যতার দেব-দেবীরা বিশেষত তাঁদের গণ-দেবতা ‘আদি শিব’ অনার্য সমাজজীবনে মূর্তিরূপে ও লিঙ্গ প্রতীকে সর্বদাই পূজিত হতেন। তাঁকে অস্বীকার করলে একদিকে যেমন নষ্ট হয় গৃহশান্তি, অন্যদিকে বাড়ে জনরোষ। শেষপর্যন্ত যা হলো, প্রকৃতি পূজক আর্যরা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশরূপের চৈতন্যসত্তাকে বিভিন্ন দেবতারূপে স্তুতি বন্দনা করতেন, সেই প্রকৃতির যে ভয়াল-ভয়ঙ্কর রূপ, যাঁকে স্তব-স্তুতি করে তুষ্ট করতে না-পারলে সৃষ্টি যায় রসাতলে, তারই অধীশ্বর হলেন রুদ্রদেব। ইনি ভয়ঙ্করের দেবতা, অমিত শক্তির অধিকারী, তিনিই হলেন ‘আদি শিবের’ বৈদিক সমীকরণ। এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে হয়তো একটা আপোসরফার আপাত সমাধান হলো। তাই ঋগ্বেদ সংহিতায় দেখা যায় বৈদিক রুদ্র একজন অত্যন্ত অপ্রধান দেবতা। যাঁর উদ্দেশে রচিত হলো মাত্র তিনটি শ্লোক বা সূক্ত, যেখানে ইন্দ্রের নামে রয়েছে অন্তত আড়াইশ সূক্ত।
সময়ের সাথে সাথে বৈদিক সাহিত্য ধীরে ধীরে পল্লবিত হতে থাকে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে। কায়িক শ্রম থেকে বিযুক্ত আর্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা ব্যস্ত হয়ে রইলেন সংহিতা ও ব্রাহ্মণের কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড নিয়ে। ফলে দুই শাখারই ক্রমপুষ্টি হতে থাকে সময়ের সাথে সাথে। এসব চর্চা ছিল অত্যন্ত মুষ্টিমেয় কিছু সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে দেশের যে বিপুল সংখ্যক জনগণ তারা ছিল এসব কিছুর থেকে বাইরে, নিতান্ত অপাঙক্তেয়ের দলে। প্রথম থেকেই যেহেতু বৈদিক আর্যরা অবৈদিক মানুষদেরকে অবজ্ঞার চোখেই দেখতেন, সেই ক্ষোভ ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে প্রতিবাদে পরিণত হয়। তাছাড়া সেই সময়ে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কর্মগুলো এতো বিস্তৃত ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছিলো যে তা রাজ-রাজড়া ছাড়া সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত হয়ে গিয়েছিল। এ তথ্য আমরা যজুর্বেদের শুল্ব সূক্ত থেকে জানতে পারি। ফলে অথর্ববেদে দেখা দেয় বৈদিক যাগ-যজ্ঞের পরিবর্তে আভিচারিক ক্রিয়াকর্ম। শুরু হয় তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, বশীকরণ, মারণ, উচাটন, তাবিচ-কবট ও মাদুলি। এভাবে সমাজে আবার জনপ্রিয় হলো ওঝা, গুনিন ইত্যাদিরা। আর এই সবই এলো প্রাগার্য-অনার্য সভ্যতার অতি প্রাচীন ধারা বেয়ে। এতদিন বৈদিক সাহিত্যে যা ছিল একান্তই অবহেলিত ও অপাঙক্তেয় রূপে, তাই-ই আবার সমাজ জীবনে ফিরে এলো নব কলেবর ধারণ করে– সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের বহু কাঙ্ক্ষিত উপায় হয়ে। এছাড়াও সাধারণ মানুষের ধর্ম-কর্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটাতে শুরু হয়ে গেলো– পূজা। যা ব্যয়বহুল যাগ-যজ্ঞের পরিবর্তে সরল অনাড়ম্বর ভক্তি নিবেদনের পদ্ধতি রূপে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে দেখলে তার প্রমাণ আমরা পরবর্তীকালের প্রাচীন সাহিত্য-নিদর্শনেই খুঁজে পেতে পারি।
মুখায় তে পশুপতে য়ানি চক্ষূম্ষি তে ভব।
ত্বচে রূপায় সম্দৃশে প্রতীচীনায় তে নমঃ।। (অথর্বঃ ১১|২|৫)
________"হে (পশুপতে) সমস্ত দৃশ্যমান প্রাণীদের রক্ষক! (ভব) হে সমস্ত সুখের উৎপাদক পরমেশ্বর! আমাদের যে (য়ানি চম্ক্ষূষি) জ্ঞানের সাধন আছে তার জন্য (ত্বচে) আমাদের ত্বচার জন্য (রূপায়) সৌন্দর্যের জন্য (সম্দৃশে) ভালো স্বাস্থ্যের জন্য (প্রতীচীনায়) আমাদের পশ্চাৎ অর্থাৎ পরোক্ষের মধ্যেও রক্ষা করার জন্য আর (মুখায়) মুখ তুল্য বিদ্বান ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য (তে নমঃ) আপনাকে নমস্কার করছি।"
বিঃদ্রঃ চিত্রে যেমন পৌরাণিক পশুপতি শিব দেখানো হয়েছে তেমন বেদ মন্ত্রে নেই। এটা পৌরাণিক কাল্পনিক চিত্র।
য়জুর্বেদের (৪০|৮) মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপের উপর বিচার করা হয়েছে।
স পর্য়॑গাচ্ছু॒ক্রম॑কা॒য়ম॑ব্র॒ণম॑স্নাবি॒রꣳ শু॒দ্ধমপা॑পবিদ্ধম্ ।
ক॒বির্ম॑নী॒ষী প॑রি॒ভূঃ স্ব॑য়॒ম্ভূর্য়া॑থাতথ্য॒তোऽর্থা॒ন্ ব্য᳖দধাচ্ছাশ্ব॒তীভ্যঃ॒ সমা॑ভ্যঃ ॥
পদার্থঃ- হে মনুষ্যগণ ! যে ব্রহ্ম (শুক্রম্) শীঘ্রকারী সর্বশক্তিমান্ (অকায়ম্) স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণশরীর রহিত (অব্রণম্) ছিদ্ররহিত এবং ছিদ্র করিবার যোগ্য নহে (অস্নাবিরম্) নাড়ি আদি সহ সম্বন্ধরূপ বন্ধন হইতে রহিত (শুদ্ধম্) অবিদ্যাদি দোষ হইতে রহিত হওয়ায় সর্বদা পবিত্র এবং (অপাপবিদ্ধম্) যিনি পাপযুক্ত, পাপকারী এবং পাপে প্রীতিকারী কখনও হয়না (পরি, অগাৎ) সব দিক দিয়া ব্যাপ্ত, যিনি (কবিঃ) সর্বজ্ঞ (মনীষী) সকল জীবদের মনোবৃত্তিকে জানেন (পরিভূঃ) দুষ্ট পাপীদেরকে তিরস্কারকারী এবং (স্বয়ম্ভুঃ) অনাদি স্বরূপ যাহার সংযোগ হইতে উৎপত্তি, বিয়োগ হইতে বিনাশ, মাতা, পিতা, গর্ভবাস, জন্ম, বৃদ্ধি ও মরণ হয় না সেই পরমাত্মা (শাশ্বতীভ্যঃ) সনাতন অনাদি স্বরূপ নিজ নিজ স্বরূপে উৎপত্তি ও বিনাশরহিত (সমাভ্যঃ) প্রজাদিগের জন্য (য়াথাতথ্যতঃ) যথার্থ ভাবপূর্বক (অর্থাৎ) বেদ দ্বারা সকল পদার্থকে (ব্যদধাৎ) বিশেষ করিয়া নির্মাণ করে । (সঃ) সেই পরমেশ্বর তোমাদের উপাসনা করিবার যোগ্য ॥
অর্থাৎ- "স পর্য়গাত্"- সেই ঈশ্বর সর্বত্র ব্যাপক। "অকায়ম্"- সেই ঈশ্বর স্থূল, সূক্ষ্ম তথা কারণ শরীর হতে রহিত। "অব্রণম্"- সেই পরমাত্মা অচ্ছেদ্য, অবিকারী সত্তা। "অস্নাবিরম্"- সেই পরমাত্মা জীবাত্মার মতো নস-নাড়ির বন্ধনে কখনও আসে না। "শুদ্ধম্"- অবিদ্যা আদি দোষে গ্রস্থ না হওয়ার কারণে সর্বদা পবিত্র। "মনীষী"- তিনি সমস্ত জীবের মনোবৃত্তিকেও জানেন। "স্বয়ম্ভূ"- তাঁর কোনো কারণ নেই, যা অনাদি স্বরূপ অর্থাৎ সেই ঈশ্বর জন্ম-মরণ তথা বৃদ্ধি-ক্ষয় হতে রহিত, ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিচার করে মহর্ষি ব্যাসজী য়োগ ভাষ্যতে ঈশ্বরকে "সদৈব মক্তঃ" বলেছেন।
ভাবার্থঃ- হে মনুষ্যগণ ! যিনি অনন্ত শক্তিযুক্ত অজন্মা, নিরন্তর, সদা যুক্ত, ন্যায়কারী, নির্মল, সর্বজ্ঞ, সকলের সাক্ষী, নিয়ন্তা, অনাদিস্বরূপ ব্রহ্ম কল্পের আরম্ভে জীবদেরকে স্বকথিত বেদ হইতে শব্দ, অর্থ এবং তাহার সম্বন্ধকে জানাইবার বিদ্যার উপদেশ না করেন তাহা হইলে কেহই বিদ্বান্ হইবে না এবং না ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ফল ভোগ করিতে সক্ষম হয়, এইজন্য এই ব্রহ্মের সর্বদা উপাসনা কর ॥
গীতার ৯।১১ নং শ্লোকে মূর্তিপূজকদের মূঢ় (মূর্খ) বলে ধিক্কার করা হয়েছে
"অবজানন্তি মাম্ মূঢ়া মানুষীম্ তনু মাশ্রিতম্।।" (গীতাঃ ৯|১১)
অর্থাৎ - পরমেশ্বরের স্বরূপকে না জেনে মূর্খ ব্যক্তি ভগবানের অপমান করে, তারা ভগবানকে শরীরধারী ভেবে পূজো করে। আর উপাসনার সত্য পদ্ধতির নির্দেশ করে গীতার মধ্যে লেখা আছে -
"সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।" (গীতাঃ ৮|১২)
"ওমিত্যেকাক্ষরম্ ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।।" (গীতাঃ ৮|১৩)
অর্থাৎ - নেত্র আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ব্রহ্ম বিষয় দিয়ে থামিয়ে রেখে, মনকে হৃদয়স্থ, জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন কেন্দ্রের মধ্যে পরমাত্মার ভক্তিতে লাগিয়ে "ও৩ম্" শব্দের উচ্চারণ করার সঙ্গে পরমেশ্বরের ধ্যান করবে।
ত্বচে রূপায় সম্দৃশে প্রতীচীনায় তে নমঃ।। (অথর্বঃ ১১|২|৫)
________"হে (পশুপতে) সমস্ত দৃশ্যমান প্রাণীদের রক্ষক! (ভব) হে সমস্ত সুখের উৎপাদক পরমেশ্বর! আমাদের যে (য়ানি চম্ক্ষূষি) জ্ঞানের সাধন আছে তার জন্য (ত্বচে) আমাদের ত্বচার জন্য (রূপায়) সৌন্দর্যের জন্য (সম্দৃশে) ভালো স্বাস্থ্যের জন্য (প্রতীচীনায়) আমাদের পশ্চাৎ অর্থাৎ পরোক্ষের মধ্যেও রক্ষা করার জন্য আর (মুখায়) মুখ তুল্য বিদ্বান ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য (তে নমঃ) আপনাকে নমস্কার করছি।"
বিঃদ্রঃ চিত্রে যেমন পৌরাণিক পশুপতি শিব দেখানো হয়েছে তেমন বেদ মন্ত্রে নেই। এটা পৌরাণিক কাল্পনিক চিত্র।
য়জুর্বেদের (৪০|৮) মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপের উপর বিচার করা হয়েছে।
স পর্য়॑গাচ্ছু॒ক্রম॑কা॒য়ম॑ব্র॒ণম॑স্নাবি॒রꣳ শু॒দ্ধমপা॑পবিদ্ধম্ ।
ক॒বির্ম॑নী॒ষী প॑রি॒ভূঃ স্ব॑য়॒ম্ভূর্য়া॑থাতথ্য॒তোऽর্থা॒ন্ ব্য᳖দধাচ্ছাশ্ব॒তীভ্যঃ॒ সমা॑ভ্যঃ ॥
পদার্থঃ- হে মনুষ্যগণ ! যে ব্রহ্ম (শুক্রম্) শীঘ্রকারী সর্বশক্তিমান্ (অকায়ম্) স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণশরীর রহিত (অব্রণম্) ছিদ্ররহিত এবং ছিদ্র করিবার যোগ্য নহে (অস্নাবিরম্) নাড়ি আদি সহ সম্বন্ধরূপ বন্ধন হইতে রহিত (শুদ্ধম্) অবিদ্যাদি দোষ হইতে রহিত হওয়ায় সর্বদা পবিত্র এবং (অপাপবিদ্ধম্) যিনি পাপযুক্ত, পাপকারী এবং পাপে প্রীতিকারী কখনও হয়না (পরি, অগাৎ) সব দিক দিয়া ব্যাপ্ত, যিনি (কবিঃ) সর্বজ্ঞ (মনীষী) সকল জীবদের মনোবৃত্তিকে জানেন (পরিভূঃ) দুষ্ট পাপীদেরকে তিরস্কারকারী এবং (স্বয়ম্ভুঃ) অনাদি স্বরূপ যাহার সংযোগ হইতে উৎপত্তি, বিয়োগ হইতে বিনাশ, মাতা, পিতা, গর্ভবাস, জন্ম, বৃদ্ধি ও মরণ হয় না সেই পরমাত্মা (শাশ্বতীভ্যঃ) সনাতন অনাদি স্বরূপ নিজ নিজ স্বরূপে উৎপত্তি ও বিনাশরহিত (সমাভ্যঃ) প্রজাদিগের জন্য (য়াথাতথ্যতঃ) যথার্থ ভাবপূর্বক (অর্থাৎ) বেদ দ্বারা সকল পদার্থকে (ব্যদধাৎ) বিশেষ করিয়া নির্মাণ করে । (সঃ) সেই পরমেশ্বর তোমাদের উপাসনা করিবার যোগ্য ॥
অর্থাৎ- "স পর্য়গাত্"- সেই ঈশ্বর সর্বত্র ব্যাপক। "অকায়ম্"- সেই ঈশ্বর স্থূল, সূক্ষ্ম তথা কারণ শরীর হতে রহিত। "অব্রণম্"- সেই পরমাত্মা অচ্ছেদ্য, অবিকারী সত্তা। "অস্নাবিরম্"- সেই পরমাত্মা জীবাত্মার মতো নস-নাড়ির বন্ধনে কখনও আসে না। "শুদ্ধম্"- অবিদ্যা আদি দোষে গ্রস্থ না হওয়ার কারণে সর্বদা পবিত্র। "মনীষী"- তিনি সমস্ত জীবের মনোবৃত্তিকেও জানেন। "স্বয়ম্ভূ"- তাঁর কোনো কারণ নেই, যা অনাদি স্বরূপ অর্থাৎ সেই ঈশ্বর জন্ম-মরণ তথা বৃদ্ধি-ক্ষয় হতে রহিত, ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিচার করে মহর্ষি ব্যাসজী য়োগ ভাষ্যতে ঈশ্বরকে "সদৈব মক্তঃ" বলেছেন।
ভাবার্থঃ- হে মনুষ্যগণ ! যিনি অনন্ত শক্তিযুক্ত অজন্মা, নিরন্তর, সদা যুক্ত, ন্যায়কারী, নির্মল, সর্বজ্ঞ, সকলের সাক্ষী, নিয়ন্তা, অনাদিস্বরূপ ব্রহ্ম কল্পের আরম্ভে জীবদেরকে স্বকথিত বেদ হইতে শব্দ, অর্থ এবং তাহার সম্বন্ধকে জানাইবার বিদ্যার উপদেশ না করেন তাহা হইলে কেহই বিদ্বান্ হইবে না এবং না ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ফল ভোগ করিতে সক্ষম হয়, এইজন্য এই ব্রহ্মের সর্বদা উপাসনা কর ॥
গীতার ৯।১১ নং শ্লোকে মূর্তিপূজকদের মূঢ় (মূর্খ) বলে ধিক্কার করা হয়েছে
"অবজানন্তি মাম্ মূঢ়া মানুষীম্ তনু মাশ্রিতম্।।" (গীতাঃ ৯|১১)
অর্থাৎ - পরমেশ্বরের স্বরূপকে না জেনে মূর্খ ব্যক্তি ভগবানের অপমান করে, তারা ভগবানকে শরীরধারী ভেবে পূজো করে। আর উপাসনার সত্য পদ্ধতির নির্দেশ করে গীতার মধ্যে লেখা আছে -
"সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।" (গীতাঃ ৮|১২)
"ওমিত্যেকাক্ষরম্ ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।।" (গীতাঃ ৮|১৩)
অর্থাৎ - নেত্র আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ব্রহ্ম বিষয় দিয়ে থামিয়ে রেখে, মনকে হৃদয়স্থ, জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন কেন্দ্রের মধ্যে পরমাত্মার ভক্তিতে লাগিয়ে "ও৩ম্" শব্দের উচ্চারণ করার সঙ্গে পরমেশ্বরের ধ্যান করবে।


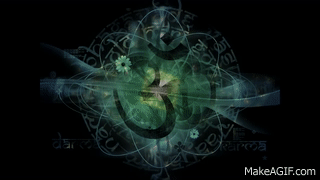




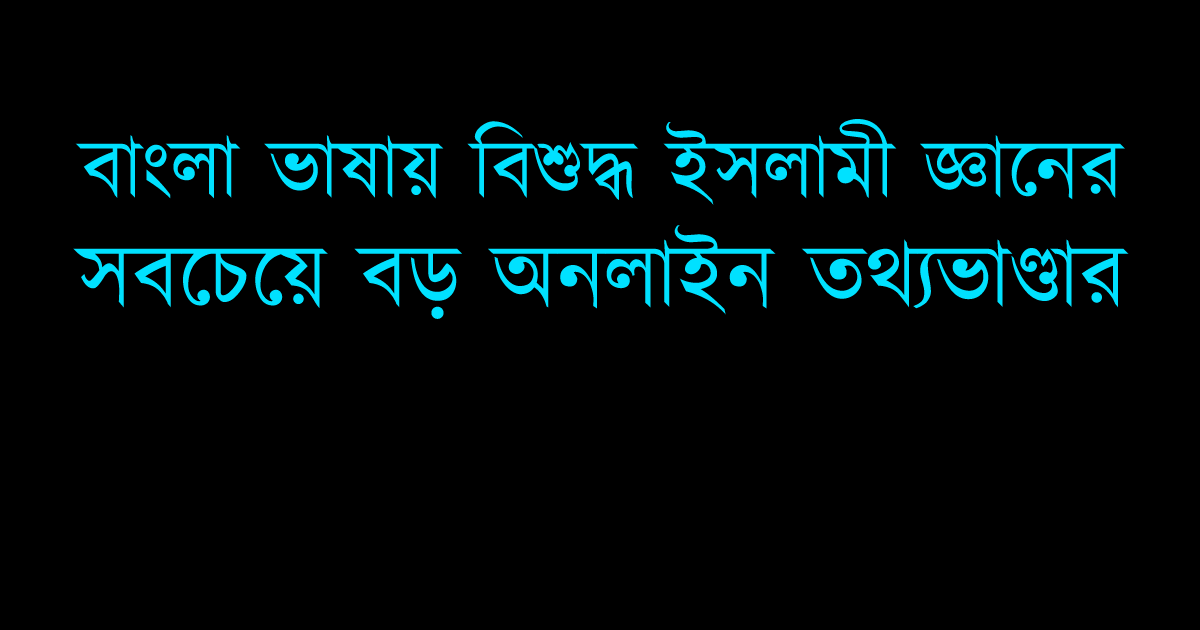
















No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ