1900 সালের কথা। বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক কাজ করছিলেন উত্তপ্ত বস্তু নিয়ে। উত্তপ্ত কোন বস্তু হতে বিভিন্ন রঙের অর্থাৎ বিভিন্ন কম্পনের যে আলো (বিকিরণ) বের হয়, তার তীব্রতা নির্ণয়ের একটা সমীকরণ তিনি বের করলেন। এবং বিখ্যাত হয়ে গেলেন – এর জন্য নোবেল পুরষ্কার পেয়ে গেলেন 1917 সালে।
আমরা সে সব সমীকরণে যাবো না, কিন্ত ঐ সমীকরণ আসলে কি বলে তা আমরা জানতে পারি। তার আগে কিছু সাধারণ ধারণা আমরা দেখতে পারি।
ঘটনা ১) ঠান্ডা বরফের মাঝেও পানির অণু থাকে, আবার তরল পানিতেও একই অণু থাকে। দুই অবস্থাতে অণু তো একই। তাহলে একবার বরফ কঠিন, অন্যবার তরল পানি হওয়ার রহস্যটা কি? আসলে যে কোন অণু সবসময়ই কাঁপে। যখন আমরা তাপ দেই, এই কম্পন বেড়ে যায়। এই কম্পন বেড়ে যায় বলেই বরফের ভেতরের পানির অণুগুলো ছোটাছুটি শুরু করে – বরফ গলে যায়।
ঘটনা 2) একেক বস্তুর ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন অণুর কম্পন নির্দিষ্ট।
একটা বেশ গরম কোন বস্তুর হয়তো আলো ছড়াচ্ছে। তারমানে তার ভেতরের অণুগুলোর একটা কম্পনাঙ্ক আছে। প্ল্যাঙ্ক এ ধরণের ঘটনা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখলেন যে একটা অবাক করা ধারণাকে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। তা হলো, কোন অণুর কেবল নির্দিষ্ট কিছু কম্পণশক্তি থাকতে পারে। এ শক্তিগুলোর মাঝামাঝি কোন শক্তি কখনোই সে ধারণ করতে পারবে না। বিষয়টা অবাক করা কেন? ধরেন আপনি ইন্টারনেট হতে কোন ফাইল ডাউনলোড করছেন। যদি আপনি দেখেন যে, ডাউনলোড স্পিড কেবল 5, 10, 15, 20, 25 কেবিপিএস ইত্যাদি কিন্তু এদের মধ্যখানে কোন মান যেমন 7, 12.5 ইত্যাদি হচ্ছে না তাহলে কি আপনি অবাক হতেন না? বলতেন না, আরে এটা আবার কি? স্পিড লাফায় লাফায় বাড়ছে কমছে কেন? স্পিড তো নিরবচ্ছিন্ন হওয়ার কথা। তাহলে কি স্পিড খন্ডায়িত? বিষয়টা হয়তো সহজে বোঝা যাবে তখন; যদি কেউ যদি বলে যে তার বয়স হলো খন্ডিত। তার বয়স নিরবচ্ছিন্ন করে বাড়ে না। হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায় তার বয়স ৫ বছর ১০ বছর করে বাড়ছে। তাহলে তার বয়সকে বলতে হবে কোয়ান্টাম বয়স!
তো, ম্যাক্স প্লাঙ্কও খুব অবাক হলেন ব্যাপারটাতে। তিনি দেখলেন, কোন অণুর এই নির্দিষ্ট শক্তি হলো h ( h প্লাঙ্কের ধ্রুবক, আসলে ভি নয়, গ্রীক নিউ(nu), যাকে দিয়ে কম্পনাঙ্ক প্রকাশ করা হচ্ছে ) এর পূর্ণ গুণিতক। এ শক্তি হতে পারে 2h, 3h, 4h কিন্তু কখনোই 3/2h, 2.5h ইত্যাদি ভগ্নাংশ কিংবা দশমিক নয়।
প্লাঙ্ক শুধু অবাক হন নি। তিনি অত্যন্ত বিব্রতও ছিলেন এ ঘটনায়। কারণ শক্তির পূর্ণ গুণিতক হলে তো আর শক্তি নিরবিচ্ছিন্ন থাকে না। শক্তি হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন। এটাতো আমরা সাধারণ জাগতিক জীবনের সাথে খাপ খায় না। আমরা দেখি জলের ধারা বিচ্ছিন্ন। একটা গাড়ি যে কোন স্পিড অর্জন করছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। আমাদের ডাউনলোড স্পীডও পাচ্ছি নিরবিচ্ছিন্ন – বাড়ছে কমছে, যে কোনমান অর্জন করছে। নিরবচ্ছিন্নর উল্টো ধারণা হলো খন্ডায়ন, বা কোয়ান্টাইজেশন। অণুর ক্ষেত্রে শক্তির যে এই সুনির্দিষ্ট কিছু বৈধ মান থাকা হলো শক্তির কোয়ান্টাইজেশন। এই ধারণাটা নিয়ৈ ম্যাক্স প্লাঙ্ক এতটাই বিব্রত ছিলেন যে ব্যার্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এই ধারণাটিকে তার তত্ত্ব হতে সরানোর! কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল এবং গণিত তাকে এই কাজটি করতে দেয় নি। এখান থেকেই কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা। পরবর্তিতে আরেক মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্লাঙ্কের এই কাজকে আরো বিকশিত করেন।
আলো এক প্রকার শক্তি। সেটা প্রাকৃতিক শক্তি। এমন শক্তি আর কী কী আছে? খুব সহজ তাই না। বিদ্যুৎ চুম্বুক, তাপ, আরেকটা আছে পারমানবিক শক্তি।
আলো, বিদ্যুৎ আর চুম্বক শক্তি আসলে আলাদা নয়। বরং তড়িৎচুম্বক শক্তির তিনটি ভিন্ন দশা হলো আলো বিদ্যুৎ ও চুম্বক শক্তি। শব্দ শক্তিকেও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গে রূপান্তর করা যায় বেতার যন্ত্রের সাহায্যে। তবু আলো-চুম্বক ও বিদ্যুৎ শক্তি থেকে শব্দ শক্তি আলাদা। শব্দ মূলত যান্ত্রিক শক্তি। সেখানে বায়ুমন্ডল নেই সেখানে এই শক্তির কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই একে একেবারে প্রাকৃতিক শক্তির কাতারে ফেলা যায় কিনা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আলো, বিদ্যুৎ আর চুম্বক শক্তি শূন্য মাধ্যতেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তৈরি করতে পারে বলক্ষেত্র। কিন্তু শব্দ মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে না। শূন্যমাধ্যম বলক্ষেত্রও তৈরি করতে পারে না। তাই শব্দকে তড়িৎচুম্বকীয় শক্তির সাথে ঠিক মেলানো যায় না। তাহলে বাকি যে শক্তিটা রয়েছে সেটা কী? তাপের কথা বলা হচ্ছে।
তাপ কি শব্দের মতো অপ্রাকৃত শক্তি?
তাপও মাধ্যমের সাহায্যে চলে। তবে তাপের চলাচলাচলের তিনটি প্রক্রিয়া আছে। পরিবহন, পরিচালন ও বিকিরণ। পরিবহন ও পরিচালন পদ্ধতিতে তাপ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে মাধ্যমের দরকার হয়। তবে এ প্রক্রিয়ায় তাপ বেশিদূর যেতে পারে না। মধ্যমের অণুগুলো এক সময় তাপ শোষণ করে তাপের শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে। তাপ বহুদূর যেতে পারে কেবল বিকিরণ পদ্ধতিতে। বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন হতে কোনো মাধ্যমের দরকার হয় না। প্রমাণ পেতে বেশিদূর যেতে হয় না।
আমাদের পৃথিবীতে যে তাপের এত কারবার, এর প্রধান উৎস সূর্য। সূর্য থেকে পৃথিবীর দুরত্ব ১৬ কোটি কিলোমিটার। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের সীমা বেশিদূর পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। বায়ুমন্ডলের শেষ ভাগ থেকে সূর্য পর্যন্ত প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার শূন্যস্থান। এই স্থান পেরিয়েই সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছায়। সেটা কীভাবে সম্ভব? সম্ভব, যদি তাপেরও তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের মতো বৈশিষ্ট্য থাকে।
আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ আসে আলোর গতিতে। আর এই বিষয়টিই তাপ আর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ খুঁজে বের করতে সহায়তা করেছে বিজ্ঞানীদের। তবে আগেকার বিজ্ঞানীদের হাতে কাল্পনিক হাতিয়ার ছিল। তাঁরা ইথারে বিশ্বাস করতেন। আর ভাবতেন ইথারই বোধহয় তাপকে সূর্য থেকে পৃথিবীতে বয়ে আনে। আমরা ইথারের পতন নিয়ে আগের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করেছি।
বিকিরণ তাপের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আলোর মতো বিকিরণ শক্তিও প্রতিফলন, প্রতিসরণ, অপবর্তন ও ব্যাতিচার ধর্ম মেনে চলে।
দুই
কোনো বস্তুর ওপর বির্কীণ তাপ পড়লে সেখানে তিনটি ঘটনা ঘটে। কিছু কিছু বিকির্ণ শক্তি ওই বস্তুটা শোষণ করে। কিছু পরিমাণ বিকির্ণ শক্তি বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়। কিছু শক্তি ওই বস্তু ভেদ করে চলে যায় ঠিক যেমনটা ঘটে আলোর ক্ষেত্রে। অনেকে হয়তো বলবেন, বস্তু স্বচ্ছ না হলে আলো ভেদ করে যায় কীভাবে? দৃশ্যমান আলো অস্বচ্ছ বস্তু ভেদ করতে পারে না। রেডিও তরঙ্গ, এক্স রে, গামা রে এদের কিন্তু ভেদনক্ষমতা যথেষ্ট। আসলে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে সে অস্বচ্ছ বস্তু ভেদ করতে পারবে কি পারবে না। বিকির্ণ তাপ বা শক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু এমন কোনো বস্তু আছে যে আলোকে পুরোপুরি গ্রাস করে নিতে পারে?
সবরকম আলো, বিকির্ণ তাপ শক্তি সে বস্তু শোষণ করবে, এমন একটা বস্তুর কথা ভাবলেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু বাস্তবে এমন বস্তু মিলল না। দেখা যায় কালো রংয়ের বস্তু সবচেয়ে বেশি আলো তাপ শোষণ করতে পারে। কেন পারে? আসলে কালো কোনো রং নয়। কালো মানে রংয়ের অভাব। কোনো বস্তুর ওপর আলো পড়লে সেই বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয় কিছু আলো। বাকি আলো শোষণ করে নেয় সেই বস্তু। কিন্তু দৃশ্যমান আলোক বর্ণালির সর রংয়ের আলো সব বস্তু শোষণ করতে পারে না। গাছের পাতা সূর্যের সাদা আলো থেকে সবুজ বাদে সবকটা রংয়ের আলো শোষণ করে নেয়। কিন্তু সবুজ আলো শোষণ করতে পারে না। সবুজ আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে বলেই গাছের পাতা আমরা সবুজ দেখি। তেমনি শরীরের রক্ত লাল বাদে সব আলো শোষণ করে নেয় বলে রক্তের রং লাল।
এতো গেল দৃশ্যমান বর্ণালীর কথা। কিন্তু সে যেসব আলো দেখতে পাই না সেগুলো যদি প্রতিফলিত বা শোষিত হয় তখন কী হয়?
বস্তুর রংয়ের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান আলো মূল ভূমিকা পালন করে। তাই অদৃশ্য আলো যেমন রেডিও তরঙ্গ, গামা রে ইত্যাদি বস্তুর স্বাভাবিক রংয়ের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। কিন্তু ওসব আলো নাইট ভিশন চশমা দিয়ে অন্ধকারে দেখতে কাজে লাগে। শরীরের ভেতরের রোগ-ব্যাধির ছবি তুলতেও অদৃশ্য আলোর ভূমিকা বিরাট। কিন্তু সেসব আমাদের আলোচনা বিষয় নয়।
আবার ফিরে আসি কালো বস্তুতে। কালো বস্তু মূলত দৃশ্যমান আলোর প্রায় সবটুকুই শোষণ করে নেয়। তাই কোনো রং আমরা দেখতে পারি না। আর রংয়ের অভাবের কারণেই সেই বস্তুটার রং কালো। এখানে কিন্তু একটা ঘাপলা আছে। কোনো বিজ্ঞ বন্ধু হয়তো প্রশ্ন করে বসতে পারেন, কালো বস্তু আলো প্রতিফলন যদি না-ই করবে, তা হলে তাকে আমরা দেখি কী করে?
হুম, প্রশ্ন বটে একখান। আগেই বলেছি, কালো বস্তু দৃশ্যমান আলোর ‘প্রায় সবটুকুই’ শোষণ করে নেয়। ‘প্রায় সবটুকু কিন্তু ‘সবটুকু’ নয়।
কিন্তু বিজ্ঞানীদের তো ‘প্রায়ই’-এ মন ভর না। তারা একটা আদর্শ কালো বস্তু চাইলেন। যে বস্তু সব আলো শুষে নেবে। দৃশ্যমান অদৃশ্যমান সব। শুষে নেবে বিকির্ণ শক্তি ও তাপ। কিছু ফিরিয়ে দেবে না। কিন্তু এমন কালো বস্তুর সন্ধান মিলল না। সুতরাং কল্পিতই থেকে গেলো আদর্শ কালো বস্তু। বিজ্ঞানীরা যার নাম দিলেন ‘ব্ল্যাক বডি’। ভালো বাংলায় যাকে বলে আদর্শ কৃষ্ণবস্তু। ‘কৃষ্ণবস্তু’ কথাটা একটা উচ্চমার্গীয়। কিন্তু শুনতে ভাল লাগে, তাই আমরা আদর্শ কালোবস্তু বা শুধু ‘কালো বস্তু’ না বলে ‘কৃষ্ণবস্তু’ লিখব।
গুস্তাভ কার্শফ image source : media.springernature.com
পৃথিবীতে যত কালো বস্তু আছে আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর কাছাকাছি হলো কালো ভেলভেট। কিন্তু কালো ভেলভেটও আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু নয়। সেও কিছুটা আলো ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানে ‘আদর্শ’ বিষয়টা বহু পুরোনো। প্রায় সবক্ষেত্রেই, কোনো না কোনো বস্তুকে বা মানকে আদর্শ ধরে নেওয়া হয়। যেমন, আদর্শ তাপমাত্রা, আদর্শ চাপ। মাপজোখের ক্ষেত্রে পানিকে আদর্শ বস্তু ধরে অনেক হিসাব-নিকাশ কষতে হয়। বিবিকিরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেও আদর্শ কৃষ্ণবস্তু অপরিহার্য হয়ে উঠল। তখন বিজ্ঞানীরা ভাবলেন তারা পরীক্ষাগারেই কৃষ্ণবস্তু তৈরি করবেন।
আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর প্রথম ধারণা দেন বিজ্ঞানী গুস্তভ কার্শফ ১৮৬০ সালে। ১৮৯৫ সাল নাগাদ কৃষ্ণ বস্তু তৈরি হয়। এরমধ্যে ফেরি আর ভিয়েনের কৃষ্ণবস্তু বেশি পরিচিত। ফেরির কৃষ্ণবস্তুটা দুই দেয়ালের ধাতব গোলক দিয়ে তৈরি। গোলকটির দুই দেয়ালের মধ্যে বায়ুশূন্য ফাঁপা। কেন্দ্রভাগও ফাঁপা। বাইরের দেয়ালের বাইরের পৃষ্ঠ নিকেল দিয়ে পালিশ করা। ভেতরের দেয়ালের ভেতরের পৃষ্ঠে থাকে ভুষা বালির প্রলেপ। গোলকের একদিকে ছোট্ট একটা ছিদ্র থাকে। ছিদ্রের ঠিক উল্টো দিকে দেয়ালে আছে পিরামিডের মতো একটা তল।
ছিদ্র দিয়ে ঢোকা বিকির্ণ তাপ শক্তি সেই পিরামিড তলে গিয়ে পড়ে। পিরামিড তলের কারণে আলো আর সোজা বিপরীত পথে ফিরে আসতে পারে না। বিকির্ণ তাপশক্তি সেই তলে প্রতিফলিত ও শোষিত হয়। প্রতিফলিত রশ্মি গিয়ে আবার দেয়ালের আরেক স্থানে পড়ে। সেখানেও বিকির্ণ তাপশক্তি শোষিত ও প্রতিফলিত হয়। সেখান প্রতিফলিত রশ্মি আবার দেয়ালের আরেক জায়গায় পড়ে। এভাবে বার বার প্রতিফলিত হবার ফলে সকল স্থানে কিছু না কিছু শক্তি শোষিত হয়। বিকিরণের শক্তি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। একসময় পুরো বিকির্ণ শক্তিই দেওয়ালের বিভিন্ন স্থানে শোষিত হয়ে পুরোপুরি শক্তি হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ সবটুকু শক্তি শোষণ করে নেয়, সেই কৃষ্ণবস্তু।
ভীনের কৃষ্ণবস্তু গোলাকার নয়, আয়তাকার। তবে কার্যপদ্ধতি একই। যাইহোক, এবার ফিরে আসার যাক কৃষ্ণবস্তুর কারিশমায়।
কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের ওপর প্রথম একটা সূত্রটাও দিয়েছিলেন জার্মান পদার্থবিদ গুস্তভ কার্শফ। তিনি বলেন, কোনো বস্তুর তাপমাত্রা যদি পরিবেশের তাপমাত্রার চেয়ে কম হয়, সেই বস্তু নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘের বিকিরণ শোষণ করে নিজের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করবে। আবার কোনো বস্তুর তাপমাত্রা যদি পরিবেশের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয় তবে সেই বস্তু নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘের আলো বিকিরণ করে তরঙ্গদৈর্ঘ হ্রাস করবে।
তখনাকার বিজ্ঞানীরা জানতেন, কোনো বস্তুকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করতে থাকলে তার বিকিরণের পরিমাণটাও বাড়তে থাকে। সাথে সাথে বিকিরণের রংয়েরও পরিবর্তন ঘটে। একটা লোহাকে উত্তপ্ত করলে বিকিরণের ব্যপারটা স্বচক্ষে দেখা সম্ভব।
লোহাকে উতপ্ত করলে প্রথমে লোহা শুধু গরমই হবে। রংয়ের কোনো পরিবর্তন হবে না। কিন্তু আরও উতপ্ত করলে তখন হালকা লাল রংয়ের আভা দেখা দেবে। তারমানে বিকিরণের রং পরিবর্তনের বিষয়টা তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এখন যদি তাপমমাত্রা আরও বৃদ্ধি করা যায়? লোহার রং তখন গাঢ় লাল হয়ে উঠবে। তাপমাত্রা ৫০০ ডিগ্রির ওপরে উঠলেই কেবল লোহার রং লাল হবে। তাপাত্রা ৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠলে গরম লোহা তখন ছড়াবে উজ্বল হলুদ দ্যূতি। তারমানে বিকিরণের তৈরঙ্গদৈর্ঘ্য কমছে। কারণ লালের চেয়ে হলুদ রংয়েল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম। লাল থেকে কিন্তু সরাসরি লোহার রং একবারেই হলুদ হয় না। ৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরে তাপমাত্রা ধীরে বাড়াতে একসময় কমলা রং দেখা যাবে।
৮০০ ডিগ্রি থেকে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকলে নিউটনের বর্ণালী বেনিআসহকলার বাকি রংগুলোও একে একে দেখা যাবে। সবুজ, আসমানী, নীল আর বেগুনি। তারপর লোহার তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে একসময় হবে সূর্য পৃষ্ঠের সমান। তখন সেই উতপ্ত লোহার রং উজ্জ্বল সাদা দেখাবে।
কোনো বস্তুর তাপমাত্রা কতটা বাড়ালে কতটুকু কতটুকু তাপ কিংবা আলোকরশ্মি বিকিরণ করবে সেটা তুলনা করার জন্য একটা আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর দরকার হয়ে পড়ে।
আদর্শ কৃষ্ণবস্তু তৈরি হলো। বিজ্ঞানীরা সেটা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। লোহার টুকরোর মতো কৃষ্ণবস্তুকেও উতপ্ত করা হলো। ধরা যাক, ৭০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কৃষ্ণবস্তুকে উৎপত্ত করা হয়েছে। ওই তাপমাত্রায় কৃষ্ণবস্তুটি যে তাপমাত্রা ও আলোকরশ্মি বিকিরণ করবে তা অন্য যেকোনো বস্তুর চেয়ে বেশি। কারণ কোনো বস্তুই কৃষ্ণবস্তুর মতো শতভাভাগ তাপমাত্রা শোষণ করতে পারে না। তাই কোনো বস্তুর বিকির্ণ তাপ ও আলো কৃষ্ণবস্তুর সমান হবে না।
জোসেফ স্টিফেন image source : Josef Stefan - Wikipedia
কৃষ্ণবস্তু তো পাওয়া গেল, এবার এর বিকিরণের জন্য একটা সমীকরণ দরকার। বিকিরণ সম্পর্কিত প্রথম সমীকরণটা দাঁড় করালেন দুই অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী জোসেফ স্টিফেন ও লুডভিগ বোলৎজম্যান। সেটা হলো,
এই সূত্রের সার কথা হলো কৃষ্ণবস্তু থেকে তাপ ও আলোর আকারে বিকির্ণ মোট শক্তি E-এর পরিমাণ বস্তুর পরম তাপমাত্রা T-এর সমানুপাতিক। সমীকরণে একটা ধ্রুবক K ব্যবহার করা হয়েছে, এটা বোলৎজম্যান ধ্রুবক।
পরম তাপমাত্র কি? একটা প্রশ্ন। সেটা জানতে হলে জানতে হবে পরমশূন্য তাপমাত্রা কী? প্রকৃতিতে এমন একটা তাপমাত্রা আছে যার এর নিচে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা নামতে পারে না। সেই তাপমাত্রায় সকল গ্যাসের আয়তন গাণিতিকভাবে শূন্য। কেলভিন স্কেলে এই তামাত্রার মান শূন্য ডিগ্রি কেলিভিন। সেলসিয়াস স্কেলে সেই তাপমাত্রার মান ২৭৩.১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিট্রিশ বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন পরমশূন্য পরম তাপমাত্রার ধারণা দেন। শুন্য ডিগ্রি কেলভিন -২৭৩ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রার ওপরে যেকোনো তাপমাত্রাই বস্তুর পরম তাপমাত্রা হতে পারে।

ধরা যাক, কৃষ্ণবস্তুর পরম তাপমাত্রা দ্বিগুণ করা হলো। তাহলে সমীকরণ অনুসারে বিকির্ণ শক্তির পরিমাণ বাড়বে ১৬ (২x২x২x২) গুণ। পরম তাপমাত্রা ৩ গুণ বাড়ালে বিকির্ণ শক্তির পরিমাণ বাড়বে ৮১ গুণ!
১৮৯৩ সালে জার্মান পদার্থবিদ উইলহেম ভীন কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের আরেকটি সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্রে ভীন বলেন, বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষ্ণবস্তু যে পরিমাণ বিকিরণ নিঃসরণ করে তার সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্রমেই কমতে থাকে। ধরা যাক, সাধারণ তাপমাত্রায একটা কৃষ্ণবস্তু একই সাথে অনেকগুলো আলোকরশ্মি বিকিরণ করে। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও সবচেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘের বিকিরণ থাকে সবচেয়ে বেশি।
ধরা যাক, একটা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘের বিকিরণ হলো বেতার তরঙ্গ। কৃষ্ণবস্তুর তাপমাত্রা বাড়ানো হোক এবার । তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে রেডিও তরঙ্গের বিকিরণ কমতে থাকতে থাকবে। একসময় দেখা যায় কৃষ্ণবস্তু লাল আলো বিকিরণ করতে শুরু করেছে। তখন বিকিরণে বর্ণালীর সবচেয়ে উজ্বল লং আলো হবে লাল। সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্যও তখন লালের। এরপর কৃষ্ণবস্তুর সবচেয়ে উজ্জ্বল রং হবে পর্যায়ক্রমে কমলা, হলুদ, সবুজ, আসমানী, নীল, বেগুনি ইত্যাদি। অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমতে থাকে। কমতে কমতে নিউটনের বর্ণালী অনুযায়ী লাল থেকে বেগুনির দিকে যাবে। ভীনের সূত্র বলে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় সবচেয়ে বড় উজ্জ্বল বিকিরণ হওয়ার কথা বেগুনি রংয়ের। অর্থাৎ কৃষ্ণবস্তুটির চেহারা তখন বেগুনি রংয়ের হওয়া উচিৎ। কিন্তু পরীক্ষা করে ফল পাওয়া গেল অন্যরকম। বেগুনি আলোতে আসার পরও কুষ্ণবস্তুতে তাপমাত্রা বাড়ানো যায়। এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় বস্তুটি উজ্জ্বল সাদা রং বিকিরণ করে।
তাহলে কি ভীনের সূত্র ভুল? বিজ্ঞানীরা বললেন, না ভুল নয়। সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় বেগুনি রংয়ের বিকিরণের পাশাপাশি অন্য রংয়ের বিকিরণও কমবেশি থাকে। তাই সব মিলেমিশে সাদা রং ধারণ করে কৃষ্ণবস্তু।
তাই যদি হয়, এরপরেও কি তাপমাত্রা বাড়ানো সম্ভব? অঙ্ক বলে সম্ভব। আর এখানেই গোলবেঁধে যায়। গণিতিক আর পরীক্ষালব্ধ ফলে বিরোধ দেখা যায়। ভীনের সূত্রে সমাধান মেলে না। ১৮৯০ দশকের শেষদিকে দুই বৃটিশ পদার্থবিদ লর্ড রেলে আর জেমস জিনস কৃষ্ণ বস্তুর নতুন একটি সূত্র দিলেন।
আমরা এর আগে স্টিফেন-বোলৎসম্যান এবং ভীনের দুটো সূত্র দেখলাম। দুটো দুইভাবে কুষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু একই সাথে দুই ধরনের ব্যাখ্যা কোনো সূত্রই করতে পারে না। তারমানে স্টিফেন-বোলৎসম্যান সূত্র কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের সবগুলো বৈশিষ্ট্যের অর্ধেক ব্যাখ্যা করতে পারে। বাকি অর্ধেক ব্যাখ্যা করতে হলে ভীনের দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান সবসময় ঐক্যবদ্ধ সূত্র দাবি করে। যেমনটি করেছিলেন নিউটন। নিউটন তাঁর সূত্রে দেখিয়েছিলেন যে কারণে একটা আপেল গাছ থেকে পড়ে সেই একই কারণে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে। ম্যাক্সওয়েল দেখিয়েছিলেন যে বলের কারণে একট চুম্বক লোহার টুকরোকে আকর্ষণ করে, সেই একই বলের কারণে বৈদ্যুতিক পাখা ঘোরো। আবার সেই একই বল লুকিয়ে থাকে আলোর ভেতরেও।
কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের ক্ষেত্রেও এমন একটা ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের দরকার হয়ে পড়ল। আর সে চেষ্টাই করলেন রেলে-জিনস। রেলে-জিনস তাদের সূত্রে বললেন, কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের তীব্রতা তাদের পরমশূন্য তাপমাত্রার সমানুপাতিক এবং তরঙ্গদৈর্ঘের ব্যস্তানুপাতিক। তবে এই সূত্রটা সেভাবে সফলতার মুখ দেখেনি। ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘের তরঙ্গের ব্যাখ্যা দিতে পারলেও বৃহৎ তরঙ্গদৈর্ঘের বিকিরণের ব্যাখ্যা দিতে পারে না রেলে-জিনস তত্ত্ব। এই তত্ত্ব থেকে দেখা যায়, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্রমেই কমতে থাকে।
কমতে কমতে তরঙ্গদৈর্ঘ কত ছোট হবে? রেলে-জিনস তত্ত্ব বলে সেটা অসীমেও চলে যেতে পারে। তার মানে, তাপমাত্রা যখন সর্বোচ্চ তখন এর তরঙ্গদৈর্ঘ অসীম মানের ক্ষুদ্র হবে। কিন্তু আলো কিংবা বিকিরণের তরঙ্গদের্ঘ্য কমতে কতে কি অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র হওয়া সম্ভব? সম্ভব নয়। বড়জোর শূন্য হতে পারে। সত্যি বলতে কি, বাস্তবে কোনও তরঙ্গেরই তরঙ্গদৈর্ঘ্য শূন্য হওয়া সম্ভব নয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্য শূন্য হলে তরঙ্গ তত্ত্বই ভেঙে পড়ে। তরঙ্গ হতে হলে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য শূন্য হলে চলবে না। নূন্যতম মান থাকতে হবে। সেই মানটা কত, সেটা পরের অধ্যায়েই আমরা জানতে পারব।
আবার ফিরে যায় রেলে-জিনস তত্ত্বে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য শূন্য আর অসীমের কথা বাদই দিলাম। রেলে-জিনস তত্ত্ব যদি আংশিক ঠিক হয় তবে ‘বেগুনি বিপর্যয়’ ঘটার কথা। সেটা আবার কেমন। রেলে-জিনসের সূত্রানুযায়ী, তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমতে থাকবে। কমতে একসময় বেগুনি আলোতে পৌঁছুবে। তারপর আরও কমলে কৃষ্ণবস্তুর রং অতিবেগুনিতে পৌঁছে যাবে। তারপর আরও ছোট তরঙ্গদৈর্ঘের আলো বিকিরণ করবে। এই যে বেগুনি বিকিরণের পরেও তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমতে থাকে, একেই বিজ্ঞানীরা ‘বেগুনি বিপর্যয়’ নাম দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে বেগুনি বিপর্যয়ের কোনো হদিস মেলেনি।
তাহলে অঙ্ক একরকম বলছে, পরীক্ষার ফল বলছে আরেকরকম। পর্দাবিজ্ঞানের কোনো পরীক্ষার ফল যদি অঙ্ক দিয়ে না মেলানো যায় তবে সেটার কোনো মূল্যই থাকনে। গণিতের ছাঁচে তাকে ফেলতেই হবে। কিন্তু কোনোভাবেই কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণকে পরিপূর্ণ একটা গাণিতিক কাঠামোত দাঁড় করানো গেল না। নিউটনের বলবিদ্যা তো এক্ষেত্রে একেবারেই অচলই। ব্যর্থ ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎগতিবিজ্ঞানও।
তাহলে উপায়? কে দেবে এর সমাধান। তখনই দৃশ্যপটে হাজির পদার্থবিজ্ঞানের আরেক বিপ্লবী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক।
প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব
রেলে-জিনসের সূত্রটা আবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ওই সূত্রে বলা হয়েছে. তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে কৃষ্ণবস্তুর সর্বোচ্চ বিকিরণের তীব্রতা বাড়ে। ভীনের ভাষায় তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে সর্বোচ্চ বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমতে থাকে। অর্থাৎ বিকিরণের কম্পাঙ্ক বাড়তে থাকে। কম্পাঙ্ক বাড়তে অসীমে চলে যায়।
এখন হিসাবটা যদি উল্টোভাবে করা হয়, তাহলে দেখা যাবে বিকির্ণ শক্তি বাড়ার সাথে সাথে বস্তুর তাপমাত্রাও বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে তা অসীমের দিকে যেতে থাকে। তাই যদি হয় মহাবিশ্ব নরককু-ে পরিণত হবে।
তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমতে কমতে শূন্যের দিকে চলে যাবে, এটা সত্যি সত্যি দুশ্চিন্তার বিষয়। প্ল্যাঙ্ক বিষয়টা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। ভাবতে শুরু করলেন একই সাথে ভীন ও র্যালে-জিনসের সূত্রের সমাধান কীভাবে করা যায়, সেটা নিয়েও। ভাবলেন, এমন একটা সমাধান দরকার যেটা বিকিরণের শক্তিকে লাগাম পরাবে। এমন একটা সমীকরণ তৈরি করতে হবে হবে, যেটা বলবে বিকিরণের শক্তি ঘনত্বের একটা মান থকবে। বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমতে কমতে শূন্যে পৌঁছানের যে প্রবণতা গণিতের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সেটাতেও লাগাম পরাবে নতুন এই সূত্র। সেই সূত্র বলে দেবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমার একটা সীমা থাকবে। একটা নির্দিষ্ট সীমার পর বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর কমবে না। তেমনি বিকিরণের শক্তির একটা নূন্যতম মান নির্ণয় করা যাবে সেই সমীকরণ দিয়ে।
আগেই বলা হয়েছে, তাপগতিবিদ্যা নিয়ে প্ল্যাঙ্কের ব্যাপক আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহ থেকেই তিনি সেসময় পর্যন্ত তাপগতিবিদ্যার যতটুক জ্ঞান আবিষ্কার হয়েছে প্রায় সবটুকুই আহরণ করে ফেলেন। পদার্থবিজ্ঞানের অন্য শাখাতেও তাঁর জ্ঞান অপরিসীম। তুখোড় পারদর্শিতা গণিতেও।
প্ল্যাঙ্ক হিসাব কষে দেখলেন, বিকিরণের শক্তির একটা নির্দিষ্ট মান আছে। ওই মানের নিচে বিকিরণের শক্তি নামতে পারে না কখনও। তাই যদি হয়, বিকিরণের শক্তির একটা সর্বনিন্ম মান থাকবে। ওই মানের নিচে বিকিরণের শক্তি নামতে পারবে না কখনো। একেক রংয়ের বিকিরণের জন্য বিকিরণের এই সর্বনিন্ম মানটাও আলাদা আলাদা হবে। সেই সর্বনিন্ম মানটাই হবে বিকিরণ শক্তির সর্বনিন্ম একক। একটা পদার্থ যেমন ভাঙতে ভাঙতে পরমাণু পাওয়া যায়, পরমাণুই বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক। যেমন এক টুকরো একটা লোহা নিয়ে দুজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা করছেন। একজন বললেন তাতে ১ কোটি পরমাণু আছে। অন্য বিজ্ঞানী বললেন, না, ভুল। লোহার টুকরোতে ১ কোটির বেশি পরমাণু আছে। কতগুলো বেশি? ১০১ টা। লোহার সেই টুকরোই ১ কোটিই থাক আর ১০১ টা বেশিই থাক সব কিন্তু ১ এর সরল গুণিতক। অর্থাৎ পরমাণু সংখ্যা কখনো ভগ্নাংশতে যাবে না। যাওয়া সম্ভব নয়। ক্ষুদ্রতম এককগুলো আসলে এমনই হয়। কোনো বস্তুতে তাদের পরিমাণ সবসময় পূর্ণসংখ্যা দিয়েই গণনা করা হয়। অর্ধেক কিংবা একা বা দুই তৃতীয়াংশ ইত্যাদির জায়গা নেই।
প্ল্যাঙ্ক বললেন বিকিরণের এমন একক আছে। সেই এককটা হলো বিকির্ণ শক্তির। শক্তির একটা সর্বনি¤œ মান থাকবে। একটা নির্দিষ্ট বিকিরণের জন্য শক্তির সর্বনিন্ম মানটাও নির্দিষ্ট।
প্ল্যাঙ্কের এই কথা মেনে নিলে একটা সমস্যা দেখা দেয়। আমরা আলোকে রশ্মি হিসেবে দেখি। সেটা হলো লম্বা আলোর স্রোত। একেবারে নিরবচ্ছিন্ন স্রোত যাকে বলে। উৎস থেকে অনবরত সেই স্রোত নির্গত হয়, নিরবিচ্ছিন্নভাবে। আলোর শক্তির নির্দিষ্ট যদি একটা মান থাকে তখন এই নিরবিচ্ছিন্ন কথাটা আর বলা যায় না। একটা রাইস মিলের কথাই ধরা যাক। মিলের হলার থেকে যখন চাল গড়িয়ে পড়ে তখন প্রতিটা চালকে আলাদাভাবে বোঝা যায় না। তার বদলে চালের একটা লম্বা ধারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিচে পড়তে থাকে। নিরবিচ্ছিন্ন দেখি বলেই কি চালের ধারা নিরবিচ্ছিন্ন?
মোটেও নয়। আর সেটা প্রমাণ করার জন্য বেশিদূর যেতে হয় না। চাল মাটিতে পড়ার পর থেমে যায়। স্তূপ জমে চালের। সেই স্তূপ থেকে খুব সহজেই প্রতিটা চালকে আলাদা আলাদা করে বোঝা যায়। আসলে চালের ধারাকে নিরবিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছিল তার গতির কারণে। একটা একটা আলাদা চাল নিয়ে চালের ধারা তৈরি হয়।
প্ল্যাঙ্ক বললেন, বিকিরণের যে সর্বনিন্ম শক্তি আসলে সেটাকে শক্তির একটা প্যাকেট বলা যেতে পারে। এই প্যাকেটই হলো বিকিরণের ক্ষুদ্রতম একক। উৎস থেকে বিকিরণ বা আলো নির্গত হয় প্যাকেট আকারেই। কিন্তু প্রচন্ড গতিতে একের পর এক প্যাকেট নির্গত হয়। তাই প্রতিটা প্যাকেট আলাদাভাবে আমাদের মস্তিষ্ক অনুধাবন করতে পারে না। সত্যি বলতে কি আমাদের চোখ ও মস্তিষ্ক প্রায়ই আমাদের বিভ্রান্ত করে। চালের ধারাটাও তেমন এক বিভ্রান্তি।
ঝর্নার পানির ধারাও নিরবিচ্ছিন্ন মনে হয়। ট্যাপকল থেকে যে পানি পড়ে সেটাও মনে হয় নিরবিচ্ছিন্ন। ট্যাপকলের পরীক্ষাটা নিজেই করতে পারেন। ট্যাপকলের চাবি ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে পানি ঝরতে থাকে অঝর ধারায়। এবার ট্যাপকলের চাবি ধীরে ধীরে আটতে থাকুন। প্রথম দিকে পানির ধারা থাকবে ঠিকই, তবে গতি কমে যাবে। এরপর আর আটুন। পানি একসময় ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে থাকবে। তবে ফোঁটাগুলো একটার পর একটা বেশ দ্রুত গতিতে পড়বে। এরপর আরো ধীরে চাবি আটুন। একটা ফোঁটার পর আরেকটা ফোঁটা আসতে বেশ সময় লাগবে। তবে ফোঁটা একটা পর একটা ধীরেই আসুক আর দ্রুতই আসুক, ফোঁটার আকার কিন্তু সবগুলো সমান। তারমানে এই ফোঁটাই ট্যাপের পানির সর্বনি¤œ গুচ্ছ। এরপর চাবি আরও আটলে একটার পর একটা ফোঁটা আসবে আরও দেরিতে। সেটা ১ সেকেন্ড পর পরও হতে পারে। এরপর চাবি আরও আঁটলে পানির পড়া একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।
আসলে একই আকারে ফোঁটা সবসময় পড়ে। কিন্তু পানির গতি যখন বেশি থাকে তখন ফোঁটাগুলো আলাদাভাবে বোঝা যায় না। মনে হয় নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় পানি পড়ছে। আসলে সবসময় পানি একটা সর্বনিন্ম গুচ্ছ বা প্যাকেট আকারেই ঝরছে। সেই গুচ্ছটা হলো পানির ফোঁটা। আমাদের মস্তিষ্কের সীমাবদ্ধতার কারণে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না।
কেন আমাদের মস্তিষ্কের এই সীমাবদ্ধতা? আলোকবিজ্ঞানে এই প্রশ্নটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কোয়ান্টামে সেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
আজকাল সিনেমা তৈরি হয় ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে। আগে ফিল্ম ক্যামেরা ব্যবহার হতো। ফিল্ম ক্যামেরায় যখন কোনো দৃশ্য ধারণ করা হয় তখন কিন্তু একের পর স্থির আলোকচিত্রই ধারণ করে ক্যামেরা। সেটা সিনেমার রিল দেখার অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তারা ভালো বুঝবেন। আমি নিজে দেখেছি। সিনেমার রিল থেকে ফিল্মের একটা লম্বা ফিতে হাতে নিয়ে দেখেছি। পাশাপাশি অনেকগুলো ছবি একই মনে হয়। কিন্তু একটা ফিল্মের পাশ থেকে যদি ১০-১২ ফিল্ম কেটে বাদ দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু পার্থক্যটা বেশ বোঝা যায়। ১ম ফিল্মের সাথে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ফিল্মের কোনো পার্থক্যই ধরা যায় না। তেমনি ৮ম এর সাথে ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ফিল্মের তেমন পার্থক্য চোখে পড়ে না। কিন্তু ১ম আর ১২তম ফিল্মটা পাশাপাশি রাখুন বেশ পার্থক্য চোখে পড়বে।
এক সেকেন্ডের একটা দৃশ্যে মেটামুটি ২৫টি স্থির ফিল্ম হলেই কাজ চলে যায়। যেকোনো দৃশ্য মানুষের মস্তিষ্কে ০.১ সেকেন্ড পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এই সময়ের মধ্যে যদি একাধিক দৃশ্য এসে যায়, তবে দুটো দৃশ্যের পার্থক্য করতে পারে না মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের এই দুর্বলতাটাই কাজে লাগানো হয় সিনেমায়। সিনেমার প্রজেক্টরে একটা অতি তীব্র সাদা আলো জ্বালানো হয়। আলোটা স্থির। সেই আলোর ফোকাস গিয়ে পড়ে সিনেমার পর্দায়। চারকোণা ফোকাস। আলোক উৎসের ঠিক ওপরে আর নিচেয় দুটো গোল রিল-হুইল বসানো থাকে। ওপরের রিলে ফিল্ম জড়ানো থাকে। আর নিচের রিলটা ফাঁকা। ওপরের রিল-হুইলে থেকে ফিল্মের ফিতে টেনে এনে নিচের হুইলের সাথে লাগানো হয়। এরপর মোটরের সাহায্যে হুইল দুটো ঘোরানো দ্রুত গতিতে। হুইল দুটোর গতি এমন হয় যেন এক সেকেন্ডে ২৫-৩০টা ফিল্ম আলোক উৎসের সামনে দিয়ে চলে যায়। ওপরের হুইল ক্রমেই খালি হয় আর নিচের হুইল হয় পূর্ণ। আলোক উৎসের সামনে দিয়ে স্বচ্ছ রঙিন ফিল্ম অনবরত চলে যায়। ফলে পর্দায় যে আলোটা পড়ে সেটা আর বাধাহীন থাকতে পারে না। স্বচ্ছ রঙিন ফিল্ম ভেদ করে গিয়ে আলো পড়ে পর্দায়। ফিল্মের ছবিগুলোই তখন একেরপর এক পর্দায় ভেসে ওঠে।
এক সেকেন্ডে যদি ২৫ টা ফিল্ম যায় আলোর সামনে দিয়ে, তবে প্রতিটা ফিল্মের জন্য সময় বরাদ্দ ১/২৫ বা ০.০৪ সেকেন্ড। ০.১ সেকেন্ডের চেয়ে অনেক ছোট এই সময়টা। ০.১ সেকেন্ড পার হতে হতে ২.৫টা ফিল্ম চলে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা নেই দুটো ছবি আলাদা করে বোঝার। মস্তিষ্ক তখন অনুভব করে চলন্ত ছবির দৃশ্য।
কিন্তু প্রজেক্টর থামিয়ে দিলেই প্রতিটা দৃশ্য আলাদা আলাদা করে বোঝা যায়। এখানে ফিল্মটাই সিনেমার সর্বনিন্ম একক। শুধু দ্রুত গতির কারণে সিনেমাকে নিরবিচ্ছন্ন চলচ্চিত্র মনে হয়।
একই কথা প্রযোজ্য আধুনিক ডিজিটাল সিনেমা বা ভিডিওগ্রাফির ক্ষেত্রেও। এখন আর ফিল্মের দরকার হয়না- একথা ঠিক। তাই বলে ডিজিটাল সিনেমা বা ভিডিও নিরবিচ্ছিন্ন চলন্ত ছবি নয়। ফিল্মের বদলে এখন ডিজিটাল ক্যামেরার মেমরিতে সেভ হয় ডিজিটাল স্থির চিত্র। এগুলোর প্রতিটাকে একেকটা ফ্রেম বলে। যারা ভিডিও এডিটিং করতে পারেন, তারা বিষয়টি আরও ভালো করে বুঝবেন। এক সেকেন্ডে ভিডিও প্লেয়ারে ২০-৩০টা ছবি অতিক্রম করা হয়। আমাদের মস্তিষ্ক সেটা দেখে ভাবে নিরবিচ্ছিন্ন চলচ্চিত্রই দেখছে। সময় যত যাচ্ছে আধুনিক হচ্ছে ডিজিটাল ভিডিওগ্রাফির মান। প্রতি সেকেন্ডে ফ্রেমের সংখ্যাও বাড়ছে। ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। কিন্তু ভিডিওগ্রাফিতে ফ্রেমের সংখ্যা কখনো অসীম হবে না। সেটা সম্ভবও নয়। তাই যত আধুনিকই হোক ভিডিওগ্রাফি কখনো নিরবিচ্ছিন্ন চলচ্চিত্র হবে না।
এত উদাহরণে অনেকে বিরক্ত হতে পারেন। তবে ধৈর্য ধরে উদাহরণগুলো পড়ে এলে লাভ আপনারই। আলোর কোয়ন্টাম তত্ত্বটা বোঝা একেবারে জলবৎ তরলং হবে।
প্ল্যাঙ্ক বললেন, বিকিরণের সময় যে শক্তি নির্গত হয় তাও নিরবিচ্ছিন্ন নয়। আলো বা বিকিরণ শক্তি নির্গত হয় গুচ্ছ বা প্যাকেট আকারে। অনেকটা রাইস মিলের প্রতিটা আলাদা চালের মতো, ট্যাপ থেকে পড়া পানির ফোঁটার মতো কিংবা সিনেমার ফিল্ম ও ভিডিওগ্রাফির ফ্রেমের মতো। বিকরণের এই প্যাকেট একটা নির্দিষ্ট শক্তি নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে উৎস থেকে নির্গত হয়। তবে খুব দ্রুত একের পর এক প্যাকেট নির্গত হয় বলে আমরা আলোর একটা নিরবিচ্ছিন্ন ধারা দেখি। যাকে আমরা বলি আলোক রশ্মি।
প্ল্যাঙ্ক শক্তির এই প্যাকেটের নাম দিলেন কোয়ান্টাম। অর্থাৎ কোয়ন্টামই হলো বিকিরণ শক্তির ক্ষুদ্রতম একক। আগেই বলেছি ভিন্ন ভিন্ন বিকিরণের জন্য এই প্যাকেটের শক্তিও ভিন্ন হয়। বিভিন্ন বিকিরণের প্যাকেটের শক্তি নির্ণয়ের জন্য একটা সমীকরণ দাঁড় করালেন। সমীকরণটা হলো-
সমীকরণের মূল বক্তব্য হলো, যেকোনো বিকিরণের কোয়ান্টাম শক্তি = E, তার কম্পাঙ্ক v, এর সমানুপাতিক। অর্থাৎ কম্পাঙ্ক যত বড় হয় কোয়ান্টামের শক্তি তত বাড়ে। সেই বাড়র পরীমাণটা কী হারে সেটাও তো জানা দরকর। প্ল্যাঙ্ক এজন্য একটা ধ্রুবকের জন্ম দিলেন। সেটা হলো
এর মান
এখন সমীকরণের চেহারাটা দাঁড়াবে এমন:
এই সমীকরণ থেকে স্পষ্ট একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। যেকোনো বিকিরণের কোয়ন্টাম শক্তি তার কম্পাঙ্ক ও প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের গুণফলের সমান। কম্পাঙ্ক বাড়লে কোয়ান্টামের শক্তিও বাড়ে। লাল আলোর বিকিরণের চেয়ে বেগুনি আলোর বিকিরণের কম্পাঙ্ক বেশি। তাই বেগুনি আলোর কোয়ান্টাম শক্তিও লাল আলোর চেয়ে বেশি।
এখন অনেকেই হয়তো বলবেন কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ আলোচনার সময় আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছি, এখানে সেটা গেল কোথায়?
খুব সহজেই প্ল্যাঙ্কের সূত্রে আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিয়ে আসতে পারি। আমরা জনি আলো বা বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম্পাঙ্ক পরস্পরের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ বিকিরণের কম্পাঙ্ক বাড়লে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে। কমাঙ্ক ও তরঙ্গ দৈর্ঘের সম্পর্কটা এমন-
=বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য
এটাই এখন প্ল্যাঙ্কের সমীকরণে বসালে পাওয়া যাবে-
এই সমীকরণ থেকে থেকে স্পষ্ট, বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়লে বিকিরণের শক্তি কমতে থাকবে। শক্তি কমার হার হবে প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবকের সরলগুণিতকের সমান।
নিউটন বর্ণালীতে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি, তাই লাল আলোর কোয়ন্টামের শক্তি সবচেয়ে কম। অন্যদিকে বেগুনি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম, তাই তার কোয়ান্টামের শক্তিও সবচেয়ে বেশি।
শুধু সমীকরণ আবিস্কার করলেই তো চলবে না, সেটাকে প্রতিষ্ঠিত তো করতে হবে!
৭ অক্টোবর ১৯০০ সাল। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। হেনরিখ রুবেন্স তখন তার গবেষণা সহকর্মী। ওইদিন রুবেন্স আর তাঁর স্ত্রী বেড়াতে আসেন প্ল্যাঙ্কের বাড়িতে। সেখানেই রুবেন্স জানান কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের পরীক্ষার কথা। পরীক্ষা থেকে কী ফল পেয়েছেন তাও বলেন। রুবেন্স বলেন, দীর্ঘ তরঙ্গের বিকিরণের ব্যাখ্যা ভীনের সূত্র দিয়েই করা যায়। কিন্তু ক্ষুদ্র তরঙ্গের জন্য সেটা অচল। আবার রেলে-জিনসের সূত্র দিয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গের বিকিরণ ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু দীর্ঘ তরঙ্গে রেলে-জিন্স তত্ত্ব অচল। তারমানে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যার জন্য দুটো সমীকরণের দরকার হচ্ছে। অথচ সমীকরণ দুটি পরস্পর বিরোধী।
সন্ধ্যায় ফিরে যান রুবেন্স ও তাঁর স্ত্রী। প্ল্যাঙ্ক তখন সমস্যাটা নিয়ে বসে গেলেন টেবিলে। এবং সেইদিনই পেয়ে গেলেন তাঁর কোয়ান্টাম সূত্রটা। যেটার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এই সূত্র দিয়ে একই সাথে ছোট ও বড় দু ধরনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যরে বিকিরণই ব্যাখ্যা করা যায়।
সূত্রটি প্ল্যাঙ্ক একটা পোস্টকার্ডে লিখলেন। তারপর সেটা পাঠিয়ে দিলেন রুবেন্সের কাছে। রুবেন্সও বোধহয় প্ল্যাঙ্কের সমীকরণের গুরুত্ব কিছুটা হলেও বুঝেছিলেন।
১৯ অক্টোবর ১৯০০। জার্মান ফিজিক্যাল সোসাইটি একটা সভার আয়োজন করে। সভার মূল বিষয়বস্তু কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল। বরাবরের মতোই বিজ্ঞানীরা সেদিনও ভীন ও রেলে জিনসের সূত্রের সাথে পরীক্ষালব্ধ ফলাফল ষোলআনা মেলাতে পারলেন না। তখন প্ল্যাঙ্ক রুবেন্সকে বললেন, তাঁর সমীকরণটা যেন বিজ্ঞানীরা যাচাই করে দেখেন। বলে সেখান থেকে বাসায় ফিরে আসেন প্ল্যাঙ্ক। পরদিন রুবেন্স প্ল্যাঙ্ককে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, তাঁর সূত্রটা অভ্রান্ত বলে রায় দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তবে প্ল্যাঙ্ক নিজেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কারণ তাঁর সূত্র অনেকটা অনুমান নির্ভর। বিজ্ঞানে অুনমান নির্ভর সূত্র প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। নিশ্চয়ই এ সূত্রের কোনো শেকড় আছে পদার্থবিজ্ঞানে। প্ল্যাঙ্ক আসলে পদার্থবিজ্ঞানের আগের কোনো সূত্র বা ফর্মুলা খুঁজছিলেন যেটা থেকে তাঁর সূত্রটা প্রতিপাদন করা যায়। অনেক চেষ্টা করেও প্ল্যাঙ্ক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যকোনো সূত্রের সাথে তাঁর নিজের সূত্রটির সম্পর্ক খুঁজে পেলেন না।
তাহলে কি পদার্থবিজ্ঞানের নতুন কোনো দ্বার খুলে গেল তাঁর হাতে? নিউটনের মতো কিংবা ম্যাক্সওয়েলের মতো? তাহলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা মহাবিপ্লবের ইঙ্গিত করছে। নাকি প্ল্যাঙ্কের সূত্রে কোনো গলদ লুকিয়ে আছে, যা তাঁ চোখে ধরা পড়ছে না। কিন্তু প্ল্যাঙ্ক নিজে কোনো গলদ খুঁজে পেলেন না। সেদিন সভায় যেসব বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন তারাও কোনো গলদ খুঁজে পাননি।
প্ল্যাঙ্ক তখন অন্য পথে হাঁটলেন, তাঁর সূত্র দিয়ে ভীন ও রেলে-জিনস দুটি সূত্রই প্রতিপাদন করা যায় কিনা সে চেষ্টা করলেন। এবং অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর সূত্র দিয়ে ভীনের সূত্র প্রতিপাদন করা যায়। প্রতিপাদন করা যায় রেলে জিনসের সূত্রও। শুধু তাই নয়, এই সূত্র দিয়ে স্টিফেন বোলৎসম্যানের সেই পুরোনো সূত্রটিও প্রতিপাদিত হয়। অথচ তাঁর সূত্র চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। প্ল্যাঙ্ক তখন নিশ্চিত হলেন বিজ্ঞান ইতিহাসের নতুন দ্বার তিনি খুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রকৃতির সম্পূর্ণ মৌলিক একটি নিয়ম তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন।
দুমাস সূত্রটা নিয়ে অনেক কাটাছেঁড়া করলেন প্ল্যাঙ্ক। তবুও কোনো ত্রুটি খুঁজে পেলেন না। প্ল্যাঙ্ক তাঁর তত্ত্বের নাম দিলেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব। তারপর অনেক খেটেখুটে একঠা প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, ‘অন দ্য থিওরি অব দ্যা এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশন ল অব দ্য নরমাল স্পেকট্রাম’। অর্থাৎ ‘স্বাভাবিক বর্ণালীর শক্তিবিভাজন সূত্র’।
সে বছর ১৪ ডিসেম্বর জার্মান ফিজিক্যাল সোসাইটির আরেকটা সভা আহবান করা হলো। সেই সভায় নিজের প্রবন্ধটি পড়ে শোনালেন প্ল্যাঙ্ক। ষেখানে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করলেন তিনি।
প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনেক বিজ্ঞানীই তখন মেনে নিতে পারেননি। হুট কররে এক জার্মান বিজ্ঞানী পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক এক শাখার কথা বলছেন সেটা হজম করতে অনেকেরই কষ্ট হয়েছিল। অনেকেই প্ল্যাঙ্কের রোমান্টিক মনের অতি কল্পনা ভেবে গুরুত্ব দেননি বিষয়টাতে। তাঁরা ভেবেছিলেন কিছুদিন আলেচনা চলবে। তারপর কোনো খুঁতটুত বেরিয়ে পড়েবে, তখন সব আলোচনা থেমে যাবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটল উল্টো ঘটনা। দিন যত গড়াল কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত তত মজবুতহলো। কিছুকাল পরে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে সার্বজনিন রূপ দিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন।


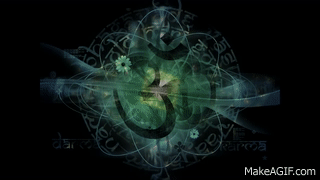




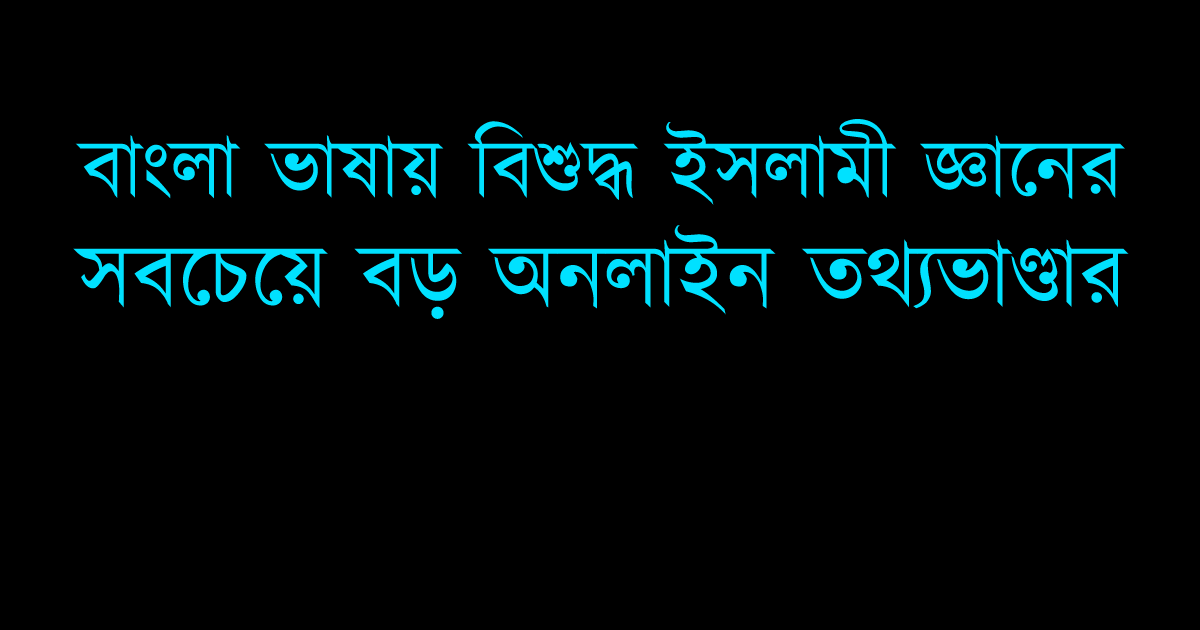

















No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ