তৃতীয় অধ্যায়েই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে মহাবিশ্বের সবকিছুকে এক বাক্যে প্রকাশ করার জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব প্রস্তুত করা বেশ কঠিন একটি কাজ। ফলে আমরা একবারে তা না করে আংশিক তত্ত্ব বের করে করে এগিয়েছি। এ তত্ত্বগুলো অল্প কিছু ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, বাকি প্রতিক্রিয়াগুলোকে হয় বাদ দিতে হয়, না হয় কিছু সংখ্যার মাধ্যমে কাছাকাছি একটি মান নেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত আমরা বিজ্ঞানের সূত্রগুলোকে যে পর্যায়ে আনতে পেরেছি তাতে অনেকগুলো সংখ্যা রয়ে গেছে। যেমন ধরুন, এখনও আমরা ইলেকট্রনের চার্জের পরিমাণ এবং প্রোটন ও ইলেকট্রনের ভরের অনুপাত তত্ত্ব প্রয়োগ করে বলতে পারি না, তথ্যগুলো পেতে হয় পর্যেবক্ষণ থেকে। আর দেখে জেনে নেওয়া এই তথ্য আমরা বসাই সমীকরণে [১]। কেউ কেউ এগুলোকে মৌলিক ধ্রুবক বলেন। অন্যরা বলেন এগুলোর কোনো মৌলিকত্ব নেই, শুধু কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের সাথে মিলানোর জন্যেই বসাতে হয়েছে।
আপনি যে মতের পক্ষেই থাকুন না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে এই সংখ্যাগুলোর মান প্রাণের উদ্ভবের পেছনে বেশ সূক্ষ্ম ভূমিকা পালন করেছে। যেমন, ইলেকট্রনের চার্জ যদি সামান্য এদিক-ওদিক হত তবে তা নক্ষত্রের মধ্যে তড়িচ্চুম্বকীয় ও মহাকর্ষীয় বলের ভারসাম্য নষ্ট করত। হয় এরা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পোড়াতে ব্যর্থ হত অথবা এরা বিস্ফোরিত হয়ে যেত [২}। দুই ক্ষেত্রেই প্রাণের অস্তিত্ব হত অসম্ভব। আমারা আশা করছি, শেষ পর্যন্ত এমন একটি পূর্ণাঙ্গ, সুসংগত, ও একীভূত তত্ত্ব পাওয়া যাবে, যা থেকে সবগুলো আংশিক তত্ত্বও বের করে নেওয়া যাবে এবং যাকে পর্যেবক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্যে সংশোধন করে বিশেষ কিছু সংখ্যা, যেমন ইলেকট্রনের চার্জ ইত্যাদি যুক্ত করতে হবে না।
এমন একটি তত্ত্বের অনুসন্ধানকে বলা হয় পদার্থবিদ্যার একীভবন (unification of physics)। এই তত্ত্ব খুঁজতে খুঁজতেই আইনস্টাইন তাঁর শেষ জীবনের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেছেন। কিন্তু সময়টা উপযুক্ত ছিল না। সে সময় মহাকর্ষ ও তড়িচ্চুম্বকীয় বলের জন্যে আংশিক তত্ত্ব ছিল, কিন্তু নিউক্লিয়ার বলসমূহ সম্পর্কে তখনকার সময়ে জ্ঞান ছিল খুব সামান্য। উপরন্তু আমরা নবম অধ্যায়ে দেখেছি যে আইনস্টাইন কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর আস্থা রাখতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু তবু দেখা যাচ্ছে অনিশ্চয়তা নীতি আমাদের মহাবিশ্বের একেবারে মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্য। অতএব, একীভূত কোনো তত্ত্বকে সফলতার মুখ দেখতে হলে এই নীতিকে অগ্রাহ্য করে তা সম্ভব হবে না।
বর্তমানে এমন একটি তত্ত্ব খুঁজে পাবার সম্ভাবনা বেড়েছে। এখন আমরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক বেশি জানি। কিন্তু আমাদেরকে সতর্কও হতে হবে, বেশি আত্মবিশ্বাসে গা ভাসিয়ে দেওয়া যাবে না। অতীত ইতিহাসেও আমরা অনেক নকল সাফল্য দেখেছি। বিংশ শতকের শুরুতে মনে করা হত, অবিচ্ছিন্ন বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা ও তাপের পরিবহন ইত্যাদি জাতীয় ধর্মগুলো দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করা যাবে। পরমাণুর কাঠামো এবং অনিশ্চয়তা নীতি আবিষ্কারের মাধ্যমে এই ধারণা বাতিল হয়ে গেল। ১৯২৮ সালে কিছু দর্শনার্থী গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ ম্যাক্স বর্নের সাথে দেখা করতে যান। তিনি তখন মন্তব্য করেন, ‘আমরা যে পদার্থবিদ্যাকে চিনি তা ছয় মাস পর বিলুপ্ত হয়ে যাবে।‘ তার কিছু দিন আগে বিজ্ঞানী পল ডিরাকের ইলেকট্রনের সমীকরণ আবিষ্কার থেকে তিনি এই আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলেন। মনে করা হয়েছিল যে একই রকম একটি সমীকরণ প্রোটনের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন শুধু এই দুটো কণিকার কথাই জানা গিয়েছিল। অতএব, মনে করা হল তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার এখানেই সমাপ্তি। কিন্তু ১৯৩২ সালে নিউট্রন আবিষ্কারের মাধ্যমে লক্ষ্য আরো দূরে সরে গেল। তবুও এই সাবধানতার কথা মাথায় রেখে আমরা আশা করতে পারি যে প্রকৃতির চূড়ান্ত সূত্রের অনুসন্ধান সাফল্যের খুব নিকটে চলে এসেছে।
কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুসারে, সকল জড় কণিকাদের মধ্যে বল ও মিথষ্ক্রিয়া বহন করে কণিকারাই। এক্ষেত্রে যা ঘটে তা হল, একটি জড় কণিকা, যেমন ইলেকট্রন বা কোয়ার্ক একটি বলবাহী (force carrying) কণিকা নির্গত করে। এই নির্গমণের ধাক্কায় জড় কণিকার বেগ বদলে যায়। এই একই কারণে গোলা নিক্ষেপের পর কামান একটু পেছনে সরে আসে। এই বলবাহী কণিকা তখন আরেকটি আরেকটি জড় কণিকার সাথে মিলিত হয়, যেটি একে শোষণ করে নেয়। ফলে এই জড় কণিকাটির বেগও পরিবর্তন হয়। দুটি জড় কণিকার মধ্যে কোনো বল কাজ করলে যে ফলাফল হত, নির্গমণ ও শোষণের এই প্রক্রিয়াও ঠিক সেরকমই।
প্রত্যেকটি বল পরিবাহিত হয় এর নিজস্ব বলবাহী কণার মাধ্যমে। বলবাহী কণার ভর বেশি হলে এদেরকে উৎপন্ন করা ও বেশি দূরত্বে পাঠানো কঠিন। ফলে, এদের বহন করা বলের পাল্লা হবে ছোট্ট। অন্য দিকে বলবাহী কণার যদি নিজস্ব ভর না থাকে, তাহলে বলের পাল্লা হবে অনেক বিশাল। জড় কণিকাদের মধ্যে বিনিময় হওয়া বলবাহী কণিকাদেরকে ভার্চুয়াল কণা বলার কারণ হচ্ছে এদেরকে বাস্তব কণিকার মতো সরাসরি শনাক্ত করা যায় না। পার্টিকেল ডিটেকটর এখানে ব্যর্থ। কিন্তু এদের পরিমাপযোগ্য প্রভাব থাকার কারণে আমরা জানি যে এদের অস্তিত্ব আছে। জড় কণিকাদের মধ্যে এরাই বল উৎপন্ন করে।
বলবাহী কণাদেরকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। এখানে বলে রাখা ভাল, এই যে চারটি ভাগ তা কিন্তু আমাদের মানুষেরই বানানো, আমাদের আংশিক তত্ত্ব তৈরির জন্যে এতে সুবিধা হয় বলে। কিন্তু এই বিভাজন আরো গভীরে নাও কাজ করতে পারে। বেশির ভাগ পদার্থবিজ্ঞানীর আশা, চারটি বলের সবগুলোকে একটি বলেরই বিভিন্ন রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করার মতো একটি একীভূত তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। অনেকের মতে বর্তমানে এটাই পদার্থবিদ্যার প্রধান লক্ষ্য।
প্রথমটি হল মহাকর্ষী বল। এই বলটি সার্বজনীন। অর্থ্যাৎ, প্রত্যেকটি কণাই এর ভর বা শক্তি অনুসারে মহাকর্ষ অনুভব করে। মহাকর্ষ অন্যান্য বলগুলোর তুলনায় অনেক অনেক দুর্বল। এটি এতই দুর্বল যে এর বিশেষ দুটি বৈশিষ্ট্য না থাকলে এর কথা আমরা জানতামই না। এক, এটি বিশাল দূরত্ব পর্যন্ত কাজ করতে পারে। দুই, এটি সব সময় আকর্ষণ করে, কখনো বিকর্ষণ করে না। এর ফলে, পৃথিবী ও সূর্যের মতো দুটো বিশাল বস্তুর প্রতিটি কণিকার মধ্যকার দুর্বল মহাকর্ষীয় বলও সব মিলিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বল তৈরি করবে। অন্য তিনটি বল হয় স্বল্প পাল্লায় কাজ করে, নয়ত কখনো আকর্ষণ করে এবং কখনো বিকর্ষণ করে প্রতিক্রিয়া হারিয়ে ফেলে।
এর পরে বলতে হয় তড়িচ্চুম্বকীয় বলের কথা। এটি ইলেকট্রন ও কোয়ার্কের মতো তড়িতগ্রস্থ (চার্জিত) কণিকাদের সাথে প্রতিক্রিয়া করে। নিউট্রনের মতো চার্জহীন কণাদের নিয়ে এটি কাজ করে না। মহাকর্ষ বলের চেয়ে এটি অনেক বেশি শক্তিশালী। দুটি ইলেকট্রনের মধ্যে ক্রিয়াশীল তড়িচ্চুম্বকীয় বল এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বলের তুলনায় ১ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি (১ এর পরে ৪২ টি শূন্য) গুণ শক্তিশালী। আবার ইলেকট্রিক চার্জ হতে পারে দুরকম। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। দুটি ধনাত্মক বা দুটি ঋণাত্মক চার্জের মধ্যে বিকর্ষণ কাজ করে। কিন্তু একটি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের মধ্যে কাজ করে আকর্ষণ বল।
সূর্য বা পৃথিবীর মতো বিশাল বস্তুদের মধ্যে প্রায় সমান সংখ্যক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ থাকে। এর ফলে, স্বতন্ত্র কণিকাদের মধ্যকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল একে অপরকে প্রায় পুরোপুরি নাকচ করে দেয় এবং খুব সামান্য পরিমাণ তড়িচ্চুম্বকীয় বল বাকি থাকে। কিন্তু পরমাণু বা অণুর খুব ক্ষুদ্র স্কেলে তড়িচ্চুম্বকীয় বলই রাজত্ব করে। মহাকর্ষের ফলে যেমন পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে, তেমনি ঋণাত্মক চার্জধারী ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক চার্জধারী প্রোটনের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বলের কারণেই পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রনরা ঘুরতে থাকে। ফোটন নামক বিপুল সংখ্যক ভার্চুয়াল কণিকা বিনিময়ের মাধ্যমে তড়িচ্চুম্বকীয় বল কাজ করে। এখানেও ফোটনদের বিনিময় ঘটে ভার্চুয়াল কণা হিসেবেই। কিন্তু একটি ইলেকট্রন এক কক্ষপথ থেকে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি আরেক কক্ষপথে চলে গেলে কিছু শক্তি নির্গত হয় এবং একটি বাস্তব ফোটন বেরিয়ে আসে। যদি এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট মানের মধ্যে থাকে, তবে একে দৃশ্যমান আলোতে আমাদের চোখ বা কোনো ফোটন ডিটেকটর, যেমন ফটোগ্রাফিক ফিল্ম দিয়ে দেখা সম্ভব। একইভাবে, একটি বাস্তব ফোটন কোনো পরমাণুর সাথে ধাক্কা খেলে নিউক্লিয়াসের কাছের কোনো কক্ষপথ থেকে একটি ইলেকট্রন আরো দূরে সরে যেতে পারে। এতে করে ফোটনের শক্তি ব্যবহৃত হয়ে যাবার কারণে এটি শোষিত হয়ে যায়।
তৃতীয় ধরনের বল হল দুর্বল নিউক্লিয়ার বল। আমরা চলতে ফিরতে কখনও সরাসরি এই বলের সাক্ষাৎ পাই না। কিন্তু এই বলটিই পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেঙে উৎপন্ন হওয়া তেজষ্ক্রিয়তার জন্যে দায়ী। ১৯৬৭ সালে দুর্বল নিউক্লিয়ার বল সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা ছিল না। ঐ বছর লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের ডঃ আব্দুস সালাম এবং হার্ভাডের স্টিভেন উইনবার্গ একই সাথে তড়িচ্চুম্বকীয় বলের সাথে এই বলের একীভবনের একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। এর প্রায় একশ বছর আগে ম্যাক্সওয়েল এভাবেই তড়িৎ ও চুম্বকীয় বলকে একত্র করেছিলেন। এই তত্ত্বের অনুমান পরীক্ষার সাথে খুব ভালো মতো মিলে যাওয়ায় ১৯৭৯ সালে সালাম ও উইনবার্গ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। একই সাথে নোবেল পান হার্ভাডের আরেক বিজ্ঞানী শেলডন গ্ল্যাশো। তিনিও তড়িচ্চুম্বকীয় ও দুর্বল নিউক্লিয়ার বলকে এক্ত্রিত করতে একই রকম একটি তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন।
চতুর্থ ধরনের বল হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী। এর নাম সবল নিউক্লিয়ার বল। আগেরটির মতো এই বলটির সাথেও আমাদের সরাসরি কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু আমাদের চারপাশের প্রায় সবকিছুকে এই বলটিই যুক্ত করে রেখেছে। প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে কোয়ার্কদেরকে যুক্ত করেছে এই বল। এই বলটিই পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও ইলেকট্রনকে ধরে রেখেছে। সবল বল না থাকলে ধনাত্মক চার্জধারী প্রোটনদের মধ্যকার বিকর্ষণের ফলে মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেঙে তছনছ হয়ে যেত। একমাত্র ব্যতিক্রম হাইড্রোজেন গ্যাস, কারণ এর নিউক্লিয়াসে মাত্র একটি প্রোটন থাকে [৩]। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস গ্লুওন (gluon) নামে একটি কণা এই বলটিকে বহন করে। এই গ্লুওন প্রতিক্রিয়া করতে পারে শুধু কোয়ার্ক ও নিজের সাথে [৪]।
তড়িচ্চুম্বকীয় ও দুর্বল নিউক্লিয়াস বলকে সফলভাবে একীভূত করার পর এই দুটোকে সবল নিউক্লিয়ার বলের সাথে একীভূত করার জন্যেও অনেকগুলো প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রস্তাবিত এই একীভূত তত্ত্বের নাম গ্র্যান্ড ইউনিফাইড থিওরি (GUT) । নামটিতে আসলে কিছুটা বাড়াবাড়ি প্রকাশ পেয়েছে। কারণ এখানে তত্ত্বটি এক দিকে খুব বেশি গ্র্যান্ড বা বড়ো নয়, আবার এটি পরিপূর্ণভাবে একীভূত তত্ত্বও নয়, কারণ এতে মহাকর্ষের কথা নেই। অন্য দিকে এটি আসলে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বও নয়, কেননা এতে অনেকগুলো এমন ধ্রুবক আছে যাদের মান তত্ত্ব থেকে বলা যায় না, পরীক্ষা করে বের করে নিতে হয়। তবে যাই হোক, পূর্ণাঙ্গ একীভূত তত্ত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে এটি প্রস্তুত করা সম্ভব হলেওতো অন্ততঃ এক ধাপ সামনে যাওয়া হবে।
মহাকর্ষকে অন্যান্য তত্ত্বের সাথে যুক্ত করতে প্রধান সমস্যা হল, মহাকর্ষের সূত্র বা সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব হচ্ছে একমাত্র তত্ত্ব, যা কোয়ান্টাম তত্ত্ব মেনে চলে না (মানে এটি একটি ননকোয়ান্টাম থিওরি)। এটি অনিশ্চয়তা নীতির ধার ধারে না। কিন্তু যেহেতু অন্যান্য বলের আংশিক তত্ত্বগুলো অনিবার্যভাবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উপর নির্ভরশীল, তাই মহাকর্ষকে অন্যান্য তত্ত্বের সাথে একীভূত করতে হলে সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্যে অনিশ্চয়তা নীতিকে স্থান দিতে হবেই। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউই কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রস্তুত করতে পারেননি।
কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব তৈরি করা এতটা কঠিন হয়ে ওঠার পেছনেও অনিশ্চয়তা নীতির হাত আছে। নীতিটি বলছে যে ‘শূন্য’ স্থানেও প্রচুর পরিমাণ ভার্চুয়াল কণা ও প্রতিকণার জোড়া রয়েছে। যদি তা না হত, মানে ‘শূন্য’ স্থান যদি আসলেই সম্পূর্ণ খালি হত, তাহলে তার অর্থ হত মহাকর্ষীয় এবং তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রসহ সবগুলো ক্ষেত্রের মান একেবারে শূন্য হত। কিন্তু একটি ক্ষেত্রের মান ও সময়ের সাথে তার পরিবর্তনের হার একটি কণার অবস্থান ও বেগের (অবস্থানের পরিবর্তন) সাথে তুলনীয়। অনিশ্চয়তা নীতি বলছে যে আপনি এই দুটি রাশির একটিকে যত বেশি সঠিকভাবে পরিমাপ করতে চাইবেন, আরেকটিতে ভুলের পরিমাণ ততই বেড়ে যাবে। অতএব, শূন্য স্থানের কোনো ক্ষেত্রের মান যদি পুরোপুরি শূন্য হয়, তার মানে একই সাথে এর মান (অর্থ্যাৎ শূন্য) এবং পরিবর্তনের হার (এটাও শূন্য) দুটোরই একটি সূক্ষ্ম হিসাব পাওয়া যাবে। এটি অনিশ্চয়তা নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। অতএব, ক্ষেত্রের মানের মধ্যে কিছু পরিমাণ অনিশ্চয়তা থাকতেই হবে। একে বলা হয় কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশান।
কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশানকে এমন এক জোড়া কণা ভাবে যেতে পারে, যারা একই সময়ে একত্রে আবির্ভূত হয়, ভিন্ন দিকে চলে, এরপর একই দিকে আসে এবং একে অপরকে ধ্বংস করে দেয়। বল বহনকারী কণিকাদের মতো এরাও ভার্চুয়াল কণিকা। বাস্তব কণিকাদের মতো এদেরকে পার্টিকেল ডিটেকটরের সাহায্যে সরাসরি শনাক্ত করা যায় না। কিন্তু এদের পরোক্ষ প্রভাব পরিমাপ করা যায়। যেমন, ইলেকট্রনের কক্ষপথের শক্তির ক্ষুদ্র পরিবর্তন পরিমাপ করা যায়। এই তথ্য তাত্ত্বিক অনুমানের সাথে বেশ নির্ভুলভাবে মিলে যায়। তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের ফ্লাকচুয়েশানের ক্ষেত্রে এই কণিকাগুলো হল ভার্চুয়াল ফোটন, আর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্যেই এই কণিকারা হল ভার্চুয়াল গ্র্যাভিটন। কিন্তু দুর্বল ও সবল নিউক্লিয়ার বলের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল জোড়া হল ইলেকট্রন, কোয়ার্ক ও তাদের প্রতিকণিকা ইত্যাদির মতো জড় কণিকাদের জোড়া।
সমস্যা হল, এই ভার্চুয়াল কণিকাদেরও এনার্জি বা শক্তি আছে। আবার যেহেতু ভার্চুয়াল কণিকার সংখ্যা অসীম, তাই এদের শক্তির পরিমাণও হবে অসীম। এর ফলে, আইনস্টাইনের সমীকরণ E = mc2 অনুসারে (পঞ্চম অধ্যায় দেখুন) এদের ভরের পরিমাণও হবে অসীম। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের ভাষায় এর অর্থ হল, মহাকর্ষ পুরো মহাবিশ্বকে গুটিয়ে অসীম সাইজের ক্ষুদ্র বানিয়ে ফেলবে। কিন্তু বাস্তবতাতো তা নয়! সবল, দুর্বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বলের মতো আংশিক তত্ত্বগুলোতেও একই রকম অদ্ভুত অদ্ভুত অসীম জিনিসের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু এদের তিনটার ক্ষেত্রেই একটি এই অসীমের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি উপায় আছে। এই কৌশলের নাম রিনর্মালাইজেশান। এর কারণেই এই বলগুলো নিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।
রিনর্মালাইজেশানের মাধ্যমে নতুন অসীম সংখ্যা নিয়ে এসে তত্ত্বে উপস্থিত অসীম সংখ্যার সাথে কাটাকাটি করা হয়। কিন্তু এদেরকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার প্রয়োজন হয় না। আমরা নতুন অসীম রাশিগুলো এমনভাবে নিতে পারি, যাতে ভাগশেষ খুব ছোট্ট হয়। এই ছোট্ট ভাগশেষদেরকে তত্ত্বে রিনর্মালাইজ করা রাশি বলা হয়।
গাণতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই কৌশলকে একটু জগাখিচুড়ি মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু এতে কাজ হয়। এই কৌশল কাজে লাগিয়ে সবল, দুর্বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বল সম্পর্কে যে অনুমান করা হয়েছিল, তা খুব দারুণভাবে পর্যবেক্ষণের সাথে মিলে গেছে। কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ থিওরি প্রস্তুত করার কথা চিন্তা করলে রিনর্মালাইজেশানের বড় একটি দুর্বলতা রয়েছে। এর কারণ হল, এটি অনুসারে বলের প্রকৃত শক্তি ও ভরের মান তত্ত্ব থেকে অনুমান করা সম্ভব হয় না, জেনে নিতে হবে পর্যবেক্ষণ থেকে। দূর্ভাগ্যের বিষয় হল, রিনর্মালাইজেশান ব্যবহার করে সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের অসীম রাশিগুলোকে দূর করতে গেলে মাত্র দুটি রাশিকে মানিয়ে নেওয়া যায়। এর একটি হল মহাকর্ষের শক্তি ও অপরটি হল মহাজাগতিক ধ্রুবক, যেটিকে আইনস্টাইন তাঁর সমীকরণে যুক্ত করেছিলেন মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে না মনে করে (সপ্তম অধ্যায় দেখুন)। কিন্তু বাস্তবতা হল, শুধু এই দুটি রাশিকে ঠিক করে সব অসীম সংখ্যার হাত থেকে বাঁচা যায় না। ফলে কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব আমাদেরকে বলছে যে স্থান- কালের বক্রতার মতোই কিছু রাশি বাস্তবিকই অসীম হবে। অথচ, এই রাশিগুলো পরিমাপ করে আমরা সম্পূর্ণ সসীম বা নির্দিষ্ট মান পাই!
সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং অনিশ্চয়তা নীতিকে একীভূত করতে গেলে যে এই সমস্যা তৈরি হবে তা অনেক দিন থেকেই আঁচ করা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালে বিস্তারিত হিসাব- নিকাশের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত হয়। চার বছর পরে একটি সম্ভাব্য সমাধান এল। এর নাম সুপারগ্র্যাভিটি। কিন্তু দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হল, সুপারগ্র্যাভিটি তত্ত্বে শেষ পর্যন্ত কোনো অসীম রাশি থাকবে কি না তা জানতে হলে এত বিশাল হিসাব- নিকাশ করতে হয় যে তা করার সাহস কারোই হয়নি। এমনকি কম্পিউটার ব্যবহার করে এই হিসাব করলেও তাতে বছরের পর বছর লেগে যাবে। আর এতেও যে অন্তত একটি বা সম্ভবত তারও বেশি ভুল থেকে যাবার সম্ভাবনাও খুব বেশি। ফলে, আমরা তখনই জানবো যে এটি সঠিক উত্তর, যখন অন্যও কেউও এই হিসাব- নিকাশ করে একই উত্তর পাবেন। আর এমন সম্ভাবনাও কিন্তু খুব ক্ষুদ্র। এছাড়াও সুপারগ্র্যাভিটি তত্ত্বের কণিকারা পর্যবেক্ষণে পাওয়া কণিকাদের সাথে মেলে না। কিন্তু তবু বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, এই থিওরিকে ঠিকঠাক করে নেওয়া যেতে পারে এবং মহাকর্ষকে অন্যান্য বলগুলোর সাথে একীভূত করার ক্ষেত্রে সম্ভবত এটাই সঠিক পথ। এরপর ১৯৮৪ সালে এসে মতামত দারুণভাবে পাল্টে গেল। লাইমলাইটে চলে এল স্ট্রিং থিওরি।
স্ট্রিং থিওরি আসার আগে মনে করা হত প্রত্যেকটি মৌলিক কণিকা একটি নির্দিষ্ট স্থান দখল করে রাখে। স্ট্রিং থিওরি অনুসারে মৌলিক বস্তুরা কোনো বিন্দু কণা নয় বরং এমন বস্তু যার শুধু দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু অন্য কোনো দিক (প্রস্থ বা উচ্চতা) নেই, অসীম পাতলা এক টুকরো সুতোর মতো। এই স্ট্রিংদের প্রান্তও থাকতে পারে (এদেরকে ওপেন বা উন্মুক্ত স্ট্রিং বলা হয়), আবার এদের কয়েকটি যুক্ত হয়ে আবদ্ধ লুপ বা চক্রও গঠন করতে পারে (এদের নাম ক্লোজড বা বদ্ধ স্ট্রিং)। প্রত্যেকটি মুহূর্তে কোনো কণিকা স্থানের একটিমাত্র বিন্দুতে অবস্থান করে। অন্য দিকে, স্ট্রিং প্রতি মুহূর্তে স্থানের একটি লাইন বা রেখা বরাবর অবস্থান করে। দুটো স্ট্রিং জোড়া লেগে একটিমাত্র স্ট্রিং গঠিত হতে পারে। ওপেন স্ট্রিংদের ক্ষেত্রে এরা প্রান্ত বরাবর যুক্ত হয়। আর ক্লোজড স্ট্রিংদের ক্ষেত্রে এদের জোড়া ট্রাউজারের মতো দেখায়। একইভাবে একটিমাত্র স্ট্রিং ভেঙে দুটি আলাদা স্ট্রিং তৈরি হতে পারে।
স্ট্রিংই যদি মহাবিশ্বের মৌলিক বস্তু হয়, তাহলে আমরা বিভিন্ন পরীক্ষায় যে কণিকাদের দেখি তারা কী? স্ট্রিং থিওরি বলছে, আগে আমরা যাকে বিভিন্ন বিন্দু কণা বলতাম, সেটা আসলে স্ট্রিং এর বিভিন্ন তরঙ্গ ছাড়া কিছুই নয়, অনেকটা ঘুড়ির কম্পমান সুতোর মতো। তবে স্ট্রিং ও এর ওপর দিয়ে চলতে থাকা কম্পন এত ক্ষুদ্র যে আমাদের সেরা প্রযুক্তি দিয়েও এদের আকৃতি বুঝতে পারা অসম্ভব। ফলে আমাদের সব পরীক্ষায় এরা বৈশিষ্ট্যহীন ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো আচরণ করে। নিকট থেকে বা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে একটি বালুকণার দিকে তাকালে এতে হয়ত এলোমেলো ছোপ ছোপ দাগ দেখা যাবে, স্ট্রিং এর মতো আকৃতিও হয়ত দেখা যেতে পারে। কিন্তু দূর থেকে দেখলে একেও বৈশিষ্ট্যহীন বিন্দুর মতোই লাগবে।
একটি কণিকা দ্বারা আরেকটির নির্গমণ বা শোষণকে স্ট্রিং থিওরিতে স্ট্রিং এর বিভাজন বা সংযোজন হিসেবে দেখা হয়। যেমন কণা তত্ত্বে পৃথিবীর উপর সূর্যের মহাকর্ষীয় বলের ব্যখ্যা দেওয়া হয়েছিল এভাবে যে, সূর্যে উপস্থিত কোনো জড় কণিকা সূর্য থেকে বলবাহী কণা গ্র্যাভিটন নির্গত করে এবং পৃথিবীতে উপস্থিত কোনো জড় কণিকা তা শোষণ করে। স্ট্রিং থিওরিতে এই কাজটি হয় H আকৃতির নল বা পাইপের মাধ্যমে (এক অর্থে স্ট্রিং থিওরি বিল্ডিং এর পাইপ সিস্টেমের মতো)। H এর খাড়া বাহু দুটি সূর্য ও পৃথিবীর কণিকার মতো কাজ করে, আর অনুভূমিক দাগটি হচ্ছে তাদের মধ্যে চলাচলকারী গ্র্যাভিটন।
স্ট্রিং থিওরির ইতিহাস বেশ আকর্ষণীয়। এর প্রথম উদ্ভব ঘটে ১৯৬০ এর দশকে। উদ্দেশ্য ছিল স্ট্রিং এর (সুতা বা দড়ি) টান বলের ব্যাখ্যা দেওয়ার তত্ত্ব খুঁজে বের করা। ভাবা হয়েছিল যে প্রোটন ও নিউট্রনের মতো কণিকাদেরকে স্ট্রিং এর তরঙ্গ মনে করা যেতে পারে। মাকড়সার জালের মতো এক স্ট্রিং এর বিটের মধ্যে চলে আসা অন্য স্ট্রিং এর টুকরোগুলোকে বিভিন্ন কণিকার মধ্যে ক্রিয়াশীল ‘সবল বল’ হিসেবে ধরা যেতে পারে। কণিকাদের মধ্যকার সবল বলের বাস্তব মান এই তত্ত্ব থেকে পেতে হলে স্ট্রিংদেরকে প্রায় দশ টন ওজোনের রবারের চুড়ির মতো হওয়া দরকার ছিল।
১৯৭৪ সালে প্যারিসের জোয়েল শের্ক ও ক্যালটেকের (ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি) বিজ্ঞানী জন সোয়ার্জ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এতে তাঁরা দেখালেন যে স্ট্রিং থিওরি মহাকর্ষীয় বলের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। তবে শর্ত হল স্ট্রিং এর টান হতে হবে দশ হাজার কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি (এক এর পরে ৩৯ টি শূন্য) টন। সাধারণ দৈর্ঘ্যের স্কেলে স্ট্রিং থিওরির অনুমান সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের সাথে হুবহু মিলে যাবে। কিন্তু এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষ কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগের (বা এক সেন্টিমিটারকে এক এর পরে ৩৩ টি শূন্য দিলে যা হয় সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে যা হয়) চেয়ে ক্ষুদ্র দূরত্বে এদের অনুমান ভিন্ন হয়। কিন্তু তাঁদের এই গবেষণা খুব নজর কাড়েনি, কারণ প্রায় ঠিক একই সময়ে বেশির ভাগ মানুষ সবল বলের মূল স্ট্রিং থিওরিকে পরিত্যাগ করেন এবং পর্যেবেক্ষণের সাথে ভালো মিল দেখে কোয়ার্ক ও গ্লুওনভিত্তিক থিওরির দিকে ঝুঁকে পড়েন। একটি মর্মান্তিক অবস্থায় শের্ক মৃত্যুবরণ করেন (তিনি ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন এবং পরে এক সময় কোমায় চলে যান। দরকার ছিল ইনসুলিন নেওয়ার। কিন্তু আশেপাশে ইঞ্জেকশান দেওয়ার মতো কেউ ছিল না।) ফলে স্ট্রিং থিওরির পক্ষে সোয়ার্জ হয়ে গেলেন একা। তবে তিনি স্ট্রিং এর টান বলের প্রস্তাবিত মান অনেক বেশি বৃদ্ধি করলেন।
১৯৮৪ সালে হঠাৎ করে স্ট্রিং থিওরি নতুন করে আলোচনায় চলে এল। এর পেছনে কাজ করেছে দুটি কারণ। এক, সুপারগ্র্যাভিটি সসীম অথবা এটি আমাদের পর্যবেক্ষণে পাওয়া কণিকাদের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম- এমন প্রমাণ পাওয়ার খুব একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। দুই, জন সোয়ার্জ এবারে লন্ডনের কুইন মেরি কলেজের মাইক গ্রিনের সাথে যৌথভাবে আরেকটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এখানে তাঁরা দেখালেন, আমাদের দেখা কিছু কণিকার মতো যেসব কণিকারা সহজাতভাবেই বামধর্মী তাদের অস্তিত্ত্ব স্ট্রিং থিওরির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। (দর্পণের মধ্যে প্রতিফলিত করে পরীক্ষার পরিবেশ পাল্টিয়ে নিলেও বেশির ভাগ কণিকার আচরণ একই থাকে, কিন্তু এই কণিকাদের আচরণ একই থাকে না। এরা হয় বাম, নয়ত ডানধর্মী। দর্পণ দিয়ে দেখলে তাই ভিন্ন রকম দেখায়।) কারণ যেটাই হোক, বিপুল সংখ্যক মানুষ স্ট্রিং থিওরি নিয়ে কাজ শুরু করলেন। তৈরি হল নতুন আরেকটি সংস্করণ। আমরা বিভিন্ন ধরনের যেসব কণিকা দেখি এটি তার ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম বলে মনে হল।
স্ট্রিং থিওরিগুলোও অসীম রাশি থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু মনে করা হয় এদের সঠিক সংস্করণটিতে অসীম রাশিগুলো কাটাকাটি হয়ে যাবে (যদিও নিশ্চিত নয়)। কিন্তু স্ট্রিং থিওরিগুলোতে এর চেয়েও বড় একটি সমস্যা আছে। এরা শুধু তখনই কাজ করে যখন স্থান- কালের মাত্রা সাধারণ চারের পরিবর্তে দশ বা ছাব্বিশ হয়। স্থান- কালের এই বাড়তি মাত্রাগুলো সায়েন্স ফিকশনে খুব সহজেই পাওয়া যায়। আর আলোর চেয়ে বেশি গতিতে ভ্রমণ করার বিপক্ষে আপেক্ষিক তত্ত্ব যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছে তা অমান্য করারও কিন্তু একটি উপায় হল এটি (দশম অধ্যায় দেখুন)। কৌশলটা হল বাড়তি মাত্রার সুযোগ কাজে লাগিয়ে শর্টকাট বা সংক্ষিপ পথে ভ্রমণ করা। মনে করুন আমরা যে স্থানে বাস করছি তা শুধু দুটি মাত্রা নিয়ে গঠিত এবং আংটি বা ডোনাটের পৃষ্ঠের মতো বাঁকানো।
আপনি যদি এর বলয়ের ভেতরের প্রান্ত থেকে এর ঠিক উল্টো পাশের কোনো বিন্দুতে আসতে চান, তাহলে আপনাকে বলয়ের ভেতরের প্রান্ত বরাবর বৃত্ত অনুসরণ করে টার্গেটে পৌঁছতে হবে। কিন্তু তৃতীয় মাত্রায় ভ্রমণ করতে পারলে আপনি বলয় ধরে না এগিয়ে সোজা অপর পাশে চলে আসতে পারেন।
বাস্তবে যদি থেকেই থাকে তাহলে এই বাড়তি মাত্রাগুলোকে আমরা দেখি না কেন? আমরা কেন শুধু স্থানের তিনটি ও সময়ের একটি মাত্রা দেখি? এর উত্তরে বলা হয়, অন্যান্য মাত্রাগুলো আমাদের পরিচিত মাত্রা থেকে ভিন্ন। এরা খুব ক্ষুদ্র সাইজের স্থানের মধ্যে কুঞ্চিত হয়ে আছে, অনেকটা এক ইঞ্চির একশ কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগের দৈর্ঘ্যের মতো। এটা এত ক্ষুদ্র যে একে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা সময়ের একটি ও স্থানের তিনটি মাত্রা দেখি, যেখানে স্থান- কাল প্রায় সমতল বা চ্যাপ্টা। এর ব্যাখ্যা বুঝতে হলে একটি স্ট্র (তরল পানীয় গ্রহণের জন্যে আমরা যে নল ব্যবহার করি) এর পৃষ্ঠের কথা ভাবুন। কাছ থেকে এর দিকে তাকালে আপনি এর পৃষ্ঠকে দ্বিমাত্রিক দেখবেন। অর্থ্যাৎ, স্ট্র এর মধ্যে অবস্থিত কোনো বিন্দুকে দুটি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এরা হল এর দৈর্ঘ্য এবং বৃত্তাকার মাত্রার চারদিকে (পরিধি বরাবর) দূরত্ব। কিন্তু এর বৃত্তাকার মাত্রা এর দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক ছোট হওয়াতে দূর থেকে দেখলে এর পুরুত্ব চোখে পড়ে না। মনে হয় এটি একটি একমাত্রিক বস্তু। অর্থ্যাৎ, এর উপরস্থ কোনো বিন্দুর অবস্থান বোঝানোর জন্যে শুধু এর দৈর্ঘ্য বলাই যথেষ্ট। তাই স্ট্রিং থিওরির সমর্থকরা বলেন, খুব ক্ষুদ্র স্কেলে স্থান- কাল দশটি মাত্রা নিয়ে গঠিত এবং এর বক্রতাও খুব বেশি। কিন্তু আরো বড় স্কেলে এই বাড়তি মাত্রাগুলোর বক্রতা দেখা যায় না।
এই ধারণ যদি সঠিক হয়, তবুও তা হবে ভবিষ্যৎ মহাকাশ যাত্রীদের জন্যে কোনো সুসংবাদ দিতে পারছে না। এই বাড়তি মাত্রাগুলো এত বেশি ক্ষুদ্র হবে যে এদের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করা সম্ভব নয়। তবে বিজ্ঞানীদের জন্যেও এটি একটি সমস্যা জমা রেখেছে। সবগুলো মাত্রার বদলে অল্প কিছু মাত্রাই কেন ক্ষুদ্র জায়গায় গুটিয়ে থাকবে? খুব সহজেই বোঝা যায়, আদি মহাবিশ্বে সবগুলো মাত্রাই কুঞ্চিত ছিল। কিন্তু সময়ের একটি ও স্থানের তিনটি মাত্রাই কেন ছড়িয়ে পড়ল? অন্য মাত্রা গুলো কেন গুটিয়েই থাকল?
এর একটি সম্ভাব্য উত্তর হল অ্যানথ্রোপিক নীতি (anthropic principle)। সংক্ষেপে এর ব্যাখ্যা হল, ‘মহাবিশ্বকে আমরা এখন যে রূপ দেখছি তার কারণ হল আমাদের অস্তিত্ব আছে’। অ্যানথ্রোপিক নীতির আবার দুর্বল ও শক্তিশালী নামে দুটি আলাদা রূপ আছে। দুর্বল অ্যানথ্রোপিক নীতি অনুসারে, স্থান- কালের হিসাবে অনেক বড় বা অসীম মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণের বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ শুধু নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলেই তৈরি হবে। ফলে এই অঞ্চলের বুদ্ধিমান প্রাণীরা নিজদেরকে বাসযোগ্য পরিবেশে দেখে মোটেই অবাক হবে না। এটা অনেকটা একজন ধনী ব্যক্তির স্বচ্ছল সমাজে বাস করার মতো, যে আশপাশে কোনো গরীব মানুষকে দেখতে পায় না।
কেউ কেউ আরেক ধাপ এগিয়ে এই নীতির শক্তিশালী রূপটি উত্থাপন করেন। এই নীতি অনুসারে, হয় মহাবিশ্ব আছে অনেকগুলো, অথবা একটি মহাবিশ্বেরই অনেকগুলো অঞ্চল আছে। এদের প্রতিটির নিজস্ব প্রাথমিক পরিবেশ এবং সম্ভবত এক গুচ্ছ আলাদা সূত্র রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ মহাবিশ্বেই জটিল প্রাণী সৃষ্টির জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। আমাদের মতো অল্প কিছু মহাবিশ্বেই বুদ্ধিমান জীবদের জন্ম হয়েছে, যাদের প্রশ্ন, ‘আমরা যেমন দেখি, মহাবিশ্ব কেন এমন হল?’ এর উত্তর খুব সহজ। আমরা যেমন দেখছি মহাবিশ্ব যদি তেমন না হত, তাহলে আমরা থাকতামই না।
দুর্বল অ্যানথ্রোপিক নীতির বিপক্ষে কম লোকই আপত্তি করবেন। কিন্তু মহাবিশ্বের দেখা রূপের ব্যাখ্যায় শক্তিশালী অ্যানথ্রোপিক নীতির বিপক্ষে অনেকগুলো আপত্তি তোলা যেতে পারে। যেমন, এতগুলো মহাবিশ্ব থকার অর্থ ঠিক কী? এরা যদি একটি অপরটি থেকে আলাদা হয়, তাহলে অন্য কোনো মহাবিশ্বে কী ঘটছে তার কোনো প্রভাব আমাদের মহাবিশ্বে পড়ার কথা নয়। অতএব আমাদেরকে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে সেই মহাবিশ্বগুলোকে আমাদের তত্ত্ব থেকে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু এরা যদি একই মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হয়ে থাকে, তাহলে প্রত্যেকটি অঞ্চলেই বিজ্ঞানের সূত্রগুলোকে একই হতে হবে। তা না হলে আমরা ক্রমাগত এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যেতে পারব না। এক্ষেত্রে এসব অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হবে এদের প্রারম্ভিক পরিবেশ। এর ফলে অ্যানথ্রোপিক নীতির শক্তিশালী রূপ দুর্বল রূপে পর্যবসিত হবে।
স্ট্রিং থিওরির বাড়তি মাত্রাগুলো কেন গুটিয়ে গেল তার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা অ্যানথ্রোপিক নীতির মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের মতো জটিল প্রাণীদের সৃষ্টির জন্যে স্থানের মাত্র দুটি মাত্রা যথেষ্ট মনে হচ্ছে না। যেমন বৃত্তে (একটি দ্বিমাত্রিক পৃথিবীর পৃষ্ঠে) বসবাসকারী প্রাণীরা একে অপরকে পার হয়ে যেতে হলে মাথার উপর দিয়ে যেতে হবে। আবার দ্বিমাত্রিক প্রাণিরা খাবার খাওয়ার পর তা পুরোপুরি হজমও করতে পারবে না। যে পথে এটি খাবার গিলেছে সে পথেই আবার তা বের করে দিতে হবে। এর কারণ হল, এর দেহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোনো পথ থাকলে তা একে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলবে। আমাদের দ্বিমাত্রিক প্রাণীটির জন্যে সমবেদনা! একইভাবে এটা বোঝাও কঠিন যে দ্বিমাত্রিক প্রাণীর দেহে রক্ত সঞ্চালন কীভাবে হবে।
আবার তিনের বেশি মাত্রা হলেও সমস্যা হবে। দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে এখানে মহাকর্ষ বলের মান তিন মাত্রার তুলনায় খুব দ্রুত কমবে। (আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতে দূরত্ব দ্বিগুণ হলে মহাকর্ষ চার ভাগের এক ভাগ হয়। চতুর্মাত্রিক জগতে তা আট ভাগের এক ভাগ হবে, পঞ্চমাত্রিক জগতে হবে ষোলো ভাগের এক ভাগ ইত্যাদি) এর ফলে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর মতো গ্রহদের কক্ষপথ হত অস্থিতিশীল। ফলে বৃত্তাকার কক্ষপথ থেকে সামান্য বিচ্যুতি (যা অন্যান্য গ্রহদের আকর্ষণে ঘটে) ঘটলেই পৃথিবী পেঁচিয়ে সূর্যের দিকে বা উল্টো দিকে চলে যেত। আমরা হয় ঠান্ডা হয়ে জমে যেতাম, নয়ত পুড়ে ছারখার হয়ে যেতাম। এমনকি তিনের চেয়ে বেশি মাত্রায় দূরত্বের সাথে মহাকর্ষের কমতির কারণে সূর্য নিজেও ঠিক থাকতে পারত না। এর বাইরের দিকের চাপ ও মহাকর্ষ ভারসাম্য ধরে রাখতে পারত না। সূর্য হয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত, নয়ত গুটিয়ে গিয়ে ব্ল্যাক হোল হয়ে যেত। দুই ক্ষেত্রেই এটি পৃথিবীর জন্যে তাপ ও আলোর ভালো উৎস হতে পারত না। আবার ছোট পারমাণবিক জগতের ক্ষেত্রেও মহাকর্ষের মতোই ঘটনা ঘটবে। যে বলের কারণে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘোরে তা বিপর্যস্ত হত, যার ফলে ইলেকট্রন হয় নিউক্লিয়াস ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেত, অথবা চলে আসত নিউক্লিয়াসের দিকে। দুই ক্ষেত্রেই আমাদের পরিচিত কোনো পরমাণু গঠিত হতে পারত না।
এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমরা অন্তত প্রাণ বলতে যা বুঝি, সেটা তৈরি হবার জন্যে সময়ের একটি এবং স্থানের তিনটি মাত্রাকে কোনোভাবেই গুটিয়ে থাকা চলবে না। এর অর্থ হচ্ছে আমরা দুর্বল অ্যানথ্রোপিক নীতি মেনে নিতে পারি। শর্ত হচ্ছে, আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে স্ট্রিং থিওরি মহাবিশ্বের এ রকম অঞ্চলের অনুমোদন দেয়। হতে পারে যে মহাবিশ্বের অন্য কোনো অঞ্চল বা অন্য কোনো মহাবিশ্বের (এর অর্থ যাই হোক না কেন) সবগুলো মাত্রাই গুটিয়ে আছে, অথবা চারের বেশি মাত্রা প্রায় সমতল অবস্থায় আছে। কিন্তু এসব অঞ্চলে ঠিক কয়টি মাত্রা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে তা দেখার জন্যে কোন বুদ্ধিমান জীব থাকবে না।
মাত্রা ছাড়াও স্ট্রিং থিওরিতে আরেকটি সমস্যা আছে। স্ট্রিং থিওরির অন্তত পাঁচটি আলাদা সংস্করণ আছে (দুটি ওপেন স্ট্রিং নিয়ে এবং বাকি তিনটি ক্লোজড স্ট্রিং নিয়ে)। আর থিওরির অনুমিত বাড়তি মাত্রাগুলো লক্ষ লক্ষ ভিন্ন উপায়ে কুঞ্চিত থাকতে পারে। একটি বিশেষ স্ট্রিং থিওরিকেই কেন বেছে নেওয়া হবে, আর কোন ধরনের কুঞ্চনই বা সঠিক হবে? কিছু দিন ধরে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে সব অগ্রগতি মুখ থুবড়ে পড়ল। ১৯৯৪ সালের দিকে আবার কিছু আবিষ্কার হাতে এল। একে বলা হচ্ছে ডুয়ালিটি বা দ্বৈততা। ভিন্ন ভিন্ন স্ট্রিং থিওরি এবং বাড়তি মাত্রাদের বেঁকে যাওয়ার ভিন্ন ভিন্ন উপায় চার মাত্রার ক্ষেত্রে হয়ত একই ফলাফল দেবে। এছাড়াও স্থানের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে থাকা কণিকা এবং রেখার মতো স্ট্রিং ছাড়াও পি- ব্রেইন (p-brane) নামে কিছু বস্তু পাওয়া গেল। এরা দুই বা তার বেশি মাত্রার স্থানের আয়তনে থাকে।
(একটি কণিকার ব্রেইন ০ (p=0), স্ট্রিং এর ব্রেইন ১ এবং এভাবে p=2, থেকে p=9 পর্যন্ত আছে। ২-ব্রেইনকে দ্বিমাত্রিক মেমব্রেন মনে করা যেতে পারে। আরো বেশি মাত্রার কথা চিন্তা করা আরো কঠিন।) এসব থেকে মনে হচ্ছে সুপারগ্রাভিটি, স্ট্রিং ও পি-ব্রেইন থিওরির মধ্যে এক ধরনের গণতন্ত্র (বক্তব্যের সমান অধিকার থাকার অর্থে) কাজ করছে। এদেরকে সবগুলোকে ঠিক মনে হচ্ছে, কিন্তু কোনোটাকেই অন্য কোনোটার চেয়ে বেশি মৌলিক বলা চলে না। বরং সবগুলোই মনে হচ্ছে অন্য কোনো মৌলিক থিওরি থেকে আসা। প্রতিটিই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সঠিক।
এই মৌলিক তত্ত্ব খোঁজারও কম চেষ্টা চলেনি। কিন্তু এ পর্যন্ত সাফল্য ধরা দেয়নি। এমনও হতে পারে যে এক গুচ্ছ গাণিতিক স্বীকার্যের মাধ্যমে যে মৌলিক তত্ত্ব তৈরি করা সম্ভব, তার বাইরে মৌলিক তত্ত্বের কোনো একক রূপ নেই। বরং এটি হয়ত মানচিত্রের মতো- আপনি একটি সমতল ম্যাপে পৃথিবীর গোলাকার পৃষ্ঠ বা আংটির পৃষ্ঠের ছবি তুলতে পারবেন না। প্রতিটি বিন্দু দেখাতে হলে পৃথিবীর ক্ষেত্রে আপনার অন্তত দুটি ম্যাপ লাগবে, আর আংটির ক্ষেত্রে লাগবে চারটি ম্যাপ [৫]। প্রত্যেকটি ম্যাপ একটি সীমিত অঞ্চলে জন্যে সঠিক থাকবে। তবে ভিন্ন ভিন্ন ম্যাপের মধ্যেও কিছু অঞ্চল একই রকম হবে। সবগুলো ম্যাপ মিলিয়ে পৃষ্ঠের একটি পূর্ণ চিত্র তৈরি হবে। একইভাবে পদার্থবিদ্যায় হয়ত ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সূত্র প্রযোজ্য হবে, কিন্তু দুটি আলাদা সূত্র আবার একই পরিবেশেও হয়ত কাজ করতে পারে।
এটা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে সবগুলো আলাদা সূত্রের সংগ্রহকে একটি পূর্ণ একীভূত তত্ত্ব বলা যেতে পারে, যদিও এই তত্ত্বটিকে একটিমাত্র বক্তব্যের মাধ্যমে লেখা যাবে না। প্রকৃতির কাছ থেকে এটাই হবে অনেক বড় পাওয়া। এটা কি সম্ভব যে বাস্তবে কোনো একীভূত তত্ত্বই নেই? আমরা মরীচিকার পেছনে ছুটছি নাতো? এখানে সম্ভাবনা আছে তিনটিঃ
এক, বাস্তবিকই একটি পূর্ণ একীভূত তত্ত্ব (অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল আছে এমন কিছু সূত্রের সমাবেশ) আছে । আমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান হলে এক দিন সেটা আবিষ্কার করতে পারব।
দুই, মহাবিশ্বের চূড়ান্ত কোনো তত্ত্ব নেই। একটির পর একটি তত্ত্ব হাতে আসে, যা মহাবিশ্বকে আরেকটু ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। এভাবে অসীম পর্যন্ত চলেও কখনো প্রকৃত তত্ত্ব পাওয়া যাবে না।
তিন, মহাবিশ্বের আসলে কোনো তত্ত্বই নেই, কোনো ঘটনার অনুমান একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত করা যাবে, তার বেশি নয়। ঘটনা ঘটে এলোমেলোভাবে। কেউ কেউ তৃতীয় যুক্তির পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলবেন, যদি পূর্ণাঙ্গ এক গুচ্ছ সূত্র থেকে থাকে তবে তা হবে ঈশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা হবে। এক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছামতো তাঁর মন বদলিয়ে বিশ্বের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না [৬]।
কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু সর্বশক্তিমান, তিনি কি চাইলেই নিজের স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করতে পারেন না? এর সাথে পুরাতন একটি প্যারাডক্সে কিছুটা মিল আছে। ঈশ্বরকি এমন কোনো পাথর বানাতে পারেন যা তিনি নিজেই তুলতে পারবেন না? সেন্ট অগাস্টিনের মতে, আসলে ঈশ্বর মন পরিবর্তন করবেন কি না এমন প্রশ্ন করা খোদ তাঁকেও সময়ের মধ্যে উপস্থিত হিসেবে কল্পনা করার সমতুল্য, যা একটি ভুল পদ্ধতি। সময় হল ঈশ্বরের সৃষ্ট মহাবিশ্বের একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র। ধরে নেওয়া যায় যে তিনি কী তৈরি করতে চাচ্ছিলেন তা ভালোমতোই জানতেন।
কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আবির্ভাবের ফলে আমাদেরকে মানতে হচ্ছে, কোনো ঘটনা সম্পর্কে একশো ভাগ নির্ভুল করে কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়। সব সময় কিছু অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। আপনি চাইলে এই র্যান্ডম বা দৈব [৭] হস্তক্ষেপের জন্যে ঈশ্বরকে দায়ী করতে পারেন। কিন্তু এই হস্তক্ষেপটা বড়ই অদ্ভুত। এমন কোনো প্রমাণ নেই যে এটি কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ সেক্ষেত্রে একে দৈব বলা যেত না। এখন আমরা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যকে নতুন করে নির্ধারণ করেছি। ফলে তৃতীয় সম্ভাবনাটি বাদ পড়ে গেছে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন এক গুচ্ছ সূত্র বের করা, যা আমাদেরকে অনিশ্চয়তা নীতির বেঁধে দেওয়া সীমার মধ্যে থেকে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুমান করে সহায়তা করবে।
অন্য দিকে, এত দিনের আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দ্বিতীয় সম্ভাবনাই পরিলক্ষিত হচ্ছে, অর্থ্যাৎ, সূত্রগুলো প্রতিনিয়ত পরিমার্জিত হবে। এভাবেই চলবে অসীম পর্যন্ত। বিভিন্ন সময় আমরা আমাদের পরিমাপের সূক্ষ্মতা বাড়িয়েছি অথবা নতুন নতুন পর্যেবেক্ষণ পেয়েছি। পেয়েছি এমন এমন নতুন পর্যবেক্ষণ, যা প্রচলিত তত্ত্ব অনুমানও করতে পারেনি। এই পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তৈরি করতে হয়েছে নতুন তত্ত্ব। এখন আমরা কোয়ার্ক ও ইলেকট্রনকে ‘মৌলিক’ কণিকা বিবেচনা করি। যেসব কণিকারা আরো বেশি বেশি শক্তি নিয়ে একে অপরের সাথে প্রতিক্রিয়া করে, তাদেরকে নিয়ে গবেষণা করে হয়ত আমরা আরো মৌলিক কোনো স্তর খুঁজে পাব।
‘বক্সের ভেতরে বক্স’ জাতীয় এই ধারায় মহাকর্ষ হয়ত বাধ সাধতে পারে। আমাদের কাছে যদি এমন কোনো কণিকা থাকে যার শক্তি কথিত প্ল্যাঙ্ক এনার্জির চেয়ে বেশি, তাহলে এটি এত বেশি সঙ্কুচিত হবে যে এটি মহাবিশ্বের বাকি অংশ থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলবে, তৈরি করবে একটি ছোট্ট ব্ল্যাক হোল। কাজেই মনে হচ্ছে যে আরো বেশি বেশি পরিমার্জিত সূত্রের ধারার একটি সীমা আছে। এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তি নিয়ে গবেষণা করতে করতে আমরা হয়ত মহাবিশ্বের চূড়ান্ত কোনো সূত্রের দেখা ঠিকই পাব। কিন্তু এখনো আমরা পরীক্ষাগারে যে শক্তি প্রস্তুত করতে পারি, প্ল্যাঙ্ক এনার্জি তা থেকে অনেক দূরে। আমাদের অনুমিত ভবিষ্যতেও পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর (যেখানে বিভিন্ন কণিকাকে উচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে বেগ বাড়িয়ে সংঘর্ষ ঘটানো হয়) এই গ্যাপ পূরণ করতে পারবে না। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রারম্ভিক সময়গুলোতে এই শক্তি নিশ্চয় ছিল। মহাবিশ্বের আদি অবস্থা নিয়ে গবেষণা করে তা গাণিতিকভাবে সুসঙ্গত উপায়ে তুলে ধরতে পারলে যে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ একীভূত তত্ত্ব পাব তার সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল। এবং তা হতে পারে আমরা যারা এখন বেঁচে আছি তারা থাকতে থাকতেই, যদি না আমরা তার আগেই নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলি!
মহাবিশ্বের চূড়ান্ত তত্ত্ব আবিষ্কারের ফল কী হবে? তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে আমরা যদি সঠিক তত্ত্বটি পেয়েও যাই, আমরা বুঝতেও পারব না এটাই সেই কাঙ্ক্ষিত তত্ত্ব, কারণ তত্ত্ব প্রমাণ করা যায় না [৮]। কিন্তু যদি তত্ত্বটি গাণিতিকভাবে সুসঙ্গত হয় এবং এর অনুমান পর্যবেক্ষণের সাথে মিলে যায়, তাহলে আমরা ধরে নিতেই পারি যে এটাই সত্যিকারের সূত্র। এর ফলে ইতিহাসের সেই গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়টির ইতি ঘটবে যা মহাবিশ্বের কলাকৌশল উদ্ঘাটন করার বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে ভরপুর। পাশাপাশি মহাবিশ্বের সূত্রগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের জগতেও বিপ্লব ঘটবে।
নিউটনের সময়েও একজন শিক্ষিত মানুষ সবগুলো জ্ঞান আয়ত্ত্বে রাখতে পারতেন, অন্তত মূলনীতিগুলো জানতেন। কিন্তু তার পর থেকে বিজ্ঞানের গতি এই কাজটিকে অসম্ভব করে তুলেছে। যেহেতু সব সময় নতুন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটে, তাই এই তত্ত্ব কখনোই সাধারণ মানুষের বোঝার মতো সহজ হয় না। বুজতে পারেন শুধু বিশেষজ্ঞরাই, এবং তার পরেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর অল্প অংশই বুঝে ওঠা সম্ভব। উপরন্তু, অগ্রগতি এত দ্রুত হচ্ছে যে আপনি স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা জানতে পারছেন তাও কিছুটা সেকেলে হয়ে পড়ে। অল্প কিছু মানুষই জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যাবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন। এটা করতে গিয়ে তঁদেরকে পুরো সময়টা একটি বিশেষ দিকের প্রতি ঝুঁকে থাকতে হয়। বাকি মানুষরা নতুন নতুন অগ্রগতি সম্পর্কে কমই জানতে পারেন, তার উত্তেজনাও অনুভব করেন কম। অন্য দিকে বিজ্ঞানী এডিংটনের মত অনুসারে, সত্তর বছর আগে মাত্র দুই ব্যক্তি আপেক্ষিক তত্ত্ব বুঝতেন। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববদ্যালয় পাস করা হাজার হাজার শিক্ষার্থী তা বোঝে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্তত এই ধারণার সাথে পরিচিত। একইভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ একীভূত তত্ত্ব পাওয়া গেলে মুহূর্তের মধ্যেই সবাই এটি বুঝে ফেলবে, পড়ানো হবে স্কুলেও, অন্তত প্রাথমিক ধারণাটুকু। তখন আমরা কিছুটা বুঝতে পারব যে মহাবিশ্ব কোন সূত্রগুলো দিয়ে চলছে এবং আমরাইবা কীভাবে এলাম।
যদি আমরা একটি সম্পূর্ণ একীভূত থিওরি হাতে পাইও, তবু এর মাধ্যমে যে সব ধরনের ঘটনা সম্পর্কে অনুমান করা যাবে তা কিন্তু নয়। এর পেছনে আছে দুটো কারণ। প্রথমটি হচ্ছে অনিশ্চয়তা নীতি, যা আমাদের অনুমানের ক্ষমতাকে খর্ব করে দেয়। আমরা কোনোভাবেই এর হাত থেকে বাঁচতে পারি না। তবে দ্বিতীয় কারণটি আরো বেশি মারাত্মক। বাস্তবে এমন তত্ত্বের সমীকরণ শুধু সরল ক্ষেত্রগুলোতে সমাধান করা যায়। আগেও আমরা বলেছি, কোনো পরমাণুর একটি নিউক্লিয়াস ও একের বেশি ইলেকট্রনের জন্যে কোয়ান্টাম সমীকরণের প্রকৃত সমাধান বের করা যায় না। এমনিক, নিউটনের সহজ- সরল মহাকর্ষ তত্ত্ব থেকেও আমরা তিনটি বস্তুর গতির সমাধান বের করতে ব্যর্থ। বস্তুর সংখ্যা আরো বাড়লে এই কাজ হয়ে পড়ে আরো কঠিন, তত্ত্ব হয়ে পড়ে জটিল থেকে জটিলতর। বাস্তবে আসন্ন সমাধান (প্রকৃত সমাধানকে সরল করে কাছাকাছি একটি মান বের করা) দ্বারা কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু সকল কিছুর একীভূত তত্ত্ব পাওয়ার আকাশচুম্বী প্রত্যাশাতো এর মাধ্যমে পূরণ হয় না।
বর্তমানে আমরা জেনে ফেলেছি যে কোন সূত্রগুলো বস্তুর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তবে চরম অবস্থায় (extreme condition) এ সূত্রদের প্রভাব কী হবে তা জানা সম্ভব হয়নি। যেমন, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের সবগুলো মৌলিক সুত্র আমরা জানি। এর পরেও আমরা চূড়ান্তভাবে বলতে পারি না যে এদের সমাধান পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। তার উপর মানুষের আচরণকে গাণিতিক সমীকরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বলা চলে আমরা প্রায় ব্যর্থ। ফলে আমরা এক গুচ্ছ মৌলিক সূত্র যদি পাইও, তবে তার আগে বহু বছর ধরে প্রচলিত সূত্রগুলো থেকে ক্রমেই বেশি নির্ভুল আসন্ন মান পাওয়ার মতো কঠিন কাজটি করে যেতে হবে। তাহলে আমরা বিভিন্ন ঘটনার জটিল ও বাস্তবে ক্ষেত্রে উপযোগী অনুমান তৈরি করতে পারব। একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসঙ্গত একীভূত তত্ত্ব পাওয়ার মাধ্যমে মাত্র এক ধাপ কাজ হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের অস্তিত্বসহ চারপাশে যেসব ঘটনা ঘটছে তার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান।
[অনুবাদকের নোটঃ
১। ব্যাপারটা অনেকটা এ রকমঃ কল্পনা করুন যে কোন দিন কটায় সূর্য উঠবে আমরা তা জানি না, যার ফলে প্রতি দিন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় এটি কটায় উঠে তা দেখার জন্যে। বাস্তবে এটা আমরা জানি। সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের সময় বলার মতো তত্ত্ব আমাদের কাছে আছে। কিন্তু ইলেকট্রনের ভর বলার মতো তত্ত্ব নেই। এটা জানতে হয় পর্যবেক্ষণ থেকে। অর্থ্যাৎ তথ্য পাওয়ার দুটো উৎস আছে। একটি হল তত্ত্ব, আরেকটি হল পর্যবেক্ষণ। অবশ্য পর্যবেক্ষণ থেকেই ধীরে ধীরে তত্ত্বের জন্ম হয়।
২। আমরা জানি, নক্ষত্রের জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় ধরে এর মধ্যে ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেনরা নিজেদের সাথে যুক্ত হয়ে হিলিয়াম হতে থাকে। এর ফলে তৈরি বাইরের দিকের চাপ নক্ষত্রের মহাকর্ষীয় টানকে প্রতিহত করে। কিন্তু এই ভারসাম্য বজায় থাকার পেছনে ইলেকট্রনের চার্জের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
৩। দুই বা তিন ভর বিশিষ্ট হাইড্রোজেন, অর্থ্যাৎ যথাক্রমে ডিউটেরিয়াম ও টিট্রিয়ামও স্থিতিশীল থাকত , কারণ এদের মধ্যেও প্রোটন একটি করেই থাকে, বেশি থাকে একটি করে নিউট্রন, যার কোনো চার্জ নেই বলে আকর্ষণ বা বিকর্ষণের মাধ্যমে পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা এর নেই।
৪। গ্লুওন (gluon) শব্দটির সাথে glue এর মিল আছে, যার অর্থ আঠা, বা আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো। যেহেতু এই কণাটি কোয়ার্কদের জোড়া লাগিয়ে নিউট্রন ও প্রোটন গঠন করে, তাই বলা যায় নামটি সার্থক হয়েছে।
৫। কারণ এর উপরের দিকে একটি পৃষ্ঠ, আবার ভেতরের দিকেও আংটির ভাঁজের কারণে আরেকটি পৃষ্ঠ আছে।
৬। কিন্তু এমনতো হতেই পারে যে ঈশ্বর আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে সূত্র দিয়ে দেবার পর তিনি আর মহাবিশ্বের কোনো কর্মকাণ্ডে নাক গলাবেন না বা মন পরিবর্তন করবেন না, অন্তত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। অথবা এমনও হতে পারে যে তিনি যে পরে কিছু সময়ের জন্যে আর নাক গলাবেন না বা মন পরিবর্তন করবেন না, এটাও সূত্রেররই অংশ হবে।
৭। গাণিতিক পরিসংখ্যানের ভাষায় সে ঘটনাকে দৈব বলা হয়, যেটি ঘটবে কি না নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, বড়জোর ঘটার একটি সম্ভাবনা বলা যাবে।
৮। অর্থ্যাৎ, কোনো তত্ত্ব আসলে ঠিক কি না তা আমরা বলতে পারি না, আমরা শুধু বলতে পারি একে এখনো ভুল বলার মতো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।]


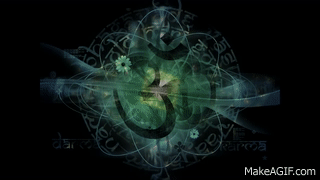




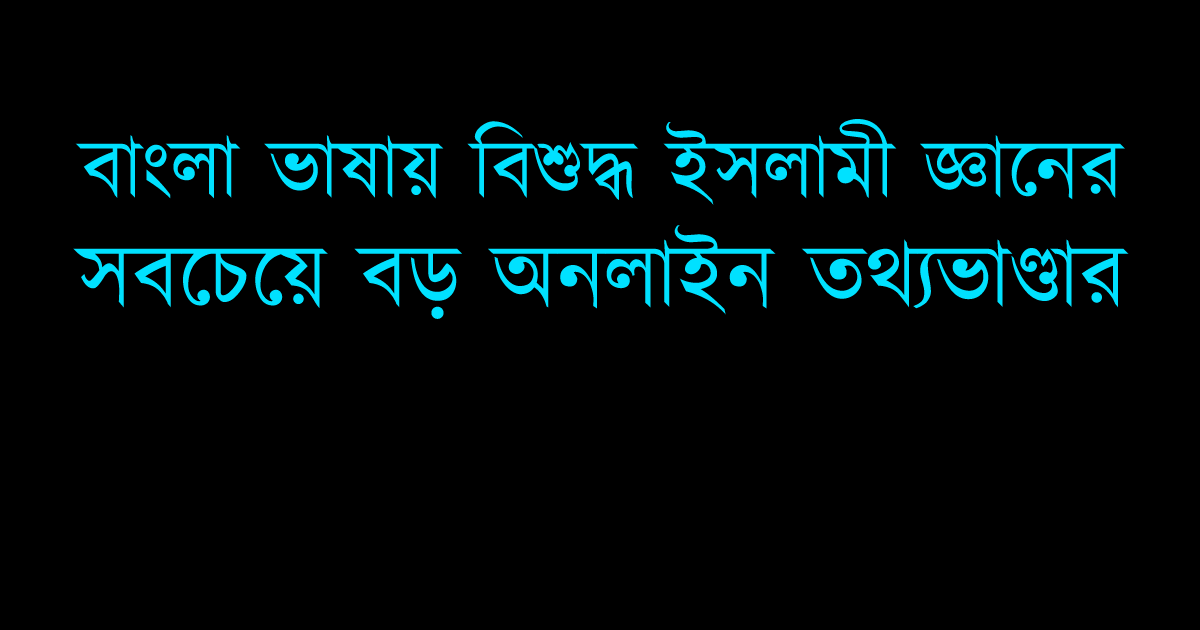






















No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ