গ্রন্থ-পরিচয়
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে গুরুভাব প্রকাশিত হইল। ঠাকুরের সাধনকালের সময় হইতে বিশেষ প্রকটভাবের পূর্ব পর্যন্ত জীবনের ঘটনাবলীই ইহাতে প্রধানতঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে কেবলমাত্র ঐসকল ঘটনা বা ঠাকুরের ঐ সময়ের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই নাই। যে মনের ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, যে উদ্দেশ্যে তিনি ঐসকল কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহারও যথাযথ আলোচনা করিয়াছি। কারণ, শরীর ও মনের সমষ্টিভূত মানবের জীবনেতিহাস কেবলমাত্র তাহার জড় দেহ ও তৎকৃত কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে পাওয়া যায় না। জড়বাদী পাশ্চাত্য জীবনী ও ইতিহাস লিখিতে যাইয়া প্রধানতঃ ঘটনাবলীর সংগ্রহেই দক্ষতার পরিচয় দেয় এবং আত্মবাদী হিন্দু মনোভাবের সুনিপুণ সংস্থানেই মনোনিবেশ করে। আমাদের ধারণা, ঐ উভয় ভাবের সম্মিলনেই যথার্থ জীবনী বা ইতিহাস সম্ভবে এবং মনের ইতিহাসকে পুরোবর্তী রাখিয়াই সর্বত্র জড়ের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য।
আর এক কথা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবন আমরা বর্তমান গ্রন্থে শাস্ত্রসহায়েও অনেক স্থলে অনুশীলন করিয়াছি; তাঁহার অসাধারণ মনোভাব, অনুভব ও কার্যকলাপের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি ভারতের এবং ঈশাদি ভারতেতর দেশের মহাপুরুষগণের অনুভব ও কার্যকলাপের তুলনার আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কারণ ঠাকুর আমাদিগের নিকট স্পষ্টাক্ষরে বারংবার নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্ব পূর্ব যুগে, “যে রাম, যে কৃষ্ণ (ইত্যাদি হইয়াছিল) সে-ই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতর রহিয়াছে!” – এবং “এখানকার (আমার) অনুভবসকল বেদ-বেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে!” বাস্তবিক ‘ভাবমুখে’ অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ঈদৃশ অলৌকিক জীবন আধ্যাত্মিক জগতে আর ইতঃপূর্বে দেখা যায় নাই।
আবার পূর্ব পূর্ব অবতারসকলের মতানুগ হইয়া সকলপ্রকার সাধনমার্গে স্বল্পকালেই সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি ‘যত মত তত পথ’-রূপ যে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার ও লোকহিতার্থ ঘোষণা করিয়াছেন, তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহাকে পূর্ব পূর্ব যুগাবির্ভূত সকল অবতারপুরুষগণের ঘনীভূত সমষ্টি ও নবাভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিতেই বাধ্য হইয়াছি। বাস্তবিকই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদৃষ্টপূর্ব পবিত্র জীবনের আমরা যতই অনুশীলন করিয়াছি, ততই উহাকে বৈদিক সার্বজনীন ও সনাতন অধ্যাত্মভাববৃক্ষের সারসমষ্টিসমুদ্ভূত প্রথমোৎপন্ন ফলস্বরূপেই নির্ধারিত করিতে বাধ্য হইয়াছি।
শ্রীরামকৃষ্ণপদাশ্রিত পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচারের পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকথা জানিবার জন্য সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া বর্তমান কালে অনেকে অনেক কথা তৎসম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিলেও ঐ অলোকসামান্য জীবনের সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া কেহই এ পর্যন্ত উহার অনুশীলন করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন সনাতন হিন্দুধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথক এক ব্যক্তি এবং সাম্প্রদায়িক মতবিশেষেরই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন – এইরূপ বিপরীত ধারণাই ঐসকল পুস্তকপাঠে মনে উদিত হইয়া থাকে। আবার ঐসকল গ্রন্থের অনেকগুলি ঠাকুরের জীবনাখ্যায়িকা সম্বন্ধে নানা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এবং অপরগুলিতে ঐসকল জীবনঘটনার প্রকৃত অর্থ এবং পূর্বাপর সম্বন্ধ ও পারম্পর্য লক্ষিত হয় না। সাধারণের তদ্ভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য ঐ মহদুদার জীবন আমাদের নিকটে যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে এবং যে ভাবোপলব্ধি করিয়া শ্রীবিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে জীবনোৎসর্গ করিয়াছি, তাহারই কিছু স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের পদানুগ হইয়া বর্তমান গ্রন্থে পাঠককে বলিবার প্রযত্ন করিয়াছি। ঠাকুরের অলৌকিক জীবনাদর্শ যদি উহাতে কথঞ্চিৎ যথার্থভাবেও অঙ্কিত হইয়া থাকে, তবে উহা তাঁহারই গুণে হইয়াছে; এবং যাহা কিছু অসম্পূর্ণতা ও অঙ্গহানিত্ব রহিয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের বুঝিবার ও বলিবার দোষেই হইয়াছে, পাঠক এ কথা বুঝিয়া লইবেন। ভবিষ্যতে ঠাকুরের অমূল্য জীবনের পূর্ব ও শেষভাগের পরিচয়ও এইভাবে পাঠককে উপহার দিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে ‘ভাবমুখে’ অবস্থিত দুরবগাহী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সনাতন বৈদিক ধর্মের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধালোচনা করিয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ যে সূত্রগুলি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখানে পাঠকের নয়নগোচর করিয়া আমরা গ্রন্থারম্ভে প্রবৃত্ত হই।
অলমিতি –
বিনীত
গ্রন্থকার
তৃতীয় খণ্ড – হিন্দুধর্ম ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
হিন্দুধর্ম ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ॥
স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তম্
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগৰ্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥1
শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত ‘বেদ’ বুঝা যায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।
পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য, যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত।
‘সত্য’ দুই প্রকার: – (১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত। (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তিগ্রাহ্য।
প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে ‘বিজ্ঞান’ বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে ‘বেদ’ বলা যায়।
‘বেদ’ নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান; সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন।
ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম ‘বেদ’।
এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্মানুভূতি। সাধকের জীবনে যতদিন উহার উন্মেষ না হয়, ততদিন ‘ধর্ম’ কেবল ‘কথার কথা’ ও ধর্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও তাহার পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে।
সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন, অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে।
সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র ‘বেদ’।
অলৌকিক জ্ঞানবেতৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদিদেশীয় ধর্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম, সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্য জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ ‘বেদ’ নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমাণভূমি।
আর্য জাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদনামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে তাহাই ‘বেদ’।
এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফলসমূহ মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে সর্বকাল অবস্থিত বলিয়া দেশ, কাল, পাত্রাদি নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতিও এই কর্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচারসকলও সৎশাস্ত্র এবং সদাচারের অবিসম্বাদী হইয়াই কালে কালে গৃহীত হইয়াছে ও হইবে। সৎশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হওয়াই আর্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।
জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্তভাগই – নিষ্কামকর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় – মুক্তিপ্রদ এবং মায়াপারনেতৃত্ব-পদে সর্বকাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এবং দেশ, কাল, পাত্রাদির দ্বারা সর্বথা অপ্রতিহত থাকা বিধায় উহাই সার্বলৌকিক, সার্বভৌমিক ও সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা।
মন্বাদি তন্ত্র কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশ-কাল-পাত্রভেদে সামাজিক কল্যাণকর কর্মের শিক্ষাই প্রধানতঃ দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র বেদান্তনিহিত তত্ত্বসকল লইয়া অবতারাদির মহান চরিত বর্ণনমুখে ঐসকল তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যানই করিতেছেন; এবং অনন্ত ভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।
কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান – এইসকল ভাববিশেষের বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য আপাতপ্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত, ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী – পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহে অসমর্থ, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহু খণ্ডে বিভক্ত এবং সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, তখন আর্য জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী দ্বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।
অনাদি বর্তমান, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষিহৃদয়ে স্বতঃ আবির্ভূত হন তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্মের পুনরুদ্ধার, পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে এইজন্য বেদমূর্তি ভগবান এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন।
বেদ – অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মের, এবং ব্রাহ্মণত্ব – অর্থাৎ ধর্মশিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান যে বারংবার শরীরধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।
প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়, পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক পতনের পর আর্যসমাজও যে শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যবান হইতেছে, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।
প্রত্যেক পতনের পর আমাদের পুনরুত্থিত সমাজ অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছে এবং সর্বভূতান্তর্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।
বারংবার এই ভারতভূমি মূর্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।
কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা, গতপ্রায়া, বর্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোন অমানিশা ইতঃপূর্বে এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।
সেইজন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় আর্য-সমাজের পূর্ব পূর্ব যুগের বোধনসমূহ সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায় মহিমাবিহীন হইবে এবং উহার এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পূর্ব পূর্ব যুগে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।
সনাতন ধর্মের সমগ্র-ভাবসমষ্টি, বর্তমান পতনাবস্থাকালে, অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-আকারে কোথাও আংশিকভাবে পরিরক্ষিত এবং কোথাও বা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছিল।
এই নবোত্থানে নববলে বলীয়ান মানবসন্তান যে সেই বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টিকৃত করিয়া নিজ জীবনে ধারণা ও অভ্যাস করিতে এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে, ইহারই নিদর্শনস্বরূপ পরম কারুণিক শ্রীভগবান বর্তমান যুগে সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাবসমন্বিত, সর্ববিদ্যাসহায়, পূর্বোক্ত যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।
অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।
এই নব-যুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং এই নব-যুগধর্মপ্রবর্তক শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পূর্বগ শ্রীযুগধর্ম-প্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ! – হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর!
হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না – গতরাত্রি পুনর্বার আসে না – বিগতোচ্ছ্বাস পূর্বরূপ আর প্রদর্শন করে না – জীবও দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি – গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি – লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও!
যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-পরিবর্তনের সহায়তা কর!
আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক – এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও!
বিবেকানন্দ
1. প্রেমের প্রবাহ যাঁর আচণ্ডালে অবারিত।
লোকহিতে রত সদা হয়ে যিনি লোকাতীত॥
জানকীর প্রাণবন্ধ উপমা নাহিক যাঁর।
ভক্ত্যাবৃত জ্ঞানবপু যিনি রাম অবতার॥
স্তব্ধ করি কুরুক্ষেত্রে প্রলয়ের হুহুঙ্কার।
দূর করি সহজাত মহামোহ-অন্ধকার॥
উঠেছিল সুগম্ভীর গীতাসিংহনাদ যাঁর।
সেই এবে রামকৃষ্ণ খ্যাতনামা ত্রিসংসার॥
তৃতীয় খণ্ড – প্রথম অধ্যায়: শ্রীরামকৃষ্ণ – ভাবমুখে
ঠাকুরের কথার গভীর ভাব
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
– গীতা, ৭/১২ – ১৩
দ্বাদশবর্ষব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক তপস্যান্তে শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরকে বলেন – “ওরে, তুই ভাবমুখে থাক”; ঠাকুরও তাহাই করেন – একথা এখন অনেকেই জানিয়াছেন। কিন্তু ভাবমুখে থাকা যে কি ব্যাপার এবং উহার অর্থ যে কত গভীর তাহা বুঝা ও বুঝানো বড় কঠিন। আটাশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন জনৈক বন্ধুকে1 বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করিয়া ঝুড়ি-ঝুড়ি দর্শন-গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে।” বন্ধুটি তৎশ্রবণে অবাক হইয়া বলেন – “বটে? আমরা তো ঠাকুরের কথার অত গভীর ভাব বুঝতে পারি না। তাঁর কোন একটি কথা ঐ ভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলবে?”
স্বামীজী – বোঝবার মাথা থাকলে তবে তো বুঝবি। আচ্ছা, ঠাকুরের যে-কোন একটি কথা ধর, আমি বুঝুচ্চি।
বন্ধু – বেশ; সর্বভূতে নারায়ণ দেখা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ঠাকুর ‘হাতি-নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণে’র যে গল্পটি বলেন সেইটি বুঝিয়ে বল।
স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ পণ্ডিতদিগের ভিতরে আবহমানকাল ধরিয়া, স্বাধীন-ইচ্ছা ও অদৃষ্টবাদ অথবা পুরুষকার ও ভগবদিচ্ছা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে অথচ কোন একটা স্থির মীমাংসা হইতেছে না, সেই সকল কথা উত্থাপন করেন এবং ঠাকুরের ঐ গল্পটি যে ঐ বিবাদের এক অপূর্ব সমাধান, তাহা সরল ভাষায় তিন দিন ধরিয়া বন্ধুটিকে বুঝাইয়া বলেন।
1. শ্রীযুত হরমোহন মিত্র।
সকল অবতারপুরুষের কথাই ঐরূপ
তলাইয়া দেখিলে বাস্তবিকই ঠাকুরের অতি সামান্য-সামান্য দৈনিক ব্যবহার ও উপদেশের ভিতর ঐরূপ গভীর অর্থ দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য হইতে হয়। অবতারপুরুষদিগের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই কথাটি সত্য। তাঁহাদের জীবনালোচনায় ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি যে দুই-একজন মহাপুরুষকে বিপক্ষদলের কুতর্কজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ধর্মসংস্থাপন করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, অপর সকল মহাপুরুষদিগের জীবনেই দেখা যায়, তাঁহারা সাদা কথায়, মর্মস্পর্শী ছোট ছোট গল্প, উপমা বা রূপকের সহায়ে যাহা বলিবার বলিয়া ও বুঝাইয়া গিয়াছেন। লম্বা-চওড়া কথা, দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস প্রভৃতির ধার দিয়াও যান নাই। কিন্তু সে সাদা কথার, সে ছোট উপমার ভিতর এত ভাব ও মানবসাধারণকে উচ্চ আদর্শে পৌঁছাইয়া দিবার এত শক্তি রহিয়াছে যে, আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের ভাবের অন্ত বা শক্তির সীমা এখনও করিতে পারিলাম না। যতই দেখি ততই উচ্চ উচ্চতর ভাব দেখিতে পাই, যতই নাড়াচাড়া তোলাপাড়া করি ততই মন ‘অনিত্য অশুভ’ সংসারের রাজত্ব ছাড়িয়া ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বতর দেশে উঠিতে থাকে, এবং ‘পরমপদপ্রাপ্তি’, ‘ব্রাহ্মীস্থিতি’, ‘মোক্ষ’ বা ‘ভগবদ্দর্শনে’র দিকে – কারণ এক বস্তুকেই নানাভাবে দেখিয়া মহাপুরুষেরা ঐসকল নানা নামে নির্দেশ করিয়াছেন – যতই কেহ অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ঐসকল সাদা কথার গভীর ভাব প্রাণে প্রাণে বুঝিতে থাকে।
দৃষ্টান্ত – গিরিশকে বকলমা দিতে বলা
ইহাই নিয়ম। ঠাকুরের কথা ও ব্যবহার সম্বন্ধেও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখি না। তাঁহার যে কথাগুলি আগে যে ভাবে বুঝিতাম, এখন সেইগুলিরই আরও কতই না গভীর ভাব দেখিতে পাই! দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি কথা বলিলেই চলিবে। শ্রীযুত গিরিশ ঠাকুরের নিকট কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর একদিন তাঁহাকে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন – “এখন থেকে আমি কি করব?”
ঠাকুর – “যা করচ তাই করে যাও। এখন এদিক (ভগবান) ওদিক (সংসার) দুদিক রেখে চল, তারপর যখন একদিক ভাঙবে তখন যা হয় হবে। তবে সকালে-বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো।” – এই বলিয়া গিরিশের দিকে চাহিলেন, যেন তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন।
গিরিশের মনের অবস্থা
গিরিশ শুনিয়া বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন, ‘আমার যে কাজ তাহাতে স্নান-আহার-নিদ্রা প্রভৃতি নিত্যকর্মেরই একটা নিয়মিত সময় রাখিতে পারি না। সকালে-বিকালে স্মরণ-মনন করিতে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইব। তাহা হইলে তো মুশকিল – শ্রীগুরুর আজ্ঞালঙ্ঘনে মহা দোষ ও অনিষ্ট হইবে। অতএব এ কথা কি করিয়া স্বীকার করি? সংসারে অন্য কাহারও কাছে কথা দিয়াই সে কথা না রাখিতে পারিলে দোষ হয়, তা যাঁহাকে পরকালের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি তাঁহার কাছে – !’ গিরিশ মনের কথাগুলি বলিতেও কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, ‘কিন্তু ঠাকুর আমাকে তো আর কোন একটা বিশেষ কঠিন কাজ করিতে বলেন নাই। অপরকে এ কথা বলিলে এখনি আনন্দের সহিত স্বীকার পাইত।’ কিন্তু তিনি কি করিবেন, আপনার একান্ত বহির্মুখ অবস্থা ঠিক ঠিক দেখিতে পাইয়াই বুঝিতেছিলেন যে, ধর্মকর্মের অতটুকু প্রতিদিন করা যেন তাঁহার সামর্থ্যের অতীত। আবার নিজের স্বভাবের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন – কোনরূপ ব্রত বা নিয়মে, ‘চিরকালের নিমিত্ত আবদ্ধ হইলাম’ – এ কথা মনে করিতে গেলেও যেন হাঁপাইয়া উঠেন এবং যতক্ষণ না ঐ নিয়ম ভঙ্গ হয় ততক্ষণ যেন প্রাণে অশান্তি। আজীবন এইরূপ ঘটিয়া আসিয়াছে। নিজের ইচ্ছায় ভালমন্দ যাহা হয় করিতে কোন গোল নাই, কিন্তু যেমন মনে হইল – বাধ্য হইয়া অমুক কাজটা আমাকে করিতে হইতেছে বা হইবে অমনি মন বাঁকিয়া দাঁড়াইল। কাজেই আপনার নিতান্ত অপারগ ও অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিতে করিতে কাতর হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন – ‘করিব’ বা ‘করিতে পারিব না’ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। আর অত সোজা কাজটা করিতে পারিবেন না, একথা লজ্জার মাথা খাইয়া বলেনই বা কিরূপে – বলিলেও ঠাকুর ও উপস্থিত সকলে মনে করিবেনই বা কি? তাঁহার একান্ত অসহায় অবস্থার কথা হয়তো বুঝিতেই পারিবেন না, আর মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মনে নিশ্চয় করিবেন – তিনি একটা ঢঙ করিয়া কথাগুলি বলিতেছেন।
ঠাকুর, গিরিশকে ঐরূপ নীরব দেখিয়া, তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তা যদি না পার তো খাবার শোবার আগে তাঁহার একবার স্মরণ করে নিও।”
গিরিশ নীরব। ভাবিলেন উহাই কি করিতে পারিবেন। দেখিলেন – কোন দিন খান বেলা দশটায়, আর কোন দিন বৈকাল পাঁচটায়; রাত্রির খাওয়া সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। আবার মামলা-মকদ্দমার ফ্যাসাদে পড়িয়া এমন দিন গিয়াছে যে, খাইতে বসিয়াছেন বলিয়াই হুঁশ নাই! কেবলই উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছেন – ‘ব্যারিস্টারকে যে ফি পাঠাইয়াছি তাহা ঠিক সময়ে তাঁহার হাতে পৌঁছিল কি না খবরটা পাইলাম না, মকদ্দমার সময় যদি তিনি উপস্থিত না হন তাহা হইলেই তো বিপদ’ ইত্যাদি। কার্যগতিকে ঐরূপ দিন যদি আবার আসে – আর আসাও কিছু অসম্ভব নয় – তাহা হইলে সেদিন ভগবানের স্মরণ-মনন করিতে তো নিশ্চয় ভুলিবেন! হায় হায়, ঠাকুর এত সোজা কাজ করিতে বলিতেছেন, আর তিনি ‘করিব’ বলিতে পারিতেছেন না! গিরিশ বিষম ফাঁপরে পড়িয়া স্থির, নীরব রহিলেন, আর তাঁহার প্রাণের ভিতরে যেন একটা চিন্তা, ভয় ও নৈরাশ্যের ঝড় বহিতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশের দিকে আবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে এইবার বলিলেন – “তুই বলবি, ‘তাও যদি না পারি’ – আচ্ছা, তবে আমায় বকলমা1 দে।” ঠাকুরের তখন অর্ধবাহ্যদশা!
1. অর্থাৎ ভার দাও। বিষয়কর্মে এক ব্যক্তি তাহার হইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা বা অধিকার অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে সে ব্যক্তি তাহার হইয়া সমস্ত লেন-দেন করে, রসিদ চিঠিপত্র লিখে এবং তাহার নামে ঐসকলে সহি করিয়া নিম্নে ‘বঃ (অর্থাৎ বকলম)’ – অমুক বলিয়া নিজের নাম লিখিয়া দেয়।
বকলমা দেওয়ার পর গিরিশের মনের অবস্থা
কথাটি মনের মতো হইল। গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। শুধু ঠাণ্ডা হইল না, ঠাকুরের অপার দয়ার কথা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভালবাসা ও বিশ্বাস একেবারে অনন্তধারে উছলিয়া উঠিল। গিরিশ ভাবিলেন, ‘যাক্ – নিয়মবন্ধনগুলিকে বাঘ মনে হয়, তাহার ভিতর আর পড়িতে হইল না। এখন যাহাই করি না কেন এইটি মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলেই হইল যে, ঠাকুর তাঁহার অসীম দিব্যশক্তিবলে কোন-না-কোন উপায়ে তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন।’ শ্রীযুত গিরিশ তখন বকলমা বা ঠাকুরের উপর সমস্ত ভার দেওয়ার এইটুকু অর্থই বুঝিলেন – বুঝিলেন তাঁহাকে নিজে চেষ্টা বা সাধন-ভজন করিয়া কোন বিষয় ছাড়িতে হইবে না; ঠাকুরই তাঁহার মন হইতে সকল বিষয় নিজশক্তিবলে ছাড়াইয়া লইবেন।
বকলমা ভালবাসার বন্ধন
কিন্তু নিয়মের বন্ধন গলায় পরা অসহ্য বোধ করিয়া তাহার পরিবর্তে যে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ভালবাসার বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া লইলেন তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না। ভাল মন্দ যে অবস্থায় পড়ুন না কেন, যশ অপযশ যাহাই আসুক না কেন, দুঃখ-কষ্ট যতই উপস্থিত হউক না কেন, নিঃশব্দে তাহা সহ্য করা ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার যে আর বলিবার বা করিবার কিছুই রহিল না, সে কথা তখন আর তলাইয়া দেখিলেন না; দেখিবার শক্তিও হইল না। অন্য সকল চিন্তা মন হইতে সরিয়া যাইয়া কেবল দেখিতে লাগিলেন – শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা! আর বাড়িয়া উঠিল – শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া শতগুণে অহঙ্কার। মনে হইল – ‘সংসারে যে যা বলে বলুক, যতই ঘৃণা করুক, ইনি তো সকল সময়ে সকল অবস্থায় আমার – তবে আর কি? কাহাকে ডরাই?’ ভক্তিশাস্ত্র1 এ অহঙ্কারকে যে সাধনের মধ্যে গণ্য করেন এবং মানবের বহুভাগ্যে আসে বলেন তাহাই বা তখন কেমন করিয়া জানিবেন? যাহা হউক শ্রীযুত গিরিশ এখন নিশ্চিন্ত এবং খাইতে-শুইতে-বসিতে ঐ এক চিন্তা – ‘শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন’ – সর্বদা মনে উদিত থাকিয়া তাঁহাকে যে ঠাকুরের ধ্যান করাইয়া লইতেছে এবং তাঁহার সকল কর্ম ও মনোভাবের উপর একটা ছাপ দিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিতেছে তাহা বুঝিতে না পারিলেও সুখী – কারণ তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) যে তাঁহাকে ভালবাসেন এবং আপনার হইতেও আপনার!
1. নারদ-ভক্তিসূত্র।
গিরিশের অতঃপর শিক্ষা
ঠাকুর চিরকাল শিক্ষা দিয়াছেন, ‘কখনো কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই’ এবং প্রত্যেক ভক্তের সহিত ঐরূপ ব্যবহারও নিত্য করিতেন। শ্রীযুত গিরিশকে পূর্বোক্ত ভাব দিয়া ধরিয়া এখন হইতে ঐ ভাবের উপযোগী শিক্ষাসকলও তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীযুত গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে কোন একটি সামান্য বিষয়ে ‘আমি করিব’ বলায় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, “ও কি গো? অমন করে ‘আমি করিব’ বল কেন? যদি না করতে পার? বলবে – ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তো করব।” গিরিশও বুঝিলেন, ‘ঠিক কথা, আমি যখন ভগবানের উপর সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার দিয়াছি এবং তিনিও সেই ভার লইয়াছেন, তখন তিনি যদি ঐ কার্য আমার পক্ষে করা উচিত বা মঙ্গলকর বলিয়া করিতে দেন তবেই তো করিতে পারিব?’ বুঝিয়া তদবধি আমি করিব, যাইব ইত্যাদি বলা ও ভাবাগুলো ত্যাগ করিতে লাগিলেন।
গিরিশের বকলমার গূঢ় অর্থবোধ
এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে ঠাকুরের অদর্শন হইল; স্ত্রী-পুত্রাদির বিয়োগরূপ নানা দুঃখ-কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল; তাঁহার মন কিন্তু পূর্বের ন্যায় প্রতি ব্যাপারে বলিয়া উঠিতে লাগিল – ‘তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ঐরূপ হওয়া তোর পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়াই ঐসকল হইতে দিয়াছেন। তুই তাঁহার উপর ভার দিয়াছিস, তিনিও লইয়াছেন; কিন্তু কোন্ পথ দিয়া তিনি তোকে লইয়া যাইবেন, তাহা তো আর তোকে লেখাপড়া করিয়া বলেন নাই? তিনি এই পথই তোর পক্ষে সহজ বুঝিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে তোর ‘না’ বলিবার বা বিরক্ত হইবার তো কথা নাই। তবে কি তাঁহার উপর বকলমা বা ভার দেওয়াটা একটা মুখের কথামাত্র বলিয়াছিলি?’ ইত্যাদি। এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল ততই গিরিশের বকলমা দেওয়ার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। এখনই কি উহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারা গিয়াছে? শ্রীযুত গিরিশকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, “এখনও ঢের বাকি আছে! বকলমা দেওয়ার ভিতর যে এতটা আছে তখন কি তা বুঝেছি! এখন দেখি যে সাধন-ভজন-জপ-তপরূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকলমা দিয়েছে তার কাজের আর অন্ত নাই – তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর (ভগবানের) উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া ‘আমি’-টার জোরে সেটি করলে!”
অবতারেরাই বকলমার ভার লইতে পারেন
বকলমার প্রসঙ্গে নানা কথা মনে উদয় হইতেছে। জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই ভগবান যীশু, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণই কখনো কখনো কাহাকেও ঐরূপ অভয় দিয়াছেন। সাধারণ গুরুর ঐরূপ করিবার সামর্থ্য বা অধিকার নাই। সাধারণ গুরু বা সাধুরা মন্ত্র-তন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষ, যাহা দ্বারা তাঁহারা নিজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহাই বড় জোর অপরকে বলিয়া দিতে পারেন। অথবা পবিত্রভাবে নিজ জীবন যাপন করিয়া লোককে পবিত্রতার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু নানা বন্ধনে জড়ীভূত হইয়া মানুষ যখন একেবারে অসহায় অবস্থায় উপস্থিত হয়, যখন ‘এইরূপ কর’ বলিলে সে হতাশ হইয়া বলিয়া উঠে, ‘করিব কিরূপে? করিবার শক্তি দাও তো করি’, তখন তাহাকে সাহায্য করা সাধারণ গুরুর সাধ্যাতীত। ‘তোমার দুষ্কৃতির সকল ভার লইলাম, আমিই তোমার হইয়া ঐ সকলের ফলভোগ করিব’ – একথা মানবকে মানবের বলা ও তদ্রূপ করা সাধ্যাতীত। মানবহৃদয়ে ধর্মের ঐরূপ গ্লানি উপস্থিত হইলেই কৃপায় শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন এবং তাহার হইয়া ফলভোগ করিয়া তাহাকে সেই বন্ধনের আবর্ত হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু ঐরূপ করিলেও তিনি তাহাকে একেবারে রেহাই দেন না। শিক্ষার নিমিত্ত তাহাকে দিয়া কিছু-না-কিছু করাইয়া লন। ঠাকুর যেমন বলিতেন – “তাঁদের (অবতারপুরুষদিগের) কৃপায় মানবের দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মে হয়ে যায়।” ব্যক্তির সম্বন্ধে যেরূপ, জাতির সম্বন্ধেও উহা সেইরূপ সত্য।
তদ্দৃষ্টান্ত
ইহাই গীতায় – বিশ্বরূপদর্শনের জন্য অর্জুনের দিব্যচক্ষুলাভ বলিয়া, পুরাণে – শ্রীভগবানের কৃপালাভ বলিয়া, বৈষ্ণবশাস্ত্রে – জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারসাধন বা পাষণ্ডদলন বলিয়া, এবং খ্রীষ্টান ধর্মে – ঈশার অপরের ভোগটা নিজের ঘাড়ে লইয়া ভগবানের কোপশমন করা (Atonement) বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে যদি ইহার আভাস না পাইতাম, তাহা হইলে কথাটিতে যে সত্য আছে তাহা কখনই বুঝিতে পারিতাম না।
বকলমা সম্বন্ধে ঠাকুরের দর্শন
কলিকাতার শ্যামপুকুরে চিকিৎসার জন্য আসিয়া ঠাকুর যখন থাকেন, তখন একদিন দেখিয়াছিলেন – তাঁহার নিজের সূক্ষ্মশরীরটা স্থূলশরীর হইতে বাহিরে আসিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে! ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “দেখলুম তার পিঠময় ঘা হয়েছে! ভাবচি কেন এমন হলো? আর মা দেখিয়ে দিচ্ছে – যা তা করে এসে যত লোকে ছোঁয়, আর তাদের দুর্দশা দেখে মনে দয়া হয় – সেইগুলো (দুষ্কর্মের ফল) নিতে হয়! সেইসব নিয়ে নিয়ে ঐরূপ হয়েছে। সেইজন্যই তো (নিজের গলা দেখাইয়া) এই হয়েছে। নইলে এ শরীর কখনও কিছু অন্যায় করেনি – এত (রোগ) ভোগ কেন?” আমরা শুনিয়া অবাক! ভাবিতে লাগিলাম – বাস্তবিকই তবে একজন অপরের কৃতকর্মের ফলভোগ করিয়া তাহাকে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে? অনেকে তখন ঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভালবাসায় ভাবিয়াছিলেন – ‘হায় হায়, কেন আমরা ঠাকুরকে মিথ্যা-প্রবঞ্চনাদি নানা দুষ্কর্ম করিয়া আসিয়া ছুঁইয়াছি! আমাদের জন্য তাঁহার এত ভোগ, এত কষ্ট! আর কখনো ঠাকুরের দেবশরীর স্পর্শ করিব না।’
ঠাকুরের ধবলকুষ্ঠ আরোগ্য করা
এ সম্বন্ধে ঠাকুরের আর একটি কথা এখানে মনে পড়িতেছে। কোন সময় একটি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত (ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ) ব্যক্তি আসিয়া ঠাকুরকে কাতর হইয়া ধরে ও বলে যে, তিনি একবার হাত বুলাইয়া দিলেই তাহার ঐ রোগ হইতে নিষ্কৃতি হয়। ঠাকুর তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলেন, “আমি তো কিছু জানি না, বাবু; তবে তুমি বলছ, আচ্ছা, হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। মার ইচ্ছা হয় তো সেরে যাবে।” – এই বলিয়া হাত বুলাইয়া দেন। সে দিন সমস্ত দিন ধরিয়া ঠাকুরের হাতে এমন যন্ত্রণা হয় যে, তিনি অস্থির হইয়া জগদম্বাকে বলেন, “মা আর কখনো এমন কাজ করব না।” ঠাকুর বলিতেন, “তার রোগ সারিয়া গেল – কিন্তু তার ভোগটা (নিজের দেহ দেখাইয়া) এইটের উপর দিয়ে হয়ে গেল।” ঠাকুরের জীবনের ঐসকল ঘটনা হইতেই মনে হয়, বেদ বাইবেল পুরাণ কোরান তন্ত্র-মন্ত্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসকল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোক-সহায়ে বুঝিলে এ যুগে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ঠাকুরও আমাদের বলিয়াছেন – “ওরে, নবাবী আমলের টাকা বাদশাই আমলে চলে না!”
বকলমা দেওয়া সহজ নয়
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বকলমা দেওয়াটা বড় সোজা কথা – দিলেই হইল আর কি। মানুষ প্রবৃত্তির দাস, ধর্মকর্ম করিতে আসিয়াও কেবল সুবিধাই খোঁজে – কিরূপে এদিক-ওদিক, সংসারসুখ ও ভগবদানন্দ, দুইটাই পাইতে পারে তাহাই কেবল দেখিতে থাকে। সংসারের ভোগসুখগুলোকে এত মধুর, এত অমৃতোপম বলিয়া বোধ করে যে, সেগুলোকে ছাড়িতে হইবে মনে হইলেও দশদিক শূন্য দেখে, মনে করে তাহা হইলে কি লইয়া থাকিব। সেজন্য আধ্যাত্মিক জগতে বকলমা দেওয়া চলে শুনিয়াই সে লাফাইয়া উঠে। মনে করে, তবে আর কি? – আমি চুরি জুয়াচুরি বাটপারি যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া যতটা পারি সংসারে সুখভোগ করি আর শ্রীচৈতন্য, যীশু বা শ্রীরামকৃষ্ণ, আমি পরকালটায় – কারণ মরিতে তো একদিন হইবেই – যাহাতে সুখী হইতে পারি, তাহা দেখুন। সে তখন বোঝে না যে, উহা আর কিছুই নহে, কেবল পাজি মনের জুয়াচুরি – বোঝে না যে ঐরূপে সে নিরন্তর আপনাকে আপনি ঠকাইতেছে। বোঝে না যে উহা আর কিছুই নহে, কেবল আপনার দুষ্কৃতসকলের ভীষণ মূর্তি দেখিতে হইবে বলিয়া সাধ করিয়া চক্ষে ঠুলি পরিয়া সর্বনাশের দিকে অগ্রসর হওয়া – বোঝে না যে ঐ ঠুলি একদিন জোর করিয়া একজন খুলিয়া দিবে এবং সে অকূল পাথার দেখিবে – দেখিবে জুয়াচোরের বকলমা কেহ লয় নাই! হায় মানব! কত রকমেই না তুমি আপনাকে আপনি ঠকাইতেছ এবং মনে করিতেছ যে, ‘বড় জিতিয়াছি!’ আর ধন্য মহামায়া! তুমি কি ভেলকিই না মানবমনে লাগাইয়াছ! শ্রীরামপ্রসাদ স্বরচিত গীতে তোমায় সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই সম্পূর্ণ সত্য –
সাবাস মা দক্ষিণাকালী, ভুবন ভেলকি লাগিয়ে দিলি
তোর ভেলকির গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি।
এমন বাজিকরের মেয়ে, রাখলি বাবারে পাগল সাজায়ে
নিজে গুণময়ী হয়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি।
মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি,
প্রসাদ রে সেই চরণ পাবি? – তুইও বুঝি পাগল হলি!
কোন্ অবস্থায় বকলমা দেওয়া চলে
বকলমা অমনি দিলেই দেওয়া যায় না। নানা উদ্যম অধ্যবসায়ের ফলে মনে বকলমা দিবার অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইলে, তখনই মানব উহা ঠিক ঠিক দিতে পারে; আর তখনই শ্রীভগবান তাহার ভার লইয়া থাকেন। সুখী হইবার আশায় সংসারের নানা কাজে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া মানব যখন বাস্তবিকই দেখে – “প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়”, সাধন-ভজন-জপ-তপ করিয়া মানব যখন প্রাণে প্রাণে বুঝে অনন্ত ভগবানকে পাইবার উহা কখনই উপযুক্ত মূল্য হইতে পারে না, অদম্য উদ্যমে পাহাড় কাটিয়া পথ করিয়া লইব ভাবিয়া সকল বিষয়ে লাগিয়া মানব যখন বুঝিতে পারে তাহার কোন ক্ষমতাই নাই, তখন সে ‘কে কোথায় আছ গো, রক্ষা কর’ বলিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিতে থাকে, আর তখনই শ্রীভগবান তাহার বকলমা লইয়া থাকেন।
মনের জুয়াচুরি হইতে সাবধান
নতুবা সাধন-ভজন করিতে বা শ্রীভগবানকে ডাকিতে আমার ভাল লাগে না, যথেচ্ছাচার করিতে ভাল লাগে, অতএব তাহাই করিব, আর কেহ ঐ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে বলিব – ‘কেন? আমি তো ভগবানকে বকলমা দিয়াছি? তিনি আমায় ঐরূপ করাইতেছেন তা কি করিব? মনটি কেন তিনি ফিরাইয়া দেন না?’ – এ বকলমা কেবল পরকে ফাঁকি দিবার এবং নিজেও ফাঁকিতে পড়িবার বকলমা; উহাতে ‘ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ’ হইতে হয়।
বকলমার শেষ কথা
আর একদিক দিয়া কথাটির আলোচনা করিলে আরও পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে। আচ্ছা বুঝিলাম – তুমি বকলমা দিয়াছ, তোমার শ্রীভগবানকে ডাকিবার বা সাধন-ভজন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ঠিক ঠিক বকলমা দিলে তোমার প্রাণে প্রাণে সর্বক্ষণ তাঁহার করুণার কথা উদয় হইতে থাকিবেই থাকিবে – মনে হইবে যে, এই অপার সংসারসমুদ্রে পড়িয়া এতদিন হাবু-ডুবু খাইতেছিলাম, আহা, তিনি আমায় কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন! বল দেখি, ঐরূপ অনুভবে তাঁহার উপর তোমার কতটা ভক্তি-ভালবাসার উদয় হইবে! তোমার হৃদয় তাঁহার উপর কৃতজ্ঞতা ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া সর্বদাই যে তাঁহার কথা ভাবিতে ও তাঁহার নাম লইতে থাকিবে – উহা করিতে তোমাকে কি আর বলিয়া দিতে হইবে? সর্পের ন্যায় ক্রূর প্রাণীও আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া বাস্তুসাপ হয় ও বাটীর কাহাকেও দংশন করে না। তোমার হৃদয় কি উহা অপেক্ষাও নীচ যে, যিনি তোমার ইহকাল পরকালের ভার লইলেন, তত্রাচ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভালবাসায় পূর্ণ হইল না? অতএব বকলমা দিয়া যদি দেখ – তোমার ভগবানকে ডাকিতে ভাল লাগে না, তাহা হইলে বুঝিও তোমার বকলমা দেওয়া হয় নাই এবং তিনিও তোমার ভার গ্রহণ করেন নাই। ‘বকলমা দিয়াছি’ বলিয়া আর আপনাকে ঠকাইও না এবং অপাপবিদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক ভগবানে নিজকৃত দুষ্কৃতির কালিমা অর্পণ করিও না। উহাতে আপনারই সমূহ ক্ষতি ও অমঙ্গল। ঠাকুরের ‘ব্রাহ্মণের গোহত্যা’ গল্পটি মনে রাখিও:
ঠাকুরের ‘ব্রাহ্মণ ও গোহত্যা’র গল্প
এক ব্রাহ্মণ অনেক যত্ন ও পরিশ্রমে একখানি সুন্দর বাগান করিয়াছিল। নানাজাতীয় ফল-ফুলের গাছ পুঁতিয়াছিল ও সেগুলি দিন দিন নধর হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণের আনন্দের আর সীমা ছিল না। এখন একদিন দরজা খোলা পাইয়া একটা গরু ঢুকিয়া সেই গাছগুলি মুড়াইয়া খাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কার্যান্তরে গিয়াছিল। আসিয়া দেখে তখনও গরুটা গাছ খাইতেছে। বিষম কোপে তাড়া করিয়া সেটাকে যেমন এক ঘা লাঠি মারিয়াছে, আর অমনি মর্মস্থানে আঘাত লাগায় গরুটা মরিয়া গেল! ব্রাহ্মণের তখন প্রাণে ভয় – তাইতো, হিন্দু হইয়া গোহত্যা করিলাম? গোহত্যার তুল্য যে পাপ নাই! ব্রাহ্মণ একটু-আধটু বেদান্ত পড়িয়াছিল। দেখিয়াছিল তাহাতে লেখা আছে যে, বিশেষ বিশেষ দেবতার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া মানবের ইন্দ্রিয়সকল স্ব-স্ব কার্য করে। যথা – সূর্যের শক্তিতে চক্ষু দেখে, পবনের শক্তিতে কর্ণ শুনে, ইন্দ্রের শক্তিতে হস্ত কার্য করে, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের সেই কথাগুলি এখন মনে পড়ায় ভাবিল – ‘তবে তো আমি গোহত্যা করি নাই। ইন্দ্রের শক্তিতে হস্ত চালিত হইয়াছে – ইন্দ্রই তবে তো গোহত্যা করিয়াছে!’ কথাটি মনে মনে পাকা করিয়া ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইল।
এদিকে গোহত্যা-পাপ ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করিতে আসিল, কিন্তু ব্রাহ্মণের মন তাহাকে তাড়াইয়া দিল। বলিল, “যাও, এখানে তোমার স্থান নাই; গোহত্যা ইন্দ্র করিয়াছে, তাহার কাছে যাও।” কাজেই পাপ ইন্দ্রকে ধরিতে গেল। ইন্দ্র পাপকে বলিলেন, “একটু অপেক্ষা কর, আমি ব্রাহ্মণের সহিত দুটো কথা কহিয়া আসি, তারপর আমায় ধরিও।” ঐ কথা বলিয়া ইন্দ্র মানবরূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিলেন ও দেখিলেন ব্রাহ্মণ অদূরে দাঁড়াইয়া গাছপালার তদারক করিতেছে। ইন্দ্র উদ্যানের শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মণের যাহাতে কানে যায় এমনভাবে প্রশংসা করিতে করিতে ধীরপদে ব্রাহ্মণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বলিলেন – “আহা, কি সুন্দর বাগান, কি রুচির সহিত গাছপালাগুলি লাগানো হইয়াছে, যেখানে যেটি দরকার ঠিক সেখানে সেটি পোঁতা রহিয়াছে!” এইপ্রকার বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন – “মহাশয়, বলিতে পারেন বাগানখানি কার? এমন সুন্দরভাবে গাছপালাগুলি কে লাগাইয়াছে?” ব্রাহ্মণ উদ্যানের প্রশংসা শুনিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল – “আজ্ঞা এখানি আমার; আমিই এগুলি সব পুঁতিয়াছি। আসুন না, ভাল করিয়া বেড়াইয়া দেখুন না।” এই বলিয়া উদ্যান সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে বলিতে ইন্দ্রকে উদ্যানমধ্যস্থ সব দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং ক্রমে ভুলিয়া মৃত গরুটা যথায় পড়িয়াছিল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ইন্দ্র যেন একেবারে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন – “রাম, রাম, এখানে গোহত্যা করিল কে?” ব্রাহ্মণ, এতক্ষণ উদ্যানের সকল পদার্থই ‘আমি করিয়াছি, আমি করিয়াছি’ বলিয়া আসিয়াছে; কাজেই গোহত্যা কে করিল জিজ্ঞাসায় বিষম ফাঁপরে পড়িয়া একেবারে নির্বাক – চুপ! তখন ইন্দ্র নিজরূপ পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, “তবে রে ভণ্ড, উদ্যানের যাহা কিছু ভাল সব তুমি করিয়াছ, আর গোহত্যাটাই কেবল আমি করিয়াছি, বটে? নে তোর গোহত্যা-কৃত পাপ।” এই বলিয়া ইন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন এবং পাপও আসিয়া ব্রাহ্মণের শরীর অধিকার করিল।
সাধকের মনের উন্নতির সহিত ঠাকুরের কথার গভীর অর্থবোধ
যাক এখন বকলমার কথা, আমরা পূর্বপ্রসঙ্গের অনুসরণ করি। ঠাকুরের প্রত্যেক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, ঠাকুরের কথাগুলির পূর্বে তাঁহারা যে অর্থগ্রহণে সমর্থ হইতেন, এখন যত দিন যাইতেছে তত সেইগুলির ভিতর আরও কত গভীর অর্থ তাঁহার কৃপায় বুঝিতে পারিতেছেন। আবার ঠাকুরের অনেক কথা বা ব্যবহার, যাহার অর্থ আমরা তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কেবল হাঁ করিয়া শুনিয়া গিয়াছি মাত্র, তাহাদের ভিতর এখন অপূর্ব অর্থ ও ভাব উপলব্ধি করিয়া অবাক হইয়া থাকিতে হয়!
‘কালে হবে’
ঠাকুরের কথাই ছিল – “ওরে, কালে হবে, কালে বুঝবি। বিচিটা পুঁতলেই কি অমনি ফল পাওয়া যায়? আগে অঙ্কুর হবে, তারপর চারাগাছ হবে, তারপর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধরবে, তারপর ফল – সেই রকম। তবে লেগে থাকতে হবে, ছাড়লে হবে না; এই গানটায় কি বলছে শোন।” এই বলিয়া ঠাকুর মধুর কণ্ঠে গান ধরিতেন –
হরিষে লাগি রহো রে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই – তেরা বিগড় বাত বনি যাই॥
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে তারে সুজন কসাই
(আওর্) শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাঈ।
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা, বেনিয়া বয়েল চালাই
(আওর্) এক বাতকো টাণ্টা পড়ে তো খোঁজ খবর না পাই।
এয়্সী ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাঈ
সেবা বন্দি আওর্ অধীনতা সহজ মিলি রঘুরাঈ॥
সাধনে লাগিয়া থাকা আবশ্যক
– গান গাহিয়া আবার বলিতেন, “তাঁর সেবা, বন্দনা ও অধীনতা – কি না দীনভাব, এই নিয়ে বিশ্বাস করে পড়ে থাকতে থাকতে সব হবে, তাঁর দর্শন পাওয়া যাবেই যাবে। তা না করে ছেড়ে দিলে কিন্তু ঐ পর্যন্তই হলো। একজন চাকরি করে কষ্টে-সৃষ্টে কিছু কিছু করে টাকা জমাত। একদিন গুণে দেখে যে হাজার টাকা জমেছে। অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে মনে করলে, তবে আর কেন চাকরি করা? হাজার টাকা তো জমেছে, আর কি? এই বলে চাকরি ছেড়ে দিলে। এতটুকু আধার, এতটুকু আশা! ঐ পেয়েই সে ফুলে উঠল, ধরাকে সরাখানা দেখতে লাগল। তারপর – হাজার টাকা খরচ হতে আর কদিন লাগে? অল্প দিনেই ফুরিয়ে গেল। তখন দুঃখে-কষ্টে আবার চাকরির জন্য ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াতে লাগল। ও রকম করলে চলবে না, তাঁর (ভগবানের) দ্বারে পড়ে থাকতে হবে; তবে তো হবে।”
ম্যাদাটে ভক্তি ত্যাগ করা
আবার কখনো কখনো গানটির দ্বিতীয় চরণ – ‘তেরা বনত বনত বনি যাই’ অর্থাৎ ভক্তি করিতে করিতে ফল পাওয়া যাইবে – গাহিতে গাহিতে বলিয়া উঠিতেন – “দূর শালা! ‘বনত বনত’ কি? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নাই। মনে জোর করতে হয় – এখনি হবে, এখনি তাঁকে পাব। ম্যাদাটে ভক্তির কর্ম কি তাঁকে পাওয়া?”
ভাবঘনমূর্তি ঠাকুরের প্রত্যেক ভাবের সহিত দৈহিক পরিবর্তন
ঠাকুরকে দেখিলেই বাস্তবিকই মনে হইত, যেন একটি জ্বলন্ত ভাবঘনমূর্তি! – যেন পুঞ্জীকৃত ধর্মভাবরাশি একত্র সম্বদ্ধ হইয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে বলিয়াই আমরা তাঁহার একটা আকার ও রূপ দেখিতে পাইতেছি! মনের ভাব-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটার পরিবর্তন হওয়ার কথা আমরা বলিয়াই থাকি ও কালে-ভদ্রে কখনো একটু-আধটু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; কিন্তু মনের ভাবতরঙ্গ যে শরীরে এতটা পরিবর্তন আনিয়া দিতে পারে, তাহা কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই। নির্বিকল্প সমাধিতে ‘আমি’-জ্ঞানের একেবারে লোপ হইল – আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের হাতের নাড়ি, হৃদয়ের স্পন্দন, সব বন্ধ হইয়া গেল; শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি ডাক্তারেরা যন্ত্রসহায়ে পরীক্ষা করিয়াও হৃৎপিণ্ডের কার্য কিছুই পাইলেন না।1 তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জনৈক ডাক্তার বন্ধু ঠাকুরের চক্ষুর তারা বা মণি অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিলেন – তথাচ উহা মৃত ব্যক্তির ন্যায় কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না! ‘সখীভাব’-সাধনকালে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী ভাবিতে ভাবিতে মন তন্ময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরেও স্ত্রী-সুলভ ভাব উঠা-বসা, দাঁড়ানো, কথা কহা প্রভৃতি প্রত্যেক কার্যে এমন প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, শ্রীযুত মথুরানাথ মাড় প্রভৃতি যাহারা চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সঙ্গে উঠা-বসা করিত, তাহারাও তাঁহাকে দেখিয়া অনেকবার কোন আগন্তুক স্ত্রীলোক হইবে বলিয়া ভ্রমে পড়িল। এইরূপ কত ঘটনাই না আমরা দেখিয়াছি ও ঠাকুরের নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছি – যাহাতে বর্তমান মনোবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের বাঁধা-ধরা নিয়মগুলিকে পালটাইয়া বাঁধিতে হয়। সেসব কথা বলিলেও কি লোকে বিশ্বাস করিবে?
1. গলরোগের চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরের বাসায় যখন ঠাকুর থাকেন, তখন আমাদের সম্মুখে এই পরীক্ষা হয়।
ঠাকুরের সকলের সকলপ্রকার ভাব ধরিবার ক্ষমতা
কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় দেখিয়াছি ঠাকুরের ভাবরাজ্যের সর্বত্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা – ছোট-বড় সব রকম ভাব বুঝিতে পারা। বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলের মনোভাব – বিষয়ী, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত, স্ত্রী, পুরুষ সকলের হৃদ্গত ভাব ধরিয়া কে কোন্ পথে কতদূর ধর্মরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছে, পূর্ব সংস্কারানুযায়ী ঐ পথ দিয়া অগ্রসর হইতে তাহার কিরূপ সাধনেরই বা বর্তমানে প্রয়োজন, সকল কথা বুঝিতে পারা ও তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করা। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ঠাকুর যেন মানবমনে যতপ্রকার ভাব উঠিয়াছে, উঠিতে পারে বা পরে উঠিবে, সে সকল ভাবই নিজ জীবনে অনুভব করিয়া বসিয়া আছেন এবং ঐসকল ভাবের প্রত্যেকটি তাঁহার নিজের মনের ভিতর আবির্ভাব হইতে তিরোভাবকাল পর্যন্ত পর পর তাঁহার যে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন! আর তজ্জন্যই ইতরসাধারণ মানব যে যখন আসিয়া যে ভাবের কথা বলিতেছে, নিজের ঐসকল পূর্বানুভূত ভাবের সহিত মিলাইয়া তখনি তাহা ধরিতেছেন, বুঝিতেছেন ও তদুপযোগী বিধান করিতেছেন। সকল বিষয়েই যেন এইরূপ। মায়ামোহ, সংসার-তাড়না, ত্যাগ-বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই কেহ কোন অবস্থায় পড়িয়া উহা হইতে উদ্ধার হইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া কাতর-জিজ্ঞাসু হইয়া আসিলে ঠাকুর পথের সন্ধান তো দিয়া দিতেনই, আবার অনেক সময়েই সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঐ অবস্থায় পড়িয়া যেরূপ অনুভূতি হইয়াছিল তাহাও বলিতেন। বলিতেন, “ওগো, তখন এইরূপ হইয়াছিল ও এইরূপ করিয়াছিলাম” ইত্যাদি। বলিতে হইবে না। – ঐরূপ করায় জিজ্ঞাসুর মনে কত ভরসার উদয় হইত এবং ঠাকুর তাহার জন্য যে পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন, কতদূর বিশ্বাস ও উৎসাহে সে সেই পথে অগ্রসর হইত। শুধু তাহাই নহে, এইরূপে নিজ জীবনের ঘটনা বলায় জিজ্ঞাসুর মনে হইত, ঠাকুর তাহাকে কত ভালবাসেন! – আপনার মনের কথাগুলি পর্যন্ত বলেন! দুই-একটি দৃষ্টান্তেই বিষয়টি সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে।
১ম দৃষ্টান্ত – মণিমোহনের পুত্রশোকের কথা
সিঁদুরিয়াপটির শ্রীযুত মণিমোহন মল্লিকের একটি উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইল। মণিমোহন পুত্রের সৎকার করিয়াই ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া বিমর্ষভাবে ঘরের একপাশে বসিলেন। দেখিলেন, ঘরে স্ত্রী-পুরুষ অনেকগুলি জিজ্ঞাসু ভক্ত বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুর তাঁহাদের সহিত নানা সৎপ্রসঙ্গ করিতেছেন। বসিবার অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুরের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল এবং ঘাড় নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি গো? আজ এমন শুকনো দেখছি কেন?”
মণিমোহন বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে উত্তর করিলেন – (পুত্রের নাম করিয়া) অমুক আজ মারা পড়িয়াছে।
বৃদ্ধ মণিমোহনের সেই রুক্ষবেশ ও শোকনিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ সকলেই স্তম্ভিত, নীরব! সকলেই বুঝিলেন, বৃদ্ধের হৃদয়ের সেই গভীর মর্মবেদনা ও উথলিত শোকাবেগ বাক্যে রুদ্ধ হইবার নহে। তথাচ বৃদ্ধের বিলাপ ও ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া – সংসারের ধারাই ঐ প্রকার, সকলকেই একদিন মরিতে হইবে, যাহা হইয়াছে সহস্র ক্রন্দনেও তাহা ফিরিবার নহে, অতএব শোক পরিত্যাগ কর, সহ্য কর – এইরূপ নানা কথায় তাঁহাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই মানব শোকসন্তপ্ত নরনারীকে ঐসকল কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া আসিতেছে; কিন্তু হায়, কয়টা লোকের প্রাণ তাহাতে শান্ত হইতেছে? কেনই বা হইবে? মন, মুখ এবং অনুষ্ঠিত কর্ম – তিনটি পদার্থ একই ভাবে ভাবিত থাকিলে তবেই আমাদের উচ্চারিত বাক্যসমূহ অপরের প্রাণস্পর্শ করিয়া তাহাতে সমভাবের তরঙ্গ উত্থাপিত করিতে পারে। এখানে যে তাহার একান্তাভাব! আমরা মুখে সংসার অনিত্য বলিয়া প্রতি চিন্তায় ও কার্যে তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; নিশার স্বপ্নসম সংসারটা অনিত্য বলিয়া ভাবিতে অপরকে উপদেশ করিয়া নিজে সর্বদা প্রাণে প্রাণে উহাকে নিত্য বলিয়া ভাবি এবং চিরকালের মতো এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া থাকি। আমাদের কথায় সে শক্তি কোথা হইতে আসিবে?
অপর সকলে মণিমোহনকে ঐরূপে নানা কথা কহিলেও ঠাকুর এক্ষেত্রে অনেকক্ষণ কোন কথাই না কহিয়া মণিমোহনের শোকোচ্ছ্বাস কেবল শুনিয়াই যাইতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার সেই উদাসীন ভাব দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইয়া ভাবিতেও লাগিলেন – ইঁহার হৃদয় কি কঠোর, কি করুণাশূন্য!
বৃদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন এবং সহসা তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীযুক্ত মণিমোহনকে লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব তেজের সহিত গান ধরিলেন –
জীব সাজ সমরে।
ঐ দেখ্ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
আরোহণ করি মহাপুণ্য-রথে ভজন-সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে তাতে
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান ভক্তি-ব্রহ্মবাণ সংযোগ কর রে।
আর এক যুক্তি আছে শুন সুসঙ্গতি,
সব শত্রু নাশের চাইনে রথরথী
রণভূমি যদি করেন দাশরথি ভাগীরথীর তীরে॥
গানের বীরত্বব্যঞ্জক সুর ও তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী ঠাকুরের নয়ন হইতে নিঃসৃত বৈরাগ্য ও তেজের সহিত মিলিত হইয়া সকলের প্রাণে তখন এক অপূর্ব আশা ও উদ্যমের স্রোত প্রবাহিত করিল। সকলেরই মন তখন শোক-মোহের রাজ্য হইতে উত্থিত হইয়া এক অপূর্ব ইন্দ্রিয়াতীত, সংসারাতীত, বিমল ঈশ্বরীয় আনন্দে পূর্ণ হইল। মণিমোহনও উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এখন শোক-তাপ ভুলিয়া স্থির, গম্ভীর, শান্ত!
গীত সাঙ্গ হইল – কিন্তু গীতোক্ত কয়েকটি বাক্যের সহায়ে ঠাকুর যে দিব্য ভাবতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঘর অনেকক্ষণ অবধি জমজম করিতে লাগিল। ঈশ্বরই একমাত্র আপনার, মন-প্রাণ তাঁহাকে অর্পণ করিলাম – তিনি কৃপা করুন, দর্শন দিন – এই ভাবে আত্মহারা হইয়া সকলে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইলে তিনি মণিমোহনের নিকটে বসিয়া বলিতে লাগিলেন –
“আহা! পুত্রশোকের মতো কি আর জ্বালা আছে? খোলটা (দেহ) থেকে বেরোয় কি না? খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ – যতদিন খোলটা থাকে ততদিন থাকে।”
এই বলিয়া ঠাকুর নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। এমন বিমর্ষ-গম্ভীরভাবে ঠাকুর কথাগুলি বলিতে লাগিলেন যে, স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন আপনার আত্মীয়ের মৃত্যু পুনরায় চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছেন! বলিলেন, “অক্ষয় মলো – তখন কিছু হলো না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম – যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে; তলোয়ারের কিছু হলো না – যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল! দেখে খুব আনন্দ হলো – খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম! তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল! তার পরদিন (ঘরের পূর্বে, কালীবাড়ির উঠানের সামনের বারাণ্ডার দিকে দেখাইয়া) ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কি, যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা যেমন নিংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্চে, অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি কচ্চে! ভাবলুম, মা, এখানে (আমার) পোঁদের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল! এখানেই (আমার) যখন এরকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়! – তাই দেখাচ্ছিস, বটে!”
কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, “তবে কি জান? যারা তাঁকে (ভগবানকে) ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সামলে যায়। চুনোপুঁটির মতো আধারগুলো একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গায় স্টীমারগুলো গেলে জেলেডিঙিগুলো কি করে? মনে হয় যেন একেবারে গেল – আর সামলাতে পারলে না। কোনখানা বা উলটেই গেল। আর বড় বড় হাজারমুণে কিস্তিগুলো দু-চারবার টাল-মাটাল হয়েই যেমন তেমনি – স্থির হলো। দু-চারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে।”
আবার কিছুক্ষণ বিমর্ষ-গম্ভীরভাবে থাকিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, “কয়দিনের জন্যেই বা সংসারের এসকলের (পুত্রাদির) সঙ্গে সম্বন্ধ! মানুষ সুখের আশায় সংসার করতে যায় – বিয়ে করলে, ছেলে হলো, সেই ছেলে আবার বড় হলো, তার বিয়ে দিলে – দিন কতক বেশ চলল। তারপর এটার অসুখ, ওটা মলো, এটা বয়ে গেল – ভাবনায়, চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত; যত রস মরে তত একেবারে ‘দশ ডাক’ ছাড়তে থাকে। দেখনি? – ভিয়েনের উনুনে কাঁচা সুঁদরীর চেলাগুলো প্রথমটা বেশ জ্বলে। তারপর কাঠখানা যত পুড়ে আসে কাঠের সব রসটা পেছনের দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গ্যাঁজলার মতো হয়ে ফুটতে থাকে আর চুঁ-চাঁ, ফুস-ফাস নানারকম আওয়াজ হতে থাকে – সেই রকম।” এইপ্রকারে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা এবং শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াতেই একমাত্র সুখ – ইত্যাদি বিষয়ে নানা কথা কহিয়া মণিমোহনকে বুঝাইতে লাগিলেন। মণিমোহনও সামলাইয়া বলিলেন, “এইজন্যই তো আপনার কাছে ছুটে এলুম। বুঝলুম – এ জ্বালা আর কেউ শান্ত করতে পারবে না।”
আমরা তখন ঠাকুরের এই অদৃষ্টপূর্ব ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম – ইঁহাকেই আমরা পূর্বে কঠোর উদাসীন ভাবিতেছিলাম। যিনি যথার্থ মহৎ তাঁহার ছোট ছোট কাজগুলিও অপর সাধারণের ন্যায় হয় না। ছোট-বড় প্রত্যেক কার্যেই তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এইমাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে সমাধি বা ঈশ্বরের সহিত নৈকট্য-উপলব্ধিতে যাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন পর্যন্ত রহিত হইয়া গিয়াছিল, ইনি কি তিনি? সেই ঠাকুরই কি বাস্তবিক মণিমোহনের অবস্থার সহিত সহানুভূতিতে একেবারে সাধারণ মানবের ন্যায় হইয়াছেন? ‘মায়া হ্যায়’ – ছোট কথা বলিয়া বৃদ্ধের কথা ইনি তো উড়াইয়া দিতে পারিতেন? সে ক্ষমতা যে ইঁহার নাই তাহা তো নহে। কিন্তু ঐরূপে মহত্ত্বখ্যাপন করিলে বুঝিতাম, ইনি বড় হন বা আর যাহা কিছু হন, লোকগুরু – জগদ্গুরু ঠাকুর নহেন। বুঝিতাম, মানবসাধারণের ভাব বুঝিবার ইঁহার ক্ষমতা নাই এবং বলিতাম, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি মমতায় দুর্বল মানব আমাদের মতো অসহায় অবস্থায় ইনি যদি একবার পড়িতেন, তবে কেমন করিয়া মায়ার খেলায় উদাসীন থাকিতে পারিতেন তাহা দেখিতাম।
২য় দৃষ্টান্ত – কাম দূর করা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা
পরক্ষণেই আবার হয়তো কোন যুবক আসিয়া বিষণ্ণচিত্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, “মশায়, কাম কি করে যায়? এত চেষ্টা করি, তবুও মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ও কুভাব মনে উপস্থিত হয়ে বড় অশান্তি আসে।”
ঠাকুর – “ওরে, ভগবদ্দর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তা (ভগবানের দর্শন) হলেও শরীর যতদিন থাকে ততদিন একটু-আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুই কি মনে করিস আমারই একেবারে গেছে? এক সময়ে মনে হয়েছিল যে কামটাকে জয় করেছি। তারপর পঞ্চবটীতে বসে আছি, আর এমনি কামের তোড় এল যে আর যেন সামলাতে পারিনি! তারপর ধুলোয় মুখ ঘসড়ে কাঁদি আর মাকে বলি, ‘মা, বড় অন্যায় করেছি, আর কখনো ভাবব না যে কাম জয় করেছি’ – তবে যায়। কি জানিস – (তোদের) এখন যৌবনের বন্যা এসেছে! তাই বাঁধ দিতে পাচ্ছিস না। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাধ মানে? বাঁধ উছলে ভেঙে জল ছুটতে থাকে। লোকের ধান-ক্ষেতের ওপর এক বাঁশ সমান জল দাঁড়িয়ে যায়! তবে বলে – কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়। আর মনে একবার আধবার কখনো কুভাব এসে পড়ে তো – ‘কেন এল’ বলে বসে বসে তাই ভাবতে থাকবি কেন? ওগুলো কখনো কখনো শরীরের ধর্মে আসে যায় – শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টার মতো মনে করবি। শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টা হয়েছিল বলে লোকে কি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে? সেই রকম ভাবগুলোকে অতি সামান্য, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান করে মনে আর আনবি না। আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা করবি, হরিনাম করবি ও তাঁর কথাই ভাববি। ও ভাবগুলো এল কি গেল – সেদিকে নজর দিবি না। এরপর ওগুলো ক্রমে ক্রমে বাঁধ মানবে।” যুবকের কাছে ঠাকুর যেন এখন যুবকই হইয়া গিয়াছেন!
৩য় দৃষ্টান্ত – যোগানন্দকে ঐ সম্বন্ধে উপদেশ
এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত যোগেনের কথা মনে পড়িতেছে। স্বামী যোগানন্দ, যাঁহার মতো ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ বিরল দেখিয়াছি, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে একদিন ঐ প্রশ্ন করেন। তাঁহার বয়স তখন অল্প, বোধ হয় ১৪।১৫ হইবে এবং অল্পদিনই ঠাকুরের নিকট গতায়াত করিতেছেন। সে সময় নারায়ণ নামে এক হঠযোগীও দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে কুটিরে থাকিয়া নেতি-ধৌতি1 ইত্যাদি ক্রিয়া দেখাইয়া কাহাকেও কাহাকেও কৌতূহলাকৃষ্ট করিতেছে। যোগেন স্বামীজী বলিতেন, তিনিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং ঐসকল ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, ঐসকল না করিলে বোধ হয় কাম যায় না এবং ভগবদ্দর্শনও হয় না। তাই প্রশ্ন করিয়া বড় আশায় ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর কোন একটা আসন-টাসন বলিয়া দিবেন, বা হরীতকী কি অন্য কিছু খাইতে বলিবেন, বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া শিখাইয়া দিবেন। যোগেন স্বামীজী বলিতেন – “ঠাকুর আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ‘খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে।’ কথাটা আমার একটুও মনের মতো হলো না। মনে মনে ভাবলুম – উনি কোন ক্রিয়া-ট্রিয়া জানেন না কিনা, তাই একটা যা তা বলে দিলেন। হরিনাম করলে আবার কাম যায়! তাহলে এত লোক তো কচ্চে, যাচ্ছে না কেন? তারপর একদিন কালীবাটীর বাগানে এসে ঠাকুরের কাছে আগে না গিয়ে পঞ্চবটীতে হঠযোগীর কাছে দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা মুগ্ধ হয়ে শুনছি, এমন সময় দেখি ঠাকুর স্বয়ং সেখানে এসে উপস্থিত। আমাকে দেখেই ডেকে আমার হাত ধরে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, ‘তুই ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাসনি। ওসব (হঠযোগের ক্রিয়া) শিখলে ও করলে শরীরের উপরেই মন পড়ে থাকবে। ভগবানের দিকে যাবে না।’ আমি কিন্তু ঠাকুরের কথাগুলি শুনে ভাবলুম – পাছে আমি ওঁর (ঠাকুরের) কাছে আর না আসি, তাই এইসব বলছেন। আমার বরাবরই আপনাকে বড় বুদ্ধিমান বলে ধারণা, কাজেই বুদ্ধির দৌড়ে ঐরূপ ভাবলুম আর কি। আমি তাঁর কাছে আসি বা না-ই আসি তাতে তাঁর (ঠাকুরের) যে কিছুই লাভ-লোকসান নাই – একথা তখন মনেও এল না। এমন পাজি সন্দিগ্ধ মন ছিল। ঠাকুরের কৃপার শেষ নাই, তাই এত সব অন্যায় ভাব মনে এনেও স্থান পেয়েছিলাম। তারপর ভাবলুম – উনি (ঠাকুর) যা বলেছেন, তা করেই দেখি না কেন – কি হয়? এই বলে একমনে খুব হরিনাম করতে লাগলুম। আর বাস্তবিকই অল্পদিনেই, ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পেতে লাগলুম।”
1. দুই অঙ্গুলি চওড়া ও দশ-পনর হাত লম্বা একটা ন্যাকড়ার ফালি ভিজাইয়া আস্তে আস্তে গিলিয়া ফেলা ও পরে তাহা আবার টানিয়া বাহির করার নাম নেতি। আর ২/৩ সের জল খাইয়া পুনরায় বমন করিয়া ফেলার নাম ধৌতি। গুহ্যদ্বার দিয়া জল টানিয়া বাহির করাকেও ধৌতি বলে। হঠযোগীরা এইরূপে শরীরমধ্যস্থ সমস্ত শ্লেষ্মাদি বাহির করিয়া ফেলেন। তাঁহারা বলেন – ইহাতে শরীরে রোগ আসিতে পারে না এবং উহা দৃঢ় হয়।
৪র্থ দৃষ্টান্ত – মণিমোহনের আত্মীয়ার কথা
এইরূপে সকলের অবস্থা ও ভাব ধরিবার কথার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সিঁদুরিয়াপটির মল্লিক মহাশয়ের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার ভক্তিমতী জনৈকা আত্মীয়াও ঠাকুরের নিকট যাওয়া-আসা করিতেন। একদিন আসিয়া তিনি বিশেষ কাতরভাবে জানাইলেন যে, ভগবানের ধ্যান করিতে বসিলে সংসারের চিন্তা, এর কথা, তার মুখ ইত্যাদি মনে পড়িয়া বড়ই অশান্তি আসে। ঠাকুর অমনি তাঁর ভাব ধরিলেন; বুঝিলেন, ইনি কাহাকেও ভালবাসেন – যাহার কথা ও মুখ মনে পড়ে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কার মুখ মনে পড়ে গো? সংসারে কাকে ভালবাস বল দেখি?” তিনি উত্তর করিলেন, “একটি ছোট ভ্রাতুষ্পুত্রকে” – যাহাকে তিনি মানুষ করিতেছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “বেশ তো, তার জন্য যা কিছু করবে, তাকে খাওয়ানো-পরানো ইত্যাদি সব, গোপাল ভেবে করো। যেন গোপাল-রূপী ভগবান তার ভেতরে রয়েছেন – তুমি তাকেই খাওয়াচ্চ, পরাচ্চ, সেবা করচ – এই রকম ভাব নিয়ে কর। মানুষের করচি ভাববি কেন গো? যেমন ভাব তেমন লাভ।” শুনিতে পাই ঐরূপ করার ফলে অল্পদিনেই তাঁহার বিশেষ মানসিক উন্নতি, এমনকি ভাবসমাধি পর্যন্ত হইয়াছিল।
ঠাকুরের স্ত্রীজাতির সর্বপ্রকার মনোভাব ধরিবার ক্ষমতা
ঠাকুরের নিজের পুরুষশরীর ছিল, সেজন্য তাঁহার পুরুষের ভাব বুঝা ও ধরাটা কতক বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু স্ত্রীজাতি – কোমলতা, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি মনোভাবের জন্য ভগবান যাহাদের পুরুষ অপেক্ষা একটা অঙ্গই অধিক দিয়াছেন – তাহাদের সকল ভাব ঠাকুর কি করিয়া ঠিক ঠিক ধরিতেন, তাহা ভাবিলে আর আশ্চর্যের সীমা থাকে না। ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তেরা বলেন, “ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলিয়াই অনেক সময় মনে হইত না। মনে হইত – যেন আমাদেরই একজন। সেজন্য পুরুষের নিকটে আমাদের যেমন সঙ্কোচ-লজ্জা আসে, ঠাকুরের নিকটে তাহার কিছুই আসিত না। যদি বা কখনো আসিত তো তৎক্ষণাৎ আবার ভুলিয়া যাইতাম ও আবার নিঃসঙ্কোচে মনের কথা খুলিয়া বলিতাম।”
উহার কারণ
‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখী বা দাসী আমি’ – এই ভাবনা দীর্ঘকাল ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া তন্ময় হইয়া ‘পুরুষ আমি’ এ ভাবটি ঠাকুর একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই কি ঐরূপ হইত? পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন, ‘তোমার মন হইতে হিংসা যদি একেবারে ত্যাগ হয়, তো মানুষের তো কথাই নাই, জগতে কেহই – বাঘ সাপ প্রভৃতিও – তোমাকে আর হিংসা করিবে না! তোমাকে দেখিয়া তাহাদের মনে হিংসা-প্রবৃত্তিরই উদয় হইবে না।’ হিংসার ন্যায় কাম-ক্রোধাদি অন্য সকল বিষয়েও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। পুরাণে এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি বলিলেই চলিবে। মায়াহীন নিষ্কলঙ্ক যুবক শুক ভগবদ্ভাবে অহরহঃ নিমগ্ন থাকিয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতেছেন, আর বৃদ্ধ পিতা ব্যাস পুত্রমায়ায় অন্ধ হইয়া ‘কোথা যাও, কোথা যাও’ বলিতে বলিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন। পথিমধ্যে সরোবর-তীরে বস্ত্র রাখিয়া অপ্সরাগণ স্নান করিতেছিলেন। শুককে দেখিয়া তাঁহাদের মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জার উদয় হইল না – যেমন স্নান করিতেছিলেন তেমনই করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাস তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিলেন। ব্যাস ভাবিলেন – ‘এতো বেশ! আমার যুবক পুত্র অগ্রে যাইল, তাহাতে কেহ একটু নড়িলও না, আর আমি বৃদ্ধ, আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা!’ কারণ জিজ্ঞাসায় রমণীরা বলিলেন, “শুক এত পবিত্র যে, ‘তিনি আত্মা’ এই চিন্তাই তাঁহার সর্বক্ষণ রহিয়াছে! তাঁহার নিজের স্ত্রীশরীর কি পুরুষশরীর সে বিষয়ে আদৌ হুঁশই নাই! কাজেই তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা আসিল না। আর তুমি বৃদ্ধ, রমণীর হাবভাব কটাক্ষের অনেক পরিচয় পাইয়াছ ও রূপলাবণ্যের অনেক বর্ণনাও করিয়াছ; তোমার শুকের মতো স্ত্রী-পুরুষে আত্মদৃষ্টি নাই এবং হইবেও না; কাজেই তোমাকে দেখিয়া আমাদের পুরুষবুদ্ধির উদয় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিল।”
স্ত্রীজাতির ঠাকুরের নিকট সর্বথা নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের কারণ
ঠাকুরের সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই মনে হয়। তাঁহার জ্বলন্ত আত্মজ্ঞান ও স্ত্রী-পুরুষ সকলের ভিতর, সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি, তাঁহার নিকটে যতক্ষণ থাকা যাইত ততক্ষণ সকলের মন এত উচ্চে উঠাইয়া রাখিত যে, ‘আমি পুরুষ’, ‘উনি স্ত্রী’ – এসকল ভাব অনেক সময়ে মনেই উঠিত না। কাজেই পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতিরও তাঁহার নিকট সঙ্কোচাদি না হইবারই কথা। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের সংসর্গে ঐ আত্মদৃষ্টি তাঁহাদের ভিতর তৎকালে এত বদ্ধমূল হইয়া যাইত যে, যে-সকল কাজকে মেয়েরা অসীম সাহসের কাজ বলেন ও কখনো কাহারও দ্বারা আদিষ্ট হইয়া করিতে পারেন না, ঠাকুরের কথায় সেইসকল কাজ অবাধে অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া আসিতেন। সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোক যাঁহারা গাড়ি-পালকি ভিন্ন কোথাও কখনো গমনাগমন করিতেন না, ঠাকুরের আজ্ঞায় তাঁহারাও কখনো কখনো তাঁহার সহিত দিনের বেলায় পদব্রজে সদর রাস্তা দিয়া গঙ্গাতীর পর্যন্ত অনায়াসে হাঁটিয়া আসিয়া নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে গমন করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, সেখানে যাইয়া হয়তো আবার ঠাকুরের আজ্ঞায় নিকটস্থ বাজার হইতে বাজার করিয়া আনিয়াছেন এবং সন্ধ্যার সময় পুনরায় হাঁটিয়া কলিকাতায় নিজ বাড়িতে ফিরিয়াছেন। এ বিষয়ে দু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিলেই কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।
ঐ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত
১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র বা আশ্বিন মাস। শ্রীশ্রীমা তখন পিত্রালয় জয়রামবাটীতে গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বলরাম বসু তাঁহার পিতার সহিত বৃন্দাবন গিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীযুত রাখাল (ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী), শ্রীযুত গোপাল (অদ্বৈতানন্দ স্বামী) প্রভৃতি ও অন্যান্য অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ গিয়াছেন। বাগবাজারের একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোকের – যিনি ঠাকুরকে কখনো দেখেন নাই, কথামাত্রই শুনিয়াছেন – ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল; পরিচিতা আর একটি স্ত্রীলোককে ঐ কথা বলিলেন। পরিচিতা স্ত্রী-ভক্তটি দুই বৎসর পূর্ব হইতে ঠাকুরের নিকট যাওয়া-আসা করিতেছেন, সেজন্যই তাঁহাকে বলা। পরামর্শ স্থির হইল; পরদিন অপরাহ্ণে নৌকায় করিয়া উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। দেখিলেন – ঠাকুরের ঘরের দ্বার রুদ্ধ। ঘরের উত্তরের দেয়ালে দুটি ফোকর আছে, তাহার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন – ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। কাজেই নহবতে, যেখানে শ্রীশ্রীমা থাকিতেন, গিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরেই ঠাকুর উঠিলেন এবং উত্তরের দরজা খুলিয়া নহবতের দ্বিতলের বারাণ্ডায় তাঁহারা বসিয়া আছেন দেখিতে পাইয়া “ওগো, তোরা এখানে আয়” বলিয়া ডাকিলেন। স্ত্রী-ভক্তেরা আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর তক্তা হইতে নামিয়া পরিচিতা স্ত্রী-ভক্তটির নিকট যাইয়া বসিলেন। তিনি তাহাতে সঙ্কুচিতা হইয়া সরিয়া বসিবার উপক্রম করিলে ঠাকুর বলিলেন, “লজ্জা কিগো? লজ্জা ঘৃণা ভয় – তিন থাকতে নয়। (হাত নাড়িয়া) তোরাও যা, আমিও তাই। তবে (দাড়ির চুলগুলি দেখাইয়া) এইগুলি আছে বলে লজ্জা হচ্ছে, না?”
এই বলিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ পাড়িয়া নানা কথার উপদেশ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী-ভক্তেরাও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ ভুলিয়া যাইয়া নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিতে ও শুনিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বিদায়কালে ঠাকুর বলিলেন, “সপ্তাহে একবার করে আসবে। নূতন নূতন এখানে আসা-যাওয়াটা বেশি রাখতে হয়।” আবার সম্ভ্রান্তবংশীয়া হইলেও গরিব দেখিয়া নৌকা বা গাড়ির ভাড়া নিত্য নিত্য কোথা পাবেন ভাবিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, “আসবার সময় তিন-চার জনে মিলে নৌকায় করে আসবে। আর যাবার সময় এখান থেকে হেঁটে বরানগরে গিয়ে ‘শেয়ারে’ গাড়ি করবে।” বলা বাহুল্য, স্ত্রী-ভক্তেরা তদবধি তাহাই করিতে লাগিলেন।
ঐ সম্বন্ধে ২য় দৃষ্টান্ত
আর একজন আমাদের একদিন বলিয়াছিলেন – “ভোলা ময়রার দোকানে বেশ সর করেছিল। ঠাকুর সর খেতে ভালবাসতেন জানতুম, তাই বড় একখানি সর কিনে আমরা পাঁচজনে মিলে নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। ওমা, এসে শুনলুম ঠাকুর কলিকাতায় গিয়েছেন। সকলে তো একেবারে বসে পড়লুম। কি হবে? রামলালদাদা ছিলেন – তাঁকে ঠাকুর কোথায় গিয়েছেন জিজ্ঞাসা করায়, বলে দিলেন, ‘কম্বুলেটোলায় মাস্টার মহাশয়ের1 বাড়িতে’। অ-র মা শুনে বললে, ‘সে বাড়ি আমি জানি, আমার বাপের বাড়ির কাছে – যাবি? চল যাই; এখানে বসে আর কি করব?’ সকলেই তাই মত করলে। রামলালদাদার হাতে সরখানি দিয়ে বলে গেলুম, ‘ঠাকুর এলে দিও’। নৌকা তো ছেড়ে দিয়েছিলুম – হেঁটে হেঁটেই সকলে চললুম। কিন্তু এমনি ঠাকুরের ইচ্ছে, আলমবাজারটুকু গিয়েই একখানা ফেরতা গাড়ি পাওয়া গেল। ভাড়া করে তো শ্যামপুকুরে সব এলুম। এসে আবার বিপদ। অ-র মা বাড়ি চিনতে পারলে না। শেষে ঘুরে ঘুরে তার বাপের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একটা চাকরকে ডেকে আনলে। সে সঙ্গে এসে দেখিয়ে দেয়, তবে হয়। অ-র মারই বা দোষ দেব কি, আমাদের চেয়ে ৩।৪ বছরের ছোট তো? তখন ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের হবে। বউ মানুষ, রাস্তাঘাটে কখনো বেরোয়নি, আর গলির ভেতরে বাড়ি – সে চিনবেই বা কেমন করে গা?
“যা হোক করে তো পৌঁছুলুম। তখন মাস্টারদের (পরিবারের) সঙ্গেও চেনাশুনা হয়নি। বাড়ি ঢুকে দেখি একখানি ছোট ঘরে তক্তাপোশের ওপর ঠাকুর বসে, কাছে কেউ নাই। আমাদের দেখেই হেসে বলে উঠলেন, ‘তোরা এখানে কেমন করে এলি গো?’ আমরা তাঁকে প্রণাম করে সব কথা বললুম। তিনি খুব খুশি, ঘরের ভেতর বসতে বললেন, আর অনেক কথাবার্তা কইতে লাগলেন। এখন সকলে বলে, মেয়েদের তিনি ছুঁতে দিতেন না! কাছে যেতে দিতেন না। আমরা শুনে হাসি ও মনে করি – তবু আমরা এখনো মরিনি! তাঁর যে কি দয়া ছিল, তা কে জানবে! স্ত্রী-পুরুষে সমান ভাব! তবে স্ত্রীলোকের হাওয়া অনেকক্ষণ সহ্য করতে পারতেন না, অনেকক্ষণ থাকলে বলতেন, ‘যা গো, এইবার একবার মন্দিরে দর্শন করে আয়’। পুরুষদেরও ঐরূপ বলতে আমরা শুনেছি।
“যাক। আমরা তো বসে কথা কইছি। আমাদের ভেতর যে দুজনের বেশি বয়েস ছিল তারা দরজার সামনেই বসেছে, আর আমরা তিনজনে ঘরের ভেতর, এককোণে; এমন সময়ে ঠাকুর যাকে ‘মোটা বামুন’ বলতেন (শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) তিনি এসে উপস্থিত। বেরিয়ে যাব – তারও জো নেই! কোথায় যাই! বুড়িরা দরজার সামনেই একটা জানালা ছিল, তাতেই বসে রইল। আর আমরা তিনটেয় ঠাকুর যে তক্তাপোশে বসেছিলেন তার নিচে ঢুকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে রইলুম। মশার কামড়ে সর্বাঙ্গ ফুলে উঠল, কি করি, নড়বার জো নেই, স্থির হয়ে পড়ে রইলুম। কথাবার্তা কয়ে বামুন প্রায় এক ঘণ্টা বাদে চলে গেল, তখন বেরুই! – আর হাসি!
“তারপর বাড়ির ভেতর জলখাবারের জন্য ঠাকুরকে নিয়ে গেল। তখন তাঁর সঙ্গে বাড়ির ভেতর গেলুম। তারপর খেয়েদেয়ে কতক্ষণ বাদে ঠাকুর গাড়িতে উঠলেন (দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন বলিয়া); তখন সকলে হেঁটে বাড়ি ফিরি। রাত তখন ৯টা হবে।
1. ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত – যিনি ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ প্রকাশ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন – তখন কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলায় একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে থাকিতেন।
স্ত্রীভক্তদিগের প্রতি ঠাকুরের সমান কৃপা
“তার পরদিন আবার দক্ষিণেশ্বরে গেলুম। যাবামাত্র ঠাকুর কাছে এসে বললেন, ‘ওগো, তোমার সর প্রায় সবটা খেয়েছিলুম, একটু বাকি ছিল; কোন অসুখ করেনি, পেটটা একটু সামান্য গরম হয়েছে’। আমি তো শুনে অবাক! তাঁর পেটে কিছু সয় না, আর একখানা সর তিনি একেবারে খেয়েছেন! তারপর শুনলুম – ভাবাবস্থায় খেয়েছেন। শুনলুম – মাস্টার মহাশয়ের বাড়ি থেকে ঠাকুর খেয়ে-দেয়ে তো রাত্রি সাড়ে দশটায় এসে পৌঁছুলেন; এসে খানিক বাদে তাঁর ভাব হয় ও অর্ধবাহ্যদশায় রামলালদাদাকে বলেন, ‘বড় ক্ষুধা পেয়েছে, ঘরে কি আছে দে তো রে’। রামলালদাদা শুনে আমার সেই সরখানি এনে সামনে দেন ও ঠাকুর তা প্রায় সব খেয়ে ফেলেন! ভাবের ঘোরে তাঁর কখনো কখনো অমন অসম্ভব খাওয়া ও খেয়ে হজম করার কথা মা-র কাছে ও লক্ষ্মীদিদির কাছে শুনেছিলুম, সেইসব কথা মনে পড়ল। এত কৃপা আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি! সে যে কি দয়া, তা বলে বোঝাবার নয়! আর সে কি টান, কেমন করে যে আমরা সব যেতুম, করতুম – তা আমরাই জানি না, বুঝি না। কই – এখন তো আর সে রকম করে কোথাও হেঁটে হেঁটে বলা নেই কওয়া নেই অচেনা লোকের বাড়িতে সাধু দেখতে বা ধর্মকথা শুনতে যেতে পারি নে! সে যাঁর শক্তিতে করতুম তাঁর সঙ্গে গিয়েছে! তাঁকে হারিয়ে এখন কেন যে বেঁচে আছি, তা জানি না!”
এইরূপ আরও কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা কখনো বাটীর বাহির হন নাই – তাঁহাদের দিয়া বাজার করাইয়া আনিয়াছেন, অভিমান অহঙ্কার দূরে যাইবে বলিয়া সাধারণ ভিখারির ন্যায় লোকের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করাইয়াছেন, সঙ্গে লইয়া পেনেটীর মহোৎসব ইত্যাদি দেখাইয়া আনিয়াছেন – আর তাঁহারাও মনে কোন দ্বিধা না করিয়া মহানন্দে যাহা ঠাকুর বলিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন! ভাবিয়া দেখিলে ইহা একটি কম ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না; সে প্রবল জ্ঞানতরঙ্গের সম্মুখে সকলেরই ভেদজ্ঞানপ্রসূত দ্বিধাভাব তখনকার মতো ভাসিয়া গিয়াছে। সে উজ্জ্বল ভাবঘনতনু ঠাকুরের ভিতর সকলেই নিজ নিজ ভাবের পূর্ণাদর্শ দেখিতে পাইয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে! পুরুষ পুরুষত্বের পূর্ণবিকাশ দেখিয়া নতশির হইয়াছে; স্ত্রী স্ত্রীজনসুলভ সকল ভাবের বিকাশ তাঁহাতে দেখিতে পাইয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার জ্ঞান করিয়াছে!
ঠাকুরের স্ত্রীসুলভ হাবভাবের অনুকরণ
স্ত্রীজাতিসুলভ হাবভাবাদি ঠাকুর কখনো কখনো আমাদের সাক্ষাতে নকল করিতেন। উহা এত ঠিক হইত যে, আমরা অবাক হইতাম। জনৈকা স্ত্রী-ভক্ত ঐ সম্বন্ধে একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, ঠাকুর একদিন তাঁহাদের সামনে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষ দেখিলে যেরূপ হাবভাব করে, তাহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন – “সে মাথায় কাপড় টানা, কানের পাশে চুল সরিয়ে দেওয়া, বুকে কাপড় টানা, ঢং করে নানারূপ কথা কওয়া – একেবারে হুবহু ঠিক। দেখে আমরা হাসতে লাগলুম, কিন্তু মনে লজ্জা আর কষ্টও হলো যে, ঠাকুর মেয়েদের এই রকম করে হেয় জ্ঞান করচেন। ভাবলুম – কেন, সকল স্ত্রীলোকেরাই কি ঐ রকম? হাজার হোক আমরা মেয়ে কিনা, মেয়েদের ওরকম করে কেউ ব্যাখ্যানা করলে মনে কষ্ট হতেই পারে। ওমা, ঠাকুর অমনি আমাদের মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন! আর বলছেন, ‘ওগো, তোদের বলচি না। তোরা তো অবিদ্যাশক্তি নোস; ওসব অবিদ্যাশক্তিগুলো করে’!”
ঠাকুরের স্ত্রী-পুরুষ উভয় ভাবের একত্র সমাবেশ
ঠাকুরে স্ত্রী-পুরুষ উভয় ভাবের এইরূপ একত্র সমাবেশ তাঁহার প্রত্যেক ভক্তই কিছু-না-কিছু উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রীযুত গিরিশ ঐরূপ উপলব্ধি করিয়া একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলেন, “মশাই, আপনি পুরুষ না প্রকৃতি?” ঠাকুর হাসিয়া তদুত্তরে বলিলেন, “জানি না”। ঠাকুর ঐ কথাটি আত্মজ্ঞ পুরুষেরা যেমন বলেন, ‘আমি পুরুষ নহি, স্ত্রীও নহি’ – সেই ভাবে বলিলেন, অথবা নিজের ভিতর উভয় ভাবের সমান সমাবেশ দেখিয়া বলিলেন, সে কথা এখন কে মীমাংসা করিবে?
ভাবমুখে থাকাতেই ঠাকুর সকলের ভাব বুঝিতে সমর্থ হইতেন
এইরূপে ভাবময় ঠাকুর ভাবমুখে থাকিয়া স্ত্রীর কাছে স্ত্রী ও পুরুষের কাছে পুরুষ হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের সকল ভাব ঠিক ঠিক ধরিতেন। আমাদের কাহারও কাহারও কাছে একথা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরম ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রীভক্ত1 আমাদিগকে বলিয়াছেন, ঠাকুর তাঁহাকে একদিন বলিতেছেন, “লোকের দিকে চেয়েই – কে কেমন বুঝতে পারি, কে ভাল কে মন্দ, কে সুজন্মা, কে বেজন্মা, কে জ্ঞানী, কে ভক্ত, কার হবে, কার হবে না (ধর্মলাভ) – সব জানতে পারি; কিন্তু বলি না – তাদের মনে কষ্ট হবে, তাই!” ভাবমুখে থাকায় সমগ্র জগৎটাই তাঁহার নিকট সদা সর্বক্ষণ ভাবময় বলিয়াই প্রতীত হইত। বোধ হইত – স্ত্রী-পুরুষ, গরু-ঘোড়া, কাঠ-মাটি সকলই যেন বিরাট মনে এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমষ্টিরূপে উঠিতেছে, ভাসিতেছে – আর ঐ ভাবাবরণের ভিতর দিয়া অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদাকাশ কোথাও অল্প, কোথাও অধিক পরিমাণে প্রকাশিত রহিয়াছে; আবার কোথাও বা আবরণের নিবিড়তায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন নাই বলিয়া বোধ হইতেছে! আনন্দময়ীর নিষ্কলঙ্ক মানসপুত্র ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে স্বেচ্ছায় শরীর-মন, চিত্তবৃত্তি, সর্বস্ব অর্পণ করিয়া সমাধিবলে অশরীরী আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় পৌঁছিয়া জগন্মাতার অন্যরূপ ইচ্ছা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহারই আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত অনির্বচনীয় অবস্থায় লীন আপনার মনকে জোর করিয়া আবার বিদ্যার আবরণে আবরিত করিয়া নিয়ত মা-র আদেশ পালন করিতে থাকিলেন! অনন্তভাবময়ী জগজ্জননীও ঠাকুরের প্রতি প্রসন্না হইয়া ঠাকুরকে শরীরী করিয়া রাখিয়াও একত্বের এত উচ্চপদে তাঁহার মনটি সর্বক্ষণ রাখিয়া দিলেন যে, অনন্ত বিরাট মনে যতকিছু ভাবের উদয় হইতেছে, তৎসকলই সেখান হইতে তাঁহার নিজস্ব বলিয়া সর্বকালে অনুভূত হইত এবং এতদূর আয়ত্তীভূত হইয়া থাকিত যে, দেখিলেই মনে হইত – যিনিই মাতা তিনিই সন্তান এবং যিনিই সন্তান তিনিই মাতা – ‘চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম’!
আমরা যতটুকু বলিতে পারিলাম বলিলাম; পাঠক, এইবার তুমি ভাবিয়া দেখ অনন্তভাবরূপী এ ঠাকুর কে?
1. স্বামী প্রেমানন্দজীর মাতাঠাকুরানী।
তৃতীয় খণ্ড – দ্বিতীয় অধ্যায়: ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা
সমাধি মস্তিষ্ক-বিকার নহে
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
– গীতা, ১৮।৬৪
ঠাকুরের আবির্ভাব বা প্রকাশের পূর্বে কলিকাতায় শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেই যে ভাব, সমাধি বা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অপূর্ব দর্শন ও উপলব্ধিসমূহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অশিক্ষিত জনসাধারণের ঐ সম্বন্ধে ভয়-বিস্ময়-সম্ভূত একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল; এবং নবীন শিক্ষিতসম্প্রদায় তখন ধর্মজ্ঞান-বিবর্জিত বিদেশী শিক্ষার স্রোতে সম্পূর্ণরূপে অঙ্গ ঢালিয়া ঐরূপ দর্শনাদি হওয়া অসম্ভব বা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত বলিয়া মনে করিতেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ভাবসমাধি হইতে উৎপন্ন শারীরিক বিকারসমূহ তাঁহাদের নয়নে মূর্ছা ও শারীরিক রোগবিশেষ বলিয়াই প্রতিভাত হইত! বর্তমান কালে ঐ অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হইলেও ভাব এবং সমাধিরহস্য যথাযথ বুঝিতে এখনো অতি অল্প লোকেই সক্ষম। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবমুখাবস্থা কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিতে হইলে সমাধিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকার নিতান্ত প্রয়োজন। সেজন্য ঐ বিষয়েই কিছু কিছু আমরা এখন পাঠককে বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।
সাধারণ মানবে যাহা উপলব্ধি করে না তাহাকেই আমরা সচরাচর ‘বিকার’ বলিয়া থাকি। ধর্মজগতের সূক্ষ্ম উপলব্ধিসমূহ কিন্তু কখনই সাধারণ মানবমনের অনুভবের বিষয় হইতে পারে না; উহাতে শিক্ষা, দীক্ষা ও নিরন্তর অভ্যাসাদির প্রয়োজন। ঐসকল অসাধারণ দর্শন ও অনুভবাদি সাধককে দিন দিন পবিত্র করে ও নিত্য নূতন বলে বলীয়ান এবং নব নব ভাবে পূর্ণ করিয়া ক্রমে চিরশান্তির অধিকারী করে। অতএব ঐসকল দর্শনাদিকে ‘বিকার’ বলা যুক্তিসঙ্গত কি? ‘বিকার’ মাত্রই যে মানবকে দুর্বল করে ও তাহার বুদ্ধি-শুদ্ধি হ্রাস করে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ধর্মজগতের দর্শনানুভূতিসকলের ফল যখন উহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন ঐসকলের কারণও সম্পূর্ণ বিপরীত বলিতে হইবে এবং তজ্জন্য ঐসকলকে মস্তিষ্ক-বিকার বা রোগ কখনো বলা চলে না।
সমাধি দ্বারাই ধর্মলাভ হয় ও চিরশান্তি পাওয়া যায়
বিশেষ বিশেষ ধর্মানুভূতিসকল ঐরূপ দর্শনাদি দ্বারাই চিরকাল অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। তবে যতক্ষণ না মনের সকল বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া মানব নির্বিকল্প অবস্থায় উপনীত ও অদ্বৈতভাবে অবস্থিত হয়, ততক্ষণ সে আধ্যাত্মিক জগতের চিরশান্তির অধিকারী হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন – “একটা কাঁটা ফুটেছে, আর একটা কাঁটা দিয়ে পূর্বের সেই কাঁটাটা তুলে ফেলে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।” শ্রীভগবানকে ভুলিয়া এই জগৎ-রূপ বিকার উপস্থিত হইয়াছে। এইসকল নানা রূপ-রসাদির অনুভবরূপ বিকার ধর্মজগতের পূর্বোক্ত দর্শনানুভবাদির দ্বারা প্রতিহত হইয়া মানবকে ক্রমশঃ ঐ অদ্বৈতানুভূতিতে উপস্থিত করে। তখন ‘রসো বৈ সঃ’ – এই ঋষিবাক্যের উপলব্ধি হইয়া মানব ধন্য হয়। ইহাই প্রণালী। ধর্মজগতের যত কিছু মত, অনুভব, দর্শনাদি সব ঐ লক্ষ্যেই মানবকে অগ্রসর করে। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজী ঐসকল দর্শনাদিকে, সাধক লক্ষ্যাভিমুখে কতদূর অগ্রসর হইল, তাহারই পরিচায়কস্বরূপ (mile-stones on the way to progress) বলিয়া নির্দেশ করিতেন। অতএব পাঠক যেন না মনে করেন, ভাববিশেষের কিঞ্চিৎ প্রাবল্যে অথবা ধ্যানসহায়ে দুই-একটি দেবমূর্তি দর্শনাদিতেই ধর্মের ‘ইতি’ হইল! তাহা হইলে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। সাধকেরা ধর্মজগতে ঐরূপ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াই লক্ষ্য হারাইয়া থাকেন এবং লক্ষ্য হারাইয়াই একদেশী-ভাবাপন্ন হইয়া পরস্পরের প্রতি দ্বেষ-হিংসাদিতে পূর্ণ হইয়া পড়েন। শ্রীভগবানে ভক্তি করিতে যাইয়া ঐ ভ্রম উপস্থিত হইলেই মানুষ ‘গোঁড়া’, ‘একঘেয়ে’ হয়। ঐ দোষই ভক্তিপথের বিষম কণ্টকস্বরূপ এবং মানবের ‘হীনবুদ্ধি’-প্রসূত।
দেবমূর্ত্যাদি-দর্শন না হইলেই যে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, তাহা নহে
আবার ঐরূপ দর্শনাদিতে বিশ্বাসী হইয়া অনেকে বুঝিয়া বসেন, যাহার ঐরূপ দর্শনাদি হয় নাই, সে আর ধার্মিক নহে। ধর্ম ও লক্ষ্যবিহীন অদ্ভুত-দর্শন-পিপাসা (miracle-mongering) তাঁহাদের নিকট একই ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু ঐরূপ পিপাসায় ধর্মলাভ না হইয়া মানব দিন দিন সকল বিষয়ে দুর্বলই হইয়া পড়ে। যাহাতে একনিষ্ঠ বুদ্ধি ও চরিত্রবল না আসে, যাহাতে মানব পবিত্রতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইয়া সত্যের জন্য সমগ্র জগৎকে তুচ্ছ করিতে না পারে, যাহাতে কামগন্ধহীন না হইয়া মানব দিন দিন নানা বাসনা-কামনায় জড়ীভূত হয়, তাহা ধর্মরাজ্যের বহির্ভূত। অপূর্ব দর্শনাদি যদি তোমার জীবনে ঐরূপ ফল প্রসব না করিয়া থাকে, অথচ দর্শনাদিও হইতে থাকে, তবে জানিতে হইবে – তুমি এখনো ধর্মরাজ্যের বাহিরে রহিয়াছ, তোমার ঐসকল দর্শনাদি মস্তিষ্ক-বিকারজনিত, উহার কোন মূল্য নাই। আর যদি অপূর্ব দর্শনাদি না করিয়াও তুমি ঐরূপ বলে বলীয়ান হইতেছ দেখ, তবে বুঝিবে তুমি ঠিক পথে চলিয়াছ, কালে যথার্থ দর্শনাদিও তোমার উপস্থিত হইবে।
ত্যাগ, বিশ্বাস এবং চরিত্রের বলই ধর্মলাভের পরিচায়ক
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের মধ্যে অনেকের ভাবসমাধি হইতেছে, অথচ তাঁহার অনেকদিন গতায়াত করিয়াও ওরূপ কিছু হইল না দেখিয়া আমাদের জনৈক বন্ধু1 কোন সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট সজলনয়নে উপস্থিত হইয়া প্রাণের কাতরতা নিবেদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন, “তুই ছোঁড়া তো ভারি বোকা, ভাবচিস বুঝি ঐটে হলেই সব হলো? ঐটেই ভারি বড়? ঠিক ঠিক ত্যাগ, বিশ্বাস ওর চেয়ে ঢের বড় জিনিস জানবি। নরেন্দ্রের (স্বামী বিবেকানন্দের) তো ওসব বড় একটা হয় না; কিন্তু দেখ দেখি – তার কি ত্যাগ, কি বিশ্বাস, কি মনের তেজ ও নিষ্ঠা!”
1. শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ঘোষ।
‘পাকা আমি’ ও শুদ্ধ বাসনা। জীবন্মুক্ত, আধিকারিক বা ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি
একনিষ্ঠ বুদ্ধি, দৃঢ় বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভক্তিসহায়ে সাধকের যখন বাসনাসমূহ ক্ষীণ হইয়া শ্রীভগবানের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন পূর্বসংস্কারবশে কাহারও কাহারও মনে কখনো কখনো ‘আমি লোক-কল্যাণ সাধন করিব, যাহাতে বহুজন সুখী হইতে পারে তাহা করিব’ – এইরূপ শুদ্ধ বাসনার উদয় হইয়া থাকে। ঐ বাসনাবশে সে আর তখন পূর্ণরূপে অদ্বৈতভাবে অবস্থান করিতে পারে না। ঐ উচ্চ ভাবভূমি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র নামিয়া আসিয়া ‘আমি, আমার’-রাজ্যে পুনরায় আগমন করে। কিন্তু সে ‘আমি’ শ্রীভগবানের দাস, সন্তান বা অংশ ‘আমি’ এইরূপে শ্রীভগবানের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লইয়াই অনুক্ষণ থাকে। সে ‘আমি’ দ্বারায় আর অহর্নিশি কাম-কাঞ্চনের সেবা করা চলে না। সে ‘আমি’ শ্রীভগবানকে সারাৎসার জানিয়া আর সংসারের রূপ-রসাদি-ভোগের জন্য লালায়িত হয় না। যতটুকু রূপ-রসাদিবিষয়-গ্রহণ তাহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সহায়ক, ততটুকুই সে ইচ্ছামত গ্রহণ করিয়া থাকে, এই পর্যন্ত। যাঁহারা পূর্বে বদ্ধ ছিলেন, পরে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল কোনরূপ ভগবদ্ভাবে কাটাইতেছেন, তাঁহাদিগকেই ‘জীবন্মুক্ত’ কহে। যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত ঐরূপ বিশিষ্ট সম্বন্ধের ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এ জন্মে কোন সময়েই সাধারণ মানবের ন্যায় বন্ধনযুক্ত হইয়া পড়েন নাই, তাঁহারাই শাস্ত্রে ‘আধিকারিক পুরুষ’, ‘ঈশ্বরকোটি’ বা ‘নিত্যমুক্ত’ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। আবার একদল সাধক আছেন, যাঁহারা অদ্বৈতভাব লাভ করিবার পরে এ জন্মে বা পরজন্মে সংসারে লোককল্যাণ করিতেও আর ফিরিলেন না – ইঁহারাই ‘জীবকোটি’ বলিয়া অভিহিত হন এবং ইঁহাদের সংখ্যাই অধিক বলিয়া আমরা গুরুমুখে শ্রুত আছি।
অদ্বৈতভাবোপলব্ধির তারতম্য
আবার যাঁহারা পূর্বোক্তরূপে অদ্বৈতভাব-লাভের পর লোককল্যাণের জন্য সমাধিভূমি হইতে নামিয়া আসেন, সেসকল সাধকদিগের মধ্যেও অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপ জগৎকারণের সহিত অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিবার তারতম্য আছে। কেহ ঐ ভাবসমুদ্র দূর হইতে দর্শন করিয়াছেন মাত্র, কেহ বা উহা আরও নিকটে অগ্রসর হইয়া স্পর্শ করিয়াছেন, আবার কেহ বা ঐ সমুদ্রের জল অল্প-স্বল্প পান করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, “দেবর্ষি নারদ দূর হতে ঐ সমুদ্র দেখেই ফিরেছেন, শুকদেব তিনবার স্পর্শমাত্র করেছেন, আর জগদ্গুরু শিব তিন গণ্ডূষ জল খেয়ে শব হয়ে পড়ে আছেন!” এই অদ্বৈতভাবে অল্পক্ষণের নিমিত্তও তন্ময় হওয়াকেই ‘নির্বিকল্প সমাধি’ কহে।
শান্ত-দাস্যাদি-ভাবের গভীরতায় সবিকল্প সমাধি
অদ্বৈতভাব-উপলব্ধির যেমন তারতম্য আছে, সেইরূপ নিম্নস্তরের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি ভাবসমূহের অথবা যে ভাবসমূহ অদ্বৈতভাবে সাধককে উপনীত করে, সেসকলের উপলব্ধি করিবার মধ্যেও আবার তারতম্য আছে। কেহ বা উহার কোনটি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন, আবার কেহ বা উহার আভাসমাত্রই পাইয়া থাকেন। এই নিম্নাঙ্গের ভাবসকলের মধ্যে কোন একটির সম্পূর্ণ উপলব্ধিই ‘সবিকল্প সমাধি’ নামে যোগশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে।
মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে শারীরিক বিকার অবশ্যম্ভাবী
উচ্চাঙ্গের অদ্বৈতভাব বা নিম্নাঙ্গের সবিকল্পভাব, সকল প্রকার ভাবেই সাধকের অপূর্ব শারীরিক পরিবর্তন এবং অদ্ভুত দর্শনাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ শরীরবিকার ও অদ্ভুত দর্শনাদির প্রকাশ আবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে লক্ষিত হয়। কাহারও অল্প উপলব্ধিতেই শারীরিক বিকার ও দর্শনাদি দেখা যায়, আবার কাহারও বা অতি গভীরভাবে ঐসকল ভাবোপলব্ধিতেও শারীরিক বিকার এবং দর্শনাদি অতি অল্পই দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, “গেড়ে ডোবার অল্প জলে যদি দু-একটা হাতি নামে তো জল ওছল্-পাছল্ হয়ে তোলপাড় হয়ে উঠে; কিন্তু সায়ের দীঘিতে অমন বিশগণ্ডা হাতি নামলেও যেমন জল স্থির, তেমনই থাকে।” অতএব শারীরিক বিকার এবং দর্শনাদি যে ভাবের গভীরতার ধ্রুব লক্ষণ, তাহাও নহে।
সর্বপ্রকার ভাব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে অবতারেরাই সক্ষম। দৃষ্টান্ত – ঠাকুরের সমাধির কথা
ভাবসমাধির দার্শনিক তত্ত্ব শ্রীগুরুর মুখ হইতে আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি। আরও কয়েকটি কথা ঐ সম্বন্ধে এখানে বলা প্রয়োজন। তবেই পাঠক উহা বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন। সাধকদিগের মধ্যে শান্তদাস্যাদি ও অদ্বৈত-ভাবোপলব্ধির তারতম্য লক্ষিত হওয়া সম্বন্ধে যেসকল কথা পূর্বে বলা হইল, তাহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, ঈশ্বরাবতারেরাও ভাবরাজ্যে কোনরূপ গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ থাকেন। তাঁহারা শান্তদাস্যাদি যখন যে ভাব ইচ্ছা, পূর্ণমাত্রায় নিজ জীবনে প্রদর্শন করিতে পারেন, আবার অদ্বৈতভাবাবলম্বনে শ্রীভগবানের সহিত একত্বানুভবে এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন যে, জীবন্মুক্ত, নিত্যমুক্ত বা ঈশ্বরকোটি কোনপ্রকার জীবেরই তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপের সহিত অতদূর একত্বে অগ্রসর হইয়া আবার তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়া এবং ‘আমি আমার’ রাজ্যে পুনরায় নামিয়া আসা – জীবের কখনই সম্ভবপর নহে। উহা কেবল একমাত্র অবতারপ্রথিত পুরুষসকলে সম্ভবে। তাঁহাদের অদৃষ্টপূর্ব উপলব্ধিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াই আধ্যাত্মিক জগতে বেদাদি সর্বশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল অনেক স্থলে যে বেদাদিশাস্ত্রনিবদ্ধ উপলব্ধিসকল অতিক্রম করিবে – ইহাতে বিচিত্র কি আছে? শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, “এখানকার অবস্থা (আমার উপলব্ধি) বেদ-বেদান্তে যা লেখা আছে, সেসকলকে ঢের ছাড়িয়ে চলে গেছে!” শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ শ্রেণীর পুরুষসকলের অগ্রণী ছিলেন বলিয়াই নিরন্তর ছয়মাস কাল অদ্বৈতভাবে পূর্ণরূপে অবস্থান করিবার পরেও আবার ‘বহুজনহিতায়’ লোকশিক্ষার জন্য ‘আমি আমার’ রাজ্যে ফিরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে বড় অদ্ভুত কথা। ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাঠককে এখানে বলা অসঙ্গত হইবে না।
বেদান্ত-চর্চা করিতে ব্রাহ্মণীর নিষেধ
শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর ঠাকুরের তৃতীয় দিবসে বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত নির্বিকল্প সমাধি বা শ্রীভগবানের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের চরম উপলব্ধি হয়। সে সময় ঠাকুরের তন্ত্রোক্ত সকলপ্রকার সাধন হইয়া গিয়াছে এবং যিনি ঐসকল সাধনার সময় বৈধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া এবং ঐসকল দ্রব্যের ব্যবহারপ্রণালী প্রভৃতি দেখাইয়া তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন, সে বিদুষী ভৈরবীও (ঠাকুর ইঁহাকে আমাদের নিকট ‘বামনী’ বলিয়া নির্দেশ করিতেন) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট বাস করিতেছেন। কারণ, ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি, উক্ত ‘বামনী’ বা ভৈরবী তাঁহাকে শ্রীমৎ তোতাপুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশামেশি করিতে নিষেধ করিয়া বলিতেন – “বাবা, ওর সঙ্গে অত মেশামেশি করো না, ওদের সব শুকনো ভাব; ওর অত সঙ্গ করলে তোমার ভাব-প্রেম আর কিছু থাকবে না।” ঠাকুর কিন্তু ঐ কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অহর্নিশি তখন বেদান্ত-বিচার ও উপলব্ধিতে নিমগ্ন থাকিতেন।
ঠাকুরের নির্বিকল্প ভূমিতে সর্বদা থাকিবার সঙ্কল্প ও উক্ত ভূমির স্বরূপ
এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ তোতাপুরী চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের তখন দৃঢ়সঙ্কল্প হইল – ‘আমি আমার’ রাজ্যে আর না থাকিয়া নিরন্তর শ্রীভগবানের সহিত একত্বানুভবে বা অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান করিব এবং তিনি তদ্রূপ আচরণও করিতে লাগিলেন। সে বড় অপূর্ব কথা – তখন ঠাকুরের শরীরটা যে আছে, সে বিষয়ের আদৌ হুঁশ ছিল না। খাইব, শুইব, শৌচাদি করিব – এসকল কথারও মনে উদয় হইত না তো অপরের সহিত কথাবার্তা কহিব – সে তো অনেক দূরের কথা! সে অবস্থায় ‘আমি আমার’ও নাই – আর ‘তুমি তোমার’ও নাই! ‘দুই’ নাই; ‘এক’ও নাই! কারণ, ‘দুই’-এর স্মৃতি থাকিলে তবে তো ‘একে’র উপলব্ধি হইবে। সেখানে মনের সব বৃত্তি স্থির – শান্ত! কেবল –
কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধিগগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥
প্রকৃতি-বিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং।1
* * * * *
কেবল আনন্দ! আনন্দ! – তার দিক নাই, দেশ নাই, আলম্বন নাই, রূপ নাই, নাম নাই। কেবল অশরীরী আত্মা আপনার অনির্বচনীয় আনন্দময় অবস্থায়, মনবুদ্ধির গোচরে অবস্থিত যতপ্রকার ভাবরাশি আছে, সেসকলের অতীত একপ্রকার ভাবাতীত ভাবে অবস্থিত! যাহাকে শাস্ত্র ‘আত্মায় আত্মায় রমণ’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন! – এইপ্রকার এক অনির্বচনীয় অবস্থার উপলব্ধি ঠাকুরের তখন নিরন্তর হইয়াছিল।
1. বিবেকচূড়ামণি, ৪০৮-০৯।
ঠাকুরের মনের অদ্ভুত গঠন
ঠাকুর বলিতেন, বেদান্তের নির্বিকল্প সমাধি-উপলব্ধিতে উঠিবার পথে সংসারের কোনও পদার্থ বা কোন সম্বন্ধই তাঁহার অন্তরায় হয় নাই। কারণ, পূর্ব হইতেই তো তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্ম সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত যতপ্রকার ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। “মা, এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান – এই নে তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম – এই নে তোর ভাল, এই নে তোর মন্দ – এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য – এই নে তোর যশ, এই নে তোর অযশ – আমায় তোর শ্রীচরণে শুদ্ধা-ভক্তি দে, দেখা দে” – এই বলিয়া মন হইতে ঠিক ঠিক সকল প্রকার বাসনা কামনা শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভালবাসিয়া তাঁহার জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। হায়, সে একাঙ্গী ভক্তি-প্রেমের কথা কি আমরা উপলব্ধি দূরে থাক, একটুও কল্পনা করিতে পারি? আমরা মুখে যদি কখনো শ্রীভগবানকে বলি, ‘ঠাকুর, এই নাও আমার যাহা কিছু সব’ তো বলিবার পরই আবার কাজের সময় ঠাকুরকে তাড়াইয়া সেসব ‘আমার আমার’ বলিতে থাকি এবং লাভ-লোকসান খতাই। প্রতি কার্যে ‘লোকে কি বলবে’ ভাবিয়া নানাপ্রকারে তোলাপাড়া, ছুটাছুটি করি; ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া কখনো অকূলপাথারে, আবার কখনো বা আনন্দে ভাসি; এবং মনে মনে একথা স্থিরনিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছি যে, দুনিয়াটা আমরা আমাদের উদ্যমে একেবারে ওলটপালট করিয়া না দিতে পারিলেও কতকটাও ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি। ঠাকুরের তো আমাদের মতো জুয়াচোর মন ছিল না; তিনি যেমন বলিলেন, “মা, এই তোর দেওয়া জিনিস তুই নে”, অমনি তদ্দণ্ড হইতে তাঁহার মন আর সে সকলের প্রতি লালসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল না! ‘বলে ফেলেছি কি করি? না বললে হতো’ – মনের এইরূপ ভাব পর্যন্তও তখন হইতে আর উদিত হইল না! সেইজন্যই দেখিতে পাই, ঠাকুর যখনই যাহা শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দিবেন বলিয়াছেন তাহা আর কখনো ‘আমার’ নিজের বলিতে পারেন নাই।
ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠা
এখানে ঐ বিষয়ে আর একটি কথাও আমরা পাঠককে বলিতে ইচ্ছা করি। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ধর্মাধর্ম, পুণ্য-পাপ, ভাল-মন্দ, যশ-অযশ প্রভৃতি শরীর-মনের সর্বস্ব অর্পণ করিয়াও ‘মা, এই নে তোর সত্য, এই নে তোর মিথ্যা’ – এ কথাটি বলিতে পারেন নাই। উহার কারণ ঠাকুর নিজ মুখেই এক সময়ে আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, ঐরূপে সত্য ত্যাগ করিলে “শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সর্বস্ব যে অর্পণ করিলাম – এ সত্য রাখিব কিরূপে?” বাস্তবিক সর্বস্ব অর্পণ করিয়াও কি সত্যনিষ্ঠাই না আমরা তাঁহাতে দেখিয়াছি। যেদিন যেখানে যাইব বলিয়াছেন, সেদিন ঠিক সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন; যাহার নিকট হইতে যে জিনিস লইব বলিয়াছেন, তাহার নিকট ভিন্ন অপর কাহারও নিকট তাহা লইতে পারেন নাই। যেদিন বলিয়াছেন, আর অমুক জিনিসটা খাইব না, বা অমুক কাজ আর করিব না, সেই দিন হইতে আর তাহা খাইতে বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুর বলিতেন, “যার সত্যনিষ্ঠা আছে, সে সত্যের ভগবানকে পায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনো মিথ্যা হতে দেয় না।” বাস্তবিকও ঐ বিষয়ের কতই না দৃষ্টান্ত আমরা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি! তাহার মধ্যে কয়েকটি পাঠককে এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।
ঐ বিষয়ের ১ম দৃষ্টান্ত
দক্ষিণেশ্বরে একদিন পরমা ভক্তিমতী গোপালের মা ঠাকুরকে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবেন। সব প্রস্তুত; ঠাকুর খাইতে বসিলেন। বসিয়া দেখেন, ভাতগুলি শক্ত রহিয়াছে – সুসিদ্ধ হয় নাই। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন, “এ ভাত কি আমি খেতে পারি? ওর হাতে আর কখনো ভাত খাব না।” ঠাকুরের মুখ দিয়া ঐ কথাগুলি বাহির হওয়ায় সকলে ভাবিলেন, ঠাকুর গোপালের মাকে ভবিষ্যতে সতর্ক করিবার নিমিত্ত ঐরূপ বলিয়া ভয় দেখাইলেন মাত্র, নতুবা গোপালের মাকে যেরূপ আদর-যত্ন করেন, তাহাতে তাঁহার হাতে আর খাইবেন না – ইহা কি হইতে পারে? কিছুক্ষণ বাদেই আবার গোপালের মাকে ক্ষমা করিবেন এবং ঐ কথাগুলির আর কোন উচ্চবাচ্য হইবে না। কিন্তু ফলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। কারণ, উহার অল্পকাল পরেই ঠাকুরের গলায় অসুখ হইল। ক্রমে উহা বাড়িয়া ঠাকুরের ভাত খাওয়া বন্ধ হইল এবং গোপালের মা-র হাতে আর একদিনও ভাত খাওয়া হইল না।
ঐ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত
একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভাবাবস্থায় বলিতেছেন, “এর পরে আর কিছু খাব না, কেবল পায়সান্ন, কেবল পায়সান্ন।” শ্রীশ্রীমা ঐ সময়ে ঠাকুরের খাবার লইয়া আসিতেছিলেন। ঐ কথা শুনিতে পাইয়া এবং ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়া যে কথা যখনি নির্গত হয় তাহা কখনই নিরর্থক হয় না জানিয়া, ভয় পাইয়া বলিলেন – “আমি মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দেব, খাবে – পায়েস কেন?” ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় বলিয়া উঠিলেন, “না – পায়সান্ন।” তাহার অল্পকাল পরেই ঠাকুরের গলদেশে অসুখ হওয়ায় বাস্তবিকই আর কোনরূপ ব্যঞ্জনাদি খাওয়া চলিল না – কেবল দুধ-ভাত, দুধ-বার্লি ইত্যাদি খাইয়াই কাল কাটিতে লাগিল।
ঐ ৩য় দৃষ্টান্ত
কলিকাতার প্রসিদ্ধ দানশীল ধনী ৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিক মহাশয়কেই ঠাকুর তাঁহার চারিজন ‘রসদ্দারে’র ভিতর দ্বিতীয় রসদ্দার বলিয়া নির্দেশ করিতেন। রানী রাসমণির কালীবাটীর নিকটেই তাঁহার একখানি বাগান ছিল। উহাতে তিনি ভগবৎ-চর্চায় ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কাল কাটাইতেন। ঐ বাগানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য ঔষধালয়ও ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পেটের অসুখ অনেক সময়ই লাগিয়া থাকিত। একদিন ঐরূপ পেটের অসুখের কথা শম্ভুবাবু জানিতে পারিয়া তাঁহাকে একটু আফিম সেবন করিতে ও রাসমণির বাগানে ফিরিবার সময় উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। ঠাকুরও সে কথায় সম্মত হইলেন। তাহার পর কথাবার্তায় ঐ কথা দুইজনেই ভুলিয়া যাইলেন।
জগদম্বা ‘বেচালে পা পড়িতে’ দেন না
শম্ভুবাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পথে আসিয়া ঠাকুরের ঐ কথা মনে পড়িল এবং আফিম লইবার জন্য পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শম্ভুবাবু অন্দরে গিয়াছেন। ঠাকুর ঐ বিষয়ের জন্য তাঁহাকে আর না ডাকাইয়া তাঁহার কর্মচারীর নিকট হইতে একটু আফিম চাহিয়া লইয়া রাসমণির বাগানে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু পথে আসিয়াই ঠাকুরের কেমন একটা ঝোঁক আসিয়া পথ আর দেখিতে পাইলেন না! রাস্তার পাশে যে জলনালা আছে, তাহাতে যেন কে পা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল! ঠাকুর ভাবিলেন – এ কি? এ তো পথ নয়! অথচ পথও খুঁজিয়া পান না। অগত্যা কোনরূপে দিক ভুল হইয়াছে ঠাওরাইয়া, পুনরায় শম্ভুবাবুর বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন – সে দিকের পথ বেশ দেখা যাইতেছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া পুনরায় শম্ভুবাবুর বাগানের ফটকে আসিয়া সেখান হইতে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সাবধানে রাসমণির বাগানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুই-এক পা আসিতে না আসিতে আবার পূর্বের মতো হইল – পথ আর দেখিতে পান না। বিপরীত দিকে যাইতে পা টানে! এইরূপ কয়েকবার হইবার পর ঠাকুরের মনে উদয় হইল – “ওঃ, শম্ভু বলিয়াছিল, ‘আমার নিকট হইতে আফিম চাহিয়া লইয়া যাইও’; তাহা না করিয়া আমি তাহাকে না বলিয়া তাহার কর্মচারীর নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া যাইতেছি, সেজন্যই মা আমাকে যাইতে দিতেছেন না! কর্মচারীর শম্ভুর হুকুম ব্যতীত দেওয়া উচিত নয়, আর আমারও শম্ভু যেমন বলিয়াছে – তাহার নিকট হইতেই লওয়া উচিত। নহিলে যেভাবে আমি আফিম লইয়া যাইতেছি, উহাতে মিথ্যা ও চুরি এই দুটি দোষ হইতেছে; সেইজন্যই মা আমায় অমন করিয়া ঘুরাইতেছেন, ফিরিয়া যাইতে দিতেছেন না!” এই কথা মনে করিয়া শম্ভুবাবুর ঔষধালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, সে কর্মচারীও সেখানে নাই – সেও আহারাদি করিতে অন্যত্র গিয়াছে। কাজেই জানালা গলাইয়া আফিমের মোড়কটি ঔষধালয়ের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “ওগো, এই তোমাদের আফিম রহিল” – বলিয়া রাসমণির বাগানের দিকে চলিলেন। এবার যাইবার সময় আর তেমন ঝোঁক নাই; রাস্তাও বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে; বেশ চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিতেন, “মার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়েছি কিনা? – তাই মা হাত ধরে আছেন। একটুকু বেচালে পা পড়তে দেন না।” ঐরূপ কতই না দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের জীবনে শুনিয়াছি! চমৎকার ব্যাপার! আমরা কি এ সত্যনিষ্ঠা, এ সর্বাঙ্গীণ নির্ভরতার এতটুকু কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারি? ইহা কি সেই প্রকারের নির্ভর, ঠাকুর যাহা আমাদিগকে রূপকচ্ছলে বারংবার বলিতেন, “ওদেশে (ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরে) মাঠের মাঝে আলপথ আছে। তার উপর দিয়ে সকলে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে যায়। সরু আলপথ – চলে গেলে পাছে পড়ে যায়, সেজন্য বাপ ছোট ছেলেটিকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে, আর বড় ছেলেটি সেয়ানা বলে নিজেই বাপের হাত ধরে সঙ্গে যাচ্ছে। যেতে যেতে একটা শঙ্খচিল বা আর কিছু দেখে ছেলেগুলো আহ্লাদে হাততালি দিচ্ছে। কোলের ছেলেটি জানে বাপ আমায় ধরে আছে, নির্ভয়ে আনন্দ করতে করতে চলেছে। আর যে ছেলেটা বাপের হাত ধরে যাচ্ছিল, সে যেই পথের কথা ভুলে বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেছে – আর অমনি ঢিপ করে পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠল! সেই রকম মা যার হাত ধরেছেন, তার আর ভয় নেই; আর যে মার হাত ধরেছে, তার ভয় আছে – হাত ছাড়লেই পড়ে যাবে।”
ঠাকুরের নির্বিকল্প ভূমিতে উঠিবার পথে অন্তরায়
এইরূপে ঈশ্বরানুরাগের প্রাবল্যে সংসারের কোন বস্তু বা ব্যক্তির উপরে মনের একটা বিশেষ আকর্ষণ বা পশ্চাৎটান ছিল না বলিয়াই নির্বিকল্প সমাধিলাভের পথে সাংসারিক কোনরূপ বাসনা-কামনা ঠাকুরের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই। দাঁড়াইয়াছিল কেবল, ঠাকুর যাঁহাকে এতকাল ভক্তিভরে পূজা করিয়া, ভালবাসিয়া, সারাৎসারা পরাৎপরা বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিতেছিলেন – শ্রীশ্রীজগদম্বার সেই ‘সৌম্যাঽসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী’ মূর্তি! ঠাকুর বলিতেন, “মন কুড়িয়ে এক করে যাই এনেচি আর অমনি মা-র মূর্তি এসে সামনে দাঁড়াল! – তখন আর তাঁকে ত্যাগ করে তার পারে আগিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না! যতবার মন থেকে সব জিনিস তাড়িয়ে নিরালম্ব হয়ে থাকতে চেষ্টা করি, ততবারই ঐরূপ হয়। শেষে ভেবে চিন্তে মনে খুব জোর এনে, জ্ঞানকে অসি ভেবে, সেই অসি দিয়ে ঐ মূর্তিটাকে মনে মনে দুখানা করে কেটে ফেললুম! তখন মনে আর কিছুই রহিল না – হু হু করে একেবারে নির্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছুল।” আমাদের কাছে এগুলি যেন অর্থহীন কথার কথা মাত্র। কারণ, কখনো তো জগদম্বার কোন মূর্তি বা ভাব ঠিক ঠিক আপনার করিয়া লই নাই। কখনো তো কাহাকেও সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে শিখি নাই। ঐপ্রকার পূর্ণ ভালবাসা – মনের অন্তস্তল পর্যন্ত ব্যাপিয়া ভালবাসা – রহিয়াছে আমাদের – এই মাংসপিণ্ড শরীর ও মনের উপর! সেজন্যই মৃত্যুতে বা মনের হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্তনে আমাদের এত ভয় হয়! ঠাকুরের তো তাহা ছিল না। সংসারে একমাত্র জগদম্বার পাদপদ্মই মনে-জ্ঞানে সার জানিয়াছিলেন, এবং সেই পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া তাঁহার শ্রীমূর্তির দিবানিশি সেবা করিয়াই কাল কাটাইতেছিলেন; কাজেই ঐ মূর্তিকে যখন একবার কোন প্রকারে মন হইতে সরাইয়া ফেলিলেন, তখন আর মন কি লইয়া সংসারে থাকিবে? একেবারে আলম্বনবিহীন হইয়া, বৃত্তিরহিত হইয়া, নির্বিকল্প অবস্থায় যাইয়া দাঁড়াইল। পাঠক, এ কথা বুঝিতে না পার, একবার কল্পনা করিতেও চেষ্টা করিও। তাহা হইলেই বুঝিবে, ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে কতদূর আপনার করিয়াছিলেন – কি ‘পাঁচসিকে পাঁচ আনা’ মন দিয়া তিনি জগদম্বাকে ভালবাসিয়াছিলেন!
একুশদিন যে ভাবে থাকিলে শরীর নষ্ট হয় সেইভাবে ছয় মাস থাকা
এই নির্বিকল্প অবস্থায় প্রায় নিরন্তর থাকা ঠাকুরের ছয়মাস কাল ব্যাপিয়া হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, “যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌঁছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিন মাত্র শরীরটে থেকে শুকনো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে তেমনি পড়ে যায়, সেইখানে ছ-মাস ছিলুম। কখন কোন্ দিক দিয়ে যে দিন আসত, রাত যেত, তার ঠিকানাই হতো না! মরা মানুষের নাকে মুখে যেমন মাছি ঢোকে – তেমনি ঢুকত, কিন্তু সাড় হতো না। চুলগুলো ধুলোয় ধুলোয় জটা পাকিয়ে গিয়েছিল! হয়তো অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তারও হুঁশ হয় নাই! শরীরটে কি আর থাকত? – এই সময়েই যেত। তবে এই সময়ে একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে রুলের মতো একগাছা লাঠি ছিল। সে অবস্থা দেখেই চিনেছিল; আর বুঝেছিল – এ শরীরটে দিয়ে মা-র অনেক কাজ এখনো বাকি আছে, এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে! তাই খাবার সময় খাবার এনে মেরে মেরে হুঁশ আনবার চেষ্টা করত। একটু হুঁশ হচ্চে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত। এই রকমে কোন দিন একটু-আধটু পেটে যেত, কোন দিন যেত না। এই ভাবে ছ-মাস গেছে! তারপর এই অবস্থার কতদিন পরে শুনতে পেলুম মা-র কথা – ‘ভাবমুখে থাক্, লোকশিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাক্।’ তারপর অসুখ হলো – রক্ত-আমাশয়। পেটে খুব মোচড়, খুব যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় প্রায় ছ-মাস ভুগে ভুগে তবে শরীরে একটু একটু করে মন নাবল – সাধারণ মানুষের মতো হুঁশ এল! নতুবা থাকত থাকত মন আপনা-আপনি ছুটে গিয়ে সেই নির্বিকল্প অবস্থায় চলে যেত!”
ঠাকুরের সমাধি সম্বন্ধে ‘কাপ্তেনের’ কথা
বাস্তবিক ঠাকুরের শরীরত্যাগের দশ-বার বৎসর পূর্বেও তাঁহার দর্শনলাভ যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি তখনো ঠাকুরের কথাবার্তা শুনা বড় একটা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। চব্বিশ ঘণ্টা ভাব-সমাধি লাগিয়াই আছে! কথা কহিবে কে? নেপাল রাজসরকারের কর্মচারী শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায় – যাঁহাকে ঠাকুর ‘কাপ্তেন’ বলিয়া ডাকিতেন – মহাশয়ের মুখে আমরা শুনিয়াছি, তিনি একাদিক্রমে তিন অহোরাত্র ঠাকুরকে নিরন্তর সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন! তিনি আরও বলিয়াছিলেন, ঐরূপ বহুকালব্যাপী গভীর সমাধির সময় ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে – গ্রীবাদেশ হইতে মেরুদণ্ডের শেষ পর্যন্ত এবং জানু হইতে পদতল পর্যন্ত, উপর হইতে নিম্নের দিকে – মধ্যে মধ্যে গব্যঘৃত মালিশ করা হইত এবং ঐরূপ করা হইলে সমাধির উচ্চ ভাবভূমি হইতে ‘আমি আমার’ রাজ্যে আবার নামিতে ঠাকুরের সুবিধা বোধ হইত।
ঐ সম্বন্ধে ঠাকুরের নিজের কথা
আমাদের নিকট ঠাকুর কতদিন স্বয়ং বলিয়াছেন, “এখানকার মনের স্বাভাবিক গতি ঊর্ধ্বদিকে (নির্বিকল্পের দিকে)। সমাধি হলে আর নামতে চায় না। তোদের জন্য জোর করে নামিয়ে আনি। কোন একটা নিচেকার বাসনা না ধরলে নামবার তো জোর হয় না, তাই ‘তামাক খাব’, ‘জল খাব’, ‘সুক্তো খাব’, ‘অমুককে দেখব’, ‘কথা কইব’ – এইরূপ একটা ছোটখাট বাসনা মনে তুলে বার বার সেইটে আওড়াতে আওড়াতে তবে মন ধীরে ধীরে নিচে (শরীরে) নামে। আবার নামতে নামতে হয়তো সেই দিকে (ঊর্ধ্বে) চোঁচা দৌড়ুল। আবার তাকে তখন ঐরূপ বাসনা দিয়ে ধরে নামিয়ে আনতে হয়!” চমৎকার ব্যাপার! শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম, আর ভাবিতাম ‘অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর’ এ কথার যদি ঐ মানে হয়, তাহা হইলে ঐরূপ করা আমাদের জীবনে হইয়াছে আর কি! শরণাগত হইয়া থাকাই দেখিতেছি আমাদের একমাত্র উপায়। ঐরূপ করিতে যাইয়াও কিছুদিন বাদে দেখি, বিষম হাঙ্গামা! ঐ পথ আশ্রয় করিতে যাইয়াও দুষ্ট মন মাঝে মাঝে বলিয়া বসে – আমাকে ঠাকুর সকলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবেন না কেন? নরেন্দ্রনাথকে যতটা ভালবাসেন আমাকেও ততটা কেন না ভালবাসিবেন? আমি তদপেক্ষা ছোট কিসে? – ইত্যাদি! যাহা হউক এখন সে কথা – আমরা পূর্বানুসরণ করি।
মনোভাবপ্রসূত শারীরিক পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মত
উচ্চাঙ্গের ভাব এবং সমাধিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা ঠাকুরের নিকট হইতে যতদূর বুঝিয়াছি, অতঃপর তাহারই কিছু কিছু পাঠককে বলিয়া ‘ভাবমুখ’ অবস্থাটা যে কি, তাহাই এখন বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি – উচ্চাবচ যে ভাবই মনে আসুক না কেন, উহার সহিত কোন না কোন প্রকার শারীরিক পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। ইহা আর বুঝাইতে হয় না – নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। ক্রোধের উদয়ে একপ্রকার, ভালবাসায় অন্যপ্রকার – এইরূপ নিত্যানুভূত সাধারণ ভাবসমূহের আলোচনাতেই উহা সহজে বুঝা যায়। আবার সৎ বা অসৎ কোনপ্রকার চিন্তার সবিশেষ আধিক্য কাহারও মনে থাকিলে তাহার শরীরেও এতটা পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাহাকে দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে – ইহার এরূপ প্রকৃতি। ‘অমুককে দেখিলেই মনে হয় রাগী, কামুক বা সাধু’ – এরূপ কথার নিত্য ব্যবহার হওয়াই ঐ বিষয়ের প্রমাণ। আবার দানবতুল্য বিকটাকৃতি বিকৃত-স্বভাবাপন্ন লোক যদি কোন কারণে সৎচিন্তায়, সাধুভাবে নিরন্তর ছয়মাস কাল কাটায় তো তাহার আকৃতি হাব-ভাব পূর্বাপেক্ষা কত কোমল ও সরল হইয়া আসে, তাহাও বোধ হয় আমাদের ভিতর অনেকের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছে। পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ বলেন – যে প্রকার ভাবই তোমার মনে উঠুক না কেন, উহা তোমার মস্তিষ্কে চিরকালের নিমিত্ত একটি দাগ অঙ্কিত করিয়া যাইবে। এইরূপে ভাল-মন্দ দুইপ্রকার ভাবের দুইপ্রকার দাগের সমষ্টির স্বল্পাধিক্য লইয়াই তোমার চরিত্র গঠিত ও তুমি ভাল বা মন্দ লোক বলিয়া পরিগণিত। প্রাচ্যের, বিশেষতঃ ভারতের যোগি-ঋষিগণ বলেন, ঐ দুইপ্রকার ভাব মস্তিষ্কে দুইপ্রকার দাগ অঙ্কিত করিয়াই শেষ হইল না – ভবিষ্যতে আবার তোমাকে পুনরায় ভাল-মন্দ কর্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে এরূপ সূক্ষ্ম প্রেরণাশক্তিতে পরিণত হইয়া মেরুদণ্ডের শেষভাগে অবস্থিত ‘মূলাধার’ নামক মেরুচক্রে নিত্যকাল অবস্থান করিতে থাকে; জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত ঐরূপ প্রেরণাশক্তিসমূহের উহাই আবাসভূমি।
কুণ্ডলিনীর সঞ্চিত পূর্ব-সংস্কারের আবাসস্থান ও ঐ সকলের নাশ কিরূপে হয়
ঐসকলের নামই সংস্কার বা পূর্ব-সংস্কার, এবং ঐসকলের নাশ একমাত্র শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলে বা নির্বিকল্প সমাধি-লাভ হইলে তবেই হইয়া থাকে। নতুবা দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবার সময়ও জীব ঐ সংস্কারের পুঁটুলিটি ‘বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ’ বগলে করিয়া লইয়া যায়।
শরীর ও মনের সম্বন্ধ
অদ্বৈতজ্ঞান বা শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শরীর ও মনের পূর্বোক্তরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। শরীরে কিছু হইলে মনে আঘাত লাগে, আবার মনে কিছু হইলে শরীরে আঘাত অনুভব হয়। আবার ব্যক্তির শরীর-মনের ন্যায়, ব্যক্তির সমষ্টি – সমগ্র মনুষ্যজাতির শরীর ও মনে এইপ্রকার সম্বন্ধ বর্তমান। তোমার শরীর-মনের ঘাত-প্রতিঘাত আমার ও অপর সকলের শরীর-মনে লাগে। এইরূপে বাহ্য ও আন্তর, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ নিত্য সম্বন্ধে অবস্থিত ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাত করিতেছে। সেইজন্যই দেখা যায় – যেখানে সকলে শোকাকুল, সেখানে তোমারও মনে শোকের উদয় হইবে। যেখানে সকলে ভক্তিমান, সেখানে তোমারও মনে বিনা চেষ্টায় ভক্তিভাব আসিবে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও বুঝিতে হইবে।
ভাবসকল সংক্রামক বলিয়াই সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠেয়
সেইজন্যই দেখা যায় শারীরিক রোগ ও স্বাস্থ্যের ন্যায় মানসিক বিকার বা ভাবসকলেরও সংক্রামিকা শক্তি আছে। উহারাও অধিকারিভেদে সংক্রমণ করিয়া থাকে। ভগবদনুরাগ উদ্দীপিত করিবার জন্য শাস্ত্র সাধুসঙ্গের এত মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। সেইজন্যই ঠাকুর যাহারা তাঁহার নিকট একবার যাইত তাহাদের “এখানে যাওয়া-আসা করো – প্রথম প্রথম এখানে বেশি বেশি যাওয়া-আসাটা রাখতে হয়” ইত্যাদি বলিতেন। যাক এখন সে কথা।
একনিষ্ঠাপ্রসূত শারীরিক পরিবর্তন
সাধারণ মানসিক ভাবসমূহের ন্যায় শ্রীভগবানের প্রতি একান্ত একনিষ্ঠ তীব্র অনুরাগে যে সমস্ত ভাব মনে উদয় হয়, সেসকলেও অপূর্ব শারীরিক পরিবর্তন আনিয়া দেয়। যথা – ঐরূপ অনুরাগ উপস্থিত হইলে সাধকের রূপরসাদির উপর টান কমিয়া যায় – স্বল্পাহার, স্বল্পনিদ্রা হয় – খাদ্যবিশেষে রুচি ও অন্যপ্রকার খাদ্যে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয় – স্ত্রীপুত্রাদি যেসকল ব্যক্তির সহিত মায়িক সম্বন্ধ তাহাকে শ্রীভগবান হইতে বিমুখ করে, তাহাদিগকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় – বায়ুপ্রধান ধাত (ধাতু) হয় – ইত্যাদি; ঠাকুর যেমন বলিতেন, “বিষয়ী লোকের হাওয়া সইতে পারতুম না, আত্মীয়-স্বজনের সংসর্গে যেন দম বন্ধ হয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যাবার মতো হতো”; আবার বলিতেন, “ঈশ্বরকে যে ঠিক ঠিক ডাকে, তার শরীরে মহাবায়ু গর-গর করে মাথায় গিয়ে উঠবেই উঠবে” ইত্যাদি।
ভক্তিপথ ও যোগমার্গের সামঞ্জস্য
অতএব দেখা যাইতেছে, ভগবদনুরাগে যেসকল মানসিক পরিবর্তন বা ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐসকলেরও এক-একটা শারীরিক প্রতিকৃতি বা রূপ আছে। মনের দিক দিয়া দেখিয়া বৈষ্ণবতন্ত্র ঐসকল ভাবকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর – এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; আর ঐসকল মানসিক বিকারকে আশ্রয় করিয়া যেসকল শারীরিক পরিবর্তন উপস্থিত হয়, তাহার দিক দিয়া দেখিয়া যোগশাস্ত্র মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কান্তর্গত কুণ্ডলিনীশক্তি ও ষট্চক্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন।
কুণ্ডলিনী কাহাকে বলে ও তাহার সুপ্ত এবং জাগ্রত অবস্থা
কুণ্ডলী বা কুণ্ডলিনীশক্তির সংক্ষেপে পরিচয় আমরা ইতঃপূর্বেই দিয়াছি। ইহজন্মে এবং পূর্ব পূর্ব জন্মজন্মান্তরে যত মানসিক পরিবর্তন বা ভাব জীবের উপস্থিত হইতেছে ও হইয়াছিল, তৎসমূহের সূক্ষ্ম শারীরিক প্রতিকৃতি অবলম্বনে অবস্থিতা মহা ওজস্বিনী প্রেরণাশক্তিকেই পতঞ্জলি-প্রমুখ ঋষিগণ ঐ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যোগী বলেন, উহা বদ্ধজীবে প্রায় সম্পূর্ণ সুপ্ত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। উহার ঐরূপ সুপ্তাবস্থাতেই জীবের স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি বৃত্তির উদয়। উহা যদি কোনরূপে সম্পূর্ণ জাগরিত বা প্রকাশাবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তবেই জীবকে পূর্ণজ্ঞানলাভে প্রেরণ করিয়া শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়। যদি বল, সুপ্তাবস্থায় কুণ্ডলিনীশক্তি হইতে কেমন করিয়া স্মৃতি-কল্পনা প্রভৃতির উদয় হইতে পারে? তদুত্তরে বলি, সুপ্ত হইলেও বাহিরের রূপ-রসাদি পদার্থ পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া নিরন্তর মস্তিষ্কে যে আঘাত করিতেছে তজ্জন্য একটু-আধটু ক্ষণমাত্রস্থায়ী চেতনা তাহার আসিয়া উপস্থিত হয়। যেমন মশকদষ্ট নিদ্রিত ব্যক্তির হস্ত স্বতই মশককে আঘাত বা কণ্ডূয়নাদি করে, সেইরূপ।
জাগরিতা কুণ্ডলিনীর গতি – ষট্চক্রভেদ ও সমাধি
যোগী বলেন, মস্তিষ্কমধ্যগত ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ অবকাশ বা আকাশে অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান। তাঁহার প্রতি পূর্বোক্ত কুণ্ডলীশক্তির বিশেষ অনুরাগ অথবা শ্রীভগবান তাহাকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু জাগরিতা না থাকায় কুণ্ডলীশক্তির সে আকর্ষণ অনুভব হইতেছে না। জাগরিতা হইবামাত্র উহা শ্রীভগবানের ঐ আকর্ষণ অনুভব করিবে এবং তাঁহার নিকটস্থ হইবে। ঐরূপে কুণ্ডলীর শ্রীভগবানের নিকটস্থ হইবার পথও আমাদের প্রত্যেকের শরীরে বর্তমান। মস্তিষ্ক হইতে আরব্ধ হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বরাবর ঐ পথ মেরুদণ্ডের মূলে ‘মূলাধার’ নামক মেরুচক্র পর্যন্ত আসিয়াছে। ঐ পথই যোগশাস্ত্র-কথিত সুষুম্নাবর্ত্ম। পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ ঐ পথকেই canal centralis (মধ্যপথ) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, কিন্তু উহার কোনরূপ আবশ্যকতা বা কার্যকারিতা এ পর্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই। ঐ পথ দিয়াই কুণ্ডলী পূর্বে পরমাত্মা হইতে বিযুক্তা হইয়া মস্তিষ্ক হইতে মেরুচক্রে বা মূলাধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছে। আবার ঐ পথ দিয়াই উহা মেরুদণ্ডমধ্যে ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে অবস্থিত ছয়টি চক্র ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে মস্তিষ্কে আসিয়া উপনীত হয়।1 কুণ্ডলী জাগরিতা হইয়া এক চক্র হইতে অন্য চক্রে যেমনি আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি জীবের এক এক প্রকার অভূতপূর্ব উপলব্ধি হইতে থাকে; এবং ঐ প্রকারে যখনি উহা মস্তিষ্কে উপনীত হয়, তখনি জীবের ধর্মবিজ্ঞানের চরমোপলব্ধি বা অদ্বৈতজ্ঞানে ‘কারণং কারণানাং’ পরমাত্মার সহিত তন্ময়ত্ব আসে। তখনই জীবের ভাবেরও চরমোপলব্ধি হয় বা যে মহাভাব অবলম্বনে অপর সকল ভাব মানবমনে সর্বক্ষণ উদিত হইতেছে, সেই ‘ভাবাতীত ভাবে’ তন্ময় হইয়া অবস্থান-করা-রূপ অবস্থা আসে।
1. যোগশাস্ত্রে এই ছয়টি মেরুচক্রের নাম ও বিশেষ বিশেষ অবস্থানস্থল পর পর নির্দিষ্ট আছে। যথা – মেরুদণ্ডের শেষভাগে ‘মূলাধার’ (১), তদূর্ধ্বে লিঙ্গমূলে ‘স্বাধিষ্ঠান’ (২), তদূর্ধ্বে নাভিস্থলে ‘মণিপুর’ (৩), তদূর্ধ্বে হৃদয়ে ‘অনাহত’ (৪), তদূর্ধ্বে কণ্ঠে ‘বিশুদ্ধ’ (৫), তদূর্ধ্বে ভ্রূমধ্যে ‘আজ্ঞা’ (৬), অবশ্য এই ছয়টি চক্রই মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্না পথেই বর্তমান – অতএব ‘হৃদয়’ ‘কণ্ঠ’ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তদ্বিপরীতে অবস্থিত মেরুমধ্যস্থ স্থলই লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।
ঐ সম্বন্ধে ঠাকুরের অনুভব
কি সরল কথা দিয়াই না ঠাকুর যোগের এইসকল জটিল তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝাইতেন! বলিতেন, “দ্যাখ, সড় সড় করে একটা পা থেকে মাথায় গিয়ে উঠে! যতক্ষণ না সেটা মাথায় গিয়ে উঠে ততক্ষণ হুঁশ থাকে; আর যেই সেটা মাথায় গিয়ে উঠল আর একেবারে বেব্ভুল হয়ে যাই, তখন আর দেখাশুনাই থাকে না, তা কথা কওয়া! কথা কইবে কে? – ‘আমি’ ‘তুমি’ এ বুদ্ধিই চলে যায়! মনে করি তোদের সব বলব – সেটা উঠতে উঠতে কত কি দর্শন-টর্শন হয় সব কথা বলব। যতক্ষণ সেটা (হৃদয় ও কণ্ঠ দেখাইয়া) এ অবধি বা এই অবধি বড় জোর উঠেছে, ততক্ষণ বলা চলে ও বলি; কিন্তু যেই সেটা (কণ্ঠ দেখাইয়া) এখান ছাড়িয়ে উঠল, আর অমনি যেন কে মুখ চেপে ধরে, আর বেব্ভুল হয়ে যায় – সামলাতে পারিনি! (কণ্ঠ দেখাইয়া) ওর উপরে গেলে কি রকম সব দর্শন হয় তা বলতে গিয়ে যেই ভাবচি কি রকম দেখিছি, আর অমনি মন হুস্ করে উপরে উঠে যায় – আর বলা যায় না!”
ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিকালের অনুভব বলিবার চেষ্টা
আহা, কতদিন যে ঠাকুর কণ্ঠের উপরিস্থ চক্রে মন উঠিলে কিরূপ দর্শনাদি হয় তাহা অশেষ প্রয়াসপূর্বক সামলাইয়া আমাদের নিকট বলিতে যাইয়া অপারগ হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না! আমাদের এক বন্ধু বলেন, “একদিন ঐরূপে খুব জোর করিয়া বলিলেন, ‘আজ তোদের কাছে সব কথা বলব, একটুও লুকোব না’ – বলিয়া আরম্ভ করিলেন। হৃদয় ও কণ্ঠ পর্যন্ত সকল চক্রাদির কথা বেশ বলিলেন, তারপর ভ্রূমধ্যস্থল দেখাইয়া বলিলেন, ‘এইখানে মন উঠলেই পরমাত্মার দর্শন হয় ও জীবের সমাধি হয়। তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে কেবল একটি স্বচ্ছ পাতলা পর্দামাত্র আড়াল (ব্যবধান) থাকে। সে তখন এইরকম দ্যাখে’ – বলিয়া যেই পরমাত্মার দর্শনের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিভঙ্গে পুনরায় বলিতে চেষ্টা করিলেন, পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন! এইরূপ বার বার চেষ্টার পর সজলনয়নে আমাদের বলিলেন, ‘ওরে, আমি তো মনে করি সব কথা বলি, এতটুকুও তোদের কাছে লুকোব না, কিন্তু মা কিছুতেই বলতে দিলে না – মুখ চেপে ধরলে!’ আমরা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম – এ কি ব্যাপার! দেখিতেছি উনি এত চেষ্টা করিতেছেন, বলিবেন বলিয়া। না বলিতে পারিয়া উঁহার কষ্টও হইতেছে বুঝিতেছি, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছেন না – মা বেটী কিন্তু ভারি দুষ্ট! উনি ভাল কথা বলিবেন, ভগবদ্দর্শনের কথা বলিবেন, তাহাতে মুখ চাপিয়া ধরা কেন বাপু? তখন কি আর বুঝি যে, মন-বুদ্ধি যাহাদের সাহায্যে বলাকহাগুলো হয়, তাহাদের দৌড় বড় বেশি দূর নয়; আর তাহারা যতদূর দৌড়াইতে পারে তাহার বাহিরে না গেলে পরমাত্মার পূর্ণ দর্শন হয় না! ঠাকুর যে আমাদের প্রতি ভালবাসায় অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতেছেন – এই কথা কি তখন বুঝিতে পারিতাম?”
সমাধিপথে কুণ্ডলিনীর পাঁচ প্রকারের গতি
কুণ্ডলিনীশক্তি সুষুম্নাপথে উঠিবার কালে যে যে রূপ অনুভব হয়, তৎসম্বন্ধে ঠাকুর আরও বিশেষ করিয়া বলিতেন, “দেখ, যেটা সড় সড় করে মাথায় উঠে, সেটা সব সময় এক রকম ভাবে উঠে না। শাস্ত্রে সেটার পাঁচ রকম গতির কথা আছে – যথা, পিপীলিকাগতি – যেমন পিঁপড়েগুলো খাবার মুখে করে সার দিয়ে সুড়সুড় করে যায়, সেই রকম পা থেকে একটা সুড়সুড়ানি আরম্ভ হয়ে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে, মাথা পর্যন্ত যায় আর সমাধি হয়! ভেকগতি – ব্যাঙগুলো যেমন টুপ টুপ টুপ – টুপ টুপ টুপ করে দু-তিন বার লাফিয়ে একটু থামে, আবার দু-তিন বার লাফিয়ে আবার একটু থামে, সেইরকম করে কি একটা পায়ের দিক থেকে মাথায় উঠছে বোঝা যায়; আর যেই মাথায় উঠল আর সমাধি! সর্পগতি – সাপগুলো যেমন লম্বা হয়ে বা পুঁটুলি পাকিয়ে চুপ করে পড়ে আছে, আর যেই সামনে খাবার (শিকার) দেখেছে বা ভয় পেয়েছে, অমনি কিলবিল কিলবিল করে এঁকে বেঁকে ছোটে, সেইরকম করে ওটা কিলবিল করে একেবারে মাথায় গিয়ে উঠে আর সমাধি! পক্ষিগতি – পক্ষীগুলো যেমন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে বসবার সময় হুস করে উড়ে কখনো একটু উঁচুতে উঠে, কখনো একটু নিচুতে নাবে, কিন্তু কোথাও বিশ্রাম করে না, একেবারে যেখানে বসবে মনে করেছে সেইখানে গিয়ে বসে, সেইরকম করে ওটা মাথায় উঠে ও সমাধি হয়! বাঁদরগতি – হনুমানগুলো যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে যাবার সময় ‘উউপ’ করে এক ডাল থেকে আর এক ডালে গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে ‘উউপ’ করে আর এক ডালে গিয়ে পড়ল – এইরূপে দু-তিন লাফে যেখানে মনে করেছে সেখানে উপস্থিত হয়, সেই রকম করে ওটাও দু-তিন লাফে মাথায় গিয়ে উঠে বোঝা যায় ও সমাধি হয়।”
বেদান্তের সপ্তভূমি ও প্রত্যেক ভূমিলব্ধ আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা
কুণ্ডলিনীশক্তি সুষুম্নাপথে উঠিবার কালে প্রতি চক্রে কি কি প্রকার দর্শন হয় তদ্বিষয়ে বলিতেন, “বেদান্তে আছে সপ্ত ভূমির কথা। এক এক রকম দর্শন হয়। মনের স্বভাবতঃ নিচের তিন ভূমিতে ওঠা-নামা, ঐ দিকেই দৃষ্টি – গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি – খাওয়া, পরা, রমণ ইত্যাদিতে। ঐ তিন ভূমি ছাড়িয়ে যদি হৃদয়ে উঠে তো তখন তার জ্যোতি দর্শন হয়। কিন্তু হৃদয়ে কখনো কখনো উঠলেও মন আবার নিচের তিন ভূমি – গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে যায়। হৃদয় ছাড়িয়ে যদি কারও মন কণ্ঠে উঠে তো সে আর ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কোন কথা – যেমন বিষয়ের কথা-টথা, কইতে পারে না। তখন তখন এমনি হতো – বিষয়কথা যদি কেউ কয়েছে তো মনে হতো মাথায় লাঠি মারলে; দূরে পঞ্চবটীতে পালিয়ে যেতাম, সেখানে ওসব কথা শুনতে পাব না। বিষয়ী দেখলে ভয়ে লুকোতুম! আত্মীয়-স্বজনকে যেন কূপ বলে মনে হতো – মনে হতো তারা যেন টেনে কূপে ফেলবার চেষ্টা করছে, পড়ে যাব আর উঠতে পারব না। দম বন্ধ হয়ে যেত, মনে হতো যেন প্রাণ বেরোয় বেরোয় – সেখান থেকে পালিয়ে এলে তবে শান্তি হতো! – কণ্ঠে উঠলেও মন আবার গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে যেতে পারে, তখন সাবধানে থাকতে হয়। তারপর কণ্ঠ ছাড়িয়ে যদি কারও মন ভ্রূমধ্যে ওঠে তো তার আর পড়বার ভয় নেই। তখন পরমাত্মার দর্শন হয়ে নিরন্তর সমাধিস্থ থাকে। এখানটার আর সহস্রারের মাঝে একটা কাচের মতো স্বচ্ছ পর্দামাত্র আড়াল আছে। তখন পরমাত্মা এত নিকটে যে, মনে হয় যেন তাঁতে মিশে গেছি; এক হয়ে গেছি; কিন্তু তখনো এক হয়নি। এখান থেকে মন যদি নামে তো বড় জোর কণ্ঠ বা হৃদয় পর্যন্ত নামে – তার নিচে আর নামতে পারে না। জীবকোটিরা এখান থেকে আর নামে না – একুশ দিন নিরন্তর সমাধিতে থাকবার পর ঐ আড়ালটা বা পর্দাটা ভেদ হয়ে যায়, আর তাঁর সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। সহস্রারে পরমাত্মার সঙ্গে একেবারে মেশামেশি হয়ে যাওয়াই সপ্তম ভূমিতে উঠা।”
ঠাকুরের শ্রুতিধরত্ব
ঠাকুরকে ঐসব বেদ-বেদান্ত, যোগ-বিজ্ঞানের কথা কহিতে শুনিয়া আমাদের কেহ কেহ আবার কখনো কখনো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, ‘মশাই, আপনি তো লেখাপড়ার কখনো ধার ধারেননি, এত সব জানলেন কোথা থেকে?’ অদ্ভুত ঠাকুরের ঐ অদ্ভুত প্রশ্নেও বিরক্তি নাই! একটু হাসিয়া বলিতেন, “নিজে পড়ি নাই, কিন্তু ঢের সব যে শুনেছি গো! সেসব মনে আছে! অপরের কাছ থেকে, ভাল ভাল পণ্ডিতের কাছ থেকে, বেদ-বেদান্ত দর্শন-পুরাণ সব শুনেছি। শুনে, তাদের ভেতর কি আছে জেনে, তারপর সেগুলোকে (গ্রন্থগুলোকে) দড়ি দিয়ে মালা করে গেঁথে গলায় পরে নিয়েচি – ‘এই নে তোর শাস্ত্র-পুরাণ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে’ বলে মার পাদপদ্মে ফেলে দিয়েছি!”
ঠাকুরের অদ্বৈতভাব সহজে বুঝান
বেদান্তের অদ্বৈতভাব বা ভাবাতীত ভাব সম্বন্ধে বলিতেন, “ওটা সবশেষের কথা। কি রকম জানিস? – যেমন অনেক দিনের পুরোনো চাকর। মনিব তার গুণে খুশি হয়ে তাকে সকল কথায় বিশ্বাস করে, সব বিষয়ে পরামর্শ করে। একদিন খুব খুশি হয়ে তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল! চাকর সঙ্কোচ করে ‘কি কর, কি কর’ বললেও মনিব জোর করে টেনে বসিয়ে বললে, ‘আঃ বস না! তুইও যে, আমিও সে’ – সেই রকম।”
ঐ দৃষ্টান্ত – স্বামী তুরীয়ানন্দ
আমাদের জনৈক বন্ধু1 এক সময়ে বেদান্তচর্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর তখন বর্তমান, এবং উঁহার আকুমার ব্রহ্মচর্য, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য উঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। বেদান্তচর্চা ও ধ্যানভজনাদিতে নিবিষ্ট হইয়া বন্ধুটি ঠাকুরের নিকট পূর্বে পূর্বে যেমন ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন সেরূপ কিছুদিন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বিষয় অলক্ষিত থাকে নাই। বন্ধুটির সঙ্গে যাতায়াত করিত এমন এক ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রে, তুই যে একলা – সে আসেনি?” জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিল, “সে মশাই আজকাল খুব বেদান্তচর্চায় মন দিয়েছে। রাত দিন পাঠ, বিচারতর্ক নিয়ে আছে। তাই বোধ হয় সময় নষ্ট হবে বলে আসেনি।” ঠাকুর শুনিয়া আর কিছুই বলিলেন না।
1. স্বামী তুরীয়ানন্দ।
বেদান্ত আর কি? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা – এই ধারণা
উহার কিছুদিন পরেই, আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, “কি গো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্তবিচার করচ? তা বেশ, বেশ। তা বিচার তো খালি এই গো – ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা – না আর কিছু?”
বন্ধু – আজ্ঞা হাঁ, আর কি?
বন্ধু বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর সেদিন ঐ কয়টি কথায় বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার চক্ষু যেন সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন – বাস্তবিকই তো, ঐ কয়টি কথা হৃদয়ে ধারণা হইলে বেদান্তের সকল কথাই বুঝা হইল!
ঠাকুর – শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা – আগে শুনলে; তারপর মনন – বিচার করে মনে মনে পাকা করলে; তারপর নিদিধ্যাসন – মিথ্যা বস্তু জগৎকে ত্যাগ করে সদ্বস্তু ব্রহ্মের ধ্যানে মন লাগালে – এই। কিন্তু তা না হয়ে শুনলুম, বুঝলুম কিন্তু যেটা মিথ্যা সেটাকে ছাড়তে চেষ্টা করলুম না – তা হলে কি হবে? সেটা হচ্চে সংসারীদের জ্ঞানের মতো; ও রকম জ্ঞানে বস্তুলাভ হয় না। ধারণা চাই, ত্যাগ চাই – তবে হবে। তা না হলে, মুখে বলচ বটে, ‘কাঁটা নেই, খোঁচা নেই’, কিন্তু যেই হাত দিয়েছ অমনি প্যাঁট করে কাঁটা ফুটে উঁহু উঁহু করে উঠতে হবে, মুখে বলচ ‘জগৎ নেই, অসৎ – একমাত্র ব্রহ্মই আছেন’ ইত্যাদি, কিন্তু যেই জগতের রূপরসাদি বিষয় সম্মুখে আসা, অমনি সেগুলো সত্যজ্ঞান হয়ে বন্ধনে পড়া। পঞ্চবটীতে এক সাধু এসেছিল। সে লোকজনের সঙ্গে খুব বেদান্ত-টেদান্ত বলে। তারপর একদিন শুনলুম, একটা মাগীর সঙ্গে নটঘট হয়েছে। তারপর ওদিকে শৌচে গিয়েছি, দেখি সে বসে আছে। বললুম, ‘তুমি এত বেদান্ত-টেদান্ত বল, আবার এসব কি?’ সে বললে, ‘তাতে কি? আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাতে দোষ নেই। যখন জগৎটাই তিন কালে মিথ্যা হলো, তখন ঐটেই কি সত্য হবে? ওটাও মিথ্যা।’ আমি তো শুনে বিরক্ত হয়ে বলি, ‘তোর অমন বেদান্তজ্ঞানে আমি মুতে দি!’ ওসব হচ্চে সংসারী, বিষয়ী জ্ঞানীর জ্ঞান। ও জ্ঞান জ্ঞানই নয়।
বন্ধু বলেন, সেদিন ঐ পর্যন্ত কথাই হইল। কথাগুলি ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটীতলে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন। ইতঃপূর্বে তাঁহার ধারণা ছিল – উপনিষৎ, পঞ্চদশী ইত্যাদি নানা জটিল গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে, সাংখ্য-ন্যায়াদি দর্শনে ব্যুৎপত্তিলাভ না করিলে বেদান্ত কখনই বুঝা যাইবে না এবং মুক্তিলাভও সুদূরপরাহত থাকিবে। ঠাকুরের সেদিনকার কথাতেই বুঝিলেন, বেদান্তের যত কিছু বিচার সব ঐ ধারণাটি হৃদয়ে দৃঢ় করিবার জন্য। ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন ও বিচারগ্রন্থ পড়িয়া যদি কাহারও মনে ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’ কথাটি নিশ্চয় ধারণা না হয়, তবে ঐসকল পড়া না পড়া উভয়ই সমান। ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং তখন হইতে গ্রন্থপাঠাদি অপেক্ষা সাধনভজনেই অধিক মনোনিবেশ করিবেন – ঐরূপ নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। এইরূপে তিনি সাধনসহায়ে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিবার সঙ্কল্প মনে স্থির ধারণা করিয়া তদবধি তদনুরূপ কার্যেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন।
ঈশ্বরকৃপা ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না
ঠাকুর কলিকাতায় কাহারও বাটীতে আগমন করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কথা তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণের মধ্যে জানাজানি হইয়া যাইত। কতকগুলি লোক যে ঐ কার্যের বিশেষভাবে ভার লইয়া ঐ কথা সকলকে জানাইয়া আসিতেন তাহা নহে। কিন্তু ভক্তদিগের প্রাণ ঠাকুরকে সর্বদা দর্শন করিবার জন্য এতই উন্মুখ হইয়া থাকিত এবং কার্যগতিকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতে না পারিলে পরস্পরের বাটীতে সর্বদা গমনাগমন করিয়া তাঁহার কথাবার্তায় এত আনন্দানুভব করিত যে, তাহাদের ভিতর একজন কোনরূপে ঠাকুরের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহা অনেকের ভিতর বিনা চেষ্টায় মুখে মুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িত। ঠাকুরের শক্তিতে ভক্তগণ পরস্পরে কি যে এক অনির্বচনীয় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বুঝানো দুষ্কর। কলিকাতায় বাগবাজার, সিমলা ও আহিরীটোলা পল্লীতেই ঠাকুরের অনেক ভক্তেরা বাস করিতেন, তজ্জন্য ঐ তিন স্থানেই ঠাকুরের আগমন অধিকাংশ সময়ে হইত। তন্মধ্যে আবার বাগবাজারেই তাঁহার অধিক পরিমাণে আগমন হইত।
পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন বাগবাজারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। বাগবাজার অঞ্চলের ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া অনেকে উপস্থিত হইলেন। আমাদের পূর্বোক্ত বন্ধুর আবাস অতি নিকটেই ছিল। ঠাকুর তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করায় পাড়ার পরিচিত জনৈক প্রতিবেশী যুবক যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। বলরামবাবুর বাটীর দ্বিতলের প্রশস্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই বন্ধু ভক্তমণ্ডলীপরিবৃত ঠাকুরকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটেই একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সহাস্যে কুশলপ্রশ্নমাত্র করিয়াই উপস্থিত প্রসঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।
দুই-একটি কথার ভাবেই বন্ধু বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন – জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হইবার নহে। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর তাঁহার মনের ভুল ধারণাটি দূর করিবার জন্যই অদ্য যেন ঐ প্রসঙ্গ উঠাইয়াছেন। মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছেন তাহা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন!
শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন – “কি জান? কাম-কাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অসৎ বলে ঠিক ঠিক মনে জ্ঞানে ধারণা হওয়া কি কম কথা? তাঁর দয়া না হলে কি হয়? তিনি কৃপা করে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে? তার কতটুকু শক্তি? সেই শক্তি দিয়ে সে কতটুকু চেষ্টা করতে পারে?” এইরূপে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশাপ্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “একটা ঠিক করতে পারে না, আবার আর একটা চায়!” ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় গান ধরিলেন –
“ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব,
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে।”
গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে এত জলধারা বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের খানিকটা ভিজিয়া গেল! বন্ধুও সে অপূর্ব শিক্ষায় দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিয়া আকুল। কতক্ষণে তবে দুইজনে প্রকৃতিস্থ হইলেন। বন্ধু বলেন, “সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেদিন হইতেই বুঝিলাম ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।”
শশধর পণ্ডিত ঠাকুরকে যোগশক্তিবলে রোগ সারাইতে বলায় ঠাকুরের উত্তর
ঠাকুরের অদ্বৈতজ্ঞানসম্বন্ধীয় গভীরতা সম্বন্ধে আর একটি কথা এখানে আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঠাকুরের তখন অসুখ – কাশীপুরের বাগানে – বাড়াবাড়ি। শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি, সঙ্গে কয়েকজন, অসুখের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিলেন। পণ্ডিতজী কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন, “মহাশয়, শাস্ত্রে পড়েছি আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করে ফেলতে পারেন। আরাম হোক মনে করে মন একাগ্র করে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করলে হয় না?”
ঠাকুর বলিলেন, “তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বললে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?”
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ ও ঠাকুরের উত্তর
পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ ভক্তেরা নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। পণ্ডিতজী চলিয়া যাইবার পরেই ঠাকুরকে ঐরূপ করিবার জন্য একেবারে বিশেষভাবে ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন, “আপনাকে অসুখ সারাতেই হবে, আমাদের জন্য সারাতে হবে।”
ঠাকুর – আমার কি ইচ্ছা রে যে, আমি রোগে ভুগি; আমি তো মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কই? সারা, না সারা, মা-র হাত।
স্বামী বিবেকানন্দ – তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন।
ঠাকুর – তোরা তো বলছিস, কিন্তু ও কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না রে!
শ্রীযুত স্বামীজী – তা হবে না মশাই, আপনাকে বলতেই হবে। আমাদের জন্য বলতে হবে।
ঠাকুর – আচ্ছা, দেখি, পারি তো বলব।
কয়েক ঘণ্টা পরে শ্রীযুক্ত স্বামীজী পুনরায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশায়, বলেছিলেন? মা কি বললেন?”
ঠাকুর – মাকে বললুম (গলার ক্ষত দেখাইয়া), ‘এইটের দরুন কিছু খেতে পারি না; যাতে দুটি খেতে পারি করে দে।’ তা মা বললেন – তোদের সকলকে দেখিয়ে – ‘কেন? এই যে এত মুখে খাচ্চিস!’ আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।
ঠাকুরের অদ্বৈতভাবের গভীরতা
কি অদ্ভুত দেহবুদ্ধির অভাব! কি অপূর্ব অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান! তখন ছয়মাস কাল ধরিয়া ঠাকুরের নিত্য আহার, বোধ হয় চারি-পাঁচ ছটাক বার্লি মাত্র, সেই অবস্থায় জগন্মাতা যাই বলিয়াছেন, ‘এই যে এত মুখে খাচ্চিস’, অমনি “কি কুকর্ম করিয়াছি, এই একটা ক্ষুদ্র শরীরকে ‘আমি’ বলিয়াছি!” – মনে করিয়া ঠাকুর লজ্জায় হেঁটমুখ ও নিরুত্তর হইলেন। পাঠক, এ ভাব কি একটুও কল্পনায় আনিতে পার?
ঠাকুরের সকল প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া
কি অদ্ভুত ঠাকুরের সঙ্গে দেখাই না আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে! জ্ঞান-ভক্তি, যোগ-কর্ম, পুরান-নবীন, সকলপ্রকার ধর্মভাবের কি অদৃষ্টপূর্ব সামঞ্জস্যই না তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি! উপনিষদ্কার ঋষি বলেন, ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ সর্বজ্ঞ ও সত্যসঙ্কল্প হন। সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার ইচ্ছা, বাহ্য জগতের সকল পদার্থ, সকল শক্তি ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লয় ও সেইভাবে পরিবর্তিত হয়। অতএব উক্ত পুরুষের নিজের শরীর-মন যে তদ্রূপ করিবে ইহাতে বিচিত্র কি আছে! উপনিষদ্কারের ঐ বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা করা সাধারণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে – তবে একথা বেশ বলা যাইতে পারে যে, যতদূর পরীক্ষা করা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভব, তাহার বোধ হয় কিছু অভাব বা ত্রুটি, আমরা সকল বিষয়ে অনুক্ষণ যেভাবে ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া লইতাম, তাহাতে হয় নাই। ঠাকুর প্রতিবারই কিন্তু সেসকল পরীক্ষায় হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যেন ব্যঙ্গ করিয়াই আমাদের বলিতেন, “এখনও অবিশ্বাস! বিশ্বাস কর্ – পাকা করে ধর্ – যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সেই ইদানীং (নিজের শরীরটা দেখাইয়া) এ খোলটার ভিতর – তবে এবার গুপ্তভাবে আসা! যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য-পরিদর্শন! যেমনি জানাজানি কানাকানি হয় অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে – সেই রকম!”
ঠাকুরের ভাবকালে দৃষ্ট বিষয়গুলি বাহ্যজগতে সত্য হইতে দেখা
ঠাকুরের জীবনের অনেক ঘটনা উপনিষদুক্ত ঐ বিষয়ে আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দেয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, মানবমনে যতপ্রকার ভাবের উদয় হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে তাহারই ‘স্বসংবেদ্য’ অর্থাৎ ঐসকল ভাবের পরিমাণ, তীব্রতা ইত্যাদি সে নিজেই ঠিক ঠিক জানিতে পারে। অপরে কেবল ভাবের বাহ্যিক বিকাশ দেখিয়া ঐসকলের অনুমানমাত্র করিয়া থাকে। ভাবসমাধির ঐরূপ স্বসংবেদ্য প্রকৃতি (subjective nature) সকলেরই প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত। সকলেই জানে ভাবসকল অন্যান্য চিন্তাসমূহের ন্যায় মানসিক বিকার বা শক্তি-প্রকাশ মাত্র – মনেতেই উহাদের উদয়, মনেতেই লয়; বাহ্যজগতে উহার ছবি বা অনুরূপ প্রতিকৃতি দেখা ও দেখানো অসম্ভব। ঠাকুরের ভাবসমাধির অনেকগুলিতে কিন্তু উহার বৈপরীত্য দেখা যায়।
ঐ দৃষ্টান্ত – পঞ্চবটীর বেড়া ইত্যাদি
ধর – সাধনকালে ঠাকুরের স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটীর চারাগাছগুলি ছাগল-গরুতে মুড়াইয়া খাইয়াছে দেখিয়া ঐ স্থানের চতুর্দিকে ঠাকুরের বেড়া দিবার ইচ্ছা হওয়া এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই গঙ্গায় বান ডাকিয়া ঐ বেড়া-নির্মাণের জন্য আবশ্যকীয় যত কিছু দ্রব্যাদি, কতকগুলি গরানের খুঁটি, বাখারি, নারিকেলদড়ি, মায় একখানি কাটারি পর্যন্ত – সেইস্থানে ভাসিয়া আসিয়া লাগা ও তাঁহার কালীবাটীর ভর্তাভারি নামক মালির সাহায্যে ঐ বেড়া-নির্মাণ! অথবা ধর – রাসমণির জামাতা মথুরানাথের সহিত তর্কে তাঁহার বলা “ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হতে পারে – লাল ফুলের গাছে সাদা ফুলও হতে পারে”, মথুরের তাহা অস্বীকার করা এবং পরদিনই ঠাকুরের বাগানের জবাগাছের একটি ডালের দুটি ফ্যাকড়ায় ঐরূপ দুটি ফুল দেখিতে পাওয়া ও ফুলসুদ্ধ ঐ ডালটি ভাঙিয়া আনিয়া মথুরানাথকে দেওয়া! অথবা ধর – তন্ত্র বেদান্ত বৈষ্ণব ইসলামাদি যখন যে মতের সাধনা করিবারই অভিলাষ ঠাকুরের প্রাণে উদয় হওয়া, তখনি সেই সেই মতের এক একজন সিদ্ধ ব্যক্তির দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁহাকে ঐ ঐ মতে দীক্ষিত করা! অথবা ধর – ঠাকুরের ভক্তদিগকে আহ্বান ও তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রত্যেককে ঠাকুরের চিনিয়া গ্রহণ করা – ঐরূপ অনেক কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনুধাবন করিলে ঐসকল ঘটনায় এইটি দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঠাকুরের মানসিক ভাবের অনেকগুলি সাধারণ মানব-মনের ভাবসকলের ন্যায় কেবলমাত্র মানসিক চিন্তা বা প্রকাশরূপেই পর্যবসিত ছিল না। কিন্তু বাহ্যজগতের অন্তর্গত ঘটনাবলী ঐসকলের দ্বারা আমাদের অপরিজ্ঞাত কি এক নিয়মবশে তদনুরূপভাবে পরিবর্তিত হইত! আমরা এখানে উক্ত সত্যের নির্দেশমাত্র করিয়াই ছাড়িয়া দিলাম। উহা হইতে পাঠকেরা যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি তদ্রূপ আলোচনা ও অনুমানাদি করুন – ঘটনা কিন্তু সত্যই ঐরূপ।
প্রত্যেক ভক্তের সহিত ঠাকুরের বিভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ
পূর্বেই বলিয়াছি, ঠাকুর নির্বিকল্পসমাধি-অবস্থার সময় ভিন্ন অপর সকল সময়ে ‘ভাবমুখে’ থাকিতেন। এইজন্যই দেখা যায় তিনি তাঁহার সমীপাগত প্রত্যেক ভক্তের সহিত এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বরাবর সেই সেই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার হ্লাদিনী ও সন্ধিনী শক্তির বিশেষ বিকাশক্ষেত্রস্বরূপ যত স্ত্রীমূর্তির সহিত ঠাকুরের আজীবন মাতৃ-সম্বন্ধের কথা এখন সাধারণে প্রসিদ্ধ। কিন্তু পুরুষভক্তদিগের প্রত্যেকের সহিত তাঁহার ঐরূপ এক-একটি সম্বন্ধ থাকার কথা বোধ হয় সাধারণে এখনও জ্ঞাত নহে। সেজন্য ঐ সম্বন্ধে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাধারণতঃ ঠাকুর তাঁর ভক্তদিগকে দুই থাকে বা শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতেন – শিবাংশসম্ভূত ও বিষ্ণু-অংশোদ্ভূত। ঐ দুই শ্রেণীর ভক্তদিগের প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার, ভজনানুরাগ প্রভৃতি সকল বিষয়ে পার্থক্য আছে বলিয়া নির্দেশ করিতেন এবং নিজে তাহা সম্যক বুঝিতে পারিতেন – কিন্তু ঐ পার্থক্য যে কি, তাহা বিশেষ করিয়া পাঠককে বুঝানো আমাদের একপ্রকার সাধ্যাতীত।
ভক্তদিগের দুই শ্রেণী
অতএব সংক্ষেপে পাঠক ইহাই বুঝিয়া লউন যে, শিব ও বিষ্ণু-চরিত্র যেন দুইটি আদর্শ ছাঁচ (type or model) এবং ঐ দুই ভিন্ন ছাঁচে যেন ভক্তদিগের প্রত্যেকের মানসিক প্রকৃতি গঠিত – এই পর্যন্ত। ঐসকল ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি সকলপ্রকার ভাবেরই সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল – অবশ্য বিভিন্ন জনের সহিত বিভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল। যথা, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলিতেন, “নরেন্দর যেন আমার শ্বশুরঘর – (আপনাকে দেখাইয়া) এর ভেতর যেটা আছে সেটা যেন মাদি, আর (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) ওর ভেতর যেটা আছে সেটা যেন মদ্দা”; শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ স্বামী বা রাখাল মহারাজকে ঠিক ঠিক নিজ পুত্রস্থানীয় বিবেচনা করিতেন – সন্ন্যাসী ও গৃহী বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগের প্রত্যেকের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ এক-একটা বিশেষ বিশেষ ভাব বা সম্বন্ধ ছিল এবং সাধারণ ভক্তমণ্ডলীর প্রত্যেকের প্রতি ঠাকুরের নারায়ণবুদ্ধি সর্বদা স্থির থাকায় তাহাদের সহিত শান্তভাবের সম্বন্ধ যে তিনি অবলম্বন করিয়া থাকিতেন, একথা বলা বাহুল্য।
ভক্তদিগের প্রকৃতি দেখিয়া ঠাকুরের প্রত্যেকের সহিত ভাব-সম্বন্ধ-পাতান
ভক্তদিগের প্রত্যেকের ভিতরকার প্রকৃতি দেখিয়াই ঠাকুরের তাহাদের সহিত ঐরূপ ভাব বা সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। কারণ ঠাকুর বলিতেন, “মানুষগুলোর ভেতর কি আছে, তা সব দেখতে পাই; যেমন কাচের আলমারির ভেতর যা যা জিনিস থাকে সব দেখা যায়, সেই রকম।” যাহার যেরূপ প্রকৃতি সে তদ্বিপরীতে কখনই আচরণ করিতে পারে না – কাজেই ভক্তদিগের কাহারও ঠাকুরের ঐ সম্বন্ধ বা ভাবের বিপরীতে গমন বা আচরণ কখনো সাধ্যায়ত্ত ছিল না। যদি কখনো কেহ অপর কাহারও দেখাদেখি বিপরীত ভাবের আচরণ করিত তো ঠাকুর তাহাতে বিশেষ বিরক্ত হইতেন ও তাহার ভুল বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। যথা, শ্রীযুত গিরিশকে ঠাকুর ভৈরব বলিতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালিকামাতার মন্দিরে ভাবসমাধিতে তাঁহাকে একদিন ঐরূপ দেখিয়াছিলেন। শ্রীযুত গিরিশের অনেক আবদার ও কঠিন ভাষা তিনি হাসিয়া সহ্য করিতেন – কারণ তাঁহার ঐরূপ ভাষার আবরণে অপূর্ব কোমল একান্ত-নির্ভরতার ভাব যে লুক্কায়িত তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন। গিরিশের দেখাদেখি ঠাকুরের অপর জনৈক প্রিয় ভক্ত একদিন ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করায় ঠাকুর তাহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হন ও পরে তাহার ভুল তাহাকে বুঝাইয়া দেন। যাক এখন সেসব কথা, আমাদের বক্তব্য বিষয়ই বলিয়া যাই।
ঠাকুর ভক্তদিগকে কত প্রকারে ধর্মপথে অগ্রসর করাইতেন
ভাবমুখাবস্থিত ঠাকুর ঐরূপে স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেক ভক্তের নিজ নিজ প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক ভাব সম্যক বুঝিয়া তাহাদের সহিত তত্তদ্ভাবানুযায়ী একটা সপ্রেম সম্বন্ধ সর্বকালের জন্য পাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। তত্তৎ ভাবসম্বন্ধাশ্রয়ে তাহাদের প্রত্যেককে ভগবদ্দর্শনলাভের পথে যে কিরূপে কত প্রকারে অগ্রসর করাইয়া দিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে পাঠককে দিয়া আমরা এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। অদ্বৈতভাবভূমি হইতে নামিয়া আসিয়াই ঠাকুর স্বয়ং সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসোপলব্ধির জন্য সাধনা করিয়া তত্তদ্ভাবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার অনেকদিন পরে যখন ভক্তেরা অনেকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখন একদিন ঠাকুরের ভাবাবস্থায় ইচ্ছা হয় ভক্তদেরও ভাবসমাধি হউক এবং জগদম্বার নিকট ঐ বিষয়ে প্রার্থনা করেন। তাহার পরই ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ঐরূপ হইতে থাকে। ঐরূপ ভাবাবস্থায় তাঁহাদের বাহ্যজগৎ ও দেহাদিবোধ কতকটা কমিয়া যাইয়া ভিতরের কোন একটি বিশেষ ভাবপ্রবাহ, যথা – কোন মূর্তিচিন্তা, এত পরিস্ফুট হইত যে, ঐ মূর্তি যেন জ্বলন্ত জীবন্তরূপে তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন ইত্যাদি তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। ভজন-সঙ্গীতাদি শুনিলেই তাঁহাদের প্রধানতঃ ঐরূপ হইত।
ভক্তদিগের দেবদেবীর মূর্তিদর্শন
ঠাকুরের আর একদল ভক্ত ছিলেন যাঁহাদের সঙ্গীতাদি শুনিলে ওরূপ হইত না, কিন্তু ধ্যানাদি করিবার কালে দেবমূর্ত্যাদির সন্দর্শন হইত। প্রথম প্রথম কেবলমাত্র দর্শনই হইত, পরে ধ্যান যত গাঢ় বা গভীর হইতে থাকিত, তত ঐসকল মূর্তির নড়াচড়া, কথাকওয়া ইত্যাদিও তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। আবার কেহ কেহ প্রথম প্রথম নানাপ্রকার দর্শনাদি করিতেন, কিন্তু ধ্যান আরও গভীরভাবপ্রাপ্ত হইলে আর ঐরূপ দর্শনাদি করিতেন না।
জনৈক ভক্তের বৈকুণ্ঠ-দর্শন
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহাদের প্রত্যেকের দর্শন ও অনুভবাদির কথা শ্রবণ করিয়াই বুঝিতেন, কে কোন্ ‘থাক’ বা শ্রেণীর এবং কাহার পক্ষে কি প্রয়োজন এবং পরেই বা তাঁহারা প্রত্যেকে কি দর্শনাদি করিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে একজনের কথাই বলি। আমাদের একটি বন্ধু1 শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া ধ্যানাদি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথম প্রথম ধ্যানের সময় ইষ্টমূর্তি নানাভাবে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। যেমন যেমন দেখিতেন, কয়েকদিন অন্তর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উহা ঠাকুরকে জানাইতেন। ঠাকুরও শুনিয়া বলিতেন, “বেশ হইয়াছে”, অথবা “এইরূপ করিস” ইত্যাদি। পরে একদিন ঐ বন্ধুটি ধ্যানের সময় দেখিলেন, যতপ্রকার দেবদেবীর মূর্তি একটি মূর্তির অঙ্গে মিলিত হইয়া গেল। ঠাকুরকে ঐকথা নিবেদন করায় ঠাকুর বলিলেন, “যা, তোর বৈকুণ্ঠদর্শন হয়ে গেল। ইহার পর আর দর্শন হবে না।” আমাদের বন্ধু বলেন, “বাস্তবিকই তাহাই হইল – ধ্যান করিতে করিতে কোন মূর্তিই আর দেখিতে পাইতাম না। শ্রীভগবানের সর্বব্যাপিত্বাদি অন্য প্রকারের উচ্চ ভাবসমূহ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। আমার তখন মূর্তিদর্শন করা বেশ লাগিত, যাহাতে আবার ঐরূপ দর্শনাদি হয় তাহার চেষ্টাও খুব করিতাম; কিন্তু করিলে কি হইবে, কিছুতেই আর কোন মূর্তির দর্শন হইত না!”
1. স্বামী অভেদানন্দ।
সাকারবাদীদের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ
সাকারবাদী ভক্তদের বলিতেন, “ধ্যান করবার সময় ভাববে, যেন মনকে রেশমের রশি দিয়ে ইষ্টের পাদপদ্মে বেঁধে রাখচ, যেন সেখান থেকে আর কোথাও যেতে না পারে। রেশমের দড়ি বলছি কেন? – সে পাদপদ্ম যে বড় নরম। অন্য দড়ি দিয়ে বাঁধলে লাগবে তাই।”
রেশমের দড়ি ও ‘জ্যোৎ’ প্রদীপ
আবার বলিতেন, “ধ্যান করবার সময় ইষ্টচিন্তা করে তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাকতে হয়? কতকটা মন সেইদিকে সর্বদা রাখবে। দেখেচ তো, দুর্গাপূজার সময় একটা যাগ-প্রদীপ জ্বালতে হয়। ঠাকুরের কাছে সর্বদা একটা জ্যোৎ (জ্যোতিঃ) রাখতে হয়, সেটাকে নিবতে দিতে নেই। নিবলে গেরস্তর অকল্যাণ হয়। সেইরকম হৃদয়পদ্মে ইষ্টকে এনে বসিয়ে তাঁর চিন্তারূপ যাগ-প্রদীপ সর্বদা জ্বেলে রাখতে হয়। সংসারের কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে ভেতরে চেয়ে দেখতে হয়, সে প্রদীপটা জ্বলচে কিনা।”
ধ্যান করবার আগে মনটা ধুয়ে ফেলা
আবার বলিতেন, “ওগো, তখন তখন ইষ্টচিন্তা করবার আগে ভাবতুম, যেন মনের ভেতরটা বেশ করে ধুয়ে দিচ্ছি! মনের ভেতর নানান আবর্জনা, ময়লা-মাটি (চিন্তা, বাসনা ইত্যাদি) থাকে কিনা? সেগুলো সব বেশ করে ধুয়ে ধেয়ে সাফ্ করে তার ভেতর ইষ্টকে এনে বসাচ্চি! – এই রকম করো!” ইত্যাদি।
সাকার বড় না নিরাকার বড়
শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক সময়ে শ্রীভগবানের সাকার ও নিরাকারভাবচিন্তা-সম্বন্ধে আমাদের বলেন, “কেহ বা সাকার দিয়ে নিরাকারে পৌঁছায়, আবার কেহ বা নিরাকার দিয়ে সাকারে পৌঁছায়।” ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে বসিয়া একদিন আমাদের এক বন্ধু1 ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন – ‘মহাশয়, সাকার বড় না নিরাকার বড়?’ তাহাতে ঠাকুর বলেন, “নিরাকার দু-রকম আছে, পাকা ও কাঁচা। পাকা নিরাকার উঁচু ভাব বটে; সাকার ধরে সে নিরাকারে পৌঁছুতে হয়। কাঁচা নিরাকারে চোখ বুজলেই অন্ধকার – যেমন ব্রাহ্মদের2।”
1. শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বসু।
2. সত্যের অনুরোধে এ কথাটি আমরা বলিলাম বলিয়া কেহ না মনে করেন, ঠাকুর বর্তমান ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মজ্ঞানীদের নিন্দা করিতেন। কীর্তনান্তে যখন সকল সম্প্রদায়ের সকল ভক্তদের প্রণাম করিতেন, তখন ‘আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম’ – এ কথাটি তাঁহাকে বার বার আমরা বলিতে শুনিয়াছি। সুবিখ্যাত ব্রাহ্মসমাজের নেতা ভক্তপ্রবর কেশবই সর্বপ্রথম ঠাকুরের কথা কলিকাতার জনসাধারণে প্রচার করেন, একথা সকলেই জানেন এবং ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের মধ্যে শ্রীবিবেকানন্দ-প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মসমাজের নিকট চিরঋণী, একথাও তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।
সাকার ও নিরাকারের সামঞ্জস্য
পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে ঐরূপ কাঁচা নিরাকার ধরিয়া সাধনায় অগ্রসর ঠাকুরের আর একদল ভক্তও ছিলেন। তাঁহাদের ঠাকুর ক্রীশ্চান পাদ্রীদের মতো সাকারভাব চিন্তার নিন্দা অথবা শ্রীভগবানের সাকারমূর্ত্যাদি-অবলম্বনে সাধনায় অগ্রসর ভক্তদিগকে ‘পৌত্তলিক’, ‘অন্ধবিশ্বাসী’ ইত্যাদি বলিয়া দ্বেষ করিতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন, “ওরে, তিনি সাকারও বটে আবার নিরাকারও বটে, আবার তা ছাড়া আরও কি তা কে জানে? সাকার কেমন জানিস – যেমন জল আর বরফ। জল জমেই বরফ হয়; বরফের ভিতরে বাহিরে জল। জল ছাড়া বরফ আর কিছুই নয়। কিন্তু দ্যাখ, জলের রূপ নেই (একটা কোন বিশেষ আকার নাই), কিন্তু বরফের আকার আছে। তেমনি ভক্তিহিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরের জল জমে বরফের মতো নানা আকার ধারণ করে।” ঠাকুরের ঐ দৃষ্টান্তটি যে কত লোকের মনে শ্রীভগবানের সাকার নিরাকার উভয় ভাবের একত্রে এক সময়ে সমাবেশ সম্ভবপর বলিয়া ধারণা করাইয়া শান্তি দিয়াছে, তাহা বলিবার নহে।
স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্ধবিশ্বাস
এখানে আর একটি কথাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঠাকুরের কাঁচা নিরাকারবাদী ভক্তদলের ভিতর সর্বপ্রধান ছিলেন – শুধু ঐ দলের কেন ঠাকুর তাঁহাকে সকল থাক্ বা শ্রেণীর সকল ভক্তদিগের অগ্রে আসন প্রদান করিতেন – শ্রীযুত নরেন্দ্র বা স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার তখন পাশ্চাত্যশিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে সাকারবাদীদের উপর একটু-আধটু কঠিন কটাক্ষ কখনো কখনো আসিয়া পড়িত। তর্কের সময়েই ঐ ভাবটি তাঁহাতে বিশেষ লক্ষিত হইত। ঠাকুর কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত সাকারবাদী কোন কোন ভক্তের ঘোরতর তর্ক বাধাইয়া দিয়া মজা দেখিতেন। ঐরূপ তর্কে স্বামীজীর মুখের সামনে বড় একটা কেহ দাঁড়াইতে পারিতেন না এবং স্বামীজীর তীক্ষ্ণ যুক্তির সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া কেহ কেহ মনে মনে ক্ষুণ্ণও হইতেন। ঠাকুরও সে কথা অপরের নিকট অনেক সময় আনন্দের সহিত বলিতেন, “অমুকের কথাগুলো নরেন্দর সে দিন ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে কেটে দিলে! – কি বুদ্ধি!” ইত্যাদি। সাকারবাদী গিরিশের সহিত তর্কে কিন্তু স্বামীজীকে একদিন নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। সেদিন ঠাকুর শ্রীযুত গিরিশের বিশ্বাস আরও দৃঢ় ও পুষ্ট করিবার জন্যই যেন তাঁহার পক্ষে ছিলেন বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছিল! সে যাহা হউক, স্বামী বিবেকানন্দ একদিন শ্রীভগবানে বিশ্বাস সম্বন্ধে কথার সময় ঠাকুরের নিকট সাকারবাদীদের বিশ্বাসকে ‘অন্ধবিশ্বাস’ বলিয়া নির্দেশ করেন। ঠাকুর তদুত্তরে তাঁহাকে বলেন, “আচ্ছা, অন্ধবিশ্বাসটা কাকে বলিস আমায় বোঝাতে পারিস? বিশ্বাসের তো সবটাই অন্ধ; বিশ্বাসের আবার চক্ষু কি? হয় বল ‘বিশ্বাস’, আর নয় বল ‘জ্ঞান’। তা নয়, বিশ্বাসের ভেতর আবার কতকগুলো অন্ধ আর কতকগুলোর চোখ আছে – এ আবার কি রকম?” স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, “বাস্তবিকই সেদিন আমি ঠাকুরকে অন্ধবিশ্বাসের অর্থ বুঝাইতে যাইয়া ফাঁপরে পড়িয়াছিলাম। ও কথাটার কোন অর্থই খুঁজিয়া পাই নাই। ঠাকুরের কথাই ঠিক বলিয়া বুঝিয়া সেদিন হইতে আর ও কথাটা বলা ছাড়িয়া দিয়াছি।”
নিরাকারবাদীদের প্রতি উপদেশ
কাঁচা নিরাকারবাদীদেরও ঠাকুর সাকারবাদীদের সহিত সমান চক্ষে দেখিতেন। তাহাদেরও কিরূপভাবে ধ্যান করিলে সহায়ক হইবে বলিয়া দিতেন। বলিতেন, “দ্যাখ্, আমি তখন তখন ভাবতুম, ভগবান যেন সমুদ্রের জলের মতো সব জায়গা পূর্ণ করে রয়েছেন, আর আমি যেন একটি মাছ – সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবছি, ভাসছি, সাঁতার দিচ্ছি! আবার কখনো মনে হতো আমি যেন একটি কুম্ভ, সেই জলে ডুবে রয়েছি, আর আমার ভিতরে বাহিরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হয়ে রয়েছেন।”
ঠাকুরের নিজমূর্তি ধ্যান করিতে উপদেশ
আবার বলিতেন, “দ্যাখ্, ধ্যান করতে বসবার আগে একবার (আপনাকে দেখাইয়া) একে ভেবে নিবি। কেন বলছি? – এখানকার ওপর তোদের বিশ্বাস আছে কি না? একে ভাবলেই তাঁকে (ভগবানকে) মনে পড়ে যাবে। ঐ যে গো, যেমন গরুর পাল দেখলেই রাখালকে মনে পড়ে, ছেলেকে দেখলেই তার বাপের কথা মনে পড়ে, উকিল দেখলেই কাছারির কথা মনে পড়ে, সেই রকম – বুঝলে কি না? মন নানান জায়গায় ছড়িয়ে থাকে কি না, একে ভাবলেই মনটা এক জায়গায় গুটিয়ে আসবে, আর সেই মনে ঈশ্বরকে চিন্তা করলে তাতে ঠিক ঠিক ধ্যান লাগবে – এইজন্যে বলছি।”
‘কাঁচা আমি ও পাকা আমি’; একটা ভাব পাকা ক’রে ধরলে তবে ঈশ্বরের উপর জোর চলে
আবার বলিতেন, “যাঁকে ভাল লাগে, যে ভাব ভাল লাগে, একজনকে বা একটাকে পাকা করে ধর তবে তো আঁট হবে। ‘সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে?’ – ভাব চাই। একটা ভাব নিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। ‘যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়। ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।’ – ভাব চাই, বিশ্বাস চাই, পাকা করে ধরা চাই – তবে তো হবে। তবে কি জান? তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে একটু সম্বন্ধ পাতানো – এরই নাম। সেইটে সর্বক্ষণ মনে রাখা, যেমন – তাঁর দাস আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি; এই হচ্ছে পাকা আমি, বিদ্যার আমি – এইটি খেতে শুতে বসতে সব সময় স্মরণ রাখা! আর এই যে বামুন আমি, কায়েৎ আমি, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি – এসব হচ্চে অবিদ্যার আমি; এগুলোকে ছাড়তে হয়, ত্যাগ করতে হয় – ওগুলোতে অভিমান-অহঙ্কার বাড়িয়ে বন্ধন এনে দেয়। স্মরণ-মননটা সর্বদা রাখা চাই, খানিকটে মন সব সময় তাঁর দিকে ফিরিয়ে রাখবে – তবে তো হবে। একটা ভাব পাকা করে ধরে তাঁকে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো তাঁর উপর জোর চলবে। এই দ্যাখ না, প্রথম প্রথম একটু-আধটু ভাব যতক্ষণ, ততক্ষণ ‘আপনি, মশাই’ ইত্যাদি লোকে বলে থাকে; সেই ভাব যেই বাড়ল, অমনি ‘তুমি তুমি’ – আর তখন ‘আপনি টাপনি’-গুলো বলা আসে না; যেই আরও বাড়লো, আর তখন ‘তুমি টুমি’-তেও মানে না – তখন ‘তুই মুই’! তাঁকে আপনার হতে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো হবে।”
নষ্ট মেয়ের দৃষ্টান্ত
“যেমন নষ্ট মেয়ে, পরপুরুষকে প্রথম প্রথম ভালবাসতে শিখচে – তখন কত লুকোলুকি, কত ভয়, কত লজ্জা, তারপর যেই ভাব বেড়ে উঠল, তখন আর কিছু নেই! একেবারে তার হাত ধরে সকলের সামনে কুলের বাইরে এসে দাঁড়াল! তখন যদি সে পুরুষটা তাকে আদর-যত্ন না করে, ছেড়ে যেতে চায়, তো তার গলায় কাপড় দিয়ে টেনে ধরে বলে ‘তোর জন্যে পথে দাঁড়ালুম, এখন তুই খেতে দিবি কি না বল।’ সেই রকম, যে ভগবানের জন্য সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েচে সে তাঁর ওপর জোর করে বলে, ‘তোর জন্যে সব ছাড়লুম, এখন দেখা দিবি কিনা – বল’!”
এজন্মে ঈশ্বরলাভ করবো – মনে এই জোর রাখা চাই
কাহারও ভগবদনুরাগে জোর কমিয়াছে দেখিলে বলিতেন, “এ জন্মে না হোক পরজন্মে পাব, ও কি কথা? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নেই। তাঁর কৃপায় তাঁকে এ জন্মেই পাব, এখনি পাব – মনে এইরকম জোর রাখতে হয়, বিশ্বাস রাখতে হয়, তা না হলে কি হয়? ওদেশে চাষীরা সব গরু কিনতে গিয়ে গরুর ল্যাজে আগে হাত দেয়। কতকগুলো গরু আছে ল্যাজে হাত দিলে কিছু বলে না, গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে – অমনি তারা বোঝে সেগুলো ভাল নয়। আর যেগুলোর ল্যাজে হাত দেবামাত্র তিড়িং মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে – অমনি বোঝে এইগুলো খুব কাজ দেবে – ঐগুলোর ভিতর থেকে পছন্দ করে কেনে। ম্যাদাটে ভাব ভাল নয়; জোর নিয়ে এসে, বিশ্বাস করে বল – তাঁকে পাবই পাব, এখনি পাব – তবে তো হবে।”
এক এক ক’রে বাসনাত্যাগ করা চাই
“কোথা ওগুলোকে সব এক এক করে ছাড়বে – না আরও বাড়াতে চললে! – তাহলে কেমন করে হবে?”
চার ক’রে মাছ ধরার মত অধ্যবসায় চাই
যখন ধ্যান-ভজন, প্রার্থনাদি করিয়া শ্রীভগবানের সাড়া না পাইয়া মন নিরাশার সাগরে ভাসিত, তখন সাকার নিরাকার উভয় বাদীদেরই বলিতেন, “মাছ ধরতে গেলে প্রথম চার করতে হয়। হয়তো চার করে ছিপ ফেলে বসেই আছে – মাছের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্চে তবে বুঝি পুকুরে মাছ নেই। তারপর হয়তো একদিন দেখলে একটা বড় মাছ ঘাই দিলে – অমনি বিশ্বাস হলো পুকুরে মাছ আছে। তারপর হয়তো একদিন ছিপের ফাতনাটা নড়ল – অমনি মনে হলো চারে মাছ এয়েছে। তারপর হয়তো একদিন ফাতনাটা ডুবল, তুলে দেখলে – মাছ টোপ খেয়ে পালিয়েছে; আবার টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে খুব সাবধানে বসে রইল। তারপর একদিন যেমন টোপ খেয়েছে, অমনি টেনে তুলতেই মাছ আড়ায় উঠল।”
ভগবান ‘কানখড়্কে’ – সব শুনেন
কখনও বলিতেন, “তিনি খুব কানখড়্কে, সব শুনতে পান গো। যত ডেকেছ সব শুনেছেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই দেবেন। অন্ততঃ মৃত্যুসময়েও দেখা দেবেন।” কাহাকেও বলিতেন – “সাকার কি নিরাকার যদি ঠিক করতে না পারিস তো এই বলে প্রার্থনা করিস যে, ‘হে ভগবান, তুমি সাকার কি নিরাকার আমি বুঝতে পারি না; তুমি যাহাই হও আমায় কৃপা কর, দেখা দাও’।” আবার কাহাকেও বলিতেন – “সত্য সত্যই ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যায় রে, এই যেমন তোতে আমাতে এখন বসে কথা কইচি এইরকম করে তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কহা যায় – সত্য বলছি, মাইরি বলছি!”
গভীর ভাব-প্রবণতার সহিত ঠাকুরের সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা
আর এক কথা – চব্বিশ ঘণ্টা ‘ভাবমুখে’ থাকিলে ভাবুকতার এত বৃদ্ধি হয় যে, তাহার দ্বারা আর সংসারের অপর কোন কর্ম চলে না, অথবা সে সংসারের ছোটখাট ব্যাপার আর মনে রাখিতে পারে না – সর্বত্র আমরা এইরূপই দেখিতে পাই। উহার দৃষ্টান্ত – ধর্ম-জগতে তো কথাই নাই, বিজ্ঞান, রাজনীতি বা অন্য সকল স্থানেও বিশেষ মনস্বী পুরুষগণের জীবনালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, তাঁহারা হয়তো নিজের অঙ্গসংস্কার বা নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের যথাযথ স্থানে রাখা ইত্যাদি সামান্য বিষয়সকলে একেবারেই অপটু ছিলেন। ঠাকুরের জীবনে কিন্তু দেখিতে পাই যে, অত অধিক ভাবপ্রবণতার ভিতরেও তাঁহার ঐপ্রকার সামান্য বিষয়সকলেরও হুঁশ থাকিত। যখন থাকিত না তখন নিজের দেহ বা জগৎ-সংসারের কোন বস্তু বা ব্যক্তিরই হুঁশ থাকিত না – যেমন সমাধিতে, আর যখন থাকিত, তখন সকল বিষয়েরই থাকিত! ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় নহে! এখানে দুই-একটি মাত্র ঐরূপ দৃষ্টান্তেরই আমরা উল্লেখ করিব।
ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত
একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হইতে বলরামবাবুর বাটী গমন করিতেছেন; সঙ্গে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল ও শ্রীযুত যোগানন্দ স্বামী যাইতেছেন। সকলে গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি ছাড়িয়া বাগানের ‘গেট’ পর্যন্ত আসিয়াছে মাত্র, ঠাকুর শ্রীযুত যোগানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন – “কিরে, নাইবার কাপড় গামছা এনেছিস তো?” – তখন প্রাতঃকাল।
শ্রীযুত যোগেন – না মশাই, গামছা এনেছি, কাপড়খানা আনতে ভুল হয়েছে। তা তারা (বলরামবাবু) আপনার জন্য একখানা নূতন কাপড় দেখে-শুনে দেবে এখন।
ঠাকুর – ও কি তোর কথা? লোকে বলবে, কোথা থেকে একটা হাবাতে এসেছে। তাদের কষ্ট হবে, আতান্তরে পড়বে – যা, গাড়ি থামিয়ে নেবে গিয়ে নিয়ে আয়।
কাজেই যোগীন স্বামীজী তদ্রূপ করিলেন।
ঠাকুর বলিতেন – ভাল লোক, লক্ষ্মীমন্ত লোক বাড়িতে এলে সকল বিষয়ে কেমন সুসার হয়ে যায়, কাকেও কিছুতে বেগ পেতে হয় না। আর হাবাতে হতচ্ছাড়াগুলো এলে সকল বিষয়ে বেগ পেতে হয়; যে দিন ঘরে কিছু নেই, তার জন্য গেরস্তকে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে, ঠিক সেই দিনেই সে এসে উপস্থিত হয়।
ঐ বিষয়ে ২য় দৃষ্টান্ত
শ্রীযুত প্রতাপ হাজরা নামক এক ব্যক্তি ঠাকুরের সময়ে দক্ষিণেশ্বরে অনেককাল সাধুভাবে কাটাইতেন। আমরা সকলে ইঁহাকে হাজরা মহাশয় বলিয়া ডাকিতাম। ইনিও মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের কলিকাতার ভক্তদিগের নিকট আগমনকালে তাঁহার সঙ্গে আসিতেন। একবার ঐরূপে আসিয়া প্রত্যাগমনকালে নিজের গামছাখানি ভুলিয়া কলিকাতায় ফেলিয়া যান। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ঐ কথা জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন – “ভগবানের নামে আমার পরনের কাপড়ের হুঁশ থাকে না, কিন্তু আমি তো একদিনও নিজের গামছা বা বেটুয়া কলিকাতায় ভুলিয়া আসি না। আর তোর একটু জপ করে এত ভুল!”
ঐ বিষয়ে ৩য় দৃষ্টান্ত – শ্রীশ্রীমার প্রতি উপদেশ
শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর শিখাইয়াছিলেন – “গাড়িতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোন জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কিনা দেখে শুনে সকলের শেষে নামবে।” ঠাকুরের অতি সামান্য বিষয়েও এত নজর ছিল।
ঐ বিষয়ে শেষ কথা
এইরূপে ‘ভাবমুখে’ নিরন্তর থাকিয়াও ঠাকুরের আবশ্যকীয় সকল বিষয়ের হুঁশ থাকিত; যে জিনিসটি যেখানে রাখিতেন তাহা সর্বদা সেইখানেই রাখিতেন, নিজের কাপড়-চোপড়, বেটুয়া প্রভৃতি সকল নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের নিজে খোঁজ রাখিতেন, কোথাও যাইবার আসিবার সময় আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যাদি আনিতে ভুল হইয়াছে কিনা সন্ধান লইতেন এবং ভক্তদিগের মানসিক ভাবসমূহের যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান রাখিতেন, তেমনি তাহাদের সংসারের সকল বিষয়ের সন্ধান রাখিয়া কিসে তাহাদের বাহ্যিক সকল বিষয়ও সাধনার অনুকূল হইতে পারে তদ্বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা করিতেন!
ঠাকুর ভাবরাজ্যের মূর্তিমান রাজা
ঠাকুরের কথা অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, তিনি যেন সর্বপ্রকার ভাবের মূর্তিমান সমষ্টি ছিলেন। ভাবরাজ্যের অত বড় রাজা মানবজগতে আর কখনো দেখা যায় নাই। ভাবময় ঠাকুর ‘ভাবমুখে’ অবস্থান করিয়া নির্বিকল্প অদ্বৈতভাব হইতে সবিকল্প সকল প্রকার ভাবের পূর্ণ প্রকাশ নিজে দেখাইয়া সকল শ্রেণীর ভক্তদিগকে স্ব স্ব পথের ও গন্তব্যস্থলের সংবাদ দিয়া অন্ধকারে অপূর্ব জ্যোতি, নিরাশায় অদৃষ্টপূর্ব আশা এবং সংসারের নিদারুণ দুঃখকষ্টের ভিতর নিরুপম শান্তি আনিয়া দিতেন। ঠাকুর যে সকলের কি ভরসার স্থল ছিলেন তাহা বলিয়া বুঝানো দায়। মনোরাজ্যে তাঁহার যে কি প্রবল প্রতাপ দেখিয়াছি তাহা বলা অসম্ভব।
মানব-মনের উপর তাঁহার অপূর্ব আধিপত্য – স্বামী বিবেকানন্দের ঐ বিষয়ক কথা
স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন – “মনের বাহিরের জড়-শক্তিসকলকে কোন উপায়ে আয়ত্ত করে কোন একটা অদ্ভুত ব্যাপার (miracle) দেখানো বড় বেশি কথা নয় – কিন্তু এই যে পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মতো হাতে নিয়ে ভাঙত, পিট্ত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতন ভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার (miracle) আমি আর কিছুই দেখি না!”
তৃতীয় খণ্ড – তৃতীয় অধ্যায়: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব
ঠাকুর, ‘গুরু’ ‘বাবা’ বা ‘কর্তা’ বলিয়া সম্বোধিত হইলে বিরক্ত হইতেন। তবে গুরুভাব তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে
আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥
– গীতা, ২।২৯
ঠাকুরকে যাঁহারা দু-চারবার মাত্র দেখিয়াছেন অথবা যাঁহারা তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন নাই, উপর উপর দেখিয়াছেন মাত্র, তাঁহারা গুরুভাবে ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের লীলার কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাইলে একেবারে অবাক হইয়া থাকেন। ভাবেন, ‘লোকটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাগুলো বলছে।’ আবার যখন দেখেন অনেকে ঐ ভাবের কথা বলিতেছে তখনো মনে করেন, “এরা সব একটা মতলব করে দল পাকিয়েচে, আর শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠাকুর করে তুলচে; তিনশ তেত্রিশ কোটির ওপর আবার একটা বাড়াতে চলেচে! কেন রে বাপু, অতগুলো ঠাকুরেও কি তোদের শানে না? যাকে ইচ্ছা, যতগুলো ইচ্ছা, ওরি ভেতর থেকে নে না – আবার একটা বাড়ানো কেন? কি আশ্চর্য এরা একবার ভাবেও না গা যে, মিথ্যা কথাগুলো ধরা পড়লে অমন পবিত্র লোকটার উপরে লোকের ভক্তি একেবারে চটে যাবে! আমরাও তো তাঁকে দেখেচি! – সকলের কাছে নিচু, নম্রভাব – একেবারে যেন মাটি, যেন সকলের চাইতে ছোট – এতটুকু অহঙ্কার নাই! তারপর একথা তো তোরাও বলিস, আর আমরাও দেখেচি যে, ‘গুরু’ কি ‘বাবা’ কি ‘কর্তা’ বলে তাঁকে কেউ ডাকলে তিনি একেবারে সইতেই পারতেন না; বলে উঠতেন, ‘ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্তা – আমি হীনের হীন, দাসের দাস, তোমার গায়ের একগাছি ছোট রোমের সমান – একগাছি বড়র সমানও নই!’ – বলেই হয়তো আবার তার পায়ের ধুলো তুলে নিজের মাথায় দিতেন! এমন দীনভাব কোথাও কেউ কি দেখেচে? আর সেই লোককে কিনা এরা ‘গুরু’, ‘ঠাকুর’ – যা নয় তাই বলচে, যা নয় তাই করচে!”
সর্বভূতে নারায়ণ-বুদ্ধি স্থির থাকায় ঠাকুরের দাসভাব সাধারণ
এইরূপ অনেক বাদানুবাদ চলা অসম্ভব নহে বলিয়াই আমরা ঠাকুরের গুরুভাব-সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহার কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ বাস্তবিকই ঠাকুর যখন সাধারণভাবে থাকিতেন, তখন আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সর্বভূতে ঠিক ঠিক নারায়ণ-বুদ্ধি স্থির রাখিয়া মানুষের তো কথাই নাই, সকল প্রাণীরই ‘দাস আমি’ এই ভাব লইয়া থাকিতেন; বাস্তবিকই তখন তিনি আপনাকে হীনের হীন, দীনের দীন জ্ঞানে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতেন; এবং বাস্তবিকই সে সময় তিনি ‘গুরু’, ‘কর্তা’ বা ‘পিতা’ বলিয়া সম্বোধিত হইলে সহিতে পারিতেন না।
কিন্তু দিব্য-ভাবাবেশে তাঁহাতে গুরুভাবের লীলা নিত্য দেখা যাইত। ঠাকুরের তখনকার ব্যবহারে ভক্তদিগের কি মনে হইত
কিন্তু সাধারণ ভাবে অবস্থানের সময় ঐরূপ করিলেও ঠাকুরের গুরুভাবের অপূর্ব লীলার কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করি? সে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যভাবাবেশে যখন তিনি যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কাহাকেও স্পর্শমাত্রেই সমাধি, গভীর ধ্যান বা ভগবদানন্দের অভূতপূর্ব নেশার ঝোঁকে1 নিমগ্ন করিতেন, অথবা কি এক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহার মনের তমোগুণ বা মলিনতা এতটা টানিয়া লইতেন যে, সে তৎক্ষণাৎ পূর্বে যেরূপ কখনো অনুভব করে নাই, এ প্রকার একটা মনের একাগ্রতা, পবিত্রতা ও আনন্দ লাভ করিত এবং আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া ঠাকুরের চরণতলে চিরকালের নিমিত্ত আত্মবিক্রয় করিত – তখন তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত এ ঠাকুর পূর্বের সেই দীনের দীন ঠাকুর নহেন; ইঁহাতে কি একটা ঐশ্বরিক শক্তি স্বেচ্ছায় বা লীলায় প্রকটিত হইয়া ইঁহাকে আত্মহারা করিয়া ঐরূপ করাইতেছে; ইনি বাস্তবিকই অজ্ঞানতিমিরান্ধ, ত্রিতাপে তাপিত, ভবরোগগ্রস্ত অসহায় মানবের গুরু, ত্রাতা এবং শ্রীভগবানের পরম পদের দর্শয়িতা! ভক্তেরা ঠাকুরের ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গুরু, কৃপাময়, ভগবান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও যথার্থ দীনভাব এবং এই দিব্য ঐশ্বরিক গুরুভাব যে একত্রে একজনে অবস্থান করিতে পারে, তাহা আমরা বর্তমান যুগে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণে যথার্থই দেখিয়াছি; এবং দেখিয়াছি বলিয়াই উহারা কেমনে একত্রে একই মনে থাকে সে বিষয়ে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিতে চেষ্টা করিতেছি।
1. বাস্তবিকই তখন অধিক পরিমাণে সিদ্ধি খাইলে যেমন নেশা হয়, তেমনি একটা নেশার ঘোর উপস্থিত হইত। কাহারও কাহারও পা-ও টলিতে দেখিয়াছি। ঠাকুরের নিজের তো কথাই ছিল না। ঐরূপ নেশার ঝোঁকে পা এমন টলিত যে, আমাদের কাহাকেও ধরিয়া তখন চলিতে হইত। লোকে মনে করিত, বিপরীত নেশা করিয়াছেন।
ভাবময় ঠাকুরের ভাবের ইতি নাই
ঐরূপ চেষ্টা করিলেও যতটুকু বুঝিয়াছি ততটুকুও ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারিব কিনা জানি না; আর সম্যক বুঝা বা বুঝানো, লেখক ও পাঠক উভয়েরই সাধ্যাতীত; কারণ ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের ভাবের ইয়ত্তা নাই। ঠাকুর বলিতেন, “শ্রীভগবানের ‘ইতি’ নাই।” আমাদের প্রত্যক্ষ এ লোকোত্তর পুরুষেরও তদ্রূপ ভাবের ‘ইতি’ নাই।
সাধারণের বিশ্বাস ঠাকুর ভক্ত ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন না। ‘ভাবমুখে থাকা’ কখন ও কিরূপে সম্ভবে বুঝিলে ঐকথা আর বলা চলে না
সচরাচর লোকে ঠাকুর ‘ভাবমুখে’ থাকিতেন শুনিলেই ভাবিয়া বসে যে, তিনি জ্ঞানী ছিলেন না। ভগবদনুরাগ ও বিরহে মনে যে সুখদুঃখাদি ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই লইয়া সদা সর্বক্ষণ থাকিতেন। কিন্তু ‘ভাবমুখে’ থাকাটি যে কি ব্যাপার বা কিরূপ অবস্থায় উহা সম্ভব, তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি তবে বর্তমান বিষয়টি বুঝিতে পারিব; সেজন্য ‘ভাবমুখে থাকা’ অবস্থাটির সংক্ষেপ আলোচনা এখানে একবার আর এক প্রকারে করিয়া লওয়া যাক। পাঠক মনে মনে ভাবিয়া লউন – তিনদিনের সাধনে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি হইল।
প্র – নির্বিকল্প সমাধিটি কি?
উ – মনকে একেবারে সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত অবস্থায় আনয়ন করা।
প্র – সঙ্কল্প-বিকল্প কাহাকে বলে?
উ – বাহ্য জগতের রূপরসাদি বিষয়সকলের জ্ঞান বা অনুভব, সুখদুঃখাদি ভাব, কল্পনা, বিচার, অনুমান প্রভৃতি মানসিক চেষ্টা এবং ইচ্ছা বা ‘এটা করিব’, ‘ওটা বুঝিব’, ‘এটা ভোগ করিব’, ‘ওটা ত্যাগ করিব’ ইত্যাদি মনের সমস্ত বৃত্তিকে।
‘আমি’-বোধাশ্রয়ে মানসিক বৃত্তিসমূহের উদয়। উহার আংশিক লোপে সবিকল্প ও পূর্ণ লোপে নির্বিকল্প সমাধি হয়। সমাধি, মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তির প্রভেদ
প্র – বৃত্তিসকল কোন্ জিনিসটা থাকিলে তবে উঠিতে পারে?
উ – ‘আমি’ ‘আমি’ এই জ্ঞান বা বোধ। ‘আমি’-বোধ যদি চলিয়া যায় বা কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তবে সে সময়ের মতো কোন বৃত্তিই আর মনে খেলা বা রাজত্ব করিতে পারে না।
প্র – মূর্ছা বা গভীর নিদ্রাকালেও তো ‘আমি’-বোধ থাকে না – তবে কি নির্বিকল্প সমাধিটা ঐরূপ একটা কিছু?
উ – না; মূর্ছা বা সুষুপ্তিতে ‘আমি’-বোধ ভিতরে ভিতরে থাকে, তবে মস্তিষ্করূপ (brain) যে যন্ত্রটার সহায়ে মন ‘আমি’ ‘আমি’ করে সেটা কিছুক্ষণের জন্য কতকটা জড়ভাবাপন্ন হয় বা চুপ করিয়া থাকে, এই মাত্র – ভিতরে বৃত্তিসমূহ গজগজ করিতে থাকে – ঠাকুর যেমন দৃষ্টান্ত দিতেন, “পায়রাগুলো মটর খেয়ে গলা ফুলিয়ে বসে আছে বা বক-বকম্ করে আওয়াজ করছে – তুমি মনে করচ তাদের গলার ভিতরে কিছুই নাই – কিন্তু যদি গলায় হাত দিয়ে দেখ তো দেখবে মটর গজগজ করচে!”
প্র – মূর্ছা বা সুষুপ্তিতে যে ‘আমি’-বোধটা ঐরূপে থাকে তা বুঝিব কিরূপে?
উ – ফল দেখিয়া; যথা – ঐসকল সময়েও হৃদয়ের স্পন্দন, হাতের নাড়ি, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি বন্ধ হয় না – ঐসকল শারীরিক ক্রিয়াও ‘আমি’-বোধটাকে আশ্রয় করিয়া হয়; দ্বিতীয় কথা, মূর্ছা ও সুষুপ্তির বাহ্যিক লক্ষণ কতকটা সমাধির মতো হইলেও ঐসকল অবস্থা হইতে মানুষ যখন আবার সাধারণ বা জাগ্রত অবস্থায় আসে, তখন তাহার মনে জ্ঞান ও আনন্দের মাত্রা পূর্বের ন্যায়ই থাকে, কিছুমাত্র বাড়ে বা কমে না – কামুকের যেমন কাম তেমনি থাকে, ক্রোধীর যেমন ক্রোধ তেমনি থাকে, লোভীর লোভ সমান থাকে ইত্যাদি।
সমাধি ফল – জ্ঞান ও আনন্দের বৃদ্ধি এবং ভগবদ্দর্শন
নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা লাভ হইলে কিন্তু ঐসকল বৃত্তি আর মাথা তুলিতে পারে না; অপূর্ব জ্ঞান ও অসীম আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জগৎকারণ ভগবানের সাক্ষাৎদর্শনে মনে আর পরকাল আছে কিনা, ভগবান আছেন কিনা – এ সকল সংশয়-সন্দেহ উঠে না।
প্র – আচ্ছা বুঝিলাম – ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিতে কিছুক্ষণের জন্য ‘আমি’-বোধের একেবারে লয় হইল – তাহার পর?
উ – তাহার পর, ঐরূপে ‘আমি’-বোধটার লোপ হইয়া কারণরূপিণী শ্রীশ্রীজগন্মাতার কিছুক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ দর্শনে ঠাকুর তৃপ্ত না হইয়া সদা-সর্বক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।
ঠাকুরের ছয় মাস নির্বিকল্প সমাধিতে থাকিবার কালের দর্শন ও অনুভব
প্র – সে চেষ্টার ফলে ঠাকুরের মনের কিরূপ অবস্থা হইল এবং কিরূপ লক্ষণই বা শরীরে প্রকাশিত হইল?
উ – কখনও ‘আমি’-বোধের লোপ হইয়া শরীরে মৃতব্যক্তির লক্ষণসকল প্রকাশিত হইয়া ভিতরে জগদম্বার পূর্ণ বাধামাত্রশূন্য সাক্ষাৎ দর্শন – আবার কখনও অত্যল্পমাত্র ‘আমি’-বোধ উদিত হইয়া শরীরে জীবিতের লক্ষণ একটু-আধটু প্রকাশ পাওয়া ও সত্ত্বগুণের অতিশয় আধিক্যে শুদ্ধ স্বচ্ছ পবিত্র মন-রূপ ব্যবধান বা পর্দার ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার কিঞ্চিৎ বাধাযুক্ত দর্শন! – এইরূপে কখনও ‘আমি’-বোধের লোপ, মনের বৃত্তিসকলের একেবারে লয় ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণ দর্শন ও কখনও ‘আমি’-বোধের একটু উদয়; মনের বৃত্তিসকলের ঈষৎ প্রকাশ ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন ঈষৎ আবরিত হওয়া। এইরূপ বার বার হইতে লাগিল।
প্র – কতদিন ধরিয়া ঠাকুর ঐরূপ চেষ্টা করেন?
উ – নিরন্তর ছয়মাস কাল ধরিয়া।
‘আমি’-বোধের সম্পূর্ণ লোপে ঐ কালে তাঁহার শরীর রহিল কিরূপে
প্র – বল কি? তবে তাঁহার শরীর রহিল কিরূপে? কারণ, ছয়মাস না খাইলে তো আর মানবদেহ থাকিতে পারে না এবং তোমরা তো বল যতটা শরীরবোধ আসিলে আহারাদি কার্য করা চলে, ঠাকুরের ঐ কালে মাঝে মাঝে ‘আমি’-বোধের উদয় হইলেও ততটা কখনই আসে নাই।
উ – সত্যই ঠাকুরের শরীর থাকিত না এবং ‘শরীরটা কিছুকাল থাকুক’ এরূপ ইচ্ছার লেশমাত্রও তখন ঠাকুরের মনে ছিল না; তবে তাঁহার শরীরটা যে ছিল সে কেবল জগদম্বা ঠাকুরের শরীরটার সহায়ে তাঁহার অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ দেখাইয়া বহুজন-কল্যাণ সাধিত করিবেন বলিয়া।
জনৈক যোগী-সাধুর আগমন ও ঠাকুরের অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে নিত্য জোর করিয়া আহার করাইয়া দেওয়া
প্র – তা তো বটে, কিন্তু ঐ ছয়মাস কাল জগদম্বা নিজে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া আসিয়া কি ঠাকুরকে জোর করিয়া আহার করাইয়া দিতেন?
উ – কতকটা সেইরূপই বটে; কারণ, ঐ সময়ে একজন সাধু কোথা হইতে আপনা-আপনি আসিয়া জোটেন, ঠাকুরের ঐরূপ মৃতকল্প অবস্থা যে যোগসাধনা বা শ্রীভগবানের সহিত একত্বানুভবের ফলে তাহা সম্যক বুঝেন এবং ঐ ছয়মাস কাল দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটীতে থাকিয়া সময়ে সময়ে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে আঘাত পর্যন্ত করিয়া একটু-আধটু হুঁশ আনিতে নিত্য চেষ্টা করিতেন; আর একটু হুঁশ আসিতেছে দেখিলেই দুই-এক গ্রাস যাহা পারিতেন, খাওয়াইয়া দিতেন। একেবারে অপরিচিত জড়প্রায় মৃতকল্প একটি লোককে ঐরূপে বাঁচাইয়া রাখিতে সাধুটির এত আগ্রহ, এতটা মাথাব্যথা কেন হইয়াছিল জানি না, তবে ঐরূপ ঘটনাবলীকেই আমরা ভগবদিচ্ছায় সাধিত বলিয়া থাকি। অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার সাক্ষাৎ ইচ্ছা ও শক্তিতেই যে ঐ অসম্ভব সম্ভব হইয়া ঠাকুরের শরীরটা রক্ষা পাইয়াছিল ইহা ছাড়া আর কি বলিব?
শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশ – ‘ভাবমুখে থাক্’
প্র – আচ্ছা, বুঝিলাম, তারপর?
উ – তাহার পর, শ্রীশ্রীজগদম্বা বা শ্রীভগবান বা যে বিরাটচৈতন্য ও বিরাট-শক্তি জগদ্রূপে প্রকাশিত আছেন এবং জড় চেতন সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আপাতবিভিন্ন নামরূপে অবস্থান করিতেছেন তিনি ঠাকুরকে আদেশ করিলেন – ‘ভাবমুখে থাক’!
একমেবাদ্বিতীয়ং-বস্তুতে নির্গুণ ও সগুণভাবে স্বগত-ভেদ এবং জগদ্ব্যাপী বিরাট আমিত্ব বর্তমান। ঐ বিরাট আমিত্বই ঈশ্বর বা শ্রীশ্রীজগদম্বার আমিত্ব; এবং উহার দ্বারাই জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়
প্র – সেটা আবার কি?
উ – বলিতেছি, কিন্তু ঠাকুরের ঐ সময়কার কথা বুঝিতে হইলে কল্পনাসহায়ে যতদূর সম্ভব ঠাকুরের ঐ সময়ের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লওয়া আবশ্যক। পূর্বে বলিয়াছি, ঠাকুরের তখন কখনো ‘আমি’-জ্ঞানের লোপ এবং কখনো উহার ঈষৎ প্রকাশ হইতেছিল। যখন ‘আমি’-বোধটার ঐরূপ ঈষৎ প্রকাশ হইতেছিল তখনো ঠাকুরের নিকট জগৎটা, আমরা যেমন দেখি তেমন দেখাইতেছিল না। দেখাইতেছিল, যেন একটা বিরাট মনে নানা ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, ভাসিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, আবার লয় হইতেছে! অপর সকলের তো কথাই নাই, ঠাকুরের নিজের শরীরটা, মনটা ও আমিত্ববোধটাও ঐ বিরাট-মনের ভিতরের একটা তরঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছিল। পাশ্চাত্য জড়বাদী পণ্ডিতমূর্খের দল যে জগচ্চৈতন্য ও শক্তিকে নিজের বুদ্ধি ও বুদ্ধিপ্রসূত যন্ত্রাদিসহায়ে মাপিতে যাইয়া বলিয়া বসে ‘ওটা এক হলেও জড়’, ঠাকুর এই অবস্থায় পৌঁছাইয়া তাঁহারই সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শন বা অনুভব করিলেন – জীবন্ত, জাগ্রত, একমেবাদ্বিতীয়ম্, ইচ্ছা ও ক্রিয়ামাত্রেরই প্রসূতি, অনন্ত কৃপাময়ী জগজ্জননী! আর দেখিলেন – সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্, নির্গুণ ও সগুণ ভাবে আপনাতে আপনি বিভক্ত থাকায় – ইহাকেই শাস্ত্রে স্বগতভেদ বলিয়াছে – তাঁহাতে একটা আব্রহ্ম-স্তম্বপর্যন্তব্যাপী বিরাট আমিত্ব বিকশিত রহিয়াছে! শুধু তাহাই নহে, সেই বিরাট ‘আমি’টা থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে; আর সেই ভাবতরঙ্গই স্বল্পাধিক পরিমাণে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিতে পাইয়া মানবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ‘আমি’গুলো উহাকেই বাহিরের জগৎ ও বহির্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া ধরিতেছে ও বলা-কহা ইত্যাদি করিতেছে! ঠাকুর দেখিলেন বড় ‘আমি’টার শক্তিতেই মানবের ছোট ‘আমি’গুলো রহিয়াছে ও স্ব স্ব কার্য করিতেছে এবং বড় ‘আমি’টাকে দেখিতে-ধরিতে পাইতেছে না বলিয়াই ছোট ‘আমি’গুলো ভ্রমে পড়িয়া আপনাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিমান মনে করিতেছে। এই দৃষ্টিহীনতাকেই শাস্ত্র অবিদ্যা ও অজ্ঞান বলেন।
ঐ বিরাট আমিত্বেরই নাম ‘ভাবমুখ’, কারণ সংসারের সকল প্রকার ভাবই উহাকে আশ্রয় করিয়া উদয় হইতেছে
নির্গুণ ও সগুণের মধ্যস্থলে এইরূপে যে বিরাট ‘আমিত্ব’টা বর্তমান, উহাই ‘ভাবমুখ’ – কারণ উহা থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবের স্ফুরণ হইতেছে। এই বিরাট আমিই জগজ্জননীর আমিত্ব বা ঈশ্বরের আমিত্ব। এই বিরাট আমিত্বের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বলিয়াছেন, অচিন্ত্যভেদাভেদস্বরূপ জ্যোতির্ঘনমূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।
পূর্ণ নির্বিকল্প এবং ঈষৎ সবিকল্প বা ‘ভাবমুখ’ অবস্থায় ঠাকুরের অনুভব ও দর্শন
ঠাকুরের আমিত্ব-জ্ঞানের যখন একেবারে লোপ হইতেছিল তখন এই বিরাট আমিত্বের গণ্ডির পারে অবস্থিত জগদম্বার নির্গুণ ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন – তখন ঐ ‘বিরাট আমি’ ও তাহার অনন্ত ভাবতরঙ্গ, যাহাকে আমরা জগৎ বলিতেছি, তাহার কিছুরই অস্তিত্ব অনুভব হইতেছিল না; আর যখন ঠাকুরের ‘আমি’-জ্ঞানের ঈষৎ উন্মেষ হইতেছিল তখন তিনি দেখিতেছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণভাবের সহিত সংযুক্ত এই সগুণ বিরাট ‘আমি’ ও তদন্তর্গত ভাবতরঙ্গসমূহ। অথবা নির্গুণভাবে উঠিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অনুভবে ঐ একমেবাদ্বিতীয়মের ভিতর স্বগতভেদের অস্তিত্বও লোপ হইতেছিল; আর ঐ সগুণ বিরাট আমিত্বের যখন বোধ করিতেছিলেন, তখন দেখিতেছিলেন – যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যে নির্গুণ সেই সগুণ, যে পুরুষ সেই প্রকৃতি, যে সাপ স্থির ছিল সেই এখন চলিতেছে, অথবা যিনিই স্বরূপে নির্গুণ তিনিই আবার লীলায় সগুণ!
‘ভাবমুখে থাক্’ – কথার অর্থ
শ্রীশ্রীজগদম্বার এই নির্গুণ-সগুণ উভয় ভাবে জড়িত স্বরূপের পূর্ণ দর্শন পাইবার পর ঠাকুর আদেশ পাইলেন ‘ভাবমুখে থাক্’ – অর্থাৎ আমিত্বের একেবারে লোপ করিয়া নির্গুণভাবে অবস্থান করিও না; কিন্তু যাহা হইতে যত প্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে সেই বিরাট ‘আমি’ই তুমি, তাঁহার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা, তাঁহার কার্যই তোমার কার্য – এই ভাবটি ঠিক ঠিক সর্বদা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া জীবনযাপন কর ও লোককল্যাণসাধন কর। অতএব ‘ভাবমুখে’ থাকার অর্থই হইতেছে – মনে সর্বতোভাবে, সকল সময় সকল অবস্থায় দেখা, ধারণা বা বোধ করা যে আমি সেই ‘বড় আমি’ বা ‘পাকা আমি’। ‘ভাবমুখ’ অবস্থায় পৌঁছিলে, আমি অমুকের সন্তান, অমুকের পিতা, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র ইত্যাদি সমস্ত কথা একেবারে মন হইতে ধুইয়া-পুঁছিয়া যায় এবং ‘আমি সেই বিশ্বব্যাপী আমি’ এই কথাটি সর্বদা মনে অনুভব হয়। ঠাকুর তাই আমাদের বার বার শিক্ষা দিতেন – “ওগো, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি, ব্রাহ্মণ আমি, শূদ্র আমি, পণ্ডিত আমি, ধনী আমি – এ সব হচ্চে কাঁচা আমি; ওতে বন্ধন নিয়ে আসে। ও সব ছেড়ে মনে করবে তাঁর (ভগবানের) দাস আমি, তাঁর ভক্ত আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি। এই ভাবটি মনে পাকা করে রাখবে।” অথবা বলিতেন – “ওরে, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তা কর!”
সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত-ভাব পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়
পাঠক হয়তো বলিবে, ঠাকুর কি তবে ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী ছিলেন না? শ্রীশ্রীজগদম্বার মধ্যে স্বগতভেদ স্বীকার করিয়া ঠাকুর যখন জগন্মাতার নির্গুণ সগুণ দুই ভাবে অবস্থান দেখিতেন, তখন তো বলিতে হইবে তিনি আচার্য শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ, যাহাতে জগতের অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় নাই, তাহা মানিতেন না? তাহা নহে! ঠাকুর অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত সকল ভাব বা মতই মানিতেন। তবে বলিতেন, ঐ তিন প্রকার মত মানবমনের উন্নতির অবস্থানুযায়ী পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়। এক অবস্থায় দ্বৈতভাব আসে – তখন অপর দুই ভাবই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। ধর্মোন্নতির উচ্চতর সোপানে উঠিয়া অপর অবস্থায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আসে – তখন নিত্য নির্গুণ বস্তু লীলায় সতত সগুণ হইয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বোধ হয়। তখন দ্বৈতবাদ তো মিথ্যা বোধ হয়ই, আবার অদ্বৈতবাদে যে সত্য নিহিত আছে তাহাও মনে উপলব্ধি হয় না। আর মানব যখন ধর্মোন্নতির শেষ সীমায় সাধনসহায়ে উপস্থিত হয় তখন শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণরূপেই কেবলমাত্র উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে অদ্বৈতভাবে অবস্থান করে। তখন আমি-তুমি, জীব-জগৎ, ভক্তি-মুক্তি, পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম – সব একাকার!
মহাজ্ঞানী হনুমানের ঐ বিষয়ক কথা
এই প্রসঙ্গে ঠাকুর দাস্যভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন মহাজ্ঞানী হনুমানের ঐ বিষয়ের উপলব্ধিটি দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতেন। বলিতেন – “শ্রীরামচন্দ্র কোন সময়ে নিজ দাস হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তুমি আমায় কি ভাবে দেখ, বা ভাবনা ও পূজা কর?’ হনুমান তদুত্তরে বলেন, ‘হে রাম, যখন আমি দেহবুদ্ধিতে থাকি অথবা আমি এই দেহটা এইরূপ অনুভব করি, তখন দেখি – তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি সেব্য, আমি সেবক; তুমি পূজ্য, আমি পূজক; যখন আমি মন বুদ্ধি ও আত্মাবিশিষ্ট জীবাত্মা বলিয়া আপনাকে বোধ করিতে থাকি, তখন দেখি – তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; আর যখন আমি উপাধিমাত্ররহিত শুদ্ধ আত্মা, সমাধিতে এই ভাব লইয়া থাকি, তখন দেখি – তুমিও যাহা, আমিও তাহা – তুমি আমি এক, কোনই ভেদ নাই।'”
অদ্বৈতভাব চিন্তা, কল্পনা ও বাক্যাতীত; যতক্ষণ বলা কহা আছে ততক্ষণ নিত্য ও লীলা, ঈশ্বরের উভয় ভাব লইয়া থাকিতেই হইবে
ঠাকুর বলিতেন, “যে ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী সে চুপ হইয়া যায়! অদ্বৈতবাদ বলবার বিষয় নয়। বলতে-কইতে গেলেই দুটো এসে পড়ে, ভাবনা-কল্পনা যতক্ষণ ততক্ষণও ভিতরে দুটো – ততক্ষণও ঠিক অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাই। জগতে একমাত্র ব্রহ্মবস্তু বা শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণভাবই কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই।” অর্থাৎ মানবের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, অথবা মানব ভাষা দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। কারণ ঐ ভাব মানবের মন-বুদ্ধির অতীত; বাক্যে তাহা কেমন করিয়া বলা বা বুঝানো যাইবে? অদ্বৈতভাব সম্বন্ধে ঠাকুর সেজন্য বার বার বলিতেন, “ওরে, ওটা শেষকালের কথা।” অতএব দেখা যাইতেছে ঠাকুর বলিতেন, “যতক্ষণ ‘আমি-তুমি’ ‘বলা-কহা’ প্রভৃতি রহিয়াছে ততক্ষণ নির্গুণ-সগুণ, নিত্য ও লীলা – দুই ভাবই কার্যে মানিতে হইবে। ততক্ষণ অদ্বৈতভাব মুখে বলিলেও কার্যে, ব্যবহারে তোমাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী থাকিতে হইবে।” ঐ সম্বন্ধে ঠাকুর আরও কতই না দৃষ্টান্ত দিতেন! বলিতেন –
ঐ বিষয়ে ঠাকুরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। যথা – গানের অনুলোম-বিলোম; বেল, থোড়, প্যাঁজের খোলা
“যেমন গানের অনুলোম-বিলোম – সা ঋ গা মা পা ধা নি সা করিয়া সুর তুলিয়া আবার সা নি ধা পা মা গা ঋ সা – করিয়া সুর নামানো। সমাধিতে অদ্বৈত-বোধটা অনুভব করিয়া আবার নিচে নামিয়া ‘আমি’-বোধটা লইয়া থাকা।
“যেমন বেলটা হাতে লইয়া বিচার করা যে, খোলা, বিচি, শাঁস – ইহার কোনটা বেল। প্রথম খোলাটাকে অসার বলিয়া ফেলিয়া দিলাম, বিচিগুলোকেও ঐরূপ করিলাম; আর শাঁসটুকু আলাদা করিয়া বলিলাম, এইটিই বেলের সার – এইটিই আদত বেল। তারপর আবার বিচার আসিল যে, যাহারই শাঁস তাহারই খোলা ও বিচি – খোলা, বিচি ও শাঁস সব একত্র করিয়াই বেলটা; সেই রকম নিত্য ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া তারপর বিচার – যে নিত্য সেই লীলায় জগৎ!
“যেমন থোড়খানার খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে মাঝটায় পৌঁছুলুম আর সেটাকেই সার ভাবলুম। তারপর বিচার এল – খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল – দুই জড়িয়েই থোড়টা।
“যেমন প্যাঁজটা খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছুই থাকে না, সেই রকম কোনটা ‘আমি’ বিচার করে দেখতে গিয়ে শরীরটা নয়, মনটা নয়, বুদ্ধিটা নয় করে ছাড়াতে ছাড়াতে গিয়ে দেখা যায়, ‘আমি’ বলে একটা আলাদা কিছুই নাই – সবই ‘তিনি’ ‘তিনি’ ‘তিনি’ (ঈশ্বর); যেমন গঙ্গার খানিকটা জল বেড়া দিয়ে ঘিরে বলা – এটা আমার গঙ্গা!”
যাক্, এখন ও-সকল কথা, আমরা পূর্বকথার অনুসরণ করি।
ভাবমুখ – নির্গুণ হইতে কয়েকপদ নিম্নে অবস্থিত থাকিলেও ঐ অবস্থায় অদ্বৈত বস্তুর বিশেষ অনুভব থাকে। ঐ অবস্থায় কিরূপ অনুভব হয়। ঠাকুরের দৃষ্টান্ত
ভাবমুখে থাকিয়া যখন বিশ্বব্যাপী আমিত্বের ঠিক ঠিক অনুভব হইত তখন ‘এক’ হইতে ‘বহু’র বিকাশ দেখিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার নিৰ্গুণভাব হইতে কয়েক পদ নিচে বিদ্যা-মায়ার রাজ্যে যে বিচরণ করিতেন, এ কথা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু সে রাজ্যেও একের বিকাশ ও অনুভব এত অধিক যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে যে যাহা করিতেছে, ভাবিতেছে, বলিতেছে, সেসকলই আমি করিতেছি, ভাবিতেছি, বলিতেছি বলিয়া ঠাকুরের ঠিক ঠিক মনে হইত! এই অবস্থার অল্প বা আভাসমাত্র অনুভবও অতি অদ্ভুত! ঠাকুর বলিয়াছিলেন, একদিন ঘাসের উপর দিয়া একজন চলিয়া যাইতেছে, আর তাঁহার বুকে বিষম আঘাত লাগিতেছে! – যেন তাঁহার বুকের উপর দিয়াই সে যাইতেছে! বাস্তবিকই তখন তাঁহার বুকে রক্ত জমিয়া কালো দাগ হইয়া তিনি বেদনায় ছটফট করিয়াছিলেন।
বিদ্যা-মায়ার রাজ্যে আরও নিম্নস্তরে নামিলে তবে ঈশ্বরের দাস, ভক্ত, সন্তান বা অংশ-‘আমি’ – এইরূপ অনুভব হয়
ঐ অবস্থা হইতে মায়ার রাজ্যের আরও নিম্নস্তরে নামিয়া যখন থাকিতেন, তখন ঠাকুরের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার দাস আমি, ভক্ত আমি, সন্তান আমি বা অংশ আমি – এই ভাবটি সর্বদা জাগরূক থাকিত। উহা হইতেও নিম্নে অবিদ্যা-মায়ার বা কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির রাজত্ব। সে রাজ্য ঠাকুর যত্নপূর্বক নিরন্তর অভ্যাস সহকারে ত্যাগ করায় তাঁহার মন তথায় আর কখনো নামিত না বা শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে নামিতে দিতেন না। ঠাকুর যেমন বলিতেন, “যে মার উপর একান্ত নির্ভর করেছে, মা তার পা বেতালে পড়তে দেন না।”
ঠাকুরের ‘কাঁচা আমি’টার এককালে নাশ হইয়া বিরাট ‘পাকা আমিত্বে’ অনেক কাল অবস্থিতি। ঐ অবস্থাতেই তাঁহাতে গুরুভাব প্রকাশ পাইত। অতএব দীনভাব ও গুরুভাব অবস্থানুসারে এক ব্যক্তিতে আসা অসম্ভব নহে
অতএব বুঝা যাইতেছে, নির্বিকল্প-সমাধিলাভের পর ঠাকুরের ভিতরের ছোট আমি বা কাঁচা আমিটার একেবারে লোপ হইয়াছিল। আর যে আমিত্বটুকু ছিল সেটি আপনাকে ‘বড় আমি’ বা ‘পাকা আমি’-টার সঙ্গে চিরসংযুক্ত দেখিত – কখনো আপনাকে দেখিত সেই বিশ্বব্যাপী আমিটার অঙ্গ বা অংশ, আবার কখনো তাহার নিকট নিকটতর নিকটতম দেশে উঠিয়া সেই বিশ্বব্যাপী ‘আমি’-তে লীন হইয়া যাইত। এই পথেই ঠাকুরের সকল মনের সকল ভাব আয়ত্তীভূত হইত। কারণ ঐ ‘বড় আমি’-কে আশ্রয় করিয়াই জগতে সকলের মনের যত প্রকার ভাব উঠিতেছে। ঠাকুর ঐ বিশ্বব্যাপী ‘আমি’-কে আশ্রয় করিয়া অনুক্ষণ থাকিতে পারিতেন বলিয়াই বিশ্বমনে যত ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, সকলই ধরিতে ও বুঝিতে সক্ষম হইতেন। ঐরূপ উচ্চাবস্থায় ‘ভগবানের অংশ আমি’, ঠাকুরের এ ভাবটিও ক্রমশঃ লীন হইয়া যাইত, এবং ‘বিশ্বব্যাপী আমি’ বা শ্রীশ্রীজগন্মাতার আমিত্বই ঠাকুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ গুরুরূপে প্রতিভাত হইত! কাজেই ঠাকুরকে দেখিলে তখন আর ‘দীনের দীন’ বলিয়া বোধ হইত না। তখন ঠাকুরের চাল-চলন, অপরের সহিত ব্যবহার প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াকলাপই অন্য আকার ধারণ করিত। তখন কল্পতরুর মতো হইয়া তিনি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিতেন, “তুই কি চাস?” – যেন ভক্ত যাহা চাহেন তাহা তৎক্ষণাৎ অমানুষী শক্তিবলে পূরণ করিতে বসিয়াছেন! দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগকে কৃপা করিবার জন্য ঐরূপ ভাবাপন্ন হইতে ঠাকুরকে আমরা নিত্য দেখিয়াছি; আর দেখিয়াছি, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি। সেদিন ঠাকুর ঐরূপ ভাবাপন্ন হইয়া তৎকালে উপস্থিত সকল ভক্তদিগকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের ভিতর ধর্মশক্তি সঞ্চারিত বা সুপ্ত ধর্মভাবকে জাগ্রত করিয়া দেন! সে এক অপূর্ব কথা – এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।
গুরুভাবে ঠাকুরের ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অপরে ধর্মশক্তি জাগ্রত করিয়া দিবার দৃষ্টান্ত – ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ ১লা জানুয়ারির ঘটনা
১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি, পৌষ মাস। কিঞ্চিদধিক দুই সপ্তাহ হইল ভক্তেরা শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল সরকার ডাক্তার মহাশয়ের পরামর্শানুসারে ঠাকুরকে কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরে রানী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালবাবুর বাগানবাটীতে আনিয়া রাখিয়াছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন কলিকাতার বায়ু অপেক্ষা বাগান অঞ্চলের বায়ু নির্মল ও যতদূর সম্ভব নির্মল বায়ুতে থাকিলে ঠাকুরের গলরোগের উপশম হইতে পারে। বাগানে আসিবার কয়েকদিন পরেই ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং লাইকোপোডিয়াম (২০০) ঔষধ প্রয়োগ করেন। উহাতে গলরোগটার কিছু উপকারও বোধ হয়। ঠাকুর কিন্তু এখানে আসা অবধি বাটীর দ্বিতল হইতে একদিন একবারও নিচের তলে নামেন নাই বা বাগানে বেড়াইয়া বেড়ান নাই। আজ শরীর অনেকটা ভাল থাকায় অপরাহ্ণে বাগানে বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই ভক্তদিগের আজ বিশেষ আনন্দ।
স্বামী বিবেকানন্দের তখন তীব্র বৈরাগ্য – সাংসারিক উন্নতিকামনাসমূহ ত্যাগ করিয়া ঠাকুরের নিকটে বাস করিতেছেন ও তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য নানাপ্রকার সাধন করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি বৃক্ষতলে ধুনি বা অগ্নি জ্বালাইয়া ধ্যান, জপ, ভজন, পাঠ ইত্যাদিতেই থাকেন! অপর কয়েকজন ভক্তও, যথা – ছোট গোপাল, কালী (অভেদানন্দ) ইত্যাদি, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনয়ন প্রভৃতি করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করেন এবং আপনারাও যথাসাধ্য ধ্যান-ভজন করেন। গৃহী ভক্তেরা বিষয়-কর্মাদিতে নিযুক্ত থাকায় সর্বদা ঠাকুরের নিকটে থাকিতে পারেন না; সুবিধা পাইলেই আসা-যাওয়া করেন এবং যাঁহারা ঠাকুরের সেবায় নিরন্তর ব্যাপৃত, তাঁহাদের আহারাদির সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন ও কখনো কখনো এক-আধ দিন থাকিয়াও যান। আর ইংরাজী বর্ষের প্রথম দিন বলিয়া ছুটি থাকায় অনেকেই কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইয়াছেন।
অপরাহ্ণ বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি, একটি পিরান, লালপাড় বসান একখানি মোটা চাদর, কানঢাকা টুপি ও চটিজুতাটি পরিয়া স্বামী অদ্ভুতানন্দের সহিত উপর হইতে ধীরে ধীরে নিচে নামিলেন এবং নিচেকার হলঘরটি দেখিয়া পশ্চিমের দরজা দিয়া বাগানের পথে বেড়াইতে চলিলেন। গৃহী ভক্তেরা কেহ কেহ ঠাকুর ঐরূপে বেড়াইতে যাইতেছেন দেখিতে পাইয়া সানন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ বালক বা যুবক ভক্তেরা তখন সমস্ত রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত থাকায় হলঘরের পাশে যে ছোট ঘরটি ছিল, তাহার ভিতর নিদ্রা যাইতেছেন। শ্রীযুত লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) তাঁহাদিগকে ঐরূপে যাইতে দেখিয়া ঠাকুরের সহিত স্বয়ং আর অধিক দূর যাওয়া অনাবশ্যক বুঝিয়া হলঘরের সম্মুখে ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটির দক্ষিণপাড় পর্যন্ত আসিয়াই ফিরিলেন এবং অপর একজন যুবক ভক্তকে ডাকিয়া লইয়া ঠাকুর উপরে যে ঘরটিতে থাকেন সেটি ঝাঁটপাট দিয়া পরিষ্কার করিতে ও ঠাকুরের বিছানা প্রভৃতি রৌদ্রে দিতে ব্যাপৃত হইলেন।
গৃহী ভক্তগণের ভিতর শ্রীযুত গিরিশের তখন প্রবল অনুরাগ। ঠাকুর কোন সময়ে তাঁহার অদ্ভুত বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অন্য ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, “গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস! ইহার পর লোকে ওর অবস্থা দেখে অবাক হবে!” বিশ্বাস-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় গিরিশ তখন হইতে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান – জীবোদ্ধারের জন্য কৃপায় অবতীর্ণ বলিয়া অনুক্ষণ দেখিতেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তাঁহার ঐ ধারণা সকলের নিকট প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইতেন। গিরিশও সেদিন বাগানে উপস্থিত আছেন এবং শ্রীযুত রাম প্রমুখ অন্য কয়েকটি গৃহী ভক্তের সহিত একটি আমগাছের তলায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।
ঠাকুর ভক্তগণ-পরিবৃত হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ প্রশস্ত পথটি দিয়া বাগানের গেটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় মধ্যপথে আসিয়া পথের ধারে আমগাছের ছায়ায় শ্রীযুত রাম ও শ্রীযুত গিরিশকে দেখিতে পাইলেন এবং গিরিশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “গিরিশ, তুমি কি দেখেছ (আমার সম্বন্ধে) যে অত কথা (আমি অবতার ইত্যাদি) যাকে তাকে বলে বেড়াও?”
সহসা ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াও গিরিশের বিশ্বাস টলিল না। তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাস্তার উপরে আসিয়া ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া করজোড়ে উপবিষ্ট হইলেন এবং গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, “ব্যাস বাল্মীকি যাঁহার কথা বলিয়া অন্ত করিতে পারেন নাই আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিতে পারি!”
গিরিশের ঐরূপ অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা শুনিয়া ঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং মন উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন। গিরিশও তখন ঠাকুরের সেই দেবভাবে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া উল্লাসে চিৎকার করিয়া ‘জয় রামকৃষ্ণ’ ‘জয় রামকৃষ্ণ’ বলিয়া বার বার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন।
ঠাকুরের ঐরূপ স্পর্শে ভক্তদিগের প্রত্যেকের দর্শন ও অনুভব
ইতোমধ্যে ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় হাস্যমুখে উপস্থিত সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তোমাদের কি আর বলিব, তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক!” ভক্তেরা সে অভয়বাণী শুনিয়া তখন আনন্দে জয় জয় রব করিয়া কেহ প্রণাম, কেহ পুষ্পবর্ষণ এবং কেহ বা আসিয়া পদস্পর্শ করিতে লাগিলেন। প্রথম ব্যক্তি পদস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান হইবামাত্র ঠাকুর ঐরূপ অর্ধবাহ্যাবস্থায় তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া নিচের দিক হইতে উপরদিকে হস্ত সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন, “চৈতন্য হোক!” দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র তাহাকেও ঐরূপ করিলেন! তৃতীয় ব্যক্তিকেও ঐরূপ! চতুর্থকেও ঐরূপ! এইরূপে সমাগত ভক্তদিগের সকলকে একে একে ঐরূপে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আর সে অদ্ভুত স্পর্শে প্রত্যেকের ভিতর অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া কেহ হাসিতে, কেহ কাঁদিতে, কেহ বা ধ্যান করিতে, আবার কেহ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহেতুক-দয়ানিধি ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য অপর সকলকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন! সে চিৎকার ও জয় রবে ত্যাগী ভক্তেরা কেহ বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কেহ বা হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, উদ্যানপথমধ্যে সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া ঐরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন! এবং দেখিয়াই বুঝিলেন, দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কৃপায় ঠাকুরের দিব্যভাবাবেশে যে অদৃষ্টপূর্ব লীলার অভিনয় হইত তাহারই অদ্য এখানে সকলের প্রতি কৃপায় সকলকে লইয়া প্রকাশ! ত্যাগী ভক্তেরা আসিতে আসিতেই ঠাকুরের সে অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া আবার সাধারণ সহজ ভাব উপস্থিত হইল। পরে গৃহী ভক্তদিগের অনেককে ঐ সময়ে কিরূপ অনুভব হইয়াছিল তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, কাহারও সিদ্ধির নেশার মতো একটা নেশা ও আনন্দ – কাহারও চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র যে মূর্তির নিত্য ধ্যান করিতেন অথচ দর্শন পাইতেন না, ভিতরে সেই মূর্তির জাজ্বল্য দর্শন – কাহারও ভিতরে পূর্বে অননুভূত একটা পদার্থ বা শক্তি যেন সড়সড় করিয়া উপরে উঠিতেছে, এইরূপ বোধ ও আনন্দ এবং কাহারও বা পূর্বে যাহা কখনো দেখেন নাই এরূপ একটা জ্যোতিঃ চক্ষু মুদ্রিত করিলেই দর্শন ও আনন্দানুভব হইয়াছিল! দর্শনাদি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন হইলেও একটা অসাধারণ দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইবার অনুভবটি সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ – এ কথাটি বেশ বুঝা গিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের ভিতরের অমানুষী শক্তিবিশেষই যে বাহ্যস্পর্শ দ্বারা সঞ্চারিত হইয়া প্রত্যেক ভক্তের ভিতর ঐরূপ অপূর্ব মানসিক অনুভব ও পরিবর্তন আনিয়া দিল, এ কথাটিও সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছিল। উপস্থিত ভক্তসকলের মধ্যে দুই জনকে কেবল ঠাকুর “এখন নয়” বলিয়া ঐরূপ স্পর্শ করেন নাই! এবং তাঁহারাই কেবল এ আনন্দের দিনে আপনাদিগকে হতভাগ্য জ্ঞান করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছিলেন।1
1. পরে একদিন ঠাকুর ইঁহাদেরও ঐরূপে স্পর্শ করিয়াছিলেন।
কখন কাহাকে কৃপায় ঠাকুর ঐ ভাবে স্পর্শ করিবেন তাহা বুঝা যাইত না
ইহা দ্বারা এ বিষয়টিও বুঝা গিয়াছিল যে, কখন কাহার প্রতি কৃপায় ঠাকুরের ভিতর দিয়া ঐ দিব্যশক্তির প্রকাশ হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই! সাধারণ অবস্থায় ঠাকুর নিজেও তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ।
‘কাঁচা আমি’টার লোপ বা নাশেই গুরুভাব-প্রকাশের কথা সকল ধর্মশাস্ত্রে আছে
অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে, কাঁচা বা ছোট আমিত্বটাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর ‘বিশ্বব্যাপী আমি’ বা শ্রীশ্রীজগদম্বার শক্তিপ্রকাশের মহান যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন! এবং ঐ কাঁচা ‘আমি’-টাকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যথার্থ ‘দীনের দীন’ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার লোকগুরু, জগদ্গুরু-ভাবটির এইরূপ অপূর্ব বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল! এইরূপে আমিত্বের লোপেই গুরুভাব বা গুরুশক্তির বিকাশ যেসকল ধর্মগত সকল অবতারপুরুষগণের জীবনেই উপস্থিত হইয়াছিল, জগতের ধৰ্মেতিহাস এ বিষয়ে চিরকাল সাক্ষ্য দিতেছে।
গুরুভাব মানবীয় ভাব নহে – সাক্ষাৎ জগদম্বার ভাব, মানবের শরীর ও মনকে যন্ত্র-স্বরূপে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত
গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে ধর্মলাভ বা ঈশ্বরলাভ হয় না, একথা আমরা আবহমান কাল ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি।
‘গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।’
– ইত্যাদি স্তুতিকথা আমরা চিরকালই বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সহিত মন্ত্রদীক্ষাদাতা গুরুর উদ্দেশে উচ্চারণ করিয়া আসিতেছি। অনেকে আবার বিদেশী শিক্ষার কুহকে পড়িয়া আপনাদের জাতীয় শিক্ষা ও ভাব বিসর্জন দিয়া মানববিশেষকে ঐরূপ বলা মহাপাপের ভিতর গণ্য করিয়া অনেক বাদানুবাদ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই! কারণ কে-ই বা তখন বুঝে যে, কোন কোন মানব-শরীরকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইলেও গুরুভাবটি মানবীয় ভাবরাজ্যেরই অন্তর্গত নহে। কে-ই বা তখন জানে যে, শরীররক্ষার উপযোগী জলবায়ু, আহার প্রভৃতি নিত্যাবশ্যকীয় বস্তুসমস্তের ন্যায়, মায়াপাশে বদ্ধ ত্রিতাপে তাপিত মানবমনের সমস্ত জ্বালানিবারণ ও শান্তিলাভের উপায়স্বরূপ হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতা স্বয়ংই ঐ ভাব ও শক্তিরূপে শুদ্ধ, বুদ্ধ, অহমিকাশূন্য মানবমনের ভিতর দিয়া পূর্ণরূপে প্রকাশিত আছেন? এবং কে-ই বা তখন ধারণা করে যে, যাহার মন যতটা পরিমাণে অহঙ্কার ত্যাগ করিতে বা ‘কাঁচা আমি’-টাকে ছাড়িতে পারে ততটা পরিমাণেই সে ঐ ভাব ও শক্তিপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়! সাধারণ মানবমনে ঐ দিব্যভাবের যৎসামান্য ‘ছিটে ফোঁটা’ মাত্র প্রকাশ, তাই আমরা ততটা ধরিতে ছুঁইতে পারি না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, যীশু প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব যুগাবতারসকলে এবং বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে ঐ দিব্যশক্তির ঐরূপ অপূর্ব লীলা যখন বহুভাগ্যফলে কাহারও নয়নপথে পতিত হয়, তখনই সে প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া থাকে যে, এ শক্তিপ্রকাশ মানবের নহে – সাক্ষাৎ ঈশ্বরের! তখনই ভবরোগগ্রস্ত পথভ্রান্ত জিজ্ঞাসু মানবের মোহ-মলিনতা দূরে অপসারিত হয় এবং সে বলিয়া উঠে, ‘হে গুরু, তুমি কখনই মানুষ নও – তুমি তিনি!’
ঈশ্বর করুণায় ঐ ভাবাবলম্বনে মানব-মনের অজ্ঞান-মোহ দূর করেন। সেজন্য গুরুভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি একই কথা
অতএব বুঝা যাইতেছে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা যে ভাবরূপে মানবমনের সকল প্রকার অজ্ঞান-মলিনতা দূর করেন, সেই উচ্চ ভাবেরই নাম গুরুভাব বা গুরুশক্তি। ঐ ভাবকেই শাস্ত্র গুরু নামে নির্দেশ করিয়াছেন ও মানবকে উহার প্রতি মনের ষোল আনা শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি, ভক্তি-শ্রদ্ধাদি সবেমাত্র শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ প্রকার মানব-মন তো আর একটা অশরীরী ভাবকে ধরিতে ছুঁইতে, ভালবাসিতে পারে না; এজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, দীক্ষাদাতা মানবকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিতে। সেজন্য যাঁহারা বলেন, আমরা গুরুভাবটিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে পারি, কিন্তু যে দেহটা আশ্রয় করিয়া ঐ ভাব আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় তাহাকে মান্য-ভক্তি কেন করিব – ঐ ভাব তো আর তাঁহার নহে? তাঁহাদিগকে আমরা বলি – ‘ভাই, করিতে পার কর, কিন্তু দেখিও যেন নিজের মনের জুয়াচুরিতে ঠকিতে না হয়; শক্তি বা ভাব এবং যদবলম্বনে ঐ ভাব প্রকাশিত থাকে তদুভয়কে কখনো তো পৃথক পৃথক থাকিতে দেখ নাই, তবে কেমন করিয়া আগুন ও আগুনের দাহিকাশক্তিকে পৃথক করিয়া একটিকে গ্রহণ ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে এবং অপরটিকে ত্যাগ করিবে, তাহা বলিতে পারি না!’ যে যাহাকে ভালবাসে বা ভক্তি করে সে প্রেমাস্পদের ব্যবহৃত অতি সামান্য জিনিসটাকেও হৃদয়ে ধারণ করে। তাঁহার স্পৃষ্ট ফুলটা বা কাপড়-চোপড়খানাও সে পবিত্র বলিয়া বোধ করে। তিনি যে স্থান দিয়া চলিয়া যান, সেখানকার মাটিটাও তাহার কাছে বহু মূল্যবান ও বহু আদরের জিনিস বলিয়া বোধ হয়। তবে তিনি যে শরীরটাতে অবস্থান করিয়া তাহার পূজা গ্রহণ করেন ও তাহাকে কৃপা করেন, সেটার প্রতি যে তাহার শ্রদ্ধা-ভক্তি হইবে – এটা কি আবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে? যাহারা গুরুভাবটি কি তাহাই বুঝে না, তাহারাই ঐরূপ কথা বলিয়া থাকে। আর যাহার গুরুভাবের প্রতি ঠিক ঠিক ভক্তি হইবে, তাহার ঐ ভাবের আধার গুরুর শরীরটার উপরেও ভক্তি-শ্রদ্ধার বিকাশ হইবেই হইবে। ঠাকুর এই বিষয়টি বিভীষণের ভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদিগকে বুঝাইতেন। যথা –
গুরুভক্তি-বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ – বিভীষণের গুরুভক্তির কথা
শ্রীরামচন্দ্রের মানবলীলাসংবরণের অনেক কাল পরে কোন সময়ে নৌকাডুবি হইয়া একজন মানব লঙ্কার উপকূলে সমুদ্রতরঙ্গের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। বিভীষণ অমর, তিন কালই তিনি লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছেন – তাঁহার নিকট ঐ সংবাদ পৌঁছিল। সভাস্থ অনেক রাক্ষসের সুকোমল মানবদেহরূপ খাদ্যের আগমনসংবাদে জিহ্বায় জল আসিল। রাজা বিভীষণের কিন্তু ঐ সংবাদ শুনিয়া এক অপূর্ব ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি গলদশ্রুলোচনে ভক্তি-গদ-গদ বাক্যে বার বার বলিতে লাগিলেন, ‘অহো ভাগ্য!’ রাক্ষসেরা তাঁহার ভাব না বুঝিতে পারিয়া সকলে একেবারে অবাক! তৎপরে বিভীষণ তাহাদের বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, ‘যে মানবশরীর আমার রামচন্দ্র ধারণ করিয়া লঙ্কায় পদার্পণ করেন ও আমাকে কৃতার্থ করেন, বহুকাল পরে আজ আবার সেই মানবশরীর দেখিতে পাইব – এ কি কম ভাগ্যের কথা! আমার মনে হইতেছে যেন সাক্ষাৎ রামচন্দ্রই পুনরায় ঐরূপে আসিয়াছেন!’ এই বলিয়া রাজা পাত্র-মিত্র সভাসদসকলকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বহু সম্মান ও আদর করিয়া উক্ত মানবকে প্রাসাদে লইয়া যাইলেন। পরে তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া নিজে সপরিবারে অনুগত দাসভাবে তাহার সেবা ও বন্দনাদি করিতে লাগিলেন! এইরূপে কিছুকাল তাহাকে লঙ্কায় রাখিয়া নানা ধন-রত্ন উপহার দিয়া সজলনয়নে বিদায় দিলেন এবং অনুচরবর্গের দ্বারা বাটী পৌঁছাইয়া দিলেন।
ঠিক ঠিক ভক্তিতে অতি তুচ্ছ বিষয়েও ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। ‘এই মাটিতে খোল হয়!’ – বলিয়াই শ্রীচৈতন্যের ভাব
গল্পটি বলিয়া ঠাকুর আবার বলিতেন, “ঠিক ঠিক ভক্তি হলে এইরূপ হয়। সামান্য জিনিস হতেও তার ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয়ে ভাবে বিভোর হয়। শুনিসনি – ‘এই মাটিতে খোল হয়’ বলে চৈতন্যদেবের ভাব হয়েছিল? এক সময়ে এক জায়গা দিয়ে যেতে যেতে তিনি শুনলেন যে সেই গ্রামে হরিসংকীর্তনের সময় যে খোল বাজে লোকে সেই খোল তৈয়ার ও উহা বিক্রয় করে দিনপাত করে। শুনেই তিনি বলে উঠলেন, ‘এই মাটিতে খোল হয়!’ – বলেই ভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলেন! কেন না, উদ্দীপনা হলো; ‘এই মাটিতে খোল হয়, সেই খোল বাজিয়ে হরিনাম হয়, সেই হরি সকলের প্রাণের প্রাণ – সুন্দরের চাইতেও সুন্দর।’ – একেবারে এত কথা মনে হয়ে হরিতে চিত্ত স্থির হয়ে গেল। সেই রকম যার গুরুভক্তি হয় তার গুরুর আত্মীয়-কুটুম্বদের দেখলে তো গুরুর উদ্দীপনা হবেই, যে গ্রামে গুরুর বাড়ি সে গ্রামের লোকদের দেখলেও ঐরূপ উদ্দীপনা হয়ে তাদের প্রণাম করে, পায়ের ধুলো নেয়, খাওয়ায় দাওয়ায় সেবা করে! এই অবস্থা হলে গুরুর দোষ আর দেখতে পাওয়া যায় না। তখনই এ কথা বলা চলে –
‘যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥’1
নইলে মানুষের তো দোষ-গুণ আছেই। সে তার ভক্তিতে কিন্তু তখন আর মানুষকে মানুষ দেখে না, ভগবান বলেই দেখে! যেমন ন্যাবা-লাগা চোখে সব হলুদবর্ণ দেখে – সেই রকম; তখন তার ভক্তি তাকে দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরই সব – তিনিই গুরু, পিতা, মাতা, মানুষ, গরু, জড়, চেতন সব হয়েছেন।”
দক্ষিণেশ্বরে একদিন একজন সরল উদ্ধত যুবক ভক্ত2 ঠাকুর যে বিষয়টি তাঁহাকে বলিতেছিলেন, তৎসম্বন্ধে নানা আপত্তিতর্ক উত্থাপিত করিতেছিল! ঠাকুর তিন চারি বার তাহাকে ঐ বিষয়টি বলিলেও যখন সে বিচার করিতে লাগিল তখন ঠাকুর তাহাকে সুমিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, “তুমি কেমন গো? আমি বলচি আর তুমি কথাটা নিচ্চ না!” যুবকের এইবার ভালবাসায় হাত পড়িল। সে বলিল, “আপনি যখন বলছেন তখন নিলুম বই কি। আগেকার কথাগুলো তর্কের খাতিরে বলেছিলাম।”
1. অর্থাৎ নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান বা ঈশ্বর।
2. শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল।
অর্জুনের গুরুভক্তির কথা
ঠাকুর শুনিয়া প্রসন্নমুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “গুরুভক্তি কেমন জান? গুরু যা বলবে তা তখনি দেখতে পাবে – সে ভক্তি ছিল অর্জুনের। একদিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে রথে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, ‘দেখ সখা, কেমন এক ঝাঁক পায়রা উড়ছে।’ অর্জুন অমনি দেখিয়া বলিলেন, ‘হাঁ সখা, অতি সুন্দর পায়রা!’ পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণ আবার দেখিয়া বলিলেন, ‘না সখা, ও তো পায়রা নয়!’ অর্জুন দেখিয়া বলিলেন, ‘তাই তো সখা, ও পায়রা নয়।’ কথাটি এখন বোঝ – অর্জুন মহা সত্যনিষ্ঠ, তিনি তো আর কৃষ্ণের খোশামোদ করিয়া ঐরূপ বলিলেন না? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাঁর এত বিশ্বাস-ভক্তি যে, যেমন যেমন শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনও তখন ঠিক ঠিক তা দেখতে পেলেন!”
ঈশ্বরীয় ভাবরূপে গুরু এক। তথাপি নিজ গুরুতে ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা চাই। ঐ বিষয়ে হনুমানের কথা
শাস্ত্র যাঁহাকে অজ্ঞানান্ধকার-দূরীকরণসমর্থ গুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহা পূর্বোক্তরূপে ঐশ্বরিক ভাববিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা এই – গুরু অনেক নহেন, এক। আধার বা যে যে শরীরাবলম্বনে ঈশ্বরের ঐ ভাব প্রকাশিত হয় তাহা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তোমার গুরু, আমার গুরু পৃথক নহেন – ভাবরূপে এক। মৃন্ময় মূর্তিতে দ্রোণকে আচার্যরূপে গ্রহণ ও ভক্তিপূর্বক একলব্যের ধনুর্বেদলাভরূপ মহাভারতীয় কথাটি ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে। অবশ্য একথাটি যুক্তিতে দাঁড়াইলেও ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম হওয়া অনেক সময় ও সাধন-সাপেক্ষ এবং হৃদয়ঙ্গম হইলেও যতক্ষণ মানবের নিজের দেহবোধ থাকে, ততক্ষণ যে শরীরের ভিতর দিয়া গুরুশক্তি তাঁহাকে কৃপা করেন সেই শরীরাবলম্বনেই শ্রীগুরুর পূজা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ঠাকুর এই কথাটির দৃষ্টান্তে নিষ্ঠা-ভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন হনুমানের কথা আমাদিগকে বলিতেন। যথা –
লঙ্কাসমরে শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ মহাবীর মেঘনাদ কর্তৃক কোন সময়ে নাগপাশে আবদ্ধ হন এবং উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নাগকুলের চিরশত্রু গরুড়কে স্মরণ করিয়া আনয়ন করেন। গরুড়কে দেখিবামাত্র নাগকুল ভয়ত্রস্ত হইয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। রামচন্দ্রও নিজভক্ত গরুড়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া গরুড়ের চিরকালপূজিত ইষ্টমূর্তি বিষ্ণুরূপে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ও তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন – যিনি বিষ্ণু তিনিই তখন রামরূপে অবতীর্ণ! হনুমানের কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে ঐরূপে বিষ্ণুমূর্তি পরিগ্রহ করিতে দেখা ভাল লাগিল না এবং কতক্ষণে তিনি পুনরায় রামরূপ পরিগ্রহ করিবেন এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন। হনুমানের ঐ প্রকার মনোভাব বুঝিতে রামচন্দ্রের বিলম্ব হইল না। তিনি গরুড়কে বিদায় দিয়াই পুনরায় রামরূপ পরিগ্রহ করিয়া হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, আমার বিষ্ণুরূপ দেখিয়া তোমার ঐরূপ ভাবান্তর হইল কেন? তুমি মহাজ্ঞানী, তোমার তো আর জানিতে ও বুঝিতে বাকি নাই যে, যে রাম সেই বিষ্ণু?” হনুমান তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “সত্য বটে, এক পরমাত্মাই উভয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং সেজন্য শ্রীনাথ ও জানকীনাথে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু তথাপি আমার প্রাণ সতত জানকীনাথেরই দর্শন চায় – কারণ তিনিই আমার সর্বস্ব! ঐ মূর্তির ভিতর দিয়াই আমি ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি –
“শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥”
সকল মানবেই গুরুভাব সুপ্তভাবে বিদ্যমান
এইরূপে গুরুভাবটি শ্রীশ্রীজগন্মাতার শক্তিবিশেষ ও সেই শক্তি সকল মানবমনেই সুপ্ত বা ব্যক্তভাবে নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই গুরুভক্তিপরায়ণ সাধক শেষে এমন এক অবস্থায় উপনীত হন যে, তখন ঐ শক্তি তাঁহার নিজের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া ধর্মের জটিল নিগূঢ় তত্ত্বসকল তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে থাকে। তখন সাধককে আর বাহিরের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্মবিষয়ক কোনরূপ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে হয় না। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন –
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥
– গীতা, ২/৫২
যখন তোমার বুদ্ধি অজ্ঞান-মোহ হইতে বিমুক্ত হইবে তখন আর এটা শুনা উচিত, ওটা শাস্ত্রে আছে ইত্যাদি কথায় আর তোমার প্রয়োজন থাকিবে না, তুমি ঐ সকলের পারে চলিয়া যাইয়া আপনিই তখন সকল বুঝিতে পারিবে; সাধকের তখন ঐরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়।
ঠাকুরের কথা “শেষে মনই গুরু হয়”
ঠাকুর ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেন, “শেষে মনই গুরু হয় বা গুরুর কাজ করে। মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কানে, (আর) জগদ্গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।” কিন্তু সে মন আর এ মনে অনেক প্রভেদ। সে সময় মন শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের উচ্চ শক্তিপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়, আর এ সময়ে মন ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া ভোগসুখ ও কামক্রোধাদিতেই মাতিয়া থাকিতে চায়।
“গুরু যেন সখী”
ঠাকুর বলিতেন, “গুরু যেন সখী – যতদিন না শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন হয়, ততদিন সখীর কাজের বিরাম নাই, সেইরূপ যতদিন না ইষ্টের সহিত সাধকের মিলন হয় ততদিন গুরুর কাজের শেষ নাই। এইরূপে মহামহিমান্বিত শ্রীগুরু জিজ্ঞাসু ভক্তের হাত ধরিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবরাজ্যে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে তাহাকে ইষ্টমূর্তির সম্মুখে আনিয়া বলেন, ‘ও শিষ্য, ঐ দেখ!’ ইহা বলিয়াই অন্তর্হিত হন।”
“গুরু শেষে ইষ্টে লয় হন; গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব – তিনে এক, একে তিন”
ঠাকুরকে একদিন ঐরূপ বলিতে শুনিয়া একজন অনুগত ভক্ত ‘শ্রীগুরুর সহিত বিচ্ছেদ তবে তো একদিন অনিবার্য’ ভাবিয়া ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করেন – “গুরু তখন কোথায় যান, মশাই?” ঠাকুর তদুত্তরে বলেন, “গুরু ইষ্টে লয় হন। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব – তিনে এক, একে তিন।”
তৃতীয় খণ্ড – চতুর্থ অধ্যায়: গুরুভাবের পূর্ববিকাশ
বাল্যাবস্থা হইতেই গুরুভাবের পরিচয় ঠাকুরের জীবনে পাওয়া যায়
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
– গীতা, ৯।১১
ঠাকুরের ভিতরে গুরুভাবের প্রকাশ বাল্যাবধিই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যৌবনে নির্বিকল্প-সমাধিলাভের পর ঐ ভাবের যে পূর্ণ বিকাশ, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। বাল্যাবধি তাঁহাতে ঐ ভাবের প্রকাশ বলাতে কেহ না মনে করেন, আমরা ঠাকুরকে বাড়াইবার জন্য কথাটি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি। যথার্থ নিরপেক্ষভাবে যদি কেহ ঠাকুরের জীবন আলোচনা করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, ঐ দোষে কখনই তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হইবে না। এ অদ্ভুত অলৌকিক জীবনের ঘটনাবলী যিনি যতদূর পারেন বিচার করিয়া দেখুন না কেন, দেখিবেন বিচারশক্তিই পরিশেষে হার মানিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে! আমাদের মনও বড় কম সন্দিগ্ধ ছিল না; আমাদের ভিতরের অনেকেই ঠাকুরকে যে ভাবে যাচাইয়া বাজাইয়া লইয়াছেন ঐরূপ করিতে এখনকার কাহারও মন-বুদ্ধিতে উঠিবেই না বলিয়া আমাদের বোধ হয়। ঐরূপে ঠাকুরকে সন্দেহ করা এবং পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজেই পরাজিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হওয়া আমাদের ভিতর কতবার কত লোকেরই ভাগ্যে যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ‘লীলাপ্রসঙ্গে’ ঐ বিষয়ের আভাস আমরা পূর্বেই পাঠককে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়াছি, পরে আরও অনেক দিতে হইবে। পাঠক তখন নিজেই বুঝিয়া লইবেন; এজন্য এ বিষয়ে এখন আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।
“আগে ফল, তারপর ফুল।” সকল অবতারপুরুষের জীবনেই ঐ ভাব
“আগে ফল, তারপর ফুল – যেমন লাউ-কুমড়ার” – ঠাকুর এ কথাটি নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটিদের জীবনপ্রসঙ্গে সর্বদাই ব্যবহার করিতেন। অর্থ – ঐরূপ পুরুষেরা জগতে আসিয়া কোন বিষয়ে সিদ্ধ হইবার জন্য যাহা কিছু সাধন করেন, তাহা কেবল ইতর-সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য যে, ঐ বিষয়ে ঐরূপ ফললাভ করিতে হইলে এইরূপ চেষ্টা তাহাদের করিতে হইবে। কারণ ঐরূপ পুরুষদিগের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহারা এতটা চেষ্টা জীবনে দেখান, সেই জ্ঞান আজীবন থাকিলে সকল কার্য যেরূপভাবে করা যায়, ঐসকল পুরুষেরা বাল্যাবধি ঠিক তদ্রূপ ব্যবহারই সর্বত্রই সকল বিষয়ে করিয়া আসিয়াছেন। যেন ঐ জ্ঞানলাভ করিবার ফল তাঁহারা পূর্ব হইতেই নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছেন। নিত্যমুক্তদিগের সম্বন্ধেই যখন ঐ কথা সত্য, তখন ঈশ্বরাবতারদের তো কথাই নাই। তাঁহাদের জীবনে ঐরূপ জ্ঞানের প্রকাশ আজীবনই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেশের সকল যুগের ঈশ্বরাবতারদের সম্বন্ধেই শাস্ত্র একথা সত্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের ঈশ্বরাবতারদিগের অনেক ব্যবহারের মধ্যে একটা সৌসাদৃশ্য আছে। যথা – স্পর্শদ্বারা ধর্মজীবন-সঞ্চারের কথা যীশু, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের জীবনেই দেখিতে পাই। ঐরূপ, তাঁহাদের জন্মগ্রহণকালে বিশেষ বিশেষ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির ঐ বিষয় অলৌকিক উপায়ে জ্ঞাত হইবার কথা, বাল্যাবধি তাঁহাদের ভিতর গুরুভাব প্রকাশিত থাকিবার কথা, তাঁহারা যে মানবসাধারণকে উন্নত করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ পথ দেখাইতে কৃপায় অবতীর্ণ, এ বিষয়টি বাল্যাবধি উপলব্ধি করিবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাই একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ঠাকুরের জীবনে বাল্যাবধি গুরুভাব প্রভৃতির প্রকাশ থাকার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কারণ ‘অবতার’-পুরুষদিগের থাক বা শ্রেণীই একটা পৃথক। সাধারণ মানবের জীবনে ঐরূপ ঘটনা কখনও সম্ভবে না বলিয়া অবতারপুরুষদিগের জীবনেও ঐরূপ হওয়া অসম্ভব মনে করিলে বিষম ভ্রমে পড়িতে হইবে।
ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের প্রথমবিকাশ – কামারপুকুরে
ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের প্রথম জ্বলন্ত নিদর্শন দেখিতে পাই তাঁহার জন্মভূমি কামারপুকুরে। তাঁহার তখন উপনয়ন হইয়া গিয়াছে; অতএব বয়স ৯।১০ বৎসর হইবে।
লাহাবাবুদের বাটীতে পণ্ডিত-সভায় শাস্ত্র-বিচার
গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাটীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদঞ্চলের খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের নিমন্ত্রণ হয় এবং অনেক পণ্ডিতের একত্র সমাবেশ হইলে যাহা হইয়া থাকে – খুব তর্কের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। অনেক তর্কেও শাস্ত্রীয় প্রশ্নবিশেষের কোনরূপ মীমাংসা হইতেছিল না, এমন সময়ে বালক শ্রীরামকৃষ্ণ বা গদাধর পরিচিত জনৈক পণ্ডিতকে বলেন, “কথাটার এই ভাবে মীমাংসা হয় না কি?” সভায় পল্লীর অনেক বালকই কৌতূহলাকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিল এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া পণ্ডিতদিগের উচ্চরবে বাগ্যুদ্ধটার বিন্দুমাত্র অর্থবোধ না হওয়ায় কেহ বা উহাকে একটা রঙ্গরসের মধ্যে ভাবিয়া হাসিতেছিল, কেহ বা বিরক্ত হইয়া পণ্ডিতদিগের অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ করিয়া সোরগোল করিতেছিল, আবার কেহ বা একেবারে অন্যমনা হইয়া আপনাদের ক্রীড়াতেই মন দিয়াছিল। কাজেই এ অপূর্ব বালক যে পণ্ডিতদিগের সকল কথা ধৈর্যসহকারে শুনিয়াছে, বুঝিয়াছে এবং মনে ভাবিয়া একটা সুমীমাংসায় উপনীত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া পণ্ডিতটি প্রথম অবাক হইলেন; তাহার পর নিজের পরিচিত পণ্ডিতদের নিকট গদাধরের মীমাংসার কথা বলিতে লাগিলেন; তাহার পর তাঁহারা সকলে উহাই ঐ বিষয়ের একমাত্র মীমাংসা বুঝিয়া অপরাপর সকল পণ্ডিতকে ঐ বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন। তখন ঐ প্রশ্নের উহাই যে একমাত্র সমাধান তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন এবং কাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঐ অপূর্ব সমাধান প্রথম দেখিতে পাইল, তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; এবং যখন নিশ্চিত জানিতে পারিলেন, উহা বালক গদাধরই করিয়াছে, তখন কেহ বা স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া বালককে দৈবশক্তিসম্পন্ন ভাবিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, আবার কেহ বা আনন্দপূরিত হইয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন!
ঈশার জীবনে ঐরূপ ঘটনা। জেরুজালেমের য়্যাভে-মন্দির
কথাটির আর একটু আলোচনা আবশ্যক। ক্রিশ্চান ধর্ম-প্রবর্তক ভগবদবতার ঈশার জীবনেও ঠিক এইরূপ একটি কথা বাইবেলে1 লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন দ্বাদশবর্ষ। তাঁহার দরিদ্র ধর্মপরায়ণ পিতামাতা ইয়ুসুফ ও মেরি সে বৎসর তাঁহাকে লইয়া অন্যান্য যাত্রীদের সহিত পদব্রজে নিজেদের বাসভূমি গ্যালিলি প্রদেশস্থ নাজারেথ্ নামক গণ্ডগ্রাম হইতে জেরুজালেম তীর্থের সুবিখ্যাত মন্দিরে দেবদর্শন ও পূজা বলি ইত্যাদি দিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। ইহুদিদিগের এই তীর্থ হিন্দুদিগের তীর্থসকলের ন্যায়ই ছিল। এখানে সুবর্ণকৌটায় য়াভে দেবতার আবির্ভাব ভক্ত-সাধক প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত; এবং উহার সম্মুখে একটি বেদীর উপর ধূপ-ধুনা জ্বালাইয়া পত্র-পুষ্প-ফল-মূল ও মেষ পায়রা প্রভৃতি পশু-পক্ষ্যাদি বলি দিয়া উক্ত দেবতার পূজা করিত। হিন্দুদিগের ৺কামাখ্যা পীঠ ও ৺বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি তীর্থে অদ্যাপি পায়রা প্রভৃতি পক্ষী বলি দেওয়া এখনো প্রচলিত।
1. লুক্, ২-৪২
সেকালের য়্যাহুদী তীর্থযাত্রী
ইয়ুসুফ ও মেরি শাস্ত্রানুসারে দর্শন, পূজা, বলি ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সঙ্গীদিগের সহিত নিজ গ্রামাভিমুখে ফিরিলেন। সে সময়ে নানা দিগ্দেশ হইতে জেরুজালেমদর্শনে আগত যাত্রীদিগের অবস্থা অনেকটা, রেল হইবার পূর্বে পদব্রজে ৺পুরী প্রভৃতি তীর্থদর্শনে অগ্রসর যাত্রীদিগের মতোই ছিল। সেই মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-কূপ-তড়াগাদিশোভিত একই প্রকার দীর্ঘ পথ, সেই মধ্যে মধ্যে বিশ্রামস্থান, চটী বা সরাই – ধর্মশালারও অভাব ছিল না শুনা যায় – সেই তীর্থযাত্রীর সহচর পাণ্ডা, সেই চাল-ডাল-আটা প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যকীয় খাদ্যাদিদ্রব্য-প্রাপ্তিস্থান মুদির দোকান, সেই ধূলা, সেই ধর্মভাববিস্মরণকারী নিদ্রালস্যের বৈরী যাত্রীদিগের পরমবন্ধু মশককুল, সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের যাত্রিবর্গের দস্যু-তস্করাদি হইতে পরস্পরের সাহায্যলাভ করিতে পারিবে বলিয়া দলবদ্ধ হইয়া গমন এবং পরিশেষে সেই যাত্রীদিগের একান্ত ঈশ্বরনির্ভরতা ও ভগবদ্ভক্তি।
য়্যাভে-মন্দিরে ঈশার শাস্ত্রব্যাখ্যা
ঈশার পিতা-মাতা আপন দলের সহিত প্রত্যাবর্তনের সময় ঈশাকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, বোধ হয় অপর কোন যাত্রীবালকের সহিত দলের পশ্চাতে আসিতেছে। কিন্তু অনেক দূর চলিয়া আসিয়াও যখন ঈশাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন বিশেষ ভাবিত হইয়া তন্নতন্ন করিয়া দলমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন ঈশা তাঁহাদের সঙ্গে নাই। কাজেই ব্যাকুল হইয়া পুনরায় জেরুজালেম-অভিমুখে ফিরিলেন। সেখানে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখেন বালক ঈশা শাস্ত্রজ্ঞ সাধককুলের ভিতর বসিয়া শাস্ত্রবিচার করিতেছে এবং শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নসকলের (যাহা পণ্ডিতেরাও সমাধান করিতে পারিতেছেন না) অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মোহিত করিতেছে।
পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মত খণ্ডন
পণ্ডিত মোক্ষমূলর তৎকৃত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত বাল্যলীলার সহিত ঈশার বাল্যলীলার সৌসাদৃশ্য পাইয়া ঐ বিষয়ের সত্যতায় বিশেষ সন্দিহান হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, একটু কটাক্ষ করিয়াও বলিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ইংরাজীবিদ্যাভিজ্ঞ শিষ্যেরা গুরুর মান বাড়াইবার জন্য ঈশার বাল্যলীলার কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ইচ্ছা করিয়াই জুড়িয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত ঐরূপে আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও আমরা নাচার, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের ঐরূপ বাল্যলীলার কথা আমরা ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরের অনেক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি এবং ঠাকুরও কখনো কখনো ঐ বিষয় আমাদের কাহারও কাহারও নিকট নিজমুখে বলিয়াছেন। এই পর্যন্ত বলিয়াই এখানে ক্ষান্ত থাকা ভাল।
ঠাকুর বিবাহ করিলেন কেন? আত্মীয়দিগের অনুরোধে? – না
ঠাকুরের জীবনালোচনা করিতে যাইয়া সকলেরই মনে হয় – ঠাকুর বিবাহিত হইলেন কেন? স্ত্রীর সহিত যাঁহার কোনকালেই শরীরসম্বন্ধ রাখিবার সঙ্কল্প ছিল না, তিনি কেন বিবাহ করিলেন, ইহার কারণ বাস্তবিকই খুঁজিয়া পাওয়া ভার। যদি বল, যৌবনে পদার্পণ করিয়াই ঠাকুর ‘ভগবান’ ‘ভগবান’ করিয়া উন্মাদপ্রায় হইলেন বলিয়াই আত্মীয়েরা জোর করিয়া বিবাহ দিলেন, তদুত্তরে আমরা বলি ওটা একটা কথাই নয়। জোর করিয়া একটা ছোট কাজও তাঁহাকে বাল্যাবধি কেহ করাইতে পারে নাই। যখন যাহা করিবেন মনে করিয়াছেন, তাহা কোন না কোনও উপায়ে নিশ্চিত সাধিত করিয়াছেন। উপনয়নকালে ধনী নাম্নী জনৈকা কামারজাতীয়া কন্যাকে ভিক্ষামাতা করাতেই দেখ না। কামারপুকুরে কলিকাতার ন্যায় সমাজবন্ধন শিথিল ছিল না যে, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে; ঠাকুরের পিতামাতাও কম স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন না, বংশগত প্রথাও ছিল – কোন না কোনও ব্রাহ্মণকন্যাকে ভিক্ষামাতারূপে নির্দিষ্ট করা এবং বালক গদাধরের অভিভাবকদিগের সকলেই বালকের কামারকন্যার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষাগ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তথাপি কেবলমাত্র গদাধরের নির্বন্ধে ধনীর ভিক্ষামাতা হওয়া সাব্যস্ত হইল – ইহা একটি কম আশ্চর্যের বিষয় নহে! এইরূপে সকল ঘটনায় যখন দেখিতে পাই, ঠাকুরের ইচ্ছা ও কথাই সকল বিষয়ে অপর সকলের বিপরীত ভাব ও ইচ্ছাকে চিরকাল ফিরাইয়া দিয়াছে, তখন কেমন করিয়া বলি তাঁহার জীবনের অত বড় ঘটনাটা আত্মীয়দিগের ইচ্ছা ও অনুরোধের জোরে হইয়াছে?
ভোগবাসনা ছিল বলিয়া? – না
আবার, যদি বল ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে সর্বস্বত্যাগের ভাবটা যে ঠাকুরের আজীবন ছিল, এ কথাটা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? ঐ কথাটা স্বীকার না করিয়া যদি বল যে, মানবসাধারণের ন্যায় ঠাকুরেরও বিবাহাদি করিয়া সংসারসুখভোগ করিবার ইচ্ছাটা প্রথম প্রথম ছিল, কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তাঁহার মনের গতির হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্তন আসিয়া পড়িল; সংসার-বৈরাগ্য ও ঈশ্বরানুরাগের একটা প্রবল ঝটিকা তাঁহার প্রাণে বহিয়া তাঁহাকে এমন আত্মহারা করিয়া ফেলিল যে, তাঁহার পূর্বেকার বাসনাসমূহ একেবারে চিরকালের মতো কোথায় উড়িয়া যাইল। ঠাকুরের বিবাহটা ঐ বিরাগ-অনুরাগের ঝড়টা বহিবার আগেই হইয়াছিল বলিলেই তো সকল কথা মিটিয়া যায়! আমরা বলি – কথাটি আপাততঃ বেশ যুক্তিযুক্ত বোধ হইলেও তৎসম্বন্ধে কতকগুলি অখণ্ডনীয় আপত্তি আছে। প্রথম – চব্বিশ বৎসর বয়সে ঠাকুরের বিবাহ হয়, তখন বৈরাগ্যের ঝড় তাঁহার প্রাণে তুমুল বহিতেছে। আর, আজীবন যিনি নিজের জন্য কাহাকেও এতটুকু কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হইতেন, তিনি যে কিছুমাত্র না ভাবিয়া একজন পরের মেয়ের চিরকাল দুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা বুঝিয়াও ঐ কার্যে অগ্রসর হইলেন, ইহা হইতেই পারে না। দ্বিতীয় – ঠাকুরের জীবনের কোন ঘটনাই যে নিরর্থক হয় নাই, একথা আমরা যতই বিচার করিয়া দেখি ততই বুঝিতে পারি। তৃতীয় – তিনি ইচ্ছা করিয়াই যে বিবাহ করিয়াছিলেন ইহা সুনিশ্চিত; কারণ বিবাহের পাত্রী অনুসন্ধানকালে নিজের ভাগিনেয় হৃদয় ও বাটীর অন্যান্য সকলকে বলিয়া দেন যে, তাঁহার বিবাহ জয়রামবাটীনিবাসী শ্রীযুত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত হইবে – ইহা পূর্ব হইতে স্থির আছে।
বিবাহের পাত্রী-অন্বেষণের সময় ঠাকুরের কথা – “কুটো বেঁধে রাখা আছে, দেখ্ গে যা।” অতএব স্বেচ্ছায় বিবাহ করা
কথাটি শুনিয়া পাঠক অবাক হইবে, অথবা অবিশ্বাস করিয়া বলিবে – “কেবলই অদ্ভুত কথার অবতারণা! বিংশ শতাব্দীতে ও-সকল কথা কি চলে?” তদুত্তরে আমাদের বলিতে হয়, “তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর বাপু, কিন্তু ঘটনা বাস্তবিকই ঐরূপ হইয়াছিল। এখনও অনেকে বাঁচিয়া আছেন যাঁহারা ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখই না কেন?” পাত্রীর অন্বেষণে যখন কোনটিই আত্মীয়দিগের মনোমতো হইতেছিল না, তখন ঠাকুর স্বয়ং বলিয়া দেন “অমুক গাঁয়ের অমুকের মেয়েটি কুটো বেঁধে1 রাখা আছে, দেখগে যা!” অতএব বুঝাই যাইতেছে ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বিবাহ হইবে এবং কোথায় কাহার কন্যার সহিত হইবে। তিনি তাহাতে কোন আপত্তিও করেন নাই। অবশ্য ঐরূপ জানিতে পারা তাঁহার ভাবসমাধিকালেই হইয়াছিল।
1. পাড়াগাঁয়ে প্রথা আছে, শশা প্রভৃতি গাছের যে ফলটি ভাল বুঝিয়া ভগবানের ভোগ দিবে বলিয়া কৃষক মনে করে, স্মরণ রাখিবার জন্য সেটিতে একটি কুটো বাঁধিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখে। ঐরূপ করায় কৃষক নিজে বা তাহার বাটীর আর কেহ সেটি ভুলক্রমে তুলিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলে না। ঠাকুর ঐ প্রথা স্মরণ করিয়াই ঐ কথা বলেন। অর্থ – অমুকের মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে একথা পূর্ব হইতে স্থির হইয়া আছে অথবা অমুক কন্যাটি তাঁহার বিবাহের পাত্রীস্বরূপে দৈবকর্তৃক রক্ষিতা আছে।
প্রারব্ধ কর্ম-ভোগের জন্যই কি ঠাকুরের বিবাহ?
তবে ঠাকুরের বিবাহ হইবার অর্থ কি? শাস্ত্রজ্ঞ কোন পাঠক এইবার হয়তো বিরক্ত হইয়া বলিবেন – তুমি তো বড় অর্বাচীন হে! সামান্য কথাটা লইয়া এত গোল করিতেছ? শাস্ত্র-টাস্ত্র একটু-আধটু দেখিয়া সাধু-মহাপুরুষের জীবনের ঘটনা লিখিতে কলম ধরিতে হয়। শাস্ত্র বলেন – ঈশ্বরদর্শন বা পূর্ণজ্ঞান হইলে জীবের সঞ্চিত ও আগামী কর্মের ক্ষয় হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ভোগ জীবকে জ্ঞানলাভ হইলেও এই দেহে করিতে হয়। একটা ব্যাধের পিঠে-বাঁধা তূণে কতকগুলি তীর রহিয়াছে, হাতে একটি তীর এখনি ছুঁড়িবে বলিয়া লইয়াছে, আর একটি তীর বৃক্ষোপরি একটি পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া সে এইমাত্র ছুঁড়িয়াছে। এমন সময় ধর, ব্যাধের মনে হঠাৎ বৈরাগ্যের উদয় হইয়া সে ভাবিল আর হিংসা করিবে না। হাতের তীরটি সে ফেলিয়া দিল, পিঠের তীরগুলিও ঐরূপে ত্যাগ করিল, কিন্তু যে তীরটি সে পাখিটাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল সেটাকে কি আর ফিরাইতে পারে? পিঠের তীরগুলি যেন তাহার জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম, আর হাতের তীরটি আগামী কর্ম বা যে কর্মসকলের ফল সে এইবার ভোগ করিবে – ঐ উভয় কর্মগুলি জ্ঞানলাভে নাশ হয়। কিন্তু তাহার প্রারব্ধ কর্মগুলি হইতেছে – যে তীরটি সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে তাহার মতো, তাহাদের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় মহাপুরুষেরা কেবল প্রারব্ধ কর্মসকলের ভোগই শরীরে করিয়া থাকেন। ঐ ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী; এবং তাঁহারা বুঝিতে বা জানিতেও পারেন যে, তাঁহাদের প্রারব্ধ অনুসারে তাঁহাদের জীবনে কিরূপ ঘটনাবলী আসিয়া উপস্থিত হইবে। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপে নিজ বিবাহ কোন্ পাত্রীর সহিত কোথায় হইবে, তাহা বলিয়া দেওয়াটা কিছু বিচিত্র নহে।
না – যথার্থ জ্ঞানী পুরুষের প্রারব্ধ ভোগ করা-না-করা ইচ্ছাধীন
ঐ কথার উত্তরে আমরা বলি – অবশ্য শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিকই নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কিন্তু যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে যথার্থজ্ঞানী পুরুষকে প্রারব্ধ কর্মসকলেরও ফলভোগ করিতে হয় না। কারণ সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিবে যে মন, সে মন যে তিনি চিরকালের নিমিত্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছেন – তাহাতে আর সুখ-দুঃখাদির স্থান কোথা? তবে যদি বল – তাঁহার শরীরটায় প্রারব্ধ ভোগ হয়, তাহাই বা কিরূপে হইবে? তিনি যদি ইচ্ছা করিয়া অল্পমাত্র আমিত্ব কোন বিশেষ কারণে – যথা, পরোপকারাদির নিমিত্ত – রাখিয়া দেন, তবেই তাঁহার আবার শরীরমনের উপলব্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধ কর্মের ভোগ হয়। অতএব যথার্থজ্ঞানী পুরুষ ইচ্ছা হইলে প্রারব্ধ ভোগ বা ত্যাগ করিতে পারেন; তাঁহাদের ঐরূপ ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্যই তাঁহাদিগকে ‘লোকজিৎ’, ‘মৃত্যুঞ্জয়’, ‘সর্বজ্ঞ’ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।
ঠাকুরের তো কথাই নাই; কারণ তাঁহার কথা – “যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ”
আর এক কথা – শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজের অনুভব যদি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাকে আর জ্ঞানী পুরুষ বলা চলে না; ঐ শ্রেণীমধ্যেই তাঁহাকে আর স্থান দিতে পারা যায় না। কেন না, তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি, “যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ”, অর্থাৎ যিনি পূর্বে রামরূপে এবং কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে বর্তমান থাকিয়া অপূর্ব লীলার বিস্তার করিতেছেন! কথাটি বিশ্বাস করিলে তাঁহাকে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব ঈশ্বরাবতার বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর ঐরূপ করিলে, তাঁহাকে প্রারব্ধাদি কোন কর্মেরই বশীভূত আর বলা চলে না। অতএব ঠাকুরের বিবাহ সম্বন্ধে অন্যপ্রকার মীমাংসাই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি এবং তাহাই এখানে বলিব।
বিবাহের কথা লইয়া ঠাকুরের রঙ্গরস
বিবাহের কথা আমাদের নিকট উত্থাপন করিয়া ঠাকুর অনেক সময় রঙ্গরসও করিতেন। উহাও বড় মধুর। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন মধ্যাহ্নে ভোজন করিতে বসিয়াছেন; নিকটে শ্রীযুত বলরাম বসু ও অন্যান্য কয়েকটি ভক্ত বসিয়া তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতেছেন। সেদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কামারপুকুরে যাত্রা করিয়াছেন কয়েক মাসের জন্য, কারণ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের বিবাহ।
ঠাকুর – (বলরামবাবুকে লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা, আবার বিয়ে কেন হলো বল দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্য হলো? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই – আবার স্ত্রী কেন?
বলরাম ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া আছেন।
ঠাকুর – ওঃ বুঝেছি; (থাল হইতে একটু ব্যঞ্জন তুলিয়া ও বলরামকে দেখাইয়া) এই – এর জন্যে হয়েছে। নইলে কে আর এমন করে রেঁধে দিত বল? (বলরামবাবু প্রভৃতি ভক্তগণের হাস্য) হাঁ গো, কে আর এমন করে খাওয়াটা দেখত। ওরা সব আজ চলে গেল – (ভক্তেরা কে চলিয়া গেল বুঝিতে না পারায়) রামলালের খুড়ী গো; রামলালের বিয়ে হবে – তাই সব কামারপুকুরে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, কিছুই মনে হলো না! সত্যি বলছি; যেন কে তো কে গেল! কিন্তু তারপর কে রেঁধে দেবে বলে ভাবনা হলো। কি জান? – সব রকম খাওয়া তো আর পেটে সয় না, আর সব সময় খাওয়ার হুঁশও থাকে না। ও (শ্রীশ্রীমা) বোঝে কি রকম খাওয়া সয়; এটা ওটা করে দেয়; তাই মনে হলো – কে করে দেবে!
দশ-প্রকারের সংস্কার পূর্ণ করিবার জন্যই সাধারণ আচার্যদিগের বিবাহ করা। ঠাকুরের বিবাহও কি সেজন্য? – না
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলেন, “বিয়ে করতে কেন হয় জানিস? ব্রাহ্মণশরীরের দশ রকম সংস্কার আছে – বিবাহ তারই মধ্যে একটা। ঐ দশ রকম সংস্কার হলে তবে আচার্য হওয়া যায়।” আবার কখনো কখনো বলিতেন, “যে পরমহংস হয়, পূর্ণ জ্ঞানী হয়, সে হাড়ী-মেথরের অবস্থা থেকে রাজা, মহারাজা, সম্রাটের অবস্থা পর্যন্ত সব ভুগে দেখে এসেছে। নইলে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য আসবে কেন? যেটা দেখেনি (ভোগ করেনি), মন সেইটে দেখতে চাইবে ও চঞ্চল হবে – বুঝলে? ঘুঁটিটা সব ঘর ঘুরে তবে চিকে ওঠে – খেলার সময় দেখনি? সেই রকম।”
ধর্মাবিরুদ্ধ ভোগসহায়ে ত্যাগে পৌঁছাইবার জন্যই হিন্দুর বিবাহ
সাধারণ গুরুদিগের বিবাহ করিবার ঐরূপ কারণ ঠাকুর নির্দেশ করিলেও, ঠাকুরের নিজের বিবাহের বিশেষ কারণ যাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই এখন বলিব। বিবাহটা ভোগের জন্য নয় – একথা শাস্ত্র আমাদের প্রতি পদে শিক্ষা দিতেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টিরক্ষারূপ নিয়ম-প্রতিপালন ও গুণবান পুত্র উৎপাদন করিয়া সমাজের কল্যাণসাধন করাই হিন্দুর বিবাহরূপ কর্মটার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত – শাস্ত্র বার বার এই কথাই আমাদের বলিয়া দিতেছেন। তবে কি উহাতে তাহার নিজ স্বার্থ কিছুমাত্র থাকিবে না – শাস্ত্র এইরূপ অসম্ভব কথা বলেন? না, তাহা নহে। শাস্ত্রকার ঋষিগণ দুর্বল মানবচরিত্রের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে দুর্বল মানব স্বার্থ ভিন্ন এ জগতে আর কোন কথাই বুঝে না; লাভ-লোকসান না খতাইয়া অতি সামান্য কার্যেও অগ্রসর হয় না। শাস্ত্রকার ঐ কথা বুঝিয়াও যে পূর্বোক্ত আদেশ করিয়াছেন তাহার কারণ – তিনি এ কথাও বুঝিয়াছেন যে, ঐ স্বার্থটাকে যদি একটা মহান উদ্দেশ্যের সহিত সর্বদা জড়িত রাখিতে পারে তবেই মঙ্গল; নতুবা মানবকে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে পড়িয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হইবে। নিজের নিত্য-মুক্ত আত্মস্বরূপ ভুলিয়াই মানব ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহ্যজগতের রূপরসাদি ভোগের নিমিত্ত ছুটিতেছে; আর, মনে করিতেছে – ঐসকল বড়ই মধুর, বড়ই মনোরম!
বিচার-সংযুক্ত ভোগ করিতে করিতে কালে বোধ হয় – ‘দুঃখের মুকুট পরিয়া সুখ আসে’
কিন্তু জগতের প্রত্যেক সুখটাই যে দুঃখের সঙ্গে চিরসংযুক্ত, সুখটা ভোগ করিতে গেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখটাও লইতে হইবে – এ কথা কয়টা লোক ধরিতে বা বুঝিতে পারে? শ্রীযুত বিবেকানন্দ স্বামীজী বলিতেন, “দুঃখের মুকুট মাথায় পরে সুখ এসে মানুষের কাছে দাঁড়ায়” – মানুষ তখন সুখকে লইয়াই ব্যস্ত! তাহার মাথায় যে দুঃখের মুকুট, উহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলে পরিণামে যে দুঃখটাকেও লইতে হইবে – এ কথা তখন সে আর ভাবিবার অবসর পায় না! শাস্ত্র সেজন্য তাহাকে ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন, ‘ওরে, সুখলাভটাই নিজের স্বার্থ – এ কথা মনে করিস কেন? সুখ বা দুঃখের একটা লইতে গেলে যে অপরটাকেও লইতে হইবে! স্বার্থটাকে একটু উচ্চ সুরে বাঁধিয়া ভাব না যে, সুখটাও আমার শিক্ষক, দুঃখটাও আমার শিক্ষক; আর যাহাতে ঐ দুয়ের হস্ত হইতে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্রাণ পাওয়া যায় – তাহাই আমার স্বার্থ বা জীবনের উদ্দেশ্য’। অতএব বুঝা যাইতেছে – বিবাহিত জীবনে বিচারসংযুক্ত ভোগের দ্বারা এবং সুখদুঃখপূর্ণ নানা অবশ্যম্ভাবী অবস্থার অনুভবের দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর সংসারের সকল আপাতসুখের উপর বিরক্ত হইয়া যাহাতে জীব ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে পূর্ণ হয় এবং তাঁহাকেই সারাৎসার জানিয়া তাঁহার দর্শনলাভের দিকে মহোৎসাহে অগ্রসর হয়, ইহা শিক্ষা দেওয়াই শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য।
ভোগসুখ ত্যাগ করিতে করিতে মনকে কি ভাবে বুঝাইতে হয়, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ
বিচার করিতে করিতে সংসারের কোন বিষয়টা ভোগ করিতে যাইলেই যে মন ঐ বিষয় ত্যাগ করিবে এ কথা নিশ্চিত; এজন্যই ঠাকুর বলিতেন, “ওরে, সদসদ্বিচার চাই। সর্বদা বিচার করে মনকে বলতে হয় যে, মন তুমি এই জিনিসটা ভোগ করবে, এটা খাবে, ওটা পরবে বলে ব্যস্ত হচ্ছ – কিন্তু যে পঞ্চভূতে আলু পটল চাল ডাল ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, সেই পঞ্চভূতেই আবার সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি তৈরি হয়েছে; যে পঞ্চভূতের হাড়-মাংস রক্ত-মজ্জায় নারীর সুন্দর শরীর হয়েছে, তাহাতেই আবার তোমার, সকল মানুষের ও গরু ছাগল ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীরও শরীর হয়েছে; তবে কেন ওগুলো পাবার জন্য এত হাঁই-ফাঁই কর? ওতে তো আর সচ্চিদানন্দলাভ হবে না! তাতেও যদি না মানে তো বিচার করতে করতে দু-একবার ভোগ করে সেটাকে ত্যাগ করতে হয়। যেমন ধর, রসগোল্লা খাবে বলে মন ভারি ধরেছে, কিছুতেই আর বাগ মানচে না – যত বিচার করচ সব যেন ভেসে যাচ্চে; তখন কতকগুলো রসগোল্লা এনে এগাল ওগাল করে চিবিয়ে খেতে খেতে মনকে বলবি – মন, এরই নাম রসগোল্লা; এ-ও আলু-পটলের মতো পঞ্চভূতের বিকারে তৈয়ারি হয়েছে; এ-ও খেলে শরীরে গিয়ে রক্ত-মাংস-মল-মূত্র হবে; যতক্ষণ গালে আছে ততক্ষণই এটা মিষ্টি – গলার নিচে নাবলে আর ঐ আস্বাদের কথা মনে থাকবে না, আবার বেশি খাও তো অসুখ হবে; এর জন্য এত লালায়িত হও! ছি ছি! – এই খেলে, আর খেতে চেও না। (সন্ন্যাসী ভক্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া) সামান্য সামান্য বিষয়গুলো এই রকম করে বিচারবুদ্ধি নিয়ে ভোগ করে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু বড় বড়গুলোতে ও রকম করা চলে না, ভোগ করতে গেলেই বন্ধনে পড়ে যেতে হয়। সেজন্য বড় বড় বাসনাগুলোকে বিচার করে, তাতে দোষ দেখে, মন থেকে তাড়াতে হয়।”
বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্যপালন করিবার প্রথার উচ্ছেদ হওয়াতেই হিন্দুর বর্তমান জাতীয় অবনতি
শাস্ত্র বিবাহের ঐরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য উপদেশ করিলেও কয়টা লোকের মনে সে কথা আজকাল স্থান পায়? কয়জন বিবাহিত জীবনে যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া আপনাদিগকে এবং জনসমাজকে ধন্য করিয়া থাকেন? কয়জন স্ত্রী স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে লোকহিতকর উচ্চব্রতে – ঈশ্বরলাভের কথা দূরে থাকুক – প্রেরণা দিয়া থাকেন? কয়জন পুরুষই বা ‘ত্যাগই জীবনের উদ্দেশ্য’ জানিয়া স্ত্রীকে তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন? হায় ভারত! পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব জড়বাদ ধীরে ধীরে তোমার অস্থি-মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে কি মেরুদণ্ডহীন পশুবিশেষে পরিণত করিয়াছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! সাধে কি আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সন্ন্যাসি-ভক্তদিগকে বর্তমান বিবাহিত জীবনে দোষ দেখাইয়া বলিতেন, “ওরে, (ভোগটাকে সর্বস্বজ্ঞান বা জীবনের উদ্দেশ্য করাই যদি দোষ হয়, তবে বিবাহের সময়) একটা ফুল ফেলে সেটা করলেই কি শুদ্ধ হয়ে গেল – তার দোষ কেটে গেল?” বাস্তবিক বিবাহিত জীবনে ইন্দ্রিয়পরতা আর কখনো ভারতে এত প্রবল হইয়াছিল কি না সন্দেহ। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ভিন্ন বিবাহের যে অপর একটা মহাপবিত্র, মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে – একথা আমরা আজকাল একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি, আর দিন দিন ঐ কারণে পশুরও অধম হইতে বসিয়াছি! নব্য ভারত-ভারতীর ঐ পশুত্ব ঘুচাইবার জন্যই লোকগুরু ঠাকুরের বিবাহ। তাঁহার জীবনের সকল কার্যের ন্যায় বিবাহরূপ কার্যটাও লোককল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত।
নিজে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া ঐ আদর্শ পুনরায় প্রচলনের জন্যই ঠাকুরের বিবাহ
ঠাকুর বলিতেন, “এখানকার যা কিছু করা সে তোদের জন্য। ওরে, আমি ষোল টাং করলে তবে যদি তোরা এক টাং করিস! আর আমি যদি দাঁড়িয়ে মুতি তো তোরা শালারা পাক দিয়ে দিয়ে তাই করবি।” এই জন্যই ঠাকুরের বিবাহিত জীবনের কর্তব্য ঘাড়ে লইয়া মহোচ্চ আদর্শ সকলের চক্ষুর সম্মুখে অনুষ্ঠান করিয়া দেখান। ঠাকুর যদি স্বয়ং বিবাহ না করিতেন তাহা হইলে গৃহস্থ মানব বলিত, ‘বিবাহ তো করেন নাই, তাই অত ব্রহ্মচর্যের কথা বলা চলিতেছে। স্ত্রীকে আপনার করিয়া এক সঙ্গে একত্র তো বাস কখনো করেন নাই, তাই আমাদের উপর লম্বা লম্বা উপদেশ দেওয়া চলিতেছে।’ সেজন্যই ঠাকুর শুধু যে বিবাহ করিয়াছিলেন মাত্র তাহা নহে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শনলাভের পর যখন দিব্যোন্মাদাবস্থা তাঁহার সহজ হইয়া গেল, তখন পূর্ণযৌবনা বিবাহিতা স্ত্রীকে দক্ষিণেশ্বরে নিজ সমীপে আনাইয়া রাখিলেন, তাঁহাতে জগদম্বার আবির্ভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীষোড়শী মহাবিদ্যাজ্ঞানে পূজা ও আত্মনিবেদন করিলেন, আটমাস কাল নিরন্তর একত্র বাস ও তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন পর্যন্ত করিলেন এবং স্ত্রীর শিক্ষা এবং প্রাণের শান্তি ও আনন্দের জন্য অতঃপর কামারপুকুরে এবং কখনো কখনো শ্বশুরালয় জয়রামবাটীতেও স্বয়ং যাইয়া দুই-এক মাস কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন!
স্ত্রীর সহিত ঠাকুরের শরীরসম্বন্ধ-রহিত অদৃষ্টপূর্ব প্রেম-সম্বন্ধ। শ্রীশ্রীমার ঐ বিষয়ক কথা
দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুর স্ত্রীর সহিত এইরূপে একত্র বাস করেন, তখনকার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীমা এখনো স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিয়া থাকেন, “সে যে কি অপূর্ব দিব্যভাবে থাকতেন, তা বলে বোঝাবার নয়! কখনো ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া – এই রকম, সমস্ত রাত! সে কি এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে! ভাবসমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না; এক দিন তাঁর আর সমাধি ভাঙে না দেখে ভয়ে কেঁদেকেটে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়! তারপর ঐরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে দিলেন – এই রকম ভাব দেখলে এই নাম শুনাবে, এই রকম ভাব দেখলে এই বীজ শুনাবে। তখন আর তত ভয় হতো না, ঐ সব শুনালেই তাঁর আবার হুঁশ হতো। তারপর অনেকদিন এইরূপে গেলেও, কখন তাঁর কি ভাবসমাধি হবে বলে সারা রাত্তির জেগে থাকি ও ঘুমুতে পারি না – এ কথা একদিন জানতে পেরে, নহবতে আলাদা শুতে বললেন।” পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা বলেন, এইরূপে প্রদীপে সলতেটি কি ভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ির প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ি যাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে প্রভৃতি সংসারের সকল কথা হইতে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।
গৃহী মানবের শিক্ষার জন্যই ঠাকুরের ঐরূপ প্রেমলীলাভিনয়
হে গৃহী মানব, কয়জন তোমরা এইভাবে নিজ নিজ স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া থাক? তুচ্ছ শরীরসম্বন্ধটা যদি আজ হইতে কোন কারণে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কয় জন তোমরা স্ত্রীকে ঐরূপে মান্য, ভক্তি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা আজীবন দিতে পার? সেইজন্যই বলি, এ অপূর্ব যুগাবতারের বিবাহ করিয়া, একদিনের জন্যও শরীর-সম্বন্ধ না পাতাইয়া, স্ত্রীর সহিত এই অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব প্রেমলীলার বিস্তার কেবল তোমারই জন্য। তুমিই শিখিতে পারিবে বলিয়া যে – ইন্দ্রিয়পরতা ভিন্ন বিবাহের অপর মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে এবং এই উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যাহাতে তুমিও বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্যের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিয়া স্ত্রী-পুরুষে ধন্য হইতে পার এবং মহামেধাবী, মহাতেজস্বী গুণবান সন্তানের পিতা-মাতা হইয়া ভারতের বর্তমান হীনবীর্য, হতশ্রী, হৃতশক্তিক সমাজকে ধন্য করিতে পার, সেইজন্য। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি রূপে পূর্ব পূর্ব যুগে যে লীলা লোকগুরুদিগের জগৎকে দেখাইবার প্রয়োজন হয় নাই, তাহাই এই যুগে তোমার প্রয়োজনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে প্রদর্শিত হইয়াছে। আজীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা ও সাধনাবলে উদ্বাহবন্ধনের অদৃষ্টপূর্ব পবিত্র ‘ছাঁচ’ জগতে এই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছে। এখন, ঠাকুর যেমন বলিতেন – তোমরা নিজ নিজ জীবন সেই আদর্শ ছাঁচে ফেল, আর নূতনভাবে গঠিত করিয়া তোল।
ঠাকুরের আদর্শে বিবাহিত জীবন গঠন করিতে এবং অন্ততঃ আংশিকভাবেও ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে। নতুবা আমাদের কল্যাণ নাই
‘কিন্তু’ – গৃহমেধিমানব এখনও বলিতেছে – ‘কিন্তু – !’ ওঃ, বুঝিয়াছি; এবং শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সাধন-ভজন সম্বন্ধে যেমন বলিতেন, তাহাই তদুত্তরে বলিতেছি, “তোরা মনে করেছিস বুঝি প্রত্যেকে এক একটা রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি? সে নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতে একটাই হয় – বনে একটা সিঙ্গিই (সিংহ) থাকে।” হে গৃহী-মানব, আমরাও তোমার ‘কিন্তু’র উত্তরে সেইরূপ বলিতেছি – ঠাকুরের ন্যায় স্ত্রীর সহিত বাস করিয়া একেবারে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য রাখা তোমার যে সাধ্যাতীত তাহা ঠাকুর বিলক্ষণ জানিতেন এবং জানিয়াও যে ঐরূপ করিয়া তোমায় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল তুমি অন্ততঃ ‘এক টাং’ বা আংশিকভাবে উহার অনুষ্ঠান করিবে বলিয়া। কিন্তু, জানিও, ঐ উচ্চ আদর্শের অনুষ্ঠান করিয়া যদি তুমি স্ত্রীজাতিকে জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রতিরূপ বলিয়া না দেখিতে এবং হৃদয়ের যথাসাধ্য নিঃস্বার্থ ভালবাসা না দিতে চেষ্টা কর, জগতের মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীমূর্তিসকলকে তোমার ভোগমাত্রৈকসহায়া পরাধীনা দাসী বলিয়া ভাবিয়া চিরকাল পশুভাবেই দেখিতে থাক, তবে তোমার আর গতি নাই; তোমার বিনাশ ধ্রুব এবং অতি নিকটে। শ্রীকৃষ্ণের কথা উপেক্ষা করিয়া যদুবংশের কি হইল, তাহা ভাবিও, ঈশার কথা উপেক্ষা করিয়া ইহুদি জাতিটার কি দুর্দশা, তাহা স্মরণ রাখিও। যুগাবতারকে উপেক্ষা করা সর্বকালেই জাতিসকলের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে।
বিবাহ করিয়া ঠাকুরের শরীর-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ রহিত হইয়া থাকা সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি ও তাহার খণ্ডন
আর একটি প্রশ্নের এখানে উত্তর দিয়াই আমরা উদ্বাহবন্ধনের ভিতর দিয়া ঠাকুরের গুরুভাবের অদৃষ্টপূর্ব বিকাশের কথা সাঙ্গ করিয়া ঐ বিষয়ের অপর কথাসকল বলিব। রূপ-রসাদি বিষয়ের দাস, বহির্মুখ মানবমনে এখনো নিশ্চিত উদয় হইতেছে যে, ঠাকুর যদি বিবাহই করিলেন, তবে একটিও অন্ততঃ সন্তানোৎপাদন করিয়া স্ত্রীর সহিত শরীর-সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে ভাল হইত। ঐরূপ করিলে বোধ হয় ভগবানের সৃষ্টিরক্ষা করাটা যে মানুষমাত্রেরই কর্তব্য, তাহা দেখানো হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রমর্যাদাটাও রক্ষা পাইত। কারণ, শাস্ত্র বলেন – বিবাহিত পত্নীতে অন্ততঃ একটি সন্তানও উৎপাদন করিতে। উহাতে পিতৃ-ঋণের হস্ত হইতে মানবের নিষ্কৃতি হয়। তদুত্তরে আমরা বলি –
প্রথমতঃ, আমরা যতটুকু দেখি, শুনি বা চিন্তা ও কল্পনা করি, সৃষ্টিটা বাস্তবিক কি ততটুকুই? সৃষ্টির নিয়মই বৈচিত্র্য থাকা। আজ এই মুহূর্ত হইতে যদি আমরা সকলে সকল বিষয়ে এক প্রকার চিন্তা ও কার্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তাহা হইলে সৃষ্টি ধ্বংস হইতে আর বড় বিলম্ব হইবে না। তারপর জিজ্ঞাসা করি – সৃষ্টিরক্ষার সকল নিয়মগুলিই কি তুমি জানিয়াছ এবং সৃষ্টিরক্ষা করিতে যাইয়াই কি তুমি আজ ব্রহ্মচর্যবিহীন? বুকে হাত দিয়া উত্তর প্রদান করিও; দেখিও, ঠাকুর যেমন বলিতেন – “ভাবের ঘরে চুরি না থাকে।” আচ্ছা, না হয় ধরিলাম সৃষ্টিরক্ষার ঐ নিয়মটি তুমি পালন করিতেছ। অপরকে ঐরূপ করিতে বলিবার তোমার কি অধিকার আছে? ব্রহ্মচর্য বা উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তিবিকাশের জন্য সাধারণ বিষয়ে শক্তিক্ষয় না করাটাও সৃষ্টি-মধ্যগত একটা নিয়ম। সকলেই যদি তোমার মতো নিম্নাঙ্গের শক্তিবিকাশেই ব্যস্ত থাকিবে, তবে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক শক্তিবিকাশ দেখাইবে কে? ঐরূপ শক্তির বিকাশ তাহা হইলে তো লোপ পাইবে।
দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রের ভিতর হইতে মনের মতো কথাগুলি বাছিয়া লওয়াই আমাদের স্বভাব। সন্তানোৎপাদনবিষয়ক কথাটিও ঐ ভাবেই বাছিয়া লওয়া হয়। কারণ, শাস্ত্র অধিকারিভেদে আবার বলেন, ‘যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ’ – যখনি ভগবানে অনুরাগ বাড়িয়া সংসারে বৈরাগ্যের উদয় হইবে, তখনি সংসার ত্যাগ করিবে। অতএব ঠাকুর যদি তোমার মতে চলিতেন, তাহা হইলে এ শাস্ত্রবচনের মর্যাদাটি রক্ষা করিত কে? পিতৃ-ঋণশোধ করা সম্বন্ধেও ঐ কথা। শাস্ত্র বলেন – যথার্থ সন্ন্যাসী তাঁহার ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ এবং অধস্তন সপ্তপুরুষকে নিজ পুণ্যবলে উদ্ধার করিয়া থাকেন। অতএব ঠাকুরের পিতৃ-ঋণশোধ হইল না ভাবিয়া আমাদের কাতর হইবার প্রয়োজন নাই।
গুরুভাবের প্রেরণাতেই যে ঠাকুরের বিবাহ, তৎপরিচয় শ্রীশ্রীমার ঠাকুরকে জগদম্বাজ্ঞানে আজীবন পূজা করাতেই বুঝা যায়
অতএব বুঝা যাইতেছে, ঠাকুরের জীবনে উদ্বাহবন্ধন কেবল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তই হইয়াছিল। বিবাহিত জীবনের কি উচ্চ, পবিত্র আদর্শ তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় শ্রীশ্রীমার আজীবন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ জগন্মাতাজ্ঞানে পূজা করার কথাতেই বুঝিতে পারা যায়। মানুষ অপর সকলের নিকট আপন দুর্বলতা আবরিত রাখিতে পারিলেও, স্ত্রীর নিকট কখনই উহা লুক্কায়িত রাখিতে পারে না – ইহাই সংসারের নিয়ম। ঠাকুর ঐ বিষয়ে কখনো কখনো আমাদের বলিতেন, “যত সব দেখিস হোমরা-চোমরা বাবু ভায়া – কেউ জজ, কেউ মেজেস্টর, বাইরের যত বোলবোলাও – স্ত্রীর কাছে সব একেবারে কেঁচো, গোলাম! অন্দর থেকে কোন হুকুম এলে, অন্যায় হলেও সেটা রদ করবার কারও ক্ষমতা নেই!” অতএব কাহারও বিবাহিতা পত্নী যদি তাহার পবিত্র, উচ্চ জীবন দেখিয়া তাহাকে অকপটে হৃদয়ের ভক্তি দেয় এবং আজীবন ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝা যায়, সে লোকটা বাহিরে যে আদর্শ দেখায় তাহাতে কিছুমাত্র ভেল নাই। ঠাকুরের সম্বন্ধে সেজন্য ঐ কথা যত নিশ্চয় করিয়া আমরা বলিতে পারি, এমন আর কাহারও সম্বন্ধে নহে। পরিণীতা পত্নীর সহিত ঠাকুরের অপূর্ব প্রেমলীলার অনেক কথা বলিবার থাকিলেও, ইহা তাহার স্থান নহে। সেজন্য এখানে ঐ বিষয়ের ভিতর দিয়া ঠাকুরের অদ্ভুত গুরুভাব-বিকাশের কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিয়াই আমরা ক্ষান্ত রহিলাম।
তৃতীয় খণ্ড – পঞ্চম অধ্যায়: যৌবনে গুরুভাব
গুরু ও নেতা হওয়া মানবের ইচ্ছাধীন নহে
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥
– গীতা, ৭/২৫
ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের বিশেষ বিকাশ আরম্ভ হয় – যেদিন হইতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় ব্রতী হইয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। ঠাকুরের তখন সাধনার কাল – ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদাবস্থা। কিন্তু হইলে কি হয়? যিনি গুরু, তিনি চিরকালই গুরু – যিনি নেতা, তিনি বাল্যকাল হইতেই নেতা। লোকে কমিটি করিয়া পরামর্শ আঁটিয়া যে তাঁহাকে গুরু বা নেতার আসন ছাড়িয়া দেয়, তাহা নহে। তিনি যেমন আসিয়া লোকসমাজে দণ্ডায়মান হন, অমনি মানবসাধারণের মন তাঁহার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হয়। অমনি নতশিরে তাহারা তাঁহার নিকট শিক্ষাগ্রহণ ও তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতে থাকে – ইহাই নিয়ম। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, মানুষ মানুষকে যে নেতা বা গুরু করিয়া তোলে, তাহা নহে, যাঁহারা গুরু বা নেতা হন, তাঁহারা ঐ অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। ‘A leader is always born and never created’ – সেজন্য দেখা যায়, অপর সাধারণে যেসকল কাজ করিলে সমাজ চটিয়া দণ্ডবিধান করে, লোকগুরুরা সেইসকল কাজ করিলেও অবনতশিরে তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া থাকে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছেন –
‘স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।’
– তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই সৎকার্যের প্রমাণ বা পরিমাপক হইয়া দাঁড়ায় এবং লোকে তদ্রূপ আচরণই তদবধি করিতে থাকে। বড়ই আশ্চর্যের কথা, কিন্তু বাস্তবিকই ঐরূপ চিরকাল হইয়া আসিয়াছে এবং পরেও হইতে থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ‘আজ হইতে ইন্দ্রের পূজা বন্ধ হইয়া গোবর্ধনের পূজা হইতে থাকুক’ – লোকে তাহাই করিতে লাগিল! বুদ্ধ বলিলেন, ‘আজ হইতে পশুহিংসা বন্ধ হউক’ অমনি ‘যজ্ঞে হনন করিবার জন্যই পশুগণের সৃষ্টি’, ‘যজ্ঞার্থে পশবো সৃষ্টাঃ’-রূপ নিয়মটি সমাজ পালটাইয়া বাঁধিল! যীশু মহাপবিত্র উপবাসের দিনে শিষ্যদিগকে ভোজন করিতে অনুমতি দিলেন – তাহাই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইল! মহম্মদ বহু বিবাহ করিলেন, তবুও লোকে তাঁহাকে ধর্মবীর, ত্যাগী ও নেতা বলিয়া মান্য করিতে লাগিল! সামান্য বা মহৎ সকল বিষয়েই ঐরূপ – তাঁহারা যাহা বলেন ও করেন, তাহাই সদাচরণের আদর্শ।
লোকগুরুদিগের ভিতরে বিরাট ভাবমুখী আমিত্বের বিকাশ সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়, সাধারণের ঐরূপ হয় না
কেন যে ঐরূপ হয় তাহাও ইতঃপূর্বে আমরা বলিয়াছি – লোকগুরুদিগের ক্ষুদ্র স্বার্থপর ‘আমি’টা চিরকালের মতো একেবারে বিনষ্ট হইয়া তাহার স্থলে বিরাটভাবমুখী ‘আমিত্ব’টার বিকাশ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে ‘আমি’টার দশের কল্যাণ খোঁজাই স্বভাব। আর ফুল ফুটিলে ভ্রমর যেমন আপনিই জানিতে পারিয়া মধুলোভে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়, ফুলকে আর ভ্রমরের নিকট সাদর নিমন্ত্রণ পাঠাইতে হয় না, সেইরূপ যেমনি কাহারও ভিতর ঐ বিরাট ‘আমি’টার বিকাশ হয়, অমনি সংসারে তাপিত লোকসকল আপনিই তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়া শান্তিলাভের নিমিত্ত ছুটিয়া আসে। সাধারণ মানবের ভিতর ঐ বিরাট ‘আমি’টার একটু-আধটু ছিটে-ফোঁটার মতো বিকাশ অনেক কষ্টে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু লোকগুরুদিগের জীবনে বাল্য হইতেই উহার কিছু না কিছু বিকাশ, যৌবনে অধিকতর প্রকাশ এবং পরিশেষে পূর্ণ প্রকাশের অদ্ভুত লীলাসকল দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদিগকে একেবারে অপৃথকভাবে দেখিতে থাকি। কারণ তখন ঐ অমানুষ-ভাবপ্রকাশ তাঁহাদের এত সহজ হইয়া দাঁড়ায় যে, উহা খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, নিঃশ্বাস-ফেলার মতো একটা সাধারণ নিত্যকর্মের মধ্যে হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই সাধারণ মানুষ আর কি করিবে? – দেখে যে, তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থের মাপকাঠি দ্বারা তাঁহাদের দেবচরিত্র মাপা চলে না এবং তজ্জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি-বিশ্বাস ও শরণ গ্রহণ করে।
ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের পূর্ণবিকাশ হইয়া উহা সহজ-ভাব হইয়া দাঁড়ায় কখন
ঠাকুরের জীবনালোচনায়ও আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই – যৌবনে সাধকাবস্থায় দিনের পর দিন ঐ ভাবের ক্রমে ক্রমে বিকাশ হইতে হইতে দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনান্তে ঐ ভাবের পূর্ণ প্রকাশ হইয়া উহা একেবারে সহজভাব হইয়া দাঁড়ায়। তখন কখন যে তিনি কোন্ ‘আমি’-বুদ্ধিতে রহিয়াছেন বা কখন যে তাঁহাতে বিরাট ‘আমি’টার সহায়ে গুরুভাবাবেশ হইল, তাহা অনেক সময়ে সাধারণ-মানবমন-বুদ্ধির গোচর হইত না। কিন্তু ওটা ঐ ভাবের পূর্ণ পরিণত অবস্থার কথা এবং যেখানকার কথা সেইখানেই উহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। এখন যৌবনে সাধকাবস্থায় ঐ ভাবে আত্মহারা হইয়া তিনি অনেক সময়ে যেরূপ আচরণ করিতেন, তাহারই কিছু পাঠককে অগ্রে বলা আবশ্যক।
সাধনকালে ঐ ভাব – রানী রাসমণি ও তদীয় জামাতা মথুরের সহিত ব্যবহার
যৌবনে ঠাকুরের গুরুভাবের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাই, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রতিষ্ঠাত্রী, রানী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরানাথ বা মথুরবাবুকে লইয়া। অবশ্য ইঁহাদের দুইজনের কাহাকেও দেখা আমাদের কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। তবে ঠাকুরের নিজ মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, প্রথম দর্শনেই ইঁহাদের মনে ঠাকুরের প্রতি একটা ভালবাসার উদয় হইয়া ক্রমে ক্রমে উহা এতই গভীরভাব ধারণ করে যে, এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। মানুষকে মানুষ যে এতটা ভক্তি-বিশ্বাস করিতে – এতটা ভালবাসিতে পারে, তাহা আমাদের অনেকের মনে বোধ হয় ধারণা না হইয়া একটা রূপকথার মতো মনে হইবে! অথচ উপর উপর দেখিলে ঠাকুর তখন একজন সামান্য নগণ্য পূজক ব্রাহ্মণমাত্র এবং তাঁহারা সমাজে জাত্যংশে বড় না হইলেও, ধনে, মানে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সমাজের অগ্রণী বলিলে চলে।
ঠাকুরের অপূর্ব স্বভাব
আবার এদিকে ঠাকুরের স্বভাবও বাল্যাবধি অতি বিচিত্র! ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, নামের শেষে বড় বড় উপাধি প্রভৃতি যেসকল লইয়া লোকে লোককে বড় বলিয়া গণ্য করে, তাঁহার গণনায়, তাঁহার চক্ষে ওগুলো চিরকালই ধর্তব্যের মধ্যে বড় একটা ছিল না। ঠাকুর বলিতেন, “মনুমেন্টে উঠে দেখলে তিনতলা চারতলা বাড়ি, উঁচু উঁচু গাছ ও জমির ঘাস সব এক সমান হয়ে গেছে দেখায়।” আমরাও দেখি, ঠাকুরের নিজের মন বাল্যাবধি, সত্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুরাগ-সহায়ে সর্বদা এত উচ্চে উঠিয়া থাকিত যে সেখান হইতে ধন-মান-বিদ্যাদির একটু-আধটু তারতম্য – যাহা লইয়া আমরা একেবারে ফুলিয়া ফাটিয়া যাইবার মতো হই ও ‘ধরাকে সরা জ্ঞান’ করি – সব এক সমান দেখা যাইত! অথবা ঠাকুরের মন, চিরকাল প্রত্যেক কার্যটা কেন করিব ও প্রত্যেক ব্যক্তি ও পদার্থের সহিত সম্বন্ধের চরম পরিণতিতে কি কতদূর দাঁড়াইবে – তাহা ভাবিয়া অপরের ঐ ঐ বিষয়ে কিরূপ বা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিয়া একটা বদ্ধমূল ধারণায় পূর্ব হইতেই উপস্থিত হইত। কাজেই ঐসকল বিষয় যে উদ্দেশ্য ও চরমপরিণতি লুকাইয়া মধুর ছদ্মবেশে তাঁহাকে ভুলাইয়া অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও মিছামিছি ঘুরাইবে, তাহার কোন পথই ছিল না। পাঠক বলিবে, ‘কিন্তু ওরূপ বুদ্ধিতে সকল বিষয়ের দোষগুলিই তো আগে চক্ষে পড়িয়া মানুষকে জড়ভাবাপন্ন করিয়া তুলিবে, জগতের কোন কার্য করিতেই আর অগ্রসর হইতে দিবে না।’ বাস্তবিকই তাহা। মন যদি পূর্ব হইতে বাসনাশূন্য বা পবিত্র না হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরলাভরূপ মহৎ উদ্দেশ্য যদি উহার গোড়ায় বাঁধা না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ বুদ্ধি বাস্তবিকই মানবকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া উদ্যমরহিত এবং কখনো কখনো উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী করিয়া তোলে। নতুবা পবিত্রতা ও উচ্চ লক্ষ্যে যদি মনের সুর চড়াইয়া বাঁধা থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ সকল বিষয়ের অন্তস্তলস্পর্শী দোষদর্শী বুদ্ধিই মানবকে ঈশ্বরদর্শনের পথে দ্রুতপদে অগ্রসর করাইয়া দেয়। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐজন্য শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন মানবকেই সর্বদা সংসারে ‘জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শন’ করিয়া বৈরাগ্যবান হইতে বলিয়াছেন। ঠাকুরের চরিত্রে বাল্যাবধি ঐ দোষদৃষ্টি কতদূর পরিস্ফুট তা দেখ। লেখা-পড়া করিতে গিয়া কোথায় ‘তর্কালঙ্কার’, ‘বিদ্যাবাগীশ’ প্রভৃতি উপাধি ও নাম-যশের দিকে দৃষ্টি পড়িবে, তাহা না হইয়া দেখিতে পাইলেন, বড় বড় ‘তর্কবাগীশ’, ‘ন্যায়চঞ্চু’ মহাশয়দের ন্যায়-বেদান্তের লম্বা লম্বা কথা আওড়াইয়া ধনীর দ্বারে খোশামুদি করিয়া ‘চাল কলা বাঁধা’ বা জীবিকার সংস্থান করা! বিবাহ করিতে যাইয়া কোথায় সংসারের ভোগসুখ আমোদ-প্রমোদের দিকে নজর পড়িবে, তাহা না হইয়া দেখিলেন দুদিনের সুখের নিমিত্ত চিরকালের মতো বন্ধন গলায় পরা, অভাববৃদ্ধি করিয়া টাকার চিন্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ানো ও সেই দুই দিনের সুখেরও অনিশ্চয়তা! টাকাতে সংসারে সব করিতে ও সব হইতে পারা যায় দেখিয়া কোথায় কোমর বাঁধিয়া রোজগারে লাগিয়া যাইবেন – না, দেখিলেন, টাকাতে কেবল ভাত, ডাল, কাপড় ও ইট, মাটি, কাঠ লাভই হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরলাভ হয় না! সংসারে গরিব-দুঃখীর প্রতি দয়া করিয়া পরের দুঃখমোচন করিয়া ‘দাতা’, ‘পরোপকারী’ ইত্যাদি নাম কিনিবেন, না, দেখিলেন, আজীবন চেষ্টার ফলে বড় জোর দুচারটে ফ্রী-স্কুল ও দুচারটে দাতব্য ডাক্তারখানা, না হয় দুচারটে অতিথিশালা স্থাপন করা যায়; তারপর মৃত্যু ও জগতের যেমন অভাব ছিল, তেমনিই থাকিল! – এইরূপ সকল বিষয়ে।
ধনী ও পণ্ডিতদের ঠাকুরকে চিনিতে পারা কঠিন। উহার কারণ
ঐরূপ স্বভাবাপন্ন ঠাকুরকে কাজেই ঠিক ঠিক ধরা বা বুঝা সাধারণ মানবের বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ আবার বিদ্যাভিমানী ও ধনীদের; কারণ, স্পষ্ট কথা সংসারে কাহারও নিকট শুনিতে না পাইয়া, লোকমান্য ও ধনমদে শুনিবার ক্ষমতাটি পর্যন্ত তাঁহারা অনেক স্থলে হারাইয়া বসেন। কাজেই তাঁহারা ঠাকুরকে অনেক সময় না বুঝিতে পারিয়া যে অসভ্য, পাগল বা অহঙ্কারী মনে করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। সেজন্যই রানী রাসমণি ও মথুরবাবুর ভক্তি-ভালবাসা দেখিয়া আরও অবাক হইতে হয়! মনে হয়, ঈশ্বরকৃপায় মহাভাগ্যোদয় হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা ঠাকুরের উপর ভালবাসা শুধু যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে, উপরন্তু তাঁহার দিব্য গুরুভাবের পরিচয় দিন দিন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে সর্বতোভাবে আত্মবিক্রয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন! নতুবা যে ঠাকুর কালীবাটী-প্রতিষ্ঠার দিনে আপনার অগ্রজ পূজায় ব্রতী হইলে এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদ ভোজন করিলেও শূদ্রান্নভোজন করিতে হইবে বলিয়া তথায় উপবাস করিয়াছিলেন এবং পরেও কিছুকাল পর্যন্ত ঐ নিমিত্ত কালীবাটীর গঙ্গাতীরে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছিলেন, যে ঠাকুর মথুরবাবু বার বার ডাকিলেও বিষয়ী লোক বলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং পরে মা কালীর পূজায় ব্রতী হইবার জন্য তাঁহার সাদর অনুরোধ বার বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, অভিমান এবং ধনমদ ত্যাগ করিয়া সেই ঠাকুরকে প্রথম হইতে ভালবাসা এবং বরাবর ঐ ভাব ঠিক রাখা রানী রাসমণি ও মথুরবাবুর সহজ হইত না।
বিবাহের পর ঠাকুরের অবস্থা। মথুরের উহা লক্ষ্য করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। অপর সাধারণের ঠাকুরের বিষয়ে মতামত
ঠাকুরের তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে – পূর্ণ যৌবন। বিবাহ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং মা-কালীর পূজায় ব্রতী হইয়াছেন; এবং পূজায় ব্রতী হইয়াই আবার ঈশ্বরপ্রেমে পাগলের মতো হইয়াছেন। ঈশ্বরলাভ হইল না বলিয়া কখনো কখনো ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া মুখ ঘষড়াইয়া ‘মা’ ‘মা’ বলিয়া এত ক্রন্দন করেন যে, লোক দাঁড়াইয়া যায়! লোকে ব্যথিত হইয়া বলাবলি করে, ‘আহা, লোকটির কোন উৎকট রোগ হইয়াছে নিশ্চয়; পেটের শূলব্যথায় মানুষকে অমনি অস্থির করে।’ কখনো বা পূজার সময় যত ফুল নিজের মাথায় চাপাইয়া নিস্পন্দ হইয়া যান। কখনো বা সাধকদিগের পদাবলী উন্মত্তভাবে কতক্ষণ ধরিয়া গাহিতে থাকেন। নতুবা যখন কতকটাও সাধারণভাবে থাকেন তখন যাহার সহিত যেমন ব্যবহার করা উচিত, যাহাকে যেমন মান দেওয়া রীতি, সে সমস্ত পূর্বের ন্যায়ই করেন। কিন্তু জগন্মাতার ধ্যানে যখন ঐরূপ ভাবাবেশ হয় – এবং সে ভাবাবেশ যে দিনের ভিতর এক-আধবার একটু-আধটু হইত, তাহা নহে – তখন ঠাকুরের আর কোন ঠিক-ঠিকানাই থাকে না, কাহারও কোন কথা শোনেন না – বা উত্তর দেন না। কিন্তু তখনো সে দেবচরিত্রে মাধুর্যের অনেক সময় লোকে পরিচয় পায়। তখনো যদি কেহ বলে, ‘মা-র নাম দুটো শোনাও না’ – অমনি ঠাকুর তাহার প্রীতির জন্য মধুর কণ্ঠে গান ধরেন এবং গাহিতে গাহিতে গানের ভাবে নিজে বিভোর হইয়া আত্মহারা হন।
ইতঃপূর্বেই রানী রাসমণি ও মথুরবাবুর কর্ণে হীনবুদ্ধি নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণ এবং ঠাকুরবাড়ির প্রধান কর্মচারী খাজাঞ্চী মহাশয়ও পূজার সময় ঠাকুরের অনাচারের অনেক কথা তুলিয়া বলিয়াছেন, ‘ছোট ভট্চাজ্1 সব মাটি করলে; মা-র (কালীর) পূজা, ভোগ, রাগ কিছুই হইতেছে না; ওরূপ অনাচার করলে মা কি কখনো পূজা ভোগ গ্রহণ করেন?’ – ইত্যাদি। কিন্তু বলিয়াও কিছুমাত্র সফলমনোরথ হন নাই; কারণ, মথুরবাবু স্বয়ং মাঝে মাঝে কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়া হঠাৎ মন্দিরে আসিয়া অন্তরালে থাকিয়া ঠাকুরের পূজার সময় ভক্তিবিহ্ব্ল, বালকের ন্যায় ব্যবহার ও শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি আবদার অনুরোধাদি দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহাদের আজ্ঞা করিয়াছেন – “ছোট ভট্টাচার্য মহাশয় যেভাবে যাহাই করুন না কেন, তোমরা তাঁহাকে বাধা দিবে না বা কোন কথা বলিবে না। আগে আমাকে জানাইবে, পরে আমি যেমন বলি তেমনি করিবে।”
রানী রাসমণিও মধ্যে মধ্যে আসিয়া মা-র শিঙ্গার (ফুলের সাজ) ইত্যাদি দেখিয়া এবং ঠাকুরের মধুর কণ্ঠে মা-র নাম শুনিয়া এতই মোহিত হইয়াছেন যে, যখনই কালীবাড়িতে আসেন, তখনই ছোট ভট্টাচার্যকে নিকটে ডাকাইয়া মা-র নাম (গান) করিতে অনুরোধ করেন। ঠাকুরও গান করিতে করিতে কাহাকেও যে শুনাইতেছেন এ কথা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকেই যেন শুনাইতেছেন, এই ভাবে গান গাহিতে থাকেন। এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, জগৎরূপ বৃহৎ সংসারের ন্যায় ঠাকুরবাড়ির ক্ষুদ্র সংসারেও যে যাহার কাজ লইয়াই ব্যস্ত এবং সাংসারিক কাজকর্ম ও স্বার্থচিন্তা বাদে যতটুকু সময় পায় তাহাতে পরনিন্দা পরচর্চাদি রুচিকর বিষয়সকলের আন্দোলন করিয়া নিজ নিজ মনের একদেশিতার অবসাদ দূর করিয়া থাকে। কাজেই ছোট ভট্টাচার্যের ভিতরে ঈশ্বরপ্রেমে যে কি পরিবর্তন হইতেছে, তাহার খবর রাখে কে? ‘ও একটা উন্মাদ, বাবুদের কেমন একটা সুনজরে পড়িয়াছে, তাই এখনো চাকরিটি বজায় আছে; তাই বা কদিন? কোন্ দিন এই একটা কি কাণ্ড করিয়া বসিবে ও তাড়িত হইবে! বড়লোকের মেজাজ – কিছু কি ঠিকঠিকানা আছে? খুশি হইতেও যতক্ষণ, আর গরম হইতেও ততক্ষণ’ – ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্তাই কর্মচারীদের ভিতর কখনো কখনো হইয়া থাকে, এই মাত্র। ঠাকুরের ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়ও তৎপূর্বেই ঠাকুরবাটীতে আসিয়া জুটিয়াছে।
1. ঠাকুরের অগ্রজকে ‘বড় ভট্টাচার্য’ বলিয়া ডাকায় ঠাকুর তখন এই নামে নির্দিষ্ট হইতেন।
গুরুভাবে ঠাকুরের রানী রাসমণিকে দণ্ডবিধান
আজ রানী রাসমণি স্বয়ং ঠাকুরবাড়িতে আসিয়াছেন। কর্মচারীরা সকলে শশব্যস্ত। যে ফাঁকিদার সে-ও আজ আপন কর্তব্য অতি যত্নের সহিত করিতেছে। গঙ্গায় স্নানান্তে রানী কালীঘরে দর্শন করিতে যাইলেন। তখন কালীর পূজা ও বেশ হইয়া গিয়াছে। জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া রানী মন্দিরমধ্যে শ্রীমূর্তির নিকট আসনে আহ্নিক-পূজা করিতে বসিলেন এবং ছোট ভট্টাচার্য বা ঠাকুরকে নিকটে দেখিয়া মা-র নামগান করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরও রানীর নিকটে বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদিগের পদাবলী গাহিতে লাগিলেন; রানী পূজা-জপাদি করিতে করিতে ঐসকল শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে ঠাকুর হঠাৎ গান থামাইয়া বিরক্ত হইয়া উগ্রভাবে রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “কেবল ঐ ভাবনা, এখানেও ঐ চিন্তা?” – বলিয়াই রানীর কোমল অঙ্গে করতল দ্বারা আঘাত করিলেন! সন্তানের কোনরূপ অন্যায়াচরণ দেখিয়া পিতা যেরূপ কুপিত হইয়া কখনো কখনো দণ্ডবিধান করেন, ঠাকুরেরও এখন ঠিক সেই ভাব! কিন্তু কে-ই বা তাহা বুঝে!
উহার ফল
মন্দিরের কর্মচারী ও রানীর পরিচারিকারা সকলে হইচই করিয়া উঠিল। দ্বারপাল শশব্যস্তে ঠাকুরকে ধরিতে ছুটিল। বাহিরের কর্মচারীরাও মন্দিরমধ্যে এত গোল কিসের ভাবিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেদিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু ঐ গোলযোগের প্রধান কারণ যাঁহারা – ঠাকুর ও রানী রাসমণি – তাঁহারা উভয়েই এখন স্থির, গম্ভীর! কর্মচারীদের বকাবকি ছুটাছুটির দিকে লক্ষ্য না করিয়া একেবারে উদাসীন থাকিয়া ঠাকুর আপনাতে আপনি স্থির ও তাঁহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি; শ্রীশ্রীজগদম্বার ধ্যান না করিয়া আজ কেবলই একটি বিশেষ মকদ্দমার ফলাফলের বিষয় ধ্যান করিতেছিলেন, রানী রাসমণি নিজের অন্তর পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখিতে পাইয়া ঈষৎ অপ্রতিভ ও অনুতাপে গম্ভীর! আবার ঠাকুর ঐ কথা কি করিয়া জানিতে পারিলেন ভাবিয়া রানীর ঐ ভাবের সহিত কতক বিস্ময়ের ভাবও মনে বর্তমান! পরে কর্মচারীদের গোলযোগে রানীর চমক ভাঙিল ও বুঝিলেন – নিরপরাধ ঠাকুরের প্রতি, এই ঘটনায় হীনবুদ্ধি লোকদিগের বিশেষ অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা। বুঝিয়া সকলকে গম্ভীরভাবে আজ্ঞা করিলেন, “ভট্টাচার্য মহাশয়ের কোন দোষ নাই। তোমরা উঁহাকে কেহ কিছু বলিও না।” পরে মথুরবাবুও নিজ শ্বশ্রূঠাকুরানীর নিকট হইতে ঘটনাটির সকল কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া কর্মচারীদিগের উপর পূর্বোক্ত হুকুমই বহাল রাখিলেন। ইহাতে তাহাদের কেহ কেহ বিশেষ দুঃখিত হইল; কিন্তু কি করিবে, ‘বড় লোকের বড় কথায় আমাদের কাজ কি’ ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিল।
শ্রীচৈতন্য ও ঈশার জীবনে ঐরূপ ঘটনা
ঘটনাটি শুনিয়া পাঠক হয়তো ভাবিবে – এ আবার কোন্ দেশী গুরুভাব? লোকের অঙ্গে আঘাত করিয়া এ আবার কি প্রকার গুরুভাবের প্রকাশ? আমরা বলি – জগতের ধৰ্মেতিহাস পাঠ কর, দেখিবে লোকগুরু আচার্যদিগের জীবনে এরূপ ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে কাজিদলন, গুরুভাবে আত্মহারা হইয়া অদ্বৈত প্রভুকে প্রহার করিয়া ভক্তিদান প্রভৃতির কথা স্মরণ কর। ভাবিয়া দেখ, মহামহিম ঈশার জীবনেও ঐরূপ ঘটনার অভাব নাই।
শিষ্যপরিবৃত ঈশা জেরুজালেমের ‘য়াভে’ দেবতার মন্দিরে দর্শনপূজাদি করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। ৺বারাণসী শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থে দেবস্থানসকল দর্শন করিতে যাইয়া হিন্দুর মনে যেরূপ অপূর্ব পবিত্র ভাবের উদয় হয়, ইহুদি-মনে জেরুজালেমের মন্দির-দর্শনেও ঠিক তদ্রূপ হইবে – ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাহার উপর আবার ভাবমুখে অবস্থিত ঈশার মন! দূর হইতে মন্দির-দর্শনেই ঈশা ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া দেবদর্শন করিতে ছুটিলেন। মন্দিরের বাহিরে, দ্বারে, প্রাঙ্গণমধ্যে কত লোক কত প্রকারে দু-পয়সা রোজগার প্রভৃতি দুনিয়াদারিতেই ব্যস্ত। পাণ্ডা পুরোহিতেরা দেবদর্শন হউক আর নাই হউক যাত্রীদিগের নিকট হইতে দু-পয়সা ঠকাইয়া লইতে নিযুক্ত। আর দোকানি পসারিরা পূজায় পশু-পুষ্পাদি দ্রব্যসম্ভার এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া কিসে দু-পয়সা অধিক লাভ করিবে, এই চিন্তাতেই ব্যাপৃত। ভগবানের মন্দির তাহার নিকটে রহিয়াছে – এ কথা ভাবিতে কাহার আর মাথাব্যথা পড়িয়াছে? যাহা হউক, ভাববিভোর ঈশার চক্ষে মন্দিরপ্রবেশকালে এসকল কিছুই পড়িল না। সরাসরি মন্দিরমধ্যে যাইয়া দেবদর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মারূপে তিনি অন্তরে রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইলেন। মন্দির ও তন্মধ্যগত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন; কারণ এখানে আসিয়াই তো তিনি প্রাণারামের দর্শন পাইলেন! পরে মন যখন আবার নিচে নামিয়া ভিতরের ভাবপ্রকাশ বাহিরের ব্যক্তি ও বস্তুর ভিতর দেখিতে যাইল, তখন দেখেন সকলই বিপরীত। কেহই তাঁহার প্রাণারামের সেবায় নিযুক্ত নহে; সকলেই কাম-কাঞ্চনের সেবাতেই ব্যাপৃত! তখন নিরাশা ও দুঃখে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। ভাবিলেন – একি? তোরা বাহিরে, সংসারের ভিতর যাহা করিস কর না, কিন্তু এখানে, যেখানে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ – এখানে আবার এসকল দুনিয়াদারি কেন? কোথায় এখানে আসিয়া দুদণ্ড তাঁহার চিন্তা করিয়া সংসারের জ্বালা দূর করিবি, তাহা না হইয়া এখানেও সংসার আনিয়া পুরিয়াছিস! – ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হইল এবং বেত্রহস্তে উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া তিনি সকল দোকানি পসারিদের বলপূর্বক মন্দিরের বাহিরে তাড়াইয়া দিলেন। তাহারাও তখন তাঁহার কথায় ক্ষণিক চৈতন্য লাভ করিয়া যথার্থই দুষ্কর্ম করিতেছি ভাবিতে ভাবিতে সুড় সুড় করিয়া বাহিরে গমন করিল; অতি বদ্ধ জীব – যাহার কথায় চৈতন্য হইল না, সে তাঁহার কশাঘাতে ঐ জ্ঞানলাভ করিয়া বহির্গমন করিল। কিন্তু কেহই ক্রোধপূর্ণ হইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইল না।
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও এইরূপে আহত ব্যক্তির জ্ঞানলাভ হইয়া তাঁহাকে ভগবদ্বুদ্ধিতে স্তবস্তুতি করার কথা, অতি বদ্ধ জীবকুলের তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে আসিয়া তাঁহার হাস্যে বা কথায় স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যাইবার কথা প্রভৃতি অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। যাক এখন ঐ সকল পৌরাণিকী কথা।
গুরুভাবের প্রেরণায় আত্মহারা ঠাকুরের অদ্ভুতপ্রকারে শিক্ষাপ্রদান ও রানী রাসমণির সৌভাগ্য
গুরুভাবে সম্পূর্ণ আত্মহারা ঠাকুর যে কিভাবে অপরের সহিত ব্যবহার ও শিক্ষাদি প্রদান করিতেন, এই ঘটনাটি উহার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। ঘটনাটি তলাইয়া দেখিলে বড় কম ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। কোথায় একজন সামান্য বেতনমাত্রভোগী নগণ্য পূজারী ব্রাহ্মণ এবং কোথায় রানী রাসমণি – যাঁহার ধন, মান, বুদ্ধি, ধৈর্য, সাহস ও প্রতাপে কলিকাতার তখনকার মহা মহা বুদ্ধিমানেরাও স্তম্ভিত! এরূপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ যে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতেই পারিবে না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হয়। অথবা যদি কখনো কোন কারণে তাঁহার সমীপস্থ হয় তো চাটুকারিতা প্রভৃতি উপায়ে তাঁহার তিলমাত্র সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে এবং তন্নিমিত্তই অবসর অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। তাহা না হইয়া একেবারে তদ্বিপরীত! তাঁহার অন্যায় আচরণের খালি প্রতিবাদ নহে, শারীরিক দণ্ডবিধান! ঠাকুরের দিক হইতে দেখিলে ইহা যেমন অল্প বিস্ময়ের কথা মনে হয় না, রানীর দিক হইতে দেখিলে ঐরূপ ব্যবহারে যে তাঁহার মনে ক্রোধ-অভিমান-হিংসাদির উদয় হইল না, ইহাও একটি কম কথা বলিয়া মনে হয় না। তবে পূর্বেই যেমন আমরা বলিয়া আসিয়াছি – স্বার্থগন্ধহীন বিরাট ‘আমি’টার সহায়ে যখন মহাপুরুষদিগের মনে এইরূপে গুরুভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইচ্ছা না থাকিলেও সাধারণ মানবকে তাঁহার নিকট নতশির হইতে হইবেই হইবে, রানীর ন্যায় ভক্তিমতী সাত্ত্বিকপ্রকৃতির তো কথাই নাই। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থনিবদ্ধদৃষ্টি মানব-মন তখন তাঁহাদের কৃপা ও শক্তিতে উন্নত হইয়া তাঁহারা যাহা করিতে বলিতেছেন তাহাতেই তাহার বাস্তবিক স্বার্থ – এ কথাটি আপনা-আপনি বুঝিতে পারে। কাজেই তখন তদ্রূপ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর থাকে না। আর এক কথা ঠাকুর যেমন বলিতেন – “তাঁহার (ঈশ্বরের) বিশেষ অংশ ভিতরে না থাকিলে কেহ কখনো কোন বিষয়ে বড় হইতে পারে না; বা মান, ক্ষমতা প্রভৃতি হজম1 করিতে পারে না!” সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্না রানীর ভিতর ঐরূপ ঐশী শক্তি বিদ্যমান ছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ কঠোরভাবে প্রকাশিত হইলেও ঠাকুরের গুরুভাবে কৃপা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, “রানী রাসমণি শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্ট নায়িকার একজন! ধরাধামে তাঁহার পূজা-প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন। জমিদারির দলিল-পত্রাদি অঙ্কিত করিবার তাঁহার যে সীলমোহর ছিল তাহাতেও লেখা ছিল – ‘কালীপদ-অভিলাষী, শ্রীমতী রাসমণি দাসী।’ রানীর প্রতি কার্যেই ঐরূপে জগন্মাতার উপর অচলা ভক্তি প্রকাশ পাইত।”
1. মান প্রভৃতি হজম করা অর্থাৎ ঐসকল লাভ করিয়াও মাথা ঠিক রাখা; অহঙ্কৃত হইয়া ঐসকলের অপব্যবহার না করা।
ঈশ্বরে তন্ময় মনের লক্ষণ-সম্বন্ধে শাস্ত্রমত
আর এক কথা – সর্বতোভাবে ঈশ্বরে তন্ময় মনের নানা ভাবে অবস্থানের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। আচার্য শ্রীমৎ শঙ্কর তৎকৃত ‘বিবেকচূড়ামণি’-নামক গ্রন্থে উহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন –
দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥ ৫৪১
– ঈশ্বরলাভ বা জ্ঞানলাভে সিদ্ধকাম পুরুষদিগের কেহ বা জ্ঞানরূপ বস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া, আবার কেহ বা বল্কল বা সাধারণ লোকের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া, কেহ বা উন্মাদের ন্যায়, আবার কেহ বা বহির্দৃষ্টে কামকাঞ্চনগন্ধহীন বালক, বা শৌচাচারবিবর্জিত পিশাচের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন।
লোকগুরুদিগের এবং বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহার বুঝা এত কঠিন কেন
‘বিরাট আমি’-টার সহিত তন্ময়ভাবে অনেকক্ষণ অবস্থান করায় সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে ইঁহাদের ঐরূপ অবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণসমর্থ গুরুভাব ইঁহাদের ভিতর দিয়াই বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি – ক্ষুদ্র স্বার্থময় ‘আমি’-টার লোপ বা বিনাশেই জগদ্ব্যাপী বিরাট আমিত্ব এবং তৎসহ লোককল্যাণসাধনকারী শ্রীগুরুভাবের প্রকাশ। ঐ সকল জ্ঞানী পুরুষদিগের ভিতর আবার যাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছায় সর্বদা গুরু বা ঋষি-পদবীতে অবস্থান করেন, তাঁহাদের আবার অপরের শিক্ষার নিমিত্ত সদ্বিষয়ে তীব্রানুরাগ, অসদ্বিষয়ে তীব্র বিরাগ বা ক্রোধ, আচার, নিষ্ঠা, নিয়ম, তর্ক, যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য ইত্যাদি সকল ভাবই অবস্থানুযায়ী সাধারণ পুরুষদিগের ন্যায় দেখাইতে হয়। ‘দেখাইতে হয়’ বলিতেছি এজন্য যে, ভিতরে ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ ব্রহ্মভাবে ভালমন্দ, ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্যাদি মায়ারাজ্যের অন্তর্গত সকল পদার্থে ও ভাবে একাকার জ্ঞান বা দৃষ্টি পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিলেও, অপরকে মায়ারাজ্যের পারে যাইবার পথ দেখাইবার জন্য ঐসকল ভাব লইয়া তাঁহারা কালযাপন করিয়া থাকেন। সাধারণ গুরু বা ঋষিদিগেরই যখন ঐরূপে লোককল্যাণের নিমিত্ত অনেক সময় কালযাপন করিতে হয়, তখন ঈশ্বরাবতার বা জগদ্গুরুপদবীস্থ আচার্যকুলের তো কথাই নাই। এজন্য তাঁহাদের বুঝা, ধরা সাধারণ মানবের এত কঠিন হইয়া উঠে; বিশেষতঃ আবার বর্তমান যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চেষ্টা ও ব্যবহারাদি ধরা ও বুঝা। কারণ অবতারকুলে যেসকল বাহ্যিক ঐশ্বর্য, শক্তি বা বিভূতির প্রকাশ শাস্ত্রে এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে, সেসকল ইঁহাতে এত গুপ্তভাবে প্রকাশিত ছিল যে, যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহার কৃপালাভ করিয়া ইঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে নিবদ্ধ না হইলে, ইঁহাকে দুই-চারি বার ভাসা ভাসা, উপর উপর মাত্র দেখিয়া কাহারও ঐসকলের পরিচয় পাইবার উপায় ছিল না। দেখ না, বাহ্যিক কোন্ গুণ দেখিয়া তুমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? বিদ্যায় – একেবারে নিরক্ষর বলিলেই চলে! শ্রুতিধরত্বগুণে বেদ-বেদান্তাদি সকল শাস্ত্র শুনিয়া যে তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, একথা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে? বুদ্ধিতে তাঁহাকে ধরিবে? “আমি কিছু নহি, কিছু জানি না – সব আমার মা জানেন” – সর্বদা এইরূপ বুদ্ধির যাঁহাতে প্রকাশ, তাঁহার নিকট তুমি কোন্ বিষয়ে কি বুদ্ধি লইতে যাইবে? আর লইতে যাইলেও তিনি যখন বলিবেন, “মাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন”, তখন কি তুমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থির রাখিয়া ঐরূপ করিতে পারিবে? তুমি ভাবিবে – “কি পরামর্শই দিলেন! ও-কথা তো আমরা সকলে ‘কথামালা’ ‘বোধোদয়’ পড়িবার সময় হইতেই শুনিয়া আসিতেছি – ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, ইচ্ছা করিলে সকল বিষয় জানাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু ঐ কথা লইয়া কাজ করিতে যাইলে কি চলে?” ধনে, নাম-যশে তাঁহাকে ধরিবে? ঠাকুরের নিজের তো ও-সকল খুবই ছিল! আবার ও-সকল তো ত্যাগ করিতেই প্রথম হইতেই উপদেশ! এইরূপ সকল বিষয়ে। কেবল আকৃষ্ট হইয়া ধরিবার একমাত্র উপায় ছিল – তাঁহার পবিত্রতা, ঈশ্বরানুরাগ ও প্রেম দেখিয়া। ইহাতে তুমি যদি আকৃষ্ট হইলে তো হইল, নতুবা তাঁহাকে ধরা ও বুঝা তোমার পক্ষে বহু দূরে! তাই বলি, রানী রাসমণি যে ঐরূপ কঠোরভাবে প্রকাশিত ঠাকুরের গুরুভাব ধরিতে পারিলেন এবং তিনি ঐরূপে যে শিক্ষাদান করিলেন, তাহা অভিমান-অহঙ্কারে ভাসাইয়া না দিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্যা হইলেন – ইহা তাঁহার কম ভাগ্যোদয়ের কথা নহে।
তৃতীয় খণ্ড – ষষ্ঠ অধ্যায়: গুরুভাব ও মথুরানাথ
‘বড় ফুল ফুটতে দেরি লাগে’
হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥
– গীতা, ১০।১৯
পূর্বেই বলিয়াছি, ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের ধীর বিকাশ রানী রাসমণি ও মথুরবাবুর চক্ষের সম্মুখেই অনেকটা হইতে থাকে। উচ্চাঙ্গের ভাববিকাশ সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, “বড় ফুল ফুটতে দেরি লাগে, সারবান গাছ অনেক দেরিতে বাড়ে।” ঠাকুরের জীবনেও অদৃষ্টপূর্ব গুরুভাবের বিকাশ হইতে বড় কম সময় ও সাধনা লাগে নাই; দ্বাদশবর্ষব্যাপী নিরন্তর কঠোর সাধনার আবশ্যক হইয়াছিল। সে সাধনার যথাসাধ্য পরিচয় দিবার ইহা স্থান নহে। এখানে চিৎসূর্যের কিরণমালায় সম্যক সমুদ্ভাসিত গুরুভাবরূপ কুসুমটির সহিতই আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ; তাহার কথাই বিশেষ করিয়া বলিয়া যাইব। তবে ঐ ভাববিকাশের কথা পূর্বাবধি শেষ পর্যন্ত বলিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন কথা আসিয়া পড়িবে। যেসকল ভক্তের সহিত ঠাকুরের ঐ ভাবের পূর্ব-পূর্বাবস্থার সময়ে সম্বন্ধ, তাহাদের কথাও কিছু না কিছু আসিয়া পড়িবে নিশ্চয়।
মথুরের সহিত ঠাকুরের অদ্ভুত সম্বন্ধ। মথুর কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল
মথুরবাবুর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ এক অদ্ভুত ব্যাপার! মথুর ধনী অথচ উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন, বিষয়ী হইলেও ভক্ত, হঠকারী হইয়াও বুদ্ধিমান, ক্রোধপরায়ণ হইলেও ধৈর্যশীল এবং ধীরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। মথুর ইংরাজী-বিদ্যাভিজ্ঞ ও তার্কিক, কিন্তু কেহ কোন কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলে উহা বুঝিয়াও বুঝিব না – এরূপ স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন না; ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ভক্ত, কিন্তু তাই বলিয়া ধর্মসম্বন্ধে যে যাহা বলিবে তাহাই যে চোখ-কান বুঁজিয়া অবিচারে গ্রহণ করিবেন, তাহা ছিল না, তা তিনি ঠাকুরই হউন বা গুরুই হউন বা অন্য যে কেহই হউন; উদার-প্রকৃতি ও সরল, কিন্তু তাই বলিয়া বিষয়কর্মে বা অন্য কোন বিষয়ে যে বোকার মতো ঠকিয়া আসিবেন, তাহা ছিলেন না, বরং বিষয়ী জমিদারগণ যে কূটবুদ্ধি এবং সময়ে সময়ে অসদুপায়-সহায়ে প্রতিনিয়ত বিষয়বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, সে সকলেরও তাঁহাতে কখনো কখনো প্রকাশ দেখা গিয়াছে। বাস্তবিকই পুত্রহীনা রানী রাসমণির অন্যান্য জামাতা বর্তমান থাকিলেও বিষয়কর্মের তত্ত্বাবধান ও সুবন্দোবস্তে কনিষ্ঠ মথুরবাবুই তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন; এবং শাশুড়ী ও জামাই উভয়ের বুদ্ধি একত্রিত হওয়াতেই রানী রাসমণির নামের তখন এতটা দপ্দপা হইয়া উঠিয়াছিল।
ঠাকুরের গুরুভাব-বিকাশে রাণী রাসমণি ও মথুরের অজ্ঞাত ভাবে সহায়তা। বন্ধু বা শত্রুভাবে সম্বদ্ধ যাবতীয় লোক অবতারপুরুষের শক্তিবিকাশের সহায়তা করে
পাঠক হয়তো বলিবে – ‘এ ধান ভানতে শিবের গীত’ কেন? ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে আবার মথুরবাবু কেন? কারণ, গুটী কাটিয়া ভাবরূপী প্রজাপতিটি যখন বাহির হইতেছিল, তখন মথুরই তাহার ভাবী সৌন্দর্যের আভাস কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রধান রক্ষক ও সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন! রানী রাসমণি একটা মহা শুদ্ধ পবিত্র প্রেরণায় এ অদ্ভুত চরিত্রের বিকাশ ও প্রসারোপযোগী স্থান নির্মাণ করিলেন, আর তাঁহার জামাতা মথুর ঐরূপ উচ্চ প্রেরণায় সেই দেবচরিত্র-বিকাশের সময় অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইল, তৎসমস্ত যোগাইলেন। অবশ্য এ কথা আমরা এখন এতদিন পরে ধরিতে পারিতেছি; তাঁহারা উভয়ে কিন্তু এই বিষয়ের আভাস কখনো কখনো কিছু কিছু পাইলেও ঐসকল কার্য যে কেন করিতেছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পরেও যে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। যুগে যুগে সকল মহাপুরুষদিগের জীবনালোচনা করিতে যাইলেই ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, কি একটা অজ্ঞাত শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া কোথা হইতে তাঁহাদের সকল বিষয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, সকল সময়ে সর্বাবস্থায় তাঁহাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, অপর সকল ব্যক্তির শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহাদের অধীনে আনিয়া দেন; অথচ ঐসকল ব্যক্তি জানিতেও পারে না যে, তাহারা নিজে স্বাধীনভাবে, প্রেমে বা ঐসকল দেবচরিত্রের উপর বিদ্বেষে যাহা করিয়া যাইতেছে, তাহা তাঁহাদেরই জন্য – তাঁহাদেরই কার্যের সহায়ক হইবে বলিয়া – তাঁহাদেরই গন্তব্য পথের বাধা-বিঘ্নগুলি সরাইয়া তাঁহাদের ভিতরের শক্তি উদ্দীপিত করিবে বলিয়া! – আর মানুষ বহুকাল পরে উহা বুঝিতে পারিয়া অবাক হইয়া থাকে! কৈকেয়ীর শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার ফল দেখ; বসুদেব দেবকীকে কারাগারে রাখিয়া কংসের আজীবন চেষ্টার শেষ দেখ; সিদ্ধার্থের পাছে বৈরাগ্যোদয় হয় বলিয়া রাজা শুদ্ধোদনের প্রমোদকানন-নির্মাণ দেখ; ক্রূর কাপালিক বৌদ্ধদিগের আচার্য শঙ্করকে অভিচারাদি-সহায়ে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা দেখ; রাজপুরুষাদির সহায়ে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মপ্রচারের বিদ্বেষ ও বিপক্ষতাচরণের ফল দেখ; আর দেখ মহামহিম ঈশাকে মিথ্যাপরাধে নিহত করিবার ফল! – সর্বত্রই ‘উলটা বুঝিলু রাম’1 হইয়া গেল! অথচ মহাপরাক্রান্ত বুদ্ধিমান বিপক্ষ ও স্নেহপরবশ স্বপক্ষকুল কূটনীতি বা বিষয়বুদ্ধি-সহায়ে চিরকালই অন্যরূপ ভাবিয়া অন্য উদ্দেশ্যে কার্য করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভাবিতে ও করিতে থাকিবে। তবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থসকলে যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে – শত্রুভাবে, ঐ ঐশী শক্তির উদ্দেশ্য ও গতিবিধির বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া যাইতে হয়, আর ভক্ত শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ঐ ঐশী শক্তির অনুগামী হইয়া কখনো কখনো উহার কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এইমাত্র; এবং ঐ জ্ঞানের সহায়ে ক্রমে ক্রমে বাসনাবর্জিত হইয়া মুক্তি ও চিরশান্তির অধিকারী হইয়া থাকে। মথুরবাবুর ক্রিয়াকলাপও শেষ ভাবের হইয়াছিল।
1. নিম্নলিখিত গল্পটি হইতে প্রচলিত উক্তিটির উৎপত্তি হইয়াছে। যথা – এক বৈরাগী সাধু বহুকাল পর্যন্ত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গের সাথী – তসলা, লোটা প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির মোটটি নিজেই বহন করিতেন। একদিন সাধুর মনে হইল, একটি ঘোড়া পাই তো মোটটি আর নিজে বহিয়া কষ্ট পাই না। ভাবিয়াই ‘এক ঘোড়া, দেলায় দে রাম’ বলিয়া চিৎকার করিয়া ঘোড়া-ভিক্ষার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। তখন সেই স্থান দিয়া রাজার পল্টন যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটি ঘোটকীর শাবক হওয়ায় উহার আরোহী ভাবিতে লাগিল, “তাইতো, পল্টন এখনি এ স্থান হইতে অন্যত্র কুচ করিবে, ঘোটকী হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু সদ্যোজাত শাবকটি কেমন করিয়া লইয়া যাই?” ভাবিয়া চিন্তিয়া শাবকটিকে বহন করিবার জন্য একটি লোকের অন্বেষণে বাহির হইয়াই ‘ঘোড়া দেলায় দে রাম’-সাধুর সহিত দেখা হইল এবং সাধুকে বলিষ্ঠ দেখিয়া কোন বিচার না করিয়া একেবারে বলপূর্বক তাঁহাকে দিয়া শাবকটি বহন করাইয়া লইয়া চলিল। সাধু তখন ফাঁপরে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন – ‘উলটা বুঝিলু রাম!’ কোথায় ঘোড়া তাঁহার মোটটি ও তাঁহাকে বহন করিবে, না, তাঁহাকে ঘোটকী-শাবক বহন করিতে হইল!
সাধারণ মানবজীবনেও ঐরূপ। কারণ, উহার সহিত অবতারপুরুষের জীবনের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে
অবতার-মহাপুরুষদিগের জীবনেই যে কেবল এই দৈবী শক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। তবে তাঁহাদের জীবনে উহার উজ্জ্বল খেলা সহজে ধরিতে পারিয়া আমরা অবাক হই – এই পর্যন্ত। নতুবা আপন আপন দৈনন্দিন জীবন এবং জগতের ব্যবহারিক জীবনের ইতিহাসের আলোচনা করিলেও আমরা ঐ বিষয়ের যৎসামান্য প্রকাশ দেখিতে পাই। বহুদর্শিতা বা মানবজীবনের বহু ঘটনার তুলনায়, আলোচনায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানব ঐ দৈবী শক্তির হস্তে সর্বক্ষণই ক্রীড়াপুত্তলীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। অবতার-মহাপুরুষদিগের জীবনের সহিত সাধারণ মানবজীবনের এরূপ সৌসাদৃশ্য থাকাটাও কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। কারণ তাঁহাদের অলৌকিক জীবনাবলীই তো ইতরসাধারণের জীবন-গঠনের ছাঁচ (type or model)-স্বরূপ। তাঁহাদের জীবনাদর্শেই তো সাধারণ মানব আপন জীবনগঠনের প্রয়াস পাইতেছে ও চিরকালই পাইবে। দেখ না, নানা জাতির নানা ভাবের সম্মিলনভূমি বিশাল ভারতজীবন রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি কয়েকটি মহাপুরুষ কেমন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন! আবার ঐ সকল পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষদিগের জীবনাদর্শসকলের একত্র সম্মিলনে অদৃষ্টপূর্ব নূতন ভাবে গঠিত বর্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ কেমন দ্রুতপদে আপন প্রবাহ বিস্তার করিয়া এই স্বল্পকালমধ্যেই বর্তমান ভারত-ভারতীর জীবন অধিকার করিয়া বসিতেছে! কালে ইহা কি ভাবে কতদূর যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা তোমার সাধ্য হয়, বল; আমরা কিন্তু, হে পাঠক, উহা বুঝিতে ও বলিতে সম্পূর্ণ অপারক।
মথুর ভক্ত ছিল বলিয়া নির্বোধ ছিল না
আর এক কথা – মথুরবাবু ঠাকুরকে যেরূপ অকপটে ‘পাঁচসিকে পাঁচ আনা’ ভক্তি-বিশ্বাস করিতেন, তাহা শুনিয়া আমাদের ন্যায় সন্দেহদুষ্ট মন প্রথমেই ভাবিয়া ফেলে – ‘লোকটা বোকা বাঁদর গোছ একটা ছিল আর কি, নতুবা মানুষকে মানুষ এতটা বিশ্বাস-ভক্তি করিতে পারে কখনো? আমরা যদি হইতাম তো একবার দেখিয়া লইতাম – শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেমন করিয়া নিজ চরিত্রবলে অতটা ভক্তি-বিশ্বাসের উদয় আমাদের প্রাণে করিতে পারিতেন!’ যেন প্রাণের ভিতর ভক্তি-বিশ্বাসের উদয় হওয়াটা একটা বিশেষ নিন্দার ব্যাপার। সেজন্য ঠাকুরের নিকট হইতে মথুরবাবুর বিষয় আমরা যতটুকু যেরূপ শুনিয়াছি ও বুঝিয়াছি, তাহাই এখানে পাঠককে বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি যে, মথুরবাবু ঐরূপ স্বভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি আমাদের অপেক্ষা বড় কম বুদ্ধিমান বা সন্দিগ্ধমনা ছিলেন না। তিনিও ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও কার্যকলাপে সন্দেহবান হইয়া তাঁহাকে প্রথম প্রথম প্রতি পদে বড় কম যাচাইয়া লন নাই। কিন্তু করিলে কি হইবে? কখনো, কোন যুগে মানব যেরূপ নয়নগোচর করে নাই, বিজ্ঞাননাদিনী প্রেমাবর্তশালিনী মহা ওজস্বিনী ঠাকুরের ভাব-মন্দাকিনীর গুরুগম্ভীর বেগ মথুরের সন্দেহ-ঐরাবত আর কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? অল্পকালেই স্খলিত, মথিত, ধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হইয়া চিরকালের মতো কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল! কাজেই সর্বতোভাবে পরাজিত মথুর তখন আর কি করিতে পারে? অনন্যমনে ঠাকুরের শ্রীপদে শরণ লইয়াছিল। অতএব মথুরের কথা বলিলেও আমরা ঠাকুরের গুরুভাবেরই কীর্তন করিতেছি, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।
ঠাকুরের প্রতি মথুরের প্রথমাকর্ষণ কি দেখিয়া এবং উহার ক্রমপরিণতি
ঠাকুরের সরল বালকভাব, মধুর প্রকৃতি এবং সুন্দর রূপে মথুর প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে সাধনার প্রথমাবস্থায় ঠাকুরের যখন কখনো কখনো দিব্যোন্মাদাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, যখন শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া এবং আপনার ভিতর তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া তিনি কখনো কখনো আপনাকেই পূজা করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, যখন অনুরাগের প্রবল বেগে তিনি বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রেমপূর্ণ নানারূপ অবৈধ, সাধারণ নয়নে অহেতুক আচরণ দৈনন্দিন জীবনে করিয়া ফেলিয়া ইতর-সাধারণের নিন্দা ও সন্দেহ-ভাজন হইতে লাগিলেন, তখন বিষয়ী মথুরের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ন্যায়পরতা বলিয়া উঠিল, “যাঁহাকে প্রথম দর্শনে সুন্দর সরলপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছি, স্বচক্ষে না দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করা হইবে না।” সেইজন্যই মথুরের গোপনে গোপনে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া ঠাকুরের কার্যকলাপ তন্নতন্ন ভাবে নিরীক্ষণ করা এবং ঐরূপ করিবার ফলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, “যুবক গদাধর অনুরাগ ও সরলতার মূর্তিমান জীবন্ত প্রতিমা; ভক্তি-বিশ্বাসের আতিশয্যেই ঐরূপ করিয়া ফেলিতেছেন!” তাই বুদ্ধিমান বিষয়ী মথুরের তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা যে, “যা রয় সয়, তাই করা ভাল; ভক্তি-বিশ্বাস করাটা ভাল কথা, কিন্তু একেবারে আত্মহারা হইলে চলে কি? উহাতে লোকের নিন্দাভাজন তো হইতে হইবেই, আবার দশে যাহা বলে তাহা না শুনিয়া নিজের মনোমত আচরণ বরাবর করিয়া যাইলে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পাগলও হইবার সম্ভাবনা”; কিন্তু ঐসকল কথা ঐরূপে বুঝাইলেও মথুরের অন্তৰ্নিহিতা সুপ্তা ভক্তি সংসর্গগুণে জাগরিতা হইয়া কখনো কখনো বলিয়া উঠিত, “কিন্তু রামপ্রসাদ প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব সাধককুলেরও তো ভক্তিতে এইরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহারের কথা শুনা গিয়াছে; শ্রীগদাধরের ঐরূপ আচরণ ও অবস্থাও তো সেইরূপ হইতে পারে।” কাজেই, মথুর ঠাকুরের আচরণে বাধা না দিয়া কতদূর কি দাঁড়ায় তাহাই দেখিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন এবং দেখিয়া শুনিয়া পরে যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে তাহাই করিবেন, ইহাই স্থির করিলেন। বিষয়ী প্রভুর অধীনস্থ সামান্য কর্মচারীর উপর ঐরূপ ব্যবহার কম ধৈর্যের পরিচায়ক নহে।
ভক্তির সংক্রামিকা শক্তিতে মথুরের পরিবর্তন
ভক্তির একটা সংক্রামিকা শক্তি আছে। শারীরিক বিকারসকলের ন্যায় মানসিক ভাবসমূহেরও এক হইতে অন্যে সংক্রমণ আমরা নিত্য দেখিতে পাই। কারণ, একই পদার্থের বিকারে একই নিয়মে যে স্থূল ও সূক্ষ্ম সমগ্র জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, ইহা আজকাল আর কেবলমাত্র বৈদিক ঋষিদিগের অনুভূতি দ্বারা প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই – জড়বিজ্ঞানও এ কথা প্রায় প্রমাণিত করিয়া আনিয়াছে। অতএব একের ভক্তিরূপ মানসিক ভাব জাগ্রত হইয়া অন্যের মধ্যে নিহিত সুপ্ত ঐ ভাবকে যে জাগ্রত করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি! এইজন্যই শাস্ত্র সাধুসঙ্গকে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিবার বিশেষ সহায়ক বলিয়া এত করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মথুরের ভাগ্যেও যে ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল, ইহা বেশ অনুমিত হয়। তিনি ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ যতই দিন দিন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভিতরের ভক্তিভাব তাঁহার অজ্ঞাতসারে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার পর পর কার্যসকলে আমরা ইহার বেশ পরিচয় পাইয়া থাকি। তবে বিষয়ী মনের যেমন হয় – এই ভক্তিবিশ্বাসের উদয়, আবার পরক্ষণেই সন্দেহ – এইরূপ বারবার হইয়া অনেকদিন পর্যন্ত দোলায়মান থাকিয়া তবে মথুরের হৃদয়ে ঠাকুরের আসন দৃঢ় ও অবিচলিত হয়, ইহা সুনিশ্চিত। সেইজন্য দেখিতে পাই, ঠাকুরের ব্যাকুল অনুরাগ ও আচরণাদি প্রথম প্রথম মথুরের নয়নে ভক্তির আতিশয্য বলিয়া বোধ হইলেও, ঠাকুরের জীবনে দিন দিন ঐসকলের যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অমনি মথুরানাথের মনে সন্দেহের উদয় – ইঁহার তো বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে না? কিন্তু এ সন্দেহে তাঁহার মনে দয়ারই উদয় হয় এবং সুচিকিৎসকের সহায়ে ঠাকুরের শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া যাহাতে ঐসকল মানসিক বিকার প্রশমিত হয়, মথুর সেই বিষয়েই মনোনিবেশ করেন।
বর্তমান ভাবে শিক্ষিত মথুরের ঠাকুরের সহিত তর্ক-বিচার। প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়া থাকে। লাল জবার গাছে সাদা জবা
ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি মথুরবাবুর মন্দ ছিল না এবং ইংরাজী বিদ্যার সহায়ে পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালী ও ভাবস্রোত মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া “আমিও একটা কেও-কেটা নই, অপর সকলের সহিত সমান” – এইরূপ যে একটা স্বাধীনভাব মানুষের মনে আনিয়া দেয়, সে ভাবটাও মথুরবাবুর কম ছিল না। সেজন্য যুক্তিতর্কাদি দ্বারা ঠাকুরকে ঐরূপে ঈশ্বরভক্তিতে একেবারে আত্মহারা হওয়ার পথ হইতে নিরস্ত করিবার প্রয়াসও আমরা মথুরবাবুর ভিতর দেখিতে পাইয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে ঠাকুর ও মথুরবাবুর জাগতিক ব্যাপারে ঈশ্বরকে স্বকৃত নিয়মের (Law) বাধ্য হইয়া চলিতে হয় কিনা – এ বিষয়ে কথোপকথনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঠাকুর বলিতেন, “মথুর বলেছিল, ‘ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন, তা রদ করবার তাঁরও ক্ষমতা নেই!’ আমি বল্লুম, ‘ও কি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে করলে সে তখনি তা রদ করতে পারে বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে।’ ও কথা সে কিছুতেই মানলে না। বললে, ‘লালফুলের গাছে লালফুলই হয়, সাদা ফুল কখনো হয় না; কেন না, তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন। কই লালফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি এখন করুন দেখি?’ আমি বললুম, ‘তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন, তাও করতে পারেন।’ সে কিন্তু ও কথা নিলে না। তার পরদিন ঝাউতলার দিকে শৌচে গেছি; দেখি যে একটা লাল জবাফুলের গাছে, একই ডালে দুটো ফেঁকড়িতে দুটো ফুল – একটি লাল, আর একটি ধপধপে সাদা, এক ছিটেও লাল দাগ তাতে নেই। দেখেই ডালটি সুদ্ধ ভেঙে এনে মথুরের সামনে ফেলে দিয়ে বল্লুম, ‘এই দেখ।’ তখন মথুর বললে, ‘হাঁ বাবা, আমার হার হয়েছে’!” এইরূপে শারীরিক বিকারেই যে ঠাকুরের মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া ঐরূপ ভক্তির আতিশয্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে, কখনো কখনো এ বিশ্বাসে মথুর যে তাঁহার সহিত নানা বাদানুবাদ করিয়া তাঁহার ঐ ভাব ফিরাইবার চেষ্টা করিতেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।
ঠাকুরের অবস্থা লইয়া মথুরের নিত্য বাধ্য হইয়া আন্দোলন
এইরূপে কতক কৌতূহলে, কতক ঠাকুরের ভাববিহ্ব্লতাটা শারীরিক রোগবিশেষ মনে করিয়া দয়ায়, এবং কখনো কখনো ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থা ঠিক ঠিক ঈশ্বরভক্তির ফল ভাবিয়া বিস্ময় ও ভক্তিপূর্ণ হইয়া বিষয়ী মথুর তাঁহার সহিত ক্রমে ক্রমে অনেক কাল কাটাইতে এবং তাঁহার বিষয়ে অনেক চিন্তা ও আন্দোলনও যে করিতে থাকেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আর স্থির নিশ্চিন্তই বা থাকেন কিরূপে? ঠাকুর যে নবানুরাগের প্রবল প্রবাহে নিত্যই এক এক নূতন ব্যাপার করিয়া বসেন! আজ পূজার আসনে বসিয়া আপনার ভিতরে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শনলাভ করিয়া পূজার সামগ্রীসকল নিজেই ব্যবহার করিয়াছেন, কাল তিন ঘণ্টা কাল ধরিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার আরতি করিয়া মন্দিরের কর্মচারীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, পরশু ভগবানলাভ হইল না বলিয়া ভূমে গড়াগড়ি দিয়া মুখ ঘষড়াইতে ঘষড়াইতে এমন ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়াছেন যে, চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে! এইরূপ এক এক দিনের এক এক ব্যাপারের কত কথাই না ঠাকুরের নিকট আমরা শুনিয়াছি!
‘মহিম্নঃস্তোত্র’ পড়িতে পড়িতে ঠাকুরের সমাধি ও মথুর
একদিন শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর ‘মহিম্নঃস্তোত্র’ পাঠ করিয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে ক্রমে যখন এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, তখন একেবারে অপূর্ব ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন –
অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥ ৩২
– হে মহাদেব, সমুদ্রগভীর পাত্রে বিশাল হিমালয়শ্রেণীর মতো পুঞ্জ পুঞ্জ কালি রাখিয়া, কোনরূপ অসম্ভব পদার্থের কামনা করিলেও যাঁহার তৎক্ষণাৎ তাহা সৃষ্টি বা রচনা করিয়া যাচকের মনোরথ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে – সেই কল্পতরু-শাখার কলম ও পৃথিবী-পৃষ্ঠসদৃশ আয়ত বিস্তৃত কাগজ লইয়া, স্বয়ং বাগ্দেবী সরস্বতীও যদি তোমার অনন্ত মহিমার কথা লিখিয়া শেষ করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলেও কখনো তাহা করিতে পারেন না।
শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে ঠাকুর শিবমহিমা হৃদয়ে জ্বলন্ত অনুভব করিয়া একেবারে বিহ্ব্ল হইয়া স্তব, স্তবের সংস্কৃত, পর পর আবৃত্তি করা প্রভৃতি সকল কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া চিৎকার করিয়া কেবলই বার বার বলিতে লাগিলেন, “মহাদেব গো! তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলব!” আর তাঁহার গণ্ড বহিয়া দরদরিত ধারে নয়নাশ্রু অবিরাম বক্ষে এবং বক্ষ হইতে বস্ত্র ও ভূমিতে পড়িয়া মন্দিরতল সিক্ত করিতে লাগিল! সে ক্রন্দনের রোল, পাগলের ন্যায় গদগদ বাক্য ও অদৃষ্টপূর্ব আচরণে ঠাকুরবাড়ির ভৃত্য ও কর্মচারীরা চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া কেহ বা অবাক হইয়া শেষটা কি হয় দেখিতে লাগিল, কেহ বা ‘ও ছোট ভট্চাজের পাগলামি! আমি বলি আর কিছু – আজ কিছু বেশি বাড়াবাড়ি দেখচি’; কেহ বা ‘শেষে শিবের ঘাড়ে চড়ে বসবে না তো হে? হাত ধরে টেনে আনা ভাল’ ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিল এবং রঙ্গরসের ঘটাও যে হইতে থাকিল, তাহা আর বলিতে হইবে না!
ঠাকুরের কিন্তু বাহিরের হুঁশ আদৌ নাই। শিবমহিমানুভবে তন্ময় মন তখন বাহ্যজগৎ ছাড়িয়া বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে – সেখানে এ জগতের মলিন ভাবরাশি ও কথাবার্তা কখনো পৌঁছে না। কাজেই কে কি ভাবিতেছে, বলিতেছে বা ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহা তাঁহার কানে যাইবে কিরূপে?
মথুরবাবু সেদিন ঠাকুরবাড়িতে; তিনিও ঐ গোলমাল ভট্টাচার্য মহাশয়কে লইয়া শুনিতে পাইয়াই সেখানে উপস্থিত হইলেন। কর্মচারীরা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। মথুরবাবু আসিয়াই ঠাকুরকে ঐ ভাবাপন্ন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ঐ সময়ে কোন কর্মচারী ঠাকুরকে শিবের নিকট হইতে বলপূর্বক সরাইয়া আনার কথা কহায় বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “যাহার মাথার উপর মাথা আছে, সে-ই যেন এখন ভট্টাচার্য মহাশয়কে স্পর্শ করিতে যায়!” কর্মচারীরা কাজেই ভীত হইয়া আর কিছু বলিতে বা করিতে সাহসী হইল না। পরে কতক্ষণ বাদে ঠাকুরের বাহ্য-জগতের হুঁশ আসিল এবং ঠাকুরবাড়ির কর্মচারীদের সহিত মথুরবাবুকে সেখানে দণ্ডায়মান দেখিয়া বালকের ন্যায় ভীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “আমি বেসামাল হয়ে কিছু করে ফেলেছি কি?” মথুরও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “না বাবা, তুমি স্তব পাঠ করছিলে; পাছে কেহ না বুঝিয়া তোমায় বিরক্ত করে, তাই আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম!”
ঠাকুরের নিকট অপরের সহজে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত
ঠাকুর আমাদের নিকট একদিন তাঁহার সাধনকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তখন তখন (সাধনকালে) যারা এখানে আসত, এখানকার সঙ্গে থেকে তাদের অতি শীঘ্র ঈশ্বর-উদ্দীপন হতো। বরানগর থেকে দুজন আসত – তারা জেতে খাট, কৈবত্ কি তামলি এমনি একটা; বেশ ভাল; খুব ভক্তি-বিশ্বাস করত ও প্রায় আসত। একদিন পঞ্চবটীতে তাদের সঙ্গে বসে আছি – আর তাদের ভেতর একজনের একটা অবস্থা হলো! দেখি বুকটা লাল হয়ে উঠেছে, চোখ ঘোর লাল, ধারা বেয়ে পড়ছে, কথা কইতে পাচ্ছে না, দাঁড়াতে পাচ্ছে না; দুবোতল মদ খাইয়ে দিলে যেমন হয়, তেমনি! কিছুতেই তার আর সে ভাব ভাঙে না! তখন ভয় পেয়ে মাকে বলি, ‘মা, একে কি করলি? লোকে বলবে, আমি কি করে দিয়েছি! ওর বাপ-টাপ সব বাড়িতে আছে; এখনই বাড়ি যেতে হবে।’ তার বুকে হাত বুলিয়ে দিই আর মাকে ঐরকম বলি। তবে কতক্ষণ বাদে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ি যায়।”
মথুরের ঠাকুরকে একাধারে শিব-শক্তিরূপে দর্শন
ঠাকুরের জ্বলন্ত জীবনের সংস্পর্শে মথুরবাবুরও যে ঐরূপ একটা অদ্ভুত অবস্থার একসময়ে উদয় হইয়া তাঁহার বিশ্বাস-ভক্তি সহস্রগুণে বর্ধিত হইয়া উঠে, ইহা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। সর্বদাই আপন ভাবে বিভোর ঠাকুর একদিন তাঁহার ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে যে লম্বা বারান্দাটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আছে, তথায় আপন মনে গোঁ-ভরে পদচারণ করিতেছিলেন। ঠাকুরবাড়ি ও পঞ্চবটীর মধ্যে যে একটি পৃথক বাড়ি আছে, যাহাকে এখনো ‘বাবুদের কুঠি’ বলিয়া ঠাকুরবাড়ির কর্মচারীরা নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহারই একটি প্রকোষ্ঠে মথুরবাবু তখন একাকী আপন মনে বসিয়াছিলেন। মথুরবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে ঠাকুর যেখানে বেড়াইতেছিলেন সে স্থানটির ব্যবধান বড় বেশি না হওয়ায় বেশ নজর হইতেছিল। কাজেই মথুরবাবু কখনো ঠাকুরের ঐরূপ গোঁ-ভরে বিচরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, আবার কখনো বা বিষয়-সম্বন্ধীয় এ কথা সে কথার মনে মনে আন্দোলন করিয়া ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করিতেছিলেন। মথুরবাবু যে বৈঠকখানায় বসিয়া ঠাকুরকে মাঝে মাঝে ঐরূপে লক্ষ্য করিতেছেন, ঠাকুর তাহা আদৌ জ্ঞাত ছিলেন না। আর জানা থাকিলেই বা কি? – দুই জনের সামাজিক, সাংসারিক ও অন্য সর্বপ্রকার অবস্থার অন্তর এতদূর যে, জানা থাকিলেও কেহ কাহারও জন্য বড় বেশি ব্যতিব্যস্ত হইবার কারণ ছিল না। সে পক্ষে বরং ঠাকুরই ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় ও অন্যমনা না থাকিলে, মথুরবাবুর কথা টের পাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া সে স্থান হইতে সরিয়া যাইবার কথা ছিল। কারণ, ধনী, মানী, বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু, যাঁহাকে ঠাকুরবাড়ির ও রানীর সমস্ত বিষয়ের মালিক বলিলেও চলে এবং যাঁহার সুনয়নে পড়িয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর এখনো ঐ স্থান হইতে তাড়িত হন নাই, তাঁহার সম্মুখে একজন সামান্য নগণ্য দরিদ্র পূজক ব্রাহ্মণ, যাঁহাকে লোকে তখন নির্বোধ, উন্মাদ, অনাচারী বলিয়াই জানিত ও বিদ্রূপাদি করিতেও ছাড়িত না, কেমন করিয়া ভীত সঙ্কুচিত না হইয়া থাকে বল? কিন্তু ঘটনা অভাবনীয়, অচিন্তনীয় হইয়া দাঁড়াইল – মথুরবাবুই হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়াইয়া ঠাকুরের নিকট আগমন করিলেন এবং প্রণত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন!
ঠাকুর বলেন, “বললুম, তুমি এ কি করচ? তুমি বাবু, রানীর জামাই, লোকে তোমায় এমন করতে দেখলে কি বলবে? স্থির হও, ওঠ। সে কি তা শোনে! তারপর ঠাণ্ডা হয়ে সকল কথা ভেঙে বললে – অদ্ভুত দর্শন হয়েছিল! বললে – ‘বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখচি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা! আর যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্চ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথম ভাবলুম, চোখের ভ্রম হয়েছে; চোখ ভাল করে পুঁছে ফের দেখলুম – দেখি তাই! এইরূপ যতবার করলুম দেখলুম তাই।’ এই বলে আর কাঁদে! আমি বললুম, ‘আমি তো কই কিছু জানি না, বাবু’ – কিন্তু সে কি শোনে! ভয় হলো, পাছে এ কথা কেউ জেনে গিন্নিকে, রানী রাসমণিকে বলে দেয়। সেই বা কি ভাববে – হয়তো বলবে কিছু গুণ টুন করেছে! অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলায় তবে সে ঠাণ্ডা হয়! মথুর কি সাধে এতটা করত – ভালবাসত? মা তাকে অনেক সময় অনেক রকম দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল। মথুরের ঠিকুজিতে কিন্তু লেখা ছিল, বাবু, তার ইষ্টের তার উপর এতটা কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীর ধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে।”
ঐ দর্শনের ফল
এখন হইতে মথুরের বিশ্বাস অনেকটা পাকা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, ইহাই তাঁহার প্রথম আভাস পাওয়া যে, প্রথম দর্শনেই যাঁহার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, অপরে না বুঝিয়া নিন্দা করিলেও যাঁহার মনোভাব ও আচরণ তিনি অনেক সময় ধরিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন, সে ঠাকুর বাস্তবিকই সামান্য নহেন; জগদম্বা তাঁহারই প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুরের শরীরের ভিতরে সাক্ষাৎ বর্তমান রহিয়াছেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে হয়, মন্দিরের পাষাণময়ীই বা শরীর ধারণ করিয়া তাঁহার জন্মপত্রিকার কথামত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন! – এখন হইতে ঠাকুরের সহিত মথুরবাবুর ঘনিষ্ঠতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল।
মথুরের মহাভাগ্য-সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ
মথুরের বাস্তবিকই মহাভাগ্যোদয় হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন, যতদিন শরীর থাকিবে ততদিন ভাল-মন্দ দুই প্রকার কর্ম মানুষকে করিতে হইবেই – সাধারণ মানুষের তো কথাই নাই, মুক্ত পুরুষদিগেরও! সাধারণ মানব স্বয়ং-ই নিজকৃত সুকৃত-দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে। এখন মুক্ত পুরুষদিগের শরীরকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ করে কে? তাঁহারা তো আর নিজে উহা করিতে পারেন না? কারণ, সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিবে যে অভিমান-অহঙ্কার, তাহা তো চিরকালের মতো তাঁহাদের ভিতর হইতে উড়িয়া-পুড়িয়া গিয়াছে; তবে উহা করে কে? আবার কর্মফল তো অবশ্যম্ভাবী এবং মুক্ত পুরুষদিগের শরীরটা যতদিন জীর্ণ পত্রের মতো পড়িয়া না যায়, ততদিন তো উহার দ্বারা ভাল-মন্দ কতকগুলি কাজ হইবেই হইবে। শাস্ত্র এখানে বলেন – যে সকল বদ্ধ পুরুষেরা তাঁহাদের সেবা করে, ভালবাসে, তাহারাই মুক্তাত্মাদিগের কৃত শুভকর্মের এবং যাহারা তাঁহাদের দ্বেষ করে, তাহারাই তাঁহাদের শরীরকৃত অশুভ কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।1 সাধারণ মুক্ত পুরুষদিগের সেবার দ্বারাই যদি ঐরূপ ফললাভ হয়, তবে ঈশ্বরাবতারদিগের ভক্তিপ্রীতিপূর্ণ সেবার যে কতদূর ফল তাহা কে বলিতে পারে?
1. বেদান্তসূত্র, ৩য় অধ্যায়, ৩য় পাদ, ২৬ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে – “তথা শাট্যায়নিনঃ পঠন্তি – ‘তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্’ ইতি। তথৈব কৌষীতকিনঃ – ‘তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতম্’ ইতি।”
পরবর্তী ভাষ্যেও ঐ বিষয়ের উল্লেখ আছে।
ঠাকুরের দিন দিন গুরুভাবের অধিকতর বিকাশ ও মথুরের তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া অনুভব
দিনের পর দিন যতই চলিয়া যাইতে লাগিল, মথুরবাবুও ততই ঠাকুরের গুরুভাবের পরিচয় স্পষ্ট – স্পষ্টতর পাইতে থাকিয়া, ঠাকুরের প্রতি অবিচলা ভক্তি করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে অনেক ঘটনা হইয়া গেল; যথা – ভগবদ্বিরহে ঠাকুরের বিষম গাত্রদাহ ও তাহার চিকিৎসা; ব্রাহ্মণী ভৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন ও বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মথুরবাবুর দ্বারা আহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে ঠাকুরের অবতারত্ব-প্রতিপাদন, মহাবৈদান্তিক জ্ঞানী তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ, ঠাকুরের বৃদ্ধা জননীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও বাস ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের দিন হইতে মথুরানাথ ঠাকুরের জীবনের প্রায় সকল দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সহিতই বিশেষভাবে সম্বদ্ধ। ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য মথুর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও ডাক্তার ৺মহেন্দ্রলাল সরকারকে দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; ঠাকুরের শ্রীশ্রীজগদম্বাকে, পশ্চিমী স্ত্রীলোকেরা যেরূপ পাঁইজর প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করেন, সেইরূপ পরাইবার সাধ হইল – মথুর তৎক্ষণাৎ তাহা গড়াইয়া দিলেন; ঠাকুর বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখীভাব-সাধনকালে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বেশভূষা করিবেন ইচ্ছা হইল – মথুরানাথ তৎক্ষণাৎ এক ‘স্যুট’ ডায়মণ্ডকাটা অলঙ্কার, বেনারসী শাড়ি, ওড়না প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন। পানিহাটি উৎসব দেখিবার ঠাকুরের সাধ জানিয়া মথুর তৎক্ষণাৎ তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই যে ক্ষান্ত থাকিলেন তাহা নহে, পাছে সেখানে ভিড়ে-ভাড়ে তাঁহার কষ্ট হয় ভাবিয়া নিজে গুপ্তভাবে দারোয়ান সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের শরীররক্ষা করিতে যাইলেন। এইরূপে প্রতি ব্যাপারে মথুরের অদ্ভুত সেবার কথা যেমন আমরা একদিকে শুনিয়াছি, তেমনি আবার অপরদিকে নষ্টস্বভাবা স্ত্রীলোকদিগকে লাগাইয়া ঠাকুরের মনে অসৎ ভাবের উদয় হয় কিনা পরীক্ষা করার কথা, ঠাকুরবাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তি ঠাকুরের নামে সমস্ত লিখিয়া-পড়িয়া দিবার প্রস্তাবে ঠাকুর ভাবাবস্থায় “কি! আমাকে বিষয়ী করতে চাস?” – বলিয়া মথুরের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে যাইবার কথা, জমিদারি-সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া নরহত্যার অপরাধে রাজদ্বারে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবার ভয়ে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার-কামনায় ঠাকুরের নিকট সকল দোষ স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া মথুরের ঐ বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাও ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। ঐসকল ঘটনাবলী হইতেই আমরা মথুরবাবুর মনে যে ঠাকুরের প্রতি ক্রমে ক্রমে ভক্তি দৃঢ়া অচলা হইয়া আসিতেছিল ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। আর ঐরূপ না হইয়া অন্যরূপই বা হয় কিরূপে? ঠাকুরের অদ্ভুত অলৌকিক দেবদুর্লভ স্বভাব যেমন একদিকে মথুরের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিনের পর দিন অধিকতর সমুজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল, অপরদিকে তেমনি ঠাকুরের অপার অহেতুক ভালবাসা মথুরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। মথুর দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিয়াও ইঁহাকে ত্যাগীর ভাব হইতে হটাইতে পারিলাম না, সুন্দরী নারীগণের দ্বারা ইঁহার মনে বিকার উপস্থিত করিতে পারিলাম না, পার্থিব মান-যশেও – কারণ মানুষকে মানুষ ভগবান বলিয়া পূজা করা অপেক্ষা অধিক মান আর কি দিতে পারে – ইঁহাকে কিছুমাত্র টলাইতে বা অহঙ্কৃত করিতে পারিলাম না, পার্থিব কোন বিষয়েই ইনি প্রার্থী নন – অথচ তাঁহার চরিত্রের সমস্ত দুর্বলতার কথা জানিয়াও তাঁহাকে ঘৃণা করিতেছেন না, আপনার হইতেও আপনার করিয়া ভালবাসিতেছেন, বিপদ হইতে বার বার উদ্ধার করিতেছেন, আর কিসে তাঁহার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয় তাহাই চিন্তা করিতেছেন! – ইহার কারণ কি? বুঝিলেন, ইনি মনুষ্যশরীরধারী হইলেও ‘যে দেশে রজনী নাই’ সেই রাজ্যের লোক। ইঁহার ত্যাগ অদ্ভুত, সংযম অদ্ভুত, জ্ঞান অদ্ভুত, ভক্তি অদ্ভুত, সকল প্রকার কর্ম অদ্ভুত এবং সর্বোপরি তাঁহার ন্যায় দুর্বল অথচ অহঙ্কৃত জীবের উপর ইঁহার করুণা ও ভালবাসা অদ্ভুত!
আর একটি কথাও মথুরানাথ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন – এ অদ্ভুত চরিত্রের মাধুর্য! এমন অলৌকিক ঐশী শক্তির বিকাশ ইঁহার ভিতর দিয়া হইলেও, ইনি নিজে যে বালক, সেই বালক! এতটুকু অহঙ্কার নাই – এ কি চমৎকার ব্যাপার! নিজের ভিতর যে কোন ভাব উঠুক না কেন, পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় তাঁহার এতটুকু লুকানো নাই! ভিতরে বাহিরে নিরন্তর এক ভাব! যাহা মনে, তাহাই অকপটে মুখে ও কার্যে প্রকাশ – অথচ অন্যের যাহাতে কোনরূপ হানি হইতে পারে, তাহা কখনো বলা নাই – নিজের শারীরিক কষ্ট হইলেও তাহা বলা নাই! ইহা কি মানবে সম্ভব?
মথুরের ভক্তিবৃদ্ধি দেখিয়া হালদার পুরোহিত
মথুরানাথের কালীঘাটের হালদার পুরোহিত, ঠাকুরের প্রতি মথুরবাবুর অবিচলা ভক্তি দেখিয়া হিংসায় জরজর; ভাবে – ‘লোকটা বাবুকে কোনরূপ গুণটুন্ করিয়া ঐরূপ বশীভূত করিয়াছে।’ ভাবে – ‘তাই তো, বাবুটাকে হাত করবার আমার এতকালের চেষ্টাটা এই লোকটার জন্য সব পণ্ড? আবার সরল বালকের ভান দেখায়। যদি এতই সরল তো বলে দিক ‘বশীকরণের’ ক্রিয়াটা। আমার যত বিদ্যা সব ঝেড়ে ঝুড়ে বাবুটা একটু বাগে আসছিল, এমন সময় এ আপদ কোথা হতে এল?’
এদিকে মথুরের ভক্তিবিশ্বাস যতই বাড়িতে থাকিল, ততই ঠাকুরের সঙ্গে সদাসর্বক্ষণ কি করিয়া থাকিতে পাইব, কি করিয়া তাঁহার আরও অধিক সেবা করিতে পাইব – এই সকল চিন্তাই বলবতী হয়। সেজন্য মাঝে মাঝে ঠাকুরকে অনুরোধ-নির্বন্ধ করিয়া কলিকাতায় জানবাজারের বাটীতে নিজের কাছে আনিয়া রাখেন; অপরাহ্ণে ‘বাবা, চল বেড়াইয়া আসি’ বলিয়া সঙ্গে করিয়া গড়ের মাঠ প্রভৃতি কলিকাতার নানাস্থানে বেড়াইয়া লইয়া আসেন। ‘বাবাকে কি যাহাতে তাহাতে খাইতে দেওয়া চলে?’ – ভাবিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের এক স্যুট বাসন নূতন গড়াইয়া তাহাতে ঠাকুরকে অন্ন-পানীয় দেন; উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিচ্ছদ প্রভৃতি পরাইয়া দেন, আর বলেন – ‘বাবা, তুমিই তো সকলের (বিষয়ের) মালিক, আমি তোমার দেওয়ান বই তো নয়; এই দেখ না, তুমি সোনার থালে, রূপার বাটি-গেলাসে খাইবার পর ঐসকলের দিকে আর না দেখিয়া ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলে, আর আমি আবার তুমি খাইবে বলিয়া সে সমস্ত মাজাইয়া ঘষাইয়া তুলিয়া রাখি, চুরি গেল কিনা দেখি, ভাঙা ফুটা হইল কিনা খবর রাখি, আর এইসব লইয়াই ব্যস্ত থাকি।’
বারাণসী শালের দুর্দশা
এই সময় এক জোড়া বেনারসী শালের দুর্দশার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। মথুর উহা সহস্র মুদ্রা মূল্যে ক্রয় করেন এবং অমন ভাল জিনিস আর কাহাকে দিব ভাবিয়া, নিজের হাতে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে উহা জড়াইয়া দিয়া মহানন্দ লাভ করেন। শালজোড়াটি বাস্তবিকই মূল্যবান – কারণ, উহার তখনকার (৫০ বৎসর পূর্বের) দামই যখন অত ছিল, তখন বোধ হয় সে প্রকার জিনিস এখন আর দেখিতেই পাওয়া যায় না। শালখানি পরিয়া ঠাকুর প্রথম বালকের মতো মহা আনন্দিত হইয়া এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, বার বার উহা নিজে দেখিতে লাগিলেন এবং অপরকে ডাকিয়া দেখাইতে ও মথুরবাবু উহা এত দরে কিনিয়া দিয়াছেন ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বালকের ন্যায় ঠাকুরের মনে অন্য ভাবের উদয় হইল! ভাবিলেন – “এতে আর আছে কি? কতকগুলো ছাগলের লোম বই তো নয়? যে পঞ্চভূতের বিকারে সকল জিনিস, সেই পঞ্চভূতেই তো এটাও তৈরি হয়েছে; আর শীতনিবারণ – তা লেপ-কম্বলেও যেমন হয়, এতেও তেমনি; অন্যসকল জিনিসের ন্যায় এতেও সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না; বরং গায়ে দিলে মনে হয় আমি অপর সকলের চেয়ে বড়, আর অভিমান অহঙ্কার বেড়ে মানুষের মন ঈশ্বর থেকে দূরে গিয়ে পড়ে! এতে এত দোষ!” এই সকল কথা ভাবিয়া শালখানি ভূমিতে ফেলিয়া – ইহাতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, ‘থু, থু’ বলিয়া থুতু দিতে ও ধূলিতে ঘষিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া পুড়াইবার উপক্রম করিলেন! এমন সময় কে সেখানে আসিয়া পড়িয়া উহা তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার করে! মথুরবাবু শালখানির ঐরূপ দুর্দশা হইয়াছে জানিয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। বলিয়াছিলেন – ‘বাবা বেশ করেছেন!’
ঠাকুরের নির্লিপ্ততা
উপরে লিখিত ঘটনাদি হইতেই বেশ বুঝা যায়, মথুরবাবু ঠাকুরকে নানা ভোগ-সুখ ও আরামের ভিতর রাখিবার চেষ্টা করিলেও ঠাকুরের মন কত উচ্চে, কোথায় নিরন্তর থাকিত! যেখানেই থাকুন না কেন, এ মন সর্বদা আপন ভাবে বিভোর! অপর সকল মন যেখানে কেবল অন্ধকারের উপর অন্ধকাররাশিই পুঞ্জীকৃত দেখে, সেখানে এ মন দেখে – আলোয় আলো – ছায়াবিহীন হ্রাসবৃদ্ধিরহিত আলো – যে আলোর সম্মুখে চন্দ্র-সূর্য-তারকার উজ্জ্বলতা, বিদ্যুতের চকমকানি, অগ্নির তো ‘কা কথা’ – সব মিটমিটে, প্রায় অন্ধকারতুল্য! সেই আলোকময় রাজ্যেই এ মনের নিরন্তর থাকা! আর এই হিংসাদ্বেষকপটতাপূর্ণ কামক্রোধের চির-আবাসভূমি এই রাজ্যে, যেন এ মনের দু-দিনের জন্য করুণায় বেড়াইতে আসা, এইমাত্র! অতএব মথুরবাবুর ভোগসুখ-বিলাসিতাপূর্ণ জানবাজারের বাড়িতে থাকিলেও, যে ঠাকুর সেই ঠাকুর – নির্লিপ্ত, নিরহঙ্কার, আপন ভাবে আপনি নিশিদিন মাতোয়ারা!
হালদার পুরোহিতের শেষ কথা
জানবাজারের বাড়িতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর একদিন অর্ধবাহ্য দশায় পড়িয়া আছেন, নিকটে কেহ নাই। ঠাকুরের সমাধি ভাঙিতেছে; বাহ্যজগতের অল্পে অল্পে হুঁশ আসিতেছে। এমন সময় পূর্বোক্ত হালদার পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে একাকী তদবস্থ দেখিয়াই ভাবিল, ইহাই সময়। নিকটে যাইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বার বার বলিতে লাগিল – ‘অ বামুন, বল্ না – বাবুটাকে কি করে হাত করলি? কি করে বাগালি, বল না? ঢঙ করে চুপ করে রইলি যে? বল্ না?’ বার বার ঐরূপ বলিলেও ঠাকুর যখন কিছুই বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না – কারণ, ঠাকুরের তখন কথা কহিবার মতো অবস্থাই ছিল না – তখন কুপিত হইয়া ‘যা শালা বললি না’ বলিয়া সজোরে পদাঘাত করিয়া অন্যত্র গমন করিল। নিরভিমান ঠাকুর, মথুরবাবু এ কথা জানিতে পারিলে ক্রোধে ব্রাহ্মণের উপর একটা বিশেষ অত্যাচার করিয়া বসিবে, বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে – কিছুকাল পরে – অন্য অপরাধে মথুরবাবুর কোপে পড়িয়া ব্রাহ্মণ তাড়িত হইলে একদিন কথায় কথায় মথুরানাথকে ঐ কথা বলেন। শুনিয়া মথুর ক্রোধে দুঃখে বলিয়াছিলেন, “বাবা, এ কথা আমি আগে জানলে বাস্তবিকই ব্রাহ্মণের মাথা থাকত না।”
মথুরানাথ ও তৎপত্নী জগদম্বা দাসীর ঠাকুরের উপর ভক্তি ও ঠাকুরের ঐ পরিবারের সহিত ব্যবহার
ঠাকুরের গুরুভাবে অপার করুণার কথা সস্ত্রীক মথুরবাবু প্রাণে প্রাণে যে কতদূর অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে যে কতদূর আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি – ঠাকুরের নিকট তাঁহাদের উভয়ের কোন কথা গোপন না রাখায়। উভয়েই জানিতেন ও বলিতেন, “বাবা মানুষ নন; ওঁর কাছে কথা লুকিয়ে কি করব? উনি সকল জানতে পারেন, পেটের কথা সব টের পান!” তাঁহারা উভয়ে যে ঐ প্রকারে কথার কথা মাত্র বলিতেন, তাহা নহে – কার্যতঃ সকল বিষয়ে ঠিক ঠিক ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতেন। বাবাকে লইয়া একত্রে আহার-বিহার এবং এক শয্যায় কতদিন শয়ন পর্যন্ত উভয়ে করিয়াছেন। বাবা সকল সময়ে সর্বাবস্থায় অন্দরে অবাধ গমনাগমন করিবেন, তাহাতে কি? উনি অন্দরে না যাইলেই বা কি? – বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ সকলের সকল প্রকার মনোভাব যে জানেন, ইহার পরিচয় তাঁহারা অনেক সময় পাইয়াছেন। আর পুরুষের, স্ত্রীলোকদের সহিত মিশিবার যে প্রধান অনর্থ – মানসিক বিকার, সে সম্বন্ধে বাবাকে ঘরের দেয়াল বা অন্য কোন অচেতন পদার্থবিশেষ বলিলেও চলে! অন্দরের কোন স্ত্রীলোকেরই মনে তো বাবাকে দেখিয়া, অপর কোন পুরুষকে দেখিয়া যেরূপ সঙ্কোচ-লজ্জার ভাব আসে, সেরূপ আসে না। মনে হয় যেন তাঁহাদেরই একজন, অথবা একটি পাঁচ বছরের ছেলে! কাজেই সখীভাবে ভাবিত ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা পরিয়া ৺দুর্গাপূজার সময়ে অন্দরের স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাহিরে আসিয়া প্রতিমাকে চামর-বীজন করিতেছেন, কখনো বা কোন যুবতীর স্বামীর আগমনে তাহাকে সাজাইয়া-গুছাইয়া বেশভূষা পরাইয়া স্বামীর সহিত কিভাবে কথাবার্তা কহিতে হয়, তাহা কানে কানে শিখাইতে শিখাইতে শয়নমন্দিরে স্বামীর পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া আসিতেছেন – এরূপ অনেক কথা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে জানিয়া আমরা ইঁহাদের ঠাকুরের উপর কি এক অপূর্ব ভাব ছিল, ভাবিয়া অবাক হইয়া থাকি! ঠাকুরের গুরুভাবে এই সকল স্ত্রীলোকদিগের মনে তাঁহার প্রতি দেবতাজ্ঞান যেমন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি আবার তাঁহার অহেতুক ভালবাসার বিশেষ পরিচয় পাইয়া ইঁহারা তাঁহাকে কতদূর আপনার হইতেও আপনার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কতদূর নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকটে উঠা-বসা ও অন্য সকল চেষ্টা ব্যবহারাদি করিতেন, তাহা আমরা কল্পনাতেও ঠিক ঠিক আনিতে পারি না!
ঠাকুরের বিপরীত ভাবের একত্র সমাবেশ
একদিকে ঠাকুরের মথুরবাবুর বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত যেমন অমানুষী কামগন্ধহীন স্বার্থমাত্রশূন্য সখীর ন্যায় ভালবাসার প্রকাশ, অপরদিকে আবার বাহিরে পুরুষদিগের নিকট, পণ্ডিতমণ্ডলীর মাঝে দিব্যজ্ঞান ও অনুপম বুদ্ধির সহিত ব্যবহারাদি দেখিলে মনে হয়, এ বহু-বিপরীত ভাবের একত্র সম্মিলন তাঁহার ভিতরে কিরূপে হইয়াছিল? এ বহুরূপী ঠাকুর কে?
দক্ষিণেশ্বরে বিগ্রহমূর্তি ভগ্ন হওয়ায় বিধান লইতে পণ্ডিতসভার আহ্বান
দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে ৺রাধাগোবিন্দের বিগ্রহমূর্তিদ্বয় তখন প্রতিদিন প্রাতে পার্শ্বের শয়নঘর হইতে মন্দিরমধ্যে সিংহাসনে আনিয়া বসানো হইত এবং পূজা-ভোগ-রাগাদির অন্তে দুই প্রহরে পুনরায় শয়নমন্দিরে বিশ্রামের জন্য রাখিয়া আসা হইত। আবার অপরাহ্ণে বেলা চারিটার পর সেখান হইতে সিংহাসনে আনিয়া পুনরায় সান্ধ্য আরাত্রিক ও ভোগ-রাগাদির অন্তে রাত্রে রাখিয়া আসা হইত। মন্দিরের মর্মর পাথরের মেঝে একদিন জল পড়িয়া পিছল হওয়ায়, ঠাকুর লইয়া যাইবার সময় পড়িয়া গিয়া পূজক ব্রাহ্মণ ৺গোবিন্দজীর মূর্তিটির পা ভাঙিয়া ফেলিলেন! একেবারে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পূজারী তো নিজে আঘাত পাইলেন, আবার ভয়ে কম্পমান! বাবুদের নিকট সংবাদ পৌঁছিল। কি হইবে? ভাঙা বিগ্রহে তো পূজা চলে না – এখন উপায়? রানী রাসমণি ও মথুরবাবু উপায়-নির্ধারণের জন্য শহরের সকল খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সসম্ভ্রমে আহ্বান করিয়া সভা করিলেন। যে সকল পণ্ডিতেরা কার্যবশতঃ উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাঁহাদেরও মতামত সংগৃহীত হইতে লাগিল। একেবারে হইচই ব্যাপার এবং পণ্ডিতবর্গের সম্মানরক্ষার জন্য বিদায়-আদায়ে টাকারও শ্রাদ্ধ! পণ্ডিতেরা পাঁজি-পুঁথি খুলিয়া বার বার বুদ্ধির গোড়ায় নস্য দিয়া বিধান দিলেন – ‘ভগ্ন মূর্তিটি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া হউক এবং তৎস্থলে অন্য নূতন মূর্তি স্থাপিত হউক।’ কারিগরকে মূর্তিগঠনের আদেশ দেওয়া হইল।
ঠাকুরের মীমাংসা ও ঐ বিষয়ের শেষ কথা
সভাভঙ্গকালে মথুরবাবু রানীমাতাকে বলিলেন, “ছোট ভট্টাচার্য মহাশয়কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা তো হয় নাই? তিনি কি বলেন জানিতে হইবে” – বলিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন! ঠাকুর ভাবমুখে বলিতে লাগিলেন, “রানীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তার জায়গায় এনে বসানো হতো – না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো? এখানেও সেই রকম করা হোক – মূর্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হচ্ছে তেমন পূজা করা হোক। ত্যাগ করতে হবে কিসের জন্য?” সকলে ব্যবস্থা শুনিয়া অবাক! তাই তো, কাহারও মাথায় তো এ সহজ যুক্তিটি আসে নাই? মূর্তিটি যদি ৺গোবিন্দজীর দিব্য আবির্ভাবে জীবন্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে সে আবির্ভাব তো ভক্তের হৃদয়ের গভীর ভক্তি-ভালবাসা-সাপেক্ষ, ভক্তের প্রতি কৃপা বা করুণায় হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা থাকিলে সে আবির্ভাব ভগ্ন মূর্তিতেই বা না হইতে পারে কেন? মূর্তিভঙ্গের দোষাদোষ তো আর সে আবির্ভাবকে স্পর্শ করিতে পারে না! তারপর, যে মূর্তিটিকে শ্রীভগবানের এতকাল পূজা করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা দিয়া আসিয়াছি, আজ তাহার অঙ্গবিশেষের হানি হওয়াতে যথার্থ ভক্তের হৃদয় হইতে কি ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে হানি হইতে পারে? আবার বৈষ্ণবাচার্যগণ ভক্তকে ঠাকুরের আত্মবৎ সেবা করিতেই উপদেশ দিয়া থাকেন। আপনি যখন যে অবস্থায় যাহা করিতে ভালবাসি, ঠাকুরও তাহাই ভালবাসেন ভাবিয়া সেইরূপ করিতেই বলেন। সে পক্ষ হইতেও মূর্তিটির ত্যাগের ব্যবস্থা হইতে পারে না। অতএব স্মৃতিতে যে ভগ্ন মূর্তিতে পূজাদি করিবে না বলিয়া বিধান আছে, তাহা প্রেমহীন, ভক্তিপথে সবে মাত্র অগ্রসর ভক্তের জন্যই নিশ্চয়। যাহা হউক, অভিমানী পণ্ডিতবর্গের কাহারও কাহারও ঠাকুরের মীমাংসার সহিত মতভেদ হইল, কেহ বা আবার মতভেদপ্রকাশে বিদায়-আদায়ের ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া স্বীয় মত পরিষ্কার প্রকাশ করিলেন না! আর যাঁহারা পাণ্ডিত্যের সহায়ে একটু যথার্থ জ্ঞান-ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঠাকুরের ঐ মীমাংসা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পরে ঠাকুর স্বহস্তে মূর্তিটি জুড়িয়া দিলেন ও তাঁহার পূজাদি পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। কারিগর নূতন মূর্তি একটি গড়িয়া আনিলে, উহা ৺গোবিন্দজীর মন্দিরমধ্যে একপার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইল মাত্র, উহার প্রতিষ্ঠা আর করা হইল না। রানী রাসমণি ও মথুরবাবু পরলোকগমন করিলে, তাঁহাদের বংশধরগণের কেহ কেহ কখনো কখনো ঐ নূতন মূর্তির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন না কোন সাংসারিক বিঘ্ন সেই সেই কালে উপস্থিত হওয়ায় ঐ কার্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাজেই ৺গোবিন্দজীর নূতন মূর্তিটি এখনো সেইভাবেই রাখা আছে।
তৃতীয় খণ্ড – সপ্তম অধ্যায়: গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা
জানবাজারে মথুরের বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া ৺দুর্গোৎসবের কথা
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥
– গীতা, ১০।২০
এ বৎসর মথুরানাথের জানবাজারের বাটীতে ৺দুর্গোৎসবে বিশেষ আনন্দ। কারণ, শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় বৎসরে বৎসরে আবালবৃদ্ধবনিতার যে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ, তাহা তো আছেই, তাহার উপর ‘বাবা’ আবার কয়েকদিন হইতে মথুরের বাটী পবিত্র করিয়া ঐ আনন্দ সহস্রগুণে বর্ধিত করিয়াছেন। কাজেই আনন্দের আর পরিসীমা নাই। মা-র নিকটে বালক যেমন আনন্দে আটখানা হইয়া নির্ভয়ে আবদার, অনুরোধ ও হেতুরহিত হাস্য-নৃত্যাদির চেষ্টা করিয়া থাকে, নিরন্তর ভাবাবেশে প্রতিমাতে জগন্মাতার সাক্ষাৎ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ‘বাবার’ সেইরূপ অপূর্ব আচরণে, প্রতিমা বাস্তবিকই জীবন্ত জ্যোতির্ময়ী হইয়া যেন হাসিতেছেন! আর ঐ প্রতিমাতে মা-র আবেশ ও ঠাকুরের দেবদুর্লভ শরীর-মনে মা-র আবেশ একত্র সম্মিলিত হওয়ায় পূজার দালানের বায়ুমণ্ডল কি একটা অনির্বচনীয়, অনির্দেশ্য সাত্ত্বিক ভাবপ্রকাশে পূর্ণ বলিয়া অতি জড়মনেরও অনুভূতি হইতেছে! দালান জম জম করিতেছে – উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! আর বাটীর সর্বত্র যেন সেই অদ্ভুত প্রকাশে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে!
হইবারই কথা। ধনী মথুরের রাজসিক ভক্তি, ঘর দ্বার ও মা-র প্রতিমা বিচিত্র সাজে সাজাইতে, পত্র পুষ্প ফল মূল মিষ্টান্নাদি পূজার দ্রব্যসম্ভারের অপর্যাপ্ত আয়োজনে এবং নহবতাদি বাদ্যভাণ্ডের বাহুল্যে মনোনিবেশ করিয়া বাহিরের কিছুরই যেমন ত্রুটি রাখে নাই, তেমনি আবার এ অদ্ভুত ঠাকুরের অলৌকিক দেবভাব বাহিরের ঐ জড় জিনিসসকলকে স্পর্শ করিয়া উহাদের ভিতর সত্য সত্যই একটা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছে! কাজেই তুষারমণ্ডিত হিমালয়বক্ষে চিরশ্যামল দেবদারুকুঞ্জের গম্ভীর সৌন্দর্যে সাধু-তপস্বীর গৈরিক বসন যে শান্তিময় শোভা আনয়ন করে, সুন্দরী রমণীর কোলে স্তন্যপায়ী সুন্দর শিশু যে করুণামাখা সৌন্দর্যের বিস্তার করে, সুন্দর মুখে পবিত্র মনোভাব যে অপূর্ব প্রকাশ আনিয়া দেয়, মথুরবাবুর মহাভাগ্যোদয়ে তাঁহার ভবনে আজ সেই সৌন্দর্যের বিচিত্র সমাবেশ! পূজাসংক্রান্ত নানা কার্যের সুবন্দোবস্তে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিলেও বাবু ও তাঁহার গৃহিণী যে ঐ ভাবসৌন্দর্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এক অব্যক্ত আনন্দে পূর্ণ হইতেছিলেন, এ কথা আর বলিতে হইবে না।
দিবসের পূজা শেষ হইল। তাঁহারাও কোনরূপে একটু সময় করিয়া ‘বাবার’ ও জগন্মাতার শ্রীচরণে মহানন্দে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন।
ঠাকুরের ভাবসমাধি ও রূপ
সন্ধ্যা সমাগতা। এইবার শ্রীশ্রীজগন্মাতার আরাত্রিক হইবে। ‘বাবা’ এখন অন্দরে বিচিত্র ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার পুরুষ-শরীরের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন! কথায়, চেষ্টায় কেবলই প্রকাশ – যেন তিনি জন্মে জন্মে যুগে যুগে শ্রীশ্রীজগন্মাতার দাসী বা সখী। জগদম্বাই তাঁহার প্রাণ-মন, সর্বস্বের সর্বস্ব; মা-র সেবার জন্যই তাঁহার দেহ ও জীবনধারণ। ঠাকুরের মুখমণ্ডল ভাবে প্রেমে সমুজ্জ্বল, অধরে মৃদু মৃদু হাসি, চক্ষের চাহনি, হাত-পা নাড়া, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীলোকদিগের ন্যায়! ঠাকুরের পরিধানে মথুরবাবু-প্রদত্ত সুন্দর গরদের চেলি – স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় করিয়া পরিয়াছেন – কে বলিবে যে, তিনি পুরুষ! ঠাকুরের রূপ তখন বাস্তবিকই যেন ফাটিয়া পড়িত – এমন সুন্দর রং ছিল; ভাবাবেশে সেই রং আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, শরীর দিয়া যেন একটা জ্যোতি বাহির হইত! সে রূপ দেখিয়া লোকে চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিত না, অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত! শ্রীশ্রীমা-র মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীঅঙ্গে যে স্বর্ণ-ইষ্ট-কবচখানি তখন সর্বদা ধারণ করিতেন, তাহার সোনার রঙে ও গায়ের রঙে যেন মেশামেশি হইয়া এক হইয়া যাইত! ঠাকুরের নিজ মুখেও শুনিয়াছি – “তখন তখন এমন রূপ হয়েছিল রে যে, লোকে চেয়ে থাকত; বুক মুখ সব সময় লাল হয়ে থাকত, আর গা দিয়ে যেন একটা জ্যোতি বেরুত! লোকে চেয়ে থাকত বলে একখানা মোটা চাদর সর্বক্ষণ মুড়ি দিয়ে থাকতুম, আর মাকে বলতুম, ‘মা, তোর বাহিরের রূপ তুই নে, আমাকে ভিতরের রূপ দে’, গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চাপড়ে চাপড়ে বলতুম, ‘ভিতরে ঢুকে যা, ভিতরে ঢুকে যা’; তবে কতদিন পরে ওপরটা এই রকম মলিন হয়ে গেল।”
কামারপুকুরে ঠাকুরের রূপ-গুণে জনতার কথা
রূপের কথায় ঠাকুরের জীবনের আর একটি ঘটনা এখানে মনে আসিতেছে। এই সময় প্রতি বৎসর বর্ষার সময় ঠাকুর তিন-চারি মাস কাল জন্মভূমি কামারপুকুরে কাটাইয়া আসিতেন। কামারপুকুরে থাকিবার সময় মাঝে মাঝে শিওড় গ্রামে ভাগিনেয় হৃদয়ের বাড়িতেও যাইতেন। ঠাকুরের শ্বশুরালয় জয়রামবাটী গ্রামের ভিতর দিয়া শিওড়ে যাইবার পথ। সেখানকার লোকেরাও উপরোধ-অনুরোধ করিয়া ঠাকুরকে সেখানে কয়েক দিন এই অবসরে বাস করাইয়া লইতেন। ঠাকুরের পরম অনুগত ভক্ত ভাগিনেয় হৃদয় তখন সর্বদা ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সর্বপ্রকার সেবা করিতেন।
কামারপুকুরে থাকিবার কালে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার মুখের দুটো কথা শুনিবার জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের ভিড় লাগিয়াই থাকিত। প্রত্যূষেই প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরা বাড়ির পাট-ঝাঁট সারিয়া স্নান করিয়া জল আনিবার জন্য কলসী কক্ষে লইয়া আসিতেন ও কলসীগুলি ঠাকুরের বাটীর নিকট হালদারপুকুরের পাড়ে রাখিয়া চাটুয্যেদের বাড়িতে আসিয়া বসিতেন; এবং ঠাকুরের বাটীর মেয়েদের ও ঠাকুরের সহিত কথাবার্তায় এক-আধ ঘণ্টা কাল কাটাইয়া পরে স্নানে যাইতেন। এইরূপ নিত্য হইত। এই অবকাশে আবার কেহ কেহ রাত্রে বাটীতে কোন ভালমন্দ মিষ্টান্নাদি তৈয়ার করা হইলে, তাহার অগ্রভাগ তুলিয়া রাখিয়া তাহা লইয়া আসিয়া ঠাকুরকে দিয়া যাইতেন। রঙ্গরসপ্রিয় ঠাকুর ইঁহারা রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে আসিয়া উপস্থিত হন দেখিয়া কখনো কখনো রঙ্গ করিয়া বলিতেন – “শ্রীবৃন্দাবনে নানাভাবে নানা সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের মিলন হতো – পুলিনে জল আনতে গিয়ে গোষ্ঠ-মিলন, সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর যখন গরু চরিয়ে ফিরতেন তখন গোধূলি-মিলন, তারপর রাত্রে রাসে মিলন – এই রকম, এই রকম সব আছে। তা, হাঁগা, এটা কি তোদের স্নানের সময়ের মিলন নাকি?” তাঁহারা ঠাকুরের কথা শুনিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেন। মেয়েরা দিবসের রন্ধনাদি করিতে চলিয়া যাইবার পর পাড়ার পুরুষেরা ঠাকুরের নিকট আসিয়া যাহার যতক্ষণ ইচ্ছা বসিয়া কথাবার্তা কহিত। অপরাহ্ণে আবার স্ত্রীলোকেরা আসিত এবং সন্ধ্যার পর রাত্রে আবার পুরুষদের কেহ কেহ আসিয়া উপস্থিত হইত। আর দূর-দূরান্তর হইতে যে সকল স্ত্রী-পুরুষেরা আসিত, তাহারা প্রায় অপরাহ্ণেই আসিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই চলিয়া যাইত। এইরূপে সমস্ত দিন রথ-দোলের ভিড় লাগিয়া থাকিত।
ঠাকুরের রূপ লইয়া ঘটনা ও তাঁহার দীনভাব
একবার কামারপুকুর হইতে ঐরূপে জয়রামবাটী ও শিওড় যাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। অনুক্ষণ ভাবসমাধিতে থাকায় ঠাকুরের অঙ্গ বালক বা স্ত্রীলোকের ন্যায় সুকোমল হইয়া গিয়াছিল। অল্প দূর হইলেও পালকি, গাড়ি ভিন্ন যাইতে পারিতেন না। সেজন্য জয়রামবাটী হইয়া শিওড় যাইবার জন্য পালকি আনা হইয়াছে। হৃদয় সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত। ঠাকুর আহারান্তে পান খাইতে খাইতে লাল চেলি পরিয়া, হস্তে সুবর্ণ ইষ্ট-কবচ ধারণ করিয়া পালকিতে উঠিতে আসিলেন। দেখেন, রাস্তায় পালকির নিকটে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে; চারিদিকে স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে! দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন – “হৃদু, এত ভিড় কিসের রে?”
হৃদয় – কিসের আর? এই তুমি আজ ওখানে যাবে, (লোকদিগকে দেখাইয়া) এরা এখন আর তোমাকে কিছুদিন দেখতে পাবে না, তাই সব তোমায় দেখতে এসেছে।
ঠাকুর – আমাকে তো রোজ দেখে; আজ আবার কি নূতন দেখবে?
হৃদয় – এই চেলি পরে সাজলে গুজলে, পান খেয়ে তোমার ঠোঁট দুখানি লাল টুকটুকে হলে খুব সুন্দর দেখায়; তাই সব দেখবে আর কি?
তাঁহার সুন্দর রূপে ইহারা আকৃষ্ট, শুনিয়াই ঠাকুরের মন এক অপূর্ব ভাবে পূর্ণ হইল। ভাবিলেন – হায় হায়! এরা সব এই দুই দিনের বাহিরের রূপটা লইয়াই ব্যস্ত, ভিতরে যিনি রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহ দেখিতে চায় না!
রূপে বিতৃষ্ণা তো তাঁহার পূর্ব হইতেই ছিল; এই ঘটনায় তাহা আরও সহস্রগুণে বর্ধিত হইল। বলিলেন –
“কি? একটা মানুষকে মানুষ দেখবার জন্য এত ভিড় করবে? যাঃ, আমি কোথাও যাব না। যেখানে যাব, সেইখানেই তো লোকে এই রকম ভিড় করবে?” – বলিয়াই ঠাকুর বাটীর ভিতরে নিজ কক্ষে যাইয়া কাপড়-চোপড় সব খুলিয়া ক্ষোভে দুঃখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। দীনভাবে পূর্ণ ঠাকুর সেদিন বাস্তবিকই জয়রামবাটী ও শিওড়ে যাইলেন না। হৃদয় ও বাটীর সকলে কত মতে বুঝাইল, সকলি ভাসিয়া গেল। আপনার শরীরটার উপর এ অলৌকিক পুরুষের যে কি তুচ্ছ, হেয় বুদ্ধি ছিল, তাহা একবার হে পাঠক, ভাবিয়া দেখ! আর ভাব আমাদের কথা, কি রূপ রূপ করিয়া পাগল! – কি মাজা-ঘষা, আরশি, চিরুণী, ক্ষুর, ভাঁড়, বেসন, সাবান, এসেন্স, পোমেডের ছড়াছড়ি! আর পাশ্চাত্যের অনুকরণে ‘হাড়মাসের খাঁচাটার’ উপর নিত্য ভ্রমের বাড়াবাড়ি করিয়া একেবারে উৎসন্ন যাইবার হুড়াহুড়ি! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শুদ্ধ পবিত্রভাবে পূর্ণ থাকা, আর এটা – দুই কি এক কথা হে বাপু? যাক আমরা জানবাজারের পূর্ব কথাই বলি।
ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গাইতে জগদম্বা দাসীর কৌশল
জগদম্বার আরাত্রিক আরম্ভ হয় হয়, ঠাকুরের কিন্তু সে ভাব আর ভাঙে না! মথুরবাবুর পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ঠাকুরকে কোনরূপে প্রকৃতিস্থ করিয়া বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত আরতি দেখিতে যাইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশের বিরাম নাই দেখিয়া এবং তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া যাওয়াটাও যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইলেন। ভাবিলেন – করি কি? আমি যাহাকেই রাখিয়া চলিয়া যাইব, একবার আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিলেই সে নিশ্চয়ই তথায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিবে। আর ‘বাবা’ও তো ভাবে বিহ্ব্ল হইলে নিজেকে নিজে সামলাইতে পারেন না। একবার তো ঐরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় গুলের আগুনের উপর পড়িয়া যাইয়াও হুঁশ হয় নাই – পরে সে ঘা কতদিনে কত চিকিৎসায় সারিয়াছে। একাকী রাখিয়া যাইলে এ আনন্দের দিনে পাছে ঐরূপ একটা বিভ্রাট হয় – তখন উপায়? কর্তাই বা কি বলিবেন? এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনে একটা উপায় আসিয়া জুটিল। তাড়াতাড়ি নিজের বহুমূল্য গহনাসকল বাহির করিয়া বাবাকে পরাইতে পরাইতে তাঁহার কানের গোড়ায় বার বার বলিতে লাগিলেন, ‘বাবা, চল; মার যে আরতি হইবে, মাকে চামর করিবে না?’
ঠাকুরের সমাধি হইতে সাধারণ অবস্থায় নামিবার প্রকার শাস্ত্রসম্মত
ভাবাবেশে ঠাকুর যতই কেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হউন না, যে মূর্তি ও ভাবে তাঁহার মন সমাধিস্থ হইয়াছে, তাহা ছাড়া অপর সকল বস্তু, ব্যক্তি ও ভাব-সম্বন্ধ হইতে তাঁহার মন যতই কেন দূরে যাইয়া পড়ুক না, এটা কিন্তু সকল সময়েই দেখা গিয়াছে যে, ঐ মূর্তির নাম বা ঐ মূর্তির ভাবের অনুকূল কথা কয়েকবার ঠাকুরের কানের কাছে বলিলেই, তখনই তাঁহার মন উহাতে আকৃষ্ট হইত এবং উহা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইত। একাগ্রচিত্তের নিয়ম ও আচরণ যে ঐরূপ হইয়া থাকে, তাহা মহামুনি পতঞ্জলি প্রভৃতির যোগশাস্ত্রে সবিস্তার না হউক সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অতএব শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকের ঠাকুরের মনের ঐরূপ আচরণের কথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আর বহু পুণ্যফলে যাঁহারা কিছুমাত্রও চিত্তের একাগ্রতা জীবনে লাভ বা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা আরও সহজে এ কথা বুঝিতে পারিবেন। অতএব আমরা প্রকৃত ঘটনারই অনুসরণ করি।
সখীভাবে ঠাকুরের ৺দুর্গাদেবীকে চামর করা
মথুরবাবুর পত্নীর কথা ঠাকুরের কর্ণে প্রবেশ করিল। অমনি তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া অর্ধ-বাহ্যদশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা ঠাকুর-দালানে পৌঁছিবামাত্র আরতি আরম্ভ হইল। ঠাকুরও স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া চামরহস্তে প্রতিমাকে বীজন করিতে লাগিলেন। দালানের এক দিকে স্ত্রীলোকেরা এবং অপর দিকে মথুরবাবু-প্রমুখ পুরুষেরা দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার আরতি দেখিতে লাগিলেন। সহসা মথুরবাবুর নয়ন স্ত্রীলোকদিগের দিকে পড়িবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার পত্নীর পার্শ্বে বিচিত্রবস্ত্রভূষণে অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যবিস্তার করিতে করিতে কে দাঁড়াইয়া চামর করিতেছেন! বার বার দেখিয়াও যখন বুঝিতে পারিলেন না তিনি কে, তখন ভাবিলেন, হয়তো তাঁহার পত্নীর পরিচিতা কোন সঙ্গতিপন্ন লোকের গৃহিণী নিমন্ত্রিতা হইয়া আসিয়াছেন।
আরতি সাঙ্গ হইল। অন্তঃপুরবাসিনীরা শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন ও নিজ নিজ কার্যে ব্যাপৃতা হইলেন। ঠাকুরও ঐরূপ অর্ধবাহ্য অবস্থায় মথুরবাবুর পত্নীর সহিত ভিতরে যাইলেন এবং ক্রমে সম্পূর্ণ সাধারণ ভাবে প্রকৃতিস্থ হইয়া অলঙ্কারাদি খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে পুরুষদিগের নিকট আসিয়া বসিলেন, ও নানা ধর্মপ্রসঙ্গ তুলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকে সরলভাবে বুঝাইয়া চিত্তহরণ করিতে লাগিলেন।
মথুরের তাঁহাকে ঐ অবস্থায় চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা
কিছুক্ষণ পরে মথুরবাবু কার্যান্তরে অন্দরে গিয়া কথায় কথায় তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আরতির সময় তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে চামর করিতেছিলেন?” মথুরবাবুর পত্নী তাহাতে হাসিয়া বলিলেন, “তুমি চিনিতে পার নাই? বাবা ভাবাবস্থায় ঐরূপে চামর করিতেছিলেন। তা হইতেই পারে, মেয়েদের মতো কাপড়-চোপড় পরিলে বাবাকে পুরুষ বলিয়া মনে হয় না।” এই বলিয়া মথুরবাবুকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। মথুরবাবু একেবারে অবাক হইয়া বলিলেন, “তাইতো বলি – সামান্য বিষয়েও না ধরা দিলে বাবাকে চেনে কার সাধ্য? দেখ না, চব্বিশ ঘণ্টা দেখে ও একত্র থেকেও আজ তাঁকে চিনতে পারলুম না।”
বিজয়া দশমী
সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পরমানন্দে কাটিয়া গিয়াছে। আজ বিজয়া দশমীর প্রাতঃকাল। পুরোহিত তাড়াতাড়ি শ্রীশ্রীজগদম্বার সংক্ষেপ পূজা সারিয়া লইতেছে, কারণ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দর্পণ-বিসর্জন করিতে হইবে। পরে সন্ধ্যার পর প্রতিমাবিসর্জন। মথুরবাবুর বাটীর সকলেরই মনে যেন একটা বিষাদের ছায়া – কিসের যেন একটা অব্যক্ত অপরিস্ফুট অভাব – যেন একটা হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সহিত অপরিহার্য আশু বিচ্ছেদাশঙ্কা! পৃথিবীর অতি বিশুদ্ধ আনন্দের পশ্চাতেও এইরূপ একটা বিষাদছায়া সর্বদা সংলগ্ন আছে। এই নিয়মের বশেই বোধ হয় অতি বড় ঈশ্বর-প্রেমিকের জীবনেও সময়ে সময়ে অসহ্য ঈশ্বরবিরহের সন্তাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। আর কঠিন মানব, আমাদের হৃদয়ও বিজয়ার দিনে প্রতিমাবিসর্জন দিতে যাইয়া উষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করে! মথুর-পত্নীর তো কথাই নাই – আজ প্রাতঃকাল হইতে হস্তে কর্ম করিতে করিতে অঞ্চলে অনেকবার নয়নাশ্রু মুছিয়া চক্ষু পরিষ্কার করিয়া লইতে হইতেছে।
মথুরের আনন্দে ঐ বিষয়ে হুঁশ না থাকা
বাহিরে মথুরবাবুর কিন্তু অদ্যকার কথা এখনও ধারণা হয় নাই। তিনি পূর্ববৎই আনন্দে উৎফুল্ল! শ্রীশ্রীজগদম্বাকে গৃহে আনিয়া এবং ‘বাবা’র অলোকসামান্য সঙ্গ ও অচিন্ত্য কৃপাবলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপনাতে আপনি ভরপুর হইয়া রহিয়াছেন। বাহিরে কি হইবে না হইবে, তাহা এখন খোঁজে কে? খুঁজিবার আবশ্যকই বা কি? মাকে ও বাবাকে লইয়া এইরূপেই দিন কাটিবে। এমন সময় পুরোহিতের নিকট হইতে সংবাদ আসিল – এইবার মা-র বিসর্জন হইবে, বাবুকে নিচে আসিয়া মাকে প্রণাম-বন্দনাদি করিয়া যাইতে বল।
দেবীমূর্তি-বিসর্জন দিবে না বলিয়া মথুরের সংকল্প
কথাটা মথুরবাবু প্রথম বুঝিতেই পারিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার হুঁশ হইল – আজ বিজয়া দশমী! আর সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে এক বিষম আঘাত পাইলেন। শোকে দুঃখে পূর্ণ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, “আজ মাকে বিসর্জন দিতে হইবে – কেন? বাবা ও মা-র কৃপায় আমার তো কিছুরই অভাব নাই। মনের আনন্দের যেটুকু অভাব ছিল, তাহা তো বাড়িতে মা-র শুভাগমনে পূর্ণ হইয়াছে। তবে আবার কেন মাকে বিসর্জন দিয়া বিষাদ ডাকিয়া আনি? না, এ আনন্দের হাট আমি ভাঙিতে পারিব না। মা-র বিসর্জন, মনে হইলেও যেন প্রাণ কেমন করিয়া উঠে!” এরূপ নানা কথা ভাবিতে ও অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।
এদিকে সময় উত্তীর্ণ হয়। পুরোহিত লোকের উপর লোক পাঠাইতেছেন, বাবু একবার আসিয়া দাঁড়ান, মা-র বিসর্জন হইবে। মথুর বিষম বিরক্ত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি মাকে বিসর্জন দিতে দিব না। যেমন পূজা হইতেছে, তেমনি পূজা হইবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ বিসর্জন দেয় তো বিষম বিভ্রাট হইবে – খুনোখুনি পর্যন্ত হইতে পারে।” এই বলিয়া মথুরবাবু গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য বাবুর ঐরূপ ভাবান্তর দেখিয়া সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল এবং পূজার দালানে যাইয়া সকল কথা পুরোহিত মহাশয়কে জানাইল। সকলে অবাক!
সকলে বুঝাইলেও মথুরের উত্তর
তখন সকলে পরামর্শ করিয়া বাবু বাটীর ভিতরে যাঁহাদের সম্মান করিতেন, তাঁহাদের বুঝাইতে পাঠাইলেন। তাঁহারাও যাইলেন, বুঝাইলেন, কিন্তু বাবুর সে ভাবান্তর দূর করিতে পারিলেন না। বাবু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, “কেন? আমি মা-র নিত্যপূজা করিব। মা-র কৃপায় আমার যখন সে ক্ষমতা আছে তখন কেন বিসর্জন দিব?” কাজেই তাঁহারা আর কি করেন, বিমর্ষভাবে ফিরিয়া আসিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন – মাথা খারাপ হইয়াছে! কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই বা উপায় কি? হঠকারী মথুরকে বাটীর সকলেরই ভালরকম জানা ছিল! সকলেই জানিত, ক্রুদ্ধ হইলে বাবুর দিক-বিদিক-জ্ঞান থাকে না। কাজেই তাঁহার অনভিমতে দেবীর বিসর্জনের হুকুম দিয়া কে তাঁহার কোপে পড়িবে বল? সে বিষয়ে কেহই অগ্রসর হইলেন না। গিন্নির নিকট অতিরঞ্জিত হইয়া সংবাদ পৌঁছিল; তিনি ভয়ে ডরে অভিভূতা হইয়া ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন; কারণ, ‘বাবা’ ভিন্ন তাঁহাদের বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার আর কে আছে? – বাবুর যদি বাস্তবিকই মাথা খারাপ হইয়া থাকে!
ঠাকুরের মথুরকে বুঝান
ঠাকুর যাইয়াই দেখিলেন, মথুরের মুখ গম্ভীর, রক্তবর্ণ, দুই চক্ষু লাল এবং কেমন যেন উন্মনা হইয়া ঘরের ভিতর বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মথুর কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, “বাবা, যে যাহাই বলুক, আমি মাকে প্রাণ থাকিতে বিসর্জন দিতে পারিব না। বলিয়া দিয়াছি, নিত্যপূজা করিব। মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব?”
ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “ওঃ – এই তোমার ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বললে? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখনো থাকতে পারে? এ তিন দিন বাইরে দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে – সর্বদা তোমার হৃদয়ে বসে তোমার পূজা নেবেন।”
ঠাকুরের কথা ও স্পর্শের অদ্ভুত শক্তি
কি এক অদ্ভুত মোহিনী শক্তিই যে ঠাকুরের স্পর্শে ও কথায় ছিল, তাহা বলিয়া বুঝানো কঠিন! দেখা গিয়াছে, অনেক সময় লোকে আসিয়া তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া খুব তর্ক করিতেছে – তাঁহার সিদ্ধান্ত কিছুতেই লইতেছে না, ঠাকুর তখন কৌশলে কোনরূপে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া দিতেন; আর অমনি তখন হইতে তাহার মনের স্রোত যেন ফিরিয়া যাইত এবং ঐ ব্যক্তি কথাটা গুটাইত – ঠাকুরের কথা বা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়া! ঐ বিষয়ে তিনি আমাদের কাহারও কাহারও নিকট বলিয়াছেনও – “কথা কইতে কইতে অমন করে ছুঁয়ে দি কেন জানিস? যে শক্তিতে ওদের অমন গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে।” এইরূপে স্পর্শমাত্রেই অপরের যথার্থ সত্য উপলব্ধি করিবার পথের অন্তরায়স্বরূপ দণ্ডায়মান শক্তিসমূহকে নিজের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহাদের প্রভাব কমাইয়া দেওয়া বা ঐসকলকে চিরকালের মতো একেবারে হরণ করার সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত ঠাকুরের জীবনে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। দেখিয়াছি, যে সকল কথা অপরের মুখ হইতে বাহির হইয়া কাহারও মনে কোনরূপ ভাবোদয় করিল না, সেই সকলই আবার তাঁহার মুখনিঃসৃত হইয়া মানবহৃদয়ে এমন অদম্য আঘাত করিয়াছে যে, সেইক্ষণ হইতে শ্রোতার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে! সে সকল পাঠককে সবিস্তারে বলিবার অন্য কোন সময় চেষ্টা করিব। এখন মথুরবাবুর কথাই বলিয়া যাই।
মথুর প্রকৃতিস্থ কিরূপে হইয়াছিল
ঠাকুরের কথায় ও স্পর্শে মথুর ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার ঐরূপে প্রকৃতিস্থ হওয়া, ঠাকুরের ইচ্ছা এবং স্পর্শে কোনরূপ দর্শনাদি হইয়াছিল কিনা, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে মনে হয়, উহাই সম্ভব। মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্তি তাঁহার হৃদয়কন্দর অপূর্ব আলোকে উজ্জ্বল করিয়া বিদ্যমান – দেখিতে পাইয়াই তাঁহার আনন্দ আরও শতগুণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়া বাহিরের প্রতিমা রক্ষা করিবার মনে যে ঝোঁক উঠিয়াছিল, তাহা কমিয়া গিয়াছিল। যথার্থ গুরু এইরূপে উচ্চতর লক্ষ্যের উজ্জ্বল ছটায় শিষ্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া দেন। কাজেই তখন নিম্নাঙ্গের ভাব-দর্শনাদি তাহার মন হইতে আপনা-আপনি খসিয়া যায়।
মথুরের ভক্তিবিশ্বাসের অবিচলতা ঠাকুরকে পরীক্ষার ফলে
মথুরের ভক্তি-বিশ্বাস আমাদের চক্ষে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইলেও উহা যে নানারূপে ঠাকুরকে যাচাইবার ফলেই উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মথুর ধন দিয়া, সুন্দরী রমণী দিয়া, নিজের ও বাটীর সকলের উপর অকুণ্ঠ প্রভুতা দিয়া, ঠাকুরের আত্মীয়বর্গ – যথা, হৃদয় প্রভৃতির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া, সকল ভাবে ঠাকুরকে যাচাইয়া দেখিয়াছিলেন – ইনি অপর সাধারণের ন্যায় বাহ্যিক কিছুতেই ভুলেন না। বাহ্যিক ভাব-ভক্তির কপটাবরণ ইঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে অধিকক্ষণ আত্মগোপন করিয়া রাখিতে পারে না! আর নরহত্যাদি দুষ্কর্ম করিয়াও মন-মুখ এক করিয়া যথার্থ সরলভাবে যদি কেহ ইঁহার শরণ গ্রহণ করে, তবে তাহার সাত খুন মাপ করিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, দিন দিন উচ্চ লক্ষ্য চিনিবার ও ধরিবার সামর্থ্য দেন এবং কি এক বিচিত্র শক্তি-বলে তাহার জন্য অসম্ভবও সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়!
মথুরের ভাবসমাধিলাভের ইচ্ছা
ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া এবং ভাবসমাধিতে তাঁহার অসীম আনন্দানুভব দেখিয়া বিষয়ী মথুরেরও এক সময়ে ইচ্ছা হইয়াছিল, ব্যাপারটা কি একবার দেখিবে ও বুঝিবে। মথুরের তখন হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, ‘বাবা ইচ্ছামাত্রেই ও-সকল করিয়া দিতে পারেন। কারণ, শিব বল, কালী বল, ভগবান বল, কৃষ্ণ বল, রাম বল – সবই তো উনি নিজে! – তবে আর কি! কৃপা করিয়া কাহাকেও নিজের কোন মূর্তি যে দেখাইতে পারিবেন, ইহার আর বিচিত্র কি!’ বাস্তবিক ইহা এক কম অদ্ভুত ব্যাপার নহে। ঠাকুরের দর্শনলাভের পর যাহারাই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছে, তাহাদেরই ক্রমে ক্রমে এইরূপ ধারণার উদয় হইত! সকলেরই মনে হইত, উঁহার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয় – উনি ইচ্ছামাত্রেই ধর্মজগতের সমস্ত সত্যই কাহাকেও উপলব্ধি করাইয়া দিতে পারেন। আধ্যাত্মিক শক্তি ও নিজ পূত চরিত্রবলে একজনের প্রাণেও ঐরূপ ভাবের উদয় করিতে পারা কঠিন – তো অনেকের প্রাণে! উহা কেবল এক অবতার-পুরুষেই সম্ভবে। তাঁহাদের অবতারত্বের বিশিষ্ট প্রমাণসমূহের মধ্যে ইহা একটি কম প্রমাণ নহে। আর, এ মিথ্যা, শঠতা ও প্রতারণার রাজ্যে তাঁহাদের নামে অনেক ভেল জুয়াচুরি চলিবে দেখিতে পাইয়াই, তাঁহারা সকলের সমক্ষে ডঙ্কা মারিয়া বলিয়া যান, “আমার অদর্শনের পর অনেক ভণ্ড ‘আমি অবতার, আমি দুর্বল জীবের শরণ ও মুক্তিদাতা’ বলিয়া তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে; সাবধান, তাহাদের কথায় ভুলিও না।”1
1. ঈশা – (Matthew XXIV – 11, 23, 24, 25, 26).
ঐ জন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা
মথুরের মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইবামাত্র ঠাকুরকে যাইয়া ধরিলেন। বলিলেন, “বাবা, আমার যাহাতে ভাবসমাধি হয়, তাহা তোমায় করিয়া দিতেই হইবে।” ঠাকুর ঐরূপ স্থলে সকল সময়েই যেমন বলিতেন, সেইরূপই বলিয়াছিলেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বলিলেন, “ওরে, কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁতবামাত্রই কি গাছ হয়ে তার ফল খেতে পাওয়া যায়? কেন, তুই তো বেশ আছিস – এদিক-ওদিক দুদিক চলছে। ও-সব হলে এদিক (সংসার) থেকে মন উঠে যাবে, তখন তোর বিষয়-আশয় সব রক্ষা করবে কে? বার ভূতে সব যে লুটে খাবে। তখন কি করবি?”
উদ্ধব ও গোপীদের দৃষ্টান্তে ঠাকুরের তাহাকে বুঝান
ও-সব কথা সেদিন শুনে কে? মথুর একেবারে ‘নাছোড়বান্দা’ – ‘বাবা’কে ভাবসমাধি করিয়া দিতেই হইবে। ঐরূপ বুঝানোয় ফল হইল না দেখিয়া ঠাকুর আর এক গ্রাম চড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, “ওরে, ভক্তেরা কি দেখতে চায়? তারা সাক্ষাৎ সেবাই চায়। দেখলে শুনলে (ঈশ্বরের) ঐশ্বর্যজ্ঞানে ভয় আসে, ভালবাসা চাপা পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীরা বিরহে আকুল! শ্রীকৃষ্ণ তাদের অবস্থা জেনে উদ্ধবকে বুঝাতে পাঠালেন। উদ্ধব জ্ঞানী কিনা! বৃন্দাবনের কান্নাকাটি ভাব, খাওয়ানো, পরানো ইত্যাদি উদ্ধব বুঝতে পারত না। গোপীদের শুদ্ধ ভালবাসাটাকে মায়িক ও ছোট বলে দেখত; তারও দেখে শুনে শিক্ষা হবে সেও এক কথা। উদ্ধব গিয়ে গোপীদের বুঝাতে লাগল – ‘তোমরা সব কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে অমন কেন করছ? জান তো, তিনি ভগবান, সর্বত্র আছেন; তিনি মথুরায় আছেন আর বৃন্দাবনে নেই, এটা তো হতে পারে না। অমন করে হা-হুতাশ না করে একবার চক্ষু মুদে দেখ দেখি, দেখবে, তোমাদের হৃদয়মাঝে সেই নবঘনশ্যাম মুরলীবদন বনমালী সর্বদা রয়েছেন’ – ইত্যাদি। তাই শুনে গোপীরা বলেছিল, ‘উদ্ধব, তুমি কৃষ্ণসখা, জ্ঞানী, তুমি এসব কি কথা বলছ! আমরা কি ধ্যানী, না জ্ঞানী, না ঋষি-মুনির মতো জপ-তপ করে তাঁকে পেয়েছি? আমরা যাঁকে সাক্ষাৎ সাজিয়েছি-গুজিয়েছি, খাইয়েছি, পরিয়েছি, ধ্যান করে তাঁকে আবার ঐ সব করতে যাব? আমরা তা কি আর করতে পারি? যে মন দিয়ে ধ্যান-জপ করব, সে মন আমাদের থাকলে তো তা দিয়ে ঐসব করব! সে মন যে অনেক দিন হলো, কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করেছি! আমাদের বলতে আমাদের কি আর কিছু আছে যে, তাইতে অহং-বুদ্ধি করে জপ করব?’ উদ্ধব তো শুনে অবাক! তখন সে গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা যে কত গভীর ও কি বস্তু, তা বুঝতে পেরে তাদের গুরু বলে প্রণাম করে চলে এল! এতেই দেখ না, ঠিক ঠিক ভক্ত কি তাঁকে দেখতে চায়? তাঁর সেবাতেই তার পরমানন্দ। তার অধিক – দেখা, শুনা, সে চায় না; তাতে তার ভাবের হানি হয়।”
ইহাতেও যখন মথুর বুঝিলেন না, তখন ঠাকুর বলিলেন, “তা কি জানি বাবু? মাকে বলব, তিনি যা হয় করবেন।”
মথুরের ভাবসমাধি হওয়া ও প্রার্থনা
তাহার কয়েক দিন পরেই মথুরের একদিন ভাবসমাধি! ঠাকুর বলিতেন, “আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। গিয়ে দেখি, যেন সে মানুষ নয়! চক্ষু লাল, জল পড়ছে; ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্চে! আর বুক থর থর করে কাঁপচে। আমাকে দেখে একেবারে পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, ‘বাবা ঘাট হয়েছে! আজ তিন দিন ধরে এই রকম, বিষয়কর্মের দিকে চেষ্টা করলেও কিছুতে মন যায় না! সব খানে খারাপ হয়ে গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাই নে।’ বললুম – ‘কেন? তুই যে ভাব হোক, বলেছিলি?’ তখন সে বললে, ‘বলেছিলুম, আনন্দও আছে; কিন্তু হলে কি হয়, এদিকে যে সব যায়। বাবা, ও তোমার ভাব তোমাকেই সাজে। আমাদের ও সবে কাজ নেই! ফিরিয়ে নাও।’ তখন আমি হাসি আর বলি, ‘তোকে তো এ কথা আগেই বলেছি?’ সে বললে, ‘হাঁ বাবা, কিন্তু তখন কি অত-শত জানি যে, ভূতের মতো এসে ঘাড়ে চাপবে? আর তার গোঁয়ে আমার চব্বিশ ঘণ্টা ফিরতে হবে? – ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারব না!’ তখন তার বুকে আবার হাত বুলিয়ে দি!”
ত্যাগী না হইলে ভাবসমাধি স্থায়ী হয় না
বাস্তবিক ভাব বা সমাধি হইলেই হয় না। উহার বেগ সহ্য করিতে – উহাকে রক্ষা করিতে পারে কয়টা লোক? এতটুকু বাসনার পশ্চাৎটান থাকিতে উহা পারা অসম্ভব। ঈশ্বরীয় পথের পথিককে শাস্ত্র সেজন্যই পূর্ব হইতে নির্বাসনা হইতে বলিয়াছেন – ‘ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ’ – একমাত্র ত্যাগ ও বৈরাগ্যই অমৃতত্ব দিতে সমর্থ। ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসে নিম্নাঙ্গের সমাধি হইল, কিন্তু ভিতরে ধন হোক, মান হোক ইত্যাদি বাসনার রাশি গজ গজ করিতেছে, এরূপ লোকের ঐ ভাব কখনই স্থায়ী হয় না।
ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্ত – কাশীপুরের বাগানে আনীত জনৈক ভক্ত যুবকের কথা
আচার্য শঙ্কর যেমন বলিয়াছেন –
আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্ ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুমুদ্যতান্।
আশাগ্রহো মজ্জয়তেঽন্তরালে, নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্য বেগাৎ॥
– বিবেকচূড়ামণি, ৭৯
অর্থাৎ, যথার্থ বৈরাগ্যরূপ সম্বল অগ্রে সংগ্রহ না করিয়া, ভবসমুদ্রের পারে যাইবার জন্য যাহারা অগ্রসর হয়, বাসনা-কুম্ভীর তাহাদের ঘাড়ে ধরিয়া ফিরাইয়া বলপূর্বক অতলজলে ডুবাইয়া দেয়। – বাস্তবিক, কতই না ঐরূপ দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের নিকট দেখিয়াছি! কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর তখন অবস্থান করিতেছেন; একদিন কয়েকজন বৈষ্ণব ভক্ত একটি উন্মনা যুবককে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত। ইঁহাদের পূর্বে কখনো আসিতে আমরা দেখি নাই। আসিবার কারণ, সঙ্গী যুবকটিকে একবার ঠাকুরকে দেখাইবেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক কি অবস্থা সহসা উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের মতামত শ্রবণ করিবেন। ঠাকুরের নিকট সংবাদ দেওয়া গেল।
যুবকটিকে দেখিলাম – বুক ও মুখ লাল, দীনভাবে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতেছে; ভগবানের নামে ঘন ঘন কম্পন ও পুলক; এবং দু-নয়নে অবিশ্রান্ত জলধারা বহায় চক্ষুর্দ্বয় রক্তিম ও কিঞ্চিৎ স্ফীতও হইয়াছে। দেখিতে শ্যামবর্ণ, না স্থূল না কৃশ, মুখমণ্ডল ও অবয়বাদি সুশ্রী এবং সুগঠিত, মস্তকে শিখা। পরিধানে একখানি মলিন সাদাধুতি, গায়ে উত্তরীয় ছিল না বলিয়াই মনে হয়; পায়ে জুতা নাই; এবং শরীর-সংস্কার বা রক্ষার বিষয়ে একেবারে উদাসীন! শুনিলাম – হরিসংকীর্তন করিতে করিতে একদিন সহসা এইরূপ উত্তেজিত অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। তদবধি আহার এক প্রকার নাই বলিলেই হয়, নিদ্রা নাই এবং ভগবানলাভ হইল না বলিয়া দিবারাত্র কান্নাকাটি ও ভূমে গড়াগড়ি! আজ কয়েক দিন হইল, ঐরূপ হইয়াছে।
আধ্যাত্মিক ভাবের আতিশয্যে উপস্থিত বিকারসকল চিনিবার ঠাকুরের শক্তি। গুরু যথার্থই ভবরোগ-বৈদ্য
আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের আতিশয্যে মানবশরীরে যেসকল বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্বিষয় ধরিবার ও চিনিবার শক্তি ঠাকুরের যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কুত্রাপি দেখি নাই! গুরুগীতাদিতে শ্রীগুরুকে ‘ভবরোগ-বৈদ্য’ ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে; তাহার ভিতর যে এত গূঢ় অর্থ আছে, তাহা ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভের পূর্বে একটুও বুঝি নাই। শ্রীগুরু যে বাস্তবিকই মানসিক রোগের বৈদ্য, এবং ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাবে মানবমনে যে যে বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা দেখিবামাত্র চিনিয়া, লক্ষণ দেখিয়া ধরিয়া অনুকূল হইলে – উহা যাহাতে সাধকের মনে সহজ হইয়া দাঁড়ায় ও তাহাকে উচ্চতর ভাবসোপানে আরোহণ করিবার ক্ষমতা দেয়, তাহার এরূপে ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং প্রতিকূল বুঝিলে তাহা যাহাতে সাধকের অনিষ্টসাধন না করিয়া ধীরে ধীরে অপনীত হইয়া যায়, তদ্বিষয়েরও ব্যবস্থা করেন, এ কথা পূর্বে কিছুই জানা ছিল না। ঠাকুরকে প্রতিদিন ঐরূপ করিতে দেখিয়াই মনে সে কথার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। দেখিয়াছি – পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম নির্বিকল্প সমাধিলাভ হইলে অমনি ঠাকুর ব্যবস্থা করিতেছেন, “তুই এখন কয়েকদিন কাহারও হাতে খাস নি, নিজে রেঁধে খাস। এ অবস্থায় বড় জোর নিজের মার হাতে খাওয়া চলে, অপর কারও হাতে খেলেই ঐ ভাব নষ্ট হয়ে যায়! পরে ঐটে সহজ হয়ে দাঁড়ালে, তখন আর ভয় নেই!” গোপালের মার বায়ুবৃদ্ধিতে শারীরিক যন্ত্রণা দেখিয়া বলিতেছেন, “ও যে তোমার হরি-বাই, ও গেলে কি নিয়ে থাকবে? ও থাকা চাই; তবে যখন বিশেষ কষ্ট হবে, তখন যা হোক কিছু খেও।” জনৈক ভক্তের বাহ্যিক শৌচে অত্যন্ত অভ্যাস ও অনুরাগের জন্য শরীর ভুলিয়া মন একেবারে ঈশ্বরে তন্ময় হয় না দেখিয়া গোপনে ব্যবস্থা করিতেছেন, “লোকে যেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করে, সেইখানকার মাটিতে তুমি একদিন ফোঁটা পরে ঈশ্বরকে ডেকো।” একজনের সংকীর্তনে উদ্দাম শারীরিক বিকার তাহার উন্নতির প্রতিকূল দেখিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন, “শালা, আমায় ভাব দেখাতে এসেছেন। ঠিক ঠিক ভাব হলে কখনো এমন হয়? ডুবে যায়; স্থির হয়ে যায়। ও কি? স্থির হ, শান্ত হয়ে যা। (অপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া) এ সব কেমন ভাব জান? যেমন এক ছটাক দুধ কড়ায় করে আগুনে বসিয়ে ফোটাচ্ছে; মনে হচ্চে, যেন কতই দুধ, এক কড়া; তারপর নামিয়ে দেখ, একটুও নেই, যেটুকু দুধ ছিল, সব কড়ার গায়েই লেগে গেছে।” একজনের মনোভাব বুঝিয়া বলিতেছেন, “যাঃ শালা, খেয়ে লে, পরে লে, সব করে লে, কিন্তু কোনটাই ধর্ম কচ্চিস বলে করিসনি”; ইত্যাদি কত লোকের কত কথাই বা বলিব!
ঐ যুবকের অবস্থা সম্বন্ধে ঠাকুরের মীমাংসা
সেই যুবককে দেখিয়াই এক্ষেত্রে ঠাকুর বলিলেন, “এ যে দেখচি মধুরভাবের1 পূর্বাভাস! কিন্তু এ অবস্থা এর থাকবে না, রাখতে পারবে না। এ অবস্থা রক্ষা করা বড় কঠিন। স্ত্রীলোককে ছুঁলেই (কামভাবে) এ ভাব আর থাকবে না! একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।” যাহা হউক, আগন্তুক ভক্তগণ ঠাকুরের কথায় যুবকটির যে মাথা খারাপ হয় নাই, এ বিষয়টি জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ফিরিলেন। তাহার পর কিছু কাল গত হইলে সংবাদ পাওয়া গেল – ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে – যুবকটির কপাল ভাঙিয়াছে! সংকীর্তনের ক্ষণিক উত্তেজনায় সে ভাগ্যক্রমে যত উচ্চে উঠিয়াছিল, হায় হায় – ভাবাবসাদে দুৰ্ভাগ্যক্রমে আবার ততই নিম্নে নামিয়াছে! পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ঐরূপ হইবার ভয়েই সর্বদা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং ঐরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা দিতেন।
1. বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারানীর যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ঊনবিংশ প্রকার অষ্টসাত্ত্বিক শারীরিক বিকার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে প্রকাশ পাইত, যথা – হাস্য, ক্রন্দন, অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, মূর্ছা ইত্যাদি – বৈষ্ণব-শাস্ত্রে উহাই মধুরভাব বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। মধুরভাবের পরাকাষ্ঠাকেই ‘মহাভাব’ বলে। ঐ মহাভাবেই ঊনবিংশ প্রকার শারীরিক বিকার ঈশ্বর-প্রেমে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা জীবের সর্বাঙ্গীণ হওয়া অসম্ভব বলিয়া কথিত আছে।
ঠাকুরের মথুরকে সকল বিষয় বালকের মত খুলিয়া বলা ও মতামত লওয়া
মথুরের যেমন ‘বাবা’র নিকট কোন বিষয় গোপন ছিল না, ‘বাবা’রও আবার মথুরের উপর ভাবসমাধির কাল ভিন্ন অপর সকল সময়ে, মাতার নিকট বালক যেমন, সখার নিকট সখা যেমন, অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলে, পরামর্শ করে, মতামত সাদরে গ্রহণ করে ও ভালবাসার উপর নির্ভর করে, তেমনি ভাব ছিল। পরাবিদ্যার সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিলে মানবের অবস্থা যে উন্মাদ, পিশাচ বা বালকবৎ সাধারণ নয়নে প্রতীত হইয়া থাকে, শাস্ত্রের এ কথা আমরা পাঠককে পূর্বেই বলিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, জগৎপূজ্য আচার্য শঙ্কর এ কথাও স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঐরূপ মানব, অতুল রাজ-বৈভব উপভোগ করিয়া বা কৌপীনমাত্রৈকসম্বল ও ভিক্ষান্নে উদরপোষণ করিয়া ইতর-সাধারণে যাহাকে বড় সুখের অবস্থা বা বড় দুঃখের অবস্থা বলিয়া গণ্য করে, তাহার ভিতর থাকিয়াও, কিছুতেই বিচলিত হন না; সর্বদা আত্মানন্দে আপনাতে আপনি বিভোর হইয়া থাকেন।
ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ
ক্বচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।
ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ॥
– বিবেকচূড়ামণি, ৫৪৩
অর্থাৎ, ‘মুক্ত ব্যক্তি কখনো মূঢ়ের ন্যায়, আবার কখনো পণ্ডিতের ন্যায়, আবার কখনো বা রাজবৎ বিভবশালী হইয়া বিচরণ করেন। তাঁহাকে কখনো পাগলের ন্যায়, আবার কখনো ধীর, স্থির, বুদ্ধিমানের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। আবার কখনো বা তাঁহাকে নিত্যাবশ্যকীয় আহার্য প্রভৃতির জন্যও যাচ্ঞারহিত হইয়া অজগরের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখা যায়। তিনি কোথাও বা বহু মান প্রাপ্ত হন, আবার কোথাও বা অপমানিত হন, আবার কোথাও বা একেবারে অপরিচিতভাবে থাকেন। এইরূপে সকল অবস্থায় তিনি পরমানন্দে বিভোর ও অবিচলিত থাকেন।’ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেই যখন ঐ কথা, তখন মহামহিম অবতার-পুরুষদিগের ঐরূপে সর্বাবস্থায় অবিচলিত থাকা ও বালকবৎ ব্যবহার করাটা আর অধিক কথা কি? অতএব মথুরের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু মথুরের তাঁহার সহিত ঐরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিয়া এত কাল কাটাইতে পারাটা বড় কম ভাগ্যের কথা নহে!
মথুরের কল্যাণের দিকে ঠাকুরের কতদূর দৃষ্টি ছিল
কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুরের মথুরের সহিত ছিল! সাধনকালে এবং পরেও কখনো কোন জিনিসের আবশ্যক হইলে, অমনি তাহা মথুরকে বলা ছিল। সমাধিকালে বা অন্য সময়ে যাহা কিছু দর্শনাদি ও ভাব উপস্থিত হইত, তাহা মথুরকে বলিয়া “এটা কেন হলো, বল দেখি?” “ওটা তোমার মনে কি হয় – বল দেখি?” ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা ছিল। তাহার পয়সার যাহাতে সদ্ব্যয় হয়, দেবসেবার পয়সাতে যাহাতে যথার্থ দেবসেবা হইয়া অতিথি, কাঙাল, সাধু-সন্ত প্রভৃতি পালিত হয় ও তাহার পুণ্যসঞ্চয় হইয়া কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে ঠাকুরের লক্ষ্য থাকিত – এইরূপ সকল বিষয়ে কত কথাই না আমরা শুনিয়াছি। পুণ্যবতী রানী রাসমণি ও মথুরের শরীর যাইবার অনেক পরে যখন আমরা সকলে ঠাকুরের নিকট গিয়াছি, তখনও ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ঐ ভাবের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। একটি দৃষ্টান্ত দিলে এখানে মন্দ হইবে না।
ঐ বিষয়ক দৃষ্টান্ত – ফলহারিণী-পূজার প্রসাদ ঠাকুরের চাহিয়া লওয়া
মথুরের আমল হইতে বন্দোবস্ত ছিল, ৺মা কালী ও ৺রাধাগোবিন্দের ভোগরাগাদির পর বড় থালে করিয়া এক থাল প্রসাদী অন্নব্যঞ্জন ও এক থাল ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের ঘরে নিত্য আসিবে ও ঠাকুর নিজে ও তাঁহার নিকট যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহারা প্রসাদ পাইবেন। তদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে মা কালী ও রাধাগোবিন্দজীকে যে বিশেষ ভোগরাগাদি দেওয়া হইত, তাহারও কিয়দংশ ঐরূপে ঠাকুরের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত।
বর্ষাকাল। আজ ফলহারিণী পূজার দিন। এ দিনে ঠাকুরবাড়িতে বেশ একটি ছোট-খাট আনন্দোৎসব হইত। শ্রীশ্রীজগন্মাতা কালিকার বিশেষ পূজা করিয়া নানা প্রকারের ফল-মূল ভোগ-নিবেদন করা হইত। আজও তদ্রূপ হইতেছে। নহবত বাজিতেছে। ঠাকুরের নিকট অদ্য যোগানন্দ স্বামীজী প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত উপস্থিত আছেন।
বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে ঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভাব-সমাধির স্বভাবতঃ উদয়
বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে ঠাকুরের শরীর-মনে বিশেষ বিশেষ দেবভাব প্রকাশিত হইত। বৈষ্ণবদিগের পর্বদিনে বৈষ্ণবভাব এবং শাক্তদিগের পর্বদিনে শক্তিসম্বন্ধীয় ভাবসমূহ প্রকাশিত হইত। যথা, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময়, বিশেষতঃ ঐ পূজার সন্ধিক্ষণে, অথবা ৺কালীপূজাদিকালে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার ভাবে আবিষ্ট, নিস্পন্দ ও কখনো কখনো বরাভয়কর পর্যন্ত হইয়া যাইতেন; জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্বদিনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর ভাবে আরূঢ় হওয়ায় কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ তাঁহার শরীরে দেখা যাইত – এইরূপ। আবার ঐ ঐ ভাবাবেশ এত সহজে স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইত যে, উহা যে কোনরূপ বিশেষ চেষ্টার ফলে হইতেছে, একথা আদৌ মনে হইত না! বরং এমন দেখা গিয়াছে, ঐরূপ পর্বদিনে ঠাকুর আমাদের সহিত অন্য নানা প্রসঙ্গে কথায় খুব মাতিয়াছেন, ঐ দিনে ঈশ্বরের যে বিশেষ লীলাপ্রকাশ হইয়াছিল, সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মন ঐসকল বাহিরের ব্যাপার হইতে গুটাইয়া একেবারে ঈশ্বরের ঐ ভাবে যাইয়া তন্ময় হইয়া পড়িল! কে যেন জোর করিয়া ঐরূপ করাইয়া দিল! কলিকাতায় শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে আমরা ঐরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ একঘর লোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণে হঠাৎ ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ হইল! তখনকার সেই হাস্যচ্ছটায় বিকশিত জ্যোতিঃপূর্ণ তাঁহার মুখমণ্ডল ও তাহার পূর্বক্ষণের অসুস্থতা-নিবন্ধন কালিমাপ্রাপ্ত বদন দেখিয়া কে বলিবে যে, ইনি সেই লোক – কে বলিবে, ইঁহার কোন অসুস্থতা আছে!
অদ্যকার ফলহারিণী পূজার দিনেও ঠাকুরের শরীর-মনে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ভাবাবেশ হইতেছে; কখনো বা তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় মা-র নাম গাহিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া সে অপূর্ব বদনশ্রীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন এবং সে অদৃষ্টপূর্ব দেবমানবের সঙ্গগুণে মনে কতপ্রকার অপূর্ব দিব্যভাব অনুভব করিতেছেন। মা-র পূজা সাঙ্গ হইতে প্রায় রাত্রি শেষ হইল। একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই প্রভাত।
বেলা প্রায় ৮।৯টার সময় ঠাকুর দেখিলেন যে, তাঁহার ঘরে যে প্রসাদী ফল-মূলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা তখনো পৌঁছায় নাই। কালীঘরের পূজারী ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না; বলিলেন – “সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য দপ্তরখানায় খাজাঞ্চী মহাশয়ের নিকট যথারীতি প্রেরিত হইয়াছে; সেখান হইতে সকলকে, যাহার যেমন পাওনা বরাদ্দ আছে, বিতরিত হইতেছে; কিন্তু এখানকার (ঠাকুরের) জন্য এখনো কেন আসে নাই, বলিতে পারি না।” রামলালদাদার কথা শুনিয়াই ঠাকুর ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন। “কেন এখনো দপ্তরখানা হইতে প্রসাদ আসিল না?” – ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর ঐ কথাই আলোচনা করেন! এইরূপে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন – তখনো আসিল না, তখন চটিজুতাটি পরিয়া নিজেই খাজাঞ্চীর নিকট আসিয়া উপস্থিত! বলিলেন, “হ্যাঁগা, ও ঘরের (নিজের কক্ষ দেখাইয়া) বরাদ্দ পাওনা এখনো দেওয়া হয়নি কেন? ভুল হলো নাকি? চিরকেলে মামুলি বন্দোবস্ত, এখন ভুল হয়ে বন্ধ হবে, বড় অন্যায় কথা!” খাজাঞ্চী মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন – “এখনো আপনার ওখানে পৌঁছায়নি? বড় অন্যায় কথা! আমি এখনি পাঠাইয়া দিতেছি।”
ঠাকুরের ঐরূপে প্রসাদ চাহিয়া লওয়ায় যোগানন্দ স্বামীর চিন্তা
স্বামী যোগানন্দ তখন বালক। সত্কুলে বনেদী সাবর্ণ চৌধুরীদের ঘরে জন্ম, কাজেই মনে বেশ একটু অভিমানও ছিল। ঠাকুরবাড়ির খাজাঞ্চী, কর্মচারী, পূজারী প্রভৃতিদের একটা মানুষ বলিয়াই বোধ হইত না। তবে ঠাকুরের ভালবাসায় ও অহেতুক কৃপায় তাঁহার শ্রীপদে মাথা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন; এবং রাসমণির বাগানের একপ্রকার পার্শ্বেই তাঁহাদের বাড়ি বলিলেও চলে। কাজেই ঠাকুরের নিকট নিত্য যাওয়া-আসার বেশ সুবিধা। আর না যাইয়াই বা করেন কি? ঠাকুরের অদ্ভুত আকর্ষণ যে জোর করিয়া নিয়মিত সময়ে টানিয়া লইয়া যায়! কিন্তু ঠাকুরকে মানেন বলিয়া কি আর ঠাকুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে প্রীতির সহিত আলাপ করা চলে? অতএব ‘প্রসাদী ফল-মূলাদি কেন আসিল না’ বলিয়া ঠাকুর ব্যস্ত হইলে তিনি বলিয়াই ফেলিলেন – “তা নাই বা এল মশায়, ভারি তো জিনিস! আপনার তো ও-সকল পেটে সয় না, ওর কিছুই তো খান না – তখন নাই বা দিলে?” আবার ঠাকুর যখন তাঁহার ঐরূপ কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া অল্পক্ষণ পরেই নিজে খাজাঞ্চীকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইলেন, তখন যোগীন ভাবিতে লাগিলেন – ‘কি আশ্চর্য! ইনি আজ সামান্য ফল-মূল-মিষ্টান্নের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? যাঁকে কিছুতে বিচলিত হতে দেখিনি, তাঁর আজ এ ভাব কেন?’ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কোনই কারণ না খুঁজিয়া পাইয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন – ‘বুঝিয়াছি! ঠাকুরই হন, আর যত বড় লোকই হন, আকরে টানে আর কি! বংশানুক্রমে চাল-কলা-বাঁধা পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, সে বংশের গুণ একটু না একটু থাকবে তো? তাই আর কি! বড় বড় বিষয়ে ব্যস্ত হন না, কিন্তু এ সামান্য বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন! তা নহিলে, নিজে ও-সব খাবেন না, নিজের কোন দরকারেই লাগবে না, তবু তার জন্য এত ভাবনা কেন? বংশানুগত অভ্যাস!’
ঠাকুরের ঐরূপ করিবার কারণ নির্দেশ
যোগীন বা যোগানন্দ স্বামীজী এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “কি জানিস, রাসমণি দেবতার ভোগ হয়ে সাধু-সন্ত ভক্ত লোকে প্রসাদ পাবে বলে এতটা বিষয় দিয়ে গেচে। এখানে যা প্রসাদী জিনিস আসে, সে সব ভক্তেরাই খায়; ঈশ্বরকে জানবে বলে যারা সব এখানে আসে, তারাই খায়। এতে রাসমণির যে জন্য দেওয়া, তা সার্থক হয়। কিন্তু তার পর ওরা (ঠাকুরবাড়ির বামুনেরা) যা সব নিয়ে যায়, তার কি ওরূপ ব্যবহার হয়? চাল বেচে পয়সা করে! কারু কারু আবার বেশ্যা আছে; ঐসব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ায়, এইসব করে! রাসমণির যেজন্য দান, তার কিছুও অন্তত সার্থক হবে বলে এত করে ঝগড়া করি!” যোগীন স্বামীজী শুনিয়া অবাক। ঠাকুরের এ কাজেরও এত গূঢ় অর্থ!
মথুরের সহিত ঠাকুরের অদ্ভুত সম্বন্ধ
এইরূপে কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুর মথুরের সহিত পাতাইয়াছিলেন! মথুরের ভালবাসা ঘনীভূত হইয়া শেষে যে ‘বাবা’-অন্ত-প্রাণ হইয়াছিল, তাহা যে ঠাকুরের এইরূপ অহেতুক কৃপার ফলে, এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহার পর ঠাকুরের বালকবৎ অবস্থা মথুরকে কম আকর্ষণ করে নাই। সাংসারিক সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ বালকের প্রতি কাহার মন না আকৃষ্ট হয়? নিকটে থাকিলে – ক্রীড়া-মত্ততায় পাছে তাহার কোন অনিষ্ট হয় বলিয়া ভয়চকিত নয়নে তাহার অকারণ-মধুর চেষ্টাদি দেখিতে ও তাহাকে রক্ষা করিতে কে না ত্রস্তভাবে অগ্রসর হয়? আর ঠাকুরের বালকভাবটাতে তো আর কৃত্রিমতা বা ভানের লেশমাত্র ছিল না! যখন তিনি ঐ ভাবে থাকিতেন, তখন তাঁহাকে ঠিক ঠিক আত্মরক্ষণাসমর্থ বালক বলিয়াই বোধ হইত! কাজেই তেজীয়ান, বুদ্ধিমান মথুরের তাঁহাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করিবার স্বতই যে একটা চেষ্টার উদয় হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অতএব একদিকে মথুর যেমন ঠাকুরের দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিতেন, অপরদিকে তেমনি আবার তিনি ‘বাবা’কে অনভিজ্ঞ বালক জানিয়া সর্বদা রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। সর্বজ্ঞ গুরুভাব ও অল্পজ্ঞ বালকভাবের ‘বাবা’তে এইরূপ বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া, মথুর বোধ হয় মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, সাংসারিক সকল ব্যাপারে, এমনকি দেহরক্ষাদি-বিষয়েও তাঁহাকে ‘বাবা’কে রক্ষা করিতে হইবে; আর মানব-চক্ষু ও শক্তির অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষ্ম পারমার্থিক ব্যাপারে ‘বাবা’ই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। অতএব একই কালে দেব ও মানব, সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ, মহাজটিল বিপরীত ভাবসমষ্টির অপরূপ সম্মিলনভূমি এ অদ্ভুত ‘বাবা’র প্রতি মথুরের ভালবাসাটাও যে একটা জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল, এ কথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ভাবমুখে অবস্থিত বরাভয়কর ‘বাবা’ মথুরের উপাস্য হইলেও বালকভাবাবিষ্ট সরলতা ও নির্ভরের ঘনমূর্তি সেই ‘বাবা’কেই আবার সময়ে সময়ে মথুরকে নানা কথায় ভুলাইতে ও বুঝাইতে হইত!
মথুরের কামকীটের কথা বলিয়া বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে বুঝান
বাবার জিজ্ঞাসিত বিষয়সকল বুঝাইবার উদ্ভাবনী শক্তিও মথুরের ভালবাসায় বেশ যোগাইত! মথুরের সহিত কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বহির্দেশে গমন করিয়া ‘বাবা’ একদিন চিন্তায় মুখখানি শুষ্ক করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মথুরকে বলিলেন, “একি ব্যারাম হলো, বল দেখি? দেখলুম, প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে শরীর থেকে যেন একটা পোকা বেরিয়ে গেল! শরীরের ভিতরে এমন তো কারুর পোকা থাকে না। আমার একি হলো?” ইতঃপূর্বেই যে ‘বাবা’ হয়তো গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল অপূর্ব সরলভাবে বুঝাইয়া মোহিত ও মুগ্ধ করিতেছিলেন, সেই ‘বাবা’ই এখন বালকের ন্যায় নিষ্কারণ ভাবিয়া অস্থির! মথুরের আশ্বাসবাক্য এবং বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছেন! মথুর শুনিয়াই বলিলেন, “ও তো ভালই হয়েছে, বাবা! সকলের অঙ্গেই কামকীট আছে। উহাই তাদের মনে নানা কুভাবের উদয় করে কুকাজ করায়। মা-র কৃপায় তোমার অঙ্গ থেকে সেই কামকীট বেরিয়ে গেল! এতে এত ভাবনা কেন?” ‘বাবা’ শুনিয়াই বালকের ন্যায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, “ঠিক বলেছ; ভাগ্যিস তোমায় এ কথা বললুম, জিজ্ঞাসা করলুম!” বলিয়া বালকের ন্যায় ঐ কথায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।
মথুরের সহিত ঠাকুরের ভক্তদিগের আগমনের কথা
কথায় কথায় একদিন ‘বাবা’ বলিলেন, “দেখ, মা সব আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েচেন, এখানকার (ঠাকুরের নিজের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে; তারা সব আসবে; এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, শুনবে, প্রত্যক্ষ করবে; প্রেমভক্তি লাভ করবে; (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা দিয়ে মা অনেক খেলা খেলবেন, অনেকের উপকার করবেন, তাই এ খোলটা এখনও ভেঙে দেন নি – রেখেচেন। তুমি কি বল? এ সব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখেচি, বল দেখি?”
মথুর বলিলেন, “মাথার ভুল কেন হবে, বাবা? মা যখন তোমায় এ পর্যন্ত কোনটাই ভুল দেখান নাই, তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে; এখনও তারা সব দেরি করচে কেন? (অন্তরঙ্গ ভক্তেরা) শিগ্গির শিগ্গির আসুক না, তাদের নিয়ে আনন্দ করি।”
‘বাবা’ও বুঝিয়া গেলেন, মা ওসব ঠিক দেখাইয়াছেন। বলিলেন, “কি জানি বাবু, কবে তারা সব আসবে; মা বলেছেন, দেখিয়েছেন, মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।”
ঠাকুরের বালকভাবের দৃষ্টান্ত – সুষনিশাক তোলার কথা
রানী রাসমণির পুত্র ছিল না, চার কন্যা ছিল। মথুরবাবু তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয়া ও কনিষ্ঠাকে পর পর বিবাহ করিয়াছিলেন। অবশ্য একজনের মৃত্যু হইলে অপরকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জামাতাদিগের ভিতর বিষয় লইয়া পরে পাছে কোন গণ্ডগোল বাধে, এজন্য বুদ্ধিমতী রানী স্বয়ং বর্তমান থাকিতে থাকিতে প্রত্যেকের ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়া যান। ঐরূপে বিষয়ভাগ হইবার পরে একদিন মথুরবাবুর পত্নী বা সেজগিন্নি অপরের ভাগের এক পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইয়া সুন্দর সুষনি শাক হইয়াছে দেখিয়া তুলিয়া লইয়া আসেন। কেবল ঠাকুর তাঁহার ঐ কার্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ কার্য দেখিয়াই ঠাকুরের মনে নানা তোলাপাড়া উপস্থিত! না বলিয়া ওরূপে অপরের বিষয় সেজগিন্নি লইয়া গেল, বড় অন্যায়। না বলিয়া ওরূপে লইলে যে চুরি করা হয়, তাহা ভাবিল না। আর অপরের জিনিসে ওরূপ লোভ করা কেন বাবু? – ইত্যাদি, ইত্যাদি। ঐরূপ নানা কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় রানীর যে কন্যার ভাগে ঐ পুষ্করিণী পড়িয়াছে, তাঁহার সহিত দেখা। অমনি ঠাকুর তাঁহার নিকট ঐ বিষয়ের আদ্যোপান্ত বলিলেন। তিনি শুনিয়া এবং সেজগিন্নি যেন কতই অন্যায় করিয়াছে বলিয়া ঠাকুরের ঐরূপ গম্ভীর ভাব দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, ‘তাই তো বাবা, সেজ বড় অন্যায় করেছে।’ এমন সময় সেজগিন্নিও তথায় আসিয়া উপস্থিত। তিনিও ভগ্নীর হাস্যের কারণ শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, ‘বাবা, এ কথাটিও কি তোমার ওকে বলে দিতে হয়? আমি পাছে ও দেখতে পায় বলে লুকিয়ে শাকগুলি চুরি করে নিয়ে এলুম, আর তুমি কিনা তাই বলে দিয়ে আমাকে অপদস্থ করলে!’ এই বলিয়া দুই ভগ্নীতে হাস্যের রোল তুলিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, “তা, কি জানি বাবু, যখন বিষয় সব ভাগ-যোগ হয়ে গেল, তখন ওরূপে না বলে নেওয়াটা ভাল নয়; তাই বলে দিলুম যে, উনি শুনে যা হয় বোঝা-পড়া করুন।” রানীর কন্যারা ‘বাবা’র কথায় আরও হাসিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, বাবার কি সরল উদার স্বভাব!
সাংসারিক বিপদে মথুরের ঠাকুরের শরণাপন্ন হওয়া
একপক্ষে ‘বাবা’র এইরূপ বালকভাব! অপর দিকে আবার অন্য জমিদারের সহিত বিবাদে মথুরের হুকুমে লাঠালাঠি ও খুন হইয়া যাওয়ায় বিপদে পতিত মথুর আসিয়া ‘বাবা’কে ধরিলেন, ‘বাবা, রক্ষা কর।’ ‘বাবা’ প্রথম চটিয়া মথুরকে নানা ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন, “তুই শালা রোজ একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে এসে বলবি ‘রক্ষা কর’! আমি কি করতে পারি রে শালা? যা, নিজে বুঝগে যা; আমি কি জানি?” তারপর মথুরের নির্বন্ধে বলিলেন, “যাঃ, মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।” বাস্তবিকই সে বিপদ কাটিয়া গেল!
কৃপণ মথুরের ঠাকুরের জন্য অজস্র অর্থব্যয়ের দৃষ্টান্ত
ঠাকুরের উভয় ভাবের পরিচায়ক এইরূপ কত দৃষ্টান্তই না বলা যাইতে পারে! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই মথুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, বহুরূপী ‘বাবা’র কৃপাতেই তাঁহার যাহা কিছু – ধন বল, মান বল, প্রতাপ বল, আর যা কিছুই বল। সুতরাং বাবাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া রাজসম্মান দেওয়া ও অচল ভক্তি-বিশ্বাস করাটা মথুরের পক্ষে একটা বিচিত্র ব্যাপার হয় নাই। বিষয়ী লোকের ভক্তির দৌড় ভক্তিভাজনের প্রতি অর্থব্যয়েই বুঝিতে পারা যায়। তাহাতে আবার মথুর – সুচতুর হিসাবে বুদ্ধিমান বিষয়ী ব্যক্তি সচরাচর যেমন হইয়া থাকে – একটু কৃপণও ছিলেন। কিন্তু ‘বাবা’র বিষয়ে মথুরের অকাতরে ধনব্যয় দেখিয়া তাঁহার ভক্তি-বিশ্বাস যে বাস্তবিকই আন্তরিক ছিল, এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। ‘বাবা’কে যাত্রা শুনাইতে সাজ-গোজ পরাইয়া বসাইয়া, গায়কদের প্যালা বা পুরস্কার দিবার জন্য মথুর তাঁহার সামনে দশ দশ টাকার থাক করিয়া একেবারে একশত বা ততোধিক টাকা সাজাইয়া দিলেন। ‘বাবা’ যাত্রা শুনিয়া যাইতে যাইতে যেমনি কোন হৃদয়স্পর্শী গান বা কথায় মুগ্ধ ও ভাবাবিষ্ট হইলেন, অমনি হয়তো সে সমস্ত টাকাগুলিই একেবারে হাত দিয়া গায়কের দিকে ঠেলিয়া তাহাকে পুরস্কার দিয়া ফেলিলেন! মথুরের তাহাতে বিরক্তি নাই! ‘বাবার যেমন উঁচু মেজাজ, তেমনি তাহার মতোই প্যালা দেওয়া হইয়াছে’, বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার ঐরূপ টাকা সাজাইয়া দিলেন! ভাবমুখে অবস্থিত ‘বাবা’ – যিনি ‘টাকা মাটি, মাটি টাকা’ করিয়া একেবারে লোভশূন্য হইয়াছেন – তাঁহার সম্মুখে উহা আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? আবার হয়তো ভাবতরঙ্গের উন্মাদ-বিহ্ব্লতায় আত্মহারা হইয়া সমস্ত টাকা এককালে দিয়া ফেলিলেন! পরে কাছে টাকা নাই দেখিয়া হয়তো গায়ের শাল ও পরনের বহুমূল্য কাপড় পর্যন্ত খুলিয়া দিয়া কেবলমাত্র ভাবাম্বর ধারণ করিয়া নিস্পন্দ সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন! মথুর তাঁহার টাকার সার্থকতা হইল ভাবিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া ‘বাবা’কে বীজন করিতে লাগিলেন।
ঐ বিষয়ক অন্যান্য দৃষ্টান্ত
কৃপণ মথুরের ‘বাবা’র সম্বন্ধে এইরূপ উদারতার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়! মথুর ‘বাবা’কে সঙ্গে লইয়া ৺কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থপর্যটনে যাইয়া ‘বাবা’র কথায় ৺কাশীতে ‘কল্পতরু’ হইয়া দান করিলেন, আবশ্যকীয় পদার্থ যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিলেন! ‘বাবা’কে সে সময়ে কিছু চাহিতে অনুরোধ করায় ‘বাবা’ কিছুরই অভাব খুঁজিয়া পাইলেন না! বলিলেন, “একটি কমণ্ডলু দাও!” ‘বাবা’র ত্যাগ দেখিয়া মথুরের চক্ষে জল আসিল।
ঠাকুরের ইচ্ছায় মথুরের বৈদ্যনাথে দরিদ্রসেবা
মথুরের সহিত কাশী বৃন্দাবনাদি তীর্থদর্শনে যাইবার কালে ৺বৈদ্যনাথের নিকটবর্তী কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় গ্রামবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া ‘বাবা’র হৃদয় একেবারে করুণায় পূর্ণ হইল। মথুরকে বলিলেন, “তুমি তো মা-র দেওয়ান; এদের এক মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।” মথুর প্রথম একটু পেছপাও হইলেন। বলিলেন, ‘বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেকগুলি লোক, এদের খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থায় কি বলেন?’ সে কথা শুনে কে? বাবার তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন, “দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।” এই বলিয়া বালকের ন্যায় গোঁ ধরিয়া দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলেন! তাঁহার ঐরূপ করুণা দেখিয়া মথুর তখন কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া ‘বাবা’র কথামত সকল কার্য করিলেন। ‘বাবা’ও গ্রামবাসীদের আনন্দ দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে মথুরের সহিত কাশী গমন করিলেন। শুনিয়াছি, মথুরের সহিত রাণাঘাটের সন্নিহিত তাঁহার জমিদারিভুক্ত কোন গ্রামে অন্য এক সময়ে বেড়াইতে যাইয়া, গ্রামবাসীদের দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে ঐরূপ করুণার আর একবার উদয় হইয়াছিল এবং মথুরের দ্বারা আর একবার ঐরূপ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন।
ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ দৈবনির্দিষ্ট; ভোগবাসনা ছিল বলিয়া মথুরের পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ঠাকুর
গুরুভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর এইরূপ মধুর সম্বন্ধে মথুরকে চিরকালের মতো আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সাধনকালে একসময়ে ঠাকুরের মনে যে অদ্ভুত ভাবের সহসা উদয় হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা করাইয়াছিল, “মা, আমাকে শুকনো সাধু করিস নি, রসে বশে রাখিস” – মথুরানাথের সহিত এই প্রকার অদৃষ্টপূর্ব সম্বন্ধ তাহারই পরিণত ফলবিশেষ। কারণ, সেই প্রার্থনার ফলেই ৺জগন্মাতা ঠাকুরকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার দেহরক্ষাদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য চারিজন রসদ্দার তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে এবং মথুরানাথই তাঁহাদের ভিতর প্রথম ও অগ্রণী। দৈবনির্দিষ্ট সম্বন্ধ না হইলে কি এতকাল এ সম্বন্ধ এরূপ অক্ষুণ্ণভাবে কখনও থাকিতে পারিত? হায় পৃথিবী, এরূপ বিশুদ্ধ মধুর সম্বন্ধ এতকাল কয়টাই বা তুমি নয়নগোচর করিয়াছ! আর বলি, হায় ভোগবাসনা, তুমি কি বজ্রবন্ধনেই না মানবমনকে বাঁধিয়াছ! এই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব অহেতুক ভালবাসার ঘনীভূত প্রতিমা এমন অদ্ভুত ঠাকুরকে দেখিয়া ও তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়া এখনও আমাদের মন তোমাকে ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহে না! জনৈক বন্ধু ঠাকুরের নিজমুখ হইতে একদিন মথুরানাথের অপূর্ব কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মহাভাগ্যের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত ও বিভোর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “(মৃত্যুর পর) মথুরের কি হলো, মশায়? তাকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না!” ঠাকুর শুনিয়া উত্তর করিলেন, “কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে আর কি! ভোগবাসনা ছিল।” এই বলিয়াই ঠাকুর অন্য কথা পাড়িলেন।
তৃতীয় খণ্ড – অষ্টম অধ্যায়: গুরুভাবে নিজগুরুগণের সহিত সম্বন্ধ
গুরুভাব অবতারপুরুষদিগের নিজস্ব সম্পত্তি
সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥
– গীতা, ১৫।১৫
পূর্বেই বলিয়াছি, যিনি গুরু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাল্যাবধিই তাঁহার ভিতর ঐ ভাবের পরিচয় বেশ পাওয়া গিয়া থাকে। মহাপুরুষ অবতারকুলের তো কথাই নাই। তাঁহাদের মধ্যে যিনি জনসমাজে যে ভাব-প্রতিষ্ঠার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, বাল্যাবধিই তাঁহাতে যেন ঐ ভাব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়! শরীরেন্দ্রিয়াদির পূর্ণতা, দেশকালাদি অবস্থাসকলের অনুকূলতা প্রভৃতি কারণসমূহ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের জীবনে ঐ ভাব পূর্ণ পরিস্ফুট হইবার সহায়তা করিতে পারে; কিন্তু ঐ সকল কারণই যে তাঁহাদের ভিতর ঐ ভাবের জন্ম দিয়া এ জীবনে তাঁহাদের গুরু করিয়া তোলে, তাহা নহে। দেখা যায়, উহা যেন তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি, উহা লইয়াই তাঁহারা যেন জীবন আরম্ভ করিয়াছেন, এবং বর্তমান জীবনে ঐ ভাবোৎপত্তির কারণানুসন্ধান করিলে সহস্র চেষ্টাতেও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবোৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে যাইলেও ঠিক ঐরূপ দেখা যায়। বাল্যে দেখ, যৌবনে দেখ, সাধনকালে দেখ, সকল সময়েই ঐ ভাবের অল্পাধিক বিকাশ তাঁহার জীবনে দেখিতে পাইয়া অবাক হইতে হয়; আর কিরূপে ঐ ভাবের প্রথম আরম্ভ তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইল, এ কথা ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। বাল্যজীবনের উল্লেখ এখানে করিয়া আমাদের পুঁথি বাড়াইতে ইচ্ছা নাই। তবে ঠাকুরের যৌবন এবং সাধনকালে, যে কালের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত মথুরবাবুকে লইয়া কত প্রকার গুরুভাবের লীলার বিকাশ হইয়াছিল, সেই কালেরই অনেক কথা এখনো বলিতে বাকি আছে এবং তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিলে মন্দ হইবে না।
ঠাকুরের বহু গুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ
মন্ত্রদাতা গুরু এক হইলেও উপগুরু বা শিক্ষাগুরু অনেক করা যাইতে পারে – এ বিষয়টি ঠাকুর অনেক সময়ে আমাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতের অবধূতোপাখ্যানের কথা তুলিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেন। ভাগবতে লেখা আছে, ঐ অবধূত ক্রমে ক্রমে চব্বিশজন উপগুরুর নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা পর পর লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনেও আমরা ঐরূপে বিশেষ বিশেষ সাধনোপায় ও সত্যোপলব্ধির জন্য বহু বহু গুরুগ্রহণের অভাব দেখি না। তন্মধ্যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী; ‘ল্যাংটা’ তোতাপুরী ও মুসলমান গোবিন্দের নামই আমরা অনেক সময়ে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। অপরাপর হিন্দুসম্প্রদায়ের সাধনোপায়সমূহ অন্যান্য গুরুগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিলেও ঠাকুর তাঁহাদের নাম বড় একটা উল্লেখ করিতেন না। কেবলমাত্র বলিতেন যে, তিনি অন্যান্য গুরুগণের নিকট হইতে অন্যান্য মতের সাধন-প্রণালী জানিয়া লইয়া তিন তিন দিন মাত্র সাধন করিয়াই ঐ সকল মতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সকল গুরুগণের নাম ঠাকুরের মনে ছিল না, অথবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে বলিয়াই ঠাকুর উল্লেখ করিতেন না, তাহা এখন বলা কঠিন। তবে এটা বুঝা যায় যে, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধও ঠাকুরের অতি অল্পকালের নিমিত্ত হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাদের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।
ভৈরবী ব্রাহ্মণী বা ‘বামনী’
ঠাকুরের শিক্ষাগুরুগণের ভিতর আবার ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকটে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। কত কাল, তাহা ঠিক নির্দেশ করিয়া বলা সুকঠিন, কারণ, ঠাকুরের শ্রীচরণপ্রান্তে আমাদের আশ্রয়গ্রহণ করিবার কিছুকাল পূর্বে তিনি দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন এবং পুনরায় আর ফিরিয়া আসেন নাই। ইহার পরে ঠাকুর তাঁহার আর একবার মাত্র সন্ধান পাইয়াছিলেন; তখন ঐ ব্রাহ্মণী ভৈরবী ৺কাশীধামে কাল কাটাইতেছিলেন।1
1. সাধকভাব (১০ম সংস্করণ), দ্বাদশ অধ্যায়।
‘বামনী’র ঠাকুরকে সহায়তা
ব্রাহ্মণী ভৈরবী যে বহুকাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এবং তন্নিকটবর্তী গঙ্গাতটে – যথা, দেবমণ্ডলের ঘাট প্রভৃতি স্থলে – বাস করিয়াছিলেন, ইহা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে চৌষট্টিখানা প্রধান প্রধান তন্ত্রোক্ত যত কিছু সাধন-প্রণালী, সকলই একে একে করাইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবমতসম্বন্ধীয় তন্ত্রাদিতেও সুপণ্ডিতা ছিলেন; তবে ঠাকুরকে সখীভাব প্রভৃতি সাধনকালেও কোন কোন স্থলে সহায়তা করিয়াছিলেন কিনা, ঐ বিষয়ে কোন কথা স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই।1 শুনিয়াছি যে, ঠাকুরকে ঐরূপে সাধনকালে সহায়তা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পরেও তিনি কয়েক বৎসর – সর্বসুদ্ধ কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর কাল, বহু সম্মানে দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াছিলেন এবং ঐ কালের মধ্যে কখনো কখনো ঠাকুর এবং তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর পর্যন্ত যাইয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে বাস করিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এই সময় হইতে ব্রাহ্মণীকে আপন শ্বশ্রূর ন্যায় সম্মান এবং মাতৃসম্বোধন করিতেন।
1. সাধকভাব (১০ম সংস্করণ), দ্বাদশ অধ্যায়।
‘বামনী’র বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্তভাবে অভিজ্ঞতা
ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবদিগের সাধন-প্রণালী অনুসরণ করিয়া সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাবসমূহের রসও কিছু কিছু নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে দেবমণ্ডলের ঘাটে অবস্থানকালে তিনি ঠাকুরের প্রতি বাৎসল্যরসে মুগ্ধ হইয়া ননী হস্তে লইয়া নয়নাশ্রুতে বসন সিক্ত করিতে করিতে ‘গোপাল’ ‘গোপাল’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেন। আর, এদিকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে সহসা ঠাকুরের মন ব্রাহ্মণীকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত। শুনিয়াছি, তখন তিনি বালক যেমন জননীর নিকট উপস্থিত হয়, তেমনি একছুটে ঐ এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং নিকটে বসিয়া ননী ভোজন করিতেন! এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণীও কখনো কখনো কোথা হইতে যোগাড় করিয়া লাল বেনারসী চেলী ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার ভক্ষ্যভোজ্যাদি হস্তে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইয়া যাইতেন। ঠাকুর বলিতেন, তাঁহার আলুলায়িত কেশ এবং ভাববিহ্ব্ল অবস্থা দেখিয়া তখন তাঁহাকে গোপালবিরহে কাতরা নন্দরাণী যশোদা বলিয়াই লোকের মনে হইত।
‘বামনী’র রূপ-গুণ দেখিয়া মথুরের সন্দেহ
ব্রাহ্মণী গুণে যেমন, রূপেও তেমনি অসামান্যা ছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, মথুরবাবু প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণীর রূপলাবণ্যদর্শনে এবং তাঁহার একাকিনী অসহায় অবস্থায় যথাতথা ভ্রমণাদি শুনিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। একদিন নাকি বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াও ফেলিয়াছিলেন, “ভৈরবী, তোমার ভৈরব কোথায়?” ব্রাহ্মণী তখন মা কালীর মন্দির হইতে দর্শনাদি করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন। হঠাৎ ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াও কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা রাগান্বিতা না হইয়া স্থিরভাবে মথুরের প্রতি প্রথম নিরীক্ষণ করিলেন, পরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পদতলে শবরূপে পতিত মহাদেবকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া মথুরকে দেখাইয়া দিলেন। সন্দিগ্ধমনা বিষয়ী মথুরও অল্পে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। বলিলেন, “ও ভৈরব তো অচল।” ব্রাহ্মণী তখন ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, “যদি অচলকে সচল করিতেই না পারিব, তবে আর ভৈরবী হইয়াছি কেন?” ব্রাহ্মণীর ঐরূপ ধীর গম্ভীর ভাব ও উত্তরে মথুর লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। পরে দিন দিন তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি ও অশেষ গুণের পরিচয় যতই পাইতে থাকিলেন, ততই মথুরের মনে আর ঐরূপ দুষ্ট সন্দেহ রহিল না।
‘বামনী’র পূর্বপরিচয়
ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী পূর্ববঙ্গের কোন স্থলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিলেই ‘বড় ঘরের মেয়ে’ বলিয়া সকলের নিঃসংশয় ধারণা হইত। বাস্তবিকও তিনি তাহাই ছিলেন। কিন্তু কোন্ গ্রামে কাহার ঘর পুত্রীরূপে আলো করিয়াছিলেন, ঘরণীরূপে কাহারও ঘর কখনো উজ্জ্বল করিয়াছিলেন কিনা, এবং প্রৌঢ় বয়সে এইরূপে সন্ন্যাসিনী হইয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিবার ও সংসারে বীতরাগ হইবার কারণই বা কি হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠাকুরের নিকট হইতে কখনই শুনি নাই। আবার এত লেখা-পড়াই বা শিখিলেন কোথায় এবং সাধনেই বা এত উন্নতিলাভ কোথায়, কবে করিলেন – তাহাও আমাদের কাহারও কিছুমাত্র জানা নাই।
ব্রাহ্মণী উচ্চদরের সাধিকা
সাধনে যে ব্রাহ্মণী বিশেষ উন্নতা হইয়াছিলেন, এ কথা আর বলিতে হইবে না। দৈবকর্তৃক ঠাকুরের গুরুরূপে মনোনীত হওয়াতেই তাঁহার পরিচয় বিশেষরূপে পাওয়া যায়। আবার যখন ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকটে আসিবার পূর্বেই যোগবলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জীবৎকালে তাঁহাকে ঠাকুরপ্রমুখ তিন ব্যক্তিকে সাধনায় সহায়তা করিতে হইবে এবং ঐ তিন ব্যক্তির সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে সাক্ষাৎ হইবামাত্র ব্রাহ্মণী তাঁহাদের চিনিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন, তখন আর ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না।
‘বামনী’র যোগলব্ধ দর্শন
ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই চন্দ্র ও গিরিজার কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, “বাবা, তাদের দুজনকে ইহার পূর্বেই পেয়েছি; আর তোমাকে এতদিন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, আজ পেলেম। তাদের সঙ্গে পরে তোমায় দেখা করিয়ে দিব।” বাস্তবিকও পরে ঐ দুই ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে আনিয়া ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সহিত দেখা করাইয়া দেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইঁহারা দুইজনেই উচ্চদরের সাধক ছিলেন। কিন্তু সাধনার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইলেও ঈশ্বরের দর্শনলাভে সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। বিশেষ বিশেষ শক্তি বা সিদ্ধাই লাভ করিয়া পথভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছিলেন।
ব্রাহ্মণীর শিষ্য চন্দ্রের কথা
ঠাকুর বলিতেন, চন্দ্র ভাবুক ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহার ‘গুটিকাসিদ্ধি’-লাভ হইয়াছিল। মন্ত্রপূত গুটিকাটি অঙ্গে ধারণ করিয়া তিনি সাধারণ নয়নের দৃষ্টিবহিৰ্ভূত বা অদৃশ্য হইতে পারিতেন এবং ঐরূপে অদৃশ্য হইয়া সযত্নে রক্ষিত দুর্গম স্থানেও গমনাগমন করিতে পারিতেন।
সিদ্ধাই যোগভ্রষ্টকারী
কিন্তু ঈশ্বরলাভের পূর্বে ক্ষুদ্র মানব-মন ঐ প্রকার সিদ্ধাইসকল লাভ করিলেই যে অহঙ্কৃত হইয়া উঠে, এবং অহঙ্কারবৃদ্ধিই যে মানবকে বাসনাজালে জড়িত করিয়া উচ্চ লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে দেয় না এবং পরিশেষে তাহার পতনের কারণ হয়, এ কথা আর বলিতে হইবে না। অহঙ্কারবৃদ্ধিতেই পাপের বৃদ্ধি এবং উহার হ্রাসেই পুণ্যলাভ, অহঙ্কারবৃদ্ধিতেই ধর্মহানি এবং অহঙ্কারনাশেই ধর্মলাভ, স্বার্থপরতাই পাপ এবং স্বার্থনাশই পুণ্য, “আমি মলে ফুরায় জঞ্জাল” – এ কথা ঠাকুর আমাদের বার বার কত প্রকারেই না বুঝাইতেন! বলিতেন, “ওরে, অহঙ্কারকেই শাস্ত্রে চিজ্জড়গ্রন্থি বলেছে; চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা; এবং জড় অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি; ঐ অহঙ্কার এতদুভয়কে একত্রে বাঁধিয়া রাখিয়া মানব-মনে ‘আমি দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদিবিশিষ্ট জীব’ – এই ভ্রম স্থির করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বিষম গাঁটটা না কাটতে পারলে এগুনো যায় না। ঐটেকে ত্যাগ করতে হবে। আর মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, সিদ্ধাইগুলো বিষ্ঠাতুল্য হেয়। ও-সকলে মন দিতে নেই। সাধনায় লাগলে ওগুলো কখনো কখনো আপনা-আপনি এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু ওগুলোয় যে মন দেয়, সে ঐখানেই থেকে যায়, ভগবানের দিকে আর এগুতে পারে না।” স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানই জীবনস্বরূপ ছিল; খাইতে শুইতে বসিতে সকল সময়েই তিনি ঈশ্বরধ্যানে মন রাখিতেন, কতকটা মন সর্বদা ভিতরে ঈশ্বরের চিন্তায় রাখিতেন। ঠাকুর বলিতেন, তিনি ‘ধ্যানসিদ্ধ’; ধ্যান করিতে করিতে সহসা একদিন তাঁহার দূরদর্শন ও শ্রবণের (বহু দূরে অবস্থিত ব্যক্তিসকল কি করিতেছে, বলিতেছে, ইহা দেখিবার ও শ্রবণ করিবার) ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত! ধ্যান করিতে বসিয়া একটু ধ্যান জমিলেই মন এমন এক ভূমিতে উঠিত যে, তিনি দেখিতেন অমুক ব্যক্তি অমুক বাটীতে বসিয়া অমুক প্রসঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছেন! ঐরূপ দেখিয়াই আবার প্রাণে ইচ্ছার উদয় হইত, যাহা দেখিলাম তাহা সত্য কি মিথ্যা, জানিয়া আসি। আর অমনি ধ্যান ছাড়িয়া তিনি সেই সেই স্থলে আসিয়া দেখিতেন, যাহা ধ্যানে দেখিয়াছেন তাহার সকলই সত্য, এতটুকু মিথ্যা নহে! কয়েক দিবস ঐরূপ হইবার পর, ঠাকুরকে ঐ কথা বলিবামাত্র ঠাকুর বলিলেন, “ও সকল ঈশ্বরলাভ-পথের অন্তরায়। এখন কিছুদিন আর ধ্যান করিসনি।”
সিদ্ধাইলাভে চন্দ্রের পতন
গুটিকাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রেরও অহঙ্কার বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, চন্দ্রের মনে ক্রমে কাম-কাঞ্চনাসক্তি বাড়িয়া যায় এবং এক অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া ঐ সিদ্ধাইপ্রভাবেই তাহার বাটীতে যাতায়াত করিতে থাকেন; এবং ঐরূপে অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার বৃদ্ধিতে ক্রমে ঐ সিদ্ধাইও হারাইয়া বসিয়া নানারূপে লাঞ্ছিত হন।
‘বামনী’র শিষ্য গিরিজার কথা
গিরিজারও অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ঠাকুর আমাদের বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, একদিন ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটীর নিকটবর্তী শ্রীযুক্ত শম্ভু মল্লিকের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। শম্ভু মল্লিক ঠাকুরকে বড়ই ভালবাসিতেন এবং ঠাকুরের কোনরূপ সেবা করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। শম্ভুবাবু ২৫০ টাকা দিয়া কালীবাড়ির নিকট কিছু জমি খাজনা করিয়া লইয়া তাহার উপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর থাকিবার জন্য ঘর করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তখন তখন গঙ্গাস্নান করিতে এবং ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে ঐ ঘরেই বাস করিতেন। ঐ স্থানে থাকিবার কালে এক সময়ে তিনি কঠিন রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্তা হন; তখন শম্ভুবাবুই চিকিৎসা, পথ্যাদি সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শম্ভুবাবুর ভক্তিমতী পত্নীও ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন; প্রতি জয়মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এখানে থাকিলে তাঁহাকে লইয়া গিয়া দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেন। এতদ্ভিন্ন শম্ভুবাবু ঠাকুরের কলিকাতায় গমনাগমনের গাড়িভাড়া এবং খাদ্যাদির যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তাহাই যোগাইতেন। অবশ্য মথুরবাবুর শরীরত্যাগের পরেই শম্ভুবাবু ঠাকুরের ঐরূপ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। শম্ভুকে ঠাকুর তাঁহার ‘দ্বিতীয় রসদ্দার’ বলিয়া নির্দেশ করিতেন এবং তখন তখন প্রায়ই তাঁহার উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া তাঁহার সহিত ধর্মালাপে কয়েক ঘণ্টাকাল কাটাইয়া আসিতেন।
গিরিজার সিদ্ধাই
গিরিজার সহিত সেদিন শম্ভুবাবুর বাগানে বেড়াইতে যাইয়া কথাবার্তায় অনেক কাল কাটিয়া গেল। ঠাকুর বলিতেন, “ভক্তদের গাঁজাখোরের মতো স্বভাব হয়! গাঁজাখোর যেমন গাঁজার কল্কেতে ভরপুর এক দম লাগিয়ে কল্কেটা অপরের হাতে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে – অপর গাঁজাখোরের হাতে ঐরূপে কল্কেটা না দিতে পারলে যেমন তার একলা নেশা করে সুখ হয় না, ভক্তেরাও সেইরূপ একসঙ্গে জুটলে একজন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, ভাবে তন্ময় হয়ে বলে ও আনন্দে চুপ করে এবং অপরকে ঐ কথা বলতে অবসর দেয় ও শুনে আনন্দ পায়।” সেদিন শম্ভুবাবু, গিরিজা ও ঠাকুর একসঙ্গে ঐরূপে মিলিত হওয়ায় কোথা দিয়া যে কাল কাটিতে লাগিল তাহা কেহই টের পাইলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা ও এক প্রহর রাত্রি হইল, তখন ঠাকুরের ফিরিবার হুঁশ হইল। শম্ভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিরিজার সহিত রাস্তায় আসিলেন এবং কালীবাটীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেজায় অন্ধকার। পথের কিছুই দেখিতে না পাওয়ায় প্রতি পদে পদস্খলন ও দিক্ভুল হইতে লাগিল। অন্ধকারের কথা খেয়াল না করিয়া, ঈশ্বরীয় কথার ঝোঁকে চলিয়া আসিয়াছেন, শম্ভুর নিকট হইতে একটা লণ্ঠন চাহিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন – এখন উপায়? কোনরূপে গিরিজার হাত ধরিয়া হাতড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেজায় কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ঐরূপ কষ্ট দেখিয়া গিরিজা বলিলেন, “দাদা, একবার দাঁড়াও, আমি তোমায় আলো দেখাইতেছি।” – এই বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে জ্যোতির একটা লম্বা ছটা নির্গত করিয়া পথ আলোকিত করিলেন! ঠাকুর বলিতেন, “সে ছটায় কালীবাটীর ফটক পর্যন্ত বেশ দেখা যাইতে লাগিল ও আমি আলোয় আলোয় চলিয়া আসিলাম।”
গুরুভাবে ঠাকুরের চন্দ্র ও গিরিজার সিদ্ধাইনাশ
এই কথা বলিয়াই কিন্তু ঠাকুর আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “কিন্তু তাদের ঐরূপ ক্ষমতা আর বেশিদিন রহিল না! এখানকার (তাঁহার নিজের) সঙ্গে কিছুদিন থাকতে থাকতে ঐসকল সিদ্ধাই চলে গেল!” আমরা ঐরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, (নিজের শরীর দেখাইয়া) “মা এর ভেতরে তাদের কল্যাণের জন্য তাদের সিদ্ধাই বা শক্তি আকর্ষণ করে নিলেন। আর ঐরূপ হবার পর তাদের মন আবার ঐসব ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল!”
সিদ্ধাই ভগবানলাভের অন্তরায়; ঐ বিষয়ে ঠাকুরের ‘পায়ে হেঁটে নদী পারের’ গল্প
এই বলিয়াই ঠাকুর আবার বলিলেন, “ও-সকলে আছে কি? ও-সব সিদ্ধাইয়ের বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে চলে যায়। একটা গল্প শোন্ – একজনের দুই ছেলে ছিল। বড়র যৌবনেই বৈরাগ্য হলো ও সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল। আর ছোট লেখা-পড়া শিখে ধার্মিক বিদ্বান হয়ে বিবাহ করে সংসারধর্ম করতে লাগল। এখন সন্ন্যাসীদের নিয়ম – বার বৎসর অন্তে, ইচ্ছা হলে একবার জন্মভূমি দর্শন করতে যায়। ঐ সন্ন্যাসীও ঐরূপে বার বৎসর বাদে জন্মভূমি দেখতে আসে এবং ছোট ভায়ের জমি, চাষ-বাস, ধন-ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে তার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে তার নাম ধরে ডাকতে লাগল। নাম শুনে ছোট ভাই বাইরে এসে দেখে – তার বড় ভাই! অনেক দিন পরে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা – ছোট ভাইয়ের আর আনন্দের সীমা রইল না! দাদাকে প্রণাম করে বাড়িতে এনে বসিয়ে তার সেবাদি করতে লাগল। আহারান্তে দুই ভাইয়ের নানা প্রসঙ্গ হতে লাগল। তখন ছোট বড়কে জিজ্ঞাসা করল, ‘দাদা, তুমি যে এই সংসারের ভোগ-সুখ সব ত্যাগ করে এতদিন সন্ন্যাসী হয়ে ফিরলে, এতে কি লাভ করলে আমাকে বল।’ শুনেই দাদা বললে, ‘দেখবি? তবে আমার সঙ্গে আয়।’ – বলেই ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির নিকটে নদীতীরে এসে উপস্থিত হলো এবং বললে, ‘এই দেখ।’ বলেই নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে পরপারে চলে গেল! গিয়ে বললে, ‘দেখলি?’ ছোট ভাইও পার্শ্বের খেয়ানৌকায় মাঝিকে আধ পয়সা দিয়ে নদী পেরিয়ে বড় ভায়ের নিকটে গিয়ে বললে, ‘কি দেখলুম?’ বড় বললে, ‘কেন? এই হেঁটে নদী পেরিয়ে আসা?’ তখন ছোট ভাই হেসে বললে, ‘দাদা, তুমিও তো দেখলে – আমি আধ পয়সা দিয়ে এই নদী পেরিয়ে এলুম। তা তুমি এই বার বৎসর এত কষ্ট সয়ে এই পেয়েছ? আমি যা আধ পয়সায় অনায়াসে করি, তাই পেয়েছ? ও ক্ষমতার দাম তো আধ পয়সা মাত্র।’ ছোটর ঐ কথায় বড় ভায়ের তখন চৈতন্য হয় এবং ঈশ্বরলাভে মন দেয়।”
সিদ্ধাইয়ে অহঙ্কার-বৃদ্ধি-বিষয়ে ঠাকুরের ‘হাতী-মরা-বাঁচা’র গল্প
ঐরূপে কথাচ্ছলে ঠাকুর কত প্রকারেই না আমাদের বুঝাইতেন যে, ধর্মজগতে ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষমতালাভ অতি তুচ্ছ, হেয়, অকিঞ্চিৎকর পদার্থ! ঠাকুরের ঐরূপ আর একটি গল্পও আমরা এখানে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না – “একজন যোগী যোগসাধনায় বাকসিদ্ধি লাভ করেছিল। যাকে যা বলত তাই তৎক্ষণাৎ হতো; এমনকি কাকেও যদি বলত ‘মর্’, তো সে অমনি মরে যেত, আবার যদি তখনি বলত ‘বাঁচ্’, তো তখনি বেঁচে উঠত! একদিন ঐ যোগী পথে যেতে যেতে একজন ভক্ত সাধুকে দেখতে পেলে। দেখলে, তিনি সর্বদা ঈশ্বরের নাম জপ ও ধ্যান কচ্ছেন। শুনলে, ঐ ভক্ত সাধুটি ঐ স্থানে অনেক বৎসর ধরে ঐরূপে তপস্যা কচ্ছেন। দেখে-শুনে অহঙ্কারী যোগী ঐ সাধুটির কাছে গিয়ে বললে, ‘ওহে, এতকাল ধরে তো ‘ভগবান ভগবান’ করচ, কিছু পেলে বলতে পার?’ ভক্ত সাধু বললেন, ‘কি আর পাব বলুন। তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া ছাড়া আমার তো আর অন্য কোন কামনা নেই। আর তাঁকে পাওয়া তাঁর কৃপা না হলে হয় না। তাই পড়ে পড়ে তাঁকে ডাকচি, দীন হীন বলে যদি কোন দিন কৃপা করেন।’ যোগী ঐ কথা শুনেই বললে, ‘যদি না-ই কিছু পেলে, তবে এ পণ্ডশ্রমের আবশ্যক কি? যাতে কিছু পাও তার চেষ্টা কর।’ ভক্ত সাধুটি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বললেন, ‘আচ্ছা মশায়, আপনি কি পেয়েছেন – শুনতে পাই কি?’ যোগী বললে, ‘শুনবে আর কি – এই দেখ।’ এই বলে নিকটে বৃক্ষতলে একটা হাতি বাঁধা ছিল, তাকে বললে, ‘হাতি, তুই মর্।’ অমনি হাতিটা মরে গেল! যোগী দম্ভ করে বললে, ‘দেখলে? আবার দেখ।’ বলেই মরা হাতিটাকে বললে, ‘হাতি, তুই বাঁচ্।’ অমনি হাতিটা বেঁচে পূর্বের ন্যায় গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল! যোগী বললে, ‘কি হে, দেখলে তো?’ ভক্ত সাধু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন; এখন বললেন, ‘কি আর দেখলুম বলুন – হাতিটা একবার মলো, আবার বাঁচল, কিন্তু বলবেন কি, হাতির ঐরূপ মরা-বাঁচায় আপনার কি এসে গেল? আপনি কি ঐরূপ শক্তিলাভ করে বার বার জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন? জরা-ব্যাধি কি আপনাকে ত্যাগ করেছে? না, আপনার অখণ্ড-সচ্চিদানন্দস্বরূপ দর্শন হয়েছে?’ যোগী তখন নির্বাক হয়ে রইল এবং তার চৈতন্য হলো।”
চন্দ্র1 ও গিরিজা এইরূপে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় ঈশ্বরীয় পথে অনেকদূর অগ্রসর হইলেও সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। ঠাকুরের জ্বলন্ত দর্শনলাভ করিয়া এবং তাঁহার দিব্যশক্তিবলে অহঙ্কারের মূল ঐ সকল সিদ্ধাইয়ের নাশ হওয়াতেই তাঁহাদের ঐ বিষয়ে চৈতন্য হয় এবং দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় ঈশ্বরীয় পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।
1. ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাত্রা করেন। উহারই কিছুকাল পরে বেলুড় মঠে একদিন এক ব্যক্তি সহসা আসিয়া আপনাকে ‘চন্দ্র’ বলিয়া পরিচয় দেন এবং প্রায় মাসাবধিকাল তথায় বাস করেন। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন সর্বদা মঠেই থাকিতেন। তাঁহার সহিত ঐ ব্যক্তির গোপনে অনেক কথাবার্তাও হইতে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি তিনি ব্রহ্মানন্দজীকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেন – “আপনি কি এখানে কিছু টের পান? অর্থাৎ, ঠাকুরের জাগ্রত সত্তা কিছু অনুভব করেন?” – ইত্যাদি।
তিনি বলিতেন, ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তাহার সমুদয় কথাই সত্য ঘটিয়াছে। কেবল মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে দর্শন দিতে যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ঐ কথাটিই সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহার তখনও বাকি আছে। লোকটি মঠের ঠাকুরঘরে গিয়া প্রতিদিন অনেকক্ষণ অতি ভক্তির সহিত জপ-ধ্যান করিতেন। ঐ সময় তাঁহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রুও পড়িত। ঠাকুরের সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইনি তৎসম্বন্ধে যাহা জানিতেন তাহা অতি আনন্দের সহিত বলিতেন। ইঁহাকে অতি শান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়াই আমাদের বোধ হইয়াছিল। লোকটিকে সর্বদা একস্থানে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে এবং সময়ে সময়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে দেখিয়া এক সময়ে একজন ইঁহাকে উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন – “মহাশয়ের কি আফিম খাওয়ার অভ্যাস আছে?” উহাতে তিনি অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন – “আমি আপনাদের নিকট কি অপরাধে অপরাধী হইয়াছি যে ঐরূপ কথা বলিতেছেন?”
ঠাকুরঘরে যাইয়া প্রথম প্রণামকালে তিনি ঠাকুরের শ্রীমূর্তিকে ‘দাদা’ বলিয়া সম্বোধন করেন এবং ভাবে-প্রেমে আবিষ্ট হইয়া অজস্র নয়নাশ্রু বর্ষণ করেন। তাঁহাকে দেখিলে সাধারণ লোকের ন্যায়ই বোধ হইত। গৈরিক বা তিলকাদির আড়ম্বর ছিল না। পরিধানে সামান্য একখানি ধুতি ও উড়ানি এবং হাতে ছাতি ও একটি কাম্বিসের ব্যাগ মাত্র ছিল। ব্যাগের ভিতর আর একখানি পরিধেয় ধুতি, গামছা ও বোধ হয় একটি জল খাইবার ঘটি মাত্র ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ঐরূপে প্রায়ই তীর্থে তীর্থে পর্যটন করিয়া বেড়ান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইঁহাকে বিশেষ আদর-সম্মান করিয়া মঠেই চিরকাল থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইনিও সম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, “দেশের জমিগুলোর একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া এখানে থাকিব।” কিন্তু তদবধি আর ঐ ব্যক্তি এ পর্যন্ত মঠে আসেন নাই। প্রসঙ্গোক্ত চন্দ্র সম্ভবতঃ তিনিই হইবেন।
‘বামনী’র নির্বিকল্প অদ্বৈতভাব-লাভ হয় নাই; তদ্বিষয়ে প্রমাণ
ভৈরবী ব্রাহ্মণী স্বয়ং সাধনে বহুদূর অগ্রসর হইলেও অখণ্ড সচ্চিদানন্দলাভে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত যে হন নাই, তাহারও পরিচয় আমরা বেশ পাইয়া থাকি। বেদান্তের শেষভূমি, নির্বিকল্প অবস্থার অধিকারী ‘ল্যাংটা’ তোতাপুরী যখন ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে প্রথম আগমন করেন, তখন ঠাকুরের ব্রাহ্মণীর সহায়তায় তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে সিদ্ধিলাভ হইয়াই গিয়াছে। তোতাপুরী ঠাকুরকে দেখিয়াই বেদান্তপথের অতি উত্তম অধিকারী বলিয়া চিনিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদান করিয়া নির্বিকল্প সমাধিসাধনের বিষয় উপদেশ করেন, তখন ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে ঐ বিষয় হইতে নিরস্ত করিবার অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, “বাবা, (ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে পুত্রজ্ঞানে ঐরূপে সম্বোধন করিতেন) ওর কাছে বেশি যাওয়া-আসা করো না, বেশি মেশামেশি করো না; ওদের সব শুষ্ক পথ। ওর সঙ্গে মিশলে তোমার ঈশ্বরীয় ভাব-প্রেম সব নষ্ট হয়ে যাবে।” ইহাতে বেশ অনুমিত হয় যে, বিদুষী ব্রাহ্মণী ভগবদ্ভক্তিতে অসামান্যা হইলেও এ কথা জানিতেন না বা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, বেদান্তোক্ত যে নির্বিকল্প অবস্থাকে তিনি শুষ্কমার্গ বলিয়া নির্দেশ ও ধারণা করিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ পরাভক্তিলাভের প্রথম সোপান – যে, শুদ্ধ-বুদ্ধ আত্মারাম পুরুষেরাই কেবলমাত্র ঈশ্বরকে সকল প্রকার হেতুশূন্য হইয়া ভক্তিপ্রেম করিতে পারেন, এবং ঠাকুর যেমন বলিতেন – ‘শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান – দুই-ই এক পদার্থ।’ আমাদের অনুমান, ব্রাহ্মণী এ কথা বুঝিতেন না এবং বুঝিতেন না বলিয়াই ঠাকুর মস্তক মুণ্ডিত করিয়া গৈরিক ধারণ ও পুরী স্বামীজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষাগ্রহণপূর্বক নির্বিকল্প সমাধি-সাধনের সময় নিজ গর্ভধারিণী মাতার নিকট যেমন উহা গোপন করিয়াছিলেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকটেও তেমনি ঐ বিষয় গোপন রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুরের বৃদ্ধা মাতা ঐ সময়ে দক্ষিণেশ্বরের উত্তর দিকের নহবতখানার উপরে থাকিতেন এবং ঠাকুর ঐরূপে বেদান্তসাধনকালে তিন দিন গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সকলের চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়াছিলেন। কেবল পুরী গোস্বামী মাত্র ঐ সময়ে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুর ব্রাহ্মণীর ঐ কথায় কর্ণপাতও করেন নাই।
তন্ত্রোক্ত পশু, বীর ও দিব্যভাব-নির্ণয়
ঠাকুরের মুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তন্ত্রোক্ত বীরভাবের উপাসিকা ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তন্ত্রে পশু, বীর ও দিব্য এই তিন ভাবে ঈশ্বরসাধনার পথ নির্দিষ্ট আছে। পশুভাবের সাধকে কাম-ক্রোধাদি পশুভাবের আধিক্য থাকে; সেজন্য তিনি সর্বপ্রকার প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকিবেন এবং বাহ্যিক শৌচাচার প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ভগবানের নামজপ, পুরশ্চরণাদিতে প্রবৃত্ত থাকিবেন। বীরভাবের সাধকে কাম-ক্রোধাদি পশুভাবের অপেক্ষা ঈশ্বরানুরাগ প্রবল থাকে। কাম-কাঞ্চন, রূপ-রসাদির আকর্ষণ তাঁহার ভিতর ঈশ্বরানুরাগকেই প্রবলতর করিয়া দেয়। সেজন্য তিনি কামকাঞ্চনাদির প্রলোভনের ভিতর বাস করিয়া উহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে অবিচলিত থাকিয়া ঈশ্বরে সমগ্র মন-প্রাণ অর্পণ করিতে চেষ্টা করিবেন। দিব্যভাবের সাধক কেবলমাত্র তিনিই হইতে পারেন, যাঁহাতে ঈশ্বরানুরাগের প্রবল প্রবাহে কাম-ক্রোধাদি একেবারে চিরকালের মতো ভাসিয়া গিয়াছে, এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় যাঁহাতে ক্ষমাৰ্জব-দয়া-তোষ-সত্যাদি সদ্গুণসমূহের অনুষ্ঠান স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে ঐ তিন ভাব সম্বন্ধে ইহাই বলা যায়। বেদান্তোক্ত উত্তম অধিকারীই তন্ত্রোক্ত দিব্যভাবের ভাবুক, মধ্যম অধিকারীই বীরভাবের এবং অধমাধিকারীই পশুভাবের সাধক।
বীর সাধিকা ‘বামনী’ দিব্যভাবের অধিকারিণী হইতে তখনও সমর্থা হন নাই
বীরভাবের সাধকাগ্রণী হইলেও ভৈরবী ব্রাহ্মণী তখনও দিব্যভাবের অধিকারিণী হইতে পারেন নাই। ঠাকুরের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সহায়তালাভ করিয়াই ব্রাহ্মণীর ক্রমে দিব্যভাবের বাসনা আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণী দেখিলেন – গ্রহণের কথা দূরে থাকুক, সিদ্ধি বা কারণের নাম মাত্রেই ঠাকুর জগৎকারণ-ঈশ্বরভাবে বিহ্ব্ল হইয়া পড়েন; সতী বা নটী কোন স্ত্রীমূর্তি দেখিবামাত্রই তাঁহার মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার হ্লাদিনী ও সন্ধিনী শক্তির কথার উদয় হইয়া তাঁহাতে সন্তানভাবই আনিয়া দেয়, এবং কাঞ্চনাদি-ধাতুসংস্পর্শে সুপ্তাবস্থায়ও তাঁহার হস্তাদি অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া যায়! এ জ্বলন্ত পাবকের নিকট থাকিয়া কাহার না ঈশ্বরানুরাগ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে? কে না এই দুই দিনের বিষয়-বিভবাদির প্রতি বীতরাগ হইয়া ঈশ্বরকেই আপনার হইতে আপনার, চিরকালের আত্মীয় বলিয়া ধারণা না করিয়া থাকিতে পারে? এজন্যই ব্রাহ্মণীর জীবনের অবশিষ্টকাল তীব্র তপস্যায় কাটাইবার কথা আমরা শুনিতে পাইয়া থাকি।
ঐ বিষয়ে প্রমাণ
ঠাকুর অপর কাহারও সহিত বেশি মেশামেশি করিলে বা অন্য কোন ঈশ্বরভক্ত সাধককে অধিক সম্মান প্রদর্শন করিলে ব্রাহ্মণীর মনে হিংসার উদয় হইত, এ কথাও আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ন্যাওটো ছেলে বড় হইয়া বাটীর অপর কাহাকেও ভালবাসিলে বা আদরযত্ন করিলে তাহার ঠাকুরমা বা অন্য কোন বৃদ্ধা আত্মীয়ার (যাহার নিকটে সে এতদিন পালিত হইয়া আসিয়াছে) মনে যেরূপ ঈর্ষা, দুঃখ ও কষ্ট উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণীরও ঠাকুরের প্রতি ঐ ভাব যে সেই প্রকারের, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি! কিন্তু ব্রাহ্মণীর ন্যায় অত উচ্চদরের সাধিকার মনে ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল না। যিনি ঠাকুরকে খাইতে, শুইতে, বসিতে, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা এতকাল ধরিয়া সকল অবস্থায় সকল ভাবে দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাঁহার ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল না। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঠাকুরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাদি অপরের ন্যায়, ‘এই আছে এই নাই’ গোছের ছিল না। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঠাকুর তাঁহার উপর যে ভক্তি-শ্রদ্ধা একবার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা চিরকালের মতোই অর্পিত হইয়াছিল – তাহাতে আর জোয়ার-ভাঁটা খেলিত না। কিন্তু হায়, মায়িক ভালবাসা ও স্ত্রীলোকের মন, তোমরা সর্বদাই ভালবাসার পাত্রকে চিরকালের মতো বাঁধিয়া নিজস্ব করিয়া রাখিতে চাও! এতটুকু স্বাধীনতা তাঁহাকে দিতে চাও না। মনে কর স্বাধীনতা পাইলেই তোমাদের ভালবাসার পাত্র আর তোমাদের থাকিবে না, অপর কাহাকেও তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া ফেলিবে। তোমরা বুঝ না যে, তোমাদের অন্তরের দুর্বলতাই তোমাদিগকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া দেয়। তোমরা বুঝ না যে, যে ভালবাসা ভালবাসার পাত্রকে স্বাধীনতা দেয় না – যাহা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া সে যাহা চাহে তাহাতেই আনন্দানুভব করিতে জানে না বা শিখে না, তাহা প্রায়ই স্বল্পকালে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব যদি যথার্থই কাহাকেও প্রাণের ভালবাসা দিয়া থাক, তবে নিশ্চিন্ত থাকিও, তোমার ভালবাসার পাত্র তোমারই থাকিবে এবং ঐ শুদ্ধ স্বার্থসম্পর্কশূন্য ভালবাসা শুধু তোমাকে নহে, তাহাকেও চরমে ঈশ্বরদর্শন ও সর্ববন্ধনবিমুক্তি পর্যন্ত আনিয়া দিবে।
ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণীর নিজ আধ্যাত্মিক অভাববোধ ও তপস্যা করিতে গমন
ব্রাহ্মণী উচ্চদরের প্রেমিক সাধিকা হইলেও যে পূর্বোক্ত কথাটি বুঝিতেন না, বা বুঝিয়াও ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই, ইহা নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিকই তাঁহার ঐ ধারণার অভাব ছিল; এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরুপদে ভাগ্যক্রমে বৃত হইয়া ‘তিনি সর্বাপেক্ষা বড়, তাঁহার কথা সকলে সর্বদা মানিয়া চলুক, না চলিলে তাহাদের কল্যাণ নাই’ – এই প্রকার ভাবসমূহও তাঁহার মনে ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে যে কখনো কখনো শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহাতেও তিনি ঈর্ষান্বিতা হইতেন। শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তাঁহার ঐ প্রকার ভাবপ্রকাশে সর্বদা ভীতা, সঙ্কুচিতা হইয়া থাকিতেন। যাহা হউক, পরিশেষে ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণী তাঁহার মনের এই দুর্বলতার কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন, এ অবস্থায় ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে থাকিলেই তবে তিনি তাঁহার এই মনোভাব-জয়ে সমর্থা হইবেন; এবং বুঝিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের প্রতি তাঁহার এই প্রকার আকর্ষণ সোনার শিকলে বন্ধনের ন্যায় হইলেও, উহা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা বেশ বুঝিতে পারি, এজন্যই ব্রাহ্মণী পরিশেষে দক্ষিণেশ্বর ও ঠাকুরের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং ‘রম্তা সাধু ও বহ্তা জল কখনো মলিন হয় না’1 ভাবিয়া অসঙ্গ হইয়া তীর্থে তীর্থে পর্যটন ও তপস্যায় কালহরণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের গুরুভাবসহায়েই যে ব্রাহ্মণীর এই প্রকার চৈতন্যের উদয় হয়, ইহা আর বলিতে হইবে না।
1. সংসার-বিরাগী সাধুদিগের ভিতর প্রচলিত একটি উক্তি। ‘রম্তা’ – অর্থাৎ নিরন্তর যিনি একস্থানে না থাকিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, এই প্রকার সাধুতে এবং যে জলে প্রবাহ বা নিরন্তর স্রোত বহিতেছে, এইরূপ জলে কখনো মলিনতা দাঁড়াইতে পারে না। নিত্যপর্যটনশীল সাধুর মন কখনো কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে আসক্ত হয় না, ইহাই অর্থ।
তোতাপুরী গোস্বামীর কথা
তোতাপুরী লম্বা-চওড়া সুদীর্ঘ পুরুষ ছিলেন। চল্লিশ বৎসর ধ্যান-ধারণা এবং অসঙ্গভাবে বাস করিবার ফলে তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে মন স্থির, বৃত্তিমাত্রহীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তত্রাপি তিনি নিত্য ধ্যানানুষ্ঠান এবং সমাধিতে অনেককাল কাটাইতেন। সর্বদা বালকের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ‘ল্যাংটা’ নামে নির্দেশ করিতেন। বিশেষতঃ আবার গুরুর নাম সর্বদা গ্রহণ করিতে নাই, বা নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে নাই বলিয়াই বোধ হয় ঐরূপ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন, ল্যাংটা কখনো ঘরের ভিতর থাকিতেন না এবং নাগাসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া সর্বদা অগ্নিসেবা করিতেন! নাগা সাধুরা অগ্নিকে মহা পবিত্রভাবে দর্শন করে; এবং সেজন্য যেখানেই যখন থাকুক না কেন, কাষ্ঠাহরণ করিয়া নিকটে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখে। ঐ অগ্নি সচরাচর ‘ধুনি’ নামে অভিহিত হয়। নাগা সাধু ধুনিকে সকাল সন্ধ্যা আরতি করিয়া থাকে এবং ভিক্ষালব্ধ আহার্যসমুদয় প্রথমে ধুনিরূপী অগ্নিকে নিবেদন করিয়া তবে স্বয়ং গ্রহণ করে। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ‘ল্যাংটা’ সেজন্য পঞ্চবটীর বৃক্ষতলেই আসন করিয়া অবস্থান করিতেন এবং পার্শ্বে ধুনি জ্বালাইয়া রাখিতেন। রৌদ্র হউক, বর্ষা হউক ‘ল্যাংটা’র ধুনি সমভাবেই জ্বলিত। আহার বল, শয়ন বল ‘ল্যাংটা’ ঐ ধুনির ধারেই করিতেন। আর যখন গভীর নিশীথে সমগ্র বাহ্যজগৎ বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে সকল চিন্তা ভুলিয়া মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় সুখশয়ন লাভ করিত, ‘ল্যাংটা’ তখন উঠিয়া ধুনি অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া অচল অটল সুমেরুবৎ আসনে বসিয়া নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির মনকে সমাধিমগ্ন করিতেন। দিনের বেলায়ও ‘ল্যাংটা’ অনেক সময় ধ্যান করিতেন। কিন্তু লোকে না জানিতে পারে এমন ভাবে করিতেন। সেজন্য পরিধেয় চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ধুনির ধারে শবের ন্যায় লম্বা হইয়া ‘ল্যাংটা’কে শয়ন করিয়া থাকিতে অনেক সময় দেখা যাইত। লোকে মনে করিত, ‘ল্যাংটা’ নিদ্রা যাইতেছেন।
ঠাকুর ও পুরী গোস্বামীর পরস্পর ভাব-আদান-প্রদানের কথা
‘ল্যাংটা’ নিকটে একটি জলপাত্র বা ‘লোটা’, একটি সুদীর্ঘ চিমটা এবং আসন করিয়া বসিবার জন্য একখণ্ড চর্মমাত্র রাখিতেন এবং একখানি মোটা চাদরে সর্বদা স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া থাকিতেন। লোটা ও চিমটাটি ‘ল্যাংটা’ নিত্য মাজিয়া ঝকঝকে রাখিতেন। ‘ল্যাংটা’র ঐরূপ নিত্য ধ্যানানুষ্ঠান দেখিয়া ঠাকুর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিলেন, ‘তোমার তো ব্রহ্মলাভ হয়েছে, সিদ্ধ হয়েছ, তবে কেন আবার নিত্য ধ্যানাভ্যাস কর?’ ‘ল্যাংটা’ ইহাতে ধীরভাবে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া লোটাটি দেখাইয়া বলিলেন, ‘কেমন উজ্জ্বল দেখছ? আর যদি নিত্য না মাজি? – মলিন হয়ে যাবে না? মনও সেইরূপ জানবে। ধ্যানাভ্যাস করে মনকেও ঐরূপে নিত্য না মেজে-ঘষে রাখলে মলিন হয়ে পড়ে।’ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর ‘ল্যাংটা’ গুরুর কথা মানিয়া লইয়া বলিলেন, “কিন্তু যদি সোনার লোটা হয়? তাহলে তো আর নিত্য না মাজলেও ময়লা ধরে না।” ‘ল্যাংটা’ হাসিয়া স্বীকার করিলেন, ‘হাঁ, তা বটে।’ নিত্য ধ্যানাভ্যাসের উপকারিতা সম্বন্ধে ‘ল্যাংটা’র কথাগুলি ঠাকুরের চিরকাল মনে ছিল এবং বহুবার তিনি উহা ‘ল্যাংটা’র নাম করিয়া আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। আর আমাদের ধারণা – ঠাকুরের ‘সোনার লোটায় ময়লা ধরে না’, কথাটি ‘ল্যাংটা’র মনেও চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। ‘ল্যাংটা’ বুঝিয়াছিল, ঠাকুরের মন বাস্তবিকই সোনার লোটার মতো উজ্জ্বল! গুরু-শিষ্যে এইরূপ আদান-প্রদান ইঁহাদের ভিতরে প্রথমাবধিই চলিত।
ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নির্ভীকতা ও বন্ধনবিমুক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র
বেদান্তশাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মানুষ একেবারে ভয়শূন্য হয়। সম্পূর্ণ অভীঃ হইবার উহাই একমাত্র পথ। বাস্তবিক কথা। যিনি জানিতে পারেন যে, তিনি স্বয়ং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব, অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বব্যাপী অজরামর আত্মা, তাঁহার মনে ভয় কিসে, কাহারই বা দ্বারা হইবে? যিনি, এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তি জগতে নাই, ইহা সত্য সত্যই দেখিতে পান, সর্বদা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তাঁহার ভয় কি করিয়া, কোথায়ই বা হইবে? খাইতে, শুইতে, বসিতে, নিদ্রায়, জাগরণে, সর্বাবস্থায়, সকল সময়ে তিনি দেখেন – তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ; সকলের ভিতর, সর্বত্র, সর্বদা তিনি পূর্ণ হইয়া আছেন; তাঁহার আহার নাই, বিহার নাই, নিদ্রা নাই, জাগরণ নাই, অভাব নাই, আলস্য নাই, শোক নাই, হর্ষ নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই – মানব পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধি-সহায়ে যাহা কিছু দেখে, শুনে, চিন্তা বা কল্পনা করে, তাহার কিছুই নাই। এই প্রকার অনুভবকেই শাস্ত্র, ‘নেতি নেতি’র বিরামাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহারই পরে পূর্ণস্বরূপ আত্মার অবস্থান ও প্রত্যক্ষদর্শন বলিয়াছেন। এই আত্মদর্শন সদা-সর্বক্ষণ হওয়ার নামই ‘জ্ঞানে অবস্থান’, এবং এই প্রকার জ্ঞানে অবস্থান হইলেই সর্ববন্ধনবিমুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠাকুর বলিতেন, এই প্রকার জ্ঞানে অবস্থান সম্পূর্ণরূপে হইলে জীবের শরীর একুশ দিন মাত্র থাকিয়া শুষ্ক পত্রের ন্যায় পড়িয়া যায় বা নষ্ট হইয়া যায় এবং আর সে এ সংসারের ভিতর অহং-জ্ঞান লইয়া ফিরিয়া আসে না। জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালের নিমিত্ত এই জ্ঞানে অবস্থান ও আত্মার দর্শন হইতে হইতে পরিশেষে পূর্ণ অবস্থান ও দর্শন আসিয়া উপস্থিত হয়। আর নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটি পুরুষ, যাঁহারা কোন বিশেষ সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুজনের কল্যাণসাধন করিতেই জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাও বাল্যাবধি মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালের জন্য এই জ্ঞানে অবস্থান করেন এবং যে কর্মের জন্য আসিয়াছেন, সেই কর্ম শেষ হইলে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করেন। আবার, যাঁহাদের অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিয়া জগৎ এ পর্যন্ত ধারণা করিতে পারে নাই, তাঁহারা ঈশ্বর স্বয়ং মানব-কল্যাণের নিমিত্ত মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, অথবা অত্যদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন মানব; সেই অবতারপুরুষেরা এই পূর্ণ জ্ঞানাবস্থায় বাল্যাবধি ইচ্ছামাত্র উঠিতে, যতকাল ইচ্ছা থাকিতে এবং পুনরায় ইচ্ছামত লোক-কল্যাণের নিমিত্ত জন্ম-জরা-শোক-হর্ষাদির মিলনভূমি সংসারে আসিতে পারেন।
তোতাপুরীর উচ্চ অবস্থা
ঠাকুরের শিক্ষাগুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী চল্লিশ বৎসর কঠোর সাধনের ফলে পূর্বোক্ত জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার আহার বিহার শয়ন উপবেশন প্রভৃতি সকল কার্যই মানবসাধারণের ন্যায় ছিল না। নিত্যমুক্ত বায়ুর ন্যায় তিনি বাধাশূন্য হইয়া যত্র তত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন; বায়ুর ন্যায়ই তাঁহাকে সংসারের দোষ-গুণ কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না এবং বায়ুর ন্যায়ই তিনি কখনো একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কারণ ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, তোতা তিন দিনের অধিক কোথাও অবস্থান করিতে পারিতেন না। ঠাকুরের অদ্ভুতাকর্ষণে কিন্তু তোতা দক্ষিণেশ্বরে একাদিক্রমে এগার মাস কাল অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের কি অদ্ভুত মোহিনীশক্তিই ছিল!
তোতার নির্ভীকতা – ভৈরব-দর্শনে
তোতার নির্ভীকতা সম্বন্ধে ঠাকুর অনেক কথা আমাদের বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ভুতুড়ে ঘটনাও বলেন, তাহা এই – গভীর নিশীথে তোতা একদিন ধুনি উজ্জ্বল করিয়া ধ্যানে বসিবার উপক্রম করিতেছেন; জগৎ নীরব; নিস্তব্ধ; ঝিল্লী ও মধ্যে মধ্যে মন্দির-চূড়ায় অবস্থিত পেচকের গম্ভীর নিঃস্বন ভিন্ন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। বায়ুরও সঞ্চার নাই। সহসা পঞ্চবটীর বৃক্ষশাখাসকল আলোড়িত হইতে লাগিল এবং দীর্ঘাকার মানবাকৃতি এক পুরুষ বৃক্ষের উপর হইতে নিম্নে নামিয়া তোতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ধীর পদবিক্ষেপে পুরী গোস্বামীর ধুনির পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। ‘ল্যাংটা’ নিজেরই ন্যায় উলঙ্গ সেই পুরুষপ্রবরকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কে তুমি?’ পুরুষ উত্তর করিলেন, ‘আমি দেবযোনি, ভৈরব; এই দেবস্থানরক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষোপরি অবস্থান করি।’ ‘ল্যাংটা’ কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, ‘উত্তম কথা, তুমিও যা, আমিও তাই; তুমিও ব্রহ্মের এক প্রকাশ, আমিও তাই; এস, বস, ধ্যান কর।’ পুরুষ হাসিয়া বায়ুতে যেন মিলাইয়া গেলেন! ‘ল্যাংটা’ও ঐ ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। পরদিন প্রাতে ‘ল্যাংটা’ ঠাকুরকে ঐ ঘটনা বলেন। ঠাকুরও শুনিয়া বলিলেন, “হাঁ, উনি ঐখানে থাকেন বটে; আমিও উঁহার দর্শন অনেকবার পেয়েছি। কখনো কখনো কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয়ও উনি আমাকে বলে দিয়েছেন। কোম্পানি, বারুদখানার (Powder Magazine) জন্য পঞ্চবটীর সমস্ত জমিটি একবার নেবার চেষ্টা করে। আমার তাই শুনে বিষম ভাবনা হয়েছিল; সংসারের কোলাহল থেকে দূরে নির্জন স্থানটিতে বসে মাকে ডাকি, তা আর হবে না – সেইজন্য! মথুর তো রানী রাসমণির তরফ থেকে কোম্পানির সঙ্গে খুব মামলা লাগিয়ে দিলে, যাতে কোম্পানি জমিটি না নেয়! সেই সময়ে একদিন ঐ ভৈরব গাছে বসে আছেন দেখতে পাই; আমাকে সঙ্কেতে বলেছিলেন, ‘কোম্পানি জায়গা নিতে পারবে না; মামলায় হেরে যাবে।’ বাস্তবিকও তাই হলো!”
তোতাপুরীর গুরুর কথা
‘ল্যাংটা’র জন্মস্থান পশ্চিমে কোন্ স্থানে ছিল, ঠাকুরের নিকট সে সম্বন্ধে আমরা কিছু শুনি নাই। ঠাকুরও হয়তো ঐ বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কোন আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। বিশেষতঃ, আবার পূর্ব নাম-ধাম-গোত্রাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসীরা উহার উল্লেখ করেন না; বলেন, ‘সন্ন্যাসীকে ঐ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং সন্ন্যাসীর তদ্বিষয়ে উত্তর দেওয়া – উভয়ই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ!’ ঠাকুর হয়তো সেইজন্যই ঐ প্রশ্ন ‘ল্যাংটা’কে কখনো করেন নাই। তবে বেলুড় মঠস্থ ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ঠাকুরের দেহান্তের পর ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণকালে প্রাচীন সন্ন্যাসী পরমহংসগণের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ পুরী গোস্বামী পঞ্জাব প্রদেশের নিকটবর্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন। তাঁহার গুরুস্থান বা গুরুর আবাস কুরুক্ষেত্রের নিকট লুধিয়ানা নামক স্থানে ছিল। তাঁহার গুরুও একজন বিখ্যাত যোগীপুরুষ ছিলেন এবং ঐ স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত মঠটি তিনি নিজে স্থাপন করেন বা তাঁহার গুরুর গুরু কেহ স্থাপন করেন, সে বিষয়ে ঠিক জানা যায় নাই। তবে শ্রীমৎ তোতাপুরীর গুরু যে ঐ মঠের মোহন্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্মানে এখনো যে ঐ স্থানে বৎসর বৎসর চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদের একটি মেলা হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে প্রাচীন সাধুগণ তাঁহাদের বলিয়াছিলেন। তিনি তামাক খাইতেন বলিয়া গ্রামবাসীরা মেলার সময় তামাক আনিয়া তাঁহার ‘সমাজে’ এখনো উপহার দিয়া থাকে। গুরুর দেহান্তে শ্রীমৎ তোতাপুরীই ঐ মঠের মোহন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হন।
নিজ গুরুর মঠ ও মণ্ডলীসম্বন্ধে তোতাপুরীর কথা
শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিজের কথাতেও মনে হয়, তিনি সন্ন্যাসিমণ্ডলীর অধীশ্বর নিজ গুরুর নিকট বাল্যেই বেদান্ত-শাস্ত্রোপদেশ পাইয়াছিলেন এবং বহুকাল তাঁহার অধীনে বাস করিয়া স্বাধ্যায়রত থাকেন ও সাধনরহস্য অবগত হন! কারণ, ঠাকুরকে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার মণ্ডলীতে সাত শত সন্ন্যাসী বাস করিয়া গুরুর আদেশমত বেদান্তনিহিত সত্যসকল জীবনে অনুভবের জন্য ধ্যানাদি নিত্যানুষ্ঠান করিত। উক্ত মণ্ডলীতে ধ্যান-শিক্ষাদিদানও যে বড় সুন্দর প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইত, এ বিষয়েও ‘ল্যাংটা’ ঠাকুরকে কিছু কিছু আভাস দিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ কথা অনেক সময়ে আমাদের নিকট গল্প বা উপদেশচ্ছলে বলিতেন। বলিতেন, “ল্যাংটা বলত, তাদের দলে সাত শত ল্যাংটা ছিল। যারা প্রথম ধ্যান শিখতে আরম্ভ করচে, তাদের গদির উপর বসিয়ে ধ্যান করাত। কেন না, কঠিন আসনে বসে ধ্যান করলে পা টনটন করবে; আর ঐ টনটনানিতে অনভ্যস্ত মন ঈশ্বরে না গিয়ে শরীরের দিকে এসে পড়বে। তারপর তার যত ধ্যান জমত ততই তাকে কঠিন হতে কঠিনতর আসনে বসে ধ্যান করতে দেওয়া হতো। শেষকালে শুধু চর্মাসন ও খালি মাটিতে পর্যন্ত বসে তাকে ধ্যান করতে হতো। আহারাদি সকল বিষয়েও ঐরূপ নিয়মে অভ্যাস করাত। পরিধানেও শিষ্যদের সকলকে ক্রমে ক্রমে উলঙ্গ হয়ে থাকতে অভ্যাস করানো হতো। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাত, কুল, শীল, মান ইত্যাদি অষ্টপাশে মানুষ জন্মাবধি বদ্ধ আছে কিনা? এক এক করে সেগুলোকে সব ত্যাগ করতে শিক্ষা দেওয়া হতো। তারপর ধ্যানাদিতে মন পাকা হয়ে বসলে তাকে প্রথম অপর সাধুদের সঙ্গে, তারপর একা একা, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে আসতে হতো। ল্যাংটাদের এই রকম সব নিয়ম ছিল।” ঐ মণ্ডলীর মোহন্ত-নির্বাচনের প্রথাও ঠাকুর পুরীজীর নিকট শুনিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ঐ সম্বন্ধে আমাদের একদিন এইরূপ বলেন, “ল্যাংটাদের ভেতর যার ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা হয়েছে দেখত, গদি খালি হলে তাকেই সকলে মিলে মোহন্ত করে ঐ গদিতে বসাত। তা না হলে টাকা, মান, ক্ষমতা হাতে পড়ে ঠিক থাকতে পারবে কি করে? মাথা বিগড়ে যাবে যে? সেজন্য যার মন থেকে কাঞ্চন ঠিক ঠিক ত্যাগ হয়েছে দেখত, তাকেই গদিতে বসিয়ে টাকা-কড়ির ভার দিত। কেন না, সে-ই ঐ টাকা দেবতা ও সাধুদের সেবায় ঠিক ঠিক খরচ করতে পারবে।”
তোতাপুরীর পূর্ব পরিচয়
পুরী গোস্বামীর ঐসকল কথায় বেশ বুঝা যায়, তিনি বাল্যাবধি সংসারের মায়া-মোহ-ঈর্ষা-দ্বেষাদি হইতে দূরে যেন এক স্বর্গীয় রাজ্যে গুরুর স্নেহে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রথা আছে যে, যে দম্পতির যথাসময়ে সন্তান জন্মে না, তাঁহারা দেবস্থানে কামনা করেন যে, তাঁহাদের প্রণয়ের প্রথম ফলস্বরূপ সন্তানকে সন্ন্যাসী করিয়া ঈশ্বরের সেবায় অর্পণ করিবেন এবং কার্যেও ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুরী গোস্বামী কি সেইরূপে গুরুর নিকট অর্পিত হইয়াছিলেন? কে বলিবে! তবে তাঁহার পূর্বাশ্রমের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতির কোন কথা ঠাকুরের নিকট কখনো উল্লেখ না করাতে ঐরূপই অনুমিত হয়।
তোতাপুরীর মন
পূর্বকৃত পুণ্যসংস্কারের ফলে গোস্বামীজীর মনটিও তেমনি সরলবিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল। আচার্য শঙ্কর তৎকৃত ‘বিবেকচূড়ামণি’ গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, ‘জগতে মনুষ্যত্ব, ঈশ্বরলাভেচ্ছা এবং সদ্গুরুর আশ্রয় – এই তিন বস্তু একত্রে লাভ করা বড়ই দুর্লভ; ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত হয় না।’ পুরী গোস্বামী শুধু যে ঐ তিন পদার্থ ভাগ্যক্রমে একসঙ্গে পাইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু ঐসকলের যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ পাইয়া মানবজীবনের চরমোদ্দেশ্য মুক্তিলাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে যেমন যেমন উপদেশ করিতেন, তাঁহার মনও ঠিক ঠিক উহা ধারণা করিয়া সর্বদা কার্যে পরিণত করিত। মনের জুয়াচুরি ভণ্ডামিতে তাঁহাকে কখনো বেশি ভুগিতে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৈষ্ণবদিগের ভিতর একটি কথা আছে –
“গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল।
একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল।”
– ‘একের’ অর্থাৎ নিজ মনের দয়া না হওয়াতে জীব বিনষ্ট হইল। পুরী গোস্বামীকে এরূপ পাজি মনের হাতে পড়িয়া কখনো ভুগিতে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সরল মন, সরলভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গুরুনির্দিষ্ট গন্তব্য পথে ধীরপদে অগ্রসর হইয়াছিল, যাইতে যাইতে একবারও পশ্চাতে সংসারের পাপ-প্রলোভনাদির দিকে অতৃপ্ত লালসার কটাক্ষপাত করে নাই। কাজেই গোসাঁইজী নিজ পুরুষকার, উদ্যম, আত্মনির্ভরতা ও প্রত্যয়কেই সর্বেসর্বা বলিয়া জানিয়াছিলেন। মন বাঁকিয়া দাঁড়াইলে ঐ পুরুষকার যে প্রবল প্রবাহের মুখে তৃণগুচ্ছের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়, ঐ আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ের স্থলে যে আপনার ক্ষমতার উপর ঘোর অবিশ্বাস আসিয়া জীবকে সামান্য কীটাপেক্ষা দুর্বল করিয়া তুলে – এ কথা গোসাঁইজী জানিতেন না। ঈশ্বরকৃপায় বহির্জগতের সহস্র বিষয়ের অনুকূলতা না পাইলে জীবের শত-সহস্র উদ্যম যে আশানুরূপ ফল প্রসব না করিয়া বিপরীত ফলই প্রসব করিতে থাকে এবং তাহাকে বন্ধনের উপর আরও ঘোরতর বন্ধন আনিয়া দেয়, পুরী গোস্বামী নিজ জীবনের দিকে চাহিয়া এ কথা কখনো স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কেনই বা ভাবিবেন? তিনি যখনই যাহা ধরিয়াছেন – আজন্ম, তখনই তাহা করিতে পারিয়াছেন, যখনই যাহা মানবের কল্যাণকর বলিয়া বুঝিয়াছেন – তখনই তাহা নিজ জীবনে কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। কাজেই ‘মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না’ এমন একটা অবস্থা যে মানবের হইতে পারে, ‘মন মুখ এক’ করিতে না পারিয়া সে যে শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা ভিতরে নিরন্তর অনুভব করিতে পারে, মনের ভিতর সহস্রটা কর্তা এবং শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়টা স্ব স্ব প্রধান হইয়া কেহ কাহারও কথা না মানিয়া চলিয়া তাহাকে যে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া হতাশার অন্ধতামিস্রে ফেলিয়া ঘোর যন্ত্রণা দিতে পারে – এ কথা গোসাঁইজী কখনো কল্পনায়ও আনিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। অথবা আনিতে পারিলেও শুনে শিখা, দেখে শিখা ও ঠেকে শিখার ভিতর অনেক তফাত। কাজেই পুরী গোস্বামীর মনে অবস্থিত মানবের ঐরূপ অবস্থার ছবিতে এবং যে ঐ প্রকারে বাস্তবিক নিরন্তর ভুগিতেছে, তাহার মনের ছবিতে ঐরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। পুরী গোস্বামী সেজন্য পরমেশ-শক্তি অনাদ্যবিদ্যা মায়ার দুরন্ত প্রভাববিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞই ছিলেন; এবং সেজন্য দুর্বল মানবমনের কার্যকলাপের প্রতি তিনি কঠোর দ্বেষ-দৃষ্টি ভিন্ন কখনো করুণার সহিত দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ঠাকুরের গুরুভাবের সম্পর্কে আসিয়াই তাঁহার এই অভাব অপনীত হয় এবং তিনি পরিশেষে মায়ার শক্তি মানিয়া ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ জানিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটী হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা এক্ষণে ঐ বিষয়েই বলিতে আরম্ভ করিব।
তোতাপুরীর ভক্তিমার্গে অনভিজ্ঞতা
ব্রাহ্মণী ভৈরবী ঠাকুরকে যেমন বলিয়াছিলেন, আকুমার ব্রহ্মচারী কঠোর যতি তোতার বাস্তবিকই ভগবদ্ভক্তিমার্গকে একটা কিম্ভূতকিমাকার পথ বলিয়া ধারণা ছিল। ভক্তি-ভালবাসা যে মানবকে ভালবাসার পাত্রের জন্য সংসারের সকল বিষয়, এমনকি আত্মতৃপ্তি পর্যন্ত ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে শিখাইয়া চরমে ঈশ্বর-দর্শন আনিয়া দেয়, যথার্থ ভক্তসাধক যে ভক্তির চরম পরিণতিতে শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানেরও অধিকারী হইয়া থাকেন এবং সেজন্য তাঁহারও সাধনসহায় জপ-কীর্তন-ভজনাদি যে উপেক্ষার বিষয় নহে – এ কথা তোতা বুঝিতেন না। না বুঝিয়া গোসাঁইজী ভক্তের ভাববিহ্ব্ল চেষ্টাদিকে সময়ে সময়ে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেন না। অবশ্য এ কথায় পাঠক না বুঝিয়া বসেন যে, পুরী গোস্বামী এক প্রকার নাস্তিক গোছের ছিলেন বা তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ ছিল না। শমদমাদিসম্পত্তিসহায় শান্তপ্রকৃতি গোসাঁইজী স্বয়ং ভক্তির শান্তভাবের পথিক ছিলেন এবং অপরের ঐ ভাবের ঈশ্বরভক্তিই বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু কল্পনাসহায়ে জগৎকর্তা মহান ঈশ্বরকে নিজ সখা, পুত্র, স্ত্রী বা স্বামিভাবে ভজনা করিয়াও সাধক যে তাঁহার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে পারে, এ কথা পুরীজীর মাথায় কখনো ঢোকে নাই। ঐরূপ ভক্তের নিজ ভাবপ্রণোদিত ঈশ্বরের প্রতি আবদার-অনুরোধ, তাঁহাকে লইয়া বিরহ, ব্যাকুলতা, অভিমান, অহঙ্কার এবং ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম হাস্য-ক্রন্দন-নৃত্যাদি চেষ্টাকে তিনি পাগলের খেয়াল বা প্রলাপের মধ্যেই গণ্য করিতেন; এবং উহাতে যে ঐরূপ অধিকারী সাধকের আশু অভীষ্ট ফললাভ হইতে পারে, এ কথা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না। কাজেই ব্রহ্মশক্তি জগদম্বিকাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করা এবং ভক্তিপথের ঐরূপ চেষ্টাদির কথা লইয়া পুরীজীর সহিত ঠাকুরের অনেক সময় ঠোকাঠুকি লাগিয়া যাইত।
ঐ বিষয়ে প্রমাণ – ‘কেঁও রোটী ঠোকতে হো’
ঠাকুর বাল্যাবধি সকাল-সন্ধ্যায় করতালি দিতে দিতে এবং সময়ে সময়ে ভাবে নৃত্য করিতে করিতে ‘হরিবোল হরিবোল’, ‘হরি গুরু, গুরু হরি’, ‘হরি প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবন’, ‘মন কৃষ্ণ – প্রাণ কৃষ্ণ – জ্ঞান কৃষ্ণ – ধ্যান কৃষ্ণ – বোধ কৃষ্ণ – বুদ্ধি কৃষ্ণ’, ‘জগৎ তুমি – জগৎ তোমাতে’, ‘আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী’ ইত্যাদি উচ্চৈঃস্বরে বার বার কিছুকাল বলিতেন। বেদান্তজ্ঞানে অদ্বৈতভাবে নির্বিকল্প সমাধিলাভের পরও নিত্য ঐরূপ করিতেন। একদিন পঞ্চবটীতে পুরীজীর নিকট অপরাহ্ণে বসিয়া নানা ধর্মকথা-প্রসঙ্গে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া ঠাকুর বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া, করতালি দিয়া ঐরূপে ভগবানের স্মরণ-মনন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া পুরীজী অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন – যিনি বেদান্তপথের এত উত্তম অধিকারী যে, তিন দিনেই নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেন, তাঁহার আবার হীনাধিকারীর মতো এ সব অনুষ্ঠান কেন? প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াও ফেলিলেন, ‘আরে, কেঁও রোটী ঠোকতে হো?’ – অর্থাৎ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্ত্রীপুরুষে অনেক সময়ে চাকি-বেলুন প্রভৃতির সাহায্য না লইয়া ময়দার নেচি হাতে লইয়া পটাপট আওয়াজ করিতে করিতে চাপড়ে চাপড়ে যেমন রুটি তৈয়ার করে, সেই রকম কেন করচ? ঠাকুর শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করচি, আর তুমি কিনা বলছ – আমি রুটি ঠুকচি!” পুরীজীও ঠাকুরের বালকের ন্যায় কথায় হাসিতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন, ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠান অর্থশূন্য নহে; উহার ভিতর এমন কোন গূঢ়ভাব আছে, যাহা তাঁহার রুচিকর নয় বলিয়া তিনি ধরিতে-বুঝিতে পারিতেছেন না। উঁহার ঐরূপ কার্যে প্রতিবাদ না করাই ভাল।
তোতাপুরীর ক্রোধত্যাগের কথা
আর একদিন সন্ধ্যার পর ঠাকুর পুরীজীর ধুনির ধারে বসিয়া আছেন। ঈশ্বরপ্রসঙ্গে ঠাকুর এবং গোসাঁইজী উভয়েরই মন খুব উচ্চে উঠিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে প্রায় তন্ময়ত্ব অনুভব করিতেছে। পার্শ্বে ধক ধক করিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া ধুনির অগ্নিমধ্যস্থ আত্মাও যেন তাঁহাদের আত্মার সহিত একত্বানুভব করিয়া আনন্দে শত জিহ্বা প্রকাশ করিয়া হাসিতেছেন! এমন সময় বাগানের চাকরবাকরদিগের একজনের তামাক খাইবার বিশেষ ইচ্ছা হওয়ায়, কল্কেতে তামাক সাজিয়া অগ্নির জন্য সেখানে উপস্থিত হইল এবং ধুনির কাঠ টানিয়া অগ্নি লইতে লাগিল। গোসাঁইজী ঠাকুরের সহিত বাক্যালাপে ও অন্তরে অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দানুভবেই মগ্ন ছিলেন, ঐ লোকটির আগমন ও ধুনি হইতে অগ্নি লওয়ার বিষয় এতক্ষণ জানিতেই পারেন নাই। হঠাৎ এখন সেদিকে লক্ষ্য পড়ায় বিষম বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন! এমন কি চিমটা তুলিয়া তাহাকে দুই এক ঘা দিবার মতোও ভয় দেখাইতে লাগিলেন! কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, নাগা-সাধুরা ধুনিরূপী অগ্নিকে পূজা ও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন!
ঠাকুর পুরীজীর ঐরূপ ব্যবহারে অর্ধবাহ্যদশায় হাস্যের রোল তুলিয়া তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন, “দূর শালা, দূর শালা!” ঐ কথা বারবার বলেন ও হাসিয়া গড়াগড়ি দেন! তোতা ঠাকুরের ঐরূপ ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “তুমি অমন করচ যে? লোকটির কি অন্যায় দেখ দেখি?” ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তা তো বটে, সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও দেখচি! এই মুখে বলছিলে – ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তাই নেই, জগতে সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁরই প্রকাশ, আর পরক্ষণেই সব কথা ভুলে মানুষকে মারতেই উঠেচ! তাই হাসছি যে, মায়ার কি প্রভাব!” তোতা ঐ কথা শুনিয়াই গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ঠিক বলেছ, ক্রোধে সকল কথা বাস্তবিক ভুলিয়া গিয়াছিলাম! ক্রোধ বড় পাজি জিনিস! আজ থেকে আর ক্রোধ করব না, ক্রোধ পরিত্যাগ করলুম।” বাস্তবিকই স্বামীজীকে সেদিন হইতে আর ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই!
মায়া কৃপা করিয়া পথ না ছাড়িলে মানবের ঈশ্বরলাভ হয় না
ঠাকুর বলিতেন, “পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে – চোখ বুজে তুমি ‘কাঁটা নেই, খোঁচা নেই’, যতই কেন মনকে বুঝাও না, কাঁটায় হাত পড়লেই প্যাঁট করে বিঁধে গিয়ে উঁহু উঁহু করে উঠতে হয়; তেমনি, যতই কেন মনকে বুঝাও না – তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, পাপ নেই, শোক নেই, দুঃখ নেই, ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই – তুমি জন্ম-জরারহিত নির্বিকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা – কিন্তু যাই শরীরে অসুস্থতা এল, যাই মন সংসারের রূপ-রসাদি প্রলোভনের সামনে পড়ল, যাই কাম-কাঞ্চনের আপাতসুখে ভুলে কোন একটা কুকাজ করে ফেললে, অমনি মোহ, যন্ত্রণা, দুঃখ সব উপস্থিত হয়ে সব বিচার-আচার ভুলিয়ে একেবারে তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে! সেজন্য ঈশ্বরের কৃপা না হলে, মায়া দোর ছেড়ে না দিলে কারুর আত্মজ্ঞানলাভ ও দুঃখের নিবৃত্তি হয় না – জানবি। চণ্ডীতে আছে শুনিসনি? – ‘সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে’ – অর্থাৎ মা কৃপা করে পথ ছেড়ে না দিলে কিছুই হবার জো নেই।”
ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত – রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বনে পর্যটনের কথা
“রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাচ্চেন। বনের সরু পথ, একজনের বেশি যাওয়া যায় না। রাম ধনুকহাতে আগে আগে চলেছেন; সীতা তাঁর পাছু পাছু চলেছেন; আর লক্ষ্মণ সীতার পাছু পাছু ধনুর্বাণ নিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মণের রামের উপর এমনি ভক্তি-ভালবাসা যে, সর্বদা মনে মনে ইচ্ছা নবঘনশ্যাম রামরূপ দেখেন; কিন্তু সীতা মাঝখানে রয়েছেন, কাজেই চলতে চলতে রামচন্দ্রকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বুদ্ধিমতী সীতা তা বুঝতে পেরে, তাঁর দুঃখে কাতর হয়ে চলতে চলতে একবার পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘এই দ্যাখ্।’ তবে লক্ষ্মণ প্রাণভরে একবার তাঁর ইষ্টমূর্তি রামরূপ দেখতে পেলেন! সেইরকম জীব আর ঈশ্বরের মাঝখানে এই মায়ারূপিণী সীতা রয়েছেন। তিনি জীবরূপী লক্ষ্মণের দুঃখে ব্যথিত হয়ে পথ ছেড়ে পাশ কাটিয়ে না দাঁড়ালে জীব তাঁকে দেখতে পায় না, জানবি। তিনি যাই কৃপা করেন, অমনি জীবের রামরূপী নারায়ণের দর্শন হয় ও সে সব যন্ত্রণার হাত থেকে এড়ায়। নৈলে, হাজারই বিচার-আচার কর না কেন, কিছুতে কিছু হয় না। কথায় বলে – এক একটি জোয়ানের দানায় এক একশটি ভাত হজম করিয়ে দেয়, কিন্তু যখন পেটের অসুখ হয়, তখন একশটি জোয়ানের দানাও একটি ভাত হজম করাতে পারে না – সেইরকম জানবি।”
জগদম্বার কৃপায় তাঁহার উচ্চাবস্থা – তোতা একথা বুঝেন নাই
তোতাপুরী স্বামীজী ৺জগদম্বার আজন্ম কৃপাপাত্র। সৎসংস্কার, সরল মন, যোগী মহাপুরুষের সঙ্গ, বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর বাল্যাবধিই লাভ করিয়াছিলেন। ভাগবতী মায়া তো তাঁহাকে কখনো তাঁহার করাল, বিভীষিকাময়ী, মৃত্যুর ছায়ার ন্যায় সর্বগ্রাসী মূর্তি দেখান নাই – তাঁহার অবিদ্যারূপিণী মোহিনী মূর্তির ফাঁদে তো কখনো ফেলেন নাই – কাজেই গোসাঁইজীর নিকট পুরুষকার ও চেষ্টাসহায়ে অগ্রসর হইয়া নির্বিকল্প-সমাধিলাভ, ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান সব সোজা কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে পথে অগ্রসর হইবার যত কিছু বিঘ্ন-বাধা, মা যে সে-সব নিজ হস্তে সরাইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন – এ কথা তিনি বুঝিবেন কিরূপে? এতদিনে সে বিষয় পুরী স্বামীজীকে বুঝাইবার জগদম্বার ইচ্ছা হইল। এতদিনে তিনি মনের ঐ ভ্রম বুঝিবার অবসর পাইলেন।
তোতাপুরীর অসুস্থতা
পুরীজীর পশ্চিমী শরীর; রোগ, অজীর্ণ, শরীরে শতপ্রকার অসুস্থতা কাহাকে বলে তাহা কখনো জানিতেন না। যাহা খাইতেন, তাহাই হজম হইত; যেখানেই পড়িয়া থাকিতেন, সুনিদ্রার অভাব হইত না। আর ঈশ্বর-জ্ঞানে ও দর্শনে মনের উল্লাস ও শান্তি শতমুখে অবিরামধারে মনে প্রবাহিত থাকিত। কিন্তু বাঙলার জল, বাঙলার বাষ্পকণাপূরিত গুরুভার উত্তপ্ত বায়ুতে, ঠাকুরের শ্রদ্ধাভালবাসায় মোহিত হইয়া কয়েক মাস বাস করিতে না করিতেই সে দৃঢ় শরীরে রোগ প্রবেশ করিল। পুরীজী কঠিন রক্তামাশয়-রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। দিবারাত্র পেটের মোচড় ও টনটনানিতে পুরীজীর ধীর, স্থির, সমাধিস্থ মনও অনেক সময়ে ব্রহ্মসদ্ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া শরীরের দিকে আসিয়া পড়িতে লাগিল! ‘পঞ্চ ভূতের ফাঁদে’ ব্রহ্ম পড়িয়াছেন, এখন সর্বেশ্বরী জগদম্বিকার কৃপা ব্যতীত আর উপায় কি?
তোতার নিজ মনের সঙ্কেত অগ্রাহ্য করা
অসুস্থ হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাঁহার সতর্ক ব্রহ্মনিষ্ঠ মন তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে, এখানে শরীর ভাল থাকিতেছে না, আর এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু ঠাকুরের অদ্ভুত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শরীরের মায়ায় তিনি চলিয়া যাইবেন? ‘শরীর – হাড়-মাসের খাঁচা’ – রসরক্তপূর্ণ, কৃমিকুলসঙ্কুল, দুই দিন মাত্র স্থায়ী দেহ – যেটার অস্তিত্বই বেদান্তশাস্ত্রে ভ্রম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতি মমতাদৃষ্টি করিয়া তিনি কিনা অশেষ-আনন্দ-প্রসূ এই দেব-মানবের সঙ্গ সহসা ত্যাগ করিয়া যাইবেন? যেখানে যাইবেন সেখানেও শরীরের রোগাদি তো হইতে পারে? আর রোগাদি হইলেই বা তাঁহার ভয় কি? শরীরটাই ভুগিবে, কৃশ হইবে, বড় জোর বিনষ্ট হইবে – তাহাতে তাঁহার কি আসে যায়? তিনি তো প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন, দেখিয়াছেন – তিনি অসঙ্গ নির্বিকার আত্মা, শরীরটার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই – তবে আবার ভয় কিসের? এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া পুরীজী মনকে ব্যস্ত হইতে দেন নাই।
তোতার ঠাকুরের নিকট বিদায় লইতে যাইয়াও না পারা ও রোগবৃদ্ধি
ক্রমে রোগের যখন সূত্রপাত ও কিছু কিছু যন্ত্রণার আরম্ভ হইল, তখন পুরীজীর স্থানত্যাগের ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে প্রবলতর হইতে লাগিল। ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় লইবেন ভাবিয়া কখনো কখনো তাঁহার নিকট উপস্থিতও হইলেন, কিন্তু অন্য সৎপ্রসঙ্গে মাতিয়া সে কথা বলিতে ভুলিয়াই যাইলেন। আবার যদি বা বিদায়ের কথা বলিতে মনে পড়িল তো তখন যেন কে ভিতর হইতে তাঁহার সে সময়ের জন্য বাক্য রুদ্ধ করিয়া দিল, বলিতে বাধ বাধ করায় পুরীজী ভাবিলেন, ‘আজ থাক, কাল বলা যাইবে’। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজী ঠাকুরের সহিত বেদান্তালাপ করিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া পঞ্চবটীতলে আসনে ফিরিলেন। দিন কাটিতে লাগিল। স্বামীজীর শরীরও অধিকতর দুর্বল এবং ক্রমে রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর স্বামীজীর শরীর ঐ প্রকার দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বিশেষ পথ্য ও সামান্য ঔষধাদি-সেবনের বন্দোবস্ত ইতঃপূর্বেই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও ফলোদয় না হইয়া রোগ বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। ঠাকুরও মথুরকে বলিয়া তাঁহার আরোগ্যের জন্য ঔষধপথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য সেবা-যত্ন করিতে লাগিলেন। এখনো পর্যন্ত স্বামীজী শরীরেই বিশেষ যন্ত্রণানুভব করিতেছিলেন, কিন্তু চিরনিয়মিত মনকে ইচ্ছামাত্রেই সমাধিমগ্ন করিয়া দেহের সকল যন্ত্রণার কথা এককালে ভুলিয়া শান্তিলাভ করিতেছিলেন।
মনকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া তোতার গঙ্গায় শরীর বিসর্জন করিতে যাওয়া ও বিশ্বরূপিণী জগদম্বার দর্শন
রাত্রিকাল – আজ পেটের যন্ত্রণা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বামীজীকে স্থির হইয়া শয়ন পর্যন্ত করিয়া থাকিতে দিতেছে না। একটু শয়ন করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াই তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন। বসিয়াও সোয়াস্তি নাই। ভাবিলেন, মনকে ধ্যানমগ্ন করিয়া রাখি, শরীরে যাহা হইবার হউক। মনকে গুটাইয়া শরীর হইতে টানিয়া লইয়া স্থির করিতে না করিতে পেটের যন্ত্রণায় মন সেই দিকেই ছুটিয়া চলিল। আবার চেষ্টা করিলেন, আবার তদ্রূপ হইল। যেখানে শরীর ভুল হইয়া যায়, সেই সমাধিভূমিতে মন উঠিতে না উঠিতে যন্ত্রণায় নামিয়া পড়িতে লাগিল। যতবার চেষ্টা করিলেন, ততবারই চেষ্টা বিফল হইল! তখন স্বামীজী নিজের শরীরের উপর বিষম বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন – এ হাড়-মাসের খাঁচাটার জ্বালায় মনও আজ আমার বশে নাই। দূর হোক, জানিয়াছি তো শরীরটা কোনমতেই আমি নই, তবে এ পচা শরীরটার সঙ্গে আর কেন থাকিয়া যন্ত্রণা অনুভব করি? এটা আর রাখিয়া লাভ কি? এই গভীর রাত্রিকালে গঙ্গায় এটাকে বিসর্জন দিয়া এখনি সকল যন্ত্রণার অবসান করিব। এই ভাবিয়া ‘ল্যাংটা’ বিশেষ যত্নে মনকে ব্রহ্মচিন্তায় স্থির রাখিয়া ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে গভীর জলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু গভীর ভাগীরথী কি আজ সত্য সত্যই শুষ্কা হইয়াছেন? অথবা তোতা তাঁহার মনের ভিতরের ছবির বহিঃপ্রকাশে ঐরূপ দেখিতেছেন? কে বলিবে? তোতা প্রায় পরপারে চলিয়া আসিলেন, তত্রাচ ডুবজল পাইলেন না! ক্রমে যখন রাত্রির অন্ধকারে অপর পারের বৃক্ষ ও বাটীসকল ছায়ার মতো নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন তোতা অবাক হইয়া ভাবিলেন, ‘একি দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার পর্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই! একি ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা!’ অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল! তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল – মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা; জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি – সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই – মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা – তুরীয়া, নির্গুণা মা! এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা! শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী-মূর্তিতে অবস্থিত – ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ!
তোতার পূর্বসংকল্প-ত্যাগ
গভীর নিশীথে তোতা ভক্তিপূরিত চিত্তে জগদম্বার অচিন্ত্য অব্যক্ত বিরাট রূপের দর্শন করিতে করিতে, গম্ভীর অম্বারবে দিকসকল মুখরিত করিয়া তুলিলেন এবং আপনাকে তৎপদে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়া পুনরায় যেমন আসিয়াছিলেন, তেমন জল ভাঙিয়া ফিরিয়া চলিলেন! শরীরে যন্ত্রণা হইলেও এখন আর তাহার অনুভব নাই। প্রাণ সমাধি-স্মৃতির অপূর্ব উল্লাসে উল্লসিত! ধীরে ধীরে স্বামীজী পঞ্চবটীতলে ধুনির ধারে আসিয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি জগদম্বার নামে ও ধ্যানে কাটাইলেন!
অসুস্থতায় তোতার জ্ঞান – ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি এক
প্রভাত হইলেই ঠাকুর স্বামীজীর শারীরিক কুশল-সংবাদ জানিতে আসিয়া দেখেন, যেন সে মানুষই নয়! মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল, হাস্যপ্রস্ফুটিত অধর, শরীরে যেন কোন রোগই নাই! তোতা ঠাকুরকে ইঙ্গিতে পার্শ্বে বসিতে বলিয়া ধীরে ধীরে রাত্রের সকল ঘটনা বলিলেন। বলিলেন, রোগই আমার বন্ধুর কাজ করিয়াছে, কাল জগদম্বার দর্শন পাইয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্তও হইয়াছি। এতদিন আমি কি অজ্ঞই ছিলাম! যাহা হউক, তোমার মাকে এখন বলিয়া কহিয়া আমাকে এ স্থান হইতে যাইতে বিদায় দাও। আমি এখন বুঝিয়াছি, তিনিই আমাকে এই শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমাকে এখানে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। নতুবা আমি এখান হইতে অনেক কাল পূর্বে চলিয়া যাইব ভাবিয়াছি, বিদায় লইবার জন্য তোমার কাছেও বার বার গিয়াছি, কিন্তু কে যেন প্রতিবারেই বিদায়ের কথা বলিতে দেয় নাই! অন্য প্রসঙ্গে ভুলাইয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রাখিয়াছে! ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “মাকে যে আগে মানতে না, আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যা ‘ঝুট’ বলে তর্ক করতে? এখন দেখলে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচে গেল। আমাকে তিনি পূর্বেই বুঝিয়েছেন, ‘ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক নয়, তেমনি’!”
তোতার জগদম্বাকে মানা ও বিদায়গ্রহণ
অনন্তর প্রভাতী সুরে নহবত-ধ্বনি হইতেছে শুনিয়া শিবরামের ন্যায় গুরুশিষ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ উভয় মহাপুরুষ উঠিয়া জগদম্বার মন্দিরে দর্শনার্থ যাইলেন এবং শ্রীমূর্তির সম্মুখে প্রণত হইলেন। উভয়েই প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, মা তোতাকে এইবার এখান হইতে যাইতে প্রসন্ন মনে অনুমতি দিয়াছেন। ইহার কয়েক দিবস পরেই তোতা ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রওনা হইলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী ইহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ দর্শন – কারণ ইহার পর পুরী গোস্বামী আর কখনো এদিকে ফিরেন নাই।
তোতার ‘কিমিয়া’-বিদ্যায় অভিজ্ঞতা
আর একটি কথা বলিলেই তোতাপুরী সম্বন্ধে আমরা যত কথা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম, তাহার সকলই প্রায় পাঠককে বলা হয়। পুরী গোস্বামী ‘কিমিয়া’ বিদ্যায় বিশ্বাস করিতেন। শুধু যে বিশ্বাস করিতেন তাহা নহে, ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন তিনি ঐ বিদ্যাপ্রভাবে তাম্রাদি ধাতুকে অনেকবার স্বর্ণে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তোতা বলিতেন, তাঁহাদের মণ্ডলীর প্রাচীন পরমহংসেরা উক্ত বিদ্যা অবগত আছেন এবং গুরুপরম্পরায় তিনি উহা পাইয়াছেন। আরও বলিতেন, ‘ঐ বিদ্যাপ্রভাবে নিজের স্বার্থসাধন বা ভোগবিলাস করিতে একেবারে নিষেধ আছে, উহাতে গুরুর অভিসম্পাত আছে। তবে মণ্ডলীতে অনেক সাধু থাকে, উহাদের লইয়া কখনো কখনো মণ্ডলীশ্বরকে তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে গমনাগমন করিতে হয় এবং তাঁহাদের সকলের আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে হয়। গুরুর আদেশ – ঐ সময়ে অর্থের অনটন হইলে ঐ বিদ্যার প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের সেবার বন্দোবস্ত করিতে পার।’
উপসংহার
এইরূপে ঠাকুরের গুরুভাবসহায়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী নিজ নিজ গন্তব্য পথে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অন্যান্য শিক্ষাগুরুগণও যে তাঁহার সহায়ে এইরূপে আধ্যাত্মিক উদারতা লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ও আমরা ইহাতেই বেশ অনুমান করিতে পারি।
ওমিতি –
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-গুরুভাবপর্বে
পূর্বার্ধ সম্পূর্ণ॥ ওঁ॥


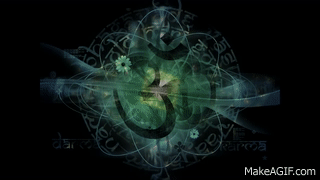




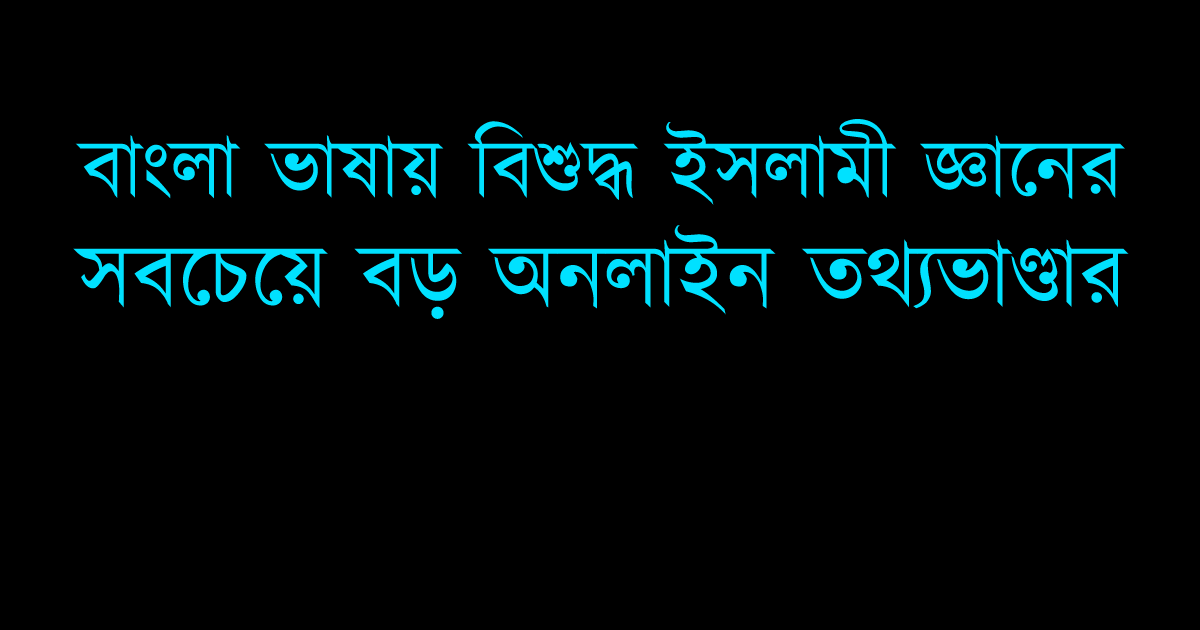

















No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ